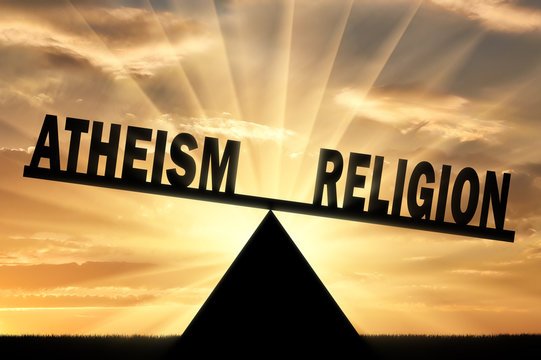লিখেছেনঃ হারুন ইয়াহিয়া
ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ বলে একটি কথা আছে। আমরা বর্তমানে তেমনি একটি সন্ধিক্ষণে (turning point) বাস করছি। কেউ একে বিশ্বায়ন বলছেন, কেউ বলছেন এটি ‘তথ্যযুগের’ সূচনা। এ-সবই সত্য। তবে এ-সময়ে আমরা আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করছি, যা তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। অনেকের অগোচরেই বিগত ২০-২৫ বছরে বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে পৃথিবী অনেক দূর এগিয়ে গেছে এবং এর ফলে নাস্তিকতাবাদ বা নিরীশ্বরবাদ-এর কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দেয়ার আয়োজন সম্পন্ন হতে চলেছে–অনেকটা অবধারিতভাবে।
একথা সত্য যে, নাস্তিকতাবাদের নিরীশ্বরবাদ তথা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করার ধারণা প্রাচীনকাল থেকেই মানবসমাজে ছিল। কিন্তু এর সত্যিকারের উত্থান শুরু হয়েছিল মূলত অষ্টাদশ শতাব্দিতে, ইউরোপে। ধর্মবিরোধী একদল চিন্তাবিদের দর্শনের ব্যাপক প্রসার ও মানবসমাজে এর রাজনৈতিক প্রভাব ওই উত্থানকে যুগিয়েছিল প্রয়োজনীয় পুষ্টি। ডিডেরট (Diderot) ও বেরন ডি হোলবাখ (Baron d’ Holbach)-এর মতো বস্তুবাদীরা তখন প্রচার করছিলেন যে, বিশ্বজগত হচ্ছে বস্তুর সমষ্টি এবং এ-জগত অনাদিকাল থেকেই অস্তিত্বশীল; বস্তুর বাইরে এ-জগতে আর কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। ঊনবিংশ শতাব্দিতে এসে নিরীশ্বরবাদ আরো প্রসার লাভ করে; মার্কস, এঙ্গেলস, নিৎসে, দুরখেইম, ফ্রয়েড প্রমুখ চিন্তাবিদরা বিজ্ঞান ও দর্শনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিরীশ্বরবাদী চিন্তা-ভাবনার প্রয়োগ করেন।
নিরীশ্বরবাদের পক্ষে সবচে বড় সমর্থনটি এসেছিল চার্লস ডারউইনের কাছ থেকে। তিনি সৃষ্টির ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং এর বিপরীতে পেশ করেন বিবর্তন তত্ত্ব (theory of evolution)। তার তত্ত্ব তথা ডারউইনবাদ আপাতদৃষ্টিতে এমন একটি প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক (?) উত্তর দিয়েছিল, যেটি যুগের পর যুগ ধরে নিরীশ্বরবাদী বা নাস্তিকদের বিব্রত করে এসেছে। প্রশ্নটি হচ্ছে: কীভাবে পৃথিবীতে মানুষ এবং অন্যান্য জীবিত বস্তুর আবির্ভাব ঘটেছে? ডারউইনের তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেক নিরীশ্বরবাদীই বিশ্বাস করতে ও তা প্রচার করতে শুরু করলেন যে, প্রকৃতিতে এমন একটা মেকানিজম (mechanism) ক্রিয়াশীল আছে যা জড় পদার্থের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করতে পারে এবং সে-মেকানিজমই–আল্লাহ নন–পুথিবীতে লক্ষ-কোটি বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী সৃষ্টি করেছে।
ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এসে নিরীশ্বরবাদীরা বিশ্বজগত সম্পর্কে এমন একটা ধারণা দিলেন যা–তাঁদের মতে–এ-জগতের সবকিছুকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। এ-বিশ্বজগতের সৃষ্টি হয়েছে–এ-সত্যকে তাঁরা মেনে নিতে অস্বীকার করলেন। তাঁরা ঘোষণা করলেন: বিশ্বজগতের কোনো শুরু নেই; এটি অনাদিকাল থেকেই অস্তিত্বশীল ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তাঁরা দাবী করে বসলেন যে, এ-জগতের কোনো লক্ষ্য নেই; এর চমৎকার শৃঙ্খলা এবং ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশের অস্তিত্বের বিষয়টি স্রেফ একটা ঘটনাচক্র মাত্র (অর্থাৎ এর পেছনে কোনো বুদ্ধিমান স্রষ্টার হাত নেই)। তাঁরা ডারউইনবাদের ওপর পূর্ণ ঈমান আনলেন বা বিশ্বাস স্থাপন করলেন। জগতে অসংখ্য প্রাণীর অস্তিত্বের ব্যাপারটি ডারউইনিজম দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব বলে তাঁরা ঘোষণা দিলেন। তাঁরা আরো বিশ্বাস করে বসলেন যে, নাস্তিক্যবাদী ধারণা-অনুমানের ওপর ভিত্তি করে মার্কস বা দুরখেইম (Durkheim) ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানকে এবং ফ্রয়েড মনোবিজ্ঞানকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছেন।
পরবর্তী কালে তথা বিংশ শতাব্দীতে এসে বিজ্ঞান প্রভূত উন্নতি সাধন করলো, আবিস্কৃত হলো নিত্যনতুন সত্য ও তত্ত্ব ; রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনও আলোকিত হলো নতুন ধারণা ও সত্যের আলোয়। এর ফলে নাস্তিক্যবাদী ধারণা ও বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত পড়লো। জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিদ্যা, মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণার ফলে বেরিয়ে-আসা সত্য, নিরীশ্বরবাদের র্ভিত্তিকে নড়বড়ে করে দিল।
জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির স্কলার প্যাট্রিক গ্লাইন (Patrick Glynn) তাঁর God: The Evidence, The Reconciliation of Faith and Reason in a Post-secular World -শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন:
‘‘প্রাথমিক পর্যায়ের আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ ও নাস্তিক চিন্তাবিদরা সৃষ্টিকর্তা তথা আল্লাহ সম্পর্কে যে-সব গুরুত্বপূর্ণ অনুমান ও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তার প্রায় সবগুলোই বিগত দুই দশকের গবেষণায় ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে, বিজ্ঞান এ-বিশ্বজগতকে আরো বেশী বিশৃঙ্খল ও যান্ত্রিক হিসেবে প্রমাণ করবে। কিন্তু বাস্তবে প্রমাণিত হলো ঠিক উল্টোটি–বিশ্বজগতে এক আশ্চর্য জটিল শৃঙ্খলা আবিষ্কার করলো বিজ্ঞান, যা এক অকল্পনীয় বিশাল পরিকল্পনা তথা পরিকল্পনাকারীর প্রতি সুষ্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, একসময় ধর্ম একটি স্নায়বিক রোগ হিসেবে চিহ্নিত হবে; কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, ধর্মীয় চেতনা মৌলিক মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে …
দৃশ্যত খুব কম লোকই বিষয়টি উপলব্দি করছে বলে মনে হয়; তবে বিজ্ঞান ও বিশ্বাসের মধ্যকার শতাব্দী-প্রাচীন বিতর্কের ফলাফল যে বিস্ময়কর, তা এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে যাবার কথা। ডারউইনের অব্যবহিত পরে হাক্সলি ও রাসেলের মতো নাস্তিক ও অজ্ঞেয়বাদীরা ‘দৈবক্রমে বিশ্বজগত ও পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টির তত্ত্ব’ তুলে ধরেছিলেন, যা অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্যও মনে হয়েছিল। আজও কোনো কোনো বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী এ-তত্ত্বকে আঁকড়ে ধরে আছেন। তাঁরা এ-তত্ত্বর পক্ষ অবলম্বন করতে যেয়ে অবাস্তব সব কথাবার্তা বলছেন বা বলতে বাধ্য হচ্ছেন। অথচ অত্যাধুনিক গবেষণা থেকে প্রাপ্ত বাস্তব ও গ্রহণযোগ্য উপাত্তসমূহ একজন সৃষ্টিকর্তা তথা আল্লাহর অস্তিত্বের অনিবার্যতাকেই প্রবলভাবে প্রকাশ করছে।’’নাস্তিক্যবাদী বা বস্তুবাদী দর্শনের ভিত্তি হিসেবে এতদিন অবাধে উপস্থাপন করা হতো বিজ্ঞানকে। বর্তমানে ঠিক উল্টোটাই ঘটছে। জেরাল্ড শ্রোয়েডার (Gerald Shroeder)-এর The Hidden Face of God গ্রন্থের ওপর লেখা এক পর্যালোচনামূলক নিবন্ধে ব্রাইস ক্রিস্টেনসেন (Bryce Christensen) লিখেছেন: “গবেষণাগার থেকে ও বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে বস্তুবাদ অক্ষম।”
যা হোক, এ-ইস্যুতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যে-সব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, সে-সব সংক্ষেপে আমরা এখানে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করবো এবং আসন্ন ‘নাস্তিকতা-পরবর্তী’ যুগ মানবজাতির জন্য কী বয়ে আনবে বা আনতে পারে, তা-ও এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করবো:-
বিশ্বতত্ত্ব : ‘বিশ্বজগত অনাদি ও অনন্ত’–এ-ধারণার অসারতা
বিংশ শতাব্দীতে নিরীশ্বরবাদের ওপর প্রথম আঘাতটি আসে বিজ্ঞানের বিশ্বতত্ত্ব (cosmology) নামক শাখা থেকে। এ-বিশ্বজগতের কোনো শুরু নেই, এটি অনাদিকাল থেকে অস্তিত্বশীল ছিল এবং অনন্তকাল পর্যন্ত থাকবে–এ ধারণা এ-সময় মিথ্যা প্রমাণিত হয়; আবিষ্কৃত হয়–এ-বিশ্বজগতের একটা শুরু ছিল। সোজাভাবে বললে, এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয় যে, এ-বিশ্বজগত শূন্য থেকে (from nothing) সৃষ্টি করা হয়েছে।
অনাদি ও অনন্ত বিশ্বজগতের ধারণা পাশ্চাত্যে এসেছিল বস্তুবাদী দর্শনের কাঁধে ভর করে। প্রাচীন গ্রীসে এ-দর্শনের জন্ম। এ-দর্শন অনুসারে: এ-বিশ্বজগত অনাদিকাল থেকে চলে আসছে ও অনন্তকাল পর্যন্ত চলবে এবং বস্তুর বাইরে এ-বিশ্বজগতে অন্য কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। যেহেতু মধ্যযুগে পাশ্চাত্যে চার্চের দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল, বস্তুবাদ সেখানে তখন ততটা পাত্তা পায়নি। আধুনিক যুগে এসে পশ্চিমা বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা গ্রীক দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং এর ফলে বস্তুবাদ আবার পাদ-প্রদীপে চলে আসে।
বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট ((Immanual Kant) ‘বস্তুবাদী’ শব্দটির প্রচলিত অর্থে বস্তুবাদী ছিলেন না। অথচ আধুনিক যুগে তিনিই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি বিশ্বজগতকে বস্তুবাদের আলোকে ব্যাখ্যা করেন। কান্ট ঘোষণা করেন: এ-বিশ্বজগত অনাদি ও অনন্ত এবং কোনো কিছুই বিশ্বজগতের বাইরে নয়। ঊনবিংশ শতাব্দী যখন শুরু হলো, তখন ব্যাপকভাবে এ-ধারণা গৃহীত হয়ে গেছে যে, এ-বিশ্বজগতের কোনো শুরু নেই এবং একে সৃষ্টিও করা হয়নি। পরবর্তী কালে কার্ল মার্কস (Karl Marx) ও এঙ্গেলস (Friedrich Engels)-এর মতো দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীরা এ-ধারণাকে সমর্থন করেন এবং ধারণাটি বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেও কমবেশি গুরুত্ব পেতে থাকে।
অনাদি ও অনন্ত বিশ্বের ধারণা সবসময়ই নিরীশ্বরবাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। বিশ্বজগত কোনো এক সময় শুরু হয়েছিল–এ-ধারণা মেনে নেয়ার অর্থ একজন স্রষ্টাকে মেনে নেয়া। তাই–বৈজ্ঞানিক কোনো ভিত্তি না-থাকা সত্ত্বেও–দাবী করা হলো যে, বিশ্বজগত অনাদি ও অনন্ত। এ-দাবী যারা করতেন তাদের মধ্যে ছিলেন জর্জেস পলিটজার (Georges Politzer)-ও। তিনি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে Principes Fondamentaux de Philosophie (The Fundamental Principles of Philosophy)-নামক গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে বস্তুবাদ ও মার্কসবাদের একজন গোড়া সমর্থক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। অনাদি ও অনন্ত বিশ্বজগতের ধারণাকে অকাট্য মেনে নিয়ে তিনি সৃষ্টির ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি লেখেন: “বিশ্বজগত কোনো সৃষ্ট বস্তু নয়। এটি সৃষ্ট হলে অবশ্যই একে শূন্য থেকে তাৎক্ষণিকভাবে একজন স্রষ্টা কর্তৃক সৃষ্ট হতে হতো। সৃষ্টির ধারণা মেনে নিতে হলে এ-কথাও মেনে নিতে হয় যে, এমন একটা সময় ছিল যখন বিশ্বজগতের অস্তিত্ব ছিল না এবং আরো মেনে নিতে হয় যে, শূন্য থেকে কোনো কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব। অথচ এটি এমন এক কথা যা বিজ্ঞান মেনে নিতে পারে না।”
সৃষ্টির ধারণার বিরুদ্ধে এবং অনাদি ও অনন্ত বিশ্বজগতের ধারণার পক্ষে অবস্থান নিয়ে পলিটজার ভেবেছিলেন, বিজ্ঞান তাঁর পক্ষে আছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল বিজ্ঞান তাঁর পক্ষে নেই। সহসাই বিজ্ঞান আবিষ্কার করলো, বিশ্বজগতের একটা শুরু ছিল। আর বিশ্বজগতের শুরু যখন আছে, তখন–পলিটজারের বিচারেই–একজন স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার না-করে উপায় থাকে না।
বিশ্বজগত যে অনাদি নয়, এক সময় যে এটি শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছিল–এ-সত্য জানা যায় ‘বিগ ব্যাং’ (Big Bang) তত্ত্বের আবিষ্কারের ফলে। বিংশ শতাব্দীর সম্ভবত সবচে’ গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার এটি। বস্তুত, একাধারে অনেকগুলো আবিষ্কারের ফসল হিসেবে বিগ ব্যাং তত্ত্বের জন্ম। ১৯২৯ সালে আমেরিকার জ্যোতির্বিদ এডউইন হাবল (Edwin Hubble) লক্ষ্য করেন যে, বিশ্বজগতের গ্যালাক্সিগুলো পরস্পর থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। অন্যভাবে বললে, তিনি আবিষ্কার করলেন, বিশ্বজগত ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে। এ-আবিষ্কার সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য করলো। সিদ্ধান্তটি হলো: এ-বিশ্বজগত সৃষ্টি হয়েছে একটি একক পয়েন্ট (single point) থেকে। জ্যোতির্বিদরা হাবলের আবিষ্কারের সারবত্তা পরীক্ষা করতে যেয়ে আবিষ্কার করলেন আরেকটি সত্য। সত্যটি হচ্ছে : বিশ্বজগত যে-একক পয়েন্ট বা বিন্দু থেকে সৃষ্টি হয়েছে, সেটির মাধ্যাকর্ষণশক্তি ছিল অসীম এবং ভর (mass) ছিল শূন্য; আর এই ভরহীন পয়েন্টে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলেই বস্তু ও সময় অস্তিত্বলাভ করে এবং সৃষ্টি হয় সম্প্রসারণশীল (expanding) এ-বিশ্বজগতের। অন্যভাবে বললে, এ-বিশ্বজগত সৃষ্টি হয়েছে শূন্য (nothing) থেকে।
বিগ ব্যাং বা ‘মহা-বিস্ফোরণ তত্ত্ব’ আবিষ্কৃত হলেও, অনেক জ্যোতির্বিদই একে সত্য বলে মেনে নিতে অস্বীকার করলেন এবং অনাদি বিশ্বজগতের পুরনো বিশ্বাসই আঁকড়ে ধরে থাকলেন। এ-গোড়ামীর কারণ খুজে পাওয়া যাবে বিখ্যাত বস্তুবাদী পদার্থবিদ আর্থার এডিংটনের (Arthur Eddington) বক্তব্যে। তিনি বলেছিলেন: “বর্তমানে আমরা যে-প্রকৃতি দেখছি, সেটি একসময় আকষ্মিকভাবে অস্তিত্বলাভ করতে শুরু করেছিল–এ-ধারণা আমার কাছে ফিলসফিক্যালি (philosophically) অগ্রহণযোগ্য।” বস্তুবাদীদের কাছে অগ্রহণযোগ্য হলেও, বিগ ব্যাং তত্ত্ব কিন্তু পরবর্তী কালে বিভিন্ন সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা সত্য প্রমাণিত হতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে আরনো পেনজিয়াস (Arno Penzias) ও রবার্ট উইলসন (Robert Wilson) নামক দুজন বিজ্ঞানী মহা-বিস্ফোরণের (Big Bang) তেজষ্ক্রিয় অবশেষ (radioactive remains) চিহ্নিত করেন। নব্বই-এর দশকে কোবে (COBE, Cosmic Background Explorer) স্যাটেলাইট বিজ্ঞানী দুজনের পর্যবেক্ষণের সত্যতা প্রমাণ করে।
এসব সত্য আবিষ্কারের ফলে কোনঠাসা হয়ে পড়ে নাস্তিকরা। প্রসঙ্গক্রমে, ‘Atheistic Humanism’-এর লেখক ও University of Reading-এর দর্শনের নাস্তিক অধ্যাপক এন্থনি ফ্লিউ (Anthony Flew)-এর আগ্রহউদ্দীপক স্বীকারোক্তির কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলছেন: “
স্বীকারোক্তি আত্মার জন্য ভালো বলে কুখ্যাতি আছে। আমি স্বীকার করছি যে, সৃষ্টিতত্ত্বসংক্রান্ত সমকালীন সর্বসম্মত মত নাস্তিকদের ভালোরকম বিব্রত করবে। কারণ, বিশ্বজগতের একটা শুরু ছিল–এ-কথাটা St. Thomas–এর মতে ফিলসফিক্যালি প্রমাণ করা সম্ভব না-হলেও, দেখা যাচ্ছে, সৃষ্টিতত্ত্ববিদরা এর সপক্ষে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ঠিকই হাজির করছেন। …(বিশ্বজগতের কোনো শুরু বা শেষ নেই–এ ধারণাটা ) যদিও আমি এখনো সঠিক বলেই বিশ্বাস করি, তথাপি বলতেই হচ্ছে যে, বিগ ব্যাং তত্ত্বের উপস্থিতিতে ওই বিশ্বাসের ওপর স্থির থাকা মোটেই সহজ ও স্বস্তিদায়ক ব্যাপার নয়।”
বিগ ব্যাং তত্ত্বের বিরুদ্ধে নাস্তিকদের ক্ষোভ প্রকাশ করার আরো উদাহরণ আছে। ১৯৮৯ সালে লিখিত এক নিবন্ধে বিখ্যাত বস্তবাদী বিজ্ঞান জার্নাল Nature-এর নিরীশ্বরবাদী সম্পাদক জন মেডক্স (John Maddox) এ-তত্ত্বের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। ‘বিগ ব্যাং নিপাত যাক’-শীর্ষক ওই নিবন্ধে মেডক্স লিখেছেন যে, বিগ ব্যাং ‘ফিলসফিক্যালি অগ্রহণযোগ্য’। তিনি আরো ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, বিগ ব্যাং তত্ত্ব পরবর্তী দশকে টিকে থাকবে এমন সম্ভাবনা কম। বলা বাহুল্য, মেডক্সের ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক প্রমাণিত হয়নি, বরং উল্টো এ-তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা পরবর্তী দশকে আরো বেড়েছে এবং অনেক আবিষ্কারই বিশ্বজগত সৃষ্টির ধারণার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে।
অবশ্য কোনো কোনো বস্তুবাদী মনীষী এ-ব্যাপারে তুলনামূলকভাবে যৌক্তিক হতে চেয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, ইংরেজ বস্তুবাদী পদার্থবিদ এইচ পি লিপসন-এর (H.P.Lipson) কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। এই বিজ্ঞানী, অনিচ্ছা সত্তেও, সৃষ্টিসম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক সত্যকে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন: “আমি মনে করি … আমাদের অবশ্যই … স্বীকার করতে হবে যে, সৃষ্টির ধারণা এ-ক্ষেত্রে একমাত্র ধারণা যা গ্রহণ করা যেতে পারে। এটা মেনে নেয়া আমার মতো অন্য পদার্থবিদদের জন্যও কঠিন। কিন্তু গবেষণালব্ধ প্রমাণাদি যখন একে সমর্থন করে, তখন তা স্বীকার না-করে উপায়ই বা কী?” (দেখুন, H.P.Lipson, “A Physicist Looks at Evolution”, Physics Bulletin, vol.138, 1980, p.241)।
মোদ্দাকথা, আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা চূড়ান্তভাবে যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, তা হচ্ছে: সময় (time) ও বস্তুর (matter) প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন থেকে অসীম ক্ষমতাধর একজন স্রষ্টা-ই ও-দুটোকে সৃষ্টি করেছেন। যে অনন্ত শক্তি বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন, তিনি-ই হলেন আল্লাহ–যিনি অফুরন্ত ক্ষমতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী।
পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যা: বিশ্বজগত এমনি এমনি সৃষ্টি হয়নি
নিরীশ্বরবাদের পক্ষে আরো একটি প্রচলিত ধারণা কাজ করছিল। ধারণাটি হলো: এ-পৃথিবীর সব পদার্থ এবং আসমানের সব বস্তু ও গ্রহ-নক্ষত্র হঠাৎ করে এমনি এমনি বা দৈবক্রমে (by chance) সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি, বিশ্বজগতে আমরা যে-সব প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন দেখতে পাই, সেগুলো সৃষ্টির পেছনেও কোনো পরিকল্পনা ছিল না, ছিল না কোনো পরিকল্পনাকারীর হাত। ওগুলোও সৃষ্টি হয়েছে দৈবক্রমে। বলা বাহুল্য, বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের জ্যোতির্বিদ্যা শাখায় আবিষ্কৃত বিভিন্ন সত্য এ-ধারণাকেও নাটকীয়ভাবে বাতিল করে দিয়েছে।
বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে এসে বিজ্ঞানীরা স্বীকার করতে শুরু করলেন যে, বিশ্বজগতে যে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিরাজ করছে, তা মানবজীবনের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় এবং এ-ভারসাম্য অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে স্থাপন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে গবেষণা এগিয়ে চললো এবং একসময় আবিষ্কৃত হলো: বিশ্বজগতের বিভিন্ন ভৌত, রাসায়নিক ও জীববৈজ্ঞানিক নিয়মসমুহ; মাধ্যাকর্ষণশক্তি ও ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিজম; অণুুর গঠনশৈলী ইত্যাদি সবকিছুই এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যেভাবে সৃষ্টি করার ওপর মানবজীবনের অস্তিত্ব নির্ভর করে। এ যেন একটি পরিকল্পিত নকশা! প্রাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা এ অসাধারণ নকশা বা ডিজাইনের নাম দিয়েছেন ‘এ্যানথ্রপিক প্রিন্সিপল’ (anthropic principle)। সোজা কথায়, উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে নয়, বরং মানবজীবনকে মাথায় রেখেই বিশ্বজগতের সবকিছু ডিজাইন করা হয়েছে ।
এ বিশ্বজগত যে দৈবক্রমে ও উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সৃষ্টি করা হয়নি, বরং পরিকল্পিতভাবে ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, নিুলিখিত বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত তথ্যসমুহ সে-কথাই প্রমাণ করে:-
১. মহাবিস্ফোরণের (Big Bang) পরমুহূর্ত থেকে বিশ্বজগত সম্প্রসারিত হতে শুরু করেছিল ঠিক সেই গতিতে, যেই গতিতে সম্প্রসারিত হওয়া ছিল অত্যাবশ্যকীয়। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন যে, যদি ওই গতিবেগ কোটি কোটি (billion billion) ভাগের একভাগও কমবেশী হতো তবে বিশ্বজগত আজকের অবস্থানে কখনও পৌঁছুতে পারতো না। অন্যভাবে বললে, বিশ্বজগত সৃষ্টির শুরুই হয়েছিল কল্পনাতীত সূক্ষ্ম হিসেব-নিকেশের ওপর ভিত্তি করে।‘
২. বিশ্বজগতে চার ধরণের প্রাকৃতিক শক্তি (physical forces) ক্রীয়াশীল আছে। এগুলো হলো: মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, দূর্র্র্বল পারমাণবিক শক্তি, শক্তিশালী পারমাণবিক শক্তি, ও ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক শক্তি। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন যে, এই শক্তিগুলো সুশৃঙ্খল বিশ্ব ও সে-বিশ্বে জীবনের অস্তিত্ব লাভের স্বার্থে ঠিকঠিক মাত্রায় বিরাজ করছে। কোনো এক বা একাধিক শক্তির মাত্রা যদি কোটি কোটি কোটি কোটি (billion billion billion billion) ভাগের একভাগও কমবেশী হতো তবে বিশ্বজগতে বিচ্ছুরিত রশ্মি (radiation) অথবা হাইড্রোজেন গ্যাস ছাড়া আর কিছুই থাকতো না । বলাবাহুল্য, তেমন ধারা এক বিশ্বে প্রাণের অস্তিত্বও থাকতো না বা থাকতে পারতো না ।
৩. বিশ্বজগতে এমন অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় আছে যা পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্বকে সম্ভব করে তুলেছে। সূর্যের আয়তন এবং পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব ; পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ ; সূর্য-রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য (wave-length); পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে বিভিন্ন গ্যাসের নিখুঁত আনুপাতিক হার; পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্র (magnetic field)–ইত্যাদি সবকিছু পৃথিবীতে মানুষের জীবনের সহায়ক করে সৃষ্টি করা হয়েছে।
মোদ্দাকথা, বিশ্বজগতের সর্বত্র বিরাজ করছে এক ধরনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভারসাম্য। এটি আধুনিক নভোবস্তুবিদ্যার (astrophysics) একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। বিখ্যাত জ্যোতির্বেত্তা পল ডেভিস (Paul Davies) তাঁর দি কসমিক ব্লুপ্রিন্ট (The Cosmic Blueprint)–শীর্ষক গ্রন্থের শেষ অনুচছদে লিখেছেন: “The impression of Design is overwhelming.” অর্থাৎ বিশ্বজগতে একটি পরিকল্পিত ডিজাইনের প্রভাব অপরিসীম।
অন্যদিকে, বিজ্ঞানবিষয়ক জার্নাল নেচার (Nature)-এ লিখিত এক নিবন্ধে নভোবস্তুবিজ্ঞানী ডব্লিউ প্রেস (W. Press) লিখেছেন: “…বিশ্বজগতে একটি চমৎকার ডিজাইনের অস্তিত্ব লক্ষ্যণীয়। এ ডিজাইন (পৃথিবীতে) বুদ্ধিমান প্রাণী সৃষ্টির জন্য সম্পূর্ণ সহায়ক।”
মজার ব্যাপার হচেছ, যে-সব বিজ্ঞানী এ তথ্যসমূহ আবিষ্কার করেছেন, তাঁদের অধিকাংশই বস্তুবাদী চিন্তা-ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন এবং অনিচছাসত্ত্বেও এসব তথ্য তুলে ধরতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁরা নিশ্চয়ই স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করার নিমিত্ত গবেষণা করেন নাই! কিন্তু তাঁদের গবেষণা এবং গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলই প্রমাণ করছে যে, এ-বিশ্বজগত একটি অনন্য পরিকল্পনার ফসল এবং এর জন্য একজন মহাপরিকল্পনাকারীর অস্তিত্ব থাকাও প্রয়োজন। দা সিমবায়োটিক ইউনিভার্স (The Symbiotic Universe)-শীর্ষক গ্রন্থে মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী জর্জ গ্রীনস্টেইন (George Greenstein) বলছেন: “(জীবনের সঙ্গে পদার্থবিদ্যার সূত্রসমূহের সঙ্গতিপূর্ণ সম্পর্কের ব্যাপারটি) কীভাবে ব্যাখ্যা করা চলে?… প্রাপ্ত সম্ভাব্য সকল তথ্য-প্রমাণ বিচার-বিশ্লেষণ করলে তাৎক্ষণিকভাবে মনে হয় যে, কিছু অতিপ্রাকৃতিক এজেন্সী–বা সঠিকভাবে বললে, একটি এজেন্সী–(বিশ্বজগত সৃষ্টির পেছনে) ক্রীয়াশীল আছে। এটা কি সম্ভব যে, ইচ্ছায় নয় বরং হঠাৎ করেই আমরা এমনসব বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণের সম্মুখীন হয়েছি যেগুলো একজন সর্বোচচ সত্তার (Supreme Being) অস্তিত্ব প্রমাণ করে ? আমাদের সুবিধার্থে এ-বিশ্বজগত অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে সৃষ্টি করেছেন কি তবে আল্লাহ-ই ?”
‘এটা কি সম্ভব’–শব্দগুচছ ব্যবহার করে গ্রীনস্টেইন–যিনি নিজে একজন নাস্তিক–সহজ সত্যকে উপেক্ষা করতে চেয়েছেন। অবশ্য অনেক বিজ্ঞানী এ-সত্যকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা না-করে বরং উদার মনে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, এ-বিশ্বজগত বিশেষভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে মানবজীবনের জন্য। আর তাই আজকাল বস্তুবাদকে একটি ত্র“টিপূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ধারণা হিসেবে দেখা হয় । আমেরিকার প্রজননবিদ্যা বিশেষজ্ঞ (geneticist) রবার্ট গ্রিফিথস (Robert Griffiths) এ-সত্যকে মেনে নিয়েছেন। তিনি বলছেন: “বিতর্কের জন্য আমার যখন একজন নাস্তিকের প্রয়োজন পড়ে তখন আমি দর্শন বিভাগে যাই। পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ এ-ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করে না ।”–((Hugh Ross, The Creator and the Cosmos, পৃষ্ঠা-১২৩)।
নেচারস ডেস্টিনি: হাও দা লজ অব বায়োলজী রিভিল পারপাস ইন দা ইউনিভার্স (Nature’s Destiny: How the Laws of Biology Reveal Purpose in the Universe)-শীর্ষক গ্রন্থে বিশ্বখ্যাত মলিকিউলার বায়োলজিষ্ট (molecular biologist) মিখায়েল ডেনটন (Michael Denton) ভৌত, রাসায়নিক ও জীববিজ্ঞানসংক্রান্ত সূত্রসমূহ আলোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন কীভাবে এগুলোকে মানবজীবনের প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী করে নিখুঁতভাবে হিসেব-নিকেশ করার পর অস্তিত্বশীল করা হয়েছে। তিনি তাঁর গ্রন্থের একস্থানে লিখেছেন: “বিগত চার শতাব্দী ধরে বৈজ্ঞানিক পরিমন্ডলে এ-ধারণা প্রচলিত ছিল যে, বিশ্বজগতে জীবন হচেছ একটি প্রান্তস্থ (peripheral) এবং ঘটনাচক্রগত (contingent) জিনিস। বিংশ শতাব্দীর জ্যোতির্বিদ্যা সে-ধারণার প্রতি নাটকীয়ভাবে ছুড়ে দিয়েছে চ্যালেঞ্জ।”
সংক্ষেপে বললে, উদ্দেশ্যহীন এলোমেলো (random) বিশ্বজগতের ধারণা–যা কিনা সম্ভবত নাস্তিকতাবাদের সবচেয়ে শক্তিশালী স্তম্ভ ছিল–ইতিমধ্যে বাতিল হয়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা এখন প্রকাশ্যে বস্তুবাদের পতনের কথা বলছেন (দেখুন, Paul Davies and John Gribbin, The Matter Myth, পৃষ্ঠা-১০) । আর কুরআন বলছে: “আমরা আসমান ও জমিন এবং উভয়ের মাঝখানের সবকিছু অকারণে সৃষ্টি করি নাই্ । অবিশ্বাসীরাই কেবল (অকারণে সৃষ্টির) ধারণা পোষণ করে …”–(কুরআন, ৩৮:২৭)। উল্লেখ্য, কুরআনের বক্তব্যের সঙ্গে বিজ্ঞান একমত হয়েছে কুরআন নাজেলের অনেক পরে–বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে এসে।
কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা এবং দৈব জ্ঞানের (divine wisdom) অস্তিত্ব আবিস্কার
কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা আধুনিক বিজ্ঞানের একটি অন্যতম শাখা। এ-শাখায় আবিস্কৃত তথ্য ও তত্ত্বসমূহ বস্তুবাদের অসারতা প্রমাণ করে এবং আস্তিকতাবাদের (theism) পক্ষে অবস্থান নেয়।
বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ নিয়ে কাজ করে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা । স্কুলের প্রত্যেক শিক্ষার্থী জানে যে, পদার্থ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণু দ্বারা গঠিত। পরমাণু আবার গঠিত একটি নিউক্লিয়াস ও সে-নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান কয়েকটি ইলেক্ট্রনের সমন্বয়ে। অবাক হবার মতো তথ্য হচেছ, ওসব উপাদান পরমাণুর মাত্র ০.০০০১ শতাংশ জায়গা দখল করে । অন্যভাবে বললে, প্রতিটি পরমাণুর ৯৯.৯৯৯৯ শতাংশই খালি বা শূণ্য!
ঘটনা এখানেই শেষ নয়। পরমাণুর নিউক্লিয়াস ও ইলেক্ট্রনগুলোকে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, ওগুলো ক্ষুদ্রতর উপাদান দিয়ে গঠিত। বিজ্ঞানীরা সে-উপাদানগুলোর নাম দিয়েছেন ‘কোয়ার্ক’ (Quarks)। আর কোয়ার্কগুলো বস্তুর সঠিক অর্থে বস্তু নয়, বরং এগুলো হচেছ ‘শক্তি’। এ-আবিষ্কারের ফলে বস্তু ও শক্তির মধ্যে পার্থক্য থাকার যে-ধারণাটি পূর্ব হতে চলে আসছিল, তা অসার বলে প্রমাণিত হলো। এ-আবিষ্কারের ফলে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, বস্তুজগতে আসলে শক্তির উপস্থিতিই সত্য। আরও স্পষ্টভাবে বললে, আমরা যাকে ‘বস্তু’ বলি সেটি আসলে জমাটবাঁধা (frozen) শক্তি ব্যতিত আর কিছু নয়। এক্ষেত্রে ঔৎসুক্য-জাগানো সত্য হচেছ: কোয়ার্কগুলো এমনভাবে কাজ করে যা পর্যবেক্ষণ করলে যে-কেউ এগুলোকে চেতনাসম্পন্ন বলে মনে করতে পারে। পদার্থবিজ্ঞানী ফ্রিম্যান ডাইসন (Freeman Dyson) টেমপ্লেটন প্রাইজ (Templeton Prize) গ্রহণকালে বলেছিলেন: “পরমাণু বড় রহস্যময় জিনিস। এগুলো নিষ্ক্রিয় বস্তুর মতো নয়, বরং সক্রিয় এজেন্টের মতো আচরণ করে।… মনে হয়, জন্মগতভাবেই ওগুলো একধরনের মন-এর অধিকারী।”–(Gerald Schroeder, The Hidden Face of God, পৃষ্ঠা-৭)।
সহজ করে বললে, বস্তুর অস্তিত্বের পশ্চাতে কাজ করছে তথ্য। আর তথ্য বস্তুজগত অস্তিত্বশীল হবার পূর্ব থেকেই অস্তিত্বশীল ছিল । এ-বিষয়ে জ্যারাল্ড শ্রোয়েডার বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। জ্যারাল্ড এমআইটি-তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন বিজ্ঞানী। তিনি পদার্থবিদ্যা ও জীববিদ্যা–উভয় বিষয় নিয়েই কাজ করেছেন এবং তিনি দ্যা সায়েন্স অব গড (The Science of God)-শীর্ষক বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা। যা হোক, তিনি তার দ্য হিডেন ফেস অব গড: সায়েন্স রিভিলস দ্য আলটিমেট ট্রুথ (২০০১) নামক গ্রন্থে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা হচেছ বস্তুজগতের পেছনে ক্রীয়াশীল বিশ্বজনীন জ্ঞানকে আবিষ্কারের একটি হাতিয়ার। তিনি বলেছেন: “…বস্তুর ভিত্তি হচেছ শক্তি এবং বস্তু আসলে জমাটবাঁধা শক্তি–এ সত্য আবিষ্কার করতে মানবজাতিকে অপেক্ষা করতে হয়েছে হাজার বছর, অপেক্ষা করতে হয়েছে একজন আইনষ্টাইনের জন্মের। আমরা হয়তো আরও একটু বেশী দেরীতে আবিষ্কার করবো যে, শক্তির চেয়েও অধিক মৌলিক কোনো অবস্তু-ই (non-thing) শক্তির ভিত্তি রচনা করেছে…।”–(The Hidden Face of God: Science Reveals the Ultimate Truth, পৃষ্ঠা-৮)।
প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও আইনস্টাইন এওয়ার্ড (Einstein Award) বিজয়ী জন আরকিবাল্ড (John Archibald) ওই একই সত্যকে ব্যাখ্যা করেছেন একটু অন্যভাবে। তিনি বলেছেন যে, তথ্য থেকেই বস্তুর সার অংশের উদ্ভব ঘটেছে।–(The Hidden Face of God: Science Reveals the Ultimate Truth, পৃষ্ঠা-৮)।
এদিকে শ্রোয়েডার তার আলোচ্য গ্রন্থের ২৮ পৃষ্ঠায় বলছেন: “ বিজ্ঞান সম্ভবত এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে যাচেছ যে, গোটা বিশ্বজগতই তথ্য, জ্ঞান বা একটি ধারণার বহি:প্রকাশ..।” এ-জ্ঞান এমনি এক সর্বজ্ঞ জিনিস (ঢ়যবহড়সবহড়হ) যা গোটা বিশ্বজগতে পরিব্যাপ্ত। শ্রোয়েডার আরও বলছেন: “একটি একক সজ্ঞান সত্ত্বা, একটি সর্বজনীন জ্ঞান গোটা বিশ্বজগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহ ইতিমধ্যেই আমাদেরকে এক বিস্ময়কর সিদ্ধান্তের কাছাকাছি নিয়ে গেছে। সিদ্দান্তটি হলো : এ বিশ্বজগতে যা কিছু অস্তিত্বশীল আছে, সে সবকিছুই ওই জ্ঞান বা wisdom-এর বহি:প্রকাশ।…পরমাণু থেকে শুরু করে পূর্ণাঙ্গ মানুষ পর্যন্ত প্রতিটি সূক্ষাতিসূক্ষ কণিকা, প্রতিটি সত্তা নির্দিষ্ট মাত্রার তথ্য ও জ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব করে বলেই মনে হয়।”–(The Hidden Face of God: Science Reveals the Ultimate Truth, পৃষ্ঠা-xi)।
এ পর্যন্ত যে-আলোচনা করা হলো তা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বস্তুজগত কিছু বিশৃঙ্খল অণুর সমন্বয়ে গঠিত একটি উদ্দেশ্যহীন জিনিস নয় যেমনটি নিরীশ্বরবাদীরা বা বস্তুবাদীরা ধরে নিয়েছেন। বরং বস্তুজগত এমন জ্ঞানের বহি:প্রকাশ, যা বিশ্বজগত সৃষ্টির পূর্বেও ছিল এবং বিশ্বজগত সৃষ্টির পর এর মধ্যে অস্তিত্বশীল সবকিছুর ওপর ওই জ্ঞানের নিয়ন্ত্রণও নিরঙ্কুশ। শ্রোয়েডারের ভাষায়: “… যেন একটি মেটাফিজিক্যাল সাবস্ট্রেইট (metaphysical substrate) ফিজিক্যাল সাবস্ট্রেইট-এর আদলে প্রকাশিত হয়েছে।”–(The Hidden Face of God: Science Reveals the Ultimate Truth, পৃষ্ঠা-৪৮)।
বিজ্ঞানের এ-আবিষ্কার বস্তুবাদের গোটা প্রাসাদকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয় এবং প্রমাণ করে যে, আমরা যে-বস্তুজগতকে পর্যবেক্ষণ করছি তা এক অতিপ্রাকৃত পরম সত্ত্বার ছায়া (shadow) বৈ আর কিছু নয়। এভাবে–যেমনটি শ্রোয়েডার ব্যাখ্যা করেছেন–কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা এমন এক পয়েণ্টে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে বিজ্ঞান ও ঈশ্বরতত্ত্ব (theology) একে অপরকে সমর্থন করে। শ্রোয়েডার বলছেন: “বিশ্বজগতের ঈশ্বরতাত্ত্বিক ব্যাখ্যামতে, বিশ্বজগতের সবকিছুই এক অতিপ্রাকৃত জ্ঞানের বহি:প্রকাশ…। যদি আমি ‘জ্ঞান’ শব্দটিকে ‘তথ্য’ শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপন করি, তবে ঈশ্বরতত্ত্ব ও কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার মধ্যে তেমন কেনো বিরোধ থাকে না । আসলে, আমরা সম্ভবত বস্তুজগতের সঙ্গে আধ্যাত্মিক জগতের বৈজ্ঞানিক মিলন প্রত্যক্ষ করছি।”–(The Hidden Face of God: Science Reveals the Ultimate Truth, পৃষ্ঠা-xii)।
কোয়ান্টাম হচেছ সেই পয়েন্ট, যে পয়েন্টে সত্য সত্যই ঈশ্বরতত্ত্ব বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, গোটা বিশ্বজগত যে জ্ঞান দ্বারা পরিবৃতÑএ-সত্যটি চৌদ্দশ বছর পূর্বেই আল-কুরআনে প্রকাশ করা হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে: “তোমাদের ইলাহ তো কেবল আল্লাহ্ই, যিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নাই। তাঁহার জ্ঞান সর্ববিষয়ে ব্যাপ্ত।”–(কুরআন, ২০: ৯৮)।
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান: ডারউইনবাদের পতন
যেমনটি এ-নিবন্ধের শুরুতে উল্লেখ করেছি, নিরীশ্বরবাদের উত্থানের পেছনে ক্রিয়াশীল ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রচারিত ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব (theory of evolution)। মানুষ থেকে শুরু করে সব জীবিত বস্তুর উৎপত্তি হয়েছে অচেতন বস্তু থেকে সম্পূর্ণ অপরিকল্পিতভাবে–ডারউইনবাদের এ-সাক্ষ্য নিরীশ্বরবাদীদের সে-সুযোগ এনে দিয়েছিল, যা তাঁরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে খুঁজে বেড়াচিছলেন। অতএব তাঁরা ডারউইনবাদকে বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিলেন এবং মার্কস ও এ্যাঙ্গেলসের মতো নাস্তিক চিন্তাবিদরা তাঁদের দর্শনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহন করলেন এ-তত্ত্বকে। সে থেকেই ডারউইনবাদের সঙ্গে নিরীশ্বরবাদের সখ্যতা। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এসে, নিরীশ্বরবাদের অন্যতম সমর্থক এই ডারউইনবাদ তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। আর সে-বিরোধিতা আসে খোদ বিজ্ঞানের তরফ থেকে। জীবাশ্ম বিজ্ঞান (paleontology), প্রাণরসায়ন (biochemistry), অঙ্গব্যবচ্ছেদবিদ্যা (anatomy), ও বংশগতিবিদ্যার (genetics) মতো বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আবিষ্কৃত তত্ত্ব ও সত্য ডারউইনবাদের ভিতকে দেয় গুড়িয়ে। আমরা বিষয়টি নিয়ে আমাদের অন্যান্য গ্রন্থ ও প্রকাশনায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে আলোচনা করছি সংক্ষেপে:
- জীবাশ্ম বিজ্ঞান (Paleontology): ডারউইনের তত্ত্ব একটি অনুমানের উপর ভিত্তি করে রচিত। অনুমানটি হলো: পৃথিবীর সব প্রাণী সৃষ্টি হয়েছে একটি একক(single) ও সাধারণ (common) পূর্বপুরুষ(ancestor) থেকে, দীর্ঘকাল ধরে ছোট ছোট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। ডারউইন ধরে নিয়েছিলেন, ফসিল বা জীবাশ্মের রেকর্ড আবিষ্কারের মাধ্যমে তাঁর তত্ত্বের সঠিকতা প্রমাণিত হবে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর জীবাশ্ম গবেষণার ফলাফল গেল ডারউইনবাদের বিরুদ্ধেই । এক প্রজাতি থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে অন্য প্রজাতির উৎপত্তি লাভের অর্থ মধ্যবর্তী কোনো প্রজাতির অস্তিত্ব থাকা। আর যেহেতু বর্তমান বিশ্বে অসংখ্য প্রাণী আছে, সেহেতু অতীতে অসংখ্য মধ্যবর্তী প্রজাতির (intermediate species) অস্তিত্ব ছিল বলে ধরে নিতে হয় । ডারউইন এ-ধরণের মধ্যবর্তী প্রজাতির জীবাশ্ম আবিষ্কারের আশায় ছিলেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, তেমন একটি প্রজাতির জীবাশ্মও আবিষ্কৃত হলো না । আবিষ্কৃত বিভিন্ন ফসিল বা জীবাশ্ম রেকর্ড থেকে বরং এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, সব প্রজাতি হঠাৎ করে পূর্ণাঙ্গ আকৃতি নিয়েই আবির্ভূত হয়েছে–বিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ রুপ পায়নি। এ-ক্ষেত্রে ক্যামব্রিয়ান এক্সপ্লোশান (Cambrian Explosion)-এর কথা উল্লেখ করা যায়। ওই আদি ভূ-তাত্ত্বিক সময়ে (geological period) প্রাণীরাজ্যের প্রায় সকল প্রাণী হঠাৎ করেই স্ব স্ব পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়ে অস্তিত্ব লাভ করেছিল বলে জীবাশ্ম বিজ্ঞান সাক্ষ্য দেয়। হঠাৎ করে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৈহিক গঠন ও ভিন্ন ভিন্ন জটিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে অসংখ্য প্রজাতির একই সঙ্গে অস্তিত্বলাভের ঘটনা ডারউইনবাদের অসারতা প্রমাণ করে। কারণ, কোনো কোনো বিবর্তনবাদীও স্বীকার করেছেন যে, প্রাণীরাজ্যে একসঙ্গে অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির আবির্ভাবের ঘটনা ইঙ্গিত করে একটি অতিপ্রাকৃত (supernatural) ডিজাইনের প্রতি–যে-ডিজাইন অনুসারে পৃথিবীর সকল প্রাণী সৃষ্টি করা হয়েছে।
- জীববিজ্ঞানসংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষণসমূহ (Biological Observations): ডারউইনের সময়ে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কুকুর ও ঘোড়া উৎপাদনের কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল। তিনি তাঁর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সেসব উদাহরণের ওপর নির্ভর করতে দ্বিধা করেননি। তিনি বিশেষ পদ্ধতিতে উৎপাদিত ওই কুকুর ও ঘোড়ার আকার-আকৃতিতে সামান্য পরিবর্তন লক্ষ্য করেন এবং দাবী করে বসেন যে, ওই একইভাবে প্রাণীজগতের প্রতিটি প্রজাতির উৎপত্তি একটি একক ও সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে হয়ে থাকবে। কিন্তু বাস্তবতা হচেছ, ডারউইন ঊনবিংশ শতাব্দীতে বসে ওই দাবী করছিলেন এবং বিজ্ঞান তখন তেমন উন্নত ছিল না। বিংশ শতাব্দীতে এসে বিজ্ঞান উন্নত হলো এবং পূর্বের অনেক ধারণা-অনুমান প্রমাণিত হলো মিথ্যা বলে। এ-শতাব্দীতে দশকের পর দশক বিভিন্ন প্রজাতির ওপর পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার কাজ করার পর বিজ্ঞানীরা এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, প্রাকৃতিক বা কৃত্রিমভাবে কোনো প্রজাতির দৈহিক গঠনে খানিকটা পরিবর্তন ঘটা সম্ভব হলেও, সে-পরিবর্তন কোনো অবস্থাতেই নির্দিষ্ট বংশগতি সীমানা (genetic boundary) অতিক্রম করে না। ডারউইন তাঁর The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition-শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন, ভালুকের একটি নির্দিষ্ট প্রজাতি প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তিত হতে হতে তিমি মাছের মতো একটি দৈত্যাকার প্রাণীর রূপ পরিগ্রহ করেছে বলে ধরে নেয়ার মাঝে তিনি কোনো সমস্যা দেখেন না। বস্তুত, ওটি ছিল ডারউইনের অজ্ঞতাপ্রসূত মন্তব্য (বিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহ সম্পর্কে অবগত থাকলে হয়তো তিনি মন্তব্যটি করতেন না)। আজকাল নব্য-ডারউইনবাদীরা (Neo-Darwinist) মিউটেশন (mutations) বা জিনগত বিশৃঙ্খলাকে বিবর্তনের মেকানিজম হিসেবে চালিয়ে দিতে চাচেছন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান সে-দাবীকেও অগ্রহণযোগ্য বলে রায় দিয়েছে।
- প্রাণের উৎপত্তি(The Origin of Life): ডারউইন একটি একক ও সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে বিশ্বের তাবৎ প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে বলে দাবী করেছেন। কিন্তু তিনি ওই একক ও সাধারণ পূর্বপুরুষের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে তা বলেননি। অন্যভাবে বললে, তিনি পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের উন্মেষ কীভাবে ঘটেছে সে-ব্যাখ্যা দেননি। ডারউইন অবশ্য Life and Letter of Charles Darwin-শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন যে, পৃথিবীতে প্রথম জীবকোষটি কোনো এক ছোট্ট উষ্ণ জলাশয়ে এলোমেলো (random) রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু পরবর্তী কালে সব ধরণের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলোর মধ্যে এলোমেলো রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে আদি জীবকোষ সৃষ্টির ধারণা একটি অসম্ভব ও অবাস্তব ফেনোমেনন(phenomenon) বৈ আর কিছু নয়। বিখ্যাত বিজ্ঞানবিষয়ক ম্যাগাজিন Nature-এ (১৯৮১ সালের ১২ নভেম্বর প্রকাশিত সংখ্যায়) নোবেল বিজয়ী নিরীশ্বরবাদী ইংরেজ বিজ্ঞানী Fred Hoyle এলোমেলো রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে হঠাৎ করে জীবকোষ উৎপত্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন: “একটি টর্নেডোর ধাক্কায় হঠাৎ করে প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ একত্রিত হয়ে একটি বোয়িং-৭৪৭ তৈরী হয়ে যাবার সম্ভাবনা যতটুকু, আলোচ্য উপায়ে জীবকোষ সৃষ্টির সম্ভাবনাও ঠিক ততটুকু।”
- ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন(Intelligent Design): বিজ্ঞানীরা জীবকোষ নিয়ে গবেষণা করেছেন, গবেষণা করেছেন সে-সব উপাদান নিয়ে যে-সব উপাদানে জীবকোষ গঠিত। জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সেগুলোর বিচিত্র ও অনন্যসাধারণ গঠনশৈলী নিয়েও তাঁরা গবেষণা করেছেন। এ-সব গবেষণা থেকে যে-সত্যটি বেরিয়ে এসেছে তা হলো: জীবজগতের প্রতিটি প্রজাতি সৃষ্টি করা হয়েছে এমন জটিল নকশার ভিত্তিতে যা মানুষের তৈরী কোনো কৃত্রিম যন্ত্রে পাওয়া সম্ভব নয়। সৃষ্টিজগত যে একটি নিখুঁত ডিজাইন অনুসারে অস্তিত্বশীল করা হয়েছে তা উপলব্ধি করার জন্য সৃষ্টিজগতের অসংখ্য আশ্চর্য সৃষ্টির মধ্যে মাত্র দু-একটা সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করা-ই যথেষ্ট: যেমন–আমাদের চোখ এত উন্নত করে সৃষ্টি করা হয়েছে যা কোনো ক্যামেরার সঙ্গে-ই তুলনীয় নয়; নিখুঁতভাবে ডিজাইন-করা পাখির ডানা দেখে মানুষ আকাশে ওড়ার যন্ত্র আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল; প্রতিটি জীবকোষের ডিএনএ (DNA)-তে এতো বিপুল তথ্য রেখে দেয়া হয়েছে যা কেবল একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অধিনে একজন পরিকল্পনাকারীই রাখতে পারেন। ক্যামেরা, উড়োজাহাজ, বা কম্পিউটার–সবকিছুই তৈরী করা হয়েছে বহু সাধ্য-সাধনার পর, নির্দিষ্ট ডিজাইন অনুসারে। এটা কী করে সম্ভব যে, যে-কোনো উন্নত ক্যামেরার চেয়ে উন্নততর চোখ সৃষ্টির ব্যাপারটি হঠাৎ করে এমনি এমনি বা দৈবক্রমে (by chance) ঘটে গেছে! অথচ বিবর্তনবাদ বলে, পৃথিবীতে অমন অসংখ্য অত্যাশ্চর্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে অসংখ্য প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে এমনি এমনি!! বৈজ্ঞানিকভাবে আবিস্কৃত বিভিন্ন তথ্য অবশ্য ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছে যে, জীবজগত এক অনন্যসাধারণ ডিজাইন অনুসারে পরিকল্পিতভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে।
এভাবেই বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আবিষ্কৃত অকাট্য সত্যের মোকাবিলায় বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এসে একেবারে কোনঠাসা হয়ে পড়ে ডারউইনবাদ। আজকাল যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমের বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান হারে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন তত্ত্ব (theory of intelligent design)। যারা এ-তত্ত্ব মেনে নিয়েছেন এবং নিচ্ছেন, তাঁরা বলছেন: বিজ্ঞানের ইতিহাসে ডারউইনবাদ একটি বড় ভুল (great error) বৈ আর কিছু নয়। বস্তুত, বৈজ্ঞানিক সত্য ও তত্ত্ব সবার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, প্রতিটি জীবিতবস্তুকে অস্তিত্বে আনা হয়েছে সুনির্দিষ্ট নকশা বা ডিজাইন অনুসারে। আর ডিজাইন যখন আছে, তখন একজন ডিজাইনারের অস্তিত্ব অস্বীকার করা চলে না। বৈজ্ঞানিকভাবে আবিস্কৃত বিভিন্ন তথ্য প্রকারান্তরে সে-ডিজাইনারের অস্তিত্বকে মেনে নিতে বিবেকবান মানুষকে বাধ্য করে, বাধ্য করে সকল জীবিতবস্তুর ডিজাইনার ও স্রষ্টা হিসেবে এক অতিপ্রাকৃত সত্ত্বা তথা আল্লাহ-কে মেনে নিতে।
মনোবিজ্ঞান : ফ্রয়েডবাদের পতন এবং ধর্মের গ্রহণযোগ্যতা অর্জন
ঊনবিংশ শতাব্দীতে মনোবিজ্ঞান শাখায় নিরীশ্বরবাদের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন অস্ট্রিয়ান সাইকিয়াট্রিস্ট (মানসিক রোগের চিকিৎসক) সিগমান্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud)। তিনি একটি মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রস্তাব করেছিলেন। তত্ত্বটি আত্মার অস্তিত্ত্ব অস্বীকার করে এবং মানবজাতির গোটা আধ্যাত্মিক জগতকে যৌনতা ও ভোগের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করে। তবে ফ্রয়েডের আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তু ছিল ধর্ম।
১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয় তার দ্যা ফিউচার অব এন ইলিউশন (The Future of an Illusion) নামক গ্রন্থ। ওই গ্রন্থে তিনি দাবী করেন যে, ধমীয় বিশ্বাস একধরনের মানসিক অসুস্থতা এবং মানবজাতির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাসও একসময় বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ফ্রয়েড যখন দাবীটি করেন তখন বিজ্ঞান তেমন উন্নত ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই, ফ্রয়েড পর্যাপ্ত গবেষণা না-করেই এবং প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণ ব্যতিরেকেই তাঁর তত্ত্ব উপস্থাপন করতে দ্বিধা করেননি। ফলে তার তত্ত্বটি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। অনুমান করি, যদি ফ্রয়েড আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে তাঁর তত্ত্ব যাচাই করার সুযোগ পেতেন তবে নিজেই নিজের তত্ত্বের দূর্বলতা ধরতে পেরে অবাক হতেন এবং নিজেই এর সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠতেন।
ফ্রয়েডের পর মনোবিজ্ঞান এগিয়ে চলছিল নিরীশ্বরবাদের ছত্রচ্ছায়ায়। শুধু ফ্রয়েড নন, মনোবিজ্ঞানের অন্যান্য স্কুলের (schools of psychology) প্রবক্তারাও (বিংশ শতাব্দীর) ছিলেন নাস্তিক বা নিরীশ্বরবাদী। তেমনি দু’জন মনোবিজ্ঞানী হলেন: আচরণবাদী স্কুলের (behaviorist school) প্রতিষ্ঠাতা বি এফ স্কিনার (B F Skinner) ও র্যাশনাল ইমোটিভ থেরাপির (rational emotive therapy) প্রতিষ্ঠাতা এলবার্ট এলিস (Albert Ellis)। এ-সময় মনোবিজ্ঞানের জগত নিরীশ্বরবাদের ফোরামে পরিণত হয়। ১৯৭২ সালে আমেরিকান সাইকোলজি এসোসিয়েশন-এর সদস্যদের মধ্যে একটি জরিপ চালানো হয়েছিল। জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মাত্র ১.১ শতাংশ আস্তিক, বাকি সবাই নাস্তিক।
কিন্তু অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানী–যারা ফ্রয়েডিয় তত্ত্বের জালে জড়িয়ে পড়েছিলেন–নিজেদের দ্বারা কৃত মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল থেকেই জানতে পেরেছিলেন যে, ফ্রয়েডের তত্ত্ব কতটা ত্রুটিপূর্ণ! তাদের গবেষণা থেকেই জানা গেল, ফ্রয়েডিয় তত্ত্বের ভিত্তি খুবই দূর্বল এবং বলতে গেলে এ-তত্ত্বের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি-ই নেই!! গবেষণা থেকে আরও প্রমাণিত হয়: ধর্ম তো মানসিক রোগ নয়ই, বরং মানসিক স্বাস্থ্যের মূল উপাদান। আমেরিকান লেখক পেট্রিক গ্লাইন (Patrick Glynn) তাঁর এড়ফ: God: The Evidence, The Reconciliation of Faith and Reason in a Post-secular World নামক গ্রন্থে লিখেছেন: “(ধর্মের প্রতি) মনোবিশ্লেষনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির (psychoanalytic vision)প্রতি বিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশ খুব সদয় ছিল না । এ-সময় প্রমাণিত হয়ে যায় যে, ধর্মের প্রতি ফ্রয়েডিয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ প্রতারণাপূর্ন। বিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে অর্থাৎ বিগত ২৫ বছরে মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে-গবেষণা হয়েছে তা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, ধর্ম মানসিক রোগ বা মানসিক রোগের উৎস–যেমনটি ফ্রয়েড ও তার অনুসারীরা দাবী করেছেন–তো নয়ই, বরং ধর্ম মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য ও সুখের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর অন্যতম। গবেষণার পর গবেষণা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, যারা ধর্মে বিশ্বাস করে এবং ধর্মচর্চা করে তাঁরা আত্মহত্যা, পানাভ্যাস, মাদকাসক্তি, তালাক, বিষন্নতা ইত্যাদি সামাজিক সমস্যাগুলোর মোকাবিলায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও স্বাস্থ্যকর সিদ্বান্ত গ্রহন করে তা বাস্তবায়ন করতে পারে। দাম্পত্য-জীবনে তৃপ্তি পাওয়ার প্রধান শর্তও যে ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মচর্চা–এ-সত্যটিও বেরিয়ে এসেছে ওসব গবেষণা থেকে।”
সবশেষে, যেমনটি গ্লাইন বলেছেন (তাঁর ওই গ্রন্থে), ‘বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে মনে হচেছ, আধুনিক মনোবিজ্ঞান ধর্মের সাথে নতুন প্রেক্ষাপটে, নতুন করে, বোঝাপড়া করছে’ এবং ‘প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে নিখাঁদ বস্তুবাদী (secular) দৃষ্টিভঙ্গি শুধু তাত্ত্বিকভাবে নয়, ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও ব্যর্থ”।
অন্যভাবে বললে, মনোবিজ্ঞানের জগতেও নিরীশ্বরবাদের ঘটেছে বড় ধরণের পরাজয়।
চিকিৎসাবিদ্যা : “শান্তি কোথায় মিলবে ?”–এ-প্রশ্নের উত্তর আবিষ্কার
National Institute for Healthcare Research-এর ডেভিড বি লারসন (David B. Larson) ও তাঁর সঙ্গীদের দ্বারা পরিচালিত একটি জরিপ থেকে বেরিয়ে এসেছিল আগ্রহ-উদ্দীপক তথ্য। তাঁরা দেখতে পান, যারা নিয়মিত চার্চে যাতায়াত করেন, তাদের আর্টেরিওস্কেলেরোটিক (arteriosclerotic) হৃদরোগ হবার সম্ভাবনা, যারা অনিয়মিত চার্চে যাতায়াত করেন তাদের তুলনায় মাত্র ষাট শতাংশ। অন্যদিকে, নিয়মিত চার্চে যাতায়াতকারী মেয়েদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা সেসব মেয়ের তুলনায় অর্ধেক যারা নিয়মিত চার্চে যাতায়াত করেন না। লারসন ও তাঁর সঙ্গীরা ওই জরিপ থেকে আরও আবিষ্কার করেন যে, যেসব ধূমপায়ী নিজেদের জীবনে ধর্মকে খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না, তাদের নরমাল ডায়াস্টলিক প্রেসার রিডিং (normal diastolic pressure readings) থাকার সম্ভাবনা সেসব ধূমপায়ীর তুলনায় সাতগুণেরও কম যেসব ধূমপায়ী ধর্মকে নিজেদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন।–(দেখুন, Patrick Glynn, God: The Evidence…পৃষ্ঠা-৮০-৮১)।
প্রশ্ন হচেছ: কেন এমন হয়? বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞানীরা একে সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করবেন “মনোবৈজ্ঞানিক কারণ” (psychological cause) হিসেবে। এ-ধরণের ব্যাখ্যানুসারে (স্রষ্টায়) বিশ্বাস মানুষের মনোবল বৃদ্ধি করে এবং এর ফলে সে মনোদৈহিক সুবিধা লাভ করে। এ-ব্যাখ্যায় হয়তো খানিকটা সত্য আছে, তবে আমরা বিষয়টার একটু গভীরে তাকালেই আরও অধিক নাটকীয় কিছু দেখতে পাবো । আসলে, স্রষ্টায় বিশ্বাস মানুষের মনোবল বৃদ্ধিতে যতটা প্রভাব ফেলতে পারে, অন্য কোনো জিনিস ততটা পারে না। ধর্মীয় বিশ্বাস ও দৈহিক স্বাস্থ্যের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণের লক্ষ্যে গবেষণা করে Harvard Medical School-এর Dr. Herbert Benson কিছু আগ্রহ-উদ্দীপক ফলাফল পেয়েছেন। বেনসন কোনো ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু তিনি গবেষণায় প্রমাণ পান যে, স্রষ্টায় বিশ্বাস ও প্রার্থনা মানুষের স্বাস্থ্য্যের ওপর যতটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলে, ততটা ইতিবাচক প্রভাব অন্য কোনো কিছুই ফেলতে পারে না । তিনি বলছেন: (গবেষণা করে আমি এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে) স্রষ্টায় বিশ্বাস মানুষের মনকে যতটা প্রশান্ত করে, ততটা প্রশান্ত অন্য কোনো ধরণের বিশ্বাস করতে পারে না।”–( দেখুন, Herbert Benson ও Mark Stark-এর লেখা গ্রন্থ Timeless Healing, পৃষ্ঠা ২০৩)।
মানুষের মন ও দেহের সঙ্গে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসের এই বিশেষ সম্পর্ক কেন? আগেই বলেছি, হার্বার্ট বস্তুবাদী গবেষক ছিলেন। অথচ তিনিই এই প্রশ্নের জবাবে বলছেন: মানুষের মন ও দেহকে স্রষ্টার জন্যই একসূত্রে বাধা হয়েছে। (দেখুন, Timeless Healing, পৃষ্ঠা- ১৯৩)।
এ সত্য–যা চিকিৎসাজগত ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করেছে–কুরআনে প্রকাশ করা হয়েছে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে। কুরআন বলছে: “ আল্লাহ তথা স্রষ্টার স্মরণেই কেবল অন্তর শান্তি পেতে পারে।”–(কুরআন, ১৩: ২৮)। যাঁরা স্রষ্টায় বিশ্বাস করেন; তাঁর উপর আস্থা রাখেন এবং তাঁর কাছে নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রার্থনা করেন–তাঁরা দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে অন্যদের তুলনায় অধিকতর স্বাস্থ্যবান হন। কেন হন? কারণ ওসব করবার মাধ্যমে তাঁরা তাদের প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ করেন। বলাবাহুল্য, মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক যে-কোনো দার্শনিক ব্যবস্থা সবসময়ই মানুষের জন্য যন্ত্রনা, দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও বিষন্নতা বয়ে আনে।
একজন ধার্মিক ব্যক্তির মনে শান্তি বিরাজ করেন। এ-শান্তির উৎস হলেন স্রষ্টা নিজে। আর ধার্মিক ব্যাক্তি স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্যই কাজ করেন। অন্যভাবে বললে, ধার্মিক ব্যক্তি বিবেকের ডাক শোনার পুরষ্কার হিসেবে লাভ করেন ওই শান্তি। এখানে বলে রাখা ভাল যে, একজন ধার্মিক লোক কেবল শান্তির জন্য বা ভাল স্বাস্থ্যের আশায় ধর্মীয় জীবন যাপন করেন না। কেবল এ-ধরনের ইচছা মনে পোষণ করে ধর্ম-কর্ম করলে কেউ সঠিক অর্থে শান্তি পেতে পারে না । স্রষ্টা জানেন একজন কী প্রকাশ করে বা মনের গভীরে কী গোপন করে। স্রষ্টার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হয়ে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে একনিষ্ঠভাবে ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনের মাধ্যমেই কেবল একজন প্রকৃত শান্তি পেতে পারে। স্রষ্টা বলছেন: “তুমি একনিষ্ঠ হইয়া নিজেকে ধর্মে বা দীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে-প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নাই। ইহাই সরল ধর্ম, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।”– (কুরআন, ৩০: ৩০)।
বিভিন্ন আবিষ্কারের আলোকে আমরা সংক্ষেপে ওপরে যে-সত্য তুলে ধরলাম, আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা সে-সত্যকে স্বীকার করতে শুরু করেছে। পেট্রিক গ্লাইন বলছেন: “সাম্প্রতিককালের চিকিৎসাবিদ্যা (medicine) স্পষ্টতই নিখাঁদ বস্তুগত (সবঃবৎরধষ) চিকিৎসার বাইরেও যে চিকিৎসা পদ্ধতি থাকতে পারে তা স্বীকার করতে যাচ্ছে।”–(Patrick Glynn, God: The Evidence…পৃষ্ঠা-৯৪)।
সমাজ : সাম্যবাদ, ফ্যাসিবাদ ও হিপ্পিবাদের পতন
বিংশ শতাব্দীতে এসে নিরীশ্বরবাদ শুধু নভোবস্তুবিদ্যা (astrophysics), জীববিদ্যা, মনোবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের দ্বারা অসার প্রমাণিত হয়েছে তা-ই নয়; এ-সময়ের রাজনীতি ও সামাজিক নৈতিকতার ক্ষেত্রেও এ-মতবাদের ঘটেছে বড় ধরণের পরাজয়।
কমিউনিজমকে আখ্যায়িত করা যেতে পারে ঊনবিংশ শতাব্দীর নিরীশ্বরবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ফল হিসেবে। মার্কস্, এ্যাঙ্গেল্স, লেলিন, ট্রটস্কি বা মাও–কমিউনিজমের সব দিকপালই নিরীশ্বরবাদকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আর তাই, সব কমিউনিস্ট শাসকের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল সমাজে নাস্তিকতাবাদ বা নিরীশ্বরবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং অন্য সবধরণের ধর্মবিশ্বাসকে ধ্বংস করে দেয়া। স্ট্যালিনের রাশিয়া, রেড চায়না, ক্যাম্বোডিয়া, আলবেনিয়া, এবং পূর্ব ব্লকের কিছু দেশে সে-লক্ষ্য অর্জনের জন্য ধার্মিক লোকদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল; সে-নির্যাতন কখনো কখনো রূপ নিয়েছিল গণহত্যায়।
এতকিছুর পরও, আশ্চর্যজনকভাবে, ঊনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকে এসে কমিউনিজমের পতন ঘটলো। কমিউনিজমের পতনের কারণগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এ-সময়ে কমিউনিজমের আবরণে আসলে পতন ঘটেছে নিরীশ্বরবাদের। প্যাট্রিক গ্লাইন লিখেছেন: “ বস্তুবাদী ঐতিহাসিকরা নিশ্চিতভাবেই বলবেন যে, অর্থনীতির সূত্রগুলোকে অস্বীকার করার চেষ্টা-ই ছিল কমিউনিজমের সবচে বড় ভুল। আসলে সমস্যা ছিল আরো…। কমিউনিজমের পতনের কারণগুলো খুঁজতে গেলে ঐতিহাসিকদের কাছে এটা আরো স্পষ্ট হবে যে, সোভিয়েত অভিজাতশ্রেণী নিরীশ্বরবাদী ‘বিশ্বাসের সংকটে’ ভুগছিল। একটি নিরীশ্বরবাদী আদর্শের অধীনে বাস করে–যে আদর্শ অনেকগুলো মিথ্যার ওপরে এবং ওই মিথ্যাগুলো একটি ‘বড়’ মিথ্যার ওপরে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত ছিল–সোভিয়েত সমাজব্যবস্থা সকল অর্থেই নীতিভ্রষ্টতা ও আত্ববিশ্বাসহীনতায় ভুগছিল। (দেশটির) জনগণ–শাসকগোষ্ঠীসহ–হারিয়ে বসেছিল সবধরণের নীতি-নৈতিকতার ধারণা এবং আশা।”–(দেখুন, Patrick Glynn; God: The Evidence, The Reconciliation of Faith and Reason in a Post-secular World; পৃষ্ঠা- ১৬১-১৬২)।
সোভিয়েত-সিস্টেম যে বড় ধরণের ‘বিশ্বাসের সংকটে’ ভুগছিল, তার আগ্রহ-উদ্দীপক ইঙ্গিত হচ্ছে প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভের সংস্কার-প্রচেষ্টা। প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই গর্বাচেভ অর্থনৈতিক সংস্কার কার্যক্রমের পাশাপাশি নৈতিক সমস্যাবলী সমাধানের ব্যাপারেও আগ্রহী ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি মদ্যপানের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তবে, সমাজের নৈতিক মনোবল বৃদ্ধির জন্য তিনি দীর্ঘদিন ধরে মার্ক্সিস্ট-লেলিনিস্ট শব্দমালা ব্যবহার করে দেখতে পান যে, সেগুলো কোনো কাজে আসছে না। তাই–যদিও তিনি নিজে একজন নাস্তিক ছিলেন–তাঁর শাসনামলের শেষদিকে এসে কোনো কোনো ভাষণে স্রষ্টার কথা উল্লেখ করা শুরু করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই, তাঁর ওই কৃত্রিম কথাবার্তা কোনো কাজে আসেনি এবং সোভিয়েত সমাজে বিশ্বাসের সংকট গভীর থেকে গভীরতর হওয়া অব্যাহত থেকেছে। ফলে অবশেষে পতন ঘটেছে বিপুলায়তন সোভিয়েত সাম্রাজ্যের।
বিংশ শতাব্দীতে শুধু কমিউনিজমের পতন ঘটেছে তা নয়, পতন ঘটেছে ফ্যাসিবাদেরও, যা ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মবিরোধী দর্শনের আরেক উপজাত। ফ্যাসিবাদ হচ্ছে এমন এক দর্শন যাকে নিরীশ্বরবাদ ও প্যাগানবাদের সংমিশ্রণ বলা যায়। ফ্যাসিবাদ ঈশ্বরবাদী ধর্মগুলোর বিরুদ্ধে সদা খড়গহস্ত ছিল। ফ্রায়েডরিখ নিৎসেকে (Friedrich Nietzsche) বলা যেতে পারে ফ্যাসিবাদের জনক। নিৎসে অতীতের প্রতিমাউপাসক বর্বর সমাজের নৈতিকতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং খৃস্টানধর্মসহ অন্যসব একেশ্বরবাদী ধমের্র বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। তিনি এমনকি নিজেকে একজন এন্টি-ক্রাইস্ট (Anti-Christ) হিসেবে তুলে ধরতেও দ্বিধা করেননি। নিৎসের শিষ্য মার্টিন হেইডেগার (Martin Heidegger) ছিলেন একজন নাজি (Nazi) সমর্থক এবং এই দুই নাস্তিক গুরু-শিষ্যের চিন্তাধারা নাজি জার্মানিকে চরম নৃশংস হতে প্ররোচিত করেছিল। মানবজাতির ওপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও চাপিয়ে দিয়েছিল ফ্যাসিবাদ ও কমিউনিজমের মতো নাস্তিক্যবাদী দর্শন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছিল সাড়ে পাঁচ কোটি আদমসন্তান।
এখানে সামাজিক ডারউইনবাদ (Social Darwinism)-এর প্রসঙ্গও আসবে স্বাভাবিকভাবেই। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্বের কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল এ-নাস্তিকতাবাদী দর্শন। হার্ভার্ডের ইতিহাসের অধ্যাপক জেমস্ জল (James Joll) তাঁর Europe Since 1870-নামক গ্রন্থে লিখেছেন: “দুটো বিশ্বযুদ্ধের পেছনেই শক্তিশালী প্রভাবকের ভূমিকা রেখেছিল সামাজিক ডারউইনবাদী ইউরোপীয় নেতাদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। এ-নেতারা বিশ্বাস করতেন যে, যুদ্ধ হচেছ একটি জৈবিক প্রয়োজন (biological necessity) এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমেই একটি জাতির জন্ম হয়।”
বিংশ শতাব্দীতে এসে নিরীশ্বরবাদের নেতিবাচক সামাজিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায় পশ্চিমা গনতান্ত্রিক দেশগুলোতে। আজকাল পশ্চিমা বিশ্বকে ‘খ্রিস্টান বিশ্ব’ হিসেবে আখ্যায়িত করার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তবে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টবাদের পাশাপাশি নিরীশ্বরবাদের উপস্থিতিও পশ্চিমা বিশ্বে লক্ষ্যণীয় এবং আজ পশ্চিমা সভ্যতায় এই দুই সংস্কৃতির মধ্যে দ্বন্ধও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর এ-উপাদানই পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ, নৈতিক অবক্ষয়, স্বৈরতন্ত্র ও অন্যান্য নেতিবাচক ফেনোমেননের আবির্ভাবের (পশ্চিমা সংস্কৃতিতে) জন্য সত্যিকার অর্থে দায়ী।
আমেরিকান লেখক প্যাট্রিক গ্লাইন তাঁর এড়ফ: God: The Evidence… নামক গ্রন্থে বিষয়টার দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং পশ্চিমা সংস্কৃতিতে ঈশ্বরভীতি ও নিরীশ্বরবাদী উপাদানের মধ্যে তুলনা করার লক্ষ্যে, আমেরিকান বিপ্লব ও ফরাসি বিপ্লবের উদাহরণ টেনেছেন। আমেরিকান বিপ্লব সংঘঠিত হয়েছিল ঈশ্বর-বিশ্বাসীদের দ্বারা। তাই আমেরিকান স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে যে, সকল মানুষ তাদের স্রষ্টাপ্রদত্ত কিছু অধিকার ভোগ করে। অন্যদিকে ফরাসী বিপ্লব যেহেতু নিরীশ্বরবাদীদের কর্মের ফল, ফরাসী মানবাধিকার ঘোষনায় স্রষ্টার নামের কোনো উল্লেখ নেই এবং সেটি নিরীশ্বরবাদী ও নব্য প্যাগান ধ্যান-ধারণা দ্বারা পূর্ণ।
ও-দুটো বিপ্লবের ফল হয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। আমেরিকায় বিপ্লবের পর একটি শান্তিপূর্ণ, সহনশীল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল, যে-পরিবেশে ধর্ম ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে যথাযথ সম্মান করা হয়। বিপরীতভাবে, ধর্মের প্রতি তীব্র আক্রমণাত্মক মনোভাব ফরাসী বিপ্লবের পর ফ্রান্সে এত রক্তপাত ঘটিয়েছে এবং বর্বরতার এমন পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে, যা ইতিহাসে বিরল। গ্লাইন বলছেন: “ নিরীশ্বরবাদের সঙ্গে নৈতিকতা ও রাজনৈতিক বিপত্তির একটি আগ্রহ-উদ্দীপক পারস্পারিক সম্পর্ক আছে।”–(দেখুন, God: The Evidence… পৃষ্টা ১৬১)। গ্লাইন আরও উল্লেখ করেছেন যে, আমেরিকাকে নাস্তিক রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টাও মার্কিন সমাজের কম ক্ষতি করেনি। (উদাহরণস্বরূপ) বিংশ শতাব্দীর ষাটের ও সত্তরের দশকে ছড়িয়ে পড়া যৌন বিপ্লব (sexual revolution) সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছিল। এ-সত্য বস্তুবাদী ঐতিহাসিকরাও স্বীকার করেছেন। –(দেখুন, God: The Evidence… পৃষ্ঠা- ১৬৩)।
ওপরে যে-সামাজিক ক্ষতির কথা বলা হলো, হিপ্পি আন্দোলন ছিল সে-ক্ষতির আরেকটি বহি:প্রকাশ। হিপ্পিরা বিশ্বাস করতো যে, ঈশ্বরবিহীন মানবতাবাদী দর্শনের মাধ্যমে এবং প্রচুর মাদক গ্রহণ ও অবাধ যৌনাচারের দ্বারা আধ্যাত্মিক মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এই যুবক-যুবতীর দল, যারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে রোমান্টিক গান গাইতো–জন লেননের (John Lennon) মতো, যিনি তাঁর গানের মাধ্যমে এমন বিশ্বের কথা বলতেন যে-বিশ্বে কোনো রাষ্ট্র থাকবে না, থাকবে না কোনো ধর্ম–তাঁরা প্রকৃত প্রস্তাবে গণ-প্রতারণার শিকার হচিছল।
বাস্তবে তাদের ধর্মহীন জগত হিপ্পিদের জন্য করুণ পরিণতিই কেবল বয়ে এনেছিল। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের হিপ্পি নেতারা সত্তরের দশকের প্রথম নাগাদ আত্মহত্যা করেছিলেন অথবা মাদকাসক্তির কারণে বরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন করুণ মৃত্যুকে। বহু তরুণ হিপ্পির পরিণতিও ওই একইরকম হয়েছিল।
যে-প্রজন্মটির যুবক-যুবতীরা হিংসার পথে পা বাড়িয়েছিল, তাঁরা অবশেষে সে হিংসার আগুনেই জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে গেল। ১৯৬৮ সালের ওই প্রজন্মের যারা স্রষ্টাবিমুখ হয়েছিল, হয়েছিল ধর্মবিমুখ এবং কল্পনা করেছিল যে, বিপ্লব বা স্বার্থপর ভোগবাদের মাধ্যমে মুক্তি পাওয়া সম্ভব–তাঁরা আখেরে শুধু নিজেদেরই ধ্বংস করেনি, ধ্বংস করে দিয়েছিল নিজেদের সমাজকেও ।
নিরীশ্বরবাদ-পরবর্তী বিশ্বের সূচনাপর্ব
এ-পর্যন্ত যে-সমস্ত তথ্য-প্রমাণ তুলে ধরেছি, তাতে এটা স্পষ্ট যে, নিরীশ্বরবাদ নিশ্চিতভাবেই পতনের শেষ প্রান্তে চলে যাচেছ। অন্যভাবে বললে, মানবজাতি (humanity) স্রষ্টার দিকে মুখ ফেরাচেছ এবং ভবিষ্যতেও ফেরাতে থাকবে। এ-সত্য কেবল বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং রাজনৈতিক পরিমন্ডলেই সীমিত নয়। বহু খ্যাতনামা রাষ্ট্রনায়ক, সিনেমার নায়ক-নায়িকা, পপগায়ক–যারা পশ্চিমা সমাজের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে থাকেন–আজকাল আগের তুলনায় অনেক বেশী ধার্মিক হিসেবে সমাজে পরিচিত হচেছন। অনেক নিরীশ্বরবাদী বা নাস্তিক এমন আছেন যারা দীর্ঘকাল নাস্তিক হিসেবে জীবন অতিবাহিত করার পর এখন সত্যকে উপলব্দি করে পুরোদস্তুর আস্তিকে পরিণত হয়েছেন (প্যাট্রিক গ্লাইন–যার গ্রন্থ থেকে বক্ষমান নিবন্ধে প্রচুর উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে–একসময় নাস্তিক ছিলেন।)
আগ্রহ-উদ্দীপক ব্যাপার হচেছ, যেসব ডেভেলপম্যান্ট (development) নিরীশ্বরবাদের বিরুদ্ধে কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে–সেগুলোর সূচনাও হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে। এ-সময় এ্যানথ্রোপিক প্রিন্সিপাল (anthropic principle) সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ওই একই সময়ে ডারউইনবাদের বিরুদ্ধেও বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণ প্রকাশিত হতে শুরু করে। ফ্রয়েডের তত্ত্বের বিরুদ্ধে যে-গ্রন্থটি ‘টার্নিং পয়েন্ট’ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে সে-গ্রন্থটি (The Road Less Traveled) স্কট পিক(Scott Peck) লিখেছিলেন ১৯৭৮ সালে। গ্লাইন তাঁর গ্রন্থের ১৯৯৭ সংষ্করণে লিখেছেন: “গত বিশ বছরে এমনসব তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য-প্রমাণ আমাদের সামনে হাজির হয়েছে যা দীর্ঘকাল ধরে প্রভাব-বিস্তার-করে-আসা আধুনিক ধর্মহীন বিশ্বদর্শনের (worldview) ভিত্তিকে গুড়িয়ে দেয়।”–(God: The Evidence…পৃষ্ঠা- ২)।
নিরীশ্বরবাদী বিশ্বদর্শনের (worldview) পতনের অর্থ অন্য একটি দর্শনের–যে-দর্শন স্রষ্টায় বিশ্বাস করে–টিকে থাকা। বস্তুত, বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকের শেষ দিকে (অথবা হিজরী সনের হিসেবে চতুর্দশ হিজরীর প্রথম দিকে) ধর্মীয় মূল্যবোধের জাগরণ প্রত্যক্ষ করেছে বিশ্ব। অন্যান্য সামাজিক প্রক্রিয়ার মতোই এ-জাগরণও একদিনে ঘটেনি। অধিকাংশ মানুষ এ-বিষয়ে বেখবর থাকতে পারেন, কারণ প্রক্রিয়াটি ডেভেলপ করেছে দীর্ঘকাল ধরে ধীরে ধীরে । যা হোক, যারা ওই ডেভেলপম্যান্ট গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন তারা স্পষ্ট বুঝবেন যে, বিশ্ব এখন একটি সন্ধিক্ষণে (turning point) অবস্থান করছে।
নিরীশ্বরবাদী বা বস্তুবাদী ঐতিহাসিকরা ইতিহাসের এ-প্রক্রিয়াকে তাদের নিজেদের ধ্যান-ধারণার আলোকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু স্রষ্টার অস্তিত্ত্ব প্রসঙ্গে তাদের ধারণা যেমন ভুল, তেমনি এ-ক্ষেত্রেও তারা ভুল সিদ্ধান্তেই উপনীত হন। সত্যি বলতে কি, ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি নির্ধারিত হয় স্রষ্টার ইচছানুসারেই। কুরআন বলছে: “আল্লাহর প্যাটার্ন (pattern) তুমি বদল হতে দেখবে না। এবং আল্লাহর প্যাটার্ন-এ তুমি কোনো ধরণের পরিবর্তন (ধষঃবৎধঃরড়হ) হতেও দেখবে না।”–(কুরআন, ৩৫:৪৩) । বস্তুত, ইতিহাসের একটা উদ্দেশ্য (purpose) থাকে এবং স্রষ্টার ইচ্ছানুসারে তা প্রকাশিত হয় । স্রষ্টার ইচছা হচেছ তাঁর আলোর পূর্ণতাপ্রাপ্তি (perfection of His light): “তাঁরা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়। অবিশ্বাসীরা অপ্রীতিকর মনে করলেও, আল্লাহ তাঁর আলোর পূর্ণ উদ্ভাসন ব্যতীত আর কিছু চান না।”–(কুরআন, ৯ : ৩২)। এ-আয়াতের অর্থ হচেছ, আল্লাহ তাঁর প্রেরিত ধর্মের মাধ্যমে মানুষের জন্য তাঁর আলো পাঠিয়েছেন (যে-আলোতে পথ চলে তারা মুক্তি পেতে পারে)। যারা বিশ্বাস করে না, তাঁরা সে-আলো মুখ দিয়ে (ইঙ্গিতে, প্রচারনার দ্বারা, দর্শনের মাধ্যমে) নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু স্রষ্টা তাঁর আলো শেষ পর্যন্ত পূর্ণরূপে প্রকাশ করবেনই এবং পৃথিবীতে ধর্মীয় মুল্যবোধের আধিপত্য কায়েম হবেই।
আমরা নিবন্ধের শুরুতে ‘ইতিহাসের সন্ধিক্ষণের’ কথা বলেছি। সম্ভবত: এটিই হচেছ ইতিহাসের সে টার্নিং পয়েন্ট। যেসব তথ্য-প্রমাণ আমরা এখানে জড়ো করেছি তা-ও আমাদের ধারণাকে সমর্থন করে। অবশ্য, আল্লাহই সবকিছু ভাল জানেন।
উপসংহার
আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সময়ে বাস করছি। নিরীশ্বরবাদ–যাকে মানুষ শত শত বছর ধরে ‘যুক্তি ও বিজ্ঞানের পথ’ হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছে–প্রমাণিত হচেছ স্রেফ যুক্তিহীনতা ও অজ্ঞতার ধারক হিসেবে। আপাতদৃষ্টিতে বিজ্ঞানকে অবলম্বন করে গড়ে-ওঠা বস্তুবাদী দর্শন অসার প্রমাণিত হয়েছে সেই বিজ্ঞানের দ্বারা-ই। নিরীশ্বরবাদের জাল থেকে আজকের বিশ্ব বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে এবং স্রষ্টা ও ধর্মের প্রতি ক্রমবর্ধমানহারে ঝুঁকছে এবং ঝুঁকবে। এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বহু পূর্বে।
এটা স্পষ্ট যে, এ-সময় বিশ্বাসীদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবার আছে। বিশ্বের চিন্তার জগতে ইতিমধ্যে যে-পরিবর্তন ঘটে গেছে এবং ভবিষ্যতে ঘটতে যাচ্ছে–সে সম্পর্কে তাদের অবশ্যই অবহিত থাকতে হবে। তাদেরকে এ-পরিকর্তন ব্যাখ্যা করতে হবে এবং বিশ্বায়ন যে-সুযোগ এনে দিয়েছে সে-সুযোগের সদ্ব্যবহার করে কার্যকরভাবে সত্যের (truth) প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। তাদের অবশ্যই জানতে হবে যে, এ-বিশ্বে মৌলিক আদর্শের দ্বন্দ্বটি হচ্ছে নিরীশ্বরবাদের সঙ্গে ঈশ্বর-বিশ্বাসের। এটি অবশ্যই পূর্বের (East) সঙ্গে পশ্চিমের (West) দ্বন্দ্ব নয়। পূর্ব এবং পশ্চিম–বিশ্বের উভয়াংশেই নাস্তিক ও আস্তিক আছে। এ-দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, বিশ্বাসী খৃষ্টান ও বিশ্বাসী ইহুদীরা বিশ্বাসী মুসলমানদের মিত্র-ই বটে। মূল বিভক্তিরেখার একপাশে মুসলমানরা ও অন্যপাশে কিতাবীরা (খৃষ্টান ও ইহুদী) আছে তা নয়; আসলে মূল বিভক্তিরেখার একপাশে আছে মুসলমান, খৃষ্টান ও ইহুদীরা এবং অন্যপাশে আছে নাস্তিক ও প্যাগানরা। অবশ্য, কোনো অবস্থাতেই আমাদের উচিত হবে না তাদের প্রতি আক্রমণাত্মক মনোভাব পোষণ করা বা প্রদর্শন করা। তাঁরা যে-ভুলের পাঁকে জড়িয়ে আছে, সে-পাঁক থেকে তাদের আত্মাকে মুক্তি দেয়ার শান্তিপূর্ণ উপায়ের কথা-ই কেবল আমরা ভাবতে পারি।
সবশেষে বলবো, দ্রুত এমন একটা যুগে আমরা প্রবেশ করতে যাচ্ছি, যে-যুগটা হবে সম্পূর্ণভাবে
নাস্তিকতাবাদমুক্ত বা নিরীশ্বরবাদমুক্ত। আজো যারা নিজেদের স্রষ্টা সম্পর্কে অজ্ঞ ও বেখবর হয়ে পড়ে আছেন, ওই সময়ে তাঁরাও বিশ্বাসের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করবেন, ইনশাআল্লাহ।■
অনুবাদ: আলিমুল হক
‘নবজাগরণ’ অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপ্লিকেশনটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।
![]()
‘নবজাগরণ’ এর টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।
‘নবজাগরণ’ এর ফেসবুক পেজে লাইক করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

 নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা
নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা