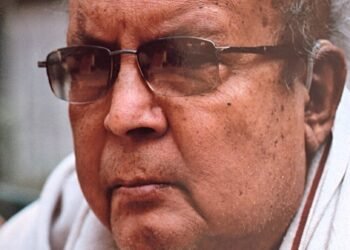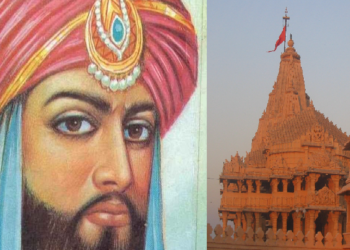খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে ব্যাবিলনে আলেকজান্ডারের মৃত্যু ঘটলে তার অধিকৃত ভারতীয় অঞ্চলে গ্রিকদের মধ্যে আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা এবং বিরােধ দেখা দেয়। এ সময়ে মগধে নন্দবংশীয় সম্রাট ধননন্দ রাজত্ব করছিলেন। তিনি মােটেও জনপ্রিয় ছিলেন না। এ অবস্থায় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মগধের সিংহাসন দখল করেন এবং উত্তর পশ্চিম ভারত থেকে গ্রিকদের বিতাড়িত করে ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য ইতিহাসে মৌর্য সাম্রাজ্য নামে বিখ্যাত। ড. রাধাকুমুদ মুখােপাধ্যায় মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনারূপে বর্ণনা করেছেন।

মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বংশপরিচয় সম্পকে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। হিন্দু সাহিত্যিক উপাদানের সাক্ষ্যানুসারে তিনি ছিলেন নন্দ বংশােদ্ভূত। তাঁর মায়ের নাম ছিল মূরা এবং তিনি ছিলেন এক নন্দ রাজার পত্নী বা উপ-পত্নী। অনেকে মনে করেন যে মাতা মূরার নামানুসারে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম হয় মৌর্য। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে মূরার পুত্র হবে ‘মৌরেয়’, মৌর্য নয়। মধ্যযুগীয় শিলালিপিতে মৌর্যদের ক্ষত্রিয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বৌদ্ধ লেখকদের মতানুসারে, মৌর্যরা ছিলেন ক্ষত্রিয়। গৌতম বুদ্ধের আমলে তারা পিপ্পলিবন নামক প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যের শাসক ছিলেন। ‘মুদ্রারাক্ষস’ নামক নাটকে চন্দ্রগুপ্তকে ‘বৃষল’ বলা হয়েছে যা থেকে অনেকেই মনে করেন যে তিনি শূদ্র ছিলেন। তবে মনে রাখা দরকার যে ‘বৃষল’ শব্দটি শুধু শূদ্রকেই বােঝায় না। এ শব্দটির অন্য দুটি অর্থ হচ্ছে রাজ-শ্রেষ্ঠ এবং জাতিচ্যুত। হিন্দু ধর্মাবলম্বী হয়েও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য গ্রিক কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন এবং শেষ জীবনে জৈন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এজন্য জাতিচ্যুত হিসাবে তাঁকে ‘বৃষল’ বলা যেতে পারে। অন্যদিকে বিশাল সাম্রাজ্য এবং সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি রাজ-শ্রেষ্ট হিসাবেও ‘বৃষল’ রূপে আখ্যায়িত হতে পারেন। জৈন কিংবদন্তী অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ছিলেন ময়ূর-পােষক এক গ্রাম-প্রধানের দৌহিত্র। বৌদ্ধ উৎসগুলাে মৌর্যদের ক্ষত্রিয় বলে বর্ণনা করেছে। মহাবংশে তাঁকে মৌর্য নামের ক্ষত্রিয় বংশের সন্তান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দিব্যাবদানেও বিন্দুসার ও অশােককে ক্ষত্রিয়রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। মহাপরিনির্বাণ সূত্রে মৌর্যদের পিপ্পলিবনের শাসকগােষ্ঠীরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখিত উৎসগুলাের মধ্যে বৌদ্ধ উৎসগুলাে সবচেয়ে প্রাচীন এবং এ কারণে পন্ডিতরা মনে করেন যে, মৌর্যরা ক্ষত্রিয় ছিলেন।
গৌতম বুদ্ধের আমলে মৌর্যরা ছিলেন পিপ্পলিবনের শাসকগােষ্ঠী। পরবর্তীকালে পিপ্পলিবন মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতকে মৌর্যরা দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বৌদ্ধ কিংবদন্তী থেকে জানা যায় যে চন্দ্রগুপ্তের পিতার মৃত্যুর পর তাঁর মাতা অন্ত:সত্তা অবস্থায় মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের জন্ম হয়। এক রাখাল চন্দ্রগুপ্তকে পােষ্যপুত্র হিসাবে গ্রহণ করে তাঁকে নিকটবর্তী এক গ্রামে নিয়ে যায়। কিংবদন্তী অনুসারে বাল্যকালে তিনি গাে-পালক ও শিকারীদের মাঝে বড় হয়ে ওঠেন। সেখান থেকে কৌটিল্য নামে তক্ষশীলার এক ব্রাহ্মণ পন্ডিত তাঁকে তক্ষশীলায় নিয়ে গিয়ে রাজনৈতিক ও সামরিক শিক্ষা দান করেন। প্রটার্ক ও জাস্টিনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময় চন্দ্রগুপ্ত মগধের অত্যাচারী নন্দরাজা ধননন্দকে উৎখাত করার জন্য আলেকজান্ডারকে আমন্ত্রণ জানাতে পাঞ্জাবে আলেকজান্ডারের শিবিরে গিয়েছিলেন। তাঁর এহেন আচরণকে ডঃ রায়চৌধুরী রাণা সংগ্রাম সিংহের বাবরকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আলেকজান্ডার চন্দ্রগুপ্তের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে বরং তাঁর মৃত্যুদন্ডের আদেশ দিলে চন্দ্রগুপ্ত পাঞ্জাব থেকে পালিয়ে আসেন। তখন থেকেই চন্দ্রগুপ্ত ভারত থেকে গ্রিক ও নন্দদের উৎখাত করার চেষ্টা করতে থাকেন।

ভারত থেকে গ্রিক-বিতাড়ন ও নন্দ-সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধনে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তক্ষশীলার ব্রাহ্মণ পন্ডিত কৌটিল্যের সাহায্যে পেয়েছিলেন। আর্থিক সাহায্যের আশায় কৌটিল্য পাটলিপুত্রে এসে নন্দরাজার কাছে অপমানিত হয়েছিলেন বলে তিনিও নন্দদের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত প্রথমে নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করেছিলেন অথবা গ্রিকদের বিতাড়িত করেছিলেন সে বিষয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। গ্রিক ঐতিহাসিক জাস্টিনের বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে চন্দ্রগুপ্ত প্রথমে পাটলিপুত্র দখল করেন এবং পরে গ্রিকদের বিতাড়িত করেন। ডঃ রায়চৌধুরী এবং ভিনসেন্ট স্মিথ এ মতকে সমর্থন করেন। ঐতিহাসিক রাধাকুমুদ মুখােপাধ্যায় অবশ্য মনে করেন যে চন্দ্রগুপ্ত প্রথমে পাঞ্জাবে গ্রিকদের পরাজিত করার পর মগধরাজ ধননন্দকে সিংহাসনচ্যুত করেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য প্রথমে পাটলিপুত্র অধিকার করেন এবং পরে গ্রিকদের বিতাড়িত করেন, এ মতই অধিক গ্রহণযােগ্য।
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সিংহাসনারােহণের তারিখ সম্পর্কে পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। গ্রিক উৎস থেকে জানা যায় যে, ৩২৬ অথবা ৩২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি পাঞ্জাবে আলেকজান্ডারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তবে তখনাে তিনি রাজা হননি। বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে জানা যায় যে গৌতম বুদ্ধের নির্বাণলাভের ১৬২ বছর পরে চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসেছিলেন। ক্যান্টনের দিনপঞ্জি অনুসারে বুদ্ধের মৃত্যু হয়েছিল ৪৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এর ১৬২ বছরের পরের সালটি হয় (৪৮৭-১৬২)=৩২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পরই চন্দ্রগুপ্ত রাজা হয়েছিলেন বলে সবাই মনে করেন। কাজেই ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসেছিলেন এ কথা অনেকেই স্বীকার করেন না। অন্যদিকে দীপবংশ থেকে জানা যায় যে গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর ২১৮ বছর পর। অশােকের অভিষেক হয়েছিল (৪৮৭-২১৮)= ২৬৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এর চার বছর আগেই তিনি সিংহাসনে বসেছিলেন ২৭৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। পুরাণের সাক্ষ্যানুযায়ী চন্দ্রগুপ্ত এবং বিন্দুসার যথাক্রমে ২৪ ও ২৫ বছর রাজত্ব করেছিলেন। কাজেই চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসেছিলেন (২৭৩+৪৯)=৩২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এ তারিখ অধিকাংশ আধুনিক পন্ডিত স্বীকার করে নিয়েছেন।
মগধের সিংহাসন দখল ও গ্রিকদের বিতাড়ণে সমকালীন পরিস্থিতি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সহায়ক হয়েছিল। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পরপরই ভারতে তার অধিকৃত অঞ্চলে গ্রিক গভর্নরদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হলে সেখানে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। সিন্ধুর গভর্নর সঙ্গে সংঘর্ষে পাঞ্জাবের গভর্নর পিথন নিহত হন। এর কিছুদিন পরে তক্ষশীলায় কৌটিল্যের নেতৃত্বে গ্রিক-বিরােধী বিদ্রোহ দেখা দেয়। এ সময় আততায়ীর হাতে পুরু নিহত হলে স্থানীয় অধিবাসীরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। এ অবস্থায় চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে সে অঞ্চল থেকে গ্রিকদের বিতাড়িত করা সহজ হয়েছিল। দ্বিতীয়ত: মগধের রাজা ধননন্দ ছিলেন অত্যাচারী। জনগণ তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। চন্দ্রগুপ্ত এ পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে নন্দদের পরাজিত করে সিংহাসন দখল করেন। তৃতীয়ত: এ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে চন্দ্রগুপ্ত নিজেকে দেশপ্রেমিক হিসাবে তুলে ধরেন। একদিকে বিদেশী শাসনের অবসান এবং অন্যদিকে অত্যাচারী শাসকের উচ্ছেদ উভয় লক্ষ্যেই তিনি জনগণের সাহায্য লাভ করেছিলেন।
পাটলিপুত্র দখলের উদ্দেশ্যে পরিচালিত প্রথম দুটি সরাসরি আক্রমণ ব্যর্থ হয়। এর পর চন্দ্রগুপ্ত কৌটিল্যের সাহায্যে মগধ সাম্রাজ্যের সীমান্ত এলাকা থেকে অভিযান শুরু করেন এবং রাজধানী পাটলিপুত্র অধিকার করতে সক্ষম হন। নন্দ সেনাপতি ভদ্রশাল বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে চন্দ্রগুপ্তকে বাধা দিয়ে পরাজিত হন। পাটলিপুত্রের সিংহাসন দখলের পর চন্দ্রগুপ্ত তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে গ্রিকদেরও বিতাড়িত করেন।
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ছিলেন একজন বিজয়ী বীর। ক্ষমতা লাভের পর তিনি ভারতের এক বিশাল অংশ জুড়ে তাঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্লুর্টাক বলেছেন যে, চন্দ্রগুপ্ত ছয়লক্ষ সৈন্য নিয়ে প্রায় সমগ্র ভারত দখল করেছিলেন। জাস্টিনও বলেছেন যে, চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন ভারতের ‘মালিক’। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিম ভারতের সৌরাষ্ট্রও জয় করেছিলেন।
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের দাক্ষিণাত্য বিজয় নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে চন্দ্রগুপ্ত নয়, দাক্ষিণাত্য জয় করেছিলেন তাঁর ছেলে বিন্দুসার। ভিনসেন্ট স্মিথ এ মতের প্রবক্তা। তিনি বলেছেন যে সাধারণ অবস্থা থেকে সিংহাসন দখল, গ্রিকদের বিতাড়ন, পশ্চিম ভারত জয়, সেলুকাসকে পরাজিত করা- এত কিছু করার পর চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে সুদূর দাক্ষিণাত্য জয় করা সম্ভব ছিল না। বিন্দুসার দাক্ষিণাত্য জয় করেছিলেন এ মতের সমর্থনে তিনি বিন্দুসার ষােলটি রাজ্যের রাজাকে পরাজিত করেছিলেন তারনাথের এ বক্তব্য তুলে ধরেছেন। কিন্তু অধিকাংশ পন্ডিতই স্মিথের এ মত গ্রহণ করেন নি। বিন্দুসার দাক্ষিণাত্য জয় করেছিলেন- এ কথা তাঁরা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, বিন্দুসারের পক্ষে দাক্ষিণাত্য জয় করা সম্ভব ছিল না। কোনাে উৎসেই বিন্দুসারের দাক্ষিণাত্য অভিযানের বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত নেই। তাছাড়া বিন্দুসার যােদ্ধাসুলভ কোনাে গুণেরও অধিকারী ছিলেন না। তাঁর রাজত্বকালে তক্ষশীলায় বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি নিজে বিদ্রোহ দমন করতে না গিয়ে তাঁর ছেলে অশােককে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। যে রাজা নিজের রাজ্যের এক অঞ্চলে বিদ্রোহ দমন করতে যাননি, তিনি পর্বর্তকীর্ণ দুর্গম দাক্ষিণাত্য জয় করেছিলেন এ কথা মেনে নেওয়া কষ্টসাধ্য। তা ছাড়া গ্রিক লেখকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বিন্দুসার ডুমুর ও মিষ্টি মদ পছন্দ করতেন এবং দরবারে বসে পন্ডিত ব্যক্তিদের সাথে দার্শনিক তত্ত্ব আলােচনা করতে ভালােবাসতেন। এ হেন চরিত্রের বিন্দুসার দাক্ষিণাত্য জয় করবেন এটা ভাবা যায়না।
ড. রায়চৌধুরী মনে করেন যে, মৌর্যদের দাক্ষিণাত্য জয় করার কোনাে প্রয়ােজনই ছিলনা। তিনি বলেছেন যে, দাক্ষিণাত্য ছিল নন্দদের সাম্রাজ্যভুক্ত। কাজেই নন্দ রাজাকে পরাজিত করে পাটলিপুত্রের সিংহাসন দখল করার সাথে সাথে নন্দ সাম্রাজ্যের অংশ হিসাবে স্বাভাবিকভাবেই দাক্ষিণাত্য মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এ মতের স্বপক্ষে তিনি গােদাবরী নদীর তীরে নও-নন্দ-দেহরা নামে একটি শহরের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। এ শহরের অস্তিত্ব থেকে তিনি মনে করেন যে, দাক্ষিণাত্যের একটা বিরাট অঞ্চল নন্দ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীন তামিল সাহিত্যেও নন্দদের বিপুল ধন-সম্পদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে দাক্ষিণাত্য কিছুকালের জন্য নন্দদের অধিকারে থাকলেও এমনও হতে পারে যে নন্দদের শাসনকালে বা তাঁদের পতনের পর সে এলাকা স্বাধীন হয়ে যায়। এ কারণেই মৌর্যদের জন্য নতুন করে দাক্ষিণাত্য জয় করা প্রয়ােজন হয়ে পড়ে। ড. কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার বলেছেন যে, একজন প্রাচীন তামিল গ্রন্থকার মৌর্যদের তিনেভেলী জেলা পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। তবে চন্দ্রগুপ্তের নাম উল্লেখ না করে তিনি এ রাজাকে ‘মৌর্যভূঁইফোড়’ বলে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে মনে করা যায় যে, সাধারণ অবস্থা থেকে সিংহাসনে উন্নীত প্রথম মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তকেই বােঝানাে হয়েছে।
মহীশুরে প্রাপ্ত কিছু শিলালিপিতে উত্তর মহীশুরে চন্দ্রগুপ্তের শাসনের উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি শিলালিপিতে বলা হয়েছে যে, শিকারপুর তালুকের অন্তর্গত নাগরখন্ড চন্দ্রগুপ্তের শাসনাধীনে ছিল। মুদ্রারাক্ষসেও চন্দ্রগুপ্তের দাক্ষিণাত্য অধিকারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কাজেই প্লুটার্ক ও জাস্টিনের বর্ণনা, তামিল সাহিত্য এবং মহীশুরে প্রাপ্ত শিলালিপির সাক্ষ্য বিবেচনা করলে মনে হয় যে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যই দাক্ষিণাত্য জয় করেছিলেন।
জৈন কাহিনীগুলােতেও দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের যােগাযােগের উল্লেখ আছে। এ প্রসঙ্গে হরিষেণের বৃহৎ-কথা, কোষ রত্নানন্দের ভদ্রবাহু-চরিত এবং রাজাবলীকথার উল্লেখ করা যায়। ঐ সব গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সিংহাসন ত্যাগ করে একদল জৈন ভিক্ষুর সঙ্গে ভদ্রবাহুর নেতৃত্বে দাক্ষিণাত্যে চলে যান এবং জৈন বিধিমতে অনাহারে মহীশুরের শ্রাবণবেলাগােলায় দেহত্যাগ করেন। সবকিছু বিবেচনা করে আধুনিক পন্ডিতরা মনে করেন যে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যই দাক্ষিণাত্য জয় করেছিলেন।
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য যে পশ্চিম ভারতও জয় করেছিলেন সে সম্পর্কে কোনাে সন্দেহের অবকাশ নেই। পশ্চিম ভারতের সৌরাষ্ট্র তাঁর শাসনাধীন ছিল। মহাক্ষত্ৰপ রুদ্রদামনের ১৫০ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ জুনাগড় প্রস্তরলিপিতে সৌরাষ্ট্রে চন্দ্রগুপ্তের রাষ্ট্রীয় পুষ্যগুপ্ত কর্তৃক বিখ্যাত সুদর্শন হ্রদ খননের উল্লেখ রয়েছে।
রাজত্বের শেষ ভাগে সেলুকাসের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে উত্তর পশ্চিম ভারতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাম্রাজ্যের আরাে বিস্তৃতি ঘটে। সেলুকাস ছিলেন আলেকজান্ডারের একজন সেনাপতি। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর ম্যাসিডনীয় সাম্রাজ্য বিভক্ত হয়ে পড়লে সেলুকাস প্রথমে ব্যাবিলন ও পরে সিরিয়া দখল করেন। এরপর তিনি ভারতে অভিযান পরিচালনা করে আলেকজান্ডারের বিজিত অঞ্চলগুলাে দখল করার চেষ্টা করেন। গ্রিক ঐতিহাসিকদের বিবরণে সেলুকাসের সিন্ধু নদী অতিক্রম ও বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব স্থাপনের উল্লেখ রয়েছে। জাস্টিন চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সেলুকাসের বন্ধুত্ব স্থাপনের কথা বলেছেন। প্লুটার্ক বলেছেন যে চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসকে ৫০০ হাতি উপহার দিয়েছিলেন। স্ট্রাবাে এ বন্ধুত্বের ফলে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন এবং উত্তর পশ্চিম ভারতে আলেকজান্ডারের অধিকৃত চারটি প্রদেশ চন্দ্রগুপ্তকে দানের কথা উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য যে গ্রিক লেখকদের বিবরণে সেলুকাসের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসের মৌর্যের যুদ্ধের কোনাে বিবরণ নেই। তারা শুধু বন্ধুত্ব স্থাপন ও সন্ধির শর্তাবলীর উল্লেখ করেছেন। মনে হয় যে এই অভিযানে সেলুকাস সাফল্য লাভ করতে পারেননি এবং সে কারণেই তিনি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। সেলুকাস তাঁর কন্যাকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন একথা স্মিথ স্বীকার করেন না। কিন্তু ড. রায়চৌধুরী মনে করেন যে জামাতাকে যৌতুক হিসাবেই সেলুকাস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে চারটি প্রদেশ দিয়েছিলেন। এ প্রদেশ চারটি ছিল হিরাট, কান্দাহার, মাকরান এবং বেলুচিস্থান। উত্তর পশ্চিমের এসব এলাকা যে মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল তা অশােকের শিলালিপি দ্বারা প্রমাণিত। বন্ধুত্বের এ সম্পর্কের সূত্রেই সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের দরবারে দূত হিসাবে মেগাস্থিনিসকে পাঠিয়েছিলেন। গ্রিকদের সঙ্গে মৌর্যদের এ কূটনৈতিক সম্পর্ক পরবর্তীকালেও অব্যাহত ছিল।
জৈনগ্রন্থ রাজাবলীকথা অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য জৈন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। রাজত্বের শেষদিকে উত্তর ভারতে এক দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন ত্যাগ করে দাক্ষিণাত্যে চলে যান। মনে হয় এ সময়ই তিনি জৈন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। মহীশুরের অন্তর্গত শ্রাবণবেলগােলায় জৈন বিধি অনুসরণ করে তিনি অনাহারে দেহত্যাগ করেন। দীর্ঘ ২৪ বছর রাজত্বের পর তিনি ২৯৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য শুধু দক্ষ যােদ্ধা ও সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সফল প্রশাসকও।। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশাল সাম্রাজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তিনি একটি সুবিন্যস্ত শাসনব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে জানার অনেকগুলাে উৎস রয়েছে। তাঁর প্রধানমন্ত্রী কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, গ্রিক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণ এবং অশােকের শিলালিপিগুলাে এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযােগ্য। তাছাড়া মহাক্ষত্ৰপ রুদ্রদামনের জুনাগড় প্রস্তরলিপি ও কিছু সাহিত্যিক রচনা থেকেও তাঁর শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা যায়।
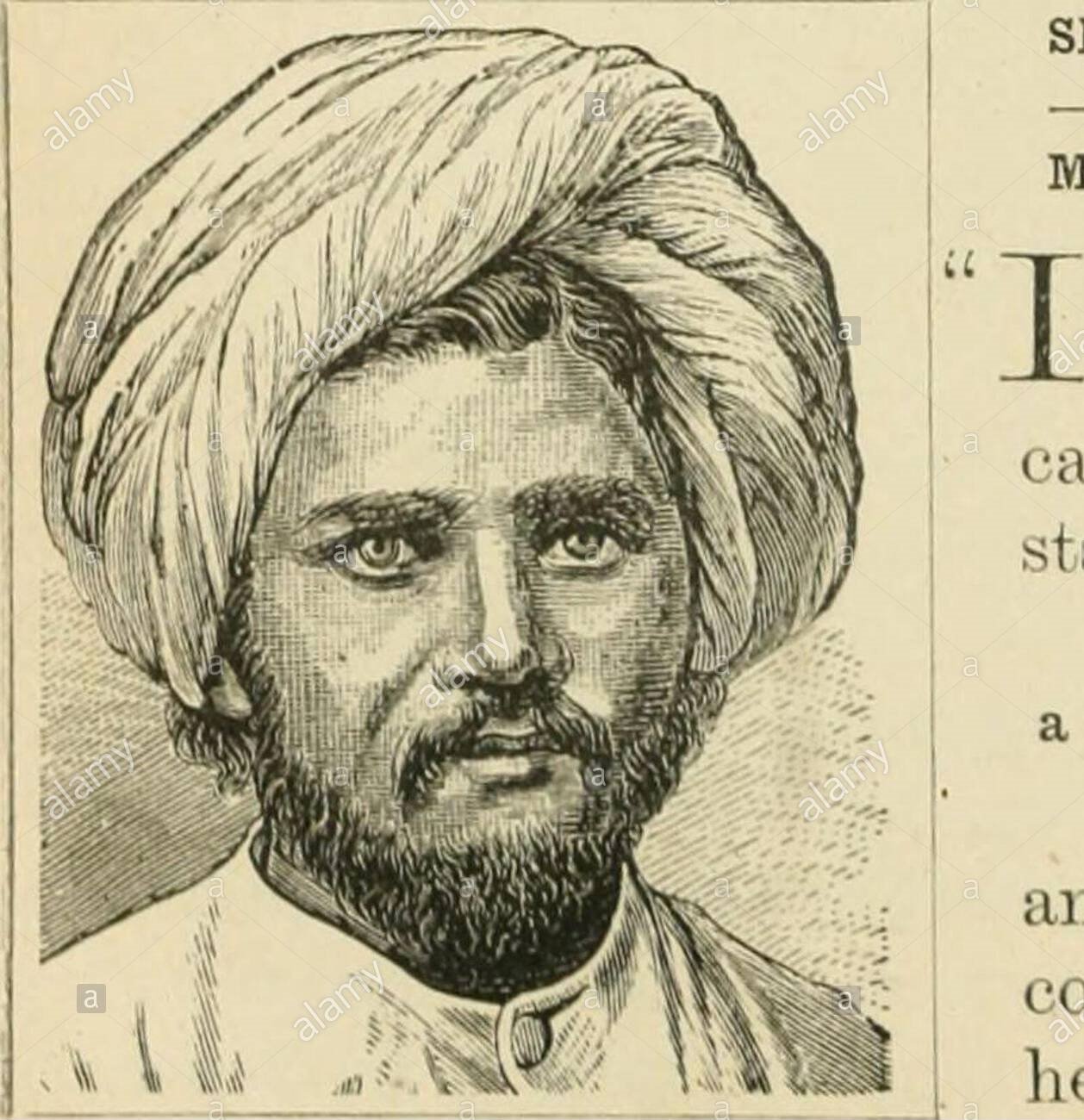
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী কৌটিল্য রচিত অর্থশাস্ত্র চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনব্যবস্থা সম্পকে জানার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এর রচয়িতা এবং রচনাকাল সম্পর্কে পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও এটা যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস সে সম্পর্কে কোনাে সন্দেহ নেই। ১৫টি বিভাগ ও ১৮০টি উপবিভাগে বিভক্ত এ গ্রন্থে প্রায় ৬০০০ শ্লোক রয়েছে। ১৯০৫ সালে আবিষ্কৃত এ গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালে। অর্থশাস্ত্র রাজনীতি সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলােচনা গ্রন্থ নয়। এটা প্রশাসকের জন্য সারগ্রন্থ। এতে সরকারের সমস্যাবলী। এবং সরকারি প্রশাসনিক যন্ত্র ও কার্যাবলী সম্পর্কে আলােচনা রয়েছে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে। জানার গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে গ্রিক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিসের রচিত ইন্ডিকা। মূল গ্রন্থটি পাওয়া না গেলেও স্ট্রাবাে, অ্যারিয়ান, ডিওডরাস-এর মত পরবর্তীকালের লেখকদের উদ্ধৃতি থেকে ইন্ডিকার বিষয়বস্তু। উদ্ধার করা সম্ভব। শােয়ানবেক এগুলাে সংকলন করেছেন এবং ম্যাকক্রিডল এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। প্রাচীনকালে মেগাস্থিনিসের ইন্ডিকাকে নির্ভরযােগ্য বিবেচনা করা হতাে, যেমনটি করেছেন অ্যারিয়ান। তিনি মেগাস্থিনিসকে বিশ্বাসযােগ্য ব্যক্তিরূপে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু স্ট্রাবাে মেগাস্থিনিসের পরস্পর বিরােধী বক্তব্যে নিদারুণ বিরক্ত হয়ে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন। প্লিনির চোখেও তিনি নির্ভরযােগ্য বিবেচিত হননি। বিদেশী পর্যটকদের কিছু সহজাত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তাঁর ইন্ডিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসরূপে বিবেচিত।
অনেকক্ষেত্রেই ইন্ডিকার বিবরণ অর্থশাস্ত্র দ্বারা সমর্থিত। অশােক চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনব্যবস্থায় কিছু কিছু পরিবর্তন করলেও মূল কাঠামাে মােটামুটি আগের মতই ছিল বলে মনে হয়। সে হিসেবে অশােকের লিপিমালা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসরূপে বিবেচিত।
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ও প্রদেশিক – এই দু ভাগে বিভক্ত ছিল। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় তিনটি অংশ ছিল যথা- রাজা, অমাত্য ও সচিব এবং মন্ত্রীপরিষদ। রাজা ছিলেন রাজ্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতাশীল ব্যক্তি। মৌর্য রাজারা নিজেদের দেবতাদের ‘প্রিয়’ রূপে অভিহিত করতেন। বিশাল সাম্রাজ্যের সম্পদের মালিকানা এবং বিশাল সেনাবাহিনীর ওপর কর্তৃত্ব ছিল তার ক্ষমতার উৎস। সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী হলেও রাজাকে কিছু প্রাচীন বিধিনিষেধ মেনে চলতে হত। রাজা প্রজাদের তার সন্তান বলে মনে করতেন। প্রজার মঙ্গল সাধনই ছিল তার কর্তব্য। স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে ক্ষমতার কিছুটা বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা ছিল এবং রাজধানীতে এবং প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলােতে কয়েকজন মন্ত্রী থাকতেন যাদের সঙ্গে আলােচনা করে রাজা তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। তাঁর সামরিক, বিচার বিষয়ক, আইন প্রণয়ন এবং নির্বাহী ক্ষমতা ছিল। সেনাপতির সঙ্গে আলােচনা করে তিনি যুদ্ধপরিকল্পনা তৈরি করতেন। যুদ্ধের সময় তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেও উপস্থিত থাকতেন। বিচারকাজ সম্পাদনের জন্য তিনি দরবারে বসতেন। স্ট্রাবাে বলেছেন যে প্রয়ােজন হলে তিনি ব্যক্তিগত আরাম আয়েশ ত্যাগ করে সারাদিনই দরবারে বিচার কাজে কাটাতেন। দরবারে বিচার কাজে বসলে কৌটিল্য রাজাকে বিচারপ্রার্থীকে অপেক্ষমান না রাখতে বা অন্যের ওপর দায়িত্ব না দিতে সাবধান করে দিয়েছেন। কারণ, এতে জনমনে অসন্তোষ ও শত্রুতার সৃষ্টি হতে পারে যা রাজার বিপদ ডেকে আনতে পারে।
রাজার আইন প্রণয়নের ব্যাপারে আমরা দেখতে পাই যে কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে রাজাকে ‘ধর্মপ্রবর্তক’ বা আইন প্রণেতা বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে ‘রাজ-শাসন’ বা রাজকীয় অনুশাসন ছিল আইনের উৎস। অশােকের শিলালিপিতে উৎকীর্ণ রাজকীয় অধ্যাদেশগুলাে হচ্ছে রাজকীয় অনুশাসনের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। আইন প্রণয়নে তিনি ‘পুরাণ-প্রকৃতি’ অর্থাৎ পুরাতন রীতি-নীতি মেনে চলতেন। প্রহরী নিয়ােগ, রাজ্যের আয়ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষামন্ত্রী, পুরােহিত ও তত্ত্বাবধায়ক নিয়ােগ,মন্ত্রী পরিষদের সঙ্গে আলােচনা, গুপ্তচরদের মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের তথ্য সংগ্রহ এবং বিদেশী দূতদের অভ্যর্থনা জানানাে ইত্যাদি ছিল রাজার নির্বাহী দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। রাজ্যশাসনের মূলনীতিগুলাে রাজা নিজেই ঠিক করতেন। সে মােতাবেক তিনি জনগণ ও কর্মকর্তাদের নির্দেশ পাঠাতেন। গুপ্তচরদের মাধ্যমে রাজা দূরবর্তী এলাকার কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ করতেন।
কৌটিল্য বলেছেন যে এক চাকায় গাড়ী চলেনা – অর্থাৎ রাজার একার পক্ষে সুষ্ঠুভাবে রাজ্যশাসন করা সম্ভব নয়। এজন্য তাঁর সহযােগিতা প্রয়ােজন। কৌটিল্যের উল্লেখিত সচিব বা অমাত্যকেই মেগাস্থিনিস সপ্তম জাতি হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা রাজাকে বিভিন্ন বিষয়ে সহযােগিতা করতেন। তাঁদের সংখ্যা কম হলেও গুরত্ব ছিল অনেক।
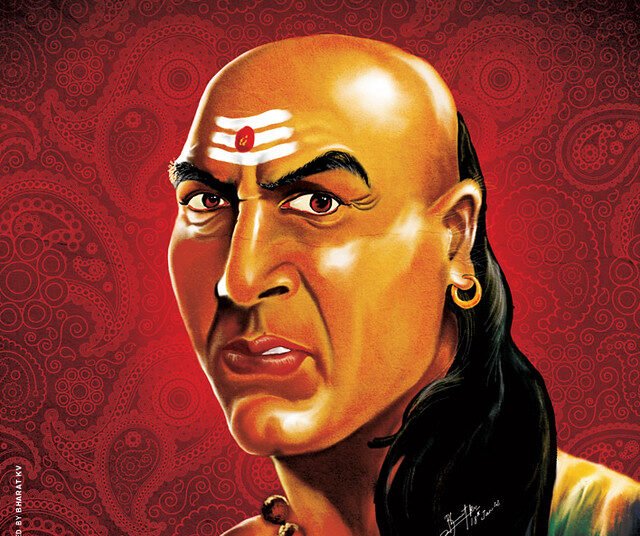
সচিব বা অমাত্যদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন তাদের বলা হতাে ‘মন্ত্রিণ’ বা ‘মহামন্ত্রী’। অশােকের শিলালিপিতে উল্লেখিত মহামাত্রগণই সম্ভবত চন্দ্রগুপ্তের আমলে ‘মন্ত্রিণ’ বা ‘মহামন্ত্রী’ নামে অভিহিত হতেন। তাঁদের বার্ষিক বেতন ছিল ৪৮০০০পাণ (রৌপ্যমুদ্রা)। শাসন সম্পর্কিত কোনাে ব্যবস্থা গ্রহণ করার আগে রাজা তিন-চারজন মন্ত্রিণের সঙ্গে আলােচনা করতেন। জরুরি অবস্থায় মন্ত্রী পরিষদের সঙ্গে মন্ত্রিণগণকেও ডাকা হতাে। মন্ত্ৰিণরা রাজার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতেন এবং সৈন্যদের উৎসাহ দিতেন। যুবরাজদের ওপরেও তাদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ ছিল। কৌটিল্যও এমনি একজন মন্ত্রিণ ছিলেন। মন্ত্ৰিণদের সংখ্যা ছিল একাধিক।
মন্ত্রিণগণ ছাড়াও মন্ত্রীপরিষদ নামে একটি উপদেষ্টা পরিষদ ছিল। মৌর্য শাসন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে এই পরিষদের অবস্থান অশােকের শিলালিপি থেকে প্রমাণিত। মন্ত্ৰিণদের তুলনায় মন্ত্রীপরিষদের সদস্যদের স্থান ছিল নিচে। এই পরিষদের সদস্যদের বার্ষিক বেতন ছিল মাত্র ১২০০০ পাণ। জরুরি পরিস্থিতি এবং শাসন সংক্রান্ত জটিল কাজের সময় রাজা এই পরিষদের পরামর্শ নিতেন। মন্ত্রিপরিষদের মতামত গ্রহণ করা রাজার পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিলনা। তবে কৌটিল্যের মত ক্ষমতাশালী মন্ত্রীর উপস্থিতিতে গৃহীত সিদ্ধান্তকে অবহেলা করাও রাজার পক্ষে সহজ ছিলনা। মন্ত্রীপরিষদ শাসনকাজে রাজাকে সাহায্য করতেন। প্রদেশপাল, উপরাজ্যপাল, কোষাধ্যক্ষ, সেনাপতি,বিচারক প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নিয়ােগের ক্ষেত্রে মন্ত্রীপরিষদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকতাে। বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের অভ্যর্থনা জানানাের সময়ও তাঁরা। রাজার সঙ্গে দরবারে উপস্থিত থাকতেন।
মন্ত্রিণ ও মন্ত্রীপরিষদের সদস্যগণ ছাড়াও তৃতীয় এক শ্রেণীর অমাত্য শাসন ও বিচার বিভাগের উঁচু পদগুলােতে নিযুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তাঁরা নিযুক্ত পেতেন। এদের মধ্যে দেওয়ানী। ও ফৌজদারী আদালতের বিচারক, সমাহর্তী (রাজস্ব আদায় বিভাগের কর্মকর্তা) সন্নিধাত্রী (কোষাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) ও প্রমােদ-উদ্যানের তত্ত্বাবধায়ক উল্লেখযােগ্য।
অন্যান্য পদস্থ রাজকর্মচারীদের মধ্যে পুরােহিতের স্থান ছিল সর্বোচ্চ। তিনি ছিলেন রাজার ধর্মীয় বিষয়ে উপদেষ্টা। রাজদ্রোহের অপরাধেও তাঁকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া যেতাে না। পুরােহিতের পরে স্থান ছিল যুবরাজের। তিনি কার্যনির্বাহী বিভাগের অন্তর্গত কোনাে নির্দিষ্ট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, অথবা সাধারণভাবে শাসনকাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে রাজনৈতিক শিক্ষালাভ করতেন তা স্পষ্ট নয়। সেনাপতি ছিলেন। সেনাবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তবে তিনি সেনাপ্রধান না যুদ্ধমন্ত্রী ছিলেন তা বলা কঠিন। রাজার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকতেন প্রতিহার।
বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব পালন করতেন অধ্যক্ষগণ। এদের মধ্যে উল্লেখযােগ্য ছিলেন নগরাধ্যক্ষ (নগর), বলাধ্যক্ষ (সেনাবিভাগ), সুতাধ্যক্ষ (কৃষি), সূত্রাধ্যক্ষ (বয়ন), শুল্কাধ্যক্ষ (শুল্ক) ইত্যাদি।
মেগাস্থিনিসের বর্ণনা থেকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সামরিক বাহিনীর সংগঠন সম্পর্কে জানা যায়। তার সেনাবাহিনীতে পদাতিক, অশ্বারােহী, রথারােহী ও হস্তি আরােহী সৈন্য ছিল। এছাড়া তাঁর একটি নৌবাহিনীও ছিল। ত্রিশজন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি পরিষদের ওপর ন্যস্ত ছিল সামরিক বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব। এই পরিষদ আবার পাঁচজন সদস্য নিয়ে ছয়টি বাের্ডে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি বাের্ড একটি নির্দিষ্ট বিভাগের দায়িত্বে নিয়ােজিত ছিল যথা: পদাতিক, অশ্বারােহী, যুদ্ধ-রথ, হস্তিবাহিনী, খাদ্য সরবরাহ ও পরিবহণ এবং নৌ-বাহিনী।
রাজধানী পাটলিপুত্রের পরিচালনার ভার ছিল সামরিক পরিষদের মত একটি নগর পরিষদের ওপর। এই পরিষদও প্রতি বাের্ডে পাঁচ জন সদস্য নিয়ে ছয়টি বাের্ডে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি বাের্ড একটি নির্দিষ্ট বিভাগের দায়িত্বে নিয়ােজিত ছিল যথা, শিল্পোৎপাদন, বিদেশী নাগরিক, জন্ম মৃত্যু, খুচরা ব্যবসায়, ওজন ও মাপ, শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রি, এবং বিভিন্ন দ্রব্যের বিক্রিত মূল্যের এক-দশমাংশ কর হিসাবে আদায়। মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের শাসনামলে শুধুমাত্র পাটলিপুত্র নগরের পরিচালনা-ব্যবস্থার বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রধান নগর তক্ষশীলা, উজ্জয়িনী ইত্যাদিতেও অনুরূপ পৌরসংগঠন ছিল বলে মনে করা ভুল হবেনা।
রাজা ছিলেন প্রধান বিচারক। দরবারে বসে তিনি বিচার করতেন। এ ছাড়া শহর ও গ্রামাঞ্চলেও বিচারালয় ছিল। শহরে বিচার করতেন মহামাত্রগণ এবং গ্রামাঞ্চলে বিচার করতেন রাজুকগণ। গ্রিক লেখকদের। বিবরণে বিদেশীদের জন্য পৃথক বিচারকের কথা পাওয়া যায়। অর্থশাস্ত্রে ধর্মীয়-দেওয়ানি আদালতকে ‘ধর্মস্থির’ এবং ফৌজদারি আদালতকে ‘কন্টকশােধন’ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মেগাস্থিনিস এবং কৌটিল্য দুজনই ফৌজদারি আইনের বিশেষ কঠোরতার কথা বলেছেন। জরিমানা ছিল সাধারণ অপরাধের শাস্তি। বড় ধরনের অপরাধের শাস্তি ছিল অঙ্গচ্ছেদ ও শিরচ্ছেদ। অপরাধীর কাছ থেকে স্বীকারােক্তি আদায়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার করা হতাে। দন্ডবিধির কঠোরতার কারণে দেশে সংঘটিত অপরাধের সংখ্যা ছিল কম। গ্রিক লেখকরা বলেছেন যে চুরির ঘটনা ছিল বিরল। বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার সংবাদ, কর্মচারীদের কার্যকলাপ এবং প্রজাদের মনােভাব জানার জন্য বহু গুপ্তচর নিয়ােগ করা হতাে। স্ট্রাবাের মতানুসারে সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তিদেরই গুপ্তচর হিসাবে নিয়ােগ করা হত। অর্থশাস্ত্রে গুপ্তচরদের সংস্থা এবং সঞ্চারা এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যারা নির্দিষ্ট স্থানে থাকত তাঁরা সংস্থা: নামে পরিচিত। তাদের মধ্যে গৃহী, ব্যবসায়ী এবং সন্ন্যাসীরা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এক স্থান থেকে স্থানান্তরে সঞ্চরণরতদের বলা হত সঞ্চারা: এ দলে থাকতাে ভিক্ষুকী সাপুড়ে, পরিব্রাজিকা, গণিকা এবং নর্তকী। স্ট্রাবাে এবং কৌটিল্য, দুজনের বর্ণনাতেই গুপ্তচর বৃত্তিতে বহু সংখ্যক মহিলা নিয়ােগের উল্লেখ রয়েছে।
সাম্রাজ্যের আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমি-কর। গ্রামাঞ্চলে সাধারণত দুধরনের কর ছিল- ভাগ এবং বলি। জমিতে উৎপন্ন ফসলের এক অংশ রাজাকে দিতে হতাে যা ভাগ নামে পরিচিত। সাধারণত এর পরিমাণ ছিল এক-ষষ্ঠাংশ। তবে প্রয়ােজনে এটা এক-চতুর্থাংশে উন্নীত বা এক অষ্টমাংশে হ্রাস করা হতাে। বলি ছিল অতিরিক্ত কর। জমি জরিপ এবং সেচ-ব্যবস্থা তত্ত্বাবধানের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করা হতাে। শহরাঞ্চলে রাজস্ব-আয়ের প্রধান উৎস ছিল জন্ম-মৃত্যু কর, জরিমানা, বিক্রিত দ্রব্যের ওপর কর ইত্যাদি। গণিকা, পানশালা, জুয়ার আড্ডা ইত্যাদি থেকেও রাজ্যের আয় হতাে। বিশাল সাম্রাজ্যের সামরিক ও বেসামরিক ব্যয়ও ছিল বিশাল। বিশাল সৈন্যবাহিনীর জন্য বহু অর্থ ব্যয় হতাে। বেসামরিক প্রশাসনের ব্যয়ও ছিল বিরাট। রাজকীয় কারখানায় নিয়ােজিত কারিগরদের সরকারি কোষাগার থেকে বেতন দেওয়া হতাে। জঙ্গল পরিষ্কার ও বন্যপ্রাণী হত্যার জন্য পশুপলক ও শিকারীদের ভাতা দেওয়া হতাে ব্রাহ্মণ ও শ্ৰমণরা রাজকোষ থেকে অর্থলাভ করতেন। জলসেচ,পথঘাট নির্মাণ, বিশ্রামাগার ও হাসপাতাল স্থাপন ইত্যাদি জনহিতকর কাজেও প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হতাে।
শিল্পসৌধ নির্মান এবং সংরক্ষণ, ধর্মপ্রচার ইত্যাদি কাজেও অর্থব্যয় করা হতাে। গরীব দু:খীকে সাহায্য দান এবং দুর্ভিক্ষজনিত দুর্দশা মােচনেও সরকারি অর্থ ব্যয় করা হতাে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল বিশাল। রাজধানী পাটলিপুত্র থেকে সুষ্ঠুভাবে শাসন করা সম্ভব ছিলনা। তাই তিনি তাঁর সাম্রাজ্যেকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করেছিলেন। রাজা শাসন করতেন কেন্দ্রে আর তাঁর প্রিয় ব্যক্তি প্রদেশপাল হিসাবে প্রদেশ শাসন করতেন। তার সময়ে মৌর্য সাম্রাজ্য কয়টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল তা সঠিকভাবে জানা যায়না। অশােকের শিলালিপিতে উত্তরাপথ, অবন্তীরথ, দক্ষিণাপথ, কলিঙ্গ এবং প্রাচ্য- এই পাঁচটি প্রদেশের উল্লেখ দেখা যায়। এগুলাের রাজধানী ছিল যথাক্রমে তক্ষশীলা, উজ্জয়িনী, সুবৰ্ণগিরি, তােসালী এবং পাটলিপুত্র। কলিঙ্গ অবশ্য বিজিত হয়েছিল অশােকের আমলে বাকি চারটি প্রদেশে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলে তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল বলে মনে করা হয়। দূরবর্তী প্রদেশগুলােতে সাধারণত রাজকুমারদের প্রদেশপাল হিসাবে নিয়ােগ কর হতাে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হতে জানা যায় যে ‘কুমার’ উপাধিকারী এ সব প্রদেশপালের বার্ষিক বেতন ছিল ১২০০০ পাণ। সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত প্রাচ্য প্রদেশটি ছিল সম্রাটের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন। এই প্রদেশের শাসনকাজে তাঁকে সাহায্য করার জন্য তিনি পাটলিপুত্র, কৌশাম্বী ইত্যাদির মত গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলােতে মহামাত্র নিয়ােগ করেন।

প্রদেশগুলাে কতগুলাে জনপদে বিভক্ত ছিল। জনপদের শাসন পরিচালনা করতেন সমাহর্তী। জনপদের একচতুর্থাংশের শাসনভার ছিল স্থানিক নামক কর্মচারীর ওপর ন্যস্ত। প্রদেষ্ট্রি নামক এক শ্রেণীর কর্মচারী ছিল সমাহর্জীর ভ্রাম্যমাণ সহকারী। পাঁচ থেকে দশটি গ্রামের শাসনভার ছিল গােপ নামক কর্মচারীর ওপর ন্যস্ত। প্রতি গ্রামের অধিবাসীরা গ্রামিক উপাধিকারী একজন কর্মচারীকে নির্বাচিত করতেন যার ওপর গ্রামের শাসনভার ন্যস্ত ছিল।
জৈন কাহিনী অনুসারে রাজত্বের শেষভাগে উত্তর ভারতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং জৈন সন্ন্যাসী ভদ্রবাহুকে অনুসরণ করে মহীশুরে চলে যান। মহীশুরের অন্তর্গত শ্রাবণবেলগােলায় ২৯৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে জৈন বিধি অনুসারে অনাহারে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য প্রাণত্যাগ করেন।
খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে ব্যাবিলনে আলেকজান্ডারের মৃত্যু হলে ভারতে তাঁর অধিকৃত অঞ্চলে গ্রিক গভর্নরদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এ সময়ে মগধে নন্দবংশীয় সম্রাট ধননন্দ রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে জনগণ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সুযােগ গ্রহণ করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য প্রথমে ধননন্দকে পরাজিত করে মগধের সিংহাসন আরােহণ করেন। অত:পর তিনি গ্রিকদের বিতাড়িত করে ভারতে এক বিশাল সামাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এ কাজে তিনি তক্ষশীলার ব্রাহ্মণ পন্ডিত কৌটিল্যের সহযােগিতা লাভ করেছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যই ইতিহাসে মৌর্য সাম্রাজ্য নামে বিখ্যাত। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য শুধু দক্ষ যােদ্ধা ও বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন না, তিনি একজন সফল প্রশাসকও ছিলেন। অধীনস্ত সাম্রাজ্যকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তিনি একটি সুবিন্যস্ত শাসনব্যবস্থাও প্রবর্তন করেন, যা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক- এই দুভাগে বিভক্ত ছিল। সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হলেও রাজাকে কিছু প্রাচীন বিধিনিষেধ মেনে চলতে হতাে। জৈন কাহিনী অনুসারে রাজত্বের শেষভাগে উত্তর ভারতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং জৈন সন্ন্যাসী ভদ্রবাহুর নেতৃত্বে একদল জৈন ভিক্ষুর সাথে মহীশুরে চলে যান। ২৯৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে শ্রাবণবেলগােলায় জৈন বিধি অনুসারে অনাহারে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।
আরও পড়ুন,
১। সাতবাহন রাজবংশঃ ইতিহাস ও তার রাজনৈতিক মূল্যায়ন
২। হিন্দু মন্দির ধ্বংস ও ভারতে মুসলিম প্রশাসনঃ একটি ঐতিহাসিক পুনর্মূল্যায়ন
৩। মুহাম্মদ বিন তুঘলক কি পাগল ছিলেনঃ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ
৪। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক ও তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাঃ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ
‘নবজাগরণ’ অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপ্লিকেশনটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।
‘নবজাগরণ’ এর টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।
‘নবজাগরণ’ এর ফেসবুক পেজে লাইক করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

 নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা
নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা