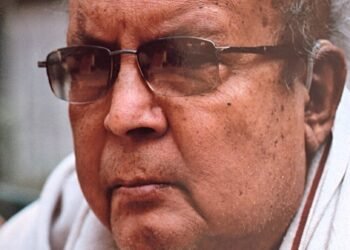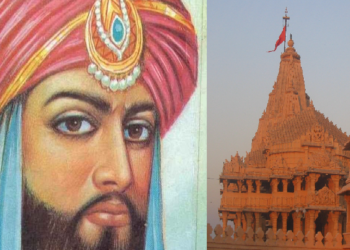বিহারের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের জন্য বখতিয়ার খলজির নির্মম আক্রমণকে দায়ী করা হয়। এ তথ্য সর্বাংশে সত্য নয়। তবে এই আলােচনায় প্রবেশের পূর্বে আমরা নালন্দার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরতে পারি। বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদানের ভিত্তি বিশ্লেষণ করে নালন্দার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতাব্দী থেকে। তখন নালন্দা ছিল একটি সমৃদ্ধ শহর। কিন্তু নালন্দার অবস্থান নিয়ে ঐতিহাসিকেরা সহমত হতে পারেননি। বিভিন্ন তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে পার্ববর্তী অনেক স্থানের সঙ্গে নালন্দাকে সনাক্ত করেছেন ঐতিহাসিকেরা। কিন্তু এইসব তথ্য প্রমাণ থেকে নালন্দার সঠিক সনাক্তকরণ সহজসাধ্য নয়। কারণ অনেক তথ্যই পরস্পর বিরােধী। তবে পালিবৌদ্ধ সাহিত্য ও জৈন উপাদান থেকে নালন্দার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, সে নালন্দা এবং বর্তমান নালন্দা মােটামুটিভাবে একই, যা কিনা বিহার রাজ্যের রাজগীর শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত।

বৌদ্ধ সংঘের সংস্কৃত বা পালি প্রতিশব্দ হল বিহার, যার প্রকৃত অর্থ বৌদ্ধ ভিদের আশ্রয়স্থল। এইসব বিহারের অনেকগুলি পরবর্তীকালে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল, তার মধ্যে কয়েকটি আবার বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল, যেমন নালন্দা। এই নালন্দার উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। কারণ ফা-হিয়েন যখন নালন্দাতে আসেন, তখন সেখানে কোনাে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল না। বি এন মিশ্র, নালন্দা সাের্সের্স অ্যান্ড ব্যাক গ্রাউন্ড, খণ্ড-১, বি আর পাবলিশিং কর্পোরেশন, ১৯৯৮, পৃ. ১৮১)। গুপ্তযুগে নালন্দা বিহার থেকে মহাবিহারে রূপান্তরিত হয়েছিল মূলত রাজকীয় অনুদানের দ্বারাই। আর কোনাে মহাবিহার নালন্দার মত রাজকীয় অনুদান পায়নি। কারণ নালন্দা ছিল বিশ্বমানের শিক্ষাক্ষেত্র। পাল রাজারাও ছিলেন নালন্দার পৃষ্ঠপােষক। পাল শাসনকালেই নালন্দা খ্যাতির চরম শিখরে পৌঁছেছিল। এই পাল রাজারা ছিলেন মহাযান বৌদ্ধধর্মের অনুসারী আর নালন্দা ছিল তাঁদের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র, যার ফলে তাঁরা মুক্তহস্তে নালন্দাতে দান করছিলেন। সেই সময় নালন্দাতে ভারতের বাইরের বিভিন্ন দেশ থেকেও শিক্ষার্থীরা আসতাে, যারা জ্ঞানার্জনের শেষে প্রচুর আর্থিক সাহায্য নালন্দাকে দিয়ে যেত—নালন্দার সমৃদ্ধির এটাও একটা অন্যতম প্রধান কারণ বলা যেতে পারে। এখানে প্রায় ১০,০০০ ছাত্র বসবাস করত ও অধ্যয়ন করত। (নালন্দা উৎখননের ফলে যে বাড়িগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে দশ হাজার ছাত্রের থাকার ব্যবস্থাকে সমর্থন করা যায় না। ৬৭০ সালে ইৎ-সিং নামে অপর এক চীনা পরিব্রাজক নালন্দা পরিদর্শন করেন। তার মতে, এখানে তিন হাজার ভি থাকত। ইৎ-সিং এর বক্তব্যই বেশি সমর্থনযােগ্য ও যুক্তিসম্মত বলে মনে করেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা। দেখুন- রামশরণ শর্মা, ভারতের প্রাচীন অতীত, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসােয়ান, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১১, পৃ. ২৬৭)। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ স্বয়ং নালন্দার অধ্যক্ষ শীলভদ্রের কাছে পড়াশুনাে করতেন। তাঁর মতে, ভারতে তখন হাজার হাজার শিক্ষাকেন্দ্র ছিল কিন্তু শিক্ষণীয় বিষয়ের বৈচিত্র্য, শিক্ষা পদ্ধতির উৎকর্ষে ও বিশালত্বে নালন্দার স্থান ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। (আর সি মজুমদার, এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া, দিল্লি, ১৯৭৪, পৃ. ৪৫২-৫৪)।
আধুনিক গবেষকদের অনেকেই মনে করেন যে, নালন্দা মহাবিহারকে আর যাই হােক বিবিদ্যালয় বলে অভিহিত করা যায় না। এখানে একটা বিশাল শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল, যা প্রায় ৮০০ বছর (পঞ্চম থেকে ত্রয়ােদশ শতক) ধরে সমগ্র এশিয়ায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। এখানকার সুবৃহৎ গ্রন্থাগারটিও ছিল বিখ্যাত। এই মহাবিহারে বহু ছাত্র আবাসিক জীবনযাপন করে শিক্ষালাভ করত। এমন সব তথ্যের ভিত্তিতে নালন্দার শিক্ষায়তনটিকে বিশ্ববিদ্যালয় ভেবে ফেলা হয়েছে। টোল-চতুষ্পঠী জাতীয় বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতে গড়ে উঠেছিল, একথা সত্যি। মুসলিম বাদশাহদের আমলেও মাদ্রাসা-মক্তব জাতীয় বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু আধুনিক স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির মতাে শিক্ষায়তন প্রাচীন ও মধ্যযুগে শুধু ভারতে কেন ইউরােপেও গড়ে উঠেনি, গড়ে উঠবার মত বাস্তব পরিস্থিতিও তখন পর্যন্ত তৈরি হয়নি। পঞ্চম থেকে ত্রয়ােদশ শতক পর্যন্ত ভারতে স্মৃতিশাস্ত্র অনুমােদিত জাতিভেদ প্রথা যেভাবে জাঁকিয়ে বসেছিল তাতে এমনিতেই সমাজের তিন-চতুর্থাংশ লােকের বিদ্যাশিক্ষার কোনাে অধিকারই ছিল না। ব্রাহ্মণদেরও গরিষ্ঠ অংশ পূজা-পাঠ-পৌরহিত্য-জ্যোতিষচর্চা করেই সন্তুষ্ট ছিল। সত্যি কথা বলতে উনিশ শতকের শেষ কিংবা বিশ শতকের গােড়া পর্যন্তও নালন্দা-তক্ষশীলা-বিক্রমপুরের মত প্রাচীন বিধবিদ্যালয়গুলির কথা কারাের মাথাতে আসেনি।
যাই হােক, এমনও সাম্প্রতিক তথ্য আমাদের সামনে আসছে যে, বখতিয়ার খলজি নালন্দায় কোনােদিন যাননি। ঐতিহাসিক কে কে কানুনগাে জার্নাল অফ দ্য এশিয়াটিক সােসাইটি অফ বেঙ্গল-এ প্রকাশিত শরৎচন্দ্র দাশের ‘অ্যান্টিকুইটি অফ চিটাগাঁও’ প্রবন্ধ থেকে জানাচ্ছেন যে, কামিরের বৌদ্ধ পণ্ডিত শাক্য শ্রীভদ্র ১২০০ সালে মগধে গিয়ে দেখেছিলেন বিক্রমশীলা ও ওদন্তপুরী বিহার ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তুর্কিদের ভয়ে শ্রীভদ্র ও ওই বিহার দুটির ভিক্ষুরা বগুড়া জেলার জগদ্দল বিহারে আশ্রয় নেন। (নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালির ইতিহাস, আদিপর্ব, দে’জ পাবলিশিং হাউস, ৭ম সংস্করণ, কলকাতা, ১৪১৬, পৃ. ৪১১)। কিন্তু শরৎচন্দ্র দাশ তার উক্ত প্রবন্ধে এমন কথা বলেননি যে, ১২০০ সালে বিক্রমশীলা ও ওদন্তপুরী বিহার দুটিকে ধ্বংস করা হয়েছিল। বরং তিনি তাঁর সম্পাদিত তিব্বতীয় শাস্ত্র ‘পাগসাম ইয়ান জাং’-এ বলেছেন, বিহার দুটি ধ্বংস হয়েছিল ১২০২ সালে। ফলে শাক্য শ্রীভদ্র জগদ্দল বিহারে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই ঘটনা বখতিয়ারের বিহার অভিযানের (১২০৩) পূর্বেকার। আর এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় হল, ক্ষতিগ্রস্ত বিহারগুলির মধ্যে নালন্দার নাম নেই। তাছাড়া মিনহাজ বা অন্য কোনাে সূত্রেও নালন্দা ধ্বংসের কথা বলা হয়নি। ১২৩৪-৩৬ সালে অর্থাৎ বখতিয়ারের বিহার জয়ের ৩১ বছর পর তিব্বতী সাধু ধর্মস্বামী মগধে আগমন করেন ও সেখানে অবস্থান করেন। নালন্দা মঠকে তিনি তখন চালু অবস্থায় দেখতে পান। সেখানে মঠাধ্যক্ষ রাহুল শ্রীভদ্রের পরিচালনায় সত্তর জন সাধু অধ্যয়নে নিয়ােজিত ছিলেন এবং তিনি নিজে ছমাস সেখানে জ্ঞানার্জন করেন। তাহলে বিষয়টা দাঁড়াল এই যে, বখতিয়ারের আক্রমণে নালন্দা সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বলে যে প্রচারণা ছিল ধর্মামীর বিবরণে তার উল্লেখ নেই। তবে তিনি বিক্রমশীলা মহাবিহারকে সম্পূর্ণ ধ্বংস অবস্থায় ও ওদন্তপুরীকে তুর্কি সামরিক ঘাঁটি রূপে দেখতে পান। (জি রােয়েরিখ সম্পাদিত, বায়ােগ্রাফি অফ ধর্মস্বামী, কে পি জয়সওয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পাটনা, ১৯৫৮, পৃ. ৬৪, ৯০-৯৩ )।

তাহলে নালন্দা ধ্বংস হল কিভাবে? এটা পূর্বে উল্লেখিত হিন্দু ও বৌদ্ধ সংঘাতের ফলশ্রুতি নয় তাে? কিংবদন্তি ও জনশ্রুতিতেও অনেক ঐতিহাসিক সত্য লুকিয়ে থাকে। বুদ্ধগয়া নালন্দা ও রাজগীরে বিখ্যাত তীর্থস্থান অথবা ধ্বংসাবশেষের উপরে লিখিত একটি পরিচিতি পুস্তিকায় এর কিছুটা আঁচ পাওয়া যাবে। যদিও সে বর্ণনায় কিছুটা অলৌকিকত্বের তত্ত্ব ঢােকানাে হয়েছে। বখতিয়ার খলজির আক্রমণ তত্ত্বের সাথে কোনও ভনিতা না করে পুস্তিকাটিতে এ তথ্য সংযােজিত হয়েছে “পঞ্চম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ দার্শনিক এবং প্রচারক কুমার ভট্ট এবং শংকরাচার্যের প্রচেষ্টাতেই বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল। প্রবাদ আছে, তারা সারা ভারতে পরিভ্রমণ করে বৌদ্ধ পন্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করে ধর্মান্তরিত করেন।…একদিন ঐ মন্দিরে যখন শাস্ত্র চর্চা চলছিল তখন দুজন কোমল স্বভাবের ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত হন। কয়েকটি অল্প বয়স্ক ভি; তাঁহাদের উপর পরিহাসােচ্ছলে জল ছিটিয়ে দেন। এতে তাঁদের ক্রোধ বেড়ে যায়। বারাে বৎসরব্যাপী সূর্যের তপস্যা করে তাঁরা যজ্ঞাগ্নি নিয়ে নালন্দার প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারে এবং বৌদ্ধ বিহারগুলিতে অগ্নিসংযােগ করেন। ফলে নালন্দা অগ্নিসাৎ হয়ে যায়।” (বুদ্ধগয়া গয়া-দর্শন রাজগীর নালন্দা পর্যটক সহায়ক পুস্তিকা, পৃ. ১৬-১৭, দ্রঃ-আমীর হােসেন, বাঙালীর বিভাজন, অনুষ্টুপ, বিশেষ শীতকালীন সংখ্যা ১৪০৮, কলকাতা)। তবে তিব্বতীয় শাস্ত্র ‘পাগসাম ইয়ান জাং’-ও ‘উগ্র হিন্দুদের হাতে নালন্দার গ্রন্থাগার পােড়ানাে হয়েছে বলে উল্লেখ করেছে। (বি এন এস যাদব, সােসাইটি অ্যান্ড কালচার ইন নর্দার্ন ইন্ডিয়া ইন দ্য টুয়েলভথ সেঞ্চুরি, এলাহাবাদ, ১৯৭৩, পৃ. ৩৪৬)। ডি আর পাতিল অবশ্য খুব পরিষ্কার করে বলেছেন যে, ওটা ধ্বংস করেছিল শৈবরা। (ডি আর পাতিল, অ্যান্টিকোয়ারিয়ান রিমেইন অফ বিহার, পাটনা, ১৯৬৩, পৃ.৩০৪)। এই মতের দীর্ঘ আলােচনা করেছেন আর এস শর্মা এবং কে এম শ্রীমালি। (আর এস শর্মা ও কে এম শ্রীমালি, এ কমপ্রিহেনসিভ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, খণ্ড৪, ভাগ-২ (৯৮৫-১২০৬), অধ্যায় ২৫-খ বৌদ্ধধর্ম, পাদটীকা, পৃ. ৭৯-৮২)।
বিশিষ্ট তাত্ত্বিক লেখক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত নালন্দা মহাবিহার ধ্বংসের জন্য ব্রাহ্মণ্যবাদীদের আক্রমণকে মান্যতা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন “নালন্দার লাইব্রেরী কয়েকবার বিধ্বস্ত হয়। P. al. Jor-এর তিব্বতীয় পুস্তকে উল্লিখিত হয়েছে যে ধর্মর্সগন্ধ অর্থাৎ নালন্দার বৃহৎ লাইব্রেরী তিনটি মন্দিরে রথিত ছিল। তীর্থিক (ব্রাহ্মণ) ভি দের দ্বারা অগ্নিসংযােগে তাহা ধ্বংস করা হয়। মগধের রাজমন্ত্রী কুকুতসিদ্ধ নালন্দায় একটি মন্দির নির্মাণ করেন। সেখানে ধর্মোপদেশ প্রদানকালে জনকতক তক্ষণ ভিক্ষু দু’জন তীর্থিক ভি দের গায়ে নােংরা জল নিক্ষেপ করে। তার ফলে তারা ক্রুদ্ধ হয়ে ‘রত্নসাগর’, ‘রত্নধনুক’ আর নয় তলাযুক্ত ‘রত্নদধি’ নামক তিনটি মন্দির অগ্নিসংযােগে ধ্বংস করে। উক্ত তিনটি মন্দিরেই সমষ্টিগতভাবে ধর্মগ্রন্থ বা গ্রন্থাগার ছিল।” (ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বাঙ্গলার ইতিহাস, চিরায়ত প্রকাশন, প্রথম পরিমার্জিত সংস্করণ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৮৬। আরও দেখুন- P. al. Jor.: History of the Rise, Progress and Downfall of Buddhism in India, Edited by S. Das, P. 92).
ষষ্ঠ শতকের রাজা মিহিরকুল বৌদ্ধদের সহ্য করতে পারতেন না। তিনি যখন পাটলিপুত্র আক্রমণ করেন তখন সম্ভবত নালন্দা মহাবিহার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এইচ হিরাস এ বিষয়ে লিখেছেন ‘Nalanda University was not far from the capital, Pataliputra and its fame had also reached Mihirakula’s ears. The buildings of Nalanda were then probably destroyed for the first time, and its priests and students dispersed and perhaps killed.’ (এইচ হিরাস, দ্য রয়েল পেট্রনস্ অফ দ্য ইউনিভার্সিটি অফ নালন্দা, জার্নাল অফ দ্য বিহার অ্যান্ড উড়িষ্যা রিসার্চ সােসাইটি, পার্ট-১, খণ্ড-১৪, ১৯২৮, পৃ. ৮-৯)। এরপর সপ্তম শতকের মাঝামাঝি মগধে সংঘটিত যুদ্ধবিগ্রহের শিকারও হতে পারে নালন্দা। ঐতিহাসিক এস এন সদাশিবন নালন্দা ধ্বংসের জন্য মুসলমান ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। (এস এন সদাশিবন, এ সােস্যাল হিস্টরি অফ ইন্ডিয়া, নিউদিল্লি, ২০০০, পৃ. ২০৯)। বুদ্ধ প্রকাশ তাঁর ‘অ্যাসপেক্ট অফ ইন্ডিয়ান হিস্টরি অ্যান্ড সিভিলাইজেশন’ গ্রন্থে (আগ্রা, ১৯৬৫) নালন্দায় অগ্নি সংযােগের জন্য হিন্দুদেরই দায়ী করেছেন। অথচ এতদিন আমরা নালন্দা মহাবিহার ধ্বংসের জন্য মােহাম্মদ বখতিয়ার খলজিকেই অভিযুক্ত করে এসেছি।
শুধু তাই নয়, ময়নামতী মহাবিহারও (অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার অন্তর্গত পাহাড়পুর গ্রামে অবস্থিত ময়নামতী) ধ্বংস হয় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাতে। নালন্দার মতাে এৰেত্রেও দায়ী করা হত মূলত মুসলিম আক্রণকারীদের। একাদশ শতকের শেষভাগে বৌদ্ধ চন্দ্রবংশ উৎখাত করে অবিভক্ত দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্মণ রাজবংশ। এই বংশেরই অন্যতম শাসক ছিলেন জাতবর্মা। রাজ্য বিস্তারের লতের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল সােমপুর মহাবিহারের প্রতি। তিনি অচিরেই বৌদ্ধবিহারটি আবদ্ধ এবং লুণ্ঠন করেন। অবশেষে অগ্নি সংযােগে মহাবিহারটি ধ্বংস করেন। (এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা, খণ্ড-২১, বিপুলশ্রী মিত্রের নালন্দা তাম্রশাসন, পৃ. ৯৭)। ওই বিহারের মঠাধ্যক্ষ সুপণ্ডিত কক্ষণাশ্রী মিত্রকেও তিনি অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করেন। (এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা, খণ্ড-২১, বিপুলশ্রী মিত্রের নালন্দা তাম্রশাসনের দ্বিতীয় পংক্তি দ্রষ্টব্য)। ভােজবর্মার বেলাবলিপি থেকেও জানা যায়, পরম বিষুক্ষভক্ত জাতবর্মা সােমপুরের মহাবিহার ধ্বংস করেছিলেন। বৌদ্ধ নিপীড়নের কিছু নমুনা প্রসঙ্গে বিখ্যাত সােমপুর মহাবিহার ধ্বংসের কথা নীহাররঞ্জন রায় এভাবে উল্লেখ করেছেন। “…ভারতীয় কোনও রাজা বা রাজবংশের পক্ষে পরধর্মবিরােধী হওয়া অস্বাভাবিক। এ যুক্তি অত্যন্ত আদর্শবাদী যুক্তি, বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি তাে নয়ই। অন্যকাল এবং ভারতবর্ষের অন্য প্রান্তের বা দেশখণ্ডের দৃষ্টান্ত আলােচনা করিয়া লাভ নাই প্রাচীনকালের বাঙলাদেশের কথাই বলি। বঙ্গাল-দেশের সৈন্য-সামন্তরা কি সােমপুর মহাবিহারে আগুন লাগায় নাই? বর্মণ রাজবংশের জনৈক প্রধান রাজকর্মচারী ভট্টভবদেব কি বৌদ্ধ পাষন্ড বৈতালিকদের উপর জাতক্রোধ ছিলেন না? সেন-রাজ বল্লাল সেন কি নাস্তিকদের (বৌদ্ধ) পদোচ্ছেদের জন্যই কলিযুগে জন্মলাভ করেন নাই?” (নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৬ ও পৃ. ৪১৯, ৩০২)।
আরও পড়ুন,
১) আলাউদ্দিন খিলজি ও রানী পদ্মাবতীর আখ্যান : ইতিহাসের পুনর্বিচার
২) শ্যামাপ্রসাদ এর সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও পশ্চিমবঙ্গের জন্ম
৩) ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুঘল সম্রাট বাবর ও তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতা
৪) দ্বিশতবর্ষে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : নতুন ভাবনা ও বিশ্লেষণ
‘নবজাগরণ’ অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপ্লিকেশনটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

 নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা
নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা