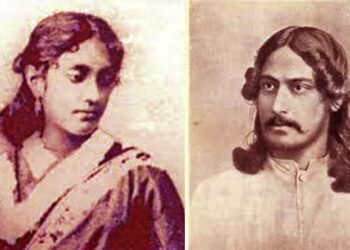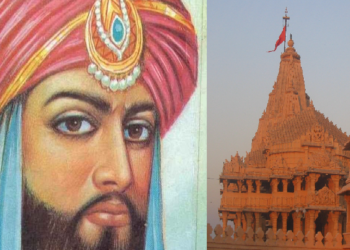বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যিনি একদিকে আধুনিক শিল্প-সাহিত্যের জগতে বিচরণ করেছেন সবলীলভাবে, পাশাপাশি রাষ্ট্রিক-সামাজিক ক্ষেত্রে লাভ করেছেন ঈর্ষণীয় সাফল্য, তিনি হচ্ছেন হুমায়ুন কবীর (১৯০৬-১৯৬৯)। বাঙালি ও মুসলমান পরিচয় ধারণা করেই তিনি ছিলেন সর্বভারতীয়ত্বের প্রতীক—এও এক তুলনারহিত দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর মাত্র তিনজন ভারতীয় পরে বিশ্বের দরবারে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতেন। তারা হলেন সর্বপল্লী রাধাকৃষান, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও হুমায়ুন কবীর। পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও আদর্শগত কারণে দেশ বিভাজনের পর ভারতের মাটিকেই হুমায়ুন কবীর পাকাপােক্ত ভাবে বেছে নিয়েছিলেন। দেশের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে তিনি দীর্ঘদিন সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। দেশ স্বাধীন হবার পর কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মাওলানা আবুল কালাম আজাদের (১৮৮৮১৯৫৮) প্রধান সহকারী হয়েছিলেন। ১৯৫৭ সালে ক্যানবেরায় বির্ষের প্রথম পূর্ব-পশ্চিম দর্শন সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ভারত সরকারের (জওহরলাল নেহরুর মন্ত্রীসভায়) শিক্ষা, অসামরিক বিমান চলাচল, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি বিষয়ক এবং পেট্রোলিয়াম-রসায়ন দপ্তরের মন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছেন।
জওহরলাল নেহেরুর মৃত্যুর (১৯৬৪) পর প্রথমে লালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং পরে নেহেরু কন্যা ইন্দিরা গান্ধী (১৯১৭১৯৮৪) প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৬৭তে ইন্দিরা গান্ধী তার মন্ত্রীসভা রদবদল করেন এবং বাদ দেন কবীরকে। অবশ্য তাকে মাদ্রাজের গভর্ণর পদের প্রস্তাব দেওয়া হয়। সে প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন ক্ষুব্ধভাবে। চলে আসেন পশ্চিমবঙ্গে যােগ দেন অজয় মুখার্জির বাংলা কংগ্রেসে। সেবার পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করতে পারল না। কিন্তু তাই বলে কংগ্রেস বিহীন সরকার গঠিত হবে এটা ছিল অনেকটা অভাবিত। সেই কাজটিই করলেন হুমায়ুন কবীর মাত্র সাতদিনের মধ্যে। (এই ইতিহাসের নাটকীয় বর্ণনা পাওয়া যাবে বরুণ সেনগুপ্তের ‘পালাবদলের পালা’ গ্রন্থে)। বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে স্বাধীন ভারতে ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার শপথ গ্রহণ করল। ‘যুক্তফ্রন্ট’ নামটিও হুমায়ুন কবীরের দেওয়া। তিনি নিজে মন্ত্রীত্ব নিলেন না বটে তবে তার ভাই জাহাঙ্গীর কবীরকে মন্ত্রী করেছিলেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের পর পর কবির ইউরােপে যান কিছুকালের জন্য। যাওয়ার সময় বন্ধু-বান্ধবদের বলেন—
“আজ বাংলাদেশে যা করে দিয়ে গেলাম ভবিষ্যতে ভারতেও তাই হবে। এই শুরু হল যুক্তফ্রন্ট রাজনীতির যুগ। সমগ্র ভারতবর্ষ এই রাজনীতিকে অনুসরণ করবে।”
আজকেও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের দিকে নজর দিলে কবীরের এই ভবিষ্যৎবাণীর সত্যতা মিলবে।
দর্শন ও ইংরেজি সাহিত্যে হুমায়ুন কবীরের পান্ডিত্য ছিল সর্বজনবিদিত। ১৯২৪ সালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমগ্র মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান লাভ, ইংরেজিতে পেলেন সর্বোচ্চ নম্বর। ডাক প্রাইজ ও সরকারি বৃত্তি লাভ করলেন। কলকাতা বিবিদ্যালয়ে অনার্স নিলেন ইংরেজিতে। ১৯২৬ সালে বি এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করলেন। এই প্রথম কোনাে মুসলমান ছাত্র এমন কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন। কলকাতা বিবিদ্যালয়ে ইংরেজিতে এম.এ-তেও তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হলেন। ইতিপূর্বে মুসলমানদের মধ্যে শুধু স্যার আবদুর রহিম ১৮৮৬ সালে অনুরূপ কৃতিত্ব অর্জন করেন। তবে হুমায়ুন এক্ষেত্রে প্রথম বাঙালি মুসলমান। এশিয়দের ভিতর তিনিই সর্বপ্রথম অক্সফোর্ডের মডার্ন গ্রেটস’ (দর্শন, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান) পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেন। দেশে ফিরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯৪০ অবধি ওই পদে আসীন ছিলেন। এশিয়বাসীর মধ্যে তিনিই প্রথম অক্সফোর্ড হারবার্টস স্পেন্সর বক্তৃতা দেন। যেখানে তার আগে আইনস্টাইন, বারট্রান্ড রাসেলের মতাে কেবল ইউরােপীয় মনীষীরা সেই বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ১৯৬১ সালে গ্রীসের ‘পিংকা’ মঞ্চ থেকে বক্তৃতা দিয়েছিলেন হুমায়ুন কবীর। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পরে তিনিই একমাত্র ভারতীয় যাঁর ভাগ্যে এই দুর্লভ সুযােগ এসেছিল। ইউরােপ, আমেরিকা ও এশিয়ার অনেক বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করেন।
হুমায়ুন কবীরের সাহিত্যবােধ ও বিশ্লেষণী শক্তি যে কত উঁচুমানের ছিল তা তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালােচনামূলক রচনা পাঠ করলে বিস্ময়ের সাথে আমরা অবলােকন করবাে। বস্তুত বাংলা সাহিত্যের এই বিভাগে তার একটি স্থায়ী আসন থাকবে। প্রথমেই উল্লেখ্য ‘বাংলার কাব্য’ গ্রন্থটি (১৯৪১)। একথা ঠিক যে, ‘বাংলার কাব্য’—এই একটি মাত্র । পুস্তক বাংলা সাহিত্যে হুমায়ুন কবিরের অমরত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট ছিল। বইটিতে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা কাব্যধারার বিকাশের ইতিহাস রচনা করা হয়েছে। এই সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে অতি অবশ্যই ভৌগােলিক ঐতিহাসিক তথ্যও ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করা হয়েছে। বৈষ্ণব কাব্যকে তিনি শুধু বাংলার নয় সমগ্র ভারতবর্ষেরই প্রথম সার্থক ও রসােত্তীর্ণ কাব্য’ বলে মনে করেন এবং এর পিছনে শুধু হিন্দু সংস্কৃতিই উৎস নয়, বৈষ্ণব কাব্যের মানবীয়তার পিছনে। মুসলমান সংস্কৃতির অবদানও যথেষ্ট। হুমায়ুন মধ্যযুগের কাব্য বিকাশের ক্ষেত্রে এককভাবে হিন্দু বা মুসলিম কোনাে পৃথক সম্প্রদায়ের নয়—বিমিশ্রক্রিয়া দেখেছেন উভয়ের ধর্মতত্ত্বের। হুমায়ুন কবীর মনে করেন, মধ্যযুগে বাঙালি হিন্দুর মানস পরিচয় লাভে কোনও কোনও মুসলমান রাজার আগ্রহ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। অপরদিকে বাঙালি হিন্দু চেষ্টা করেছিল মুসলিম সংস্কৃতির বর্ধিষ্ণু আধিপত্য থেকে আত্মরক্ষার। ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক সাহিত্য সৃষ্টির জোয়ার আত্মরক্ষার এই প্রয়ােসের ফল। কিন্তু আত্মরক্ষা করতে গিয়ে পরােক্ষ মুসলিম প্রভাবকে যে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল মধ্যযুগের সাহিত্যে ধর্মতত্ত্বের বিবর্তনই তার নিদর্শন। হিন্দুর ধর্মতত্ত্ব বিবর্তিত হয়েছিল আধুনিক যুগে এসেও। এক্ষেত্রেও ছিল আত্মরক্ষার তাগিদ। ‘বাংলার কাব্যে’-এ হুমায়ুন কবীর লিখেছেন,
“রামমােহন প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ইউরােপের সংস্কৃতির সমন্বয়ে নতুন জীবন দর্শন গড়তে প্রয়াসী হয়েছিলেন।”
এই জীবনদর্শন আধুনিক বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে প্রভাবিত করেছিল প্রত্যক্ষ এবং পারােক্ষ ভাবে।
বলা হয়েছে যে, ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। প্রধান শরিক ছিল ‘বাংলা কংগ্রেস’, যার হােতা ছিলেন অজয় মুখার্জি ও হুমায়ুন কবীর। অর্থাৎ বাঙালিকে ফ্রন্ট সরকারের স্বাদ এনে দেওয়ার মূলে হুমায়ুন কবীরের রাজনৈতিক প্রজ্ঞাও কাজ করে। কিন্তু সেকথা আজ কজনই বা মনে রাখেন! রাখেন না, কেননা এদেশে ভুলিয়ে দেওয়ার আবহও তৈরি হয় যখন-তখন। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই বিদেশ থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে অধ্যাপক কবীর বাংলা সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা দিতে যান। তখন প্রথম সারির একটি বাংলা দৈনিকে প্রশ্ন তােলা হয়, তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করার কে? এ প্রর্ণ শুধু মুঢ়তামূলক নয়, পক্ষপাতিত্বমূলকও। কেননা প্রকারী জানতেন যে, তার প্ররের উত্তর রয়েছে হুমায়ুন কবীরের জীবন ও সাহিত্যকর্মে। জানতেন যে, ইংরেজি ও বাংলা মিলিয়ে পদ্যে-গদ্যে অন্তত ৪৫টি গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। উভয় ভাষায় ছিল তার সমান দক্ষতা। সব্যসাচী লেখক। কী করে বুঝব, কেমন ছিল তার কাব্যপ্রতিভা, যদি না চোখ রাখি তার ‘স্বপ্নসাধ’, ‘সাথী’, ‘অষ্টাদশী’ ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের পাতায়। কাব্যসমীক্ষায় তাঁর বৈদগ্ধ্য কেমন ছিল তা জানা যাবে না, যদি না খুলে দেখি তার ‘পােয়েটি, মােনাডস অ্যান্ড সােসাইটি’ গ্রন্থটি, যেটি কলকাতা বিবিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। খুব সংক্ষিপ্ত হলেও হুমায়ুন কবীর কথাসাহিত্যের জগতেও নিজেকে বিস্তৃত করেছেন। তিরিশের দশকে তার লেখা কয়েকটি ছােটগল্প স্বনামে ও বেনামে প্রকাশিত। ১৯৪৫ সালে তার ‘নদী ও নারী’ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় এবং একই বছর ‘মেন অ্যান্ড রিভার্স’ নামে এর একটি ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। উপন্যাসে কবীর নদীকেন্দ্রিক সমাজজীবনের একটি নিখুঁত চিত্র উপস্থাপন করেছেন। ১৯৫৫ সালে ঢাকায় উপন্যাসটি চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। আমরা তার শিক্ষা ভাবনার খোঁজ রাখি না। কেননা পড়িনি তার এ ন্যাশনাল –‘ম্যান অফ এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া’, ‘স্টুডেন্ট ইনডিসিনি’, ‘টু স্টাডিজ অন এডুকেশন’, ‘নয়া ভারতের শিক্ষা’, ‘এডুকেশন ইন নিউ ইন্ডিয়া’, ‘শিক্ষক ও শিক্ষার্থী’, ‘এডুকেশন ফর টুমরাে’, ‘দিল্লি-ওয়াসিংটন-মস্কো’, ‘অ্যান ইন্ডিয়ান লুকস অ্যাট আমেরিকান এডুকেশন, স্টুডেন্ট আনরেস্ট কজ অ্যান্ড কিওর ইত্যাদি অমূল্য গ্রন্থ। তার সাহিত্য-সন্ধিৎসার কথা আমরা জানি না। কেননা পড়ে দেখিনি তাঁর ‘বাংলার কাব্য’ কিংবা তার সম্পাদিত ‘পােয়েমস অফ টেগাের’-এর ভূমিকা, ‘মসদ্দসে হালী’ (অনুবাদ), পড়িনি তার সাহিত্য সন্দর্ভ, শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জি। পড়িনি ‘ধারাবাহিক’, ‘দ্য ইন্ডিয়ান হেরিটেজ’, ‘দ্য কালচারাল হেরিটেজ অফ ইন্ডিয়া’, ‘কংগ্রেস মতবাদ’, ‘ভারতবর্ষ ও সমাজতন্ত্রবাদ’, ‘গান্ধীয়ান ফিলােজফি’, ‘মার্কসবাদ’, ‘মির্জা আবু তালিব খান’ ইত্যাদি গ্রন্থও। ফলে আমরা জানতে পারিনি হুমায়ুন কবীরের রাজনৈতিক মতবাদ, ভারতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কিত বিশুদ্ধ ধারণা। কেমন ছিল তাঁর দর্শন-বিচার, বলতে পারি না, কেননা আমরা পড়িনি তাঁর ‘ইমানুয়েল কান্ট’ (১৯৩৯) কিংবা ‘ ফিলােজফি অফ এডুকেশন’ (১৯৬১)। আসলে হুমায়ুন কবীরের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে যে প্রর্ন তােলা হয়, তার কারণ অজ্ঞতা নয়, অনীহা। আর কোনাে উত্তরই যে প্রকারীকে খুশি করবে না তারও কারণ পক্ষপাতমূলক অনড় ধারণা ও একদেশদর্শিতা। কিন্তু এ নিয়ে আমাদের আক্ষেপ করা বৃথা।
সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে হুমায়ুন কবীরের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ড কখনই ভেদবাদকে প্রশ্রয় দেয়নি। এ বিষয়ে তাঁর ‘মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল’ গ্রন্থটি খুবই কার্যকরী। তাঁর ‘ধারাবাহিক’ গ্রন্থের কিছু প্রবন্ধেও তৎকালীন মুসলিম সমাজ-রাজনীতি তথা ভারতীয় রাজনীতির গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলােচনা হয়েছে। তৎকালীন রাজনীতির পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করে তিনি জানিয়েছিলেন যে মুসলিম লিগ ছিল প্রকৃতপক্ষে উচ্চশ্রেণির (মূলত অবাঙালি) মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার দল, মুসলমানদের ধর্মীয় বা অন্য কোনাে স্বার্থ রক্ষা করার জন্য নয়। ১৯০৬ সালের পর থেকে ইংরেজ যে কিছুটা মুসলিম প্রীতি দেখাল তাঁর কারণ তারা হিন্দু মধ্যবিত্তের কংগ্রেসকে ভীতির চোখে দেখছিল।
শুধু সমসাময়িক রাজনীতির পর্যালােচনা নয় রাজনৈতিক দর্শনের আলােচনাও তিনি করেছেন। এমনকি শুধু মার্কসবাদের পরিচয়মূলক গ্রন্থও তার আছে, যদিও তিনি মার্কসবাদী নন। তবে প্রথমেই বলে নিয়েছেন,
“গােড়াতে মার্ক্সবাদের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি স্পষ্টভাবে জানা প্রয়ােজন। সেজন্য সমালােচনা বা বিচারের প্রশ্ন প্রথমে না তুলে মার্কসবাদের প্রধান সূত্রগুলি উপস্থিত পাঠকের সামনে ধরা যাক। মার্ক্সবাদ সম্বন্ধে ধারণা খানিকটা স্পষ্ট হলে তখনই সমালােচনার প্রণ উঠবে। মার্কসপন্থী বা মার্কসবিরােধী যেন মনে না করেন যে মার্ক্সবাদের প্রতিপাদ্যকে উপস্থিত করার অর্থই তাকে গ্রহণ করা।”
তিনি নিশ্চয়ই অনুভব করেছিলেন যে, দেশে যারা নিজেদের মার্কসপন্থী বলে প্রচার করেন তারাও বােধগম্যভাবে তত্ত্বটিকে উপস্থিত করেননি, বা তারা নিজেরাই বিষয়টি সম্যকভাবে বােঝেন না এবং হুমায়ুন যে ওই তত্ত্বটির আগাপাশতলা আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই, নতুবা মার্কসবাদকে এত সহজ-সরল-বােধগম্য ভাষায় পরিবেশন সম্ভব হত না। তার দৃষ্টি নিরপেক্ষ ছিল বলেই মার্কসবাদী না হয়েও তিনি বলেছিলেন,
“দুনিয়ায় আজ যে সমস্ত চিন্তাধারার প্রচলন, তার মধ্যে মাকর্সবাদের গুরুত্ব যে খুবই বেশী, সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বঞ্চিত ও নির্যাতিতের কাছে মার্ক্সবাদ নতুন ভরসার বাণী এনেছে। বিত্তশালী ও দৌলতমন্দ যে পরিমাণে মার্ক্সবাদের বিরােধী, মজলুম ও সর্বহারা ঠিক সেই পরিমাণেই মার্ক্সর্সবাদকে সাগ্রহে গ্রহণ করেছে।” (মার্কসবাদ’)।
আসলে হুমায়ুন কবীর কার্ল মার্কসকে একজন খাঁটি দার্শনিক হিসেবেই বিবেচনা করতেন এবং একজন দার্শনিকের তত্ত্বে যে তার নিজস্ব জীবনাভিজ্ঞতার কারণেই সীমাবদ্ধতা চলে আসে, সেকথাই বলেছেন তার আরেকটি রাজনৈতিক দর্শনের গ্রন্থে। ‘কংগ্রেস মতবাদ’ শীর্ষক গ্রন্থে কবীর বলেছেন,
“মার্ক্স বহু বিষয়ে বহুদর্শী ব্যক্তি ছিলেন একথা নিঃসন্দেহ। কিন্তু তার দর্শন বিচার ও দর্শন দৃষ্টি আংশিক ও বহুৰেত্রে ভ্রান্ত, একথাও সমান সত্য।”
‘মার্কসবাদ’, ‘কংগ্রেস মতবাদ’ (১৯৬৪) ছাড়াও হুমায়ুন কবীরের অন্যান্য রাজনৈতিক-দর্শনের গ্রন্থ ‘ভারতবর্ষ ও সমাজতন্ত্রবাদ’, ‘গান্ধীয়ান ফিলােজফি’ (১৯৬৪) ইত্যাদি। এছাড়া তঁার সাধারণ দর্শন-বিষয়ক প্রবন্ধ রয়েছে। ইমানুয়েল কান্ট বিষয়ক তঁার বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থ রয়েছে (‘ইমানুয়েল কান্ট’ ও ‘কান্টস অন ফিলােজফি ইন জেনারেল’)। ধর্মতত্ত্ব নিয়ে কবীরের পৃথক কোনাে গ্রন্থ না থাকলেও তিনি এ বিষয়েও লেখালেখি করেছেন এবং তা তার ধর্ম ইসলাম নিয়েই। ‘দ্য মিনিং অফ ইসলাম’ নামক প্রবন্ধের প্রথমেই বলেছেন,
“The essential fact about Islam is that it is a non-ascetic religion.’ (সার্ভেন্ট অফ হিউম্যানিটি মে ১৯৩৯)।
হুমায়ুনের ‘বাংলার জাগরণ’ (চতুরঙ্গ বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬৪) শীর্ষক আলােচনা উভয়বঙ্গের বিদ্বৎসমাজকে আলােড়িত করে। আলােচনাটি বঙ্গীয় নবজাগরণের মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণে দিক নির্দেশিকার ভূমিকা গ্রহণ করে। তিনি শ্রীলংকার কলম্বােয় জাহিরা কলেজে ইসলাম ও ভারতবর্ষ’ শিরােনামে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ইসলামের সবিশেষ অবদান ও ভূমিকা প্রসঙ্গে ১৯৫৯ সালে ৯ মে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা খুবই তাৎপর্যবাহী। এ ক্ষেত্রে তাঁর ‘মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল’, সায়েন্স ডেমােক্রেসি অ্যান্ড ইসলাম’, ‘মাইনরিটিজ ইন ডেমােক্রেসি’ গ্রন্থগুলিও স্মরণীয়।
সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক অনন্যসাধারণ ত্রৈমাসিক পত্রিকা ‘চতুরঙ্গ’ হুমায়ুন কবীরের শ্রেষ্ঠ অবদান। ১৯৩৮ সালে বুদ্ধদেব বসুকে সঙ্গে নিয়ে শুরু করেন ‘চতুরঙ্গ’—লেখালেখি বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই। ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত হুমায়ুন কবীর এই পত্রিকার পরিচালক ছিলেন। এ ব্যাপারে তার প্রধান সহযােগী ছিলেন পূর্ববঙ্গের পাবনার অধিবাসী আতাউর রহমান। দুজনেই ‘চতুরঙ্গ’কে এমনভাবে পরিচালনা করেছিলেন যা বাংলা সাহিত্যে নতুন নতুন প্রতিভাকে প্রতিষ্ঠা ও প্রেরণা দানে সক্ষম হয়েছিল এবং পত্রিকার পাঠক সমাজের অনুসন্ধিৎসাকে সর্বতােমুখী ও তাদের নান্দনিক বােধকে সুদুরপ্রসারী করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। প্রখ্যাত সাহিত্যিক শওকত ওসমান ‘চতুরঙ্গ’কে বাংলা সাহিত্যের লাইট হাউস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ১৯৬৪ সালে কবি সমর সেনকে সম্পাদক করে হুমায়ুন কবীর নিয়ে আসেন নিজের পরিচালনাধীন ইংরেজি সাপ্তাহিক ‘Now’ পত্রিকায়। হুমায়ুন কবীর ছয়ের দশকের শেষ দিকে নিয়া বাংলা পত্রিকাটিও প্রকাশ করতেন। এটি ছিল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পত্রিকা। সম্পাদক ছিলেন অচ্যুত গােস্বামী, যদিও মূলত কাজী আবদুল ওদুদ ও সাহিত্যিক আবদুল জব্বার তা দেখাশােনা করতেন। ইংল্যাণ্ডে থাকাকালে তিনি ‘ভারত’ নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন। ভারতে ফিরে আসার পর হুমায়ুন কবীরের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত যে পত্রিকাটির কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ্য তার নাম ‘কৃষক’। ১৯৩৮ সালে ডিসেম্বর মাসে এ কে এম ফজলুল হকের নির্দেশে কৃষক প্রজাপার্টির মুখপত্র হিসেবে ‘দৈনিক কৃষক’ প্রকাশিত হয়। হুমায়ুন কবীর ছিলেন এই পত্রিকার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পত্রিকাটি তখনকার দিনে অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের কারণে ও কৃষক শ্রমিক তথা মেহনতি মানুষের স্বার্থের প্রবক্তা হিসেবে নাম করেছিল।
ভারতীয়ত্ব সম্পর্কে হুমায়ুন কবীরের ধারণা অভিব্যত্তি পেয়েছে ‘দ্য ইন্ডিয়ান হেরিটেজ’ গ্রন্থটিতে। বইটির ভূমিকায় তিনি লিখেছেন রাজ-রাজড়াদের কাহিনির তুলনায় ভারতীয় জনগণের সত্য এবং বিস্তারিত কাহিনি লিখিত হওয়া অত্যন্ত জরুরি। তার ধারণা, এই ইতিহাস লিখিত হলে ভারতের ঐক্য ও সংহতির উৎস যে সমন্বয় একথাই আমাদের বােধগম্য হবে সহজেই। আসলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘ভারততীর্থ’ কবিতাটিতে যে সমন্বয়ের বার্তা ঘােষণা করেছেন হুমায়ুন কবীরের ‘ইন্ডিয়ান হেরিটেজ’ গ্রন্থের অনুসন্ধানের বিষয় ছিল সেটাই। এই সমন্বয়ের কথা হুমায়ুন কবীরের ‘দ্য কালচারাল হেরিটেজ অফ ইন্ডিয়া’, ‘মির্জা আবু তালিব খান’ ইত্যাদি গ্রন্থেও স্থান পেয়েছে। লক্ষ্ণৌ-এ জন্মগ্রহণ করলেও মির্জা আবু তালিব খান (১৭৫২-১৮০৬) বাংলার মুর্শিদাবাদেই জীবনের অধিকাংশ দিন কাটিয়েছেন। মূল ইংরেজি গ্রন্থটি সংগ্রহ করা যায়নি। ‘চতুরঙ্গে’ প্রকাশিত ‘মির্জা আবু তালিব খাঁ’ নিবন্ধ থেকে তার পরিচয় হুমায়ুন কবীরের জবানীতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি,
“মির্জা আবু তালিবের মতন মনীষীর আবির্ভাব বিস্ময়কর।…রাষ্ট্রের ভাগ্য নির্ণয়ে সামুদ্রিক শত্তির তাৎপর্য তিনি যেভাবে ব্যক্ত করেছেন, ভারতবর্ষে তার পূর্বে কেউ করেনি, ইউরােপীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যেও এরকম স্বচ্ছ দৃষ্টির পরিচয় বেশী মেলে না। ইংলন্ডে তখন যে শিল্প-বি-ব চলছে তার প্রকৃতিও তিনি অধিকাংশ ইউরােপীয় অর্থনীতিবিদ বা ঐতিহাসিকের চেয়ে বেশী স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছিলেন।… বােধ হয় আবু তালিবের পুর্বে কোন ভারতবাসী ইয়ােরােপ এবং ইংলণ্ড নিয়ে ভ্রমণ কাহিনী লেখেননি।… একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে মার্কস ইতিহাসের যে অর্থনৈতিক বিবরণ দিতে চেয়েছিলেন, মার্কসের পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে আবু তালিবের রচনায় তার স্পষ্ট পূর্বাভাস মেলে।… মানুষের ইতিহাসে নৌশক্তির তাৎপর্য লক্ষ্য করে এডমিরাল মাহান প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। কিন্তু মাহানের প্রায় একশাে বছর আগে আবু তালিব সে বিষয়ে যে সুসঙ্গত আলােচনা করেছেন, তাতে তার দূরদৃষ্টি দেখে বিস্মিত হতে হয়। আবু তালিবকে তাই মার্ক বা মাহানের পূর্বদ্রষ্টা বলা চলে, বলা চলে যে অষ্টাদশ শতকে ভারতবর্ষের এই ঐতিহাসিক ইতিহাস পাঠের যে পথনির্দেশ করেছিলেন, আজো বহুল পরিমাণে ঐতিহাসিকেরা সেই ধারা অনুসরণ করে চলেছেন।” (চতুরঙ্গ বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬৯)।
তবে আমাদের বিস্মিত হতে হয় এই ভেবে যে, আবু তালিবের মতাে মনীষীর পরিচয় আমরা জানি না, স্বীকৃতি দেই না। এভাবে আরও কত অহঙ্কার-ঐতিহ্যের সন্ধান রাখি না কিংবা অবমূল্যায়ন করে চলেছি। এর অন্যতম কারণ হুমায়ুন কবীরের মতাে স্বচ্ছ দৃষ্টির অধিকারী, আন্তরিক, উদার প্রজ্ঞাবান, কর্মপ্রিয় ব্যক্তির আজ বড়ই অভাব।
হুমায়ুন কবীরের আর একটি উল্লেখযােগ্য অবদান স্মরণ না করলেই নয়। বাংলা সাহিত্যিকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি ইংরেজিতে বেশ কয়েকখানি বই লিখেছিলেন। বইগুলি হল শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জি’ (‘শরৎ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব’), ‘রবীন্দ্রনাথ টেগাের’ এবং বাংলা উপন্যাসের উপর ইংরেজি বই ‘দ্য বেঙ্গলি নভেল’ ‘দ্য বেঙ্গলি নভেল’ হচ্ছে। ১৯৬৭ সালে আমেরিকার উইসকন্সিন বিবিদ্যালয়ে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মৃতি বক্তৃতার সংকলন। রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে হুমায়ুন কবীর প্রথমেই জানিয়েছেন, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনায় অনেক বেশি প্রজ্ঞা ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তবে বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস আলােচনার সময় ভুলে গেলে চলবে না যে, রবীন্দ্রনাথ প্রধানত কবি। গীতিকবি হয়ে থাকেন নির্জনতাপ্রিয় ও আত্মকেন্দ্রিক, উপন্যাস অনেক বেশি সমাজ-সম্পৃক্ত। রবীন্দ্রনাথ পুর্বসুরি বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহ্যেই বড় হয়েছেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মতাে তার প্রথম দিকের উপন্যাসগুলােও ঐতিহাসিক পটে উপস্থাপিত। তবে ‘বৌঠাকুরাণীর হাটে’র পর রবীন্দ্রনাথের গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস ‘চোখের বালি’।
২০০৬ সাল ছিল হুমায়ুন কবীরের জন্ম শতবর্ষ। কিন্তু কলকাতায় তাকে নিয়ে সেভাবে কোনও উন্মাদনা ছিল না। কলকাতার বাংলা একাডেমি সে সময় দায়সারা গােছের একটি অনুষ্ঠান করেছিল ওই বছরের ২২ ফেব্রুয়ারি। বরং বিকোষ পরিষদ ও চতুরঙ্গ পত্রিকা প্রয়াত হুমায়ুন কবীরকে নিয়ে যে শ্রদ্ধানুষ্ঠান করেছিল তা অনেকটাই প্রাণবন্ত ছিল। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হুমায়ুন কবীরের জন্মদিন প্রতি বছর নীরবেই চলে যায়। কলকাতা কিন্তু নীরবেই থাকে। যে ব্যক্তিত্ব ছিলেন দেশভাগের পূর্ব ও পরের যুগসন্ধিক্ষণের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি তার সম্পর্কে নতুন প্রজন্ম কিছু জানবে না?
‘নবজাগরণ’ অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপ্লিকেশনটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।
‘নবজাগরণ’ এর টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।
‘নবজাগরণ’ এর ফেসবুক পেজে লাইক করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

 নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা
নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা