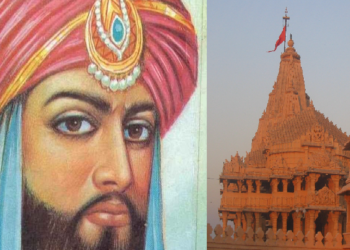লিখেছেনঃ সত্যজিৎ রায়
চলচ্চিত্রের ইতিহাস পরিধিতে সংক্ষিপ্ত হলেও বহু ঘটনায় আবর্তিত। চলচ্চিত্র প্রবর্তনের পরে দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধ গেছে, বিশ্ববাণিজ্যের বাজারে ক্রমান্বয়ে সাংঘাতিক ওঠাপড়া হয়েছে, এবং বিজ্ঞান গবেষণায় অকল্পনীয় উন্নতির পরিণতি ঘটেছে পরমাণুর পরম বিস্ফোরণে। চলচ্চিত্রের প্রধান উপকরণ হচ্ছে মানবজীবন, কাজেই মানব-ইতিহাসের সঙ্গে তার ইতিহাসও অঙ্গাঙ্গী গ্রথিত। মানব সমাজের প্রতিটি পরিবর্তন তার চিহ্ন রেখে গেছে চলচ্চিত্রের বিকাশের পথে।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানুষের সৃষ্টি-চেতনাকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে গেছে। আর সেই আঘাতের ফলে চলচ্চিত্র-শিল্প পরিণতির পথে হঠাৎ এক লক্ষে যতদিন অগ্রসর হয়েছে তার প্রতিতুলনা বিরল। যুদ্ধের সময় যন্ত্র-শিল্প উম্ভাবনায় যা উন্নতি হয়েছে চলচ্চিত্রের পরিণত বিকাশের পক্ষে নিঃসন্দেহে তার দান প্রভূত। ফলে এই শিল্পের মধ্যবর্তিতায় ভাব প্রকাশের শক্তি গেছে অনেক বেড়ে।

ফিল্ম তােলার আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদির এতদুর আজ উন্নতি হয়েছে যে কল্পনায় কি বাস্তবের জগতে হেন বস্তু নেই পরিচালকের ইচ্ছামতাে যাকে দৃশ্যপর্দায় রূপ দেওয়া না যায়। অবশ্য শুধুমাত্র উৎকৃষ্ট উপাদানই উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টির একমাত্র সর্ত নয়, উৎকৃষ্ট পােট্রেট আঁকায় যেমন যথেষ্ট নয় উৎকৃষ্ট ইজেল। উপাদান হচ্ছে উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক। যিনি সষ্টি করেন তাঁর অনুভবের প্রকৃতির উপরেই চলচ্চিত্রের তথা সমস্ত সৃষ্টিকর্মের উৎকর্ষের নির্ভর। যদি রুচি না থাকে, যদি কল্পনা পঙ্গু হয়, তাহলে পৃথিবীর সমস্তের সেরা উপাদান একত্র করেও সিন্ধি হবে না। যুদ্ধান্তিক চলচ্চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই একথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে। স্বতন্ত্র কারণবশত ভারতবর্ষকে যদি ধরা না যায় তাহলে দেখা যাবে চলচ্চিত্র উৎপাদনের প্রধান প্রধান দেশগুলি যশ্ৰোৎকর্ষের সচ্ছল সুখ যতই ভােগ করুক কেন, সমসাময়িক চলচ্চিত্রের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট সষ্টি এসেছে যে দেশ থেকে সেই ইতালিতে সেদিন পর্যন্ত যন্ত্রপাতি ছিল আদ্যিকালের।
ইতালীয় ফিল্মের এই বখ্যাত বাস্তবিকতা, সারল্য আর মানবতাই এ যুগের চলচ্চিত্র-শিল্পের যথার্থ সুরের সন্ধান দিয়েছে।
চলচ্চিত্রে এই বাস্তবিকতার প্রবর্তনা বিশেষভাবে যুধান্ত কোনাে বৈশিষ্ট্য নয়, এবং রােমেও তার উৎস নয়। বহুদিন আগে ১৯২৩ সালে হলিউডে ‘গ্রীড’ নামে যে ছবিটি তােলা হয়েছিল, ফিল্মে বাস্তবিকতার সেটি একটি শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। অতুলনীয় চ্যাপলিন-এর সৃষ্টিপ্রেরণাও বাস্তবিকতার গভীরে নিহিত। তাছাড়া পরিদৃশ্যমানের অন্তরালে যে ধরপে লুকিয়ে আছে চলচ্চিত্র নির্মাণকারী প্রত্যেক দেশই মাঝে মাঝে তার মর্মোঘাটন করে দেখিয়েছে। সম্প্রতি সেই পুরাতন ফিল্মগুলি পুনরায় দেখে সকলেই স্বীকার করেছেন যে বাস্তবপন্থী ফিল্ম সময়ের অগ্নিপরীক্ষা যেমন পার হতে পেরেছে আর কোনাে ফিল্ম তা পারেনি। কিন্তু অতীতে সংখ্যায় সেগুলি নগণ্য ছিল। সম্প্রতি গােটা চলচ্চিত্র-শিল্পের প্রধান গতি হচ্ছে এই বাস্তবিকতার পথে। বাস্তবিকতা বলতে অবশ্য একটিমাত্র জিনিস বােঝায় না। মােটামুটিভাবে বলতে গেলে চলচ্চিত্রের দুদিক থেকে বিচার চলে — ভিতরের বস্তু আর বাইরের রূপ।
কাহিনীর গঠন, সৃষ্ট চরিত্রের সমস্যা, তাদের চরিত্ররূপ, পরস্পরের সম্পর্কঘটিত নাট্যগতির রস আর তাদের হৃদয়াবেগের প্রকাশভঙ্গী— এই সব হচ্ছে এক শ্রেণীর বিচার্য। গ্রন্থাকারে, চলচ্চিত্রে বা মঞ্চের অভিনয়ে সর্বত্রই কাহিনী বর্ণনা করতে গেলেই এই সব সমস্যা এসে পড়ে। কিন্তু ফিল্মের যেটা দৃশ্যেরপ—চোখের সামনে আমরা কি জিনিস দেখছি এবং কোন জিনিস কি ভাবে দেখানাে হচ্ছে তার সমস্যা হচ্ছে চলচ্চিত্রের নিজস্ব সমস্যা। পরিচালক তাঁর ক্যামেরার সাহায্যে কি করেছেন তার উপরেই এই দৃশ্যরূপের নির্ভর।
বলা বাহুল্য পরিচালকের সামর্থ্য অনুযায়ী চলচ্চিত্রের এই দুই অংশেরই প্রকৃতির মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু জীবনের কোনাে এক অংশের যুগপৎ ব্যাখ্যা এবং যথাযথ প্রতিরপ আঁকার সময় তাঁরা যে দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসরণ করেন সেটা পরিচালক ভেদেও একই থাকে।
উল্লিখিত দুইটি দিকের কোনাে এক অংশে বাস্তব যথার্থতার হানি হলে সমগ্র সষ্টির পক্ষে ক্ষতি হয়। আশা উদ্রেককারী বহু মার্কিন ছবি আমাদের যে শেষ পর্যন্ত হতাশ করে তার কারণ হচ্ছে যে উপরােক্ত যে কোনাে একদিকে কিম্বা উভয়দিকেই সেগুলির ব্যর্থতা। আর যুগপৎ উভয়বিধ বাস্তবিকতাই ইতালীয় ছবিতে উৎকর্ষের মল। বাস্তবমুখিনতাই যখন আধুনিক চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট্য তখন ছবির বহিরগের
রুপটিকেই ভালাে করে আলােচনা করা যাক। কল্পনাােেক সৃষ্টিতে চলচ্চিত্রের যে সব পরিণতি ঘটেছে সে বিষয়ে বর্তমানে উল্লেখ নিপ্রয়ােজন, কেননা বিষয়ভেদে তার রসসষ্টির সমস্যাও ভিন্ন।
দৃশ্য-শিল্পরুপের প্রকৃতি বিচার করলেই বাস্তবিকতায় সিদ্ধিলাভের যে কতখানি মূল্য তা হদয়ঙ্গম হবে। দেখতে হবে শিল্পস্রষ্টার ব্যবহার্য উপকরণের মধ্যবর্তিতায় বাস্তবিকতাকে কতদুর রসরপে রুপান্তরিত করা গেছে। চলচ্চিত্র নির্মাণে চতুষ্কোণ সেলুলয়েড ফিতার উপর বাস্তবদৃশ্যের যথাযথ রুপান্তরের প্রথম সহায় হচ্ছে ক্যামেরা। পরের কাজটুকু চিত্র-সম্পাদকের। চিত্র-সম্পাদকই প্রয়ােজন মতাে ছাঁটকাট করে বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সমবায়ে সমগ্র ছবিতে ছন্দগতি এবং ব্যঞ্জনার সষ্টি করেন।
এই সব পদ্ধতির প্রয়ােগের জন্য বাস্তবিকতার যেটুকু হানি হয় সেটা গ্রাহ্য। শিল্পসষ্টির সমস্ত ক্ষেত্রে এই রুপান্তর স্বীকার করতে হয়। শিল্পী মাত্রেই বাস্তব বিশ্বের নীর ত্যাগ করে ক্ষীর গ্রহণ করে থাকেন। বর্জন করে এভাবে গ্রহণ করার মধ্যেই শিল্পীর শিল্পীত্ব। গ্রহণে বর্জনেই বাস্তব বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি শিল্পের নির্দিষ্ট কোনাে রূপ দান করে ভাব সঞ্চার করেন। কিন্তু যেসব উপকরণ নিয়ে শিল্পের সষ্টি সেই উপকরণই যদি যথার্থ বাস্তবিক জীবনের বিকৃতি হয় তাহলে তার পরিণামে ব্যর্থতা সুনিশ্চিত। হলিউডেব অপ্রাকৃত দৃশ্য, জমকালাে সাজসজ্জা, লাস্যময়ী নটী আর দর্জির বিজ্ঞাপন সদশ নট জীবনের বাস্তবিকতা সষ্টির পথে প্রকাণ্ড বাধা।
স্টুডিও-জাত বাস্তবের অনুকৃতি কিছু পরিমাণে প্রকৃত বাস্তবের অভাব পূরণ করে দিতে পারে বটে, কিন্তু অনুকৃতি যত পুঙ্খানুপুঙ্খই হােক না কেন বাস্তবের সঙ্গে তার প্রভেদ বিস্তর। অপ্রাকৃত পরিবেশ এবং দশ্যে রচনার এই দুর্বলতা দূর করতে হলে উৎকৃষ্ট কাহিনী এবং চরিত্র সষ্টির গভীরতা চাই।
এই জাজ্জল্যমান কথাটা হৃদয়ঙ্গম করতে হলিউডের এতদিন লাগল এটাই তাজ্জবকর। ব্রিটেনেও মাত্র যুদ্ধের সময় ডকুমেন্টারি ফিল্মের প্রভূত প্রসার হওয়ার ফলে চলচ্চিত্রে সম্প্রতি এই বােধ দেখা দিয়েছে। অথচ যে প্রচুর উপকরণের সম্ভার চলচ্চিত্রে এবংবিধ প্রবঞ্চনার সহায় সেই সমস্ত উপকরণের অভাব থাকাতেই ইতালীয় চলচ্চিত্র-শিল্পকে বাস্তবপন্থী হতে হয়েছিল। ভালাে স্টুডিও না থাকায় বাস্তব দৃশ্য নিয়েই তাঁদের ছবি তুলতে হয়েছে। অভিনয় যাদের পেশা নয়, তাদের নিলে খরচ কম, কাজেই সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে নর-নারী-শিশুদের নিয়ে তাদের অভ্যস্ত পেশা অনুযায়ী ভূমিকায় অভিনয় করাতে হয়েছে। সুখের কথা এই যে ইতালীয়রা—অন্তত তাঁদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা এ সমস্ত কাঁচা উপাদান নিয়েই আশ্চর্য প্রতিভাবলে তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করেছেন। ইতালীয় ফিল্ম যে আজ এতদর খ্যাতি পেয়েছে, জনপ্রিয় হয়েছে, নিঃসন্দেহে সেগুলি তার যােগ্য।
জনকয়েক বশ চলচ্চিত্র-পরিচালকও অতীতে এ ধরনের পরীক্ষা করেছেন বাধ্য হয়ে নয়, তাঁদের শিল্পীক আদর্শের দরুন। তার ফলেই ‘পােটেমকিন’, ‘রােড ট লাইফ’, ‘চাইল্ডহড অভ ম্যাক্সিম গাের্কী’, ‘প্রফেসার ম্যামলক’ প্রভৃতি ছবিতে সাম্প্রতিক ইতালীয় ফিল্মের বাস্তবানুগতি এতদর প্রকট হতে পেরেছিল। প্রায় পচিশ বৎসর পরে আজও ‘পপাটেমকিন’-এর বাস্তবিকতা আমাদের চিত্তহরণ করে— এ বাস্তবিকতা দশ্য এবং আন্তর – উভয়বিধ। তবে গঠনরীতির কতিপয় কৌশল নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকার দরুন আইসেনস্টাইন-এর ফিল্মগুলি একট, আড়ষ্ট হয়েছে।
গ্রিফিথ, স্ট্রোহাইম, আইসেনস্টাইন প্রমুখ মহৎ চলচ্চিত্র-শিল্পীরা যেমন বাস্তবমুখী আধুনিক কাহিনী চিত্রের, ফ্লাহাটি তেমনি ডকুমেন্টারি চলচ্চিত্রের আদি স্রষ্টা। এমন কি এই বরেণ্য শিল্পীদের সাধনার ফলেই ডকুমেন্টারি চলচ্চিত্রের উন্মেষ হয়। সমসাময়িক চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মনে উল্লিখিত বরেণ্যদের দৃষ্টান্ত যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে বিদেশী চলচ্চিত্রের দিকে তাকালেই তা বােঝা যায়।
আমেরিকায় এই বাস্তবমুখী সার্থক সষ্টির মধ্যে ‘দি গ্রেপস অভ রথ’, ‘অক্সবাে ইনসিডেন্ট’, ‘দি লস্ট উইক-এণ্ড’, ‘দি সাদার্নার’ প্রভৃতির নাম করা যায়। ‘দি মার্চ অভ টাইম’ সিরিজের উদ্যোক্তা ই ডি রশমন্ট এদিকে যথেষ্ট উদ্যম দেখিয়েছেন, এবং বাস্তব পরিবেশে স্বাভাবিক নরনারীদের সাহায্যে ছবি তােলার কাজে অগ্রসর হয়ে প্রশংসাভাজন হয়েছেন।
সম্প্রতি একাধিক চলচ্চিত্র প্রযােজকের দৃষ্টি এদিকে পড়েছে বলে এই মার্কিনী স্টুডিও থেকেই সম্প্রতি বেশ কয়েকখানি এমন ছবি বেরিয়েছে যার বাস্তবানুগতি রীতিমতাে তাক লাগায়। আর ‘মেরাঙ’, ‘দি নেকেড সিটি’, ‘ক্রসফায়ার’, ‘দি সার্চ বা ‘জনি বেলিণ্ডা’-র মতাে যেসব ছবিতে পর্বে উল্লিখিত দ্বিবিধ বাস্তবিকতার মিলন ঘটেছে সে সব ছবিই যুগপৎ রসােত্তীর্ণ এবং অর্থকরী হতে পেরেছে।
বাস্তবসধানী তরুণ চিত্রপরিচালকের সংখ্যা এখন আর নগণ্য নয়। নাম করতে গেলে এলিয়া কাজান, এডােয়াড ডিমিট্ৰীক, জলস, ড্যাসিন, রবার্ট রসেন, নিকোলাস রে, ফ্রেড জিনেম্যান, মার্ক রবসন প্রভৃতির সঙ্গে আরাে অনেকের কথা বলতে হয়। এদের মধ্যে সকলের শক্তি এক নয়; কিন্তু অবাস্তব চাকচিক্যের প্রতি এদের বিতৃষ্ণা সমপরিমাণে উগ্র। বিষয়ের গভীর মর্ম উঘাটনে এদের সকলেরই সমান আগ্রহ। প্রতিষ্ঠাবান বয়ােজ্যেষ্ঠ চিত্রপরিচালকেরা পর্যন্ত ধীরে ধীরে এই পথে আসছেন। এই নব্যরীতিতে তাঁদেরও যে আস্থা আছে, তাঁরাও যে এই রীতির শক্তির কথা জানেন তা উইলিয়াম ওয়াইলার-এর ‘দি বেস্ট ইয়ারস অভ আওয়ার’। লাইভস’, বিলি ওয়াইল্ডার-এর ‘দি লস্ট উইক-এণ্ড’ আর ‘ডাবল, ইণ্ডেমনিটি, জন হাস্টন-এর ‘ট্রেজার অভ সিয়েরা মাদ্রে’ সে কথার সাক্ষ্য দেবে।
ইংলণ্ডে ডকুমেন্টারি ফিল্মের যথেষ্ট প্রসার হয়েছে, কাজেই এই বাস্তব রীতিতে তাদের আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। অলিভিয়ার-এর সেক্সপীয়ার চিত্র এবং পাওয়েল আর প্রেসবার্গার-এর ফিল্মে কল্পলােক সষ্টির কথা না ধরলে অধিকাংশ ইংরেজ চলচ্চিত্রপরিচালকই এ পথের পথিক। ডেভিড লীন আর নােয়েল কাওয়ার্ড-এর ‘ীফ এনকাউন্টার’ ছবিটি সে দেশে বাস্তবরীতির সার্থক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আইরিশ রপক অনুসরণে ক্যারল রীড অবশ্য প্রতীক পথার সহায়তা নিতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তাঁর ছবিতেও ডাবলিন শহরকে তিনি জীবন্তভাবে উপস্থিত করেছেন। এমন কি ডিকেন্স-এর ‘অলিভার টুইস্ট’ আর ‘গ্রেট এক্সপেক্টেশান্স’-এর চলচ্চিত্ররুপ-এ লীন আশ্চর্য নিপুণভাবে উনিশ-শতকী ইংলণ্ডের পুনরাবতরণ করেছেন।
যে ফরাসী ছবির কথা আমরা প্রচুর শনি, সামান্য দেখি—সেই ফরাসী ফিল্মেও বাস্তবিকতার প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। সাম্প্রতিক ফিল্মগুলিতেও – অন্তত খবর পড়ে যা মনে হয় এর ব্যতিক্রম নেই। জাক বীকার, জর্জ কুজো, জাঁ দেলানয় আর ক্লদ ওতা-লারা-র ন্যায় তরুণ চলচ্চিত্র-পরিচালকেরা রেনােয়া, কানে, দভিভিয়ে, প্যাঞেল-এর ন্যায় অগ্রজগুণীদের সাধনার উত্তরাধিকার লাভ করে বাস্তবপখী চলচ্চিত্রের ধারা অব্যাহত রাখছেন।
ইউরােপীয় অন্যান্য দেশের চলচ্চিত্রও এই এক পথেই চলেছে। প্রবধ শেষ করার আগে আর একবার ইতালীয় সিনেমায় ফিরে আসা যাক। ইতালীয় ফিল্ম এত আলােড়ন তুলেছে কেন ভেবে দেখতে গেলে কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। হলিউড এতকাল ধরে তিলে তিলে যে সমস্ত অবাস্তব রীতির প্রতিষ্ঠা করেছে, একমাত্র ইতালি পেরেছে সেই আজগুবী রীতিকে ফুঁ দিয়ে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিতে। অভিনয়ের জন্য তারকারাজি সম্মেলন করার রীতি যে কত বড় বিরাট মুর্খতা, ইতালীয়রা তা হাতে হাতে প্রমাণ করে দিয়েছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন যে ছবি তুলতে কুবের ভাণ্ডার উজাড় করার, কিম্বা চটুল চাকচিক্যের জৌলুষ দেওয়ার এবং সেই ছবি কাটতির জন্য একটা বিশ্বব্যাপী হৈহৈ রৈরৈ আওয়াজ তােলার কোনােই প্রয়ােজন নেই। বলতে গেলে প্রায় সচনা থেকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে হয়েছে বলে ইতালীয়রা চলচ্চিত্রের মল ভিত্তির সন্ধান রাখেন। ব্যাপারটা বড় সহজ হয়নি। চলচ্চিত্র নির্মাণের পদ্ধতিটাই তাে জটিল। কিন্তু তার মধ্যেই ইতালীয়রা সারল্যে, সততায়, বাঘবিকতায় সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করে এসেছেন। নতুন পদ্ধতির এই নতুন পাঠশালায় রসেলিনী, ডি সিকা, ভিসকোন্তি, লাতুয়াদা—এরাই হচ্ছেন গুরু। দেশ নির্বিশেষে তাঁদের সাধনা প্রতিটি চলচ্চিত্র নির্মাতার অনুকরণযােগ্য। এদের বিষয়ে আলােচনা পাঠ করলেও মনে উৎসাহ জাগে। চলচ্চিত্রের মানুষ যে স্বাভাবিক মানুষের মতােই হাত-পা নেড়ে কথাবার্তা বলে, পুতুলের মতাে মখ নাড়ে না, এবং তার দৃশ্যাবলী যে হাতে অাঁকা পট না হয়ে যথার্থই বাস্তব দৃশ্য হতে পারে, আমাদের চলচ্চিত্র পরিচালকবর্গ হেন কথা কোনাে কালে শ্রবণ করেছেন বলেও বােধ হয় না। ইতালীয় ফিল্মগুলি স্বচক্ষে দেখলে তাঁদের সম্বিৎ হতে পারে।

 নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা
নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা