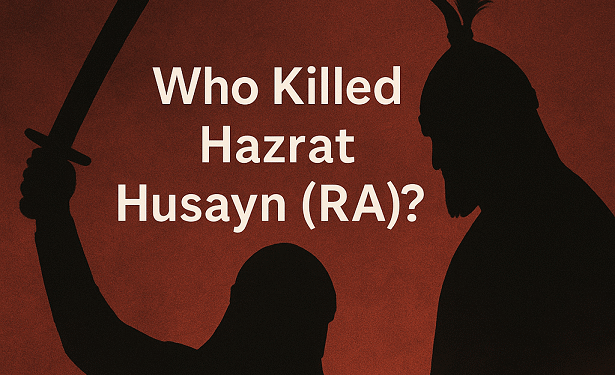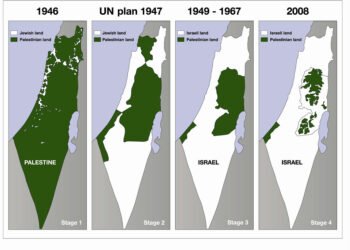লিখেছেনঃ মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম
প্রথমেই একটি কথা স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন—এই আলোচনা কোনো ব্যক্তি বিশেষের পক্ষাবলম্বন করে লেখা নয়। বরং ইতিহাসের এক গূঢ় ও বিতর্কিত অধ্যায়ের প্রেক্ষিতে সত্যের অনুসন্ধান এবং তা বাংলাভাষী মুসলমানদের সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরাই এই লেখার লক্ষ্য। আবেগ নয়, দলীয় আনুগত্য নয়, বরং প্রামাণিক সূত্রের আলোকে ইতিহাসের নিরপেক্ষ মূল্যায়নই এখানে মুখ্য।
কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার কথা স্মরণ করলেই যে নামটি প্রথম উচ্চারিত হয় তা হলো ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া। বহুকাল ধরে তাঁকে কেন্দ্র করেই একটি নির্দিষ্ট বয়ান সমাজে চালু রয়েছে—তিনি যেন হজরত হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হত্যার মূল হোতা, ষড়যন্ত্রকারী এবং আহলে বাইতের শত্রু। কিন্তু এই প্রচলিত ধারণার পেছনে কতটুকু ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে? কতটুকু তথ্য যাচাই করে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হই?
শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, “সকল মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকের ঐকমতে ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া হুসাইন (রাঃ) কে হত্যার আদেশ দেননি। বরং তিনি উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদকে চিঠির মাধ্যমে আদেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন ইরাকের ভুখণ্ডে হুসাইন (রাঃ) কে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে বাধা দেন।” এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, ইয়াজিদের আদেশের মূলকথা ছিল প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রশ্নে হস্তক্ষেপ, সরাসরি সংঘাত নয়।
ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায়, হজরত হুসাইন (রাঃ) যখন ইরাকের পথে রওনা দেন, তখন তিনি নিজের পরিবারসহ চলছিলেন। কুফাবাসীদের আমন্ত্রণেই তিনি এই দীর্ঘ যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু তাঁর কুফায় পৌঁছার আগেই রাজনৈতিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর যিনি ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত হন—উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ, তিনিই মূলত পুরো ঘটনার কৌশলগত নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠেন। ইয়াজিদ তৎকালীন কেন্দ্রীয় শাসক ছিলেন, কিন্তু কূটনৈতিক নির্দেশদানের বাইরে তিনি সরাসরি কোনো সামরিক পদক্ষেপে জড়িত ছিলেন না—এমনটিই প্রামাণ্য ইতিহাসের ভাষ্য।
এমনকি বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী, হজরত হুসাইন (রাঃ) এর শাহাদতের সংবাদ যখন ইয়াজিদের কাছে পৌঁছায়, তখন তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। “ইয়াজিদের বাড়িতে কান্নার ছাপ প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি হুসাইন (রাঃ) পরিবারের কোনো মহিলাকে বন্দি বা দাসীতে পরিণত করেননি; বরং পরিবারের সকল সদস্যকে সম্মান করেছেন। সসম্মানে হজরত হুসাইন (রাঃ) পরিবারের জীবিত সদস্যদেরকে মদিনায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন।”—এই বর্ণনায় যে মনোভাব প্রতিফলিত হয়, তা ক্ষমতালোভী এক নৃশংস শাসকের নয়, বরং এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পর আত্মসমালোচনায় নিমগ্ন এক শাসকের।

তবে সমাজে যে অভিযোগটি সবচেয়ে বেশি প্রচলিত, তা হলো—আহলে বাইতের মহিলাদের অসম্মান করা হয়েছে, বন্দি করে দামেশকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাঁদের ইজ্জতহানি করা হয়েছে। অথচ “যে সমস্ত রেওয়াতে বলা হয়েছে যে, ইয়াজিদ আহলে বাইতের মহিলাদেরকে অপদস্থ করেছেন এবং তাদেরকে বন্দি করে দামেস্কে নিয়ে বেইজ্জতি করেছেন, তার কোনো ভিত্তি নেই।” এই ধরনের বিবরণ ইতিহাসে পরবর্তীতে বিশেষ মতাদর্শের প্রতিফলন হিসেবে যুক্ত হয়েছে বলেই গবেষকদের অনেকে মনে করেন।
বিষয়টি এখানেই শেষ নয়। বনী উমাইয়ার রাজনীতি ও পারিবারিক নীতি বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায়, তাঁরা বনী হাশেমকে অপমান করতেন এমন প্রমাণ নেই। বরং “বনী উমাইয়াগণ বনী হাশেমকে খুব সম্মান করতেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যখন ফাতেমা বিনতে আবদুল্লাহ বিন জাফরকে বিয়ে করলেন তখন আবদুল মালিক বিন মারওয়ান এই বিয়ে মেনে নেননি। তিনি হাজ্জাজকে বিয়ে বিচ্ছিন্ন করার আদেশ দিয়েছেন।”—এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, বংশের মর্যাদা রক্ষায় তাঁরা বরং অতিরিক্ত সতর্ক ছিলেন।
অপরদিকে, ইতিহাসের আরেকটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, “হুসাইন (রাঃ) হত্যার জন্য দায়ী উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদের কাছে যখন হুসাইন (রাঃ) এর পরিবারের মহিলাদেরকে উপস্থিত করা হল তখন তিনি আলাদাভাবে তাদের জন্য একটি ঘরের ব্যবস্থা করলেন এবং তাদের ভরণ-পোষণ ও পরিধেয় বস্ত্রের ব্যবস্থা করলেন।” এই বিবরণ ইবনে জারীর তাবারীর মাধ্যমে পাওয়া যায়, এবং তা হাসান সনদে বর্ণিত।
তথ্যসূত্র ও ইতিহাসবিদদের মূল্যায়নেও এই চিত্রটিই ফুটে ওঠে। ইজ্জত দাররুযা যেমন বলেন, “হুসাইন (রাঃ) হত্যার জন্য ইয়াজিদকে সরাসরি দায়ী করার কোনো দলিল বা প্রমাণ নেই। তিনি তাঁকে হত্যার আদেশ দেননি। তিনি যেই আদেশ দিয়েছেন, তার সারসংক্ষেপ হচ্ছে, তাঁকে ঘেরা করা হোক এবং তিনি যতক্ষণ যুদ্ধ না করবেন ততক্ষণ যেন তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করা হয়।” এটি নিছক রাজনীতি নয়, বরং ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষায় একটি সাময়িক কৌশল বলেই বিবেচনা করা যেতে পারে।
ইমাম ইবনে কাসির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, “এটি প্রায় নিশ্চিত যে ইয়াজিদ যদি হুসাইন (রাঃ) কে জীবিত পেতেন, তাহলে তাঁকে হত্যা করতেন না। তাঁর পিতা হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) তাকে এ মর্মে অসিয়তও করেছিলেন। ইয়াজিদ এই কথাটি সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছিলেন।” এই ঘোষণায় আন্তরিকতা কতটুকু ছিল, তা বিচার না করলেও এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, হুসাইন (রাঃ) এর রক্তে হাত রাঙানোর দায় তিনি নিজে স্বীকার করেননি, বরং তার দায় কাঁধে নেওয়ার মতো কিছু করাও তাঁর পক্ষ থেকে ইতিহাসে দেখা যায় না।
অতএব, একপাক্ষিক আবেগের বদলে ইতিহাসকে সত্যের নিরিখে দেখা জরুরি। ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা গোষ্ঠীগত শ্রদ্ধার মোড়কে আবদ্ধ করে রাখলে ইতিহাস বিকৃত হয়, আর বিকৃত ইতিহাস কখনোই জাতির জন্য কল্যাণকর হয় না। হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদত নিঃসন্দেহে ইসলামি ইতিহাসের এক অশ্রুসিক্ত অধ্যায়। তবে এই অধ্যায়ের সত্য উচ্চারণ করতে হলে আবেগ নয়, প্রয়োজন নির্ভুল গবেষণা, গভীর পাঠ এবং ঐতিহাসিক সততা। তা হলেই ইতিহাসের প্রতি আমাদের কর্তব্য পূর্ণতা পাবে।
তাহলে কে হুসাইন (রাঃ) এর হত্যাকারী কে?
কারবালার অশ্রুসিক্ত স্মৃতি মুসলমানদের হৃদয়ে এক চিরন্তন ক্ষতের মতো জেগে আছে। ইতিহাসের এই অধ্যায় এতটাই বেদনাবিধুর যে, একে ঘিরে আবেগ, ক্ষোভ, ঘৃণা, প্রেম—সবই যুগে যুগে প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এসব আবেগের মাঝেও কখনো কখনো এমন কিছু প্রশ্ন মাথা তোলে, যেগুলোর জবাব দেওয়া হয়তো অনেকের পক্ষে কঠিন, অস্বস্তিকর, কিংবা বিশ্বাসঘাতকতার শামিল মনে হতে পারে। তবু ইতিহাসের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকেই সত্যকে স্বীকার করা আবশ্যক।
একটি প্রশ্ন বারবার ফিরে আসে—কে হজরত হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে হত্যা করল? এই প্রশ্নের জবাবে কেউ বলেন ইয়াজিদ, কেউ বলেন আমীর মুয়াবিয়া, কেউ আবার গোটা সুন্নি সমাজকেই দায়ী করেন। কিন্তু ইতিহাস কি সত্যিই এই দায়ভার তাঁদের কাঁধে চাপিয়ে দেয়? নাকি সত্য আরও গভীরে, আরও জটিলভাবে লুকিয়ে আছে?
যতদূর নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক দলিলপত্র থেকে জানা যায়, হুসাইন (রাঃ)-এর মৃত্যুর জন্য যাঁরা সরাসরি দায়ী, তাঁরা ছিলেন কুফাবাসী—অর্থাৎ সে সময়কার ইরাকের অধিবাসী, যারা নিজেদের শিয়া পরিচয়ে পরিচিত করতেন। আশ্চর্যের হলেও সত্য, তাঁরাই হজরত হুসাইন (রাঃ)-কে চিঠি লিখে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তাঁকে খলিফা হিসেবে গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তাঁর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছেন হাজার হাজার অনুসারী। হুসাইন (রাঃ) সেই আশ্বাসকে বিশ্বাস করে পরিবার-পরিজন নিয়ে কুফার উদ্দেশ্যে রওনা দেন।
কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সেই আশ্বাস ছিল মিথ্যা, সেই প্রতিশ্রুতি ছিল প্রতারণার। কুফাবাসীরা তাঁকে প্রতিরোধ করার পরিবর্তে উল্টো তাঁকেই নির্জন প্রান্তরে, ফোরাত নদীর তীরে একা ফেলে রেখে প্রতিপক্ষের সৈন্যদের হাতে সমর্পণ করে। ফলে হুসাইন (রাঃ) হয়ে পড়েন সম্পূর্ণ নিঃসহায়। তাঁর সঙ্গীদের একে একে শহিদ করা হয়, তাঁর শিশুপুত্র পর্যন্ত রেহাই পাননি। শেষপর্যন্ত হুসাইন (রাঃ) নিজেও শহীদের মর্যাদায় ভূষিত হন। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়—এই হত্যাযজ্ঞের প্রকৃত দায় কার?
এই বিষয়ে একটি জোরালো সাক্ষ্য পাওয়া যায় একজন খ্যাতনামা শিয়া লেখক সাইয়্যেদ মুহসিন আল-আমীনের লেখায়। তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন, “বিশ হাজার ইরাকবাসী হুসাইন (রাঃ)-এর পক্ষে বায়াত নেয়। পরবর্তীতে তারা তাঁর সাথে খেয়ানত করেছে, তাঁর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেছে এবং তাঁকে হত্যা করেছে।” (আয়ানুশ শিয়া, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪)
এই বক্তব্য শুধু একজন শিয়া মনীষীর অনুশোচনা নয়, বরং এক জাতিগত আত্মসমালোচনার নির্ভীক প্রকাশ। এটি প্রমাণ করে, সত্য গোপন করে রাখা যত কঠিনই হোক না কেন, ইতিহাসের নির্দয় আলো একদিন তাকে উদ্ভাসিত করেই ছাড়ে।
অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, যারা তাঁকে প্রথম আহ্বান জানিয়েছিল, তারাই তাঁকে ছেড়ে দেয়, তাদের ভয়ে কেউ সাহস করে তাঁর পাশে দাঁড়ায় না। অথচ এঁরাই নিজেদের আহলে বাইতের প্রেমিক বলে দাবি করে। এই বিশ্বাসঘাতকতা ইসলামের ইতিহাসে এক অবর্ণনীয় কলঙ্ক। এমনকি ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একবার ইরাক থেকে আগত এক লোককে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, “তুমি মাছি মারা বৈধ কি না তা জানতে চাইছো অথচ তোমরাই নবীর নাতিকে (ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু) হত্যা করেছো!” তাঁর এই বক্তব্য শুধু ক্ষোভ নয়, বরং এক মহা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ধিক্কার।

সত্য হলো, কারবালার ঘটনায় যাঁরা সরাসরি অস্ত্র ধরেছে, যারা হুসাইন (রাঃ)-কে একা ফেলে দিয়েছিল, যারা তাঁকে আশ্বাস দিয়ে প্রতারিত করেছিল—তাঁরাই তাঁর শাহাদতের জন্য প্রকৃত দায়ী। ইয়াজিদের নাম, মুয়াবিয়ার ভূমিকা, সুন্নিদের দায়—এসব নিয়ে বহু বিতর্ক চলেছে এবং চলবেও। কিন্তু সরাসরি হত্যায় অংশগ্রহণকারী কারা, হুসাইন (রাঃ)-এর দলছুট হওয়ার পেছনে কারা দায়ী—এই প্রশ্নের জবাব ইতিহাস খুব স্পষ্ট করে দিয়েছে।
কাজেই সত্য যতই তিক্ত হোক, যতই কষ্টদায়ক হোক, তাকে গ্রহণ না করলে ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সৎ ও ন্যায্য থাকে না। হজরত হুসাইন (রাঃ)-এর স্মৃতি শুধুই কান্না আর মিছিলের জন্য নয়, বরং তাঁর জীবন ও শাহাদতের শিক্ষা গ্রহণ করাই প্রকৃত শ্রদ্ধা। আর সেই শিক্ষা শুরু হয় সত্যকে স্বীকার করার সাহস থেকে।
হুসাইন (রাঃ) এর হত্যাকারী নির্ধারণে ইবনে উমর (রাঃ) এর মত
ইতিহাসের নির্মম পরিহাস এই যে, যারা মুখে নবীপ্রেমের দাবি করে, তারাই অনেক সময় এমন কাজ করে বসে যা সেই প্রেমকে চরমভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। এমনই এক দৃশ্য আমরা দেখি সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণনায়, যেখানে তিনি এক সহজ প্রশ্নের জবাবে ইতিহাসের গভীরে আঘাত করেন এবং সত্যকে নির্মমভাবে উন্মোচিত করেন।
ইবনে আবী নু’ম (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত রয়েছে—“আমি একদা আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন একজন লোক তাঁকে মশা হত্যা করার হুকুম জানতে চাইল। তিনি তখন লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কোন দেশের লোক? সে বলল: ইরাকের। ইবনে উমর (রাঃ) তখন উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, “তোমরা এই লোকটির প্রতি লক্ষ্য কর। সে আমাকে মশা হত্যা করার হুকুম জিজ্ঞেস করছে। অথচ তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাতিকে হত্যা করেছে। আর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, এরা দুজন (হাসান ও হুসাইন (রাঃ) আমার দুনিয়ার দুটি ফুল।” (সহীহ বুখারী, হাদিস নম্বর–৫৯৯৪)
এই সংলাপ কেবল একটি আক্ষেপ নয়, বরং এটি এক গভীর বেদনার বহিঃপ্রকাশ—যেখানে এক সাহাবি মুখোমুখি হয়েছেন এমন এক বাস্তবতার, যা তাঁকে শিহরিত করে তুলেছে। একটি নগণ্য প্রাণীর (মশা) রক্ত ঝরানো বৈধ কি না, তা জানতে চাওয়া মানুষটি এমন এক অঞ্চল থেকে এসেছে, যার অধিবাসীরা সদ্য ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কজনক হত্যাকাণ্ডে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে অংশ নিয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-এর কণ্ঠে ফুটে ওঠা বিস্ময়, ক্ষোভ ও হতাশা—সবই যেন একত্রিত হয়ে ধ্বনিত হয় একটিমাত্র বাক্যে, “তারা নবীর নাতিকে হত্যা করেছে।”
এই ঘটনার পটভূমিতে রয়েছে কারবালার নির্মম সত্য। হজরত হুসাইন (রাঃ) যে কুফাবাসীদের ডাকে সাড়া দিয়ে ঘর ছেড়েছিলেন, তাঁরাই পরে তাঁকে বিশ্বাসঘাতকতার ফাঁদে ফেলে দেয়। তাঁর পক্ষের বায়াতকারী হাজার হাজার মানুষ মুখ ফিরিয়ে নেয়, অনেকেই শত্রু পক্ষের সঙ্গে হাত মেলায়। আর যাঁরা নিরব ছিলেন, তাঁরাও দাঁড়িয়ে দেখেন কীভাবে নবী (সা.)-এর প্রিয় নাতিকে পিপাসার্ত রেখে হত্যা করা হচ্ছে। এই নির্লজ্জতা, এই নিষ্ঠুরতা কেবল শত্রুর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং বন্ধু ও অনুসারীর মুখোশ পরা বিশ্বাসঘাতকেরাই এই ঘটনায় বড় ভূমিকা রাখে।
ইবনে উমর (রাঃ) এর উক্তি এই দিকটি খুব সুস্পষ্টভাবে সামনে এনে দেয়। একদিকে একটি তুচ্ছ প্রাণের মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন, অন্যদিকে বিশ্বমানবতার এক মহাপ্রাণের অবমাননাকর মৃত্যু নিয়ে কোনো অনুশোচনাই নেই—এই বৈপরীত্য তাঁকে স্তব্ধ করে দেয়। যে জাতি একদিকে আহলে বাইতের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার দাবি করে, অন্যদিকে তাদেরই রক্তে হাত রাঙায়, তাদের ভণ্ডামি ইবনে উমর (রাঃ)-এর চোখে ধরা পড়ে যায়।
এই হাদিসের আরেকটি দিক হলো, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বক্তব্য, “এরা দুজন (হাসান ও হুসাইন) আমার দুনিয়ার দুটি ফুল।” এ শুধু আবেগমাখা প্রশংসা নয়, বরং একটি ঐশী স্বীকৃতি—এই দুই সন্তান শুধু পারিবারিক নয়, বরং উম্মাহর জন্য এক বিশেষ আশীর্বাদ। সেই ফুল ছিঁড়ে ফেলা, সেই সুগন্ধ বিলীন করে দেওয়া যেন স্রেফ একটি মানবহত্যা নয়, বরং একটি ঐতিহাসিক আত্মহত্যা।
আজ যখন আমরা কারবালার ঘটনা স্মরণ করি, তখন শুধু কান্না আর শোক প্রকাশ করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। ইতিহাসের গভীরে ডুবে গিয়ে দেখতে হয়, কে কার পক্ষে ছিল, কে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, কারা নিষ্ক্রিয় থেকেছিল। সাহাবি ইবনে উমর (রাঃ)-এর এই সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর কথার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এক অমোঘ প্রশ্ন—আমরা কোন পক্ষে ছিলাম, কাদের উত্তরসূরি হয়ে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছি?
এই আত্মজিজ্ঞাসা থেকেই ইতিহাসের সত্য উদ্ভাসিত হয়। আর সেই সত্যকে স্বীকার করাই ইতিহাসের প্রতি প্রকৃত সম্মান। হজরত হুসাইন (রাঃ) ছিলেন সত্য, ন্যায় ও আত্মত্যাগের প্রতীক। তাঁর শাহাদত যেন আমাদেরকে শুধু আবেগে নয়, বরং বিবেকেও জাগ্রত করে তোলে। ইতিহাসের এই আয়নায় তাকিয়েই আমরা বুঝতে পারি, কোনটা ফুল, আর কোনটা কাঁটা।
হজরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর ভাষণ থেকে প্রমাণিত যে ইয়াজিদ তাঁর হত্যাকাণ্ডের জন্য সরাসরি দায়ী নয়
ইতিহাসের এক অমোচনীয় দাগ হয়ে আজও কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা মুসলিম হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটায়। এই ঘটনা শুধুমাত্র এক মহাপুরুষের শাহাদত ছিল না; এটি ছিল প্রতারণার, বিশ্বাসভঙ্গের এবং দ্বিচারিতার এক নিষ্ঠুর দলিল। হজরত হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন ইয়াজিদের বায়আতের বিরোধিতা করে মদিনা ত্যাগ করেন, তখন তিনি যুদ্ধের জন্য নয়, বরং সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নেয়ার জন্যই রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে যারা আহ্বান জানিয়েছিল, তারাই যখন তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র তোলে, তখন সেই বিশ্বাসঘাতকতার গ্লানি থেকে তাঁরা আর কখনও মুক্ত হতে পারেনি।
কারবালার প্রান্তরে দাঁড়িয়ে হুসাইন (রাঃ) যখন তাঁর জীবন ও পরিবার নিয়ে সংকটের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন, তখন তিনি তাঁরই ডাকা অনুসারীদের প্রতি তীব্র আক্ষেপ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন—“তোমরা কি পত্রের মাধ্যমে আমাকে এখানে আসতে আহ্বান করোনি? আমাকে সাহায্য করার ওয়াদা করোনি? অকল্যাণ হোক তোমাদের! যেই অস্ত্র দিয়ে আমরা ও তোমরা মিলে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি, এখন সেই অস্ত্র তোমরা আমাদের বিরুদ্ধেই চালাতে যাচ্ছো। মাছির মতো তোমরা আমার পক্ষে কৃত বায়আত থেকে সরে যাচ্ছো, পোকামাকড়ের ন্যায় উড়ে যাচ্ছো এবং সকল ওয়াদা-অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছো। ধ্বংস হোক এই উম্মতের তাগুতেরা!” (দেখুন: আল-ইহতেজাজ লিত্ তাবরুসী)
এই ভাষণ নিছক ক্ষোভপ্রকাশ নয়; এটি ছিল নির্ভরতার মৃত্যুতে এক মহামানবের হৃদয়বিদারক আর্তনাদ। হুসাইন (রাঃ) তাঁর এই ভাষণে একবারও ইয়াজিদের নাম নেননি, তাঁকে দায়ী করেননি; বরং তাঁর সমগ্র আক্ষেপ কুফার সেই মানুষদের প্রতি, যারা তাঁরই ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁকে আহ্বান করেছিল, এবং পরে তাকে একা ফেলে দিয়ে তার রক্তপাতের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
এই নির্মম বিশ্বাসঘাতকতা তখন আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন হুসাইন (রাঃ)-এরই পক্ষে অবস্থান নেয়া এক সাহসী ব্যক্তি, হুর বিন ইয়াজিদ, নিজেই সৈন্যদলের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন—“তোমরা কি এই নেককার বান্দাকে এখানে আসতে আহ্বান করোনি? তিনি যখন তোমাদের কাছে এসেছেন, তখন তোমরা তাঁকে পরিত্যাগ করেছ এবং তাঁকে হত্যা করার জন্য তাঁর শত্রুতে পরিণত হয়েছ। আর তিনি এখন তোমাদের হাতে বন্দি হয়েছেন। আল্লাহ যেন কিয়ামতের দিন তোমাদের পিপাসা না মেটান এবং তোমাদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করেন!” (দেখুন: ইরশাদ লিল মুফীদ, পৃষ্ঠা ২৩৪; আলামুল ওরা, পৃষ্ঠা ২৩৪)
এই আহ্বান ছিল এক আত্মগ্লানিতে ভরা অভিশাপ, যা ওই বিশ্বাসঘাতকদের অন্তরে কোনো তাপ সৃষ্টি করেছিল কি না, ইতিহাস তা বলে না। তবে হুসাইন (রাঃ) নিজে তাঁদের জন্য যে বদদোয়া করেছিলেন, তা যেন সময়ের স্রোতে একের পর এক বাস্তব হয়ে ওঠে।
তিনি বলেছিলেন—“হে আল্লাহ! আপনি যদি তাদের হায়াত দীর্ঘ করেন, তাহলে তাদের দলের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করে দিন। তাদেরকে দলে দলে বিচ্ছিন্ন করে দিন। তাদের শাসকদেরকে তাদের উপর কখনই সন্তুষ্ট করবেন না। তারা আমাদেরকে সাহায্য করবে বলে ডেকে এনেছে। অতঃপর আমাদেরকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হয়েছে।” (দেখুন: ইরশাদ লিল মুফীদ, পৃষ্ঠা ২৪১; আলামুল ওরা, পৃষ্ঠা ৯৪৯; কাশফুল গুম্মা ১৮:২ ও ৩৮)
এই বদদোয়া থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, হুসাইন (রাঃ) তাঁর শাহাদতের পেছনে সরাসরি দায়ী করেছেন সেই কুফাবাসীদের, যাঁরা শিয়া পরিচয়ে নিজেদের গর্বিত ভাবতেন, কিন্তু প্রয়োজনে তাঁর পক্ষে দাঁড়াননি। বরং তাঁকে শত্রুদের হাতে তুলে দিয়ে নিজে প্রাণ রক্ষা করেছেন এবং উমাইয়া শাসকদের সন্তুষ্টি অর্জন করেছেন। হুসাইন (রাঃ) এদের জন্যই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন, যাতে তাদের দল বিভক্ত হয়, তারা দলাদলিতে লিপ্ত থাকে এবং তাদের শাসকদের প্রতি তারা যেন কোনোদিন শান্তিতে থাকতে না পারে।
এই দোয়ার পরিণতি ইতিহাস স্বয়ং সাক্ষ্য দিয়ে গেছে। একসময় যাঁরা হুসাইন (রাঃ)-এর রক্তে হাত রাঙিয়েছিল, তারাই একে একে নির্মম পরিণতির শিকার হয়েছে। উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ, যার নেতৃত্বে এই হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছিল, তাকেও পরবর্তী সময়ে অত্যন্ত অপমানজনক ও করুণভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়। তার পতন শুধু ব্যক্তিগত ছিল না, বরং এক রাজনৈতিক দল এবং মতেরও পতনের বার্তা বয়ে এনেছিল।
হুসাইন (রাঃ)-এর হত্যার দায় সরাসরি কোনো দূরবর্তী খলিফার নয়, বরং যারা তাঁকে ডেকেছিল, যারা তাঁর সঙ্গে থাকার শপথ করেছিল, যারা তাঁর পেছনে নামাজ আদায় করেছিল, তারাই তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ইতিহাসে এমন নিষ্ঠুর প্রতারণার দৃষ্টান্ত খুব কমই দেখা যায়। আর এই ইতিহাস আমাদের শেখায়—সত্যের দাবিদার হয়ে মিথ্যার সঙ্গে আপস করা যে কত বড় অপরাধ, তা শুধু মুখে নয়, বরং ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রক্ত দিয়ে লেখা থাকে।
হুসাইন (রা) এর পুত্র আলি বিন হুসাইন (রাঃ) তাঁর পিতার হত্যার জন্য কুফা বাসীদেরকে দায়ী করেছেন?
ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, একদিকে প্রতারণা, আর অন্যদিকে সেই প্রতারণার উপর কান্না—এই দ্বিচারিতা শুধু মর্মান্তিকই নয়, এক ভয়াবহ আত্মপ্রতারণার প্রতিফলনও বটে। হজরত হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদতকে কেন্দ্র করে যারা নিজেদের নিঃস্ব, ব্যথিত, শোকগ্রস্ত বলে দাবি করে, সেই তারাই যখন এই হত্যাকাণ্ডের পেছনের মূল চরিত্র, তখন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানো ছাড়া আর কোনো পথ থাকে না।
শিয়া ঐতিহাসিক ইয়াকুবী লিখেছেন—
“আলি বিন হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন কুফায় প্রবেশ করলেন, তখন দেখলেন কুফার নারীরা হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হত্যার বেদনায় বিলাপ করছে ও চোখের জল ফেলছে। তখন তিনি বিস্ময়ভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, “এরা কি আমাদের হত্যার জন্য বিলাপ করছে? তাহলে আমাদেরকে হত্যা করল কে?” অর্থাৎ, যারা এখন শোক করছে, তারাই আমাদের পরিবার ও আত্মীয়দের হত্যা করেছে।” (দেখুন: তারিখে ইয়াকুবী ১/২৩৫)
এই বক্তব্য যেন এক তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের মতো ভেসে আসে ইতিহাসের গভীর থেকে। এটি শুধু কুফার নারীদের নয়, বরং সমগ্র শিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এক জাগ্রত অভিযোগ, যারা নিজেদের হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রেমিক বলে দাবি করে, অথচ বাস্তবে তাঁকে একা ফেলে দিয়েছিল। তাঁকে ডেকে এনে পিপাসার্ত রেখে হত্যা করেছিল। অতঃপর সময়ের ব্যবধানে তারাই আবার কাঁদতে শুরু করে, বুক চাপড়ে শোক প্রকাশ করে—এ যেন ঘাতকেরই পরে ক্রন্দনরত রূপ!
এই দ্বিমুখী আচরণ আজও বহু জায়গায় বিদ্যমান। যারা নিজেরাই হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মৃত্যুর জন্য দায়ী, তারাই আজ নানা আয়োজন করে তাঁকে স্মরণ করে, তাঁর নামে মিছিল করে, মাতম করে। অথচ সেই কান্না, সেই শোক কী নিঃস্বার্থ ভালোবাসা থেকে? না কি এক অপরাধবোধের আবরণমাত্র?
প্রশ্নটা এখানেই—যদি এই শোক প্রকাশ হয় আহলে বাইতের প্রতি গভীর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ, তাহলে একই ভালোবাসা কেন পাওয়া যায় না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচা সায়্যেদুনা হামজা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি? তিনি তো “শহীদদের সরদার” উপাধি লাভ করেছেন। তাঁর মৃত্যু কি হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদতের চেয়ে কম করুণ? উহুদের প্রান্তরে তাঁকে শুধু হত্যা করা হয়নি, বরং তাঁর দেহ টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছিল, তাঁর কলিজা বের করে চিবানো হয়েছিল। এ কেমন পাশবিকতা! কিন্তু আমরা কি দেখতে পাই তাঁর জন্য কোনো বাৎসরিক মাতম, শোক মিছিল, বুক চাপড়ানো বা কাপড় ছিঁড়ে আহাজারি?
এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মৃত্যু—যা গোটা উম্মাহর ওপর সবচেয়ে বড় আঘাত, সে মৃত্যুতে কি কেউ বাৎসরিক শোক পালন করে? কেউ কি বুক চাপড়ে ক্রন্দন করে?—না, এমন কিছু দেখা যায় না। তাহলে কেন শুধু হজরত হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ক্ষেত্রেই এই অতিরিক্ত আবেগ ও কর্মসূচি?
এই প্রশ্নের উত্তর অনেকের কাছে অস্বস্তিকর হলেও, তা খোলাসা করাই ইতিহাসের দায়িত্ব। হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একজন পারস্য বংশোদ্ভূত নারীকে বিয়ে করেছিলেন। অনেক শিয়া ঐতিহাসিক এই তথ্যটিকে তাঁদের আবেগের উৎস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এটি অস্বীকার করার কোনো প্রয়োজন নেই যে, জাতিগত টান অনেক সময় ধর্মীয় আবেগকে ছাপিয়ে যায়। সেই টানই হয়তো হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদতের প্রতি অতিরিক্ত আবেগের একটি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার অনেকে এমনও বিশ্বাস করেন যে, আহলে বাইতের প্রতি অতি আবেগপ্রবণতা আসলে সুস্থ ভালোবাসা নয়, বরং একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস ও নির্ভেজাল আবেগনির্ভর রাজনীতি।
এই মিথ্যা আবেগ চিরকালই ইতিহাসকে বিকৃত করেছে। হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর পিতা আলি (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে নিয়ে শিয়াদের আকীদা বা ধর্ম বিশ্বাস ও বিশ্বাস বহু ক্ষেত্রেই মূলধারার ইসলাম থেকে বিচ্যুত। তবে সেই প্রসঙ্গে প্রবেশ না করে এখানেই বিষয়টি সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে। উদ্দেশ্য কাউকে আঘাত করা নয়, বরং ইতিহাসের আয়নায় সত্যের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা।
এই প্রতিচ্ছবিতে দেখা যায়—হত্যাকারীই কান্নাকারী, আর প্রতারণার ইতিহাস ঢাকতে গিয়ে শোকের মুখোশ পরে চলেছে এক সম্প্রদায়, যারা হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নামে আজও রাস্তায় নামে, অথচ তাঁর আদর্শ ও সত্যের পথে দাঁড়াতে গিয়ে একদিন তাঁকেই একা ফেলে দিয়েছিল। ইতিহাস কখনো ভুলে না। আর ইতিহাস যখন কথা বলে, তখন চোখের জলও অনেক সময় তা ধুয়ে দিতে পারে না।
হুসাইন (রাঃ) এর কাটা মাথা কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?
কারবালার প্রান্তরে ঘটিত হজরত হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদতের পরবর্তী ইতিহাস নিয়ে বহু মুখে বহু কথা চালু থাকলেও, ইসলামের বিশ্বস্ত গ্রন্থসমূহে যেটুকু বিশুদ্ধ তথ্য সংরক্ষিত আছে, তা থেকেই আমরা কিছুটা নির্ভরযোগ্য চিত্র আঁকতে পারি। বহুল প্রচলিত একটি ধারণা রয়েছে যে, হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সম্মানিত মাথা দামেস্কে ইয়াজিদের দরবারে প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সূত্রসমূহ এই তথ্যকে সমর্থন করে না। কোনো সহিহ সনদের হাদিসে কিংবা স্বীকৃত ইতিহাস গ্রন্থে এমনটি নিশ্চিতভাবে বর্ণিত হয়নি।
পরীক্ষিত ও গ্রহণযোগ্য তথ্য অনুযায়ী, হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সম্মানিত মাথা প্রথমে কুফার গভর্নর উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ইমাম বুখারির প্রসিদ্ধ হাদিসে আনাস ইবন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর একটি গভীর হৃদয়বিদারক বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, “হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মাথা উবাইদুল্লাহর নিকট নিয়ে যাওয়া হলে তিনি তা একটি থালার মধ্যে রেখে একটি কাঠি হাতে নিয়ে মাথার নাকের ছিদ্র দিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। মুখের সৌন্দর্য দেখে কিছু আবেগমিশ্রিত বাক্যও তিনি বলে ফেলেন। এরপর আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন—“হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ।” (বুখারি)
আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উবাইদুল্লাহকে লক্ষ্য করে বলেন, “তুমি যে স্থানে কাঠি রাখছো, সেই স্থানে আমি নিজ চোখে দেখেছি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুমু খেয়েছেন। অতএব, এই কাঠি সরিয়ে ফেলো।” এই কথায় উবাইদুল্লাহ কাঁপতে থাকেন এবং কাঠি সরিয়ে নেন। (দেখুন: ফতহুল বারী ৭/৯৬)
এই ঘটনাবলির আলোকে দেখা যায়, হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সম্মানিত মাথার পরবর্তী গন্তব্য নিয়ে স্পষ্টতা পাওয়া যায় না। কোথায় তাঁর দাফন হয়েছে, মাথা ও দেহ একত্রে মাটিচাপা পেয়েছে কিনা—এসব বিষয়ে কোনো নির্ভরযোগ্য দলিল পাওয়া যায় না।
তবে ইতিহাসে এক অমোঘ সত্য বারবার প্রতিফলিত হয়—“যেমন কর্ম, তেমন ফল।” দুনিয়ায় যাঁরা যুলুমের পথে হেঁটেছেন, ইতিহাস কখনো তাদের ছেড়ে দেয়নি। উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ, যিনি কারবালার ঘটনার নেপথ্য কারিগর, তাঁকেও শেষ পর্যন্ত নির্মম পরিণতি বরণ করতে হয়েছে। তিনি যখন মুকাবালায় নিহত হন, তখন তাঁর মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কুফার মসজিদে আনা হয়। জনসাধারণের সামনে তাঁর মাথা প্রদর্শনের সময় এক অবাক করা ঘটনা ঘটে—একটি সাপ এসে তাঁর কাটা মাথার চারপাশে ঘুরতে থাকে। তারপর সেই সাপ তাঁর নাকের ছিদ্র দিয়ে ঢুকে মুখ দিয়ে বের হয়। আবার মুখ দিয়ে ঢুকে নাক দিয়ে বের হয়। এভাবে তিনবার এমন দৃশ্য দেখা যায়। (দেখুন: তিরমিযী, ইয়াকুব ইবন সুফিয়ান)

এ ঘটনা ইতিহাসে শুধু একটি অলৌকিক দৃষ্টান্ত নয়; এটি এক প্রতীকী প্রতিশোধ, যা যেন আল্লাহর পক্ষ থেকেই তাঁর অপকর্মের জবাব ছিল। যিনি রাসূলের দৌহিত্রকে নির্মমভাবে শহীদ করার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তিনিই একসময় নিজেই নির্মম পরিণতির স্বীকার হন। ইতিহাস এইভাবেই প্রতিহিংসার জবাব দেয়। মানবজাতির জন্য এর মধ্যে রয়েছে গভীর শিক্ষা।
আমরা দেখতে পাই, এই ঘটনার শুরুতে যাঁরা অন্যায় করেছিল, শেষ পর্যন্ত তারাই সেই অন্যায়ের তীব্র প্রতিক্রিয়ার মুখে পড়েছে। যুগ যুগ ধরে ইতিহাস এসব শাসকদের নাম শুধু অভিশাপের সাথেই উচ্চারণ করে এসেছে। পক্ষান্তরে যাঁরা সত্য ও ন্যায়ের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের নাম আজো উচ্চারিত হয় শ্রদ্ধা, ভালোবাসা আর অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে। হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন সেই সত্যের প্রতীক, যাঁকে হত্যা করেও ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলা যায়নি। বরং যাঁরা তাঁকে হত্যা করেছিল, তারাই ইতিহাসে চিরদিনের জন্য ঘৃণার পাত্র হয়ে রয়েছে।
ইয়াজিদ সম্পর্কে একজন মুসলিমের কিরকম ধারণা রাখা উচিত
তাফসীর, হাদীস, আকীদা, জীবনী ও ইতিহাস বিষয়ক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহ পর্যালোচনা করলে যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়, তা হলো—ইসলামের প্রাথমিক যুগের শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম, যাঁদেরকে সালফে সালেহীন বলা হয়, তাঁদের কারো মাধ্যমেই ইয়াজিদ ইবনু মুয়াবিয়ার ওপর প্রকাশ্যে লানত করা, গালাগাল করা, কিংবা তাঁকে অভিশপ্ত বলার অনুমোদন পাওয়া যায় না। ইসলামী জ্ঞানতাত্ত্বিক ধারাবাহিকতায় যাঁরা সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ইমাম, মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিস হিসেবে পরিচিত, তাঁদের রচনাবলিতে কখনোই ইয়াজিদের নামের শেষে “রাহিমাহুল্লাহ” (আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন) কিংবা “লাআনাহুল্লাহ” (আল্লাহ তাঁর উপর অভিশাপ বর্ষণ করুন)—এই দুটি বাক্যের কোনোটিই ব্যবহার করা হয়নি। এ এক নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ যে, তাঁরা এ বিষয়ে মৌন থাকাকেই নিরাপদ মনে করেছেন।
ইসলামী শরীয়তের মৌলিক নীতিমালায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা রয়েছে—“যে বিষয় সম্পর্কে তুমি নিশ্চিত নও, তা নিয়ে কথা বলা থেকে বিরত থাকো।” ইয়াজিদের ব্যক্তিজীবন ও আমল নিয়ে ইতিহাসে যত আলোচনা রয়েছে, তার বেশিরভাগই নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে নয়, বরং কিয়দংশ সন্দেহযুক্ত, বিভ্রান্তিকর বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এমনকি যেসব অপরাধের কথা তাঁর বিরুদ্ধে প্রচার করা হয়—যেমন মদ্যপান, অশ্লীল কাজে জড়ানো, খেলাধুলায় ডুবে থাকা—এসবের পক্ষে সহিহ সূত্রভিত্তিক প্রমাণ এখনও পর্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। উপরন্তু, ইসলামী শরীয়তের নির্দেশনা হলো, কেউ যদি ইসলামের ঘোষিত বিশ্বাসের ওপর থেকে না সরে যায়, তাহলে তাকে মুসলিম গণ্য করতে হবে এবং তার গোনাহ আল্লাহর বিচারাধীন।
ইমাম যাহাবী, যিনি ইসলামী ইতিহাসে এক নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য গবেষকের মর্যাদায় অভিষিক্ত, ইয়াজিদের সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—
“لانسبه ولانحبه“
অর্থাৎ, “আমরা তাঁকে গালি দিবো না, আবার ভালোও বাসবো না।”
এ বক্তব্যের ভেতরে নিহিত রয়েছে এক সংযমী দৃষ্টিভঙ্গি। কেননা, ইতিহাসে বহু চরিত্র রয়েছে যাদের কার্যকলাপে বিরোধ ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু তাদের পরিণতি নিয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না, কারণ আমরা কেউই তাদের মৃত্যুর সময়কার ঈমানের অবস্থা জানি না।
হজরত হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি ইয়াজিদের অবস্থান, কিংবা কারবালার ঘটনায় তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা নিয়ে বহু আলোচনা থাকলেও, এই আলোচনার ভিত্তিতে তাঁর ওপর আজীবন লানত বর্ষণ করা বা তাঁকে ইসলামের সীমার বাইরে ঠেলে দেওয়া ইসলামী আকীদা অনুযায়ী সঙ্গত নয়। কেননা শরীয়তের মৌলিক বিধান হলো, কোনো ব্যক্তি অপরাধী হলে তার বিচার শরীয়তের প্রক্রিয়ায় করতে হয়। অথচ আমরা জানি না, ইয়াজিদের অন্তরের অবস্থা কী ছিল কিংবা তিনি মৃত্যুর আগে সত্যিকার অর্থে অনুতপ্ত হয়েছিলেন কিনা।
তাছাড়া, ইয়াজিদের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ইতিহাসে এমন এক ঘটনা দিয়ে চিহ্নিত হয়েছে, যা কিছুটা আশাব্যঞ্জক। ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীস উল্লেখ করেন, যেখানে তিনি বলেন:
“আমার উম্মতের একটি বাহিনী কুস্তুনতিনিয়ায় যুদ্ধ করবে, এবং তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন।”
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, কুস্তুনতিনিয়ার (বর্তমান ইস্তাম্বুল) প্রথম মুসলিম অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া। সেই অভিযানে হজরত হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-ও অংশ নিয়েছিলেন একজন সাধারণ সেনানী হিসেবে। এই তথ্য জানার পর যদি হাদীসটির মাহাত্ম্য গ্রহণ করা হয়, তাহলে বলা যেতে পারে—তাঁর জন্য ক্ষমা লাভের একটি সম্ভাবনা রয়ে যায়। তবে চূড়ান্ত বিচার একমাত্র আল্লাহর এখতিয়ারে।
সুতরাং, কোনো মুসলিমের জন্য এ বিষয়টি একেবারে স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, যাঁর ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য দলিল নেই, যাঁর অন্তরের অবস্থা আমরা জানি না, এবং যাঁর শেষ জীবনের ঈমানের অবস্থা আমাদের অজানা—তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা, গালাগাল করা বা অভিশাপ বর্ষণ করা ইসলামী শিষ্টাচারের পরিপন্থী। বরং ইসলামের সৌন্দর্য এখানেই যে, আমরা যে কারও বিচার আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেই এবং নিজেদের আমলের প্রতি মনোযোগী হই। কারণ, কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমলের জবাবদিহি করবে। ইয়াজিদের আমল নিয়ে আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছা বিচার করবেন; কিন্তু আমাদের জবান যদি সীমা লঙ্ঘন করে, তাহলে তার জবাবদিহি আমাদেরকেই করতে হবে। তাই সব দিক বিবেচনায় নিরবতা ও সংযমই এখানে উত্তম পথ।
ইয়াজিদের ব্যপারে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মত
ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার ব্যক্তিত্ব ও তার শাসনকাল নিয়ে ইসলামী ইতিহাসে নানামাত্রিক মতভেদ রয়েছে। সময়ের ধারায় মুসলিম সমাজ তার বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করেছে। এ বিষয়ে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া গভীর ও পরিমিত বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন, যা মুসলিম ঐতিহাসিক এবং ধর্মতত্ত্ববিদদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে।
ইবনে তাইমিয়া বলেন, ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ানের ব্যাপারে মানুষ তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল— দুটি দল ছিল চরমপন্থী, এবং একটি ছিল মধ্যপন্থী। প্রথম চরমপন্থী দলটি তাকে ঘৃণা করত এবং তার বিরুদ্ধে কঠোর ও তীব্র অভিযোগ আনত। তারা বলত, সে একজন কাফির এবং মুনাফিক, কারণ সে রাসূলের প্রিয় দৌহিত্র হুসাইন ইবনে আলিকে হত্যা করেছে। তাদের মতে, সে নবীকে ঘৃণা করত এবং বদরের যুদ্ধে নিহত তার আত্মীয়-স্বজনদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গি মূলত শিয়া মতবাদপ্রবণ রাফেযীদের অন্তর্গত, যারা আবু বকর, উমর ও উসমানকে বিশ্বাস করে না এবং কাফির মনে করে। ফলে তাদের পক্ষে ইয়াজিদকে কাফির মনে করা সহজ।
অন্যদিকে, দ্বিতীয় চরমপন্থী দলটি তার ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান নেয়। তারা মনে করে, ইয়াজিদ ছিলেন একজন ধার্মিক ও ন্যায্য শাসক, বরং কেউ কেউ তাকে সাহাবী দাবি করে, এমনকি কেউ কেউ তাকে আবু বকর ও উমরের চেয়েও উচ্চতর স্থান দেয়, আবার কেউ কেউ তাকে নবীর সমকক্ষ মনে করে। এই অবস্থানটি অসত্য এবং বিভ্রান্তিকর। এমন ধারণা কেবল সেইসব লোকের পক্ষেই সম্ভব, যাদের জ্ঞানের পরিধি সংকীর্ণ এবং যারা ইসলামের প্রাথমিক যুগের বাস্তবতা ও সাহাবীদের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ। এই মতামতকে কোনো সুস্থ চিন্তার মানুষ কিংবা সুন্নাহপন্থী কোনো জ্ঞানী পণ্ডিত সমর্থন করেন না।
তবে তৃতীয় ও মধ্যপন্থী মতটি হলো— ইয়াজিদ ছিলেন মুসলিমদের একজন বাদশাহ, যিনি যেমন ভালো কাজ করেছেন, তেমনি মন্দ কাজও করেছেন। তিনি উসমান ইবনে আফফানের খেলাফতের সময়ও জন্মগ্রহণ করেননি, ফলে সাহাবী ছিলেন না। তিনিও আল্লাহর কোনও প্রিয় বন্ধু ছিলেন না। তিনি যে অপরাধগুলো করেছেন, যেমন হুসাইনের হত্যাকাণ্ডে তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পৃক্ততা, হাররা নামক স্থানে মদিনাবাসীদের ওপর তার বাহিনীর আক্রমণ, এগুলো তার শাসনামলের কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত। তা সত্ত্বেও তাকে কাফির বলে রায় দেওয়া যায় না। এই মধ্যপন্থী মতই অধিকাংশ জ্ঞানী, বিচক্ষণ এবং আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের পণ্ডিতদের অবস্থান।
তাঁদের মতে, ইয়াজিদের ব্যাপারে তিনটি প্রবণতা সমাজে গড়ে ওঠে— একদল তাকে অভিশাপ দেয়, একদল তাকে ভালোবাসে এবং গুণগান করে, আরেক দল তার না প্রশংসা করে, না নিন্দা করে। এই শেষোক্ত দলটি হলো সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ, যারা অতিরঞ্জন বা ঘৃণার চরম পথে না গিয়ে যুক্তি ও ইতিহাসের আলোকে সংযত মূল্যায়ন করে।
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এর বক্তব্য এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে গুরুত্ববহ। তাঁর পুত্র সালেহ ইবনে আহমদ একবার তাঁকে বলেছিলেন— কিছু লোক দাবি করে যে তারা ইয়াজিদকে ভালোবাসে। উত্তরে ইমাম আহমদ বলেছিলেন, “হে আমার পুত্র, কেউ কি ইয়াজিদকে ভালোবাসতে পারে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে?” আবার সালেহ জিজ্ঞাসা করেছিলেন— “তবে আপনি তাকে অভিশাপ দেন না কেন?” উত্তরে তিনি বলেন, “হে আমার পুত্র, তুমি কখন তোমার পিতাকে কাউকে অভিশাপ দিতে দেখেছো?” এ উত্তরের মধ্যে ইসলামী আদব ও ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে।
আবু মুহাম্মদ আল-মাকদিসিকে যখন ইয়াজিদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তিনি বলেন, “আমি যা শুনেছি তা অনুসারে তাকে অভিশপ্ত করা উচিত নয় এবং তাকে ভালোবাসাও উচিত নয়।” একই প্রশ্ন করা হয়েছিল ইবনে তাইমিয়াকেও। তিনি বলেন, “আমরা তার ভালো গুণাবলী অস্বীকার করি না বা সেগুলি সম্পর্কে অতিরঞ্জন করি না।” এটিই সবচেয়ে ন্যায়সংগত এবং পরিমিত দৃষ্টিভঙ্গি।
আসলে ইসলামী চিন্তায় কোনো ব্যক্তির মূল্যায়ন শুধু আবেগ দিয়ে নয়, বরং দলিল, ইতিহাস এবং প্রাসঙ্গিক বিচার দিয়ে করতে হয়। ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার ক্ষেত্রে ঠিক সেটিই হওয়া উচিত। ইতিহাস তাকে এমন এক শাসকেরূপে স্মরণ করে, যার শাসনকাল মুসলিম উম্মাহর জন্য গভীর বেদনা, শোক ও বিভেদের সূচনা করেছিল। তাঁর কর্ম ও চরিত্র নিয়ে দ্বিমত থাকা স্বাভাবিক, তবে যেকোনো অবস্থান গ্রহণের আগে সংযম, ন্যায্যতা ও প্রমাণনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গিই কাম্য। ইসলামের নীতিমালা অনুযায়ী, না তো তাকে ফেরেশতার মর্যাদা দেওয়া যাবে, না তাকে চূড়ান্তভাবে অভিশপ্ত ঘোষণা করা যায়— বরং তার ভালো-মন্দ দুয়েরই স্বীকৃতি দেওয়া উচিত যথাযোগ্য পরিপ্রেক্ষিতে। ইতিহাসকে বুঝতে হলে আবেগ নয়, বরং প্রজ্ঞা, জ্ঞান এবং ইনসাফই হওয়া উচিত আমাদের পথপ্রদর্শক।
একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, হজরত হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইসলামের ইতিহাসে এক মহান আত্মত্যাগের প্রতীক। তিনি সত্যের পক্ষে দৃঢ় অবস্থানে ছিলেন এবং সর্বোচ্চ আত্মবলিদান করে সেই অবস্থানকে অমর করে তুলেছেন। তাঁর ওপর যে অন্যায়, নিষ্ঠুরতা ও জুলুম করা হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে ইতিহাসের এক করুণ অধ্যায়। তিনি নিঃসন্দেহে একজন মাজলুম ছিলেন। তাঁকে শহীদ করা হয়েছিল নির্মম ও অবিচারের মাধ্যমে।
কিন্তু এই মর্মান্তিক ঘটনার পেছনে কার কতটুকু দায়—বিশেষত ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার দায় কতখানি—এই প্রশ্নের উত্তরে সরাসরি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ নয়। কারণ, এ সংক্রান্ত সব তথ্য-প্রমাণ ইতিহাসনির্ভর। আর ইতিহাস, বিশেষত প্রাচীন কালের ইতিহাস, নির্ভরযোগ্য সূত্রে দুর্ভাগ্যজনকভাবে সংরক্ষিত হয়নি। বরং দেখা যায়, শিয়া ও কিছু পক্ষপাতদুষ্ট ঐতিহাসিকেরা এই ঘটনাগুলোকে তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন, যাতে আবেগ ও দলীয় প্রবণতার প্রভাব সুস্পষ্ট। কুরআন ও সহীহ হাদীসে এই ব্যাপারে নির্ভরযোগ্যভাবে কিছু উল্লেখ নেই। ফলে এখানে মন্তব্য করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সাবধানতা ও সংযম জরুরি।
ইসলামী আকীদার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এমন কোনো বিষয়ের বিষয়ে চূড়ান্ত রায় না দেওয়া যার পক্ষে নিশ্চিত দলিল নেই। ইয়াজিদের উপর অভিশাপ বর্ষণ বা তাকে কাফের বলা এমন একটি কাজ যার ব্যাপারে ইসলামের নির্ভরযোগ্য মনীষীদের অধিকাংশই নিরব থাকাকেই শ্রেয় ও নিরাপদ জ্ঞান করেছেন। কারণ, কেউ যদি ঈমানের সঙ্গে মারা গিয়ে থাকে, তবে তাকে কাফের বলা কঠিনতম অন্যায়, যা ইসলামের মৌলিক নীতির পরিপন্থী।
এ বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অবস্থান স্পষ্ট ও ভারসাম্যপূর্ণ। তাঁরা কোনো দিন ইয়াজিদের পক্ষে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় লিপ্ত হননি, আবার তাঁকে প্রকাশ্যে গালাগাল করাও অনুমোদন করেননি। কারণ, হজরত হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিরোধিতায় অংশ নেওয়া কিংবা তাঁর শাহাদাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা রাখা একজন মুসলমানের জন্য মারাত্মক অন্যায় ও ঘৃণার বিষয়। কিন্তু ইতিহাস যদি এই ভূমিকার সত্যতা নির্ভরযোগ্যভাবে প্রমাণ করতে না পারে, তাহলে কারও বিরুদ্ধে ফতোয়া দেওয়া কিংবা আখিরাতের ব্যাপারে চূড়ান্ত রায় দেওয়া শরিয়তের দৃষ্টিতে অবিবেচকের কাজ। এই বিষয়ে নিরব থাকা, দ্বিধার জায়গায় না জড়ানো—এটাই প্রকৃত প্রজ্ঞার পরিচয়।
এই মনোভাবই পরবর্তীকালে কবিতার ভাষায় প্রতিফলিত হয়, যেখানে বলা হয়েছে—
“ولم يلعن يزيدا بعد موت
سوى المكثار فى الأغراء غال”
অর্থাৎ
“ইয়াজিদের মৃত্যুর পর কেউ তাকে অভিশাপ দেয়নি,
শুধু সেই উগ্রবাদী ছাড়া, যে উসকানিতে প্রলুব্ধ হয়ে বাড়াবাড়ি করেছে।”
এই বক্তব্যে বোঝানো হয়েছে, ইয়াজিদের মৃত্যুর পর কেবলমাত্র উগ্র ও উস্কানিমূলক মতাবলম্বীরাই তার ওপর লানত বর্ষণ করেছে; সাধারণ মুসলিমসমাজ এবং সালাফে সালেহীনদের কেউ নয়।
মোল্লা আলি কারী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এই কবিতার ব্যাখ্যায় আরও স্পষ্ট করে বলেন—
“لم يلعن أحد من السلف يزيد بن معاوية سوى الذين اكثر والقول فى التحريض على لعنه وبالغوا فى أمره وتجاوزوا عن حده كالرافضية والخوارج وبعض المعتزلة… فلا شك ان السكوت أسلم”
অর্থাৎ, “ইয়াজিদের ওপর সালাফে সালেহীনদের কেউ অভিশাপ বর্ষণ করেননি। কেবলমাত্র রাফেজি, খারেজি ও কিছু মুতাজিলাই এ বিষয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করেছে। অথচ সবচেয়ে নিরাপদ পথ হচ্ছে—নিরবতা।”
সত্যই, নিরবতাই নিরাপদ। কারণ, যাঁর বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান নেই, তাঁর ব্যাপারে মুখ খুলে নিজেকে বিপদে ফেলার কোনো অর্থ নেই। আল্লাহ তাঁর ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, তা সর্বোচ্চ ন্যায়বিচারের ভিত্তিতেই হবে। আমরা আমাদের আমলের হিসাব নিয়েই ব্যস্ত থাকি—এটাই কাম্য।
হজরত হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাত নিঃসন্দেহে ইসলামের ইতিহাসে গভীর শোকের উপলক্ষ। তাঁকে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও তাঁর আদর্শ অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। তবে সেই ভালোবাসা যেন এমন কোনো মাত্রায় না যায়, যেখানে ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করে অন্য কাউকে অযথা কাফের বা অভিশপ্ত বলে ফতোয়া দেওয়া হয়। আমাদের দ্বীন সংযমের শিক্ষা দেয়। ব্যক্তিগত আবেগ নয়, বরং নির্ভরযোগ্য দলিল, হিকমত এবং ইনসাফ—এই তিনের সমন্বয়ে গঠিত নীতিতেই আমরা বিশ্বাস করি।
এই জন্যই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নীতি হলো—”لا نسبه ولا نحبه”—আমরা ইয়াজিদের গালিও দিব না, আবার প্রশংসাও করব না। কেননা তার জীবনে ভাল ও মন্দের মিশ্রণ ছিল। আল্লাহ জানেন তার অবস্থান। তিনিই সর্বোচ্চ বিচারক। আমাদের দায়িত্ব হলো—আমাদের অন্তর ও মুখকে এমন সব ব্যাপার থেকে সংযত রাখা, যা আমাদের ঈমান ও পরকালকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

 নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা
নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা