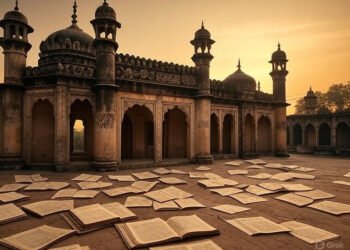লিখেছেনঃ ড. শ্যামাপ্রসাদ বসু
রবীন্দ্রনাথ জওহরলালের চেয়ে আঠাশ বছরের বড় ছিলেন, সুভাষচন্দ্রের চেয়ে ছত্রিশ বছরের। ব্যবধানটা ছিল খুবই বেশি। সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রথম শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন মাত্র সতেরাে বছর বয়সে। দেশােদ্ধারের উপদেশ নিতে। সেই সতেরাে বছরের অপরিণত তরুণকে চোখের সামনে দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ একচল্লিশ বছরের যুবাবয়সে কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতির আসনে বসতে। এ যেন এক চারাগাছের আবহাওয়ার প্রতিকূলতাকে (কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দলাদলি) অগ্রাহ্য করে আপন প্রাণশক্তির জোরে বড় হওয়ার ইতিহাস। আর এই বড় হওয়ার প্রতিটি পর্যায় রবীন্দ্রনাথ পরম আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করেছিলেন।
১৯৪০ সালে (১৮/১৯ এপ্রিল) ‘শনিবারের চিঠি’ পত্রিকার সম্পাদক সজনীকান্ত দাসকে রবীন্দ্রনাথ একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। তাতে তিনি স্বদেশি যুগের স্মৃতির বর্ণনা দিতে গিয়ে বাংলায় কংগ্রেসের দলাদলির প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। যার একদিকে ছিলেন সুভাষপন্থীরা আর অন্যদিকে বিরােধীরা যাঁদের বলা হতাে অ্যাড-হকপন্থী (সুভাষচন্দ্রকে সরিয়ে দিয়ে তৈরি হয়েছিল কংগ্রেসের নতুন নেতৃত্ব)। সে সময়ে অ্যাডহকপন্থীরা গুজব ছড়িয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের ইঙ্গিত সুভাষচন্দ্রের প্রতি। তিনি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছেন। এ ধরনের মিথ্যা গুজব রবীন্দ্রনাথকে এত আহত করেছিল যে তিনি শেষ পর্যন্ত এক প্রেস বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন, মােকাবিলায় আমি সুভাষকে কখনাে ভৎর্সনা করিনি তা নয়, করেছি তার কারণ তাঁকে স্নেহ করি। (৩ জুলাই, ১৯৪০)।
এটা পরিস্কার বলে রাখা ভাল, যতদিন সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসে ছিলেন ততদিন গান্ধিজির সঙ্গে শিল্পায়ন এবং অর্থনীতিতে তার বিরাট কোনাে মৌল পার্থক্য ছিল না। আবার এটাও ঠিক নয় যে তথাকথিত কোনাে মৌল পার্থক্যের জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি এসেছিলেন এবং তাঁর স্নেহধন্য হয়েছিলেন। কারণ রবীন্দ্রনাথও উপরােক্ত দুটি বিষনে গান্ধিজির চেয়ে খুব কিছু তফাতে ছিলেন না।
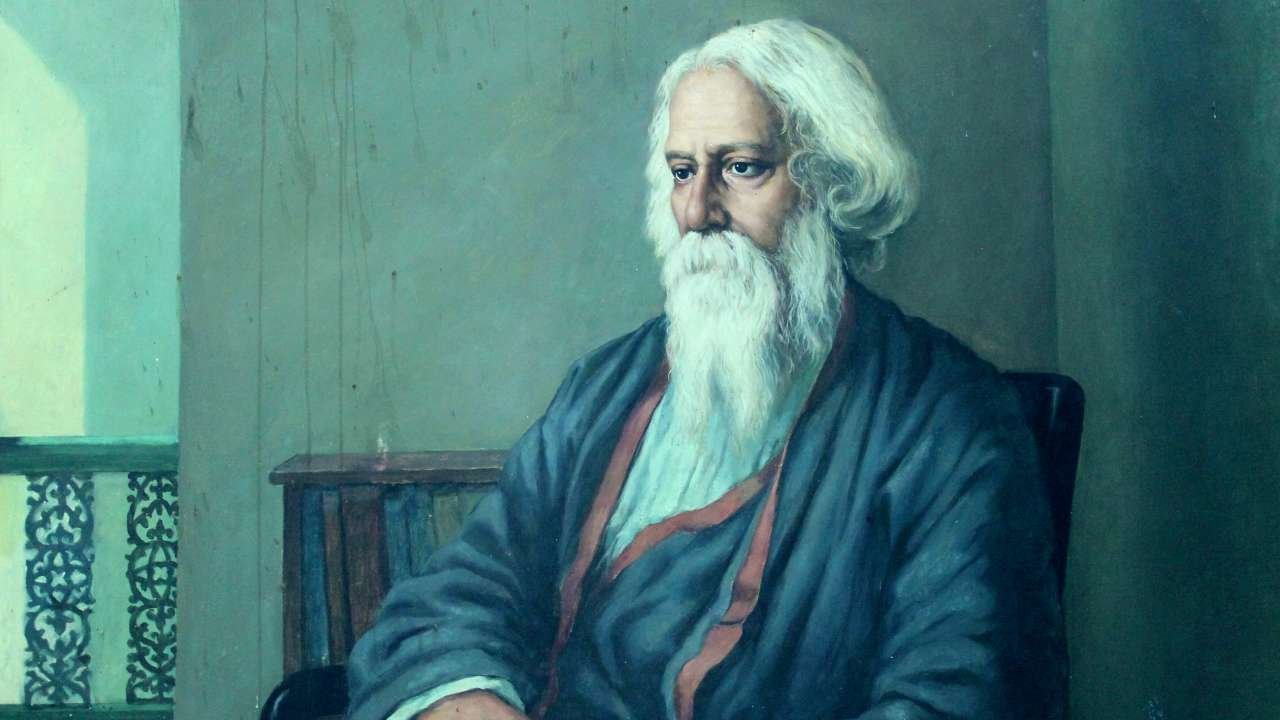
একথা সুবিদিত গান্ধিজি খাদি তথা কুটিরশিল্পের উপর জোর দিয়েছিলেন। যন্ত্রের বিরােধী ছিলেন না। তাঁর বক্তব্য ছিল যন্ত্র যেন মানুষকে নিষ্পিষ্ট না করে দেয়। তাঁর ধারণা ছিল যন্ত্র শ্রমকে বাঁচায় আর তার ফলে হাজার হাজার লােক কাজ বেকার হয়ে পড়ে।
রবীন্দ্রনাথ চরকাকে কখনাে যন্ত্রের বিকল্প হিসেবে স্বীকার করেননি। যন্ত্রকে তিনি বিজ্ঞানের আশীর্বাদ বলেই মনে করতেন। কিন্তু একইসঙ্গে যন্ত্র যেখানে মানুষের আশাআকাঙক্ষায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সেখানে তিনি সরাসরি যন্ত্রের বিরুদ্ধে। কারণ তিনি ‘মুক্তধারা’য় বিশ্বাসী। ‘স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধে বিচিত্র কুটিরশিল্প প্রবর্তন প্রভৃতি বহু পন্থা নির্দেশ করেছিলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল শক্তিলাভ কেননা বিনা শক্তিতে কোনাে জাতি কিছু করে উঠতে পারে না।
হরিপুরা কংগ্রেস (১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮)-এর উদ্বোধনী ভাষণে গান্ধিজি খাদি ও কুটিরশিল্পের উপর গুরুত্ব আরােপ করলেন এবং প্রত্যেকের কাছে আবেদন রাখলেন তারা যেন নিজেদের বাড়িতে অন্তত একটি করে চরকা ব্যবহার করেন। ১৯ ফেব্রুয়ারি সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্ট হিসাবে তাঁর ভাষণে বললেন,
আমাদের শিল্পায়ন-করণকে মেনে নিয়ে দেখতে হবে কীভাবে এর খারাপ দিকটাকে কমানাে যায় এবং একই সাথে কুটিরশিল্পকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে যেখানে বাঁচার সুযােগ আছে বড় কারখানার প্রতিযােগিতা থাকলেও। ভারতের মতাে দেশে কুটিরশিল্পের প্রচুর সুযােগ আছে বিশেষ করে হাতে তৈরি সুতাে ও বােনার ক্ষেত্রে। ঘটনাক্রমে সুভাষচন্দ্র খদ্দর পরতে ভালবাসতেন।
১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন কোনােভাবে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভারতীয়দের হাতে দেয়নি। তবু কংগ্রেস, মুসলিম লিগের মতাে প্রাচীন রাজনৈতিক দলগুলি পরীক্ষামূলকভাবে তা গ্রহণ করতে রাজি হয়েছিল।
অনেকের ধারণা ভারত শাসন আইনের সমালােচনার ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথেব অবস্থান ছিল কাছাকাছি—যা গান্ধিজির থেকে অনেকটা দূরে।
কিন্তু তথ্যের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র এবং গান্ধিজি—প্রত্যেকের সমালােচনাই প্রায় এক সুরে বাঁধা। কেউই সরাসরি ভারত শাসন আইনকে বর্জনের কথা বলেননি। হরিপুরা কংগ্রেসের কয়েকদিন পরে রবীন্দ্রনাথ ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকায় (১০ মার্চ, ১৯৩৮) ভারত শাসন আইনকে সমালােচনা করে খােলা চিঠি দেন। তাতে তিনি লেখেন—
আমার ইংরেজ বন্ধুগণ ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আমার অভিমত জানাবার জন্য অনুরােধ করিয়াছেন। সর্বপ্রথম আমি সুস্পষ্টভাবে জানাইতে ইচ্ছা করি যে, পাশ্চাত্যে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে যে, ভারতবর্যে যে যুক্তরাষ্ট্র প্রায়-প্রবর্তিত হইতে যাইতেছে তাহা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের চেয়ে কম নহে। …আমাকে অতি সাধারণ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিতে দিন। যে দেশের লােক নিরস্ত্র, যাহাদিগকে জাতীয় অর্থভাণ্ডারের পাঁচভাগের চারিভাগের অধিক অর্থের উপর কর্তৃত্ব হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, যাহাদিগকে তাহাদের নিজেদের বৈদেশিক ব্যাপারে কিছু করিতে অনুমতি দেওয়া হয় না, তাহারা কিরূপে স্বায়ত্তশাসন পাইতে পারে? আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে ইংরেজগণত যদি তাহাদের দেশে এইরূপ কিছুর সহিত সামান্য সামঞ্জস্যসম্পন্ন বা স্বাধীনতা দায়েত কোনাে প্রহসনও সহ্য করিতে হয় তাহা হইলে তাহারা নিজেরাই নিজেদের কার্য ঘণার চোখে দেখিবেন।
নির্বাচনে অংশ নেওয়াটাকে যদি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের একটা রূপ ধরা হয় তাহলে গান্ধিজি ভারতশাসন আইনকে সাময়িকভাবে একটা ট্রায়াল বা পরীক্ষা করে দেখতে প্রস্তুত ছিলেন। সুভাষচন্দ্রও তার অন্যথা ছিলেন না। ১৯৩৭ সালে প্রদেশগুলিতে যে নির্বাচন হয়েছিল, তাতে সুভাষচন্দ্রও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন। কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে জোর দেওয়া হয়েছিল পূর্ণস্বাধীনতা এবং সংবিধানসভার উপর। বলা হল নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আইনসভায় গিয়ে ভারতশাসন। আইনের সাফল্যের জন্য সহযােগিতা করবে না, এর বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং এই আইনকে খতম করার চেষ্টা করবে (“but to combat it and seek to end it”) সহজেই অনুমেয় এই নির্বাচনী ইস্তাহার গান্ধিজির অজ্ঞাতে রচিত হয়নি।
ভারতশাসন আইনে যুক্তরাষ্ট্রীয় বা ফেডারেল ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছিল। দুটি কক্ষ নিয়ে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা গঠিত হবে। আইনসভার অর্ধেক আসন দেশীয় রাজাদের প্রতিনিধিদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল।
প্রস্তাবিত ফেডারেল কাঠামােতে দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করার অর্থ হল ব্রিটিশদের আজ্ঞাবহ এই সামন্তপ্রভুদের মারফৎ কেন্দ্রে প্রকৃত জনপ্রতিনিধিদের কণ্ঠস্বর দাবিয়ে রাখা।
কংগ্রেসের কতিপয় নেতা ব্যতীত গান্ধিজি সহ সবাই এ ধরনের ফেডারেল ব্যবস্থার বিরােধী ছিলেন। জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র সবচেয়ে বেশি সােচ্চার ছিলেন। গান্ধিজি অবশ্য কিছু শর্তসাপেক্ষে একে গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন। কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাসের (১৯৩৮) প্রথম সপ্তাহেই (৪ ফেব্রুয়ারি) ওয়ার্ধাতে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে বর্তমান আকারে ফেডারেশন পরিকল্পনা বাতিল করা হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র তীব্র ভাষায় আক্রমণ চালান এবং জওহরলাল তাকে জোরালাে সমর্থন করেছিলেন। গান্ধিজিও জানতেন ফেডারেশন কখনাে চালু হবে না। ১৯৩৯ সালের মে মাসের মাঝামাঝি নিডহরণ টাইমস পত্রিকার মিঃ স্টিলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গান্ধিজি ফেডারেশন সম্পকে ভবিষ্যদ্বাণী করতে গিয়ে বলেছিলেন, “আমি স্থির নিশ্চিত ফেডারেশন হবে না। (‘feel quite certain that the federation will not come.”)
অনেকে মনে করেন ফেডারেশন বিরােধী মনােভাব সুভাষচন্দ্রকে রবান: কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কৌতুহলের বিষয়, যেখানে গান্ধিজি সরাসরি ফেডারেশনের সপক্ষে কোনো প্রকাশ্য বিবৃতি দেন নি—একমাত্র বড়লাট লিনলিথগোর সঙ্গে এ বিষয়ে শর্তসাপেক্ষ আলােচনা ছাড়া, সেখানে রবীন্দ্রনাথ কি ধরে নেবেন গান্ধিজি ফেডারেশনের পক্ষে? এবং তিনিও লক্ষ করেছেন ভারত শাসন আইন নিয়ে কংগ্রেস তথা গান্ধিজির অসন্তোষ। বস্তুত তিনি ‘ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান’-এ (১০ মার্চ ১৯৩৮) খােলা চিঠি পাঠিয়ে কংগ্রেসের অসন্তোষের কথাই বকলমে তুলে ধরেছিলেন।
উল্টোদিকে হরিপুরা ভাষণে সুভাষচন্দ্র ভূমিব্যবস্থার সংস্কার বলতে গিয়ে যখন জমিদারি ব্যবস্থা উচ্ছেদের কথা বলেন, তখন তা তৎকালীন পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজি উভয়ের কাছেই অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে না মনে হওয়াই সম্ভব।
সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক গণফ্রন্ট গড়ে তুলেছিলেন গান্ধিজি, তার সঙ্গে জমিদারি ব্যবস্থা উচ্ছেদের বক্তব্য আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। জমিদারদের বিচ্ছিন্ন করার কোনাে ইচ্ছা গান্ধিজির ছিল না। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন জমিদারি উচ্ছেদের অর্থ হল জমিদারদের সামাজিক কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন থেকে বঞ্চিত করা।
তিরিশের দশক থেকে রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক ক্রমবিকাশকে যত লক্ষ করেছেন ততই চমৎকৃত হয়েছেন। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক প্রত্যুষ তার কাছে হয়তাে আকর্ষণীয় ছিল না কিন্তু মধ্যাহ্নকালের সুভাষচন্দ্রের তেজোদৃপ্ত সৌরকিরণ যে তার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল, সেকথা স্বীকার করতে তিনি এতটুকু কুণ্ঠিত হননি। তাঁর অপ্রকাশিত ‘দেশনায়ক’ প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, আজ তুমি যে আলােকে প্রকাশিত তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্য দিনে তােমার পরিচয় সুস্পষ্ট। বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তােমার জীবন, কর্তব্যক্ষেত্রে তােমার যে পরিণত তার থেকে পেয়েছি তােমার প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ।
রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের ‘প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ’ দেখেছেন, শুনেছেন দেশের জন্য একের পর এক অসমসাহসিকতার কাহিনি। তার আহ্বানে বৃদ্ধ বয়সে, অশক্ত শরীরে প্রকাশ্য জনসভায় সাড়া না দিয়েও পারেননি। ১৯৩১ সালে স্বাধীনতার দ্বিতীয় বার্ষিকী (২৬ জানুয়ারি) পালন করতে গিয়ে সুভাষচন্দ্র পুলিশের লাঠির নির্মম আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন এবং দারুনভাবে জখম হলেন। সুস্থ হয়েই বন্যাত্রাণের (জুলাই) সেবাকার্যে উত্তর ও পূর্ববঙ্গের সাধারণ গৃহহারা মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন। ১৬ সেপ্টেম্বর তার ও যতীন্দ্রমােহনের আহ্বানে সত্তর বছর বয়সেও রবীন্দ্রনাথকে ময়দানে এসে হিজলির হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানাতে হল। রবীন্দ্রনাথ দেখলেন আইন অমান্য আন্দোলনের শুরুতেই সুভাষচন্দ্রকে কীভাবে ইংরেজের পুলিশ গ্রেপ্তার করল। জেলের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়লেন সুভাষচন্দ্র। সুচিকিৎসার জন্য নিজ ব্যয়ে ইউরােপে গেলেন। সেখানে পুরােপুরি সুস্থ হওয়ার আগেই লখনউ অধিবেশনে (১৯৩৬) যােগ দেবার তাগিদে ভারতে আসতেই আবার গ্রেপ্তার হলেন। রবীন্দ্রনাথ চুপ থাকতে পারলেন না।
প্রতিবাদ করে বললেন, “এ হল দেশের অসম্মান।” অসুস্থ সুভাষচন্দ্রকে প্রেরণা ও উৎসাহ দেবার জন্য সঞ্চয়িতা’ পাঠালেন। ততদিনে রবীন্দ্রনাথ বুঝে গেছেন শুধু গান্ধিজি, জওহরলাল নয়, বিশ্বভারতীকে যদি আগামী দিনগুলিতে সচল, সজীব করে রাখতে হয় তাহলে সুভাষচন্দ্রেরও সাহায্য প্রয়ােজন। সেকথা তিনি কলকাতায় শ্রীনিকেতন শিল্পভাণ্ডার-এর উদ্বোধন উপলক্ষে তার ভাষণে সুভাষচন্দ্রের কাছে অকপটে লিখে পাঠালেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ মারফৎ। সুভাষচন্দ্রও আশ্বাস দিতে দ্বিধা করেন নি। সুতরাং সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট বিতর্কে তিনি যে সুভাষচন্দ্রের হয়ে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লেন এবং স্বতঃপ্রণােদিতভাবে (সুভাষচন্দ্র এ বিষয়ে কোনাে বিশেষ অনুরােধ করেছিলেন বলে কোনাে প্রমাণ নেই) গান্ধিজিকে অনুরােধ করে চিঠি দিয়ে নিজের হাত পােড়াবেন এতে আর আশ্চর্য কী! গান্ধিজি এনড্রুজ মারফৎ এক কড়া উত্তর পাঠিয়েছিলেন।
শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের গােষ্ঠীদ্বন্দ্বের কোনাে সমাধান খুঁজে না পেয়ে। প্রেসিডেন্ট পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন (২৯ এপ্রিল)। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে এই পদক্ষেপই তাকে ‘দেশনায়ক’ (মে) করে দিল। তিনি লিখলেন, “দুঃখকে তুমি করে তুলেছ সুযােগ, বিঘ্নকে করেছে সােপান।” লেখাটি তার জীবদ্দশায় যদি ছাপা নাও হয়ে থাকে তাতে লেখার বিষয়বস্তু অর্থহীন হয়ে যায় না। কারণ লেখক তারপরেও দুবছর বেঁচেছিলেন, সুযােগ থাকলেও কোনাে সংশােধন করেননি। যেহেতু সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এটাই ছিল প্রাণের কথা। ২১ জানুয়ারি (১৯৩৯) শান্তিনিকেতনে বসে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হিসেবে সুভাষচন্দ্রকে কলকাতায় রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনা (৩ ফেব্রুয়ারি) দেওয়ার কথা বলেও শেষ পর্যন্ত অনিবার্য কারণ এবং শারীরিক দুর্বলতার জন্য তিনি সংবর্ধনা দিতে পারলেন না। কিন্তু তার জন্য সুভাষচন্দ্রের যে মূল্যায়ন তিনি ২১ জানুয়ারির স্বাগত ভাষণে (শান্তিনিকেতন) করেছিলেন তা থেকে তিনি কখনাে পিছু হঠেননি। সেই ভাষণে তিনি প্রকাশ্যে বললেন, সুভাষচন্দ্রকে “আমি রাষ্ট্রনেতা রূপে স্বীকার করেছি মনে মনে।” সুতরাং যিনি মনে মনে একজনকে রাষ্ট্রনেতা রূপে স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি যদি তাকে কোনাে কারণে প্রকাশ্য সংবর্ধনা দিতে অসমর্থও হন তার দ্বারা কোনােভাবেই প্রমাণিত হয় না তিনি তাকে মন থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। তা যে নয় তার প্রমাণ অসুস্থ শরীরেও তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছেন সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের সংবাদ পেয়ে। এমনকী একান্তে সচিব অনিল চন্দকে (৩০ জানুয়ারি, ১৯৪১) পাঠিয়েছিলেন কলকাতায় শরৎচন্দ্র বসুর কাছে বিস্তারিত সংবাদের জন্য। মনে রাখা প্রয়ােজন, সংবর্ধনা না দিতে পারার ত্রুটিকে তিনি অনেকটাই ঢেকে দিয়েছেন ‘তাসের দেশ’ (দ্বিতীয় সংস্করণ) উৎসর্গ করে। সুভাষচন্দ্রও খুশি মনে তা গ্রহণ করেছেন। লক্ষণীয়, ১৯৩৯ সালে ২৭ জানুয়ারি যেমন রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে জানাচ্ছেন, “আপাতত তােমার অভিনন্দন সভা বন্ধ রাখতে হলাে,” তেমনি একই সঙ্গে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি (মাঘ, ১৩৪৫) মাসেই তাকে ‘তাসের দেশ’ উৎসর্গ করে লিখেছেন, “স্বদেশের চিত্তে নতুন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্য ব্রত তুমি গ্রহণ করেছ।” কেন অভিনন্দনসভা বন্ধ। হয়েছিল তার সঠিক ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। অনেক সমালােচক রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে স্ববিরােধিতা দেখতে পেয়েছেন এইসব ঘটনা পর্যালােচনা করে।
কিন্তু একটু গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যাবে এর মধ্যে কোনাে স্ববিরােধিতা রবীন্দ্রনাথেব তরফে ছিল না। অসুস্থ স্ত্রী কমলা ও শিশুকন্যা ইন্দিরাকে ঘিরে জওহরলালের সঙ্গে যে ইমােশনাল সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথের গড়ে উঠেছিল সে সুসম্পর্ক যেমন গান্ধিজির সঙ্গে গড়ে ওঠেনি, তেমনি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গেও। তাই সরাসরি এঁদের ক্ষেত্রে কোদালকে কোদাল বলতে তার কখনাে বাধেনি। গুণীকে গুণীর সম্মান দিয়েও যেখানেই তাদের সঙ্গে সুর মেলেনি, সেখানে বেসুরাে গাইতে দ্বিধা করেননি—তবে একই সঙ্গে লক্ষ করেছেন শ্রোতারা যেন তাদের ত্যাগ না করে। অসহযােগ আন্দোলনের জাতীয় শিক্ষা কর্মসূচি যে রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত ছিল না সে কথা প্রথম সভাতেই সুভাষচন্দ্রকে বলেছেন, হয়তাে কিছুটা ব্যঙ্গ করে। সদ্য কংগ্রেসের স্বীকৃত নেতা হয়েছেন সুভাষচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ আশা করেননি সিটি কলেজ হস্টেলের ছেলেদের একটা সাধারণ পূজা নিয়ে তার মতাে তরুণ নেতা জড়িয়ে পড়বেন (১৯২৭)। কড়া ভাষায় সমালােচনা করতে তিনি দ্বিধা করেননি। বিষয়টি তার কাছে এমন তিক্ত লেগেছিল যে বারাে বছর পর সুভাষচন্দ্রের সভাপতি হওয়ার প্রাক্কালেও তিনি তা মনে রেখেছিলেন এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে সে প্রসঙ্গে চিঠিও লিখেছিলেন। পরে সুভাষচন্দ্রকে যখন আরাে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন তখন মনে হয় এইসব বিষযগুলিকে তিনি র্যাশানালাইজ করে নিয়েছিলেন, মনে করেছিলেন তরুণ বয়সের অতি উৎসাহের ঘটনা, যার কোনাে স্থায়ী মূল্য নেই। কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি হয়তাে অতীতের ওইসব ঘটনায় কুণ্ঠা বােধ করবেন। ব্রাহ্মদের কলেজে সুভাষচন্দ্র মূর্তিপূজায় সমর্থন জানিয়েছিলেন।
রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিক ছিলেন না, রাজনীতি থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতেন কিন্তু রাজনীতিবিদদের থেকে নয়। ফলে অনেক সময়ে তাত্ত্বিক রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তেন। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ গান্ধিজির প্রতিটি আন্দোলনের কর্মসূচি সম্পর্কে তার নিজস্ব প্রতিবেদন। অনশন থেকে আন্দোলন পর্যন্ত প্রতি পদক্ষেপের সূচনায় গান্ধিজি তাঁর কাছে শুভেচ্ছা প্রার্থনার বেনামিতে মতামত জানতে চেয়েছেন। তিনিও নির্দ্বিধায় তা জানিয়েছিলেন। আবার একইভাবে রাজনীতির মধ্যে না থেকেও কংগ্রেস থেকে সুভাষচন্দ্রের বহিষ্কারকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু একই সঙ্গে বােলপুর স্টেশনে (১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০) যখন সুভাযপন্থীরা (সুভাষচন্দ্র অবশ্য বারণ করেছিলেন)
সস্ত্রীক গান্ধিজির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল, তখন রবীন্দ্রনাথ সেই বিক্ষোভকে ব্যক্তিগতভাবে তার অতিথির বিরুদ্ধে অসম্মান বলে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তার অসন্তোষ গােপন রাখেননি। বাঁকুড়ার বক্তৃতায় এ ধরনের উজ্জ্বলতাকে কড়া সমালােচনা করেছিলেন।
এক জওহরলাল ছাড়া সুভাষচন্দ্র বা অন্য কেউ রবীন্দ্রনাথকে স্বতঃসিদ্ধ বা ‘টেকেন ফর গ্রান্টেড’ হিসাবে ধরে নিতে পারেননি। অর্থাৎ অনুরােধ করলেই তা রক্ষিত হবে এমন নিশ্চয়তা সম্ভবত জওহরলাল ছাড়া কেউ দিতে পারতেন না। অন্যদের মতাে সুভাষচন্দ্রকেও রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন যুক্তি ও বিবেচনা দিয়ে, আর জওহরলালের ক্ষেত্রে এর সঙ্গে যােগ হয়েছিল অতিরিক্ত হৃদয়ানুভূতি।
এই কারণে দেখা যায় সুভাষচন্দ্রের অনুরােধ কখনাে রক্ষিত হয়েছে আর কখনাে রক্ষিত হয়নি। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে সুভাষচন্দ্রের প্রতি তার স্নেহে কোনাে ঘাটতি ছিল।
বাংলায় কংগ্রেসের নেতৃত্বে বন্যাত্রাণ কমিটিতে সুভাষচন্দ্রের অনুরােধে (সেপ্টেম্বর ১৯৩১) রবীন্দ্রনাথ সভাপতি হতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে দলাদলির আশঙ্কায় সুভাষচন্দ্রের অনুরােধ সত্ত্বেও তিনি স্বদেশি মেলা পরিদর্শনে রাজি হলেন না।
বিদেশ যাওয়ার সময় (ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩) সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাছে রমা রলাঁর জন্য এক পরিচয়পত্র চেয়েছিলেন। তিনি সে অনুরােধ রেখেছিলেন। মামুলি বলে যদি তা সুভাষচন্দ্রের পছন্দ না হয়ে থাকে, সেটা অন্য প্রশ্ন। কিন্তু সেই সুভাষচন্দ্র যখন তার বইয়ের (দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল) ভূমিকা লিখে দেওয়ার জন্য বার্নার্ড শ অথবা এইচ. জি. ওয়েলসকে অনুরােধপত্র লিখে দিতে রবীন্দ্রনাথকে অনুরােধ করলেন, তিনি সে অনুরােধ রাখলেন না নিজস্ব যুক্তি দেখিয়ে। অথচ তারই কিছুকাল আগে (৩১ অক্টোবর, ১৯৩২) তিনি জেলখানায় অসুস্থ সুভাষচন্দ্রের দ্রুত আরােগ্য কামনা করে বার্তা পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর দুঃখবরণকে গভীর সহানুভূতি জানিয়েছিলেন। তার ভাষায়—
দেশের কল্যাণব্রতে যাঁরা প্রাণান্তিক দুঃখ ভােগ করছেন, সে দুঃখকে আমরা যেন সাধারণ লােকের দুঃখের মতাে গণ্য না করি।
অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কাছে এই আপাত বিসদৃশ আচরণ কোনাে বিস্ময়কর ঘটনা নয়। যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে তিনি ‘সাধারণ মেয়ে’ কবিতার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, তার মৃত্যুর পর তার সম্পর্কেই এক চিঠিতে আক্ষেপ করে লিখেছিলেন যে শরৎচন্দ্রকে ভাল করে চেনা হল না। তেমনি ১৯৩৭ সালে গান্ধিজিকে নােবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাবকে সমর্থনের অনুরােধ করা হলে রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাবকদের লিখে জানালেন তিনি তাকে পুরাে জানেন না। অথচ জওহরলালের কোনাে অনুরােধ তাকে কখনাে ঠেলতে দেখি না।
বরং সেখানে যেন তিনি অতিরিক্ত উদার। স্নেহশীল পিতার মতাে। কোনাে কিছুতেই ‘না’ নেই। ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য ‘ভারতীয় ব্যক্তি স্বাধীনতা সংঘ’ (Indian Civil Liberties Union) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জওহরলাল অন্যান্যদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সহযােগিতা প্রার্থনা করে চিঠি পাঠালেন (২২ এপ্রিল, ১৯৩৬)। কবি সম্মতি দিলেন। আবার দুমাস পরে (৪ জুলাই) অনুরােধ করলেন প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তাঁর নামের অন্তর্ভুক্তিতে তিনি যেন সম্মত হন। শুধু তাই নয়, সংঘের সভাপতি হিসেবে শ্রীমতী সরােজিনী নাইডুর নামটিকেও যেন সমর্থন করেন। রবীন্দ্রনাথ চিঠি দিয়ে (১৮ জুলাই) উভয় ক্ষেত্রেই সমর্থন জানালেন। লক্ষণীয়, এসব ব্যাপারে জওহরলাল রবীন্দ্রনাথেব সঙ্গে কোনাে প্রাথমিক আলােচনাই করেননি। কেবল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে তিনি সমর্থন জানিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, বয়ঃকনিষ্ঠা সরােজিনী নাইডুকে সভাপতি রেখে জওহরলাল চাইলেন রবীন্দ্রনাথ যেন সংঘের সম্মাননীয় সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ কেবল রাজি হলেন তাই নয়, ভবিষ্যতের জন্যও তাকে আগাম নিশ্চয়তা দিয়ে রাখলেন (২৮ জুলাই), যে কাজে আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে সে কাজে আমার নাম যদি কোনাে সাহায্যে আসে, তাহলে নিশ্চয় তুমি তা পাবে।

জওহরলালের পাঠানাে ‘আত্মচরিত’ (An Autobiography) পড়ে রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত। লিখলেন (৩১ মে, ১৯৩৬), “আমি তােমার সাফল্যে গর্বিত এবং গভীরভাবে প্রভাবিত।” সুভাষচন্দ্রের ‘ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল’ সম্পর্কে তেমন কোনাে হৃদয়-উৎসারী মন্তব্য রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে দেখা যায়নি।
শিল্পকে সাধারণ মানুষের ‘সহজলভ্য করতে হবে’ সুভাষচন্দ্রের এ ধরনের বক্তব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একমত হতে পারেননি। তিনি বলেন, ‘যেখানে আর্টের উৎকর্ষ’ সেখানে সবাই অনায়াসে পৌঁছবে এমন আশা করা যায় না। অর্থাৎ শিল্পের পূর্বনির্ধারিত সংজ্ঞা নির্ধারণে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি।
ত্রিপুরিতে যে-পরিস্থিতিতে সুভাষচন্দ্রকে পদত্যাগ, (২৯ এপ্রিল, ১৯৩৯) করতে হয়েছিল তা রবীন্দ্রনাথকে ব্যথিত করেছিল। পুরী থেকে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠিতে সুভাষচন্দ্রকে নতুন ‘কর্মবীর’ আখ্যা দিয়ে তাঁর প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিলেন, কংগ্রেসের অভিমুখে যদি কোনাে কৃতী নতুন পথ খুলতে বেরােন, আমি অনভিজ্ঞ, তার সিদ্ধি কামনা করি, দেখব তাঁর কামনার অভিব্যক্তি কিন্তু দূর থেকে…..
ত্রিপুরি-পরবর্তী সুভাষচন্দ্রের কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে রবীন্দ্রনাথ উপরােক্ত চিটিতে লিখেছিলেন, মহাত্মাজীর স্বীকৃত সকল অধ্যবসায়ই চরমতা লাভ করবে এমন কথা শ্রদ্ধেয় নয়। অন্য কোনাে কর্মবীরের মনে নতুন সাধনার প্রেরণা যদি জাগে তাহলে দোহাই পাড়লেও সে বীর হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন না। সেজন্য হয়তাে অভ্যস্ত পথে যূথভ্রষ্ট হয়ে অনভ্যস্ত পথে তাঁকে দল বাঁধতে হবে, সে দলের সম্পূর্ণ পরিচয় পেতে ও তাকে আয়ত্ত করতে সময় লাগবে।
রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের ক্ষেত্রে যূথভ্রষ্টতাকে স্বীকার করে নিলেন, তঁাকে ‘দল’ বাঁধার স্বাধীনতাও দিলেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে রামগড়ে আপস-বিরােধী সম্মেলনে কবিতা বা গান দূরে থাকুক একটা শুভেচ্ছার বার্তাও পাঠালেন না। অথবা রামগড় সম্মেলনে (আপসবিরােধী সম্মেলন) সুভাষচন্দ্রের কার্যকলাপকে সমর্থন করে কোথাও কোনাে প্রবন্ধ বা চিঠি (যেমনটি তিনি কংগ্রেস সম্বন্ধে অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছিলেন) পরবর্তী সময়ে লিখলেন না। সম্পূর্ণ নিরুত্তর থাকলেন এ বিষয়ে।
বস্তুত রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের তথা গান্ধিজির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ককে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার পর্যায়ে দেখতে চাননি। কারণ গান্ধিজির সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেও তার অপরিহার্যতা সম্পর্কে তিনি ছিলেন দৃঢ় নিশ্চিত। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা উপরােক্ত চিঠিতে যেখানে তিনি সুভাষচন্দ্রকে ‘বাংলাদেশের জননায়কের প্রধান পদ’ দিয়েছেন সেখানেও দেশের ইতিহাসে গান্ধিজির মহান ভূমিকা বর্ণনা করতে ভােলেননি। তিনি লিখছেন, মহাত্মা যখন স্বদেশকে জাগানাের ভার নিয়েছিলেন তখন একান্ত মনে কামনা করেছিলুম, তিনি জনগণের বিচিত্র শক্তিকে বিচিত্র পদে উদ্বোধিত করবেন। কেনা না আমি জানি দেশকে পাওয়া বলতে বােঝায় তাকে তার পরিপূর্ণতার মধ্যে পাওয়া। দেশের যথার্থ স্বাধীনতা হচ্ছে তাই যাতে তার সমস্ত অবরুদ্ধ শক্তি মুক্তিলাভ করে।
কিন্তু এতদসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের স্নেহভরা দৃষ্টির আড়ালে সুভাষচন্দ্র ছিলেন না। এখানে কাজ করেছে জাতীয়তার চেয়েও জন্মভূমি বাংলার শ্যামলিমা, ‘সােনার বাংলা আমি তােমায় ভালবাসি’। কংগ্রেস প্রবন্ধে (অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি) ত্রিপুরি কংগ্রেসের ‘গােলমাল’-এর কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, আমার মন আঁকড়ে ধরে আছে বাংলাকে, যে বাংলাকে বড়াে করব সেই বাংলাকেই বড়াে করে লাভ করবে সমস্ত ভারতবর্ষ। তার অন্তরের ও বাহিরের সমস্ত দীনতা দূর করবার সাধনা গ্রহণ করবেন এই আশা করে আমি সুদৃঢ়-সঙ্কল্প সুভাষকে অভ্যর্থনা করি এবং এই অধ্যবসায়ে তিনি সহায়তা প্রত্যাশা করতে পারবেন আমার কাছ থেকে, আমার যে বিশেষ শক্তি তাই দিয়ে। বাংলাদেশের সার্থকতা বহন করে বাঙালি প্রবেশ করতে পারবে সসম্মানে ভারতবর্ষের মহাজাতীয় রাষ্ট্রসভায়। সেই সার্থকতা সম্পূর্ণ হােক সুভাষচন্দ্রের তপস্যায়।
১৯৩৯ সালের জুন মাসে লেখা এই প্রবন্ধের (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৬) পর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। ১১ আগস্ট সুভাষচন্দ্র কার্যত কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন তথাপি রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হয়ে ‘মহাজাতি সদন’-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন (১৯ আগস্ট) করলেন। কারণ তিনি যে কর্মবীর সুভাষচন্দ্রকে কথা দিয়েছিলেন তাঁর “অধ্যবসায়ে তিনি সহায়তা প্রত্যাশা করতে পারবেন।” এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান পর্যন্ত তাঁর প্রতি কৌতুহল অব্যাহত রেখেছিলেন। (নতুন চিঠি, শারদ সংখ্যা, ২০০৮)

 নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা
নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা