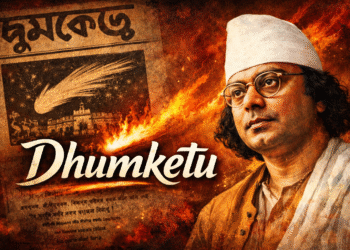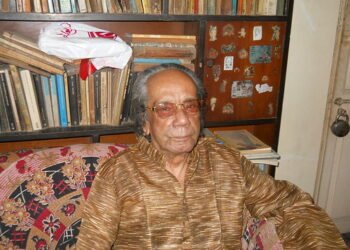লিখেছেনঃ মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম
আশাপূর্ণা দেবী বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। তাঁর রচনায় যে রচনাশৈলী এবং শিল্পরূপ ব্যবহার করা হয়েছে, তা বাংলা ছোটগল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর লেখায় সামাজিক সংকট, ব্যক্তিগত সংগ্রাম এবং মানবিক সম্পর্কের জটিলতা তুলে ধরেছেন। তাঁর গল্পের প্লট এবং গ্রন্থনাটি সাধারণত সরল ও সহজ হলেও এতে গভীর মানবিক অনুভূতি ও সমাজের মূলে থাকা অস্থিরতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
আশাপূর্ণা দেবী যে প্লট গঠন করেন, তা কোনো জটিল বা অতি নিখুঁত নির্মাণ নয়, বরং তিনি সাধারণ মানুষের জীবনের প্রতিফলন ঘটান। তাঁর গল্পের প্লটগুলো প্রায়শই একধরনের ‘গল্প শোনার’ অনুভূতি তৈরি করে, যেখানে পাঠক মনে করেন, যেন কোনো লোক তাঁদের জীবনের সাধারণ ঘটনা বা দুঃখের কাহিনী বলছে। প্লটের গঠন কখনো খুব সুরক্ষিত থাকে না, কখনো মাঝে মাঝে শিথিলভাবে এগিয়ে যায়। তাঁর গল্পে এই শিথিলতা এক ধরনের মানবিক সত্যতা এবং স্বতঃস্ফূর্ততার প্রতিফলন। যেহেতু তিনি এমন এক সমাজের চিত্র তুলে ধরেন, যেখানে সত্য সব সময় অত্যন্ত স্পষ্ট বা পরিকল্পিত নয়, বরং অনেক সময় জীবনের প্রতিকূলতার মধ্যে তবুও কিছুটা আশার আলো থাকতে পারে, সে কারণে তাঁর গল্পে প্লটের যে কঠোরতা দেখা যায় না, তা এক ধরনের কাব্যিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করে।
আশাপূর্ণা দেবী নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ও সামাজিক পরিবেশকে তার গল্পে তুলে ধরেছেন। তাঁর গল্পের মূল উপজীব্য বিষয় ছিল আধুনিক সমাজে নারীদের অবস্থান এবং তাদের মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনযাত্রা। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর লেখায় মানুষের পারিবারিক জীবন ও সম্পর্কের জটিলতা ও সংকটকে তুলে ধরেছেন, বিশেষ করে নারীর আত্মসুখের প্রতি প্রবণতা এবং এর ফলস্বরূপ সমাজের ভাঙন বা অবক্ষয়কে কেন্দ্র করে তাঁর গল্প এগিয়েছে।
তিনি বলেন, “আমার বেছে নেওয়া উপকরণ হচ্ছে সাধারণ সমাজবদ্ধ ঘরোয়া মানুষ। নিতান্তই সাধারণ, যে সাধারণেরা শুধু প্রাণপাত করে দিনের ঋণ শোধ করে চলে।” এই বক্তব্যের মাধ্যমে আশাপূর্ণা দেবী বুঝিয়েছেন, তাঁর গল্পের চরিত্ররা সাধারণ, যেখানে নাটকীয় কোনো ঘটনা ঘটেনা, তবে সেই মানুষের জীবনে এক ধরনের অন্তর্নিহিত যন্ত্রণা এবং তিক্ততা থাকে যা কখনো অতিরিক্ত উচ্চস্বরে বা নাটকীয়ভাবে প্রকাশ পায় না। কিন্তু সেই নিরব, অল্প কণ্ঠস্বরিত আহাজারি, সেই আত্মীয়-স্বজনহীন সমাজের আত্মহনন, মনের অতৃপ্তি, এই সবই আশাপূর্ণা দেবী তাঁর লেখায় অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন।
এছাড়া, তিনি আরও বলেছেন, “এদের জীবনে রোগ শোক দারিদ্র্য আর আকস্মিক দুর্ঘটনা ছাড়া কোন নাটকীয় ঘটনা বড় একটা ঘটে না, তাই তাদের আত্মার ক্রন্দনধ্বনি কখনই উত্তাল হয়ে বাজে না। শুধু কান পাতলে শোনা যায়। সেই অস্ফুট ধ্বনিটুকুকে পৌঁছে দেওয়াই আমার সাহিত্য।” এই চিন্তাধারা তাঁর সাহিত্য রচনার মূলে নিহিত। আশাপূর্ণা দেবীর সাহিত্য সাধারণ মানুষের জীবনের অশ্রু ও হাসির মাঝখানে ঘটে যাওয়া ক্ষুদ্র কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে গড়ে ওঠে। তিনি সমাজের আদর্শ ও সংস্কারের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন, এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানুষকে সেই সমাজের মধ্যে থেকেই নিজের পথ তৈরি করতে হয়।
তাঁর ছোটগল্পে গল্প বলার মাধুর্য এবং সহজতাই ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। আশাপূর্ণা দেবী বুঝেছিলেন, গল্পের কেন্দ্রে পাঠকের সংযোগ স্থাপন করার জন্য জটিল পদ্ধতি বা আঙ্গিকের প্রয়োজন নেই। বরং যেভাবে গল্পটি বলা হবে, সেই সাদাসিধে শৈলীই পাঠককে একাত্ম হতে সাহায্য করবে। এই কারণে তিনি লেখার সময় কখনোই আঙ্গিক নিয়ে খুব বেশি ভাবতেন না। তাঁর লেখায় গল্প বলার ধরনটাই ছিল প্রধান। যেখানে পাঠক সহজেই নিজের পরিচিত পরিবেশ খুঁজে পেতেন এবং সেই পরিবেশের মধ্যে ডুবে যেতেন।
সামাজিক কাঠামোতে বড় ধরনের পরিবর্তন যখন আসতে শুরু করেছিল, তখন নারীরা একে একে বড় পরিবারের কঠোর শাসন থেকে বের হয়ে স্বাধীনতার দিকে যাত্রা শুরু করেছিল। এসব ভাঙন আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পের প্লটের মধ্যে তুলে এনেছেন। বিশেষ করে একান্নবর্তী পরিবারগুলোতে নারীদের অবস্থান এবং তাদের সমাজে অপ্রকাশিত এক ধরনের দুঃখ এবং অহংকার তাঁর গল্পের মূল উপজীব্য ছিল। নারীর জীবনের মধ্যে এই ‘আত্মসুখ’ আসতে শুরু করলে, সমাজের ঐতিহ্য ও পুরনো মূল্যবোধের প্রতি একধরনের বিরোধিতা তৈরি হতে শুরু করেছিল, যা আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পের পটভূমিতে সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন।
তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, “শিল্পী মাত্রেই নিজস্ব মনোভঙ্গীর অনুকূলে তার শিল্পের উপকরণ বেছে নেয়।” এই বাক্যটি তার শিল্পবোধের মূল মন্ত্র। তাঁর সাহিত্য ছিল সাধারণ মানুষের গল্প, যেখানে কল্পনা এবং বাস্তবতার মধ্যে সূক্ষ্ম রেখা ছিল। তিনি কখনোই সোজাসুজি সমাজের পবিত্রতার দিকে তাকাননি, বরং সে সমাজের ভেতরকার অস্বস্তি, শঙ্কা, অসন্তুষ্টি এবং মানুষের একাকিত্ব তুলে ধরেছেন। তাঁর গল্পের চরিত্ররা অধিকাংশ সময়ই কোনো নাটকীয় কাহিনীতে না গিয়ে তাদের জীবন যাপন করতেন, যেখানে সাধারণ ঘটনাগুলোই ছিল সবচেয়ে বড় ঘটনা।
এছাড়া, তাঁর গল্পে দেখা যায় যে, তিনি মানুষের আত্মিক দুঃখ ও খেদকে এক নতুন ভাষায় রূপ দিয়েছেন। তাঁর গল্পে গল্পের চরিত্ররা কখনো কখনো নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করেন, আবার কখনো কখনো ওই সম্পর্ক থেকে মুক্তি পেতে চান, যেমন ‘ছিন্নমস্তা’ গল্পে মা জয়াবতী, ‘আয়ন’ গল্পে ঠাকুর্দা লোকনাথ প্রভৃতি চরিত্রে দেখা যায়।
আশাপূর্ণা দেবী সমাজের পরিবর্তন এবং নারীর আত্মসুখের প্রবণতার মধ্যে যে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উত্তেজনা দেখতে পেয়েছিলেন, তা তাঁর গল্পের মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এই গল্পগুলো সমাজের সাধারণ মানুষের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক ধরনের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রণা এবং সংগ্রামের ছবি তুলে ধরে, যা সাধারণত অতিরিক্ত অভিজ্ঞান বা মহান চরিত্রগঠনের মাধ্যমে প্রকাশ পায় না, বরং সরল এবং কোমল চিত্রের মাধ্যমে ফুটে ওঠে।
এভাবেই আশাপূর্ণা দেবীর সাহিত্য তাঁর গল্পের সহজ বর্ণনা এবং মানুষের গভীর অভ্যন্তরীণ যন্ত্রণার প্রকাশের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকে।
আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পের ধরন ও গঠন একদিকে যেমন সহজ, তেমনি আরেকদিকে গভীর, যেটি পাঠককে ভাবনায় এক গভীরতার দিকে ঠেলে দেয়। তাঁর লেখায় যে শিল্পরূপ এবং রচনাশৈলী আমরা দেখতে পাই, তা একাধারে সরলতা ও জটিলতার মিশ্রণ। আশাপূর্ণা দেবীর গল্পে যেমন সামাজিক বাস্তবতা, পারিবারিক সম্পর্ক ও নৈতিকতা প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি তাঁর গল্পে মানবিক দুঃখ ও আনন্দের অন্তর্নিহিত সত্যও সুনিপুণভাবে ফুটে উঠেছে। এই লেখাটি আশাপূর্ণা দেবীর রচনাশৈলী, শিল্পরূপ এবং তাঁর গল্পের সামাজিক প্রেক্ষাপট নিয়ে বিশদ আলোচনা করবে।
আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পগুলোর মধ্যে প্লটের ধরন নিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাঁর অধিকাংশ গল্পে সরল প্লটেরই প্রাধান্য ছিল। যেমন তাঁর বিখ্যাত গল্প ‘ছিন্নমস্তা’তে আমরা দেখতে পাই একটি সরল কিন্তু গভীর প্লট, যেখানে গল্পের শুরু, মধ্য এবং শেষ এককথায় চমৎকারভাবে সংহত হয়েছে। এখানে সময় সন্ধ্যা, পাত্র জয়াবতী এবং স্থান বাড়ির নির্দিষ্ট উল্লেখ দিয়ে গল্প শুরু হয়েছে। জয়াবতী, একটি সাধারণ স্নেহবৎসলা মা, তাঁর নবীন পুত্রবধূ প্রতিভার আগমনে আনন্দিত। তবে গল্পের প্লট সেখানে থেমে যায় না, বরং তীব্র এক শঙ্কা, যন্ত্রণার পরিণতিতে পাঠককে নিয়ে যায় এক অন্ধকার মহলে। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পের প্লটকে একেবারে সরল রেখেই কিভাবে একটি চরিত্রের ভেতরে থাকা মানসিক উত্তেজনা এবং সমাধানের মধ্য দিয়ে গল্পের পরিণতি এনে দেন, তা তাঁর এক অনন্য দক্ষতা।
গল্পের মধ্যে স্নেহ, ভালবাসা, অপমান এবং অন্তর্গত যন্ত্রণা যে সঠিকভাবে মিশে যেতে পারে, তাও আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ‘ছিন্নমস্তা’ গল্পের জয়াবতী, যদিও একদিকে মাতৃস্নেহে আচ্ছন্ন, তবুও নিজের পুত্রবধূ প্রতিভার প্রতি এক রকমের বিরাগে অভিভূত। এই বিরাগের অভ্যন্তরে আমরা যে মানসিক দ্বন্দ্ব দেখি, তা খুবই জটিল এবং প্রায়শই ছোটগল্পে খুব বেশি দেখা যায় না। জয়াবতী নিজের সন্তানের রক্তপানে তৃপ্তি খুঁজে পেয়েছেন—এই চিত্রটি আশাপূর্ণা দেবীর রচনায় এক অবিশ্বাস্য ক্ষমতা হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। এখানে তিনি মায়ের ভেতরে গভীর আবেগ ও সামাজিক চাপের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত বিরোধ উন্মোচন করেছেন।
এছাড়া, আশাপূর্ণা দেবীর গল্পগুলিতে সাধারণত আত্মকথন রীতির ব্যবহার কম ছিল। তাঁর চরিত্রগুলো স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের আবেগ এবং অনুভূতির স্বরূপ উপলব্ধি করলেও কখনোই তারা আত্মবিশ্লেষণ কিংবা দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়েনি। আত্মকথন রীতিতে যে গল্পগুলো লিখিত হয়, সেগুলোতে চরিত্রটি একে একে তার ভেতরের সত্তার অনুসন্ধান করতে থাকে। কিন্তু আশাপূর্ণা দেবীর চরিত্ররা এ ধরনের দ্বন্দ্বে আটকা পড়ে না, বরং তাদের জীবনের সমস্যাগুলো বাইরে থেকেই উদ্ভূত হয়, সমাজের প্রেক্ষাপট থেকে। তিনি কোন কিছুই কৃত্রিমভাবে তৈরী করেন না, বরং নিজের চোখে দেখা বাস্তবতার গভীরে ডুব দিয়ে সেই বাস্তবতাকেই তিনি তুলে ধরেন।
আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পে সমাজকে মূল উপজীব্য হিসেবে নিয়েছেন। সমাজের অভ্যন্তরীণ সংঘাত, পারিবারিক জীবনের টানাপোড়েন এবং নারীর অবস্থান এসব বিষয় তাঁর রচনার মূল অবলম্বন ছিল। তিনি পুরুষদের তুলনায় নারীর ভূমিকাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন, কারণ তাঁর কাছে নারীর জীবনই ছিল সবচেয়ে গভীর অনুসন্ধানীয়। আশাপূর্ণা দেবী বুঝেছিলেন যে সমাজের অদৃশ্য সংস্কৃতির মধ্যে নারীর অবস্থান কতটা গুরুত্বপূৰ্ণ। তিনি তাঁর গল্পে নারীর আত্মসম্মান, সামাজিক দায়বদ্ধতা, এবং পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন, তা খুবই প্রশংসনীয়।
আশাপূর্ণা দেবী যে চরিত্রগুলো সৃষ্টি করেছেন, তারা প্রায়শই আমাদের সমাজের সাধারণ মানুষ, যাদের জীবন এতটুকু ঘটনাবহুল বা নাটকীয় নয়, কিন্তু তাদের অন্তর্নিহিত যন্ত্রণাগুলোই তাঁদের বাস্তবতা। তাঁর গল্পে এই সাধারণ মানুষের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম অতি সাধারণভাবে, কিন্তু একেবারে নিখুঁতভাবে ফুটে ওঠে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের জীবনযাত্রা এবং তাদের মধ্যে থাকা সম্পর্কের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আশাপূর্ণা দেবীর গল্পের প্রধান আকর্ষণ।
আশাপূর্ণা দেবী সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি এক গভীর বিশ্বাস রাখতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানুষের জীবনযাত্রা, তার সম্পর্ক, এবং তার দুঃখ-কষ্টের জন্য সে নিজেই দায়ী। তাঁর গল্পে কখনোই কোনো চরিত্র একেবারে ভালো বা একেবারে খারাপ হয় না। তারা তাদের নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থান, সংস্কৃতি এবং চেতনা অনুযায়ী চলতে থাকে। তাই তাঁর ছোটগল্পে কোন চরিত্রের পতন বা উত্থান কখনোই নিখুঁতভাবে দেখানো হয় না। সেখানে শুধু জীবনের স্রোত থাকে, যেটি কখনো ঠিকে থেমে থাকে না।
এছাড়া, আশাপূর্ণা দেবী নারীর সামাজিক পরিস্থিতি ও তার আত্মরক্ষার সংগ্রামকে চিত্রিত করেছেন। নারীর সামাজিক বাধাগুলির বিরুদ্ধে তাঁর অবিচল প্রয়াস তাঁর গল্পে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি দেখিয়েছেন যে নারীরা তাদের অবস্থান বদলাতে পারবে, কিন্তু এজন্য তাদের যে অসীম সংগ্রাম করতে হবে, তা সহজ নয়। সমাজের মূল্যবোধ, পারিবারিক নীতি এবং পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে আটকা পড়ে নারীরা এক কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেদের স্বাধীনতা এবং স্বাভাবিক জীবনের জন্য লড়াই করে।
আশাপূর্ণা দেবী তাঁর সাহিত্যে পরিবারের ঐতিহ্য, সমাজের নিয়ম এবং সংস্কারের মধ্য দিয়ে যে মানবিক চিত্র এঁকেছেন, তা একদিকে যেমন বাস্তব, তেমনি মানবিক অনুভূতির প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতিকে নির্দেশ করে। তাঁর গল্পে এভাবেই সমাজের ভিতরের সত্য, বিশেষত নারীর জীবনের যন্ত্রণার গভীরতা, স্পষ্ট ও প্রখরভাবে উঠে এসেছে।
আশাপূর্ণা দেবী বাংলা সাহিত্যের এমন এক রূপকার, যিনি তাঁর গল্পে কখনোই অতীতের স্মৃতিচারণার প্রচলিত রীতি অনুসরণ করেননি। তিনি অতীত বা স্মৃতি নিয়ে গল্প বলেননি, বরং চলমান জীবনের ক্ষুদ্র কিন্তু গভীর ঘটনাগুলোকেই তাঁর কল্পনার মাটিতে রচনা করেছেন। তাঁর সাহিত্যে কোনো আক্ষেপ বা পুনর্বিন্যস্ত অতীতের গল্প নেই। তিনি প্রতিটি গল্পে বর্তমানকে অবলম্বন করেছেন, যেন তাঁর গল্পের চরিত্ররা সমসাময়িক সময়ের, বাস্তবের, এবং চিরকালীন মানবিক দ্বন্দ্বের অংশ হয়ে ওঠে।
আশাপূর্ণা দেবীর সাহিত্যজীবনে সময়ের প্রবাহ ধরে নীরবে হেঁটে যাওয়ার কৌশলটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর গল্পের চরিত্ররা তাদের সত্ত্বা, অনুভূতি এবং সঙ্কট নিয়ে ভাবেন না, বরং তারা যা কিছু ঘটছে তার মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকে। এই প্রবাহে তারা পরিণতি বা সিদ্ধান্তের আশায় থাকে না, বরং জীবন তাদের কাছে এক নির্মমতা, এক স্বাভাবিক অভ্যস্ততা হয়ে দাঁড়ায়। তিনি বলেছেন, “যা দেখি তাই লিখি। আর পরে ভাবতে চেষ্টা করি কেন এমন হয়? আমি কখনও ‘এইটা হওয়া উচিত’ একথা মনে করে কিছু লিখিনি। জানি কি হয় সেটাই বলবার। কি উচিত বলবার আমি কে?” (পৃ. ১৭, ‘আর এক আশাপূর্ণা’)। এখান থেকেই বুঝা যায় যে, আশাপূর্ণা দেবী কখনোই ভবিষ্যতের জন্য কোনো ধারণা বা শিক্ষাকে সামনে এনে গল্প তৈরি করেননি। তাঁর গল্পগুলি জীবনের সাময়িকতা ও বাস্তবতা নিয়ে গঠিত, যা তার অন্তর্নিহিত সংকট বা নাটকীয়তা থেকেও খালি থাকে।
এছাড়া, স্মৃতিচারণায় অবতীর্ণ হতে গেলে একজন লেখককে তার অন্তর্গত অনুভূতিগুলোর গভীরে প্রবাহিত হতে হয়, তা তিনি নিজের জীবনের প্রতিটি স্তরে কি ঘটছে বা কিভাবে ভাবছেন তা সংরক্ষণ করতে চান। আশাপূর্ণা দেবী এই অভ্যন্তরীণ বিস্মৃতি বা স্মৃতির প্রবাহে তেমন কোনো সময় ব্যয় করেননি। বরং তিনি সোজাসুজি চোখের সম্মুখে যা দেখেছেন, তাতেই জীবনকে তার গতি ধরে রচনা করেছেন। তাঁরা যারা স্মৃতিচারণা পদ্ধতিতে আগ্রহী, তাদের প্রয়োজন হয় একটা অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বা চেতনার গভীরে ডুব দেওয়ার, যা আশাপূর্ণা দেবীর চরিত্রদের মধ্যে খুবই কমই লক্ষ্য করা যায়। বরং তাঁর গল্পের চরিত্ররা, যেগুলি তাদের মধ্যে বিভেদ ও সংকটের সূত্রে কখনোই একটি চরিত্রের জীবন চিন্তা করা হয়নি, সেই চরিত্রের অন্তর্নিহিত মনস্তত্ত্ব এবং সত্তার পরিবর্তে আশাপূর্ণা দেবী তাঁদের একেবারে বাস্তব জীবন থেকে তৈরি করেছেন।
ছোটগল্পে জীবনের প্রতিটি স্তর ও পদক্ষেপের সাথে সম্পর্কিত উপাদান রাখা আশাপূর্ণা দেবীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে আশাপূর্ণা দেবী নিজেকে তাঁর গল্পের উপাদান হিসেবে নিয়েছিলেন। তাঁর গল্পে যখন একটা চরিত্র খোলামেলা চিন্তাভাবনায় জড়িয়ে পড়ে, তখন সে মানবিক সংকট, সমস্যা ও দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। এর মধ্যে আশাপূর্ণা দেবী কখনোই গল্পের পরিণতির দিকে কোনো আঙ্গিক গড়ে তোলেননি। তিনি কখনোই বলেননি যে, ঘটনা বা চরিত্রের পরিণতি কি হবে। তিনি সত্যিকার অর্থে আসলে প্রতিদিনের জীবন ও ঘটনাগুলোকেই জেনেবুঝে তুলে ধরেছেন, যেখানে কোনো নির্মাণ বা কৃত্রিমতার আশ্রয় নেয়নি।
এটি ঠিক যে, আশাপূর্ণা দেবী চেকভের মতো গল্পের উপাদানকে জীবনের গভীর সংযোগে রাখেন। চেকভের মতে, গল্পের প্রতিটি উপাদান এক একটি প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়, যা গল্পের কেন্দ্রীয় সংকট বা পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এক্ষেত্রে আশাপূর্ণা দেবীও তাঁর গল্পের উপাদানগুলোর মধ্যে প্রতীকের ব্যবহার করেছেন, যদিও এটি চেকভের চেয়ে অনেকটা ভিন্ন। তিনি প্রতীকগুলোর মাধ্যমে গল্পের নকশা শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়েছেন, কিন্তু প্রতীক গঠন কখনোই তাঁর গল্পে প্রধান হয়ে দাঁড়ায়নি। তার কাছে প্রতীক ছিল জীবনের সাধারণ রূপ, যেটি তার প্রতিটি গল্পে আলাদা আলাদাভাবে ফুটে উঠেছে।
আশাপূর্ণা দেবী গল্পের নির্মাণে অত্যন্ত দক্ষতা দেখিয়েছেন। তিনি এই নির্মাণটি সমাজের অগোছালো, কখনো মসৃণ কখনো অপ্রত্যাশিত দিকগুলোকেই তুলে ধরেছেন। তাঁর গল্পের প্রতিটি চরিত্র জীবনের অন্তর্নিহিত অনুভূতির সমষ্টি, যেখানে তারা সমাজের ভেতর নিজেদের অস্তিত্ব খুঁজে পায়। এসব চরিত্র কখনোই সমাজের খোলামেলা ফ্রেমে তাদের জীবনকে দেখতে চায় না, বরং তারা নিজের জন্যই জীবন যাপন করে। তাদের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস বা পরিচয়ের অভাব রয়েছে, তা আশাপূর্ণা দেবী খুব সহজভাবেই প্রকাশ করেছেন। তাতে সমাজের প্রথা এবং রীতি নীতির গতি রুদ্ধ হয়ে উঠলেও, চরিত্রদের জীবনের চলমানতা অব্যাহত থাকে।
আশাপূর্ণা দেবী তাঁর ছোটগল্পে পারিবারিক ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সামাজিক দায়বদ্ধতা, এবং নৈতিকতার প্রতি যে নিবিড় মনোযোগ দিয়েছেন, তা তাঁর গল্পগুলিকে এক অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। তিনি কখনোই এককভাবে নারীর স্বাধীনতা বা পুরুষের আধিপত্য নিয়ে আলোচনা করেননি, বরং তিনি দেখিয়েছেন সমাজে নারীর সামাজিক পরিচয়ের সীমাবদ্ধতা এবং তাঁর আত্মসম্মান। তিনি মনে করেন, সমাজের রীতি ও প্রথার মধ্যে নারী নিজেকে আবদ্ধ রেখে পূর্ণতা অর্জন করতে পারে না, বরং সে নিজেকে জানার জন্য বা জীবনের অভ্যন্তরীণ অনুভূতির সত্যতা উপলব্ধি করতে সমাজের বাইরে গিয়ে নতুন পথ খুঁজে নিতে পারে।
এরই মধ্যে আশাপূর্ণা দেবী দেখিয়েছেন, সাধারণ মানুষের মধ্যে যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব থাকে, তার ফলেই সমাজে পরিবর্তন আসতে পারে। সমাজের মধ্যে থাকা এই পরিবর্তনের দিকে তাঁর গল্পের চরিত্ররা কখনোই মনোযোগ দেন না, বরং তারা তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছোট ছোট উপলব্ধি থেকে শিখে নেন। তাঁর গল্পে সমাজের মধ্যে থাকা সংকট এবং ব্যক্তিগত সংগ্রামের মিলনে যে অস্পষ্টতা দেখা যায়, তা তাঁর সাহিত্যকে প্রখর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তবতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানায়।
আশাপূর্ণা দেবী সমাজ ও ব্যক্তির সংযোগে যে জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন, তা শুধু সাহিত্যের মাধ্যমেই সম্ভব। তিনি এই বিষয়টিকে সমাজের সীমানা পেরিয়ে সৃষ্টির শক্তিতে অনুবাদ করেছেন। তাঁর গল্পের চরিত্ররা সাধারণ হলেও তাদের জীবন বা পরিস্থিতি কখনোই সাধারণ ছিল না, তা ভাবনা, জীবনযাত্রা এবং মনোবিজ্ঞান দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পের প্রতিটি চরিত্র, তাঁর প্রতীক এবং তাঁর নির্মাণশৈলী আজও পাঠকদের কাছে অমলিন হয়ে আছে।
আশাপূর্ণা দেবী বাংলা ছোটগল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনাকারী হিসেবে তাঁর সাহিত্যে যে প্রতীকের ব্যবহার করেছেন, তা অসাধারণ। তাঁর গল্পগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত প্রতীকের মধ্যে একটি হল অট্টালিকা। প্রায় প্রতিটি গল্পেই এই প্রতীকটি উঠে আসে এবং এটি শুধু একটি নির্মাণ বা স্থাপত্য হিসেবে নয়, বরং সামাজিক, পারিবারিক ও ঐতিহ্যগত মূল্যবোধের গভীর প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। আশাপূর্ণা দেবীর গল্পে অট্টালিকা শুধুমাত্র শ্রী বা ঐশ্বর্যের প্রতীক নয়, এটি একটি ভাঙন, অবক্ষয় এবং সংস্কারের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত জীবনের চিত্রও উপস্থাপন করে।
আশাপূর্ণা দেবী তাঁর ছোটগল্পে এককথায় বললে, কখনোই অতীতের স্মৃতির প্রবাহ ধরে চলেননি। তিনি কখনোই তার চরিত্রদের অতীতের স্মৃতিতে ডুব দিয়ে, সময়ের প্রবাহে প্রাচীন ঘটনা বা চিহ্নের আলোকে রচনা করেননি। বরং তিনি সমসাময়িক জীবন এবং সময়ের প্রবাহকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর গল্পে চরিত্ররা তাদের চোখের সামনে ঘটে যাওয়া ঘটনা থেকেই নিজেদের জীবনের অর্থ খোঁজে। তিনি বলেছেন, “যা দেখি তাই লিখি। আর পরে ভাবতে চেষ্টা করি কেন এমন হয়? আমি কখনও ‘এইটা হওয়া উচিত’ একথা মনে করে কিছু লিখিনি। জানি কি হয় সেটাই বলবার। কি উচিত বলবার আমি কে?” (পৃ. ১৭, ‘আর এক আশাপূর্ণা’)। এর মাধ্যমে তিনি স্পষ্ট করেছেন যে তাঁর সাহিত্যকর্ম কখনোই উপদেশমূলক নয়, বরং এটি শুধুমাত্র বাস্তবতার নিখুঁত প্রতিফলন।
আশাপূর্ণা দেবী যে অট্টালিকার প্রতীক ব্যবহার করেছেন, তা একদিকে যেমন সংসারের শ্রী-ঐশ্বর্যের চিহ্ন, তেমনি অন্যদিকে সমাজের অবক্ষয় এবং সময়ের পরিবর্তনকে বুঝিয়ে দেয়। অট্টালিকা, বিশেষ করে তিনতলা বা দোতলা ভবন, তাঁর গল্পে প্রাচীন বনেদীয়ানার এক ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে উপস্থিত থাকে। গল্পের অনেক চরিত্রের বাসস্থানেই এই অট্টালিকা বা বড় বড় বাড়ির বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু, আশাপূর্ণা দেবী এই অট্টালিকাকে কখনোই শুধু আভিজ্ঞান বা ঐতিহ্যের লেবাসে বাঁধা রাখেননি, বরং এই বাড়িগুলোর ভাঙনের মাধ্যমে সমাজের ঐতিহ্যবোধের পরিবর্তনকেও তুলে ধরেছেন।
অট্টালিকা কখনো শ্রী-যুক্ত হতে পারে, আবার কখনো ভাঙনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার হয়। এসব বাড়ি, একসময় যেগুলোর নির্মাণ বা মালিকানার জন্য ব্যক্তির আর্থিক ক্ষমতা এবং সামাজিক অবস্থান প্রমাণিত ছিল, বর্তমানে সেগুলো জীর্ণ হয়ে পড়েছে। আশাপূর্ণা দেবী গল্পের মধ্যে এই ভাঙনের প্রতীক হিসেবে বাড়ির শ্রীহীনতাকে ব্যবহার করেছেন। বাড়িগুলোর বাইরে বা ভিতরে রং ছিল না, পলেস্তারা উঠে গেছে, বৈদ্যুতিক সংযোগও ঠিকঠাক ছিল না, আর এই অদৃশ্য আভিজ্ঞান সত্ত্বেও বাড়িগুলোর অধিকারী এবং বসবাসকারীরা এক ধরনের অস্থিরতা এবং অসুবিধার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন।
এখানেই আশাপূর্ণা দেবীর দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। তাঁর কাছে বাড়ির অবস্থা কখনোই শুধু শ্রী বা ঐশ্বর্য নয়, বরং এটি পারিবারিক সম্পর্কের অবস্থা, পারিবারিক ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধের পরিবর্তন বা ভাঙনের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিবর্তনটি শুধুমাত্র বাড়ির কাঠামো বা বাহ্যিক পরিবেশের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি পুরো পরিবারের অন্তর্গত জীবনের ভাঙন এবং তার ঐতিহ্য ও আদর্শের অবক্ষয়ের প্রতীক। একান্নবর্তী পরিবারগুলোর মধ্যে যে একতা ও সম্পর্ক ছিল, তা আজকের সমাজে প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে। পুরোনো সময়ের সংস্কার এবং একতার ঐতিহ্য আজকে ভাঙনের মুখে। বহু বাড়ির কর্তা-গিন্নীরা আর একত্রে থাকতেন না, তাঁদের মধ্যে স্নেহ, ভালবাসা, মূল্যবোধ ছিল না। এই পরিবর্তনটি, যা আশাপূর্ণা দেবী খুব সূক্ষ্মভাবে ধরেছেন, আজকের সমাজে প্রচলিত এক ধরনের ব্যক্তিগত জীবনের পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত করে।
বাড়িগুলোর ভগ্নদশা বা অট্টালিকার সুরাহাহীনতা একেবারে পারিবারিক ভাঙনের চিত্র। আশাপূর্ণা দেবী যে বিষয়টি তুলে ধরেছেন তা হলো, পরিবারের অশান্তি, অভ্যন্তরীণ সংঘাত এবং নতুন চিন্তার প্রবাহের কারণে পরিবারের ঐতিহ্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তিনি এই অট্টালিকার মাধ্যমে শুধু শ্রীহীনতার চিত্রই দেখাননি, বরং পারিবারিক ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধের অবক্ষয়কেও চিহ্নিত করেছেন। বাড়িগুলোতে যেখানে একসময়ে বড় বড় পরিবারের সদস্যরা একত্রে থাকতেন, সেখানে আজকাল একের পর এক সদস্য পরিবারের বাইরে চলে যাচ্ছেন, আর একে একে এই অট্টালিকাগুলো ভেঙে পড়ে।
আশাপূর্ণা দেবী এই সামাজিক পরিবর্তন এবং ভাঙনের চিত্র অত্যন্ত বাস্তবিকভাবে তুলে ধরেছেন। এই পরিবর্তনের মধ্যে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যক্তিগত সংগ্রামের নানান দিক প্রবাহিত হয়েছে। বাড়িগুলোর শ্রীহীনতা কিংবা ভাঙন যে শুধুমাত্র বাহ্যিক দৃষ্টিতে ঘটছে তা নয়, বরং এর পিছনে থাকা পারিবারিক সংকট এবং সামাজিক বিপর্যয়ের চিত্রও ফুটে উঠেছে। পুরোনো দিনের ঐতিহ্য, পারিবারিক বন্ধন এবং আদর্শগুলো আজকের দিনে হালকা হয়ে গিয়েছে, যেখানে বৈদ্যুতিক সংযোগ বা আধুনিক সুবিধা না থাকা সত্ত্বেও মানুষ কেবল ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির লেবাসে আবদ্ধ ছিল।
আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পে, যেমন ‘ছিন্নমস্তা’ এবং অন্যান্য গল্পগুলোতে, তিনি প্রতীকী ভাবে এই ভাঙনের চিত্র রচনা করেছেন। বাড়ির ভগ্নদশা, একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন, এবং পুরোনো ঐতিহ্যগুলোর অদৃশ্য হওয়া—এই প্রতীকগুলো একে একে গল্পের মধ্যে জীবন্ত হয়ে ওঠে। বাড়ি বা অট্টালিকার ভাঙন শুধু পারিবারিক জীবনের অবক্ষয় নয়, বরং এটি পুরো সমাজের একটা পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিকে প্রকাশ করে। সমাজের ভেতরের চাহিদা, মূল্যবোধ এবং একক পরিবারগুলির মধ্যে ঐক্যের অভাব, একে একে সামাজিক সম্পর্কের অবক্ষয়কে নির্দেশ করছে।
অট্টালিকার শ্রীহীনতা ও ভগ্নদশা যে শুধু ঘর বা স্থাপত্যের বিষয় নয়, বরং এটি একটি সামগ্রিক সামাজিক পরিস্থিতিরও প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা আমরা খুব সহজেই আশাপূর্ণা দেবীর গল্পে দেখতে পাই। এখানে মানবিক সংকট, পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা, এবং সামাজিক পরিবর্তনের যে ছবি উঠে আসে, তা একদিকে যেমন বাস্তব, তেমনি আমাদের সবার জন্য চিন্তা-ভাবনার জায়গা তৈরি করে। আশাপূর্ণা দেবী এই অট্টালিকার প্রতীক ব্যবহার করে সেই পরিবর্তনের গভীরতা এবং তার সাথে জড়িত মানুষের মনের অবস্থা সুনিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন, যা শুধু তার গল্পের পরিসরেই নয়, বরং আমাদের সমাজের সর্বস্তরের এক কঠিন বাস্তবতা প্রকাশ করে।
এভাবেই আশাপূর্ণা দেবী তাঁর সাহিত্যকে সশক্ত ও গভীর করেছেন। তাঁর গল্পে যে প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে, তা শুধুমাত্র বাস্তবতার একটি অংশ নয়, বরং এটি সেই সমাজের গভীর অন্ধকার এবং তার পরিবর্তনশীল পরিবেশের পরিচায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে।
আশাপূর্ণা দেবী বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য রচনাকারী, যিনি তাঁর ছোটগল্পে সমাজ, সংস্কৃতি এবং পরিবারের জটিল সম্পর্কগুলোকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর রচনায় এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হিসেবে উঠে এসেছে অট্টালিকা, যা শুধুমাত্র একটি নির্মাণ বা স্থাপত্য নয়, বরং এর মধ্যে নিহিত রয়েছে পরিবার, সমাজ এবং ঐতিহ্যের মর্মবোধ। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পের চরিত্র, পারিবারিক সম্পর্ক এবং ভাঙনের চিত্র রচনার মাধ্যমে অট্টালিকার প্রতীক ব্যবহার করেছেন, যা শুধু শ্রী বা ঐশ্বর্যের চিহ্ন নয়, বরং পারিবারিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের অবক্ষয়েরও একটি দৃশ্যমান প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।
প্রতীকীভাবে, আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পে অট্টালিকা বা বাড়ির ভগ্নদশা এবং সেই বাড়ির মালিকদের পরিবারের পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন, যা একটি বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। তাঁর গল্পের অধিকাংশ জায়গাতেই অট্টালিকা বা প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ প্রকাশিত হয়েছে, যা একসময় সমাজের শ্রী বা ঐশ্বর্যের প্রতীক ছিল, কিন্তু বর্তমান সমাজে তা ভেঙে পড়ে, অবহেলার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়। এই ভগ্নদশা একদিকে যেমন পারিবারিক ঐতিহ্যের অবক্ষয়ের চিহ্ন, তেমনি অন্যদিকে এটি সমাজের জন্য একটি সতর্কবার্তা, যেখানে প্রাচীন আদর্শ ও মূল্যবোধ ধীরে ধীরে অতিক্রম করে, নতুন সমাজ ও পরিবারের প্রবাহ সৃষ্টি হচ্ছে।
‘আমায় ক্ষমা করো’ গল্পে মজুমদার বংশের পুরানো প্রাসাদ-শ্রেণির বর্ণনা দিয়ে লেখিকা একাধিক দিক তুলে ধরেছেন। বাড়ির মহল, অন্দরমহল, নাটমন্দির, রান্নাবাড়ি, দূর্গাদালান—এই শব্দগুলো শুধু বাড়ির শ্রী এবং ঐতিহ্যের পরিচায়ক নয়, বরং সেই সময়কার জমিদারি কাঠামোর রূপও প্রকাশ করে। মজুমদার পরিবারের প্রাচীন গৌরবের কথা লেখিকা যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি সেই গৌরবের সঙ্গেই যে একসময় ধ্বংসের ঢেউ এসেছে, তা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ফুটে উঠেছে। পরিবারের সদস্যদের সংখ্যাও এখন অনেক কমে গেছে, এবং বাড়ির ভগ্নদশার মধ্যে বসবাসকারী পুরনো সদস্যরা এখন জীবনের শেষ অধ্যায়ে এসে পৌঁছেছে। “তাহার (বাড়ীটির) সামনে মাথাটা আপনিই কেমন নত হইয়া আসে, আর আসে একটা ‘হায় হায়’ ভাব … কেমন ছিল সেই বিচিত্র সমারোহের কোলাহলময় দিনগুলি … কেমনই বা ছিল ইহাদের অধিবাসীরা …” (পৃ. ৭০, গল্পসমগ্র ২য় খণ্ড)। এভাবেই লেখিকা অতীতের গৌরবের মূক সাক্ষী হিসেবে বাড়ির ধ্বংসাবশেষকে তুলে ধরেছেন, যা পরিবারের ঐতিহ্য এবং সঙ্কটের চিত্র হিসেবে কাজ করছে।
এছাড়া, ‘অঙ্গার’ গল্পে একসময়ের জমিদার বাড়ির জীর্ণ অবস্থা উঠে এসেছে, যেখানে সুকান্ত নামে একজন ব্যক্তি বাড়ির মেরামত করতে গিয়ে তার প্রাসাদের জীর্ণ অবস্থার মুখোমুখি হয়। “বেশী রাত্রে সুকান্ত বাড়ী ফিরে দেখল দোতলার একটা ঘর যথাসম্ভব পরিষ্কার করে তার বিছানাটা রয়েছে পাতা।” (পৃ. ১১১, ঐ)। সুকান্ত কোলকাতায় চাকরিসূত্রে বসবাস করলেও, বাড়ি মেরামত করতে এসে দেখে, বাড়ির একটি অংশ অনেকটাই ভেঙে পড়েছে। এই জীর্ণ অবস্থা শুধুমাত্র বাড়ির অবস্থা নয়, বরং পরিবারের পারিবারিক ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধেরও অবক্ষয়। “আচ্ছা, ভাঙাবাড়ি মেরামত করবার কি এত আরো চৌদ্দ বছরের ঝড়-বৃষ্টি-ভূমিকম্পে ধসে পড়ে যাক না ফাট ধরা নোনা লাগা পচা দেওয়ালগুলো।” (পৃঃ ১১৩, ঐ)। পরিবারের আর্থিক সমস্যার কারণে একদিকে বাড়ি ঠিকঠাক রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছিল না, অন্যদিকে পারিবারিক বন্ধনও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বাড়ির এই অবস্থা শুধুমাত্র পারিবারিক দুরবস্থা বা অভাবের চিহ্ন নয়, বরং একটি বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনের প্রতীক হিসেবে কাজ করছে।
‘অভিশপ্ত’ গল্পে প্রাসাদ-শ্রেণির ধ্বংসাবশেষ আরও স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। একসময়ে যে অট্টালিকা ছিল সমাজের শ্রী এবং ঐশ্বর্যের প্রতীক, আজ তা ভেঙে পড়ে এক অন্ধকারের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। “দক্ষিণের দোতলাটা সমস্ত ধ্বসে গিয়ে একতলার ছাদে জন্মেছে আগাছার জঙ্গল, আর নাটমন্দিরের জয়গায় খানিকটা জমাট অন্ধকার।” (পৃ. ১৬৩, ঐ)। এই অট্টালিকার ভাঙন একদিকে যেমন পারিবারিক ঐতিহ্যের অবক্ষয়, তেমনি অন্যদিকে এটি সমাজের একটা বড় পরিবর্তনকেও নির্দেশ করছে। যে অট্টালিকা একসময় শোভিত ছিল, সেখানে এখন শুধু ধ্বংসের চিহ্ন রয়েছে। আশাপূর্ণা দেবী তার এই প্রতীক দ্বারা সমাজের আদর্শ এবং মূল্যবোধের ক্ষয়কে গভীরভাবে তুলে ধরেছেন।
‘বহুরূপী’ গল্পেও এই অট্টালিকার প্রতীকটি উঠে আসে, যেখানে পরিবারের সদস্যদের মধ্যকার অমিল এবং জীবনের সংকট একসময় এই পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। “দৈন্যাবস্থা দিনের পর দিন পরিবারটিকে গ্রাস করলেও বাড়ির ছোট ছেলের সিনেমায় নেমে কিছু রোজগারকে পরিবারের পক্ষে অত্যন্ত অপমানের বলে মনে করে।” পরিবারটির মধ্যে আভিজাত্যবোধ এখন আর আগের মতো নেই, বরং নতুন সমাজের প্রবাহের সঙ্গে সেটি টেকসই নয়। বাড়ির ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য একে একে পরিবারের সদস্যরা বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছে এবং এই অট্টালিকার প্রতীকী ধ্বংসের চিত্র আরো গভীর হয়ে উঠছে।
আশাপূর্ণা দেবী তার গল্পের মাধ্যমে শুধু বাড়ির ভগ্নদশাই নয়, বরং একটি সমাজের, পরিবারের এবং ব্যক্তির সঙ্কট ও পরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরেছেন। বাড়ির ভাঙন, অট্টালিকার ধ্বংস, এবং পারিবারিক ঐতিহ্যের অবক্ষয়—এই সবই আশাপূর্ণা দেবীর গল্পে এক গভীর সামাজিক বিশ্লেষণের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অট্টালিকার অবস্থা যেন সেই পরিবারের ইতিহাসের প্রতীক, যেখানে একসময় ঐতিহ্য এবং ক্ষমতার প্রতীক ছিল, কিন্তু আজ তা শুধুমাত্র একটি স্মৃতিরূপে পরিণত হয়েছে।
আশাপূর্ণা দেবী এই প্রতীকগুলো ব্যবহার করে শুধু ব্যক্তিগত জীবনের সংকটই নয়, বরং একটি বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন, যা আমাদের সমাজের অভ্যন্তরে ঘটে যাচ্ছে। তাঁর গল্পের এই প্রাসাদ, অট্টালিকা, বা ধ্বংসাবশেষ শুধু শ্রী ও ঐশ্বর্যের প্রমাণ নয়, বরং সমাজের মূল্যবোধ, আদর্শ এবং পারিবারিক সম্পর্কের অবক্ষয়ের অশুভ চিহ্ন।
আশাপূর্ণা দেবী বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য রচনাকারী যিনি সমাজ, পরিবার এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভাঙন ও পরিবর্তনের চিত্র অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্থাপত্যের প্রতীক ব্যবহার। বিশেষত, অট্টালিকা বা বাড়ির ভগ্নদশা তাঁর গল্পে এক বিশেষভাবে উঠে এসেছে, যা সমাজের অবক্ষয়, পারিবারিক সম্পর্কের দুর্বলতা এবং ঐতিহ্যগত মূল্যবোধের পতনের প্রতীক হিসেবে কাজ করে। তাঁর ছোটগল্পে অট্টালিকা শুধু একটি স্থাপত্য নয়, বরং এটি জীবনের নানান প্রতীক—পারিবারিক ঐতিহ্য, সামাজিক সংকট এবং জীবনের মধুরতা ও তিক্ততার দ্বৈততা।
‘ছেঁড়া তার’ গল্পে অট্টালিকার প্রতীকটি অত্যন্ত প্রতিভার সাথে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে বিনয় মল্লিকের জীবনের স্মৃতিচারণ এবং অতীতের পরিস্ফুটন ঘটানো হয়েছে, বিশেষত প্রাসাদী ঐতিহ্যের বর্ণনায়। “আটচালার নীচে গ্যাসের আলো জ্বালিয়া ময়রারা ভিয়ান বসাইয়াছিল আর বাতাসে আসা ঘিয়ের গন্ধ কি অরুচিকরই লাগিতেছিল।” (পৃ. ৩৩৪, ২য় খণ্ড) এই চিত্রটি লেখিকার গভীর পর্যবেক্ষণ এবং বাস্তব জীবনের সাথে সম্পৃক্ততা সুনিপুণভাবে প্রকাশ করে। একসময় বিশাল বাড়িতে বসবাসকারী পরিবারের সদস্যরা তাদের সমৃদ্ধির দিনগুলোর স্মৃতি রোমন্থন করে, কিন্তু বর্তমানে সেই পরিবারের আধ্যাত্মিকতা এবং ঐতিহ্য নিঃশেষ হয়ে গেছে। গরমকালে ছাদে ওঠার স্মৃতির মাধ্যমে লেখিকা অতীতের সৌন্দর্য এবং বর্তমানের নিঃস্বতার কনট্রাস্ট তুলে ধরেছেন।
‘একদিন নাকি ইহাদের “রাজা” বলিয়া খ্যাতি ছিল’—এটি শুধু একটি বংশীয় ইতিহাসের সঙ্গতি নয়, বরং লেখিকা এখানে একটি বিশাল সময়কাল এবং পরিবর্তনের প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন, কীভাবে অতীতের গৌরব আজকের অক্ষুণ্ণ অবস্থা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। বাড়ির ভগ্নদশা, কালে কালে সৃষ্ট অযত্ন এবং পরিবারের সদস্যদের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ভগ্ন অবস্থায় থাকা এই বাড়ি, একদিকে যেমন শ্রীহীনতার চিত্র, তেমনি অন্যদিকে এটি সমাজের কাঠামো পরিবর্তন, মানুষের অভ্যন্তরীণ জীবনের দুর্বলতা এবং পারিবারিক ঐতিহ্যের অবক্ষয়ের সুস্পষ্ট প্রতীক।
‘একরাত্রি’ গল্পেও একই ধরনের অট্টালিকার চিত্র দেখা যায়। গল্পের চরিত্ররা যেমন একতলা এবং দোতলা বাড়িতে বসবাস করে, তেমনি তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনের সংকট এবং পরিবারের অস্থিরতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক তলার বাড়ির বাকি অংশের সঙ্গে যোগাযোগ বা কোনো সম্পর্ক তৈরি হতে না পেরে, পরিবারের সদস্যদের বসবাসের জন্য জায়গা তৈরি করা হয়। এই পরিবর্তনটি শুধু বাড়ির আকারের পরিবর্তন নয়, বরং এটি পরিবারে পরিবর্তনশীল সম্পর্কের চিত্রও। একসময় যে বিশাল বাড়ি একটি আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতীক ছিল, আজ তা নিজস্বতায় সংকুচিত হয়ে গেছে, যেখানে ছোটখাটো জায়গায় থাকা সদস্যদের জন্য সঠিক জায়গা বা স্বাতন্ত্র্য নেই।
‘উদ্বাস্তু’ গল্পে, আমরা দেখতে পাই সেই বাড়ি যেটি পূর্বপুরুষদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল, তার পুনর্নির্মাণ এবং ভাড়ার ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা। “বসত বাড়ীর আধখানাই ভাড়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম বটে, করিয়াছিলাম সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক কারণেই। … বড়লোক নই, দু’পাঁচখানা বাড়ীও নাই সত্যি, কিন্তু বাড়ীটা বেশ বড়ই।” (পৃ. ২৭, ৩য় খণ্ড)। এখানে ‘বাড়ি’ কথাটি শুধু একটি স্থাপত্য নয়, বরং লেখিকা এটি মাধ্যমে পরিবার ও ঐতিহ্যের পরিবর্তন ও সংকট তুলে ধরেছেন। বাড়ির আয়ের জন্য ভাড়া দেওয়া বা অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্য এই বাড়ির অবস্থান পরিবর্তিত হওয়া—এটি সমাজের পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।
‘সিঁড়ি’ গল্পে কথক যখন বলেন “বাড়ীটা নিজস্ব বটে কিন্তু ওই বৃহৎ এখানেও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে বৃহৎ বাড়িটার মতো করেই”, (পৃ. ৮৪, ঐ), তিনি আসলে একেবারে বাস্তবিক দৃষ্টিতে দেখছেন কীভাবে এক সময়ের বিশাল এবং শক্তিশালী পরিবার ধীরে ধীরে অবকাঠামোগত এবং মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এখানে বাড়ির শ্রীহীনতা এবং ভেঙে পড়া বাড়ির চিত্র সোজাসুজি পারিবারিক দুর্দশার প্রতীক হয়ে ওঠে।
‘পদাতিক’ গল্পে একটি দ্বিতল বাড়ির চিত্র পাওয়া যায়, যা সময়ের সাথে সাথে নিজস্বতাকে হারিয়ে ফেলেছে। বিজনবাবু এবং তার পরিবার খুব কষ্টে সংসারের অর্থনৈতিক ভার বহন করছে, কিন্তু বাড়ির সংস্কারের কথা কখনোই ভাবা যায় না, কারণ পরিবারের আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি হয়ে গেছে। “হঠাৎ অসুস্থ হয়ে অথর্ব হয়ে যাওয়া গিন্নী – আর পায়ে হেঁটে নিচের তলায় নামবেন না।” (পৃ. ১৫৩, ঐ) এই চিত্রটি বাস্তব জীবনের বিপর্যয়ের সঙ্গে যুক্ত এবং এটি সেই বাড়ির প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়, যা একসময় পরিবারের প্রাচীন ঐতিহ্য এবং সম্মানের প্রতীক ছিল, কিন্তু এখন তা অবক্ষয় এবং জীর্ণতার প্রতীক হয়ে গেছে।
‘একটি ভাঙাচোরা গল্প’ গল্পে সেই ভগ্ন বাড়ির প্রতীক আরেকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে। কথক নিজের অতীত এবং সেই বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কিত স্মৃতির কথা বলছেন, যদিও তিনি সেই বাড়ির পূর্ণ অবয়ব কখনও দেখেননি। “যদি জানা যাইত কেমন দেখিতেছিল এই বিরাট অট্টালিকাখানা, কেমন তরো ছিল ইহার বাসিন্দারা।” এখানে বাড়ির অভ্যন্তরে ক্ষতিগ্রস্ত জায়গাগুলির বর্ণনা যেমন—“খিলান, সিঁড়ি, আগাছার ফাঁকে ফাঁকে”—এগুলো শুধু বাড়ির ধ্বংসাবশেষের চিত্র নয়, বরং এটি পরিবারের ঐতিহ্যের ক্ষয় এবং সংস্কৃতির অবক্ষয়েরও প্রতীক।
আশাপূর্ণা দেবী এই সমস্ত গল্পে ভগ্নদশা এবং অবক্ষয়ের প্রতীক হিসেবে অট্টালিকাকে ব্যবহার করেছেন, যা পারিবারিক জীবনের সংকট, ঐতিহ্যের পতন এবং আধুনিক সমাজের পরিবর্তনের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিটি গল্পে বাড়ির অবস্থা কেবল পারিবারিক অবস্থা নয়, বরং একটি বৃহত্তর সামাজিক পরিস্থিতিরও ইঙ্গিত দেয়। একসময়ের শ্রী-ঐশ্বর্য এবং গৌরব আজকের সামাজিক অবক্ষয়ের, পারিবারিক বিচ্ছিন্নতার এবং এককথায়, পুরোনো সমাজের পতনের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।
আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পে এই প্রতীকী ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের জীবনের অভ্যন্তরীণ সংকট, তাদের পারিবারিক পরিস্থিতি এবং সামাজিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করেছেন। বাড়ির ভগ্নদশা এবং তার প্রাসাদী ইতিহাসের পরিবর্তন সমাজের ভিতরের এক ধরনের শক্তির অবক্ষয়কেই উদ্ভাসিত করে, যা আমরা প্রতিদিনের জীবনেও লক্ষ্য করতে পারি।
আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পগুলির মধ্যে যে সামাজিক এবং পারিবারিক অভ্যন্তরের সংকট তুলে ধরেছেন, তা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত এবং সমাজের গভীর পরিবর্তনগুলোর প্রতি তাঁর এক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রকাশ করে। তাঁর ছোটগল্পের প্রতীকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো অট্টালিকা বা বড় বাড়ি, যা শুধুমাত্র একটি স্থাপত্য নয়, বরং একটি পারিবারিক ঐতিহ্যের, গৌরবের এবং সামাজিক পরিস্থিতির প্রতীক হয়ে ওঠে। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর সাহিত্যে অট্টালিকার মাধ্যমে সেই সময়ের সমাজের অবক্ষয়, ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার সংকট এবং একটি পরিবর্তিত জীবনধারার ইঙ্গিত দিয়েছেন।
‘ছেঁড়া তার’ গল্পে বিনয় মল্লিকের বর্ণনায় যে অট্টালিকার চিত্র পাওয়া যায়, তা পারিবারিক ঐতিহ্যের ধ্বংস ও অবক্ষয়ের চিত্র। “আন্দাজে আন্দাজে পরিচয় করাইয়া দেন কোথায় ছিল ঠাকুর দালান, কোথায় বৈঠকখানা, কোনখানে বা অন্তঃপুরের সীমানা।” (পৃ. ২৭৩, ঐ)। এই বাক্যটি গল্পের ভিতর দিয়ে প্রাচীন পরিবারের ঐতিহ্য, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাদের দীর্ঘ ইতিহাসের প্রতিফলন। একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত অট্টালিকা তার ভেতরের গভীরতা, ইতিহাস এবং অতীতের গৌরবকে বুকে ধারণ করে, অথচ তা এখন এক ধ্বংসস্তূপের মতো অবস্থান করছে, যেখানে জীবন চালানোর জন্য কোনো ধরণে নিত্যদিন টিকে থাকতে হচ্ছে। এখানেই একদম স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, ভাঙনের মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকা, পরিবার এবং তার ঐতিহ্যের অবক্ষয়—এই সব কিছুই একটি নতুন সমাজের ইঙ্গিত দিচ্ছে, যা আর পুরনো কাঠামোতে বাঁধা পড়তে চায় না।
‘কসাই’ গল্পেও অট্টালিকার প্রতীকটি উঠে এসেছে। একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে যে বিশাল বাড়ি ছিল, সেটি এখন নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য সংগ্রাম করছে। “বিধবা ননদ সেইমাত্র ঠাকুরঘর থেকে নেমে আসেন।” “মরীয়া হয়ে ক্রন্দনরত ছেলেটাকে টানতে টানতে উঠে যায় কমলা তিনতলার ছাদে।” (পৃ. ৮৩, পঞ্চম খণ্ড)। এই চিত্রটি স্পষ্টভাবে এ কথা বলছে যে, একান্নবর্তী পরিবারের ঐতিহ্য এবং অভ্যন্তরীণ সম্পর্কগুলো ভেঙে পড়েছে, আর সেই পরিবারের মঞ্চস্থ বড় বাড়িটি এখন শ্রীহীন, ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় অবস্থান করছে। সংসারের অর্থনৈতিক সংকট এবং পারস্পরিক সম্পর্কের অবক্ষয় উভয়ই এই পরিবারের জন্য চূড়ান্ত বিপদে পরিণত হচ্ছে। বাড়ির ভগ্নদশা আর সদস্যদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা—এগুলি একে অপরকে পরিপূরক করে চলেছে।
‘মণিকোঠা’ গল্পে সুনন্দা ও সীতেশের জীর্ণ, শীর্ণ বাড়ির চিত্র দেয়া হয়েছে। একদিকে তারা একমাত্র সন্তানকে ভালো শার্ট পর্যন্ত পরাতে পারে না, অন্যদিকে তারা একটি দ্বিতীয়তলা বাড়িতে বসবাস করছে, তবে বাড়ির চেহারাও ভাঙাচোরা। “সরু ইটপাতা সিঁড়ি! ভাঙাভাঙা এবড়ো খেবড়ো।” (পৃ. ২৭, ৩য় খণ্ড)। তাদের এই অর্থনৈতিক সংকট শুধুমাত্র তাদের পরিবারের অবস্থা নয়, বরং এই পরিবারের পুরনো ঐতিহ্য এবং তাদের মধ্যে থাকা শ্রী-বৈভবের হারিয়ে যাওয়ার চিত্র। বাড়ির পুরনো অবস্থান এখন আর তাদের জন্য কোনো সুখের স্মৃতি তৈরি করতে পারে না, বরং এটি একটি দীনহীন, অচল পরিসরে পরিণত হয়েছে, যেখানে তারা কেবল প্রাচীন গৌরবের স্মৃতিচিহ্ন ধারণ করে বেঁচে আছে।
অট্টালিকার যে পরিণতির চিত্র আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পগুলিতে তুলে ধরেছেন, তা এক দিকে যেমন পারিবারিক সম্পর্কের ভাঙনের সাক্ষী, তেমনি অন্য দিকে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের একটি অবিশ্বাস্য বাস্তব চিত্র। ‘স্বাধীনতার সুখ’ গল্পে, যেখানে উজ্জ্বলা নামে এক চরিত্র পুরোনো বাড়ি, পুরোনো পারিবারিক সম্পর্ক পরিত্যাগ করে নিজের স্বাধীন জীবন শুরু করেছে, তাতে এই পরিবর্তনের প্রতীকী চিত্র ফুটে উঠেছে। “এখন উজ্জ্বলা স্বাধীন হয়েছে। সাবেক বাড়ি থেকে চলে এসে এ পাড়ায় বাড়ি কিনে বাস করছে আর সেই অবধি যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে চঞ্চলা।” (পৃ. ৩০২, ৩য় খণ্ড)। এখানে লেখিকা দেখাচ্ছেন যে, একটি পরিবারের ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধ আর কোনো আগ্রহের বিষয় নয়, বরং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং আত্মসুখের প্রবণতা পরিবার এবং ঐতিহ্যবোধকে অতিক্রম করে নতুন জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে।
উজ্জ্বলার চরিত্রের মাধ্যমে আশাপূর্ণা দেবী দেখিয়েছেন যে, একান্নবর্তী পরিবারগুলোর মধ্যে আধ্যাত্মিকতার অভাব এবং ব্যক্তি সত্তার অনুভূতির জাগরণে পরিবারগুলো ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। একসময় যে বিশাল প্রাসাদগুলো ছিল পরিবারের সম্মান, ঐতিহ্য এবং ভক্তির কেন্দ্র, সেগুলো এখন হয়ে উঠেছে অতীতের ইতিহাসের অবশেষ। “এতো বড়ো দোতলাখানা ধুলিসাৎ হয়ে গিয়াছে, অথচ একতলার রান্নাঘরখানা দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে প্রায় অবিকৃত অবস্থায় কেবলমাত্র মাথাটা হারিয়ে।” (পৃ. ১৬৩, ঐ)। এই চিত্রটি পুরনো পরিবারের ঐতিহ্য এবং শ্রীহীনতার প্রতীক হিসেবে দাঁড়াচ্ছে, যেখানে একসময় পরিবারের সদস্যরা ঐক্যবদ্ধভাবে বাস করত, কিন্তু এখন সে ঐক্য আর নেই।
‘সিঁড়ি’ গল্পেও, গল্পের মধ্যে বাড়ির ধ্বংসের চিত্রটি ফুটে উঠেছে। এখানে বাড়িটি এখনও প্রাচীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, তবে তা অল্প কিছুই অবিকৃত। “বাড়ীটা নিজস্ব বটে কিন্তু ওই বৃহৎ এখানেও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে বৃহৎ বাড়িটার মতো করেই।” (পৃ. ৮৪, ঐ)। এই বাড়ি এবং তার পারিবারিক কাঠামোর মাধ্যমে আশাপূর্ণা দেবী যে সামাজিক অবক্ষয় এবং অর্থনৈতিক সংকট দেখিয়েছেন, তা একদিকে যেমন একটি বাস্তব চিত্র, তেমনি অন্যদিকে এটি আমাদের একটি বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যেখানে পরিবারের ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে এবং আধুনিক ব্যক্তিগত চাহিদাগুলো একে একে তার জায়গা দখল করছে।
তাঁর গল্পগুলির মধ্যে এই অট্টালিকার প্রতীকী ব্যবহারের মাধ্যমে, আশাপূর্ণা দেবী আমাদের সমাজের অবক্ষয়ের বিভিন্ন স্তরকে, পারিবারিক সম্পর্কের পরিপূর্ণতা এবং আধুনিক সমাজের উদ্ভূত সংকটের গভীরতা তুলে ধরেছেন। অট্টালিকার ভগ্নদশা একদিকে যেমন মানুষের ভিতরের অস্থিরতা, হতাশা, এবং সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতা প্রকাশ করে, তেমনি এটি সামাজিক প্রবৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত মুক্তির খোঁজে চলতে থাকা এক নতুন যুগেরও ইঙ্গিত দেয়।
আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পের মধ্যে যে প্রতীকটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তা হলো অট্টালিকা বা বিশাল বাড়ি। এই বাড়িগুলো কখনো শ্রী ও ঐতিহ্যের প্রতীক, আবার কখনো সমাজ ও পারিবারিক অবক্ষয়ের চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আশাপূর্ণা দেবী একে শুধু একটি স্থাপত্যিক উপাদান হিসেবে তুলে ধরেননি, বরং এটি হয়ে ওঠে সমাজের সংকট, পরিবার ও ঐতিহ্যের পতনের এক প্রতীক। তাঁর গল্পে বাড়ির ভগ্নদশা, তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং পরিবারের ভাঙন—এই তিনটি বিষয় একত্রে মিলিত হয়ে সমাজের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন এবং মানুষের মানসিক অবস্থা প্রমাণ করে।
‘অভিনেত্রী’ গল্পে এই প্রতীকের চিত্র আরও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। এখানে একসময়ের জমিদার পরিবারের যে বিশাল বাড়ি ছিল, তা এখন প্রায় ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় আছে। লেখিকার বর্ণনায় দেখা যায়, বাড়িটি এখন আর ঐশ্বর্য ও শ্রী ধারণ করে না, বরং এর ভিতরে নিঃস্বতা ও অবক্ষয়ের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। “কালের পরিবর্তন হয়েছে বটে – স্থানটা ঠিক আছে। ‘পাত্র’টাও বলা চলে। সেই দালানে ঠিক সেই জায়গাতেই সেই ভঙ্গীতে বসে আছেন গৃহিণী অনুপমা, … আসনটা আর বাসনগুলো বাপের আমলের, তবে আহার আয়োজনটা নয়। তা’তে এ যুগের শীর্ণ ছাপ! অনুরোধ-উপরোধের কাজটা ফুরিয়েছে গৃহিণীদের। … সংসারের এই নবাবীচাল চেলে আর কতদিন চালাতে পারবেন তারকনাথ?” (পৃ. ৩২৬, ঐ) এখানে যে পরিবারের ঐতিহ্য আর সংস্কৃতি ছিল, তা একদিকে যেমন ফুরিয়ে যাচ্ছে, তেমনি আরেকদিকে তার জায়গা দখল করছে আর্থিক সংকট এবং সামাজিক অবক্ষয়। বাড়িটি আর সেই আগের গৌরব বজায় রাখতে পারছে না, ঠিক যেমন পরিবারের সদস্যরা নিজেদের পুরোনো সত্ত্বা ও গৌরবকে হারাতে বসেছে।
‘রাহু’ গল্পে একইভাবে একটি বড় অট্টালিকার বর্ণনা পাওয়া যায়, যা একসময় পরিবারের মর্যাদা ও ঐতিহ্যের প্রতীক ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং সদস্যদের সংখ্যা বাড়তে থাকায়, বাড়ির গুরুত্ব কমে গেছে এবং তার মর্যাদাও ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেছে। “কইয রে রতন, বড় সুটকেস্টা কি করলি? দোতলায় তুলে দিয়েছিস্?” (পৃ. ১১৫, গল্পসমগ্র ২য় খণ্ড)। এখানেও পরিবারের আর্থিক অসুবিধা এবং সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের অবক্ষয় ধীরে ধীরে বাড়ির অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও পরিচিতিকে ভেঙে ফেলছে। বাড়ির বিশালতা থাকলেও, তার মধ্যে চলমান জীবনযাত্রা এবং পারিবারিক সম্পর্কগুলো অনেকটাই বিচ্ছিন্ন এবং আড়ালে চলে গেছে। এই বিচ্ছিন্নতা এবং অবক্ষয়ের ছবি আশাপূর্ণা দেবী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।
‘পদ্মলতার স্বপ্ন’ গল্পেও অট্টালিকার চিত্র একেবারে স্পষ্টভাবে এসেছে। এখানে, বড় একটি বাড়ির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যেটি একসময় অত্যন্ত গৌরবময় ছিল, কিন্তু এখন তা প্রায় ভেঙে পড়েছে। “যদু লাহিড়ীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ‘বোলবোলাও’ ঘুচিয়াছিল।” (পৃ. ১২৩ – গল্পসমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড)। এই বর্ণনা থেকেই বোঝা যায় যে, বাড়িটির অবস্থা এখন কতটা শীর্ণ এবং অবহেলিত। বাড়ির বাইরের সৌন্দর্য এবং ভেতরের অবস্থা একে অপরের সাথে অমিল হয়ে পড়েছে। একসময় যা ছিল ঐতিহ্য ও গৌরবের প্রতীক, তা এখন পরিণত হয়েছে পুরনো স্মৃতির ধ্বংসাবশেষে। বাড়ির ভেতরের খাঁজ, সিঁড়ি, পুরনো আসবাব—এইসব ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থাপনা একে একে বর্তমান সমাজের অবক্ষয়, পরিবারের মধ্যকার বিচ্ছিন্নতা এবং ব্যক্তিগত সংগ্রামের এক প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।
‘ছিন্নমস্তা’ গল্পে যেভাবে বাড়ির ভগ্নদশার চিত্র পাওয়া যায়, তাতে পুরো পরিবারের অবস্থা, সম্পর্ক এবং ঐতিহ্যের অবক্ষয় সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। এখানে, বিধবা শাশুড়ি জয়াবতী, পুত্রবধূ প্রতিভা এবং পুত্র বিমলেন্দুর মধ্যে সম্পর্কের জটিলতা এবং সংসারের ক্ষয়শীল অবস্থা বিশেষভাবে চিত্রিত হয়েছে। “রাত্রি দশটায় জয়াবতী যখন বিরক্তি তিক্ত কণ্ঠে আহারের জন্য ডাক দেন, তখন নামিয়া আসে বিমলেন্দু, চুপ করিয়া খাইয়া উঠিয়া যায়।” (পৃ. ১৬৫, আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন)। এটি সেই পরিবারটির অবক্ষয়ের চিত্র, যেখানে একসময় পিতৃপুরুষের গৌরব এবং ঐতিহ্য ছিল, কিন্তু বর্তমানে সেই ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শীতলতা এবং ব্যক্তিগত চাহিদার প্রতি প্রবণতা তাদের ঐতিহ্যবোধের ক্ষয় ঘটাচ্ছে। বাড়ির অবস্থা এবং সম্পর্কের অস্থিরতা একে অপরের সাথে সম্পর্কিত, যেখানে পরিবারের সদস্যরা একে অপরের পাশে থাকতে ব্যর্থ হচ্ছে।
আশাপূর্ণা দেবী এই ভগ্নদশার প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে শুধু পারিবারিক অবক্ষয় নয়, বরং সামাজিক অবক্ষয়েরও ইঙ্গিত দিয়েছেন। প্রতিটি বাড়ি, যা একসময় শ্রী ও ঐতিহ্যের প্রতীক ছিল, তা এখন মানবিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটের সামনে টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম করছে। সমাজের পুরনো কাঠামো, পরিবার এবং সম্পর্কগুলোর ভিতরে যে ভাঙন এবং অবক্ষয় চলছে, তা আশাপূর্ণা দেবীর গল্পের মধ্যে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর গল্পে অট্টালিকার ভগ্নদশা শুধু পারিবারিক ইতিহাসের অবক্ষয় নয়, বরং একটি বৃহত্তর সমাজের পরিবর্তনের সূচক।
অটল শ্রীহীনতার মধ্যে থাকা এই পরিবারের সদস্যরা এখন নিজেদের গৌরব এবং ঐতিহ্য রক্ষা করতে পারছে না। তারা নিজেদের পারিবারিক অবস্থা এবং সাংসারিক সমস্যা মোকাবেলা করতে ব্যস্ত, কিন্তু একে অপরকে বোঝার এবং সহানুভূতির মধ্যে আগের মতো ঐক্য নেই। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পগুলিতে এই পরিবর্তন এবং ভাঙনের চিত্র অত্যন্ত গভীরভাবে তুলে ধরেছেন, যা শুধু এক সময়ের আভিজাত্যকে নয়, বরং সমাজের ভিতরের এক শক্তিশালী পরিবর্তনকে নির্দেশ করে।
তাঁর গল্পগুলিতে অট্টালিকার ভগ্নদশা শুধু একটি স্থাপত্যের অবস্থা নয়, বরং এটি সামাজিক, পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত সংকটের এক জীবন্ত চিত্র। আশাপূর্ণা দেবী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের সমাজ এবং সম্পর্কের পরিবর্তন, এর সংকট এবং নতুন সময়ের আগমনকে গভীরভাবে তুলে ধরেছেন।
আশাপূর্ণা দেবী ছোটগল্পের মাধ্যমে মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবন, সামাজিক বিশৃঙ্খলা এবং সামাজিক পরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁর গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো প্রতীক ব্যবহার, বিশেষত অট্টালিকা বা বাড়ি, যা শুধুমাত্র একটি শারীরিক কাঠামো নয়, বরং এটি পারিবারিক ঐতিহ্য, গৌরব, এবং অবক্ষয়ের এক চিত্র হয়ে ওঠে। তাঁর লেখায় একদিকে যেমন পুরনো ঐতিহ্যের চিহ্নস্বরূপ অট্টালিকা স্থান পেয়েছে, তেমনি অন্যদিকে তা বর্তমান সমাজের ভাঙন এবং আধুনিকতা গ্রহণের সংকেতও বহন করে। আশাপূর্ণা দেবী তাঁদের গল্পগুলিতে পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে যে ভাঙন, সম্পর্কের অবক্ষয় এবং ঐতিহ্যবোধের পরিণতিকে দেখিয়েছেন, তা বর্তমান সমাজের চলমান সংকটের একটি সত্য চিত্র তুলে ধরে।
‘একরাত্রি’ (১৩৫৪) গল্পে আমরা দেখতে পাই, একসময় যেটি ছিল একটি বিশাল বাড়ি, এখন সেই বাড়ির অবস্থাও প্রায় ধ্বংসপ্রায়। এখানে বাড়ির শ্রীহীনতার চিত্র একদম স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। “ছোট্ট ঘরের লাগোয়া মস্ত ছাদটার এক কোণে ইজি চেয়ার পেতে শুয়ে তারা ভরা আকাশের” (পৃ. ৩৩৪, গল্পসমগ্র ২য় খণ্ড)। এখানে আশাপূর্ণা দেবী বাড়ির অভ্যন্তরের অবস্থা বর্ণনা করেছেন, যেখানে একটি তিনতলা বাড়ির সদস্যরা নিজেদের জন্য কোনো স্থান খুঁজে পায় না, এবং একে অপরের মধ্যে সীমানা নির্ধারণের জন্য সংগ্রাম করে। এমনকি আত্মীয়রা বেড়াতে আসলে তাদের জায়গা খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে, এবং এই চিত্রটি সমাজের সামাজিক অবক্ষয়ের প্রতিনিধিত্ব করে। বাড়ির বিশালতা, একসময় যার মধ্যে আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া যেত, এখন তা এক নিষ্প্রাণ অবকাঠামো হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেখানে সম্পর্কগুলোর মধ্যে কোনো আন্তরিকতা বা সমঝোতা আর নেই।
‘বহুরূপী’ (১৩৫৪) গল্পেও আমরা অট্টালিকার অবনতির চূড়ান্ত রূপ দেখতে পাই। গিরীন্দ্রমোহনের পরিবারে যথেষ্ট পরিমাণে সদস্য থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক সংকট এবং অর্থের অভাব বাড়ির সমস্ত ঐতিহ্য এবং গৌরবকে ক্রমশ ক্ষয়ে ফেলছে। “গিরীন্দ্রমোহনের অন্ধকার দেখার ফাঁকে চোখ তুলে একবার বাড়িখানার আপাদমস্তক দেখে নেয় নিখিল। বাড়িখানা প্রকাণ্ড সন্দেহ নেই, জমি আছে বিস্তর, কিন্তু জীর্ণতার শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে।” (পৃ. ২৫৫, গল্পসমগ্র ২য় খণ্ড)। এই চিত্রটি সঠিকভাবে দেখাচ্ছে যে, যে বাড়ি একসময় ছিল শ্রী এবং সম্মানের প্রতীক, আজ তা জীর্ণতার মধ্যে হারিয়ে গেছে। বাড়ির পুরনো কাঠামো, স্থাপত্য এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গন সবই সময়ের সাথে বদলে গেছে, আর তার ভেতর দিয়ে পুরনো ঐতিহ্য আর শ্রী আজ এক নিঃস্ব অবস্থায় পরিণত হয়েছে।
আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পে বাড়ির শ্রীহীনতা এবং পরিবারের অভ্যন্তরের পরিবর্তনকে খুব দক্ষতার সাথে তুলে ধরেছেন। গল্পগুলিতে দেখানো হয়েছে যে, একসময় যেসব পরিবারের মধ্যে ছিল সম্পূর্ণ ঐতিহ্য, গৌরব এবং সম্মান, আজ সেগুলো শুধুমাত্র স্মৃতির আস্তরণে পরিণত হয়েছে। ‘পদ্মলতার স্বপ্ন’ গল্পে, লাহিড়ী পরিবারের বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই, বাড়ির শ্রীহীনতা এবং অবস্থা ক্রমশ অবনতি হচ্ছে। “যদু লাহিড়ীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ‘বোলবোলাও’ ঘুচিয়াছিল।” (পৃ. ১২৩, গল্পসমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড)। এখানেও বাড়ি একসময় ছিল প্রাচীন মর্যাদা এবং ঐতিহ্যের প্রতীক, কিন্তু এখন তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। বাড়ির অভ্যন্তরের ধ্বংস, বালির আস্তরণ, মাকড়সার জাল—এই সবই পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এক শূন্যতার, এক অবক্ষয়ের চিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।
‘ছিন্নমস্তা’ গল্পের মধ্যে যে চিত্রটি উঠে আসে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। এখানে জয়াবতী, প্রতিভা এবং বিমলেন্দু—এই তিনটি চরিত্রের মাধ্যমে পারিবারিক অবক্ষয়ের চিত্র অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরা হয়েছে। “রাত্রি দশটায় জয়াবতী যখন বিরক্তি তিক্ত কণ্ঠে আহারের জন্য ডাক দেন, তখন নামিয়া আসে বিমলেন্দু, চুপ করিয়া খাইয়া উঠিয়া যায়।” (পৃ. ১৬৫, আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন)। এখানে পারিবারিক অভ্যন্তরের সেই আন্তরিকতা আর সম্পর্কের শূন্যতা পরিষ্কারভাবেই ফুটে উঠছে। পরিবারের মধ্যে যত্ন, ভালোবাসা এবং একে অপরের প্রতি সহানুভূতির অভাব, আর বাড়ির অবস্থা যা একসময় ছিল গৌরবের প্রতীক, তা এখন এক শূন্যতায় পরিণত হয়েছে।
এছাড়া, ‘মণিকোঠা’ গল্পে সুনন্দা এবং সীতেশের জীবনযাত্রা এবং তাদের বাড়ির অবস্থান, অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং পরিবারের মধ্যে শ্রীহীনতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সুনন্দা এবং সীতেশ তাদের একমাত্র সন্তানকে যতটা সম্ভব সঙ্গতিপূর্ণ জীবন দেওয়ার চেষ্টা করছেন, তবে বাড়ি এবং পরিবেশ তাদের সে প্রচেষ্টায় কোনো সাহায্য করতে পারছে না। “সরু ইটপাতা সিঁড়ি! ভাঙাভাঙা এবড়ো খেবড়ো।” (পৃ. ২৭, ৩য় খণ্ড)। এই চিত্রটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি দেখাচ্ছে যে, যে বাড়ির ভিতরে একসময় ছিল আনন্দ, সমৃদ্ধি এবং গৌরব, আজ সেটি ধীরে ধীরে জীর্ণ হয়ে গিয়ে মৃতদেহের মতো দাঁড়িয়ে আছে।
আশাপূর্ণা দেবী যেভাবে অট্টালিকার প্রতীক ব্যবহার করেছেন, তা শুধু বাড়ির অবস্থা নয়, বরং একটি বৃহত্তর সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পারিবারিক অবক্ষয়ের চিত্র। তিনি যে পারিবারিক ঐতিহ্য, সম্পর্ক, এবং গৌরবের পতনের ছবি অট্টালিকার ভগ্নদশা দিয়ে তুলে ধরেছেন, তা সমাজের ভিতরের বড় ধরনের পরিবর্তনকে ইঙ্গিত দেয়। সমাজে অর্থনৈতিক সংকট এবং সামাজিক ভাঙনের ফলে যে একান্নবর্তী পরিবারের শ্রী এবং ঐতিহ্য ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তা খুবই স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।
তাঁর গল্পগুলিতে অট্টালিকার শ্রীহীনতা এবং ভাঙন পারিবারিক জীবনযাত্রার পরিবর্তন, ব্যক্তিগত সংগ্রাম এবং সমাজের পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই গল্পগুলির মধ্যে যে ভগ্নদশার চিত্র উঠে এসেছে, তা আমাদের জীবনের পরিবর্তনশীল বাস্তবতার সঠিক প্রতিফলন। আশাপূর্ণা দেবী প্রতিটি গল্পের মাধ্যমে আমাদের দেখিয়েছেন যে, পুরনো ঐতিহ্য, গৌরব এবং শ্রী কখনোই স্থায়ী হয় না; সমাজ, অর্থনীতি এবং মানুষের চিন্তাধারা পরিবর্তিত হলে সবকিছুই ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে।
এভাবেই আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পের মাধ্যমে সমাজের অবক্ষয়, পরিবারের সম্পর্কের অবস্থা এবং ঐতিহ্যবোধের ভাঙনকে তুলে ধরেছেন। তাঁর রচনাগুলি আজও আমাদের সমাজের অন্তর্নিহিত সংকট, পরিবর্তন এবং মানুষের জীবনের বাস্তবতা নিয়ে চিন্তা করতে বাধ্য করে।
আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পে যে সামাজিক ও পারিবারিক বিচ্ছিন্নতার চিত্র ফুটে ওঠে, তা একদিকে যেমন মানুষের ব্যক্তিগত দুঃখ-দুর্দশা, তেমনি অন্যদিকে সমাজের ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের ভাঙন। তিনি তাঁর গল্পের চরিত্রগুলির মাধ্যমে সেই সময়ের সমাজের ভিতরকার পরিবর্তন ও তার অভিঘাতকে তুলে ধরেছেন। বিশেষত, তাঁর গল্পে প্রবাদ প্রবচনগুলির ব্যবহার গল্পের বিষয়বস্তু এবং চরিত্রের মধ্যে গভীরতা সৃষ্টি করে। আশাপূর্ণা দেবী গল্পে প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার, চরিত্রের বিকাশ এবং তাদের সামাজিক সচেতনতা নিয়ে যে চমৎকার রচনা করেছেন, তা সাহিত্যাঙ্গনে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে।
‘গলায় দড়ি’ গল্পে তিনি যে প্রবাদটি উল্লেখ করেছেন—“কাঁগালের হয়েছে ঘটি, জল খেয়ে ম’লো বেটি”—এটি সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন। এই প্রবাদটি এমন একজন মানুষকে বর্ণনা করে যে অনেক কিছু করার পরেও কিছুই লাভ করতে পারে না। এই প্রবাদটি লেখিকার মাধ্যমে বাস্তব জীবনের দুর্দশাকে তুলে ধরে, যেখানে একজন মানুষ নিজের পরিশ্রম এবং দুঃখের বিনিময়ে কোনো ফল পায় না। “গলায় দড়ি” গল্পের মাধ্যমে আশাপূর্ণা দেবী সামাজিক অবস্থা, অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং ব্যক্তিগত অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের চিত্র আঁকছেন। সত্যজিতের পিসি এই প্রবাদটি ব্যবহার করে তাঁর পরিবারে অনিশ্চয়তার অনুভূতি এবং বাস্তবতা প্রকাশ করেন। গল্পের বিষয়বস্তু ও চরিত্রের মধ্যে সংলাপের মাধ্যমে লেখিকা সমাজের সীমাবদ্ধতা এবং মানুষের আত্মবিশ্বাসের অভাবকে চিত্রিত করেছেন।
আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পের মধ্যে প্রবাদ প্রবচন ব্যবহার করে চরিত্রদের চিন্তা-ভাবনা, তাদের মনোভাব এবং তাদের অবস্থান সম্পর্কে অনেক কিছু ব্যক্ত করেন। ‘নীলকণ্ঠ’ গল্পে কাকার প্রতি ব্যবহৃত প্রবাদ—“মরদকা বাত, হাতিকা দাঁত”—এটি একজন পুরুষ চরিত্রের গৌরব এবং মর্যাদাকে তুলে ধরে। “হাতির দাঁত যেমন দামী তেমনি সত্যিকারের ভদ্র ব্যক্তির কথাও তেমনই দামী” এই প্রবাদটি ব্যবহার করে লেখিকা চরিত্রের মুখে যে মর্যাদা এবং আদর্শবোধ তুলে ধরেছেন, তা বাস্তবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যখন ভদ্রলোক তার উচ্চ মান এবং কথার দামের মাধ্যমে অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে ওঠেন, তখন তা একটি সামাজিক প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়।
আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পের চরিত্রগুলির মধ্যে সামাজিক আদর্শবোধ এবং মনোভাবের প্রকাশ ঘটান, যা গল্পের মূল বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত। তাঁর গল্পের চরিত্ররা সাধারণত সমাজের বিধি-বিধান, আচার-অনুষ্ঠান এবং সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী তাদের জীবনযাপন করে। আশাপূর্ণা দেবী এভাবেই চরিত্রের মধ্যে সমাজের গভীর সত্য উন্মোচন করেন। ‘রাহু’ গল্পে যখন বাড়ির সদস্যরা একত্রে বসবাস করে, সেখানে অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং পারিবারিক অস্থিরতার পাশাপাশি বাড়ির সঙ্কট ও ভাঙনও প্রকাশিত হয়। “কইয রে রতন, বড় সুটকেস্টা কি করলি? দোতলায় তুলে দিয়েছিস্?” (পৃ. ১১৫, গল্প সমগ্র ২য় খণ্ড) এই বক্তব্যে আমরা দেখতে পাই, যেখানে পরিবার একসময় ঐক্যবদ্ধ এবং স্থিতিশীল ছিল, সেখানে এখন সদস্যদের মধ্যে একে অপরের প্রতি আগ্রহ এবং আন্তরিকতা কমে যাচ্ছে। এই ভাঙন এবং বাড়ির শ্রীহীনতার চিত্র আশাপূর্ণা দেবীর গল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হিসেবে কাজ করে।
অবশ্য, এই ধরনের গল্পে প্রবাদ প্রবচন কেবলমাত্র একজন বা একটি চরিত্রের ব্যক্তিগত অভ্যন্তরীণ সংকটকে তুলে ধরার জন্য ব্যবহার করা হয় না, বরং এটি সমাজের বৃহত্তর পরিবর্তন এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সংকেতও প্রদান করে। ‘পদ্মলতার স্বপ্ন’ গল্পে দেখা যায়, যে বাড়িটি এক সময় গৌরবময় ছিল, তা এখন এক ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে। “যদু লাহিড়ীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ‘বোলবোলাও’ ঘুচিয়াছিল।” (পৃ. ১২৩, গল্পসমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড)। এই গল্পে বাড়ির অবস্থা এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যকার সম্পর্কের তীব্র পরিবর্তন এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়কে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরা হয়েছে।
আশাপূর্ণা দেবীর গল্পগুলিতে চরিত্রের বিকাশ এবং তাদের চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে যে ভালো-মন্দের সংমিশ্রণ, তা প্রবাদ প্রবচনগুলির মাধ্যমে উঠে আসে। ‘নীলকণ্ঠ’ গল্পে যখন কাকা ভাত সেদ্ধ করতে না পারার অভিযোগ করেন, তখন চরিত্রের মধ্যে সৎ এবং অসৎ ব্যবহারের যে পার্থক্য ফুটে ওঠে, তা একে অপরের মধ্যে একটি সামাজিক যোগসূত্র তৈরি করে। প্রবাদটি ব্যবহার করে তিনি সামাজিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটান, যা চরিত্রের মধ্যে সুপ্ত দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ।
আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পের চরিত্রগুলির মধ্যে যে মানবিক উপাদানটি ফুটিয়ে তুলেছেন, তা আধুনিক সমাজের বাস্তবতাকে সামনে আনতে সহায়তা করেছে। তাঁর চরিত্রেরা প্রায়শই সমাজের নিয়মকানুন, আচার-অনুষ্ঠান এবং প্রথার মধ্যে আবদ্ধ থাকে, তবে মাঝে মাঝে তারা তাদের আত্মপরিচয়ের সন্ধানও করে। বিশেষ করে নারী চরিত্রগুলোয় এই আত্মপরিচয়ের সন্ধান অধিক দৃঢ়ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আশাপূর্ণা দেবী নারীদের চরিত্রে যে চেতনাবোধ এবং আত্মসচেতনতা তুলে ধরেছেন, তা সাহিত্যে একটি বড় পরিবর্তন এনেছে। নারীরা সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে, তাদের আত্মসম্মান ও ন্যায়বোধের প্রতি সচেতন হয়ে উঠেছে, যা আশাপূর্ণা দেবীর গল্পে এক বিদ্রোহী চরিত্রের রূপে প্রতিফলিত হয়েছে।
‘স্বাধীনতার সুখ’ গল্পে উজ্জ্বলার চরিত্রের মাধ্যমে এই সচেতনতার দৃশ্যমানতা ফুটে উঠেছে। “এখন উজ্জ্বলা স্বাধীন হয়েছে। সাবেক বাড়ি থেকে চলে এসে এ পাড়ায় বাড়ি কিনে বাস করছে আর সেই অবধি যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে চঞ্চলা।” (পৃ. ৩০২, ৩য় খণ্ড)। এই পরিবর্তন নারীর মনোভাবের বিকাশ, সমাজের প্রতি তাদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবনের প্রতি তাদের আত্মবিশ্বাসের প্রতীক হিসেবে কাজ করছে। আশাপূর্ণা দেবী এই চরিত্রের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, পুরনো পরিবারের ঐতিহ্য, সামাজিক বাধা এবং গোঁড়ামি থেকে মুক্তি পেয়ে নতুন সমাজে নিজেদের অবস্থান গড়ে তোলার চেষ্টা করছে নারীরা।
আশাপূর্ণা দেবী প্রবাদ প্রবচনের মাধ্যমে তাঁর চরিত্রগুলির মধ্যে যা তুলে ধরেছেন তা শুধুমাত্র জীবনের কিছু দিক নয়, বরং সমাজ, ঐতিহ্য, গৌরব এবং ভাঙনগুলোর একটি প্রতীকও। তাঁর গল্পে চরিত্রের বিকাশ, সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন এবং মানুষের মধ্যে যাওয়া আসার প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে ফুটে উঠেছে, যা তাকে বাংলা সাহিত্যে একটি অনন্য স্থান দিয়েছে।
আশাপূর্ণা দেবী বাংলা ছোটগল্পের অগ্রগণ্য লেখিকা, যিনি তাঁর গল্পের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন দিক, বিশেষ করে নারীর সামাজিক অবস্থান, পরিবারের অবক্ষয়, এবং সাধারণ মানুষের অন্তর্গত সংগ্রামকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর রচনায় চরিত্র, ভাষা এবং প্রতীক ব্যবহারে যে গভীরতা রয়েছে, তা তাঁকে বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ স্থান প্রদান করেছে। আশাপূর্ণা দেবী সাধারণ জীবনের অন্তর্নিহিত সত্যগুলো প্রকাশ করেছেন এবং সেই সত্যগুলোকে তাঁর গল্পের চরিত্রগুলির মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে সমাজের কাছে তুলে ধরেছেন। তাঁর গল্পে বিশেষত নারীদের চরিত্ররা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সেই চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে তিনি পুরনো সামাজিক কাঠামো ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।
আশাপূর্ণা দেবী গল্পের নারী চরিত্রগুলির মধ্যে এমন এক বিস্তৃত বৈচিত্র্য রেখেছেন যা সামাজিক অবস্থান, পারিবারিক অবস্থান এবং সম্পর্কের জটিলতার একটি জ্ঞানের প্রতিফলন। ‘শাস্তি’ গল্পে মহামায়া, ‘অভিনেত্রী’ গল্পে অনুপমা, ‘তাসের ঘর’ গল্পে মমতা, ‘অঙ্গার’ গল্পে নতুন বৌদি, ‘ছিন্নমস্তা’ গল্পে জয়াবতী, ‘অহমিকা’ গল্পে হেমলতা, ‘বহুরূপী’ গল্পে মমতাময়ী নারী চরিত্রগুলির প্রতিটি একে একে সমাজের মধ্যে নারীর অবস্থান এবং কর্তৃত্বের একটি নতুন দিক তুলে ধরে। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পে পুরুষের মত, নারীকেও শক্তিশালী, দায়িত্ববান এবং একান্তভাবে স্বাধীন হিসেবে তুলে ধরেছেন। তবে তাঁর গল্পের নারী চরিত্রগুলি কখনোই পরিপূর্ণ বা নিখুঁত নয়, বরং তাদের মধ্যেও মানবিক দুর্বলতা, হতাশা এবং দ্বন্দ্ব রয়েছে, যা তাদের আরও বাস্তবিক এবং প্রাসঙ্গিক করে তোলে।
‘ছিন্নমস্তা’ গল্পে জয়াবতী চরিত্রের মধ্যে যে পরিবর্তন এবং সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখা যায়, তা আশাপূর্ণা দেবীর শ্রেষ্ঠ কাহিনির একটি উদাহরণ। গল্পের মূল চরিত্র জয়াবতী একজন বিধবা মা, যিনি নিজের সন্তান এবং পরিবারের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সমাজের চাপের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। সমাজের পুরনো নিয়ম এবং পারিবারিক দায়বদ্ধতার প্রতি তার নিষ্ঠা কখনো কখনো তাকে অসহায় করে তোলে, আবার কখনো তাকে এক শক্তিশালী নারীতে পরিণত করে। জয়াবতী যখন ‘ছিন্নমস্তা’ হয়ে ওঠেন, তখন তাঁর মানসিক সংগ্রাম এবং আত্মসম্মানবোধ তার শক্তিকে প্রকাশ করে। এটি শুধু একটি চরিত্রের পরিবর্তন নয়, বরং এটি সমাজের মধ্যে নারীর অবস্থান এবং আত্মমর্যাদার প্রতি তাঁর সংগ্রামের একটি প্রকাশ।
আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পে যা কিছু বর্ণনা করেছেন তা অত্যন্ত বাস্তব, সহজ এবং সরল ভাষায়। তাঁর গল্পের চরিত্রগুলো কখনোই জটিল বা বিমূর্ত নয়, বরং তারা খুব সাধারণ জীবনযাপন করে, যার ফলে পাঠক সহজেই তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর চরিত্রগুলির ভাষা ব্যবহারেও সমাজের শোষিত, অবহেলিত শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাঁর গল্পগুলিতে নারী চরিত্রের ভাষা প্রায়শই আঞ্চলিক ভাষায়, প্রকৃতির ভাষায় এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনের ভাষায় অভ্যস্ত থাকে। এটি যেন গল্পের পরিবেশকে আরও প্রকৃত এবং বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে।
‘বহুরূপী’ গল্পে গিরীন্দ্রমোহনের সংসারের জীর্ণ অবস্থা এবং পরিবারের মধ্যে শ্রী ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টার চিত্র উঠে এসেছে। “গিরীন্দ্রমোহনের অন্ধকার দেখার ফাঁকে চোখ তুলে একবার বাড়িখানার আপাদমস্তক দেখে নেয় নিখিল। বাড়িখানা প্রকাণ্ড সন্দেহ নেই, জমি আছে বিস্তর, কিন্তু জীর্ণতার শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে।” (পৃ. ২৫৫, গল্পসমগ্র ২য় খণ্ড)। এটি শুধু বাড়ির অবস্থা নয়, বরং পরিবারে ঘটে চলা অবক্ষয়ের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। গিরীন্দ্রমোহনের পরিবারে সদস্যদের মধ্যে যে মানসিক অস্থিরতা এবং দারিদ্র্যবোধ বিরাজ করছে, তা বাড়ির অবস্থার মাধ্যমে আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানেও বাড়ি একটি প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা শুধু পারিবারিক ঐতিহ্য ও গৌরবের নয়, বরং সমাজের দারিদ্র্য, সংকট এবং সামাজিক পরিবর্তনের এক নিদর্শন।
আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পে যে ভাষার ব্যবহার করেছেন, তা সাধারণত সাবলীল, সরল এবং প্রাঞ্জল। তাঁর গল্পের চরিত্ররা সবসময় মৃদু ও বাস্তবিক ভাষায় নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করে, যা গল্পের ভিতরের ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্ব ও সম্পর্কের জটিলতাকে আরও প্রকৃত এবং অনুরণনশীল করে তোলে। তাঁর গল্পের ভাষা স্নিগ্ধ, মিষ্টি এবং প্রাকৃত, যা গল্পের চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্বের গভীরতা এবং সামাজিক সম্পর্কের প্রতি সচেতনতা প্রকাশ করে।
চরিত্রগুলির ভাষার ব্যবহারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে আশাপূর্ণা দেবীর নিপুণতা। তাঁর গল্পের নারীরা সমাজের পুরনো এবং পরিবর্তিত নীতির মধ্যে নিজেদের স্থান খুঁজে বের করতে চেষ্টা করছে। ‘নদীর চরে’ গল্পে সুনীলার চরিত্রটির বাচনভঙ্গি যেমন একটি নারীর জীবনচরিতের অভ্যন্তরীণ সংগ্রামকে তুলে ধরেছে, তেমনি সে নিজেকে একজন সেবিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর সমস্ত কাজ, অনুভূতি এবং ভাষা দিয়ে সুনীলা একটি জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে, যা তাঁর অস্থির, সংগ্রামী জীবনের প্রতিফলন।
আশাপূর্ণা দেবীর রচনায় নারী চরিত্রগুলো সাধারণত সমাজের প্রতি তাদের স্থান, দায়িত্ব এবং কর্তব্যের দিকে খুব সচেতন থাকে। তবে তিনি কখনোই নারীদের শুধু সাহসী বা সংগ্রামী চরিত্র হিসেবে তুলে ধরেননি, বরং সেই সঙ্গে তাদের মানবিক দুর্বলতা এবং ব্যক্তিগত চাহিদাও একে অপরের মধ্যে মিশে গেছে। ‘স্বাধীনতার সুখ’ গল্পে উজ্জ্বলা যখন পুরনো পরিবারের শৃঙ্খলা এবং ঐতিহ্য পরিত্যাগ করে নিজের স্বাধীন জীবন শুরু করে, তখন এটি কেবল একজন নারীর আত্মবিকাশের চিত্র নয়, বরং এটি সমাজের পরিবর্তিত মূল্যবোধেরও একটি প্রতীক।
আশাপূর্ণা দেবীর গল্পে চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্ব, সমাজের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভাষার মাধ্যমে যে স্রোত তৈরি হয়েছে, তা একটি শক্তিশালী সাহিত্যিক দক্ষতা প্রকাশ করে। তাঁর গল্পের চরিত্রগুলো কখনোই একধরনের নয়, বরং তারা ব্যক্তিগত সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে, সামাজিক অবক্ষয় ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিজেদের পরিচয় তৈরি করে। এই চরিত্রগুলির মধ্যে আত্মসম্মান, সংগ্রাম, প্রতিবাদ এবং মানবিক সম্পর্কের নিঃশব্দ অঙ্গীকার ফুটে ওঠে, যা আশাপূর্ণা দেবীর লেখনীকে একটি বিশেষ স্থান প্রদান করে।
আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পগুলিতে সাধারণ মানুষের জীবন এবং তাদের অন্তর্গত সংগ্রামের চিত্র অত্যন্ত বাস্তবভাবে উঠে আসে। তিনি ছোটগল্পের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন দিক, বিশেষ করে নারীর অবস্থা, পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক অসঙ্গতি এবং ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের চিত্র তুলে ধরেছেন। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর লেখনিতে যে ভাষার ব্যবহার করেছেন তা স্বাভাবিক, সহজ এবং অত্যন্ত প্রাঞ্জল। তিনি বাচনভঙ্গি এবং ভাষার মাধ্যমে যে আঙ্গিক তৈরি করেছেন, তা তাঁর গল্পের চরিত্রগুলিকে জীবন্ত এবং বাস্তবিক করে তোলে।
প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার আশাপূর্ণা দেবীর গল্পে একটি উল্লেখযোগ্য দিক। তিনি তাঁর চরিত্রগুলির ভাষার মধ্যে প্রবাদ প্রবচন ব্যবহার করে তাদের জীবন ও মনোভাবকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। ‘পেতল চিনি না? ঘাস তো খাই না!’ (পৃ. ১৯৬, ‘নিগড়’) এবং ‘তোমার সেই বুনঝিকে বোলো ছোট মা; এ একেবারে অব্যর্থ’ (পৃ. ২২২, ‘মনের গহনে’)—এই ধরনের প্রবচন গল্পের চরিত্রদের মানসিক অবস্থা এবং তাঁদের মধ্যে ঘটে চলা সামাজিক ও পারিবারিক পরিবর্তনগুলো অত্যন্ত সহজভাবে প্রকাশ করে। এসব প্রবচন শুধু চরিত্রের ভাবনা-চিন্তার প্রতিফলন নয়, বরং সমাজের অন্দরমহল, পারিবারিক সম্পর্ক এবং মানুষের হতাশা, ক্ষোভ বা প্রত্যাশার প্রতীকও হয়ে দাঁড়ায়। আশাপূর্ণা দেবী যে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করেছেন, তা গল্পের বাস্তবতা ও চরিত্রের গভীরতাকে আরও স্পষ্ট করে তোলে।
‘মরণ যে তোমার কেন হয় না মা, এও এক মস্ত আশ্চর্য!… কানু দেখলি তো বাবা? ও পাপিষ্ঠির নরকেও ঠাঁই হবে তুই ভাবিস?’ (পৃ. ১০৯, ‘অঙ্গার’)—এই উক্তি একেবারে সাধারণ, অথচ জীবনের এক কঠিন বাস্তবতা প্রতিফলিত করে। একটি সাধারণ নারীর চাহিদা, দুঃখ, আক্ষেপ এবং পারিবারিক সমস্যাগুলোর মাঝে যে ব্যথা এবং তিক্ততা থাকে, তা আশাপূর্ণা দেবী অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর লেখায় যে ধরনের ভাষার ব্যবহার, বিশেষত নারীদের ক্ষেত্রে, তা সাধারণ জীবনের অনুষঙ্গ হিসেবে ধরা পড়ে। এই ভাষা এমন এক ধরনের অভ্যন্তরীণ বিশ্বকে প্রকাশ করে, যা খুব সহজে পাঠককে গল্পের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। নারীর মুখ থেকে এমন কথাবার্তা যে এতটাই প্রাকৃত হতে পারে, তা গল্পের চরিত্রগুলিকে আরও বাস্তবিক করে তোলে। এই ধরনের ভাষা গল্পের চরিত্রগুলিকে যেমন সজীব করে তোলে, তেমনি সমাজের বিশুদ্ধতা ও কপটতাকে নিখুঁতভাবে প্রকাশ করে।
‘বহুরূপী’ গল্পে গিরীন্দ্রমোহনের পরিবার এবং তাদের আর্থিক সংকট তুলে ধরার ক্ষেত্রে আশাপূর্ণা দেবী ভাষার ব্যবহার করেছেন এমনভাবে যে, এটি পরিবারের মধ্যে ঘটিত অবক্ষয়, সম্পর্কের জটিলতা এবং পারিবারিক ঐতিহ্যের ক্ষয়কেই প্রকাশ করে। গিরীন্দ্রমোহনের বাড়ির শ্রীহীনতা এবং অবস্থা যে ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছে, তা উক্তির মাধ্যমে ফুটে ওঠে। “গিরীন্দ্রমোহনের অন্ধকার দেখার ফাঁকে চোখ তুলে একবার বাড়িখানার আপাদমস্তক দেখে নেয় নিখিল। বাড়িখানা প্রকাণ্ড সন্দেহ নেই, জমি আছে বিস্তর, কিন্তু জীর্ণতার শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে।” (পৃ. ২৫৫, গল্পসমগ্র ২য় খণ্ড)। এখানে বাড়ির বিশালতার মধ্যে যে শূন্যতা এবং অভ্যন্তরীণ অবক্ষয় রয়েছে, তা শুধু বাড়ির অবস্থা নয়, বরং পরিবার ও সমাজের একটি বৃহত্তর সংকটের ইঙ্গিত দেয়।
আশাপূর্ণা দেবী তাঁর রচনায় যে চরিত্রগুলিকে তুলে ধরেছেন, তারা সমাজের প্রতিটি স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে। ‘পাকা ঘর’ গল্পে এক নারীর যে কষ্টের চিত্র উঠে এসেছে, তা প্রমাণ করে যে সমাজের মধ্যে যারা শ্রেণিগতভাবে নিচু অবস্থানে রয়েছে, তারা নিজেদের জীবনযাত্রা, সংসার পরিচালনা, এবং সমাজের প্রথাগুলোর মধ্যে আটকে রয়েছে। “সেই যে বলে না আমার এ হয়েছে তাই। খাটতে খাটতে আপনার জান্ নিলে গেল গুরুকন্যে পোষা হচ্ছে! চোখের চামড়াকে বলিহারি দিই, খাবো আর শোবো বুঝিনে বাবা! পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেতে এতো মিষ্টি লাগে?” (পৃ. ২৩২, গল্পসমগ্র ৩য় খণ্ড)। এখানে যে হতাশা এবং সামাজিক অবিচার প্রকাশিত হয়েছে, তা পুরোপুরি একটি বৃহত্তর সামাজিক সংকটের প্রতিফলন।
এছাড়া, ‘নিগড়’ গল্পে পিতৃগৃহে প্রতিস্থাপিত এবং শ্বশুরবাড়ির প্রতি অক্ষমতার অনুভূতি, সেখানকার কষ্টকর অভিজ্ঞতা, এবং সামাজিক শ্রেণী-বৈষম্যের দৃষ্টিকোণ থেকে নানাবিধ অনুভূতি উঠে এসেছে। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পের চরিত্রগুলোকে অনেক গভীরতার সঙ্গে সামাজিক স্তরের মধ্যে তাদের অবস্থান তুলে ধরার জন্য তৈরি করেছেন। প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে একটি ব্যক্তিগত সংগ্রাম থাকে, যা তাদের নিজস্ব জীবনযাত্রা এবং সমাজে তাদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করে।
আশাপূর্ণা দেবীর গল্পে চরিত্রের মধ্যে যে পরিবর্তন আসে, তা সাধারণত একটি সমাজবদ্ধ জীবনকে ধরে রাখার প্রয়াসের প্রতিফলন। তাঁর চরিত্রগুলির মধ্যে সর্বদা এক ধরনের সংগ্রাম রয়েছে, যেখানে তারা নিজেদের অস্তিত্ব এবং পরিবারকে রক্ষা করতে চেষ্টা করছে, কিন্তু তারা কখনোই একা নয়, বরং সমাজের নির্ধারিত কাঠামো, সম্পর্ক এবং পুরনো প্রথা তাদের পথের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এর মধ্যে আশাপূর্ণা দেবী বেমানান সামাজিক সম্পর্কের অবক্ষয়ের এবং পুরনো ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অঙ্গীকার সৃষ্টি করেছেন।
অর্থাৎ, আশাপূর্ণা দেবীর গল্পের প্রতিটি নারী চরিত্র, তাদের ভাষার ব্যবহার এবং তাদের মধ্যকার সম্পর্কের জটিলতা একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি বৃহত্তর সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গের অংশ হয়ে ওঠে। তাঁর গল্পের ভাষা, চরিত্র, সামাজিক বিশ্লেষণ এবং পারিবারিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ একটি নতুন সামাজিক বাস্তবতার উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেখানে সামাজিক পরিবর্তন এবং সম্পর্কের পরিবর্তন একসঙ্গে মিশে গেছে।
আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পে ভাষার ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাঁর গল্পে চরিত্রগুলোর মাধ্যমে যে ভাষার উপস্থাপনা ঘটেছে, তা শুধু তাদের মানসিক অবস্থা নয়, বরং সমাজের স্তরবিন্যাস, সম্পর্কের জটিলতা এবং পারিবারিক অবক্ষয়ের চিত্রও প্রতিফলিত করে। আশাপূর্ণা দেবী যে ভাষার ব্যবহার করেছেন, তা মূলত গল্পের বাস্তবতা, চরিত্রের অন্তর্নিহিত দৃষ্টি, এবং সমাজের এক একটি স্তরের অন্তর্নিহিত সংকটকে তুলে ধরে। তাঁর গল্পে যেমন নারীদের ভাষা প্রাধান্য পেয়েছে, তেমনি পুরুষদের ভাষাও সেই সময়ের সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং চরিত্রগুলির জটিলতা ও দ্বন্দ্বের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
‘অনাচার’ গল্পে সুভাষ কাকীমার সম্পর্কে পাড়ার মহিলাদের উক্তিতে নারীদের ভাষার পরিচয় স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। “ওগো কার ভেতরে কি থাকে, সে শুধু সময় এলেই ধরা পড়ে! সুভাষ ছোঁড়া যখন ছিলো, তখন মনে হ’তো বুঝি এমন ভালোবাসাবাসি আর জগতে নেই। তারপর ছোঁড়া হঠাৎ চলেই বা গেলো কেন তাই বা কে বলবে?” (পৃ. ৩৪৭, গল্প সমগ্র ৩য় খণ্ড)। এই উক্তি থেকে নারী চরিত্রের অভ্যন্তরীণ দুঃখ ও বোধের গভীরতা প্রতিফলিত হয়। সুভাষ কাকীমার প্রেমের প্রতি আকর্ষণ এবং তার পরিণতি যে কীভাবে দুঃখের সম্মুখীন হয়েছে, তা এই ভাষায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখানকার ভাষা সরল হলেও এর মধ্যে একটি গভীর সামাজিক চেতনা রয়েছে। এই ধরনের ভাষার ব্যবহার আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পের মাধ্যমে মানুষের অন্তর্নিহিত মনোবেদনা এবং সমাজের বাস্তবতাকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেন।
‘পত্রাবরণ’ গল্পে পঙ্কজের মা মহামায়ার উক্তি একটি ভিন্ন ধরনের সামাজিক ভাষার পরিচয় দেয়। “শোন কথা! ভারি তো পদার্থ জিনিস, দুখানা তেলেভাজা কচুরি! তার আবার না খেলো না, হ্যানো হ’ল না – আমি কি খাচ্ছি না? বৌমা আমার যখন তখনই তো খাবার করছে।” (পৃ. ১১৬, গল্প সমগ্র ৪র্থ খণ্ড)। এখানে মহামায়ার ভাষার সরলতা, হাস্যরস, এবং সমাজের প্রতি তার এক ধরনের অসন্তোষ প্রকাশ পায়। এ ধরনের ভাষা কেবলমাত্র একজন সাধারণ নারী চরিত্রের ক্ষোভ এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিবাদকে প্রতিফলিত করে, যা পাঠককে চরিত্রের সামাজিক অবস্থান এবং তার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত করে তোলে।
‘পাতাল প্রবেশ’ গল্পে মায়ের সঙ্গে মেয়ে সম্পর্কের মাধ্যমে ভাষার প্রভাব আরও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। “কী বললি লক্ষ্মী ছাড়ি? মেয়ে হয়ে তুই বাপের মরণবাক্যি মুখে আনিস? পয়সা আনতে পারে না বলে সে বাপই নয় কেমন?” (পৃ. ১৫৯, ৪র্থ খণ্ড)। মায়ের এই উক্তির মধ্যে যে ভাষাগত তীব্রতা রয়েছে, তা মায়ের দুঃখ ও অভিমানের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে মায়ের ভাষা তীব্র ও প্রখর, যা সমাজের প্রতি তাঁর অসন্তোষ এবং পরিবারের অবস্থা নিয়ে হতাশার চিত্র ফুটিয়ে তোলে। এটি গল্পের চরিত্রের মধ্যে এক ধরনের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সম্পর্কের জটিলতার পরিচয় দেয়।
‘বেহুঁশ’ গল্পে দুই নারী চরিত্রের মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে আশাপূর্ণা দেবী যে ভাষার ব্যবহার করেছেন তা অত্যন্ত প্রাঞ্জল এবং বাস্তব। “আচ্ছা দিদি তোমার শ্বশুর বাড়িতে কেউ নেই বুঝি?” “নেই কি লা? বালাই ষাট! সোনার বিন্দাবন, চাঁদের হাটবাজার।” (পৃ. ১০০, গল্প সমগ্র ২য় খণ্ড)। এই ধরনের বাচনভঙ্গি চরিত্রগুলোর সামাজিক স্তর এবং সম্পর্কের শূন্যতা প্রকাশ করে। এখানে একটি সাধারণ পরিবারে যে ধরনের কথাবার্তা চলে, তা আশাপূর্ণা দেবী তাঁর ভাষার মাধ্যমে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।
‘পাকা ঘর’ গল্পে একজন নারীর ভাষা যে ধরনের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনচিত্র তুলে ধরে, তা আশাপূর্ণা দেবীর ভাষাশৈলীর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। “সেই যে বলে না আমার এ হয়েছে তাই। খাটতে খাটতে আপনার জান্ নিলে গেল গুরুকন্যে পোষা হচ্ছে! চোখের চামড়াকে বলিহারি দিই, খাবো আর শোবো বুঝিনে বাবা!” (পৃ. ২৩২, গল্প সমগ্র ৩য় খণ্ড)। এখানে চরিত্রের ভাষায় তার সংগ্রাম, আর্থিক দুরবস্থা এবং সামাজিক বাস্তবতা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। আশাপূর্ণা দেবী এই ভাষার মাধ্যমে গল্পের গভীরতা এবং চরিত্রের অবস্থা ফুটিয়ে তুলেছেন, যা গল্পের মূল বিষয়বস্তু ও চরিত্রের মনস্তত্ত্বকে আরো বাস্তবিক করে তোলে।
শিশুদের ভাষাও আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পে অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে ব্যবহার করেছেন। ‘শিশু’ গল্পে শিশুর মুখে যে উক্তি রয়েছে, তা তার শিশু সুলভ চপলতা এবং সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। “দুষ্টু পাজী লাকোস দূর যা” (পৃ. ৭৭, গল্প সমগ্র প্রথম পর্ব) এই ধরনের বাক্যবিন্যাস শিশুর অবাধ ভাষার প্রতিফলন। আশাপূর্ণা দেবী শিশুর ভাষার মাধ্যমে শিশুদের অনুভূতি ও মনোভাব প্রকাশ করেছেন, যা গল্পের বাস্তবতাকে আরও প্রকৃত করে তোলে।
বস্তিবাসীদের মধ্যে যে কলহ এবং কথোপকথন ঘটে, তা আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পে অত্যন্ত বাস্তব এবং সরল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। “বলছি টাকা শুধবি কি যম এসে যখন গলায় গামছা বেঁধে নে যাবে তখন?” (পৃ. ১৭৬, গল্প সমগ্র পঞ্চম খণ্ড)। বস্তিবাসীর মধ্যকার যাত্রা, আশা, হতাশা এবং একে অপরের প্রতি সম্পর্কের দূরত্ব এই ধরনের সাধারণ, কিন্তু তীব্র ভাষার মাধ্যমে সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। এই ধরনের ভাষা ব্যবহার গল্পের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়।
আশাপূর্ণা দেবী যে ভাষার ব্যবহার করেছেন তা তাঁর গল্পের চরিত্রগুলির অনুভূতি, সমাজের অবস্থান এবং মানুষের সম্পর্কের জটিলতাকে খুব সহজে ফুটিয়ে তোলে। তাঁর ভাষা কখনোই অলংকৃত বা জটিল নয়, বরং তা প্রকৃত এবং বাস্তব। ভাষার সহজতা এবং সরলতার মধ্যে তিনি যে গভীরতা এবং তীব্রতা ফুটিয়ে তুলেছেন, তা তাঁর লেখনীর সার্থকতা প্রমাণ করে। চরিত্রের ভাষার মাধ্যমে তিনি সমাজের সকল স্তরের মানুষের সংগ্রাম এবং তাদের সম্পর্কের মধ্যে যে কষ্ট, দ্বন্দ্ব, এবং পরিবর্তন রয়েছে, তা গভীরভাবে উঠে এসেছে।
আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পের চরিত্রগুলির মাধ্যমে যে বাস্তবতা তুলে ধরেছেন, তা কোনো কল্পনার জগৎ নয়, বরং সমাজের প্রতিদিনের ঘটনা এবং মানুষের জীবনের কঠিন বাস্তবতা। তাঁর ভাষা, বাচনভঙ্গি, এবং চরিত্রের বিকাশ সৃজনশীল এবং ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই ভাষার মধ্য দিয়ে তিনি সমাজের অঙ্গনে যে সংকট এবং পরিবর্তন ঘটছে, তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন, যা তাঁর গল্পগুলিকে সময় ও সমাজের সত্যিকারের চিত্র হিসেবে চিহ্নিত করে।
আশাপূর্ণা দেবী বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য রত্ন, যাঁর গল্পে বাংলা সমাজের নানা রূপ ফুটে ওঠে। তিনি যেভাবে সামাজিক শ্রেণী, সম্পর্ক, নারীর জীবন, এবং প্রতিদিনের সংগ্রামকে গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন, তা অবিস্মরণীয়। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর লেখায় যে বাস্তবতার চিত্র এঁকেছেন, তা সত্যিই অভূতপূর্ব। তাঁর গল্পের চরিত্রগুলো সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্যে যেমন বাস্তবতার গভীরতার অনুসন্ধান করেছে, তেমনি তিনি বাচনভঙ্গি ও ভাষার মাধ্যমে সেইসব চরিত্রের মানসিক অবস্থাকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন।
আশাপূর্ণা দেবী প্রায় সব গল্পেই ভাষার ব্যবহার অত্যন্ত নিখুঁতভাবে করেছেন। তাঁর গল্পের চরিত্রগুলোর মুখে যে ভাষা উঠে আসে, তা তাদের সামাজিক অবস্থা, চরিত্রের মানসিকতা এবং জীবনযাত্রার বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে। ‘অনাচার’ গল্পে সুভাষ কাকীমার সম্পর্কে পাড়ার মহিলাদের, বিশেষ করে যিনি কথক তার নিজের পিসি-কাকীমা-মায়ের উক্তি, তা থেকে নারীর নিরলঙ্কৃত ভাষার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। “ওগো কার ভেতরে কি থাকে, সে শুধু সময় এলেই ধরা পড়ে! সুভাষ ছোঁড়া যখন ছিলো, তখন মনে হ’তো বুঝি এমন ভালোবাসাবাসি আর জগতে নেই। তারপর ছোঁড়া হঠাৎ চলেই বা গেলো কেন তাই বা কে বলবে?” (পৃ. ৩৪৭, গল্প সমগ্র ৩য় খণ্ড) — এই ভাষা ব্যবহারে নারীর অভ্যন্তরীণ বিচারের প্রবণতা, তার হতাশা এবং পুরুষের প্রতি প্রতিক্রিয়া যেমন বেরিয়ে আসে, তেমনি সেই সমাজের রুচি ও বিচারের ব্যাপারে খোলামেলা ধারণাও উঠে আসে।
‘পত্রাবরণ’ গল্পে পঙ্কজের মা মহামায়ার উক্তি চিরাচরিত ভাষায় এক রকম সামাজিক বিরোধিতা প্রকাশ করে। “শোন কথা! ভারি তো পদার্থ জিনিস, দুখানা তেলেভাজা কচুরি! তার আবার না খেলো না, হ্যানো হ’ল না – আমি কি খাচ্ছি না? বৌমা আমার যখন তখনই তো খাবার করছে।” (পৃ. ১১৬, গল্প সমগ্র ৪র্থ খণ্ড)। মহামায়ার এই ভাষা চরিত্রের অভ্যন্তরীণ দুঃখের, তিক্ততার, এবং পরিবারে নারীর অবস্থান নিয়ে একধরনের অভিযোগের প্রকাশ ঘটায়। এই ধরনের ভাষা গৃহস্থালি জীবনের সংকট এবং সম্পর্কের কঠিন বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে।
‘পাতাল প্রবেশ’ গল্পে, মায়ের মুখে যে ভাষা এসেছে তা একধরনের সামাজিক চাপ এবং অভ্যন্তরীণ অভিমান প্রকাশ করে। “কী বললি লক্ষ্মী ছাড়ি? মেয়ে হয়ে তুই বাপের মরণবাক্যি মুখে আনিস? পয়সা আনতে পারে না বলে সে বাপই নয় কেমন?” (পৃ. ১৫৯, ৪র্থ খণ্ড)। এখানে মায়ের ভাষায় যে তীব্রতা রয়েছে, তা সমাজের নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে নারীর অবস্থান এবং তার মানসিক অবস্থা খুব ভালোভাবে ফুটিয়ে তোলে। এই ভাষার মাধ্যমে সমাজে নারীর প্রতি যে প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়, তা একটি গভীর প্রভাব ফেলেছে।
‘বেহুঁশ’ গল্পে, দুই নারীর মধ্যে কথোপকথন একটি সাধারণ, কিন্তু তীব্র সামাজিক বাস্তবতার প্রতীক হয়ে ওঠে। “আচ্ছা দিদি তোমার শ্বশুর বাড়িতে কেউ নেই বুঝি?” “নেই কি লা? বালাই ষাট! সোনার বিন্দাবন, চাঁদের হাটবাজার।” (পৃ. ১০০, গল্প সমগ্র ২য় খণ্ড)। এই ধরনের ভাষা ব্যবহারে শুধু কথোপকথনের সার্বিক বাস্তবতা নয়, বরং দুটি নারী চরিত্রের মাঝে সম্পর্কের গতিবিধি এবং তাঁদের মনোভাবও উঠে আসে। লেখিকা এখানে সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্যে সমাজের গভীরতাকে সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন।
আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পগুলিতে যে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করেছেন তা এই ভাষার সমৃদ্ধি এবং বৈচিত্র্যকে আরও গভীরভাবে ফুটিয়ে তোলে। ‘উদ্বাস্তু’ গল্পে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত রিফিউজিদের মুখে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা স্থান এবং সময়ের মধ্যে সম্পর্ককে তুলে ধরেছে। “হালার পুত হালা ঘর ভাড়া দেওনের সাদ অইচ! দেড়শ’ টাহা ভারা লওনের সাদ! মস্করা পাইচ হালা! … দেখুম কোন বিয়াকুব ভাড়া দেয় ? নারায়ণ গঞ্জের ছাওয়ালরে চেন নাই বটে! হালার বাড়ি ছাড়ুম … ভিটায় ঘুঘু চরাইয়া ছাড়ুম।” (পৃ. ৩১, গল্প সমগ্র ৩য় খণ্ড) — এই ধরনের ভাষার মাধ্যমে আশাপূর্ণা দেবী শুধুমাত্র রিফিউজিদের অভিজ্ঞতা নয়, বরং তাঁদের সামাজিক অবস্থা, লজ্জা, এবং নতুন পরিবেশে বসবাসের চ্যালেঞ্জও তুলে ধরেছেন।
‘দ্বন্দ্ব’ গল্পে সাঁওতাল ভাষাভাষি নারী চরিত্রের যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, তা খুব কমই দেখা যায়। তবে যেটুকু রয়েছে, তা একটি ভিন্ন ভাষার শুদ্ধতা এবং ওই শ্রেণির সামাজিক অবস্থা এবং মনোভাবকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। “ই-ইয়ে … মাইজী, বাবু মরগেই” … (পৃ. ৩৭৭, গল্প সমগ্র ২য় খণ্ড) — এখানে সাঁওতাল ভাষায় নারীর অভিব্যক্তি তার সরলতা এবং সামাজিক অবস্থানকে স্পষ্ট করে তোলে।
আশাপূর্ণা দেবী তাঁর রচনায় নারী চরিত্রের ভাষার মাধ্যমে যে সামাজিক বাস্তবতা, সম্পর্কের সংকট এবং পারিবারিক দ্বন্দ্বের ছবি এঁকেছেন, তা পাঠককে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তাঁর ভাষার ব্যবহার কখনও সাধারণ, কখনও তীব্র, কখনও মৃদু, কিন্তু সব সময়েই তা চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্ব এবং সমাজের কংক্রিট কাঠামোকে তুলে ধরে। ভাষার সহজতা এবং স্বাভাবিকতা গল্পের বাস্তবতার সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায় এবং চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তোলে। আশাপূর্ণা দেবীর রচনায় ভাষার ব্যবহার নিঃসন্দেহে একটি অন্যতম শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে কাজ করেছে, যা তাঁর গল্পের সার্থকতা প্রতিষ্ঠা করেছে।
নির্বাচিত চরিত্রগুলির ভাষার মধ্যে যে শক্তি রয়েছে, তা আশাপূর্ণা দেবীর সৃজনশীলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তিনি ভাষার মাধ্যমে কেবলমাত্র চরিত্রের অনুভূতি প্রকাশ করেননি, বরং সমাজের গভীরতর সংকট, সম্পর্কের অস্থিরতা, এবং পারিবারিক অবক্ষয়ও তুলে ধরেছেন। তাঁর ভাষার মধ্যে যে শুদ্ধতা, সরলতা এবং গভীরতা রয়েছে, তা বাংলা সাহিত্যের পরিপূর্ণ রূপে একটি অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করেছে।
আশাপূর্ণা দেবী বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য রত্ন, যাঁর গল্পগুলো সমাজের নানা স্তরের মানুষের জীবনচিত্র ফুটিয়ে তোলে। তাঁর লেখায় নারীদের জীবনের বাস্তবতা এবং সামাজিক অস্থিরতার চিত্র এমনভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, যা কেবল সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমাজের প্রতিটি স্তরের গভীরে প্রবাহিত হয়ে এক শক্তিশালী সামাজিক সেতু তৈরি করেছে। তাঁর গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—একদিকে যেমন তিনি জীবনের নানান দিক নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ করেছেন, তেমনি ভাষার ব্যবহারেও তিনি যথেষ্ট সৃজনশীল এবং স্বতন্ত্র ছিলেন। আশাপূর্ণা দেবী চরিত্রের ভাষা, উপমা এবং প্রবাদ প্রবচন ব্যবহারের মাধ্যমে মানবিক অনুভূতি এবং সামাজিক সংগ্রামকে তুলে ধরেছেন, যা তাঁর লেখার সার্থকতা এবং গভীরতাকে প্রতিফলিত করে।
আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পে ভাষার ব্যবহার বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি নিজে ছিলেন একজন নারী, এবং পুরুষদের তুলনায় নারীদের ভাষার ব্যবহার তাঁর লেখায় বেশি উঠে এসেছে। তাঁর গল্পগুলিতে নারীদের মুখে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, তা সমাজের প্রতিকৃতি এবং সেই সমাজের মধ্যে নারীদের অবস্থানকে স্পষ্ট করেছে। নারীর ভাষা, তার মনের জটিলতা এবং সমাজের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করেছে। ‘অনাচার’ গল্পে সুভাষ কাকীমার চরিত্রের মুখে যে উক্তি এসেছে, তা নারীর ভিতরের অনুভূতি এবং সমাজের প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত করেছে। “ওগো কার ভেতরে কি থাকে, সে শুধু সময় এলেই ধরা পড়ে! সুভাষ ছোঁড়া যখন ছিলো, তখন মনে হ’তো বুঝি এমন ভালোবাসাবাসি আর জগতে নেই। তারপর ছোঁড়া হঠাৎ চলেই বা গেলো কেন তাই বা কে বলবে?” (পৃ. ৩৪৭, গল্প সমগ্র ৩য় খণ্ড)। এই ভাষায় নারীর অভ্যন্তরীণ হতাশা, প্রেম এবং প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ পাওয়া গেছে, যা ওই সময়কার সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এবং নারীর প্রতি তার অবস্থানকে একীভূতভাবে তুলে ধরেছে।
আশাপূর্ণা দেবী নিজের রচনায় যে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করেছেন, তা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ‘উদ্বাস্তু’ গল্পে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত রিফিউজিদের মুখে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা শুধুমাত্র তাদের সামাজিক অবস্থা বা আত্মবিশ্বাসের অভাব নয়, বরং তাদের নতুন জায়গায় বসবাসের সংকট এবং ভাষার জগতেও এক ধরনের বিভাজন ফুটিয়ে তুলেছে। “হালার পুত হালা ঘর ভাড়া দেওনের সাদ অইচ! দেড়শ’ টাহা ভারা লওনের সাদ! মস্করা পাইচ হালা! … দেখুম কোন বিয়াকুব ভাড়া দেয় ? নারায়ণ গঞ্জের ছাওয়ালরে চেন নাই বটে! হালার বাড়ি ছাড়ুম … ভিটায় ঘুঘু চরাইয়া ছাড়ুম।” (পৃ. ৩১, গল্প সমগ্র ৩য় খণ্ড)। এই ধরনের আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পের চরিত্রগুলিকে একটি অনন্য বাস্তবতা প্রদান করেছে। এটি সমাজের প্রতি তাদের হতাশা, জীবনের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, এবং তাঁদের প্রতি সমাজের বৈষম্য ও অস্বীকৃতির চিত্র তুলে ধরে।
আশাপূর্ণা দেবী খুব নিখুঁতভাবে সামাজিক ও পারিবারিক অবক্ষয়ের চিত্র প্রকাশ করেছেন তাঁর গল্পে, বিশেষতঃ বিধবাদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি। ‘ছিন্নমস্তা’ গল্পে বিধবা জয়াবতীর চরিত্রের মধ্যে এমন এক দুঃখ প্রকাশ পায়, যা সমাজের চোখে বিধবাদের প্রতি অবহেলা এবং তাচ্ছিল্যকে প্রতিফলিত করে। “তা বলে বিধবা মাগীদের মতন গাদাগাদা চচ্চড়ি খাবার এতো সখ নেই আমার। নামিয়ে দিয়ে নষ্ট করলেন কেন, রাখলেই পারতেন নিজের জন্যে। আপনার লোভের জিনিস” (পৃ. ১৬৮, গল্প সমগ্র ৩য় খণ্ড)। এই উক্তি থেকে বুঝা যায় যে, সমাজের নির্দিষ্ট স্তরের নারীরা কিভাবে তাদের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ দুঃখ-বেদনা এবং অভিমান প্রকাশ করেন। এই ধরনের ভাষার মধ্যে নারী চরিত্রের সামাজিক অবস্থান, তার সংগ্রাম, এবং অসহায়তার চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
‘বেহুঁশ’ গল্পে, বিধবাদের মুখে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, তা আরও গভীরভাবে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের প্রতিফলন। “অসভ্যর মতো হাসছে দেখো। বিধবা মানুষের অতো হাসি কেন? দেখলে গা জ্বলে যায়।” (পৃ. ৯৮, গল্প সমগ্র ৩য় খণ্ড)। এভাবে আশাপূর্ণা দেবী বিধবাদের সামাজিক অগ্রগতি, সম্পর্কের সংকট, এবং তাঁদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। বিধবাদের মধ্যে যে এক ধরনের হতাশা, সামাজিক চাপ এবং নিষ্কলঙ্ক জীবনযাত্রা রয়েছে, তা এই ভাষার মাধ্যমে ফুটে উঠেছে।
‘পাকা ঘর’ গল্পে, বিধবার যে অবস্থা এবং সে কিভাবে সমাজের মধ্যস্থানে অদৃশ্য হয়ে যায়, তা বেশ পরিস্কারভাবে ফুটে উঠেছে। “একলা মানুষ বিধবা, তার যে আস্ত একখানা ঘরের কি দরকার বুঝিও না।” (পৃ. ১৬৭, গল্প সমগ্র ৩য় খণ্ড)। এখানে একটি বিধবার সমাজের প্রতি অভ্যন্তরীণ প্রতিবাদ এবং তার মনের দুর্দশা প্রকাশ পায়। একাকী, অব্যবহৃত, এবং পরিত্যক্ত অবস্থায় বিধবাদের জীবন কীভাবে সমাজের বিবিধ কাঠামোর মধ্যে আটকে যায়, তা এই ভাষার মাধ্যমে উঠে এসেছে।
অথচ আশাপূর্ণা দেবী কখনোই মুষড়ে পড়েননি। তাঁর গল্পের ভাষার মধ্য দিয়ে তিনি সমাজের অগ্রগতি, নারীর স্বাধীনতা এবং সবার জন্য একটি ভাল জীবনযাত্রার চিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁর ভাষার সরলতা, আর্থিক-সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, এবং নারীর মুক্তির সংগ্রাম এই লেখনীকে সমৃদ্ধ করেছে। এই ভাষার মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক ধারাও রয়েছে, যেখানে সাধারণ মানুষের মুখ থেকে উচ্চারিত কথাগুলো অন্দরমহলের সংকট এবং বাস্তবতার চিত্র তুলে ধরেছে।
আশাপূর্ণা দেবী যেভাবে নারীদের ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের ক্ষত-বিক্ষত অংশগুলো প্রকাশ করেছেন, তা বাংলা সাহিত্যে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করেছে। তিনি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি চরিত্রের ভাষায় বাস্তবতার মুখাবেধ উপস্থাপন করেছেন। তাঁর গল্পের মধ্যে যে ভাষার সরলতা, সহজতা এবং সরল বাচনভঙ্গি রয়েছে, তা পাঠককে এক স্বপ্নময় বাস্তবতায় নিয়ে যায়, যেখানে জীবন-জগতের প্রতিটি মুহূর্ত অন্তর্নিহিত অর্থ নিয়ে আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে।
আশাপূর্ণা দেবীর রচনাসম্ভার আমাদের সমাজের নানা দিক এবং বিশেষত নারীর জীবনের অভ্যন্তরীণ সংকটকে প্রকাশ করেছে। তাঁর গল্পে যে বিষাদ, সংগ্রাম, এবং আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের চিত্র ফুটে উঠেছে, তা পাঠককে সমাজের গভীরে প্রবাহিত করে এবং সমাজের প্রত্যেক স্তরের মানুষের জীবনের সার্থকতার সন্ধানে প্রেরণা যোগায়। আশাপূর্ণা দেবী বিশেষ করে নারী চরিত্রের গভীর বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাঁদের ভাষা, মনোভাব, সামাজিক অবস্থান, এবং সম্পর্কের পরিবর্তনকে অত্যন্ত সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর লেখনির মূল শক্তি হল চরিত্রের প্রাকৃতিক বিকাশ, ভাষার সঠিক ব্যবহার, এবং গভীর সামাজিক সচেতনতা, যা তাঁর গল্পগুলোকে এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেয়।
আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পের মাধ্যমে নারীদের জীবনের নানা দিক সঠিকভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি যে ধরনের ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা নারী চরিত্রগুলির বাস্তবতা এবং তাদের অভ্যন্তরীণ সংকটকে অত্যন্ত প্রাকৃতিকভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। যেমন, ‘অনাচার’ গল্পে সুভাষ কাকীমার চরিত্রের ভাষা খুব সাধারণ, কিন্তু সেই সাধারণ ভাষাতেই যে গভীর মানবিকতা এবং সামাজিক বাস্তবতার প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। “ওগো কার ভেতরে কি থাকে, সে শুধু সময় এলেই ধরা পড়ে! সুভাষ ছোঁড়া যখন ছিলো, তখন মনে হ’তো বুঝি এমন ভালোবাসাবাসি আর জগতে নেই। তারপর ছোঁড়া হঠাৎ চলেই বা গেলো কেন তাই বা কে বলবে?” (পৃ. ৩৪৭, গল্প সমগ্র ৩য় খণ্ড)। এই ভাষার মাধ্যমে সুভাষ কাকীমার চরিত্রের অভ্যন্তরীণ বিভ্রান্তি, তার হতাশা এবং পরবর্তী পরিস্থিতির প্রতিফলন ঘটেছে।
এর পাশাপাশি, আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পে অত্যন্ত সহজ সরল ভাষার মাধ্যমে নারীদের মনোভাবকে ফুটিয়ে তুলেছেন। ‘পত্রাবরণ’ গল্পের মহামায়ার উক্তি অত্যন্ত সাধারণ, কিন্তু সেখানেও যে নারীর জীবনের সংকট এবং তার মনোভাব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে তা দেখা যায়। “শোন কথা! ভারি তো পদার্থ জিনিস, দুখানা তেলেভাজা কচুরি! তার আবার না খেলো না, হ্যানো হ’ল না – আমি কি খাচ্ছি না? বৌমা আমার যখন তখনই তো খাবার করছে।” (পৃ. ১১৬, গল্প সমগ্র ৪র্থ খণ্ড)। এই সাধারণ কথার মধ্যে যে নারীর প্রভাবিত চেতনা এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে, তা আশাপূর্ণা দেবীর নিপুণ ভাষাশৈলীর এক অনন্য দৃষ্টান্ত।
আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পে যে ভাষার সহজতা এবং পরিচিত শব্দ চয়নের মাধ্যমে সমাজের বাস্তবতার চিত্র আঁকেন, তা চিরকালীন মানবিক সংকটের বহিঃপ্রকাশ। তাঁর গল্পগুলিতে নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের অভ্যন্তরীণ বেদনা এবং সংগ্রামের চিত্র অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি নারী চরিত্রের যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা তাদের সামাজিক অবস্থান, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং জীবনের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব।
নির্দিষ্ট সামাজিক স্তরের নারী চরিত্রদের ভাষার মাধ্যমে আশাপূর্ণা দেবী তাঁদের নিজস্ব ভাবনা, সামাজিক অবস্থান এবং মানসিকতা তুলে ধরেছেন। বিশেষত, ‘ছিন্নমস্তা’ গল্পে বিধবা জয়াবতী চরিত্রের মাধ্যমে সমাজের প্রতি নারীর প্রতিবাদ এবং তার অনুভূতির প্রকাশ পাওয়া যায়। “তা বলে বিধবা মাগীদের মতন গাদাগাদা চচ্চড়ি খাবার এতো সখ নেই আমার। নামিয়ে দিয়ে নষ্ট করলেন কেন, রাখলেই পারতেন নিজের জন্যে। আপনার লোভের জিনিস” (পৃ. ১৬৮, গল্প সমগ্র ৩য় খণ্ড)। এই ভাষার মাধ্যমে একদিকে যেমন নারীর প্রতি সমাজের অবহেলা এবং তার সামাজিক শর্তাবলী তুলে ধরা হয়, তেমনি সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি গভীর মানবিক দৃষ্টি প্রদান করা হয়।
আশাপূর্ণা দেবী শুধু নারীর ভাষা ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, তিনি পুরুষ চরিত্রের ভাষাও যথাযথভাবে ব্যবহার করেছেন। পুরুষ চরিত্রগুলির উক্তি এবং তাদের ভাষার মাধ্যমে তিনি সমাজের অবস্থা, মানসিকতা এবং নারীর প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করেছেন। ‘পাঠান’ গল্পে আমরা দেখতে পাই, পুরুষ চরিত্রের ভাষা নারীর প্রতি একধরনের সোহমতা এবং বিরোধের চিত্র তুলে ধরে, যা সমকালীন সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবিম্ব।
অন্যদিকে, আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পে যে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করেছেন, তা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনের বৈচিত্র্য এবং বাস্তবতা তুলে ধরেছে। ‘উদ্বাস্তু’ গল্পে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত রিফিউজিদের মুখে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা কেবল তাদের সামাজিক অবস্থান কিংবা অভ্যন্তরীণ দুঃখের প্রকাশ নয়, বরং তাদের নতুন স্থান, নতুন জীবন এবং ভাষাগত বিভাজনও তুলে ধরেছে। “হালার পুত হালা ঘর ভাড়া দেওনের সাদ অইচ! দেড়শ’ টাহা ভারা লওনের সাদ! মস্করা পাইচ হালা! … দেখুম কোন বিয়াকুব ভাড়া দেয় ? নারায়ণ গঞ্জের ছাওয়ালরে চেন নাই বটে! হালার বাড়ি ছাড়ুম … ভিটায় ঘুঘু চরাইয়া ছাড়ুম।” (পৃ. ৩১, গল্প সমগ্র ৩য় খণ্ড)। এই ধরনের আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পে চরিত্রগুলির মধ্যে বিশিষ্টতার সৃষ্টি করেছে এবং একই সঙ্গে সমাজের পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গি এবং পারস্পরিক সম্পর্কের প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে।
আশাপূর্ণা দেবী যখন তাঁর চরিত্রগুলির মধ্যে কাব্যিক ভাষার ব্যবহার করেন, তখন সেটা সেই চরিত্রগুলির সাংস্কৃতিক এবং ব্যক্তিগত পরিচয়ের সাথে যুক্ত হয়ে উঠেছে। ‘পাকা ঘর’ গল্পে চরিত্রের ভাষায় যে আভিজ্ঞান এবং দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠে, তা কেবল তার সামাজিক অবস্থা বা মনোভাব নয়, বরং তার ব্যক্তিত্বের বিকাশও নির্দেশ করে। “এতো বড়ো বাড়ির ভেতরে আজও একরকম খালি জানলা এবং ফাটল দেখা গেছে, যেন বাড়ির ভাঙা দেয়ালও জীবন্ত হয়ে উঠেছে।” (পৃ. ২৩৩, গল্প সমগ্র ৩য় খণ্ড)। এই ভাষা চরিত্রের দুঃখ, সামাজিক প্রতিকূলতা এবং তার জীবনের অন্তর্নিহিত সংগ্রামকে একত্রে প্রতিফলিত করে।
আশাপূর্ণা দেবী তাঁর রচনার মধ্যে যে ভাষাশৈলী এবং সামাজিক সচেতনতার সমন্বয় ঘটিয়েছেন, তা বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছে। তাঁর গল্পের ভাষার সরলতা এবং চরিত্রের মধ্যে যে আন্তরিকতা ফুটে উঠেছে, তা পাঠককে এক জীবন্ত অভিজ্ঞতায় প্রবাহিত করে। তাঁর ভাষা, চরিত্র, এবং সামাজিক বিশ্লেষণ বাংলা সাহিত্যের একটি শক্তিশালী ধারা তৈরি করেছে, যা আমাদের সমাজের গভীরতম আবেগ এবং বাস্তবতাকে স্পষ্ট করে তোলে।
আশাপূর্ণা দেবী বাংলা সাহিত্যে যে বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন, তা কেবল তাঁর সৃষ্টির জন্য নয়, বরং তাঁর শিল্পরীতি ও চিন্তা-চেতনার জন্যও। তিনি কখনোই আঙ্গিক, গঠন কৌশল বা বিদেশি সাহিত্য পাঠের প্রয়োজনীয়তার প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব দেননি। তাঁর ভাষায় প্রতিফলিত হয়েছে সহজ ও স্বাভাবিক জীবনদর্শন, যা প্রতিটি শব্দের মধ্যে নিজের পরিচয়কে খুঁজে পাওয়ার সুযোগ দেয়। আশাপূর্ণা দেবী নিজেই বলেছিলেন, “যা বলতে চেয়েছি, তা না বলে আঙ্গিকের দিকে বেশি নজর দেওয়া প্রয়োজন হয়নি।” তাঁর গল্পের মূল শক্তি ছিল চরিত্র, তাদের আবেগ ও সম্পর্কের জটিলতা, যা কখনোই কৃত্রিমভাবে উপস্থাপন করা হয়নি।
আশাপূর্ণা দেবী কোনো জটিল প্লট বা গঠন কৌশলের দিকে মনোনিবেশ করেননি। তাঁর গল্পের কাহিনী সরল, একমুখী এবং বাস্তব। তাঁর জীবনে যা ঘটেছিল, যা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেটাই তাঁর লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে। বাস্তবতার সঙ্গে মিথ বা কল্পনার কোনও সম্পর্ক ছিল না, বরং প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র যেন তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত। এই সহজ, সরল কাহিনী বিন্যাসের মাধ্যমে তিনি সমাজের নানা স্তরের মানুষের জীবনের সত্যি চিত্র তুলে ধরেছেন। বিশেষত নারীর জীবনযাত্রা, তাদের সমস্যাগুলো এবং তাদের সমাজের সঙ্গে সম্পর্কের বিবরণ, যা খুবই বাস্তবসম্মতভাবে তাঁর গল্পে ধরা পড়েছে। তাঁর লেখার মধ্যে যে মানবিকতা ও সমাজ সচেতনতা ছিল, তা প্রায় প্রতিটি চরিত্রে পরিস্ফুটিত হয়েছে।
একটি বিশেষ দিক যা আশাপূর্ণা দেবীর লেখায় প্রাধান্য পেয়েছে, তা হলো ভাষার শালীনতা ও শব্দচয়নে নিপুণতা। তিনি ভাষার ক্ষেত্রে কোনো বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না। তার রচনায় শব্দ ছিল সুনির্বাচিত এবং প্রাসঙ্গিক। চরিত্রের ভাষা, তাদের বাচনভঙ্গি, এবং সমাজের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের প্রতিফলন খুবই স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল। একজন লেখক হিসেবে আশাপূর্ণা দেবী জানতেন, কীভাবে চরিত্রের মধ্যে একটি বিশিষ্টতা আনতে হয়, আর ভাষা এবং সংলাপের মাধ্যমে সে বিশিষ্টতা ফুটিয়ে তুলতেন। তাঁর গল্পগুলিতে নারী চরিত্রের দুঃখ, সংগ্রাম, এবং তাদের সমাজে স্থান পাওয়া, সব কিছু খুবই প্রকৃতিপূর্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছে।
আশাপূর্ণা দেবীর গল্পের ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল এবং সহজ ছিল, যা পাঠককে তাত্ক্ষণিকভাবে আকর্ষণ করত। তাঁর গল্পের চরিত্রগুলির ভাষায় একটি অন্তর্নিহিত সত্যতা ছিল, যা তাঁদের আবেগ, মনোভাব, এবং সামাজিক অবস্থান থেকে উদ্ভূত ছিল। প্রতিটি চরিত্র যেন জীবন্ত হয়ে উঠত, তাদের মুখের ভাষার মাধ্যমে। নারীর সামাজিক অবস্থান, তাদের প্রতিবন্ধকতা, এবং সমাজের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের পরিবর্তন তাঁর গল্পের মাধ্যমে খুবই সজীবভাবে ফুটে উঠেছে।
আরেকটি বিশেষ দিক ছিল আশাপূর্ণা দেবীর চরিত্রের গভীরতা। তাঁর গল্পের চরিত্রগুলি কোন না কোন ভাবে বাস্তবতার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। তারা জীবনের সংকট, তাদের ব্যক্তি-জীবন, এবং সামাজিক জীবনে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে যুদ্ধ করত। এই চরিত্রগুলির মধ্যে অহংকার, মর্যাদা, নিরাশা, সাহস, এবং মানবিক গুণাবলীর যে অসামান্য সমন্বয় ছিল, তা শুধু আশাপূর্ণা দেবীর লেখার শক্তি নয়, বরং বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য রত্ন হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।
আশাপূর্ণা দেবী সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের জীবনকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর গল্পগুলো কেবল সমাজের দরিদ্র, হতদরিদ্র, মধ্যবিত্ত, অথবা উচ্চবিত্তদের জীবনই তুলে ধরে না, বরং এক-একটি চরিত্রের মধ্যে নারীর আত্মসম্মানবোধ এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশও দেখান। বিশেষত বিধবা নারীদের নিয়ে তাঁর লেখার একটি বিশেষত্ব ছিল। ‘ছিন্নমস্তা’ গল্পের জয়াবতী চরিত্রের মাধ্যমে তিনি বিধবাদের সমাজে শোচনীয় অবস্থান এবং তাদের জীবনের ব্যথা, কষ্ট, একাকিত্ব, এবং সামাজিক অবজ্ঞার চিত্র অত্যন্ত বাস্তবভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।
এছাড়া তাঁর রচনায় চিরকালীন মানবিক সমস্যাগুলির মধ্যে সবার আগে স্থান পেয়েছে নারীর অবস্থান, তার অধিকার, এবং মর্যাদাবোধের প্রশ্ন। ‘অভিশপ্ত’ গল্পের পিণাক পানি চৌধুরী, ‘কসাই’ গল্পের সমরেশ, ‘পৌরুষ’ গল্পের নিতাই প্রভৃতি পুরুষ চরিত্রেও আশাপূর্ণা দেবী সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানবিক সম্পর্ক এবং তাঁদের ব্যক্তিত্বকে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। পুরুষদের জীবনেও ছিল জটিলতা, এবং নারী চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কের এই যূথবদ্ধতা সমাজের কঠিন বাস্তবতা তুলে ধরেছে।
তাঁর রচনায় যে ভাষার ব্যবহার ছিল, তা শুধুমাত্র শব্দের মাধ্যমে এক ধরনের প্রকাশ ঘটিয়েছে, বরং সেই ভাষার মধ্যে সমাজের প্রতি লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গিও ফুটে উঠেছে। যখন তিনি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বিভাজন, সংকট, সম্পর্ক, এবং সামাজিক অবস্থা তুলে ধরেছেন, তখন সেই ভাষা যেন মানুষের মনস্তত্ত্ব এবং অনুভূতির গভীরে পৌঁছে গিয়েছে। তাঁর ভাষার গঠন এবং চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কের গভীরতা, সেই চরিত্রের ভাষা ও উপলব্ধি, সব কিছুই তাঁর সৃষ্টিকে এক অভিনব মাত্রায় নিয়ে গেছে।
এছাড়া তাঁর ভাষার মধ্যে ছিল এক ধরনের কাব্যিক সৌন্দর্য যা গদ্য এবং কবিতার মধ্যে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সেতু তৈরি করেছে। তিনি নিজের রচনায় কবিতা, গান, এবং সংগীতের পংক্তি প্রয়োগ করেছেন যা গল্পের পরিবেশ এবং চরিত্রের সঙ্গতি অনুসারে ছিল উপযুক্ত। তাঁর লেখায় যে কাব্যিকতা, ভাবগম্ভীরতা, এবং ভাষার মধ্যে মাধুর্য ছিল, তা একটি অদ্বিতীয় সত্ত্বার প্রতিফলন। যেমন ‘রাহু’ গল্পে, “আমায় বাঁশীতে ডেকেছে কে, ওগো ললিতে” (পৃ. ১১৮, ২য় খণ্ড), “পবিত্র তুমি, নিৰ্ম্মল তুমি, তুমি দেবী তুমি সতী; কুৎসিত দীন অধম পামর পঙ্কিল আমি অতি।” (পৃ. ১১৯, ঐ)। এই কবিতাগুলো চরিত্রের মনের অতল গভীরতা, তার দুঃখ-কষ্ট এবং তার জীবনের সংগ্রামের নিদর্শন হিসেবে কাজ করেছে।
পরিশেষে, আশাপূর্ণা দেবী তাঁর রচনাতে যে ধরনের সরলতা, মানবিক গুণাবলি এবং ভাষার জাদু ব্যবহার করেছেন, তা শুধুমাত্র গল্পের চরিত্রগুলোকে জীবন্ত করে তোলে না, বরং পাঠকের মনের ভিতরেও গভীর রেখাপাত করে। তাঁর চরিত্রগুলির ভাষা, মনোভাব, এবং সামাজিক অবস্থা আমাদের সমাজের চিত্রই তুলে ধরে, যা একদিকে যেমন চিরকালীন মানবিক মূল্যবোধের পরিচায়ক, তেমনি অন্যদিকে সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতিরও এক অদ্বিতীয় রূপরেখা দেয়।

 নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা
নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা