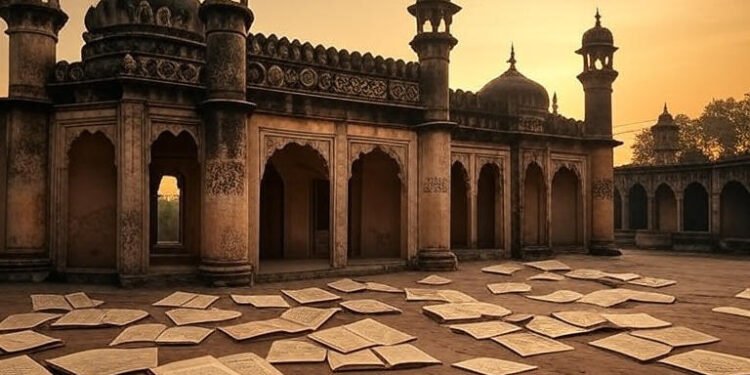লিখেছেনঃ মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম
গজনীর মাহমুদ ও মহম্মদ ঘোরীর ধারাবাহিক ও সফল সামরিক অভিযানের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটে। এই আক্রমণ কেবল সীমান্তবর্তী ভূখণ্ড দখলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা ছিল তুর্কি ও আফগান শাসনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের প্রথম পদক্ষেপ। “তুর্কী ও আফগানদের শাসন প্রতিষ্ঠার এই হল সূচনা”—এই সত্যকে সমকালীন ভারতীয় রাজনীতির অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা অনুধাবন করলেও, স্থানীয় সমাজে নবাগত শক্তিকে নিয়ে তেমন কোনো ব্যাপক কৌতূহল দেখা যায়নি। রাজদণ্ডের মালিকানা পরিবর্তনের সম্ভাবনা অনেকেই টের পেয়েছিল, কিন্তু এই পরিবর্তনের প্রভাব যে কেবল রাজনৈতিক সীমারেখার মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে না—বরং দীর্ঘমেয়াদে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সমাজজীবনে গভীর ছাপ ফেলবে—এমন দূরদৃষ্টি তখন খুব কম লোকের মধ্যেই ছিল।
তুর্কি ও আফগান সেনানায়কেরা প্রথমে দিল্লী ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নিজেদের ক্ষমতার ভিত্তি সুসংহত করেন। দিল্লী তখন কেবল একটি নগরী নয়, বরং একটি কৌশলগত সামরিক কেন্দ্র—যেখান থেকে সহজেই গাঙ্গেয় সমভূমি, উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে অভিযান চালানো সম্ভব ছিল। দিল্লীর প্রতিরক্ষা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা প্রমাণ করেছে চৌহানদের তীব্র প্রতিরোধ—যা মূলত দিল্লী অঞ্চল থেকেই সংঘটিত হয়েছিল। ফলে, তুর্কি শাসকগণ দিল্লীকেই তাদের প্রধান প্রতিরোধকেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। এর সঙ্গে ভৌগোলিক আরেকটি সুবিধা ছিল—আফগানিস্তান থেকে দিল্লীতে পৌঁছনো তুলনামূলকভাবে সহজ, যা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আগত তুর্কি ও আফগান বাহিনীর জন্য এক বড় কৌশলগত লাভ এনে দেয়।
দিল্লীর সিংহাসনে বসা তুর্কি সুলতানদের আমলকে ইতিহাসে ‘সুলতানী যুগ’ নামে অভিহিত করা হয়। প্রচলিত ঐতিহাসিক পরিভাষায় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত উত্তর ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক ইতিহাসই এই ‘সুলতানী আমল’-এর অন্তর্ভুক্ত। এই নামকরণ অবশ্য যুগবিভাগের দিক থেকে সুবিধাজনক হলেও, মনে রাখা জরুরি যে ‘সুলতানী আমল’ বলতে সর্বভারতব্যাপী এককেন্দ্রিক সাম্রাজ্য বোঝায় না। বিভিন্ন প্রাদেশিক শক্তির উত্থান-পতন সত্ত্বেও, এই দীর্ঘ সময়ে দিল্লীর সুলতানরাই উত্তর ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে মুখ্য শক্তি হিসেবে বিরাজ করেছিলেন।
বাংলার মধ্যযুগের সূচনা নির্ধারণে অধিকাংশ ঐতিহাসিকই একমত যে, তা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আরম্ভ হয় এবং সমাপ্তি ঘটে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে, যখন মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ‘সুবাহ বাংলার’ দেওয়ানি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে তুলে দেন। এই দীর্ঘ সময়ে বাংলার ইতিহাসলিখন পরম্পরা ছিল বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্ন; অধিকাংশ প্রামাণ্য দলিল ও বিবরণ রচিত হয়েছিল বাংলার বাইরে। ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা ভারতীয় ইতিহাসচর্চার এক নতুন ধারা সূচনা করেছিল—যেখানে ইতিহাস রচনা সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে বিকশিত হয়। ‘ভারতীয় সংস্কৃতিতে মুসলমানদের এক মহান অবদান’ হিসেবে এই ইতিহাসচর্চার ধারা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। তবে, এই ঐতিহাসিক চর্চা বাংলায় তেমন গভীরভাবে প্রোথিত হয়েছিল বলে প্রমাণ মেলে না।
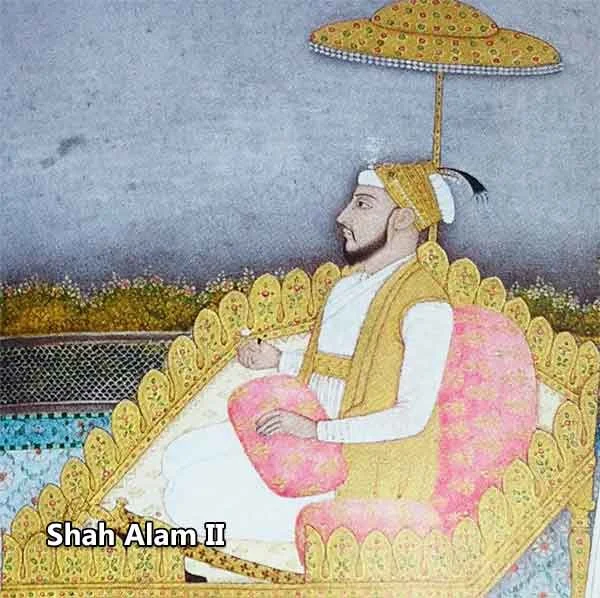
ভারতের মধ্যযুগ চিহ্নিত করা ইউরোপীয় ধাঁচে সময়সীমা নির্ধারণ করে সম্ভব নয়। ইউরোপে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিপুল পরিবর্তন ঘটে, তার ভিত্তিতে সেখানকার প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের রেখা টানা যায়; কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে তেমন সরল বিভাজন প্রযোজ্য নয়। ইউরোপে যখন মধ্যযুগ সমাপ্তির পথে, তখনও ভারতের বহু অঞ্চলে প্রাচীন যুগের রাজনৈতিক কাঠামো কার্যকর ছিল। আবার ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, যখন ভারতবর্ষ গভীরভাবে মধ্যযুগে নিমজ্জিত, তখন ইউরোপ আধুনিক যুগের প্রস্তুতিপর্বে প্রবেশ করছে।
অতএব, ইতিহাসের যুগবিভাগ কেবল কালানুক্রমের ভিত্তিতে নয়, বরং সমাজ-অর্থনীতি ও রাজনৈতিক কাঠামোর রূপান্তরের চরিত্রের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। প্রাচীন রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভাঙন, উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন, বাণিজ্যের প্রসার এবং সামরিক সংগঠনের রূপান্তর—এই সব উপাদান মিলিয়েই যুগান্তরের সূচনা ঘটে। ইউরোপে পঞ্চম শতকের শেষভাগে যেমন প্রাচীন সভ্যতার অবসান হয়েছিল, তেমনি ভারতেও মধ্যযুগীয় চরিত্রের বিকাশ ঘটেছিল নিজস্ব রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতির প্রভাবে—যা বাইরের আক্রমণ, স্থানীয় প্রতিরোধ এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের সম্মিলিত ফলাফল।
ঐতিহাসিক উপাদান
ইতিহাস চর্চা কেবল অতীত কাহিনির সরল বর্ণনা নয়—এটি এক বিজ্ঞানমনস্ক প্রক্রিয়া, যেখানে প্রাপ্ত তথ্যসূত্রকে সঠিক পদ্ধতি ও বিশ্লেষণপদ্ধতির মাধ্যমে যাচাই করে সত্য উদঘাটন করা হয়। অতীতের ঘটনাবলি, ব্যক্তিচরিত্র কিংবা সামাজিক রূপান্তরের বিশদ বিবরণকে নির্ভুল ও যুক্তিনিষ্ঠভাবে বিন্যস্ত করেই ইতিহাসের প্রকৃত রূপ নির্মিত হয়। ইতিহাসবিদ নিজে ইতিহাস ‘গড়ে তোলেন’ না; তিনি কেবল বিদ্যমান প্রমাণ, দলিল এবং প্রাসঙ্গিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে ঘটনাবলির নিরপেক্ষ পুনর্গঠন করেন। এই কারণে, যে কোনো যুগের ইতিহাস অধ্যয়নে সচেতন পাঠকের প্রথম কাজ হওয়া উচিত সেই ইতিহাস রচনায় ব্যবহৃত মূল উপাদান ও সূত্রের অনুসন্ধান করা—যা থেকে লেখক তাঁর বিবরণ নির্মাণ করেছেন।
প্রাচীন ভারতের ইতিহাসচর্চার উপাদান এবং মধ্যযুগের ইতিহাসচর্চার উপাদান—দুটিই একই ধারার মধ্যে জন্মালেও তাদের প্রকৃতি ও প্রয়োগে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। প্রাচীন ভারতে ঘটনাপ্রবাহ লিপিবদ্ধ করার প্রচেষ্টা বহুবার গ্রহণ করা হলেও, সন-তারিখ সংযুক্ত করে বৈজ্ঞানিকভাবে ইতিহাস রচনার চর্চা তেমন দেখা যায়নি। রাজারা প্রায়শই দরবারের কবি বা পণ্ডিতদের দ্বারা নিজেদের বীরত্বগাথা, দানশীলতা, ধর্মীয় অনুশাসন বা প্রশাসনিক নির্দেশাবলি তাম্রশাসন, প্রস্তরফলক কিংবা লিপিপত্রে উৎকীর্ণ করাতেন। অনেক সময় রাজা বা ধর্মনেতাদের জীবনীগ্রন্থ রচিত হত, যেখানে প্রাসঙ্গিকভাবে কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ পেত, কিন্তু সেগুলি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের মর্যাদা লাভ করত না।
কিছু প্রাচীন গ্রন্থ আজও আমাদের হাতে এসেছে, কিন্তু সেগুলো অধিকাংশই কাহিনিনির্ভর, যেখানে ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুপস্থিত। ফলে সমসাময়িক প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসগ্রন্থ প্রায় অনুপস্থিত বললেই চলে। এই শূন্যতায় একটি বিশেষ ব্যতিক্রম হল কাশ্মীরের মহাকবি কলহন রচিত রাজতরঙ্গিনী—যাকে প্রাচীন ভারতের প্রথম প্রামাণ্য ইতিহাসগ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হয়। যদিও এর মধ্যেও পৌরাণিক উপাদান রয়েছে, তবুও ঘটনাপ্রবাহ ও ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে এটি ইতিহাসচর্চায় নতুন মাত্রা যুক্ত করেছিল। এর ফলে স্পষ্ট হয়, প্রাচীন ভারতের হাজার বছরের ইতিহাস পরবর্তী যুগের ইতিহাসবিদদেরকে নানা বিচ্ছিন্ন উপাদানের ভেতর থেকে পুনর্গঠন করতে হয়েছে।
মধ্যযুগে এসে ইতিহাস রচনার ধারা ভিন্ন রূপ পায়। মুসলমান শাসনের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে এই কালপর্বে ইতিহাসচর্চার সম্ভাবনা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। মুসলমানদের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল—তারা ইতিহাস-সচেতন জাতি হিসেবে পরিচিত। সুলতানি ও মুঘল আমলে সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু ইতিহাসগ্রন্থ রচিত হয়, যেগুলোতে সমকালীন ঘটনাবলির পাশাপাশি পূর্বতন যুগের বিবরণও সংযোজিত হয়। মুঘল আমলে সম্রাটগণ প্রায়শই রাজদরবারে ইতিহাসবিদ নিয়োগ করতেন, যারা সরকারিভাবে সমসাময়িক রাজনৈতিক, সামরিক ও প্রশাসনিক ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করতেন। তবে এই পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত গ্রন্থগুলো ব্যবহার করার সময় সতর্ক থাকা জরুরি, কারণ দরবারি লেখকেরা প্রায়শই রাজদরবারের ভাবমূর্তি রক্ষার্থে তথ্য উপস্থাপন করতেন, যা নিরপেক্ষতার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াত।
দরবারি ইতিহাসবিদদের লেখায় অমুসলিম শাসক বা হিন্দু রাজাদের বীরত্ব ও কৃতিত্বের বর্ণনা সচরাচর পাওয়া যায় না। দৃষ্টিভঙ্গির এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে হলে সমসাময়িক সাহিত্য, বিদেশি ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলিকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হয়। মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাস মূলত দুটি প্রধান রাজনৈতিক পর্বে বিভক্ত—সুলতানি শাসনপর্ব ও মুঘল শাসনপর্ব—এবং উভয় পর্বের ইতিহাসচর্চার উপাদানে বিশেষ বৈচিত্র্য বিদ্যমান। বাংলার ক্ষেত্রে এই সময়ে দিল্লির সুলতানদের মতো পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে স্থানীয় ইতিহাস রচনার প্রথা গড়ে ওঠেনি। ইলিয়াস শাহী বা হোসেন শাহী সুলতানদের আমলেও এমন উদ্যোগের প্রমাণ পাওয়া যায় না। এর ফলে বাংলার মধ্যযুগীয় ইতিহাসের বহু উপাদানই সংগ্রহ করতে হয়েছে বাংলার বাইরে রচিত ইতিহাসগ্রন্থ বা বিদেশি ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে।
এই ধরনের বহিঃউৎসের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মিনহাজ-ই-সিরাজের তবকাত-ই-নাসিরী। মিনহাজ-ই-সিরাজ ছিলেন দিল্লি সুলতান (১২১০–১২৩৬) ও তাঁর উত্তরসূরিদের দরবারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদের রাজত্বকালে (১২৪৬–১২৬৬) তিনি এ গ্রন্থ রচনা করেন এবং সুলতানের মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে তাঁর নাম অনুসারে গ্রন্থের নামকরণ করেন। তবকাত-ই-নাসিরী মুসলিম বিশ্বের এক সাধারণ ইতিহাসগ্রন্থ, যাতে ২৩টি তবকাত বা অধ্যায় রয়েছে। ২২তম তবকাতে তিনি মুসলমানদের বঙ্গবিজয় থেকে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করেন।
মিনহাজ-ই-সিরাজ ছিলেন একমাত্র সমসাময়িক ঐতিহাসিক যিনি বাংলায় সরাসরি এসেছিলেন (১২৪২–১২৪৪)। তিনি বিশেষ যত্ন নিয়ে বাংলার মুসলমান শাসনের প্রাথমিক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করেন, বিশেষত বখতিয়ার খলজীর জীবিত সহযোদ্ধাদের কাছ থেকে—যেমন মুতামিদ্দৌলা—তথ্য আহরণ করেন। ফলে বঙ্গবিজয়ের প্রথম পর্যায় এবং শাসকদের কর্মকাণ্ড নিয়ে তাঁর বিবরণ আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক ও মুদ্রাতাত্ত্বিক প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত একমাত্র প্রামাণ্য সমসাময়িক দলিল।
এরপর গুরুত্বের দিক থেকে স্থান পায় জিয়াউদ্দীন বরনীর তারিখ-ই-ফিরুজশাহী। বরনী তাঁর ইতিহাসে ১২৬৬ সালে সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের সিংহাসন আরোহণ থেকে ফিরুজশাহ তুগলকের রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষ (১৩৫৭) পর্যন্ত ঘটনাবলি বর্ণনা করেছেন। অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণকারী বরনী নিজে দিল্লির দরবারে দীর্ঘদিন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং মুহম্মদ বিন তুগলকের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা হিসেবে ১৭ বছর কাজ করেন। তিনি বলবন ও প্রাথমিক খলজী সুলতানদের বিষয়ে আত্মীয়স্বজন ও দরবারি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন; বাকি সময়ের ক্ষেত্রে তিনি প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবেই বর্ণনা দেন।
বরনী কখনও বাংলায় আসেননি। বাংলার খবর তিনি সংগ্রহ করেন দিল্লির দরবারে আগত সৈনিক, কর্মকর্তাদের কাছ থেকে—যেমন তাঁর মাতামহ হিশামউদ্দীন, যিনি বাংলায় সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। তাঁর রচনাকালীন সময়ে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অশান্ত ও অনিশ্চিত, ফলে বিশদ তথ্য সংগ্রহ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই তারিখ-ই-ফিরুজশাহী-তে বাংলার বিবরণ সংক্ষিপ্ত হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা বিকৃত নয়। তবে সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতা অর্জনই যেহেতু তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তাই বিদ্রোহী বাংলার প্রতি সহানুভূতি তাঁর লেখায় অনুপস্থিত। বরং তিনি বাংলার রাজধানী লক্ষ্নৌতিকে ‘বলগাকপুর’ বা বিদ্রোহের নগর আখ্যা দিয়েছেন এবং স্বাধীন সুলতানদের সমালোচনা করেছেন। তবুও, এই গ্রন্থ মধ্যযুগীয় বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অমূল্য উৎস হিসেবে আজও গুরুত্ব বহন করে।
খাজা আবদুল মালিক ইসামী রচিত ফুতুহ-উস-সালাতীন মধ্যযুগীয় বাংলার ইতিহাস-উপাদানের এক উল্লেখযোগ্য উৎস হিসেবে বিবেচিত। বাহমনী সুলতান আলাউদ্দীন হাসানের রাজত্বকালে (১৩৪৭–১৩৫৮ খ্রি.) ১৩৪৯ খ্রিস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে রচিত এই গ্রন্থ মূলত পদ্যরূপে বিন্যস্ত। এই কাব্যধর্মী আঙ্গিকের ফলে এতে অলঙ্কারপ্রিয়তার পাশাপাশি অতিরঞ্জনের প্রবণতাও দেখা যায়, যা নিয়ে পণ্ডিতমহলে সমালোচনা রয়েছে। ইসামী নিজে কখনও বাংলায় আসেননি, কিন্তু বিস্ময়করভাবে তাঁর বিবরণে এমন কিছু তথ্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যা বরনীর তারিখ-ই-ফিরুজশাহী-তে অনুপস্থিত। অনুমান করা যায়, দিল্লির দৃষ্টিতে তখনকার দুটি বিদ্রোহী রাজ্যের মধ্যে সদ্ভাব বজায় ছিল এবং উভয় দেশের মানুষের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের পথ খোলা ছিল। এই সূত্রেই ইসামী বাংলা সম্পর্কিত কিছু নির্ভরযোগ্য উপাদান সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। তবে তুলনামূলক বিচারে, ফুতুহ-উস-সালাতীন-এ বাংলার ঘটনাবলির বিশদতা তারিখ-ই-ফিরুজশাহী-এর মতো সমৃদ্ধ নয়।
ফিরুজশাহ তুগলকের রাজত্বকালে (১৩৫১–১৩৮৮) শামস-ই-সিরাজ আফিফ রচনা করেন তারিখ-ই-ফিরুজশাহী—যা সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলির অন্যতম প্রধান দলিল। এ গ্রন্থে ফিরুজশাহের বাংলা-অভিযানগুলিরও বিবরণ রয়েছে। কিন্তু যেহেতু এই সময়ে বাংলা স্বাধীন ছিল, তাই আফিফ তাঁর পৃষ্ঠপোষক ফিরুজশাহের প্রতি অনুরাগের কারণে বাংলার সুলতানদের (ইলিয়াস শাহ ও সিকান্দর শাহ) বিরুদ্ধে অভিযানের ব্যর্থতা গোপন করেছেন। তিনি দিল্লির সুলতানের প্রশস্তি করেছেন এবং বাংলার শাসকদের ‘বিদ্রোহী’ রূপে চিত্রিত করেছেন। তবুও অন্যান্য বিষয়ে তাঁর বর্ণনা প্রায়শই নির্ভুল এবং ঐতিহাসিকভাবে সহায়ক প্রমাণিত হয়েছে। ফিরুজশাহ তুগলকের আমলের আরেকটি দলিল হচ্ছে অজ্ঞাতনামা লেখকের সিরাত-ই-ফিরুজশাহী, যদিও এতে বাংলার বিষয়ে অতি সংক্ষিপ্ত তথ্যই পাওয়া যায়।
পরবর্তী সময়ে, ইয়াহিয়া বিন আহমদ বিন আবদুল্লাহ সরহিন্দি সুলতান সৈয়দ মুবারক শাহের শাসনকালে (১৪২১–১৪৩৪) রচনা করেন তারিখ-ই-মুবারকশাহী। এতে মুহম্মদ ঘোরীর আমল থেকে শুরু করে ১৪২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লি সুলতানদের শাসনকাল ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। দিল্লিকেন্দ্রিক বর্ণনার পাশাপাশি বাংলার রাজনৈতিক ঘটনাও তিনি যথেষ্ট নির্ভুলভাবে তুলে ধরেছেন, যা মধ্যযুগীয় বঙ্গ-ইতিহাসের একটি মূল্যবান সূত্র।
মধ্যযুগীয় বাংলার ইতিহাসচর্চায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নাম আমীর খসরু। তাঁর কাব্যগ্রন্থ কিরাণ-উস-সাদাইন (অর্থাৎ “দুই নক্ষত্রের মিলন”) মূলত সাহিত্যিক রূপে রচিত হলেও, এর ভেতরে লুকিয়ে আছে এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল। ১২৮০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান বলবনের বাংলা অভিযানের সময় এবং পরে ১৩২৪–২৫ খ্রিস্টাব্দে সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুগলকের সঙ্গে তিনি বাংলায় আসেন। এর মধ্যবর্তী সময়ে (১২৮৯ খ্রি.) দিল্লির সুলতান মুইজউদ্দীন কায়কোবাদ তাঁর পিতা, বাংলার শাসক বুগরা খানের বিরুদ্ধে অভিযান চালালে আমীর খসরু তাঁকে সহগামী হন। সরযূ নদীর তীরে কায়কোবাদ ও বুগরা খানের মিলন এক গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতার জন্ম দেয়—যা কার্যত দিল্লি ও বাংলার স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্তার পারস্পরিক স্বীকৃতি নির্দেশ করে। এই ঘটনার সমসাময়িক এবং সর্বাধিক বিশদ বর্ণনা কিরাণ-উস-সাদাইন-এ সংরক্ষিত আছে। গ্রন্থটি সুলতানি দরবারের আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কেও বিস্তৃত তথ্য দেয় এবং কালানুক্রমের দিক থেকে এটি একদিকে তবকাত-ই-নাসিরী ও অন্যদিকে দুটি তারিখ-ই-ফিরুজশাহী-এর মধ্যবর্তী সময়কে যুক্ত করেছে।
ইলিয়াসশাহী আমলের পরবর্তী বৃহত্তর অংশ এবং সমগ্র হোসেনশাহী আমলে বাংলার ঘটনাবলি নিয়ে কোনো উল্লেখযোগ্য সমসাময়িক ইতিহাসগ্রন্থ রচিত হয়নি, এমনকি দিল্লিকেন্দ্রিক গ্রন্থেও বাংলার প্রসঙ্গ প্রায় অনুপস্থিত। এই শূন্যতা আংশিকভাবে পূরণ করেছে বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত, যা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস পুনর্গঠনে বিশেষ সহায়ক।
ইবনে বতুতা তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণবৃত্তান্ত রিহলা-তে ১৩৪৬–৪৭ খ্রিস্টাব্দের বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন। যদিও রাজনৈতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে তাঁর অনেক তথ্য পরে ভুল প্রমাণিত হয়েছে, তবুও সামাজিক-অর্থনৈতিক চিত্র অঙ্কনে তাঁর বিবরণ অমূল্য। তিনি নিজে বাজারে গিয়ে পণ্যের মূল্য লিপিবদ্ধ করেছেন এবং দৈনন্দিন জীবনের নানা দিক পর্যবেক্ষণ করেছেন।
চীনা ভ্রমণকারী মা হুয়ান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের আমলে (১৩৯১–১৪১০/১১) চীনা সম্রাটের দূতাবাসের দোভাষী হিসেবে বাংলায় আসেন। তাঁর বিবরণ ইং ইয়াই শেং লান পুস্তকে সংরক্ষিত, যেখানে বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা চিত্রিত হয়েছে, যদিও সুলতান বা রাজধানীর নাম উল্লেখ করা হয়নি।
১৫০৩–১৫০৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইতালীয় বণিক লুডোভিকো দ্য ভার্থেমা বাংলায় আসেন এবং ‘বাঙ্গালা’ নগরীকে এক সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে বর্ণনা করেন। একই সময়ে পর্তুগিজ বণিক দোমিঙ্গো পায়েস বা বারবোসা বাংলায় এসে নগরীর সম্পদ ও সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেন। এসব বিবরণে সুলতানি বাংলার বিশেষ করে হোসেনশাহী আমলের (১৪৯৩–১৫৩৮) অর্থনৈতিক শক্তি ও বাণিজ্যিক উন্নতির প্রতিফলন স্পষ্ট।
১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহ বাংলা জয় করলে প্রায় চার দশক (১৫৭৬ খ্রি. পর্যন্ত) বাংলা আফগান শাসনের অধীনে থাকে। এই সময়ে কয়েকজন আফগান ইতিহাসবিদ আফগান সুলতানদের রাজনৈতিক ও সামরিক কর্মকাণ্ডের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন, যা বাংলার উত্তর-মধ্যযুগীয় ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।
বাংলার আফগান শাসনপর্বের ইতিহাস পুনর্গঠনে কয়েকটি বিশেষ গ্রন্থ অমূল্য দলিল হিসেবে গণ্য হয়—যেমন আব্বাস খান সরওয়ানীর তারিখ-ই-শেরশাহী বা তোহফা-ই-আকবরশাহী, খাজা নিয়ামতউল্লাহর তারিখ-ই-খান জাহানী ওয়া মাখজান-ই-আফগানী, আহমদ ইয়াদগারের তারিখ-ই-শাহী এবং আবদুল্লাহর তারিখ-ই-দাউদী। এর মধ্যে শেষোক্ত গ্রন্থটি সম্ভবত দাউদ খান কররানীর (১৫৭২–১৫৭৬) দরবারেই রচিত হয়েছিল এবং তাই এটিকে সমসাময়িক উৎস হিসেবে বিবেচনা করা যায়। অপর তিনটি গ্রন্থ মুঘল আমলে রচিত হলেও, বাংলায় আফগান শাসনের রাজনৈতিক ও সামরিক ইতিহাস অনুধাবনের জন্য এগুলির মূল্য অপরিসীম। আব্বাস খান সরওয়ানী ও খাজা নিয়ামতউল্লাহ যথাক্রমে আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজদরবারে উচ্চপদে কর্মরত ছিলেন, যা তাঁদের রচনায় রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি এবং সাম্রাজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি উভয়ই এনে দিয়েছে।
১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে মুঘলদের হাতে বাংলা আফগান শাসনের অবসান ঘটে। এর পরবর্তী সময়ে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে বহু ইতিহাসগ্রন্থ রচিত হয়—কিছু দিল্লিতে, কিছু বাংলায় এবং আরও কিছু মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে বা এমনকি সাম্রাজ্যের বাইরেও। এই গ্রন্থগুলি অধিকাংশই ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের সাধারণ ইতিহাস, যেখানে বাংলার উল্লেখ এসেছে প্রসঙ্গক্রমে। স্বাভাবিকভাবেই, দিল্লির রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা এবং সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা বজায় রাখা ছিল এ ধরনের রচনার মূল উদ্দেশ্য। ফলত, বাংলার ঘটনাবলির বর্ণনায় প্রায়শই একপাক্ষিকতা, অতিরঞ্জন বা বাস্তববিমুখতা দেখা যায়, বিশেষত যখন লেখকরা স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান রাখতেন না।
সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬–১৬০৫) তিনটি শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয়—আবুল ফজলের আকবরনামা, নিজামউদ্দীন আহমদ বখশীর তবকাত-ই-আকবরী, এবং মোল্লা আবদুল কাদির বদাউনী রচিত মুনতাখাব-উৎ-তাওয়ারিখ। এই তিনটি গ্রন্থেই কররানী সুলতানদের (১৫৬৩–১৫৭৬) পতনের প্রেক্ষাপট এবং আকবরের বাংলা-বিজয়ের কাহিনী বিশদভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ঐতিহাসিক মানদণ্ডে এগুলিকে সমসাময়িক বিবরণ হিসেবে ধরা হয়।
আকবরনামা তিন খণ্ডে বিভক্ত—যার তৃতীয় খণ্ড আইন-ই-আকবরী এক ধরনের প্রশাসনিক গেজেটিয়ার, যেখানে সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা, রাজস্ব কাঠামো, সামরিক ও সামাজিক পরিসংখ্যান বিশদভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। ১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবরের নিকট পেশকৃত এই গ্রন্থে বাংলা সম্পর্কিত তথ্য থাকলেও, সেগুলি সর্বদা নির্ভুল নয়। আবুল ফজল সমগ্র বাংলাকে আকবরের অধীন বলে ধরে নিয়েছিলেন, যা বাস্তবে সত্য ছিল না। তাঁর রাজস্ব ও প্রশাসনিক বিভাগের বর্ণনা আপাতদৃষ্টিতে সুশৃঙ্খল মনে হলেও, বাস্তবের সঙ্গে তা বহু ক্ষেত্রে অসঙ্গত। পূর্ব বাংলার বারো ভূঁইয়ার নেতা ঈসা খান সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যও বিভ্রান্তিকর ও পরস্পরবিরোধী।
অন্যদিকে, তবকাত-ই-আকবরী বাংলার ইতিহাসের দিক থেকে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। ১৫৯২–৯৩ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত এই সাধারণ ইতিহাসগ্রন্থে গজনীয় যুগ থেকে শুরু করে আকবরের রাজত্বের ৩৬তম বছর পর্যন্ত ঘটনা ধারাবাহিকভাবে স্থান পেয়েছে। বাংলার মুসলিম শাসকদের নিয়ে একটি বিশেষ অধ্যায়ে প্রাক-মুঘল যুগের বিশদ বিবরণ রয়েছে, যেখানে দাউদ খান কররানীর সঙ্গে আকবরের যুদ্ধের বর্ণনা তথ্যনির্ভর ও সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বদাউনী তাঁর মুনতাখাব-উৎ-তাওয়ারিখ-এ দিল্লির সুলতানদের ইতিহাস বর্ণনার পাশাপাশি বাংলার ঘটনাবলিও উল্লেখ করেছেন।
আবুল কাসিম ফিরিশতা (১৫৭০–১৬২৩) রচিত তারিখ-ই-ফিরিশতা বাংলার ঘটনাবলির জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বিজাপুরের ইবরাহিম আদিল শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত এই গ্রন্থে লেখক নিজে সারা ভারত ভ্রমণ করে মৌলিক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। ভূমিকা, বারোটি অধ্যায় ও উপসংহারে বিভক্ত এই ইতিহাসগ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে বাংলা ও বিহারের সুলতানদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। ফিরিশতা এখানে হাজী মুহম্মদ সাফাহারির একটি পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেছেন বলে উল্লেখ করেন, যা তাঁর বিবরণকে আরও প্রামাণ্য করে তুলেছে।
বাংলায় অবস্থানরত কয়েকজন মুঘল কর্মকর্তা তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্থানীয় জীবন, সমাজ এবং রাজনৈতিক ঘটনার উপর ইতিহাস রচনা করেছিলেন। কিছু গ্রন্থ সাধারণ ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হলেও, কিছু স্পষ্টতই প্রাদেশিক ইতিহাস হিসেবে বিবেচিত। মুহম্মদ সাদিকের সুবহ-ই-সাদিক গ্রন্থে মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃত ইতিহাসের ভেতরে বাংলারও উল্লেখ রয়েছে।
তবে বাংলার মধ্যযুগীয় ইতিহাসচর্চায় যে দুজন মুঘল যুগের ইতিহাসকার বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার, তারা হলেন মির্জা নাথান ও শিহাবউদ্দীন তালিশ। মির্জা নাথানের বাহারিস্তান-ই-গায়েবী এবং তালিশের আজিবা-ই-গরীবা (যা ফতোয়া-ই-ইবরিয়া নামেও পরিচিত) ও তারিখ-ই-মুলক-আসাম—এই তিনটি রচনা বাংলার রাজনৈতিক, সামরিক এবং সামাজিক ইতিহাসের প্রত্যক্ষ ও নিরপেক্ষ দলিল।
মির্জা নাথান এক ইরানি বংশোদ্ভূত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মালিক আলী (ইহতিমাম খান) সম্রাট আকবরের আমলে ২৫০ অশ্বারোহীর সেনাপতি এবং কিছুদিন আগ্রার কোতোয়াল ছিলেন। ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁকে বাংলার নৌবাহিনীর প্রধান (মীর বহর) পদে নিযুক্ত করেন। যুবক মির্জা নাথানও নৌবাহিনীতে পিতার সহকারী হিসেবে যোগ দেন এবং বাংলার বারো ভূঁইয়া, মগ জলদস্যু ও ফিরিঙ্গি আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধে অংশ নেন। তিনি শুধু অংশগ্রহণই করেননি, বরং বহু অভিযানে সরাসরি নেতৃত্ব দিয়েছেন।
বাংলায় কর্মরত অবস্থায়ই মির্জা নাথান তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থ সংকলন শুরু করেন। তিনি ‘গায়েবী’ ছদ্মনাম গ্রহণ করে গ্রন্থটির নাম দেন বাহারিস্তান-ই-গায়েবী। জাহাঙ্গীরের শাসনামলে (১৬০৫–১৬২৭) বাংলা ও আসামে যে সকল ঘটনায় তিনি প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন, তার সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি কেবল নিজের দেখা ও অভিজ্ঞ ঘটনারই বিবরণ দিয়েছেন—যা এটিকে মধ্যযুগীয় বাংলার অন্যতম নির্ভরযোগ্য সমসাময়িক উৎসে পরিণত করেছে।
বাহারিস্তান-ই-গায়েবী এমন এক অনন্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ, যেখানে বাংলার সুবাহদার ইসলাম খানের নিযুক্তি (১৬০৮ খ্রি.) থেকে শুরু করে ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহী শাহজাদা শাহজাহানের আকবরমহল ত্যাগ পর্যন্ত প্রায় আঠারো বছরের বিস্তৃত ঘটনাপ্রবাহ ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়কালে বাংলায় পর্যায়ক্রমে তিনজন সুবাহদারের শাসনকাল এবং শাহজাহানের অবস্থানকে ভিত্তি করে গ্রন্থটি চারটি খণ্ডে বিভক্ত—(১) ইসলামনামা, (২) কাসিমনামা, (৩) ইবরাহিমনামা এবং (৪) ওয়াকিয়াত-ই-জাহানশাহী। গ্রন্থকার প্রথম তিন খণ্ড রচনা সমাপ্ত করেন শাহজাহানের রাজত্বের পঞ্চম বছরে (১৬৩২ খ্রি.), এবং চতুর্থ খণ্ডও সম্ভবত একই সময়ে সংকলিত হয়।
মির্জা নাথানের এই রচনা মূলত ব্যক্তিগত স্মৃতিকথার আকারে গড়ে উঠেছে। তিনি প্রায় দুই দশক বাংলায় কর্মরত থেকে এ প্রদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, প্রাকৃতিক পরিবেশ, রাজনৈতিক অবস্থা, প্রশাসনিক কাঠামো এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। বাংলায় তাঁর কর্মকালের সামরিক অভিযানসমূহ—বারো ভূঁইয়া দমন, মগ ও ফিরিঙ্গিদের প্রতিরোধ, সীমান্ত প্রতিরক্ষা—সবই তিনি সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। এতে সমকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতা, মুগল প্রশাসনিক কৌশল এবং প্রাদেশিক ক্ষমতার প্রতিযোগিতা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এর মাধ্যমে জাহাঙ্গীর শাসনামলে বাংলার ইতিহাসে যে বিরাট শূন্যতা ছিল, তা পূর্ণ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এর আগে বাংলার ইতিহাসকে এভাবে ধারাবাহিক রূপ দেওয়ার কোনো প্রচেষ্টা দেখা যায়নি; অন্যান্য ঐতিহাসিকরা সাম্রাজ্যের সাধারণ ইতিহাসে বিচ্ছিন্নভাবে বাংলার প্রসঙ্গ তুলেছিলেন মাত্র।
তবে মির্জা নাথান, একজন মুঘল কর্মকর্তা হিসেবে, রাজদরবারের দৃষ্টিভঙ্গি ও আনুগত্যের সীমাবদ্ধতা পুরোপুরি এড়াতে পারেননি। তবুও বাহারিস্তান-ই-গায়েবী বাংলার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা, আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক রীতি ও কুসংস্কার, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং প্রাদেশিক স্বকীয়তা সম্পর্কে সমৃদ্ধ তথ্যভাণ্ডার হিসেবে অপরিসীম মূল্য বহন করে।
যেখানে বাহারিস্তান-ই-গায়েবী-র বিবরণ শেষ হয়, সেখান থেকেই শুরু মুহম্মদ সাদিকের সুবহ্-ই-সাদিক। ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে নবনিযুক্ত সুবাহদার কাসিম খান জুইনির সঙ্গে ওয়াকিয়ানবিশ (সংবাদলেখক) হিসেবে বাংলায় আগমন করেন সাদিক এবং ১৬৩৯ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ শাহ শুজার সুবাহদারি শুরুর আগ পর্যন্ত, তিনি বাংলায় অবস্থান করেন। বহু বছর তিনি জাহাঙ্গীরনগরে (ঢাকা) বসবাস করেন এবং ১৬৩৭–৩৮ খ্রিস্টাব্দে মুঘলদের কোচ-হাজো অভিযানে সরাসরি অংশ নেন।
সাদিক ছিলেন বহুশিক্ষিত ও পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ব্যক্তি। বিশ্বের ইতিহাস ও ভূগোল গ্রন্থাকারে উপস্থাপনের বৃহৎ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তিনি সুবহ্-ই-সাদিক রচনা করেন, যা চার খণ্ডে বিভক্ত। তৃতীয় খণ্ডের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে রয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে লেখা বাংলার ঘটনা। সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনাবলির পাশাপাশি তিনি বাংলার বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন, অভিজাত শ্রেণির রুচি ও আচরণ, এমনকি সাম্প্রদায়িক ও বিদেশি প্রভাব সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। বিশেষভাবে তিনি উল্লেখ করেছেন শাহ শুজার সুবাহদারি আমলে (১৬৩৯–১৬৬০) পারস্য থেকে বিপুলসংখ্যক শিয়া অভিজাত ব্যক্তির বাংলায় আগমনের কথা, যা প্রাদেশিক সমাজ ও সংস্কৃতিতে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।
শাহ শুজার শাসনকালকে কেন্দ্র করে আরেকটি বিশেষ ঐতিহাসিক দলিল হলো মুহম্মদ মাসুম রচিত তারিখ-ই-শাহ শুজাই। শিহাবউদ্দীন মুহম্মদ তালিশ, যিনি মীর জুমলার সুবাহদারি আমলে (১৬৬০–১৬৬৩) বাংলায় উচ্চপদে কর্মরত ছিলেন, তাঁর আজিবা-ই-গরীবা-তে এই বিবরণের আংশিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন। তালিশ মীর জুমলার আসাম অভিযানে সরাসরি অংশ নেন এবং পরবর্তীতে শায়েস্তা খানের সুবাহদারি (১৬৬৪–১৬৭৮ ও ১৬৭৯–১৬৮৮) আমলের বিশেষত ১৬৬৬ সালের চট্টগ্রাম বিজয়ের ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর রচনা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করায় সমকালীন বাংলার ইতিহাসের জন্য এটি এক অনন্য মূল্যবান উৎস। এতে রাজনৈতিক ঘটনাবলির পাশাপাশি বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার দিকেও তিনি সমান মনোযোগ দিয়েছেন।
আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর (১৭০৭) পরবর্তী সময়ে বাংলার শাসক বা নওয়াবদের নিয়ে একাধিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয়, যার অধিকাংশই ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভিক পর্বে, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে। এই গ্রন্থকারেরা প্রায় সকলেই ছিলেন বাংলার শাসকদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী বা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, এবং তাঁরা বর্ণিত বহু ঘটনার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী।
এই ধারার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো আজাদ হোসেনের নওবাহার-ই-মুর্শিদকুলী খানী। আজাদ হোসেন ছিলেন পারস্য-অভিবাসী এক বিদ্বান, যিনি জাহাঙ্গীরনগরে স্থায়ী হন। তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক মির্জা লুৎফুল্লাহ্—দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খান রুস্তম জঙ্গ—এর উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি রচনা করেন। মির্জা লুৎফুল্লাহ্ ছিলেন নওয়াব শুজাউদ্দীনের (১৭২৮–১৭৩৯) জামাতা এবং ১৭২৮ থেকে জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাজিম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, পরে তাঁকে উড়িষ্যায় বদলি করা হয়। গ্রন্থে সুবাহদার ও নওয়াবদের জীবনী, পরামর্শ এবং রাজনৈতিক কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে, যা মুসলিম শাসনামলে বাংলার দরবারি সংস্কৃতি, সামাজিক শিষ্টাচার ও পরিশীলিত রুচির একটি জীবন্ত প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে।
এরপর ইউসুফ আলী—যিনি আলীবর্দী খানের বিশ্বস্ত সহযোগী, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং নওয়াব সরফরাজ খানের (১৭৩৯–১৭৪০) জামাতা—তাঁর মনিব আলীবর্দী খানের (১৭৪০–১৭৫৬) রাজত্বকাল নিয়ে ইতিহাস রচনা করেন। পরবর্তীতে তিনি নওয়াব মীর কাসিমের (১৭৬০–১৭৬৪) অধীনে কাজ করেন। ১৭৬৩ সালের নভেম্বরে ইংরেজদের হাতে পাটনা পতনের পর মীর কাসিমের সঙ্গে বিহার থেকে এলাহাবাদে পালিয়ে যান, যদিও পরে অসুস্থতার অজুহাতে তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হন। তিনি পুনরায় মীর জাফরের অনুগ্রহভাজন হতে ব্যর্থ হন, তবে মীর জাফরের মৃত্যু (১৭৬৫) তাঁর ব্যক্তিগত বিপদকালের অবসান ঘটায়।
ইউসুফ আলী তাঁর গ্রন্থ সমাপ্ত করতে পারেননি এবং কোনো শিরোনামও দেননি। পরবর্তীতে ঐতিহাসিকরা একে আহওয়াল-ই-মহববত জং নামে অভিহিত করেন। এতে মূলত আলীবর্দী খানের কর্মজীবন ও রাজত্বের বিবরণ রয়েছে, যদিও মাঝে মাঝে শাহ শুজা ও সরফরাজ খানের শাসনকালের ঘটনাও তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি ১৭৪২ সাল পর্যন্ত আলীবর্দীর শাসনের বিস্তারিত, তথ্যনির্ভর বিবরণ দিয়েছেন। গ্রন্থের অসম্পূর্ণতার জন্য তিনি দায়ী করেছেন বিভিন্ন প্রতিকূলতাকে—যেমন মীর কাসিমের পরাজয় ও পলায়ন, তাঁর বৃদ্ধ পিতার মৃত্যু, এলাহাবাদে নিজ অসুস্থতা, মীর জাফরের বিরূপ মনোভাব, এবং সরকারি দলিলপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহে বাধা।
ইউসুফ আলী তাঁর গ্রন্থে নওয়াব আলীবর্দী খানের শাসনকালের ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দ পরবর্তী ঘটনাবলি প্রধানত স্মৃতিনির্ভরভাবে বর্ণনা করেছেন। ফলে এই অংশে বিবরণ তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত এবং বহু ক্ষেত্রে ঘটনার তারিখ নিয়ে অসঙ্গতি দেখা যায়—যা এমন পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও, পূর্ববর্তী অংশের মতোই এই অংশেও তিনি বর্ণনার বিশ্বস্ততা ও মান বজায় রেখেছেন। এই নিরপেক্ষতা ও প্রামাণিকতা তাঁর ইতিহাসকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেছে। সমকালীন ইতিহাসকাররাও তাঁর কাজের প্রশংসা করেছেন। গোলাম হুসেন তাবাতাবাঈ তাঁর সিয়ার-উল-মুতাখেরীন গ্রন্থে প্রায়ই ইউসুফ আলীর ইতিহাসের উল্লেখ করেছেন এবং বহু ক্ষেত্রে আহওয়াল-ই-মহববত জং-এর বিবরণ হুবহু অনুসরণ করেছেন।
আলীবর্দী খানের আত্মীয় করম আলী বাংলার নায়েব দীউয়ান মুহম্মদ রেজা খান মুজাফফর জং-এর পৃষ্ঠপোষকতায় মুজাফফরনামা রচনা করেন। রেজা খান ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। করম আলীর বর্ণনা ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয়ে তাঁর নিজ সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে তিনি ছিলেন সিরাজউদ্দৌলার খালাতো ভাই ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী শওকত জঙ্গ-এর সমর্থক; ফলে সিরাজউদ্দৌলার প্রতি তাঁর গ্রন্থে সুস্পষ্ট পক্ষপাত দেখা যায় এবং এর মূল্যায়নে এ দিকটি বিবেচনায় নিতে হয়।
গভর্নর হেনরি ভ্যান্সিটাটের (১৭৬০–১৭৬৪) নির্দেশে সলিমুল্লাহ তাওয়ারিখ-ই-বাঙ্গালা নামে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করেন। এতে সুবাহদার ইবরাহিম খানের (১৬৮৯–১৬৯৭) সময় থেকে আলীবর্দী খানের মৃত্যু (১৭৫৬) পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। বিশেষত মুর্শিদকুলী খান ও আলীবর্দী খানের কর্মজীবন, রাজস্বব্যবস্থা ও প্রশাসনিক নীতি সম্পর্কে এই গ্রন্থটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। যদিও এর কালানুক্রমে কিছু ত্রুটি রয়েছে এবং কিছু বিবরণ পরস্পরবিরোধী, তবুও সামাজিক জীবন ও অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কিত তথ্যের জন্য এটি অমূল্য।
আলীবর্দী খানের রাজত্বকালের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দলিল হলো ওয়াকিয়াত-ই-ফতেহ্ বাঙ্গালা, যা ওয়াকিয়াত-ই-মহববত জং নামেও পরিচিত। নওয়াবের আত্মীয় মুহম্মদ ওয়াফা এটি রচনা করেন। আলীবর্দীর অধীনে কর্মরত থাকার কারণে তিনি তাঁর প্রভুর প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়েছেন এবং গ্রন্থে স্পষ্ট স্তাবকসুলভ মনোভাব দেখা যায়।
আঠারো শতকের শেষভাগে মালদহের এক শিক্ষক ইলাহি বখশ খুরশীদ জাহান নুমা নামে একটি সাধারণ ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটির বহু গুরুত্বপূর্ণ অংশ ইংরেজ অনুবাদক হেনরি বেভারিজ অনুবাদ করে ১৮৯৫ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি–এর জার্নালের ৬৪তম খণ্ডে প্রকাশ করেন। বাংলার সামাজিক ইতিহাস পুনর্গঠনে এই গ্রন্থও সহায়ক।
এ সময়ে রচিত সর্বাধিক বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ইতিহাসগ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম হলো গোলাম হুসেন তাবাতাবাঈ-র সিয়ার-উল-মুতাখেরীন। তাঁকে প্রায়শই মুসলিম ভারতের শেষ শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক বলা হয়। তাঁর শিক্ষা, পারিবারিক সংযোগ ও বহুমুখী অভিজ্ঞতা তাঁকে এক অসাধারণ ইতিহাসবিদে পরিণত করেছিল। তাঁর পিতা হিদায়েত আলী খান দিল্লি ও আজিমাবাদের (পাটনা) শাহী দরবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন; আত্মীয়স্বজনেরা আলীবর্দী খানের অধীনে উচ্চপদে চাকরি করেছেন। তাবাতাবাঈ নিজেও আলীবর্দীর আত্মীয় ছিলেন এবং তাঁর সরকারে ও উত্তরাধিকারীদের আমলেও দায়িত্ব পালন করেন। দিল্লি, আজিমাবাদ, অযোধ্যা, মুর্শিদাবাদ, পূর্ণিয়া প্রভৃতি প্রশাসনিক কেন্দ্রে বাস করে তিনি তৎকালীন রাজনীতির প্রধান ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসেন এবং ঘটনাবলির প্রত্যক্ষ সাক্ষী হন।
তিনি শাহজাদা আলী গওহরের (পরবর্তী সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম) দরবারে রামনারায়ণের অধীনে, মীর কাসিমের দরবারে মেজর কার্ণার্কের সঙ্গে এবং পরে পুনরায় ইংরেজ শাসনে মীর কাসিমের দূত হিসেবে কাজ করেছেন। এর ফলে তিনি ইংরেজ, মারাঠা, আওধ ও অন্যান্য সমসাময়িক শক্তির কর্মকাণ্ড নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, পারিবারিক রাজনৈতিক সংযোগ এবং নথিপত্রে প্রবেশাধিকার মিলিয়ে তাঁর ইতিহাসে অদ্বিতীয় প্রামাণিকতা এসেছে।
সিয়ার-উল-মুতাখেরীন তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে প্রাচীনকাল থেকে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল পর্যন্ত উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ড শুরু হয়েছে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরবর্তী সময় থেকে; এতে তাঁর উত্তরাধিকারীদের রাজনীতি, মুর্শিদাবাদ নিজামতের উত্থান, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় ইংরেজ আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা, এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসনিক ও আইন কাঠামো বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে দ্বিতীয় শাহ আলমের আমলের ঘটনা, অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ, হায়দার আলী ও মারাঠাদের বিষয় এবং নওয়াব মীর কাসিমের মৃত্যুর বিবরণ রয়েছে; এটি ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজ কর্মকাণ্ডের ইতিহাস দিয়ে সমাপ্ত। এম. রেমন্ড নামক এক ফরাসি, ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর হাজী মুস্তফা নামে পরিচিত, দ্বিতীয় খণ্ডের অধিকাংশ ফারসি থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ বক্সারের যুদ্ধ (২২ অক্টোবর ১৭৬৪)–পরবর্তী ইংরেজ-শুজাউদ্দৌলা সন্ধির বর্ণনার মধ্য দিয়ে শেষ হয়।
গোলাম হুসেন তাবাতাবাঈ ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। তাঁর কাছে ইতিহাস ছিল কেবল অতীতের দলিল নয়, বরং অভিজ্ঞতা, শিক্ষা এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ভাণ্ডার। তিনি আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকে তাঁর নিজ সময় পর্যন্ত ইতিহাসের শূন্যতা পূরণে সচেষ্ট হন। তাঁর নিজের বক্তব্য অনুযায়ী, তিনি হিংসা, অনুগ্রহ বা ভয়ের প্রভাবমুক্ত থেকে সত্য ঘটনা তুলে ধরেছেন এবং পক্ষপাত এড়ানোর চেষ্টা করেছেন। এই নিরপেক্ষতা ও নির্ভুলতার কারণেই তিনি মুসলিম ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারক হিসেবে স্বীকৃত।
সিয়ার-উল-মুতাখেরীন-এর প্রথম খণ্ড মূলত আকবরনামা, আইন-ই-আকবরী এবং আরও কয়েকটি পূর্ববর্তী ইতিহাসগ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্তসার ও অনুলিপি—ফলে এই অংশে গোলাম হুসেন তাবাতাবাঈকে কোনো মৌলিকত্বের দাবি দেওয়া যায় না। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই দুই খণ্ডে ১৭০৭ থেকে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের বিশদ ইতিহাস স্থান পেয়েছে—একটি এমন সময়কাল, বিশেষত বাংলার নিজামত সম্পর্কিত ঘটনাবলি, যার সমপর্যায়ের অন্য কোনো পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক দলিল তৎকালীন সময়ে বিদ্যমান ছিল না। এই দিক থেকে তিনি বাংলার ইতিহাসের এক বিরাট শূন্যতা পূরণ করেছেন।
তবু গোলাম হুসেনের এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ কিছু সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত নয়। একজন কূটনৈতিক দূত হিসেবে তিনি প্রায়শই অবিশ্বস্ত ও দায়সারা মনোভাব প্রদর্শন করেছেন। ইতিহাসের সূত্রে আমরা জানতে পারি, তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ী রামনারায়ণ এবং মীর কাসিমের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন এবং তাঁদের বহু গোপন তথ্য ইংরেজদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাঁর লেখনী থেকেই স্পষ্ট হয় যে, নওয়াব মীর কাসিমের গোপন পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি ইংরেজদের আগাম সতর্ক করেছিলেন এবং এই কাজকে তিনি নিজের গর্বের বিষয় মনে করতেন। নিজের স্বার্থে ও ইংরেজদের অনুগ্রহ লাভের লক্ষ্যে তিনি এমনকি নিজের মনিব ও জাতির ক্ষতিও সাধন করেছিলেন। তাঁর বিবরণে নওয়াব সিরাজউদ্দৌলার প্রতি গভীর বৈরিতাও প্রকাশ পেয়েছে। বাস্তবে গোলাম হুসেন ছিলেন এক ইংরেজপন্থী ঐতিহাসিক, যিনি নতুন শাসক ইংরেজদের স্বাগত জানিয়েছেন, তাঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন এবং তাঁদের নীতি ও কর্মকাণ্ডের ন্যায্যতা জোর দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন।
এসব রাজনৈতিক পক্ষপাত সত্ত্বেও সিয়ার-উল-মুতাখেরীন বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক অসাধারণ তথ্যভাণ্ডার। এখানে সেকালের সমাজজীবনের নানা দিক উন্মোচিত হয়েছে—যেমন ক্রমশ অবক্ষয়প্রবণ সামাজিক রীতি, উৎসব-অনুষ্ঠান, শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। তিনি আজিমাবাদ ও মুর্শিদাবাদের সাংস্কৃতিক জীবনের সমৃদ্ধ চিত্র অঙ্কন করেছেন এবং রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিকশিত বহু পণ্ডিত, কবি, চিকিৎসক, ধর্মতত্ত্ববিদ ও জ্ঞানী ব্যক্তির নামও সংরক্ষণ করেছেন।
গোলাম হুসেন সেলিম জায়েদপুরী রচিত রিয়াজ-উস-সালাতীন বাংলার মুসলমানদের উপর রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসগ্রন্থ হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সেলিম ছিলেন আঠারো শতকের আশির দশকে মালদহে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক প্রতিনিধি জর্জ উডনির অধীনে কর্মরত ডাকমুন্সী। উডনির অনুরোধেই তিনি ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটি সম্পন্ন করেন। এর রচনায় তিনি তবকাত-ই-নাসিরী, তারিখ-ই-ফিরুজশাহী এবং অন্যান্য মুঘল ঐতিহাসিকদের গ্রন্থাবলির পাশাপাশি বহু স্বল্পপরিচিত এবং আজ আর প্রাপ্তিযোগ্য নয় এমন উৎস ব্যবহার করেছেন। এছাড়া তিনি গৌড় ও পান্ডুয়ার প্রাচীন শিলালিপি এবং স্থাপত্যাবশেষ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করেছেন।
গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদক আবদুস সালাম (১৯০৫) যথার্থভাবেই গোলাম হুসেন সেলিমকে “মুসলিম বাংলার অগ্রগণ্য ঐতিহাসিক” আখ্যা দিয়েছেন। মধ্যযুগীয় বাংলার ইতিহাসচর্চায় প্রথম সারির পণ্ডিতেরা বরাবরই রিয়াজকে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচনা করেছেন। চার্লস স্টুয়ার্ট তাঁর হিস্ট্রি অব বেঙ্গল (১৮১৩) গ্রন্থে বহু অংশ রিয়াজ-এর উপর ভিত্তি করে রচনা করেন। হেনরি ফার্ডিনান্ড ব্লকম্যান এটিকে ফারসি ভাষায় রচিত বাংলার মুসলমানদের ইতিহাসের সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যদিও বর্তমান কালে আবিষ্কৃত কিছু মুদ্রা ও শিলালিপির আলোকে রিয়াজ-এর কিছু তারিখ ও তথ্য সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, তবুও এর গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ।
সমস্ত আলোচনার নির্যাসে বলা যায়—মুঘল বিজয়ের পূর্বে বাংলার ভৌগোলিক সীমানার ভেতরে কোনো প্রমাণযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থ রচিত হয়েছিল বলে জানা যায় না। মুঘল আমলে এ প্রদেশে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের রচনায় বাংলার বহু ঘটনাবলি সংরক্ষিত হলেও সেগুলি প্রায়ই সাম্রাজ্যকেন্দ্রিক ছিল। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক, অর্থাৎ ব্রিটিশ যুগে উত্তরণের প্রাক্কালে বাংলার বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত মাত্র কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসগ্রন্থ রচিত হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, এই দীর্ঘ সময়ের ইতিহাস রচনায় আমরা থুকিডাইডিসের নির্দেশিত উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত, সত্য উদঘাটনে কঠোর বিশ্লেষণপ্রবণ, কিংবা পলিবিয়াসের দৃষ্টিতে ঘটনাবলির ন্যায়সংগত মূল্যায়নকারী কোনো ইতিহাসবিদ পাই না। এই সময়ে রচিত অধিকাংশ গ্রন্থকে আমরা কেবল ঘটনাবলির প্রাথমিক উৎস হিসেবে গ্রহণ করতে পারি; আধুনিক গবেষণাপদ্ধতি ও প্রমাণনির্ভর বিশ্লেষণ প্রয়োগের মাধ্যমেই আমরা মধ্যযুগীয় বাংলার প্রকৃত ও নির্ভুল ইতিহাসের রূপরেখা নির্মাণ করতে পারি।
নিম্নে সুলতানি শাসন পর্বের ইতিহাস চর্চার উপাদানসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করা হলোঃ
সুলতানি যুগের উপাদানসমূহ
ভারত বিজয়ী তুর্কি মুসলমানরা কেবল অস্ত্রের শক্তি ও যুদ্ধজয়ের অভিজ্ঞতা নিয়েই উপমহাদেশে প্রবেশ করেননি, তাঁরা সঙ্গে এনেছিলেন তাঁদের দীর্ঘদিনের সমৃদ্ধ ইতিহাসরচনার ঐতিহ্যও। অতীত রক্ষার এই চর্চা তাঁদের সভ্যতার অন্তর্গত ছিল, যা তাঁরা এখানে প্রতিষ্ঠা ও বিকশিত করেন। ফলে মুসলিম শাসনের সূচনা থেকে পতন পর্যন্ত পুরো সময়কালকে ধারণ করে এমন বিপুল সংখ্যক দলিল, ঘটনাপঞ্জি ও রেকর্ড রয়ে গেছে, যা মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাস নির্মাণে এক অমূল্য ভাণ্ডার হয়ে উঠেছে। শুধু রাজনৈতিক ইতিহাস নয়—সমসাময়িক সাহিত্য, বিদেশি পর্যটকের পর্যবেক্ষণমূলক বিবরণ, এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন—সব মিলেই গড়ে উঠেছে সুলতানি যুগের এক বহুমাত্রিক চিত্র।
সুলতানি যুগের ইতিহাস রচনার উৎসসমূহ সাধারণভাবে চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—
১. সমসাময়িক ইতিহাসগ্রন্থ,
২. সমসাময়িক সাহিত্য,
৩. বিদেশি পর্যটকের বিবরণ,
৪. প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্র।
১. সমসাময়িক ইতিহাসগ্রন্থ
প্রথমত, সমসাময়িক ইতিহাসগ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন এবং তাৎপর্যপূর্ণ নিদর্শন হলো আবু রায়হান আল বেরুনীর কিতাব-উল-হিন্দ। আল বেরুনী ছিলেন গজনির সুলতান মাহমুদের সভাসদ, যিনি পাঞ্জাব জয়ের সময় গজনি থেকে ভারতে আসেন। তিনি কেবল একজন ইতিহাসবিদ নন—তিনি ছিলেন গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ, চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ এবং ভাষাতত্ত্বজ্ঞ, যাঁর জ্ঞানান্বেষণ তাকে ভারতীয় পণ্ডিতদের নিকটবর্তী করে তোলে। সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করে তিনি ভারতীয় দর্শন, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির গভীরে প্রবেশ করেন। তাঁর রচিত কিতাব-উল-হিন্দ কেবল একটি রাজনৈতিক ইতিহাস নয়, বরং সমকালীন ভারতের সামাজিক কাঠামো, ধর্মীয় আচার, ভাষা-সাহিত্য, অর্থনীতি এবং সাংস্কৃতিক জীবনের এক অনন্য দলিল। এতে মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজের নিখুঁত ও নিরপেক্ষ চিত্র ফুটে উঠেছে, যা আজও ইতিহাসবিদদের জন্য অপরিহার্য।
মুসলমানদের ইতিহাসচর্চা আরব সমাজেই নবযুগ লাভ করে। হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী, হাদিসসংগ্রহ এবং প্রাথমিক ইসলামী বিজয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে এই ধারা বিকশিত হয়। আরবীয় ঐতিহাসিকরা কেবল যুদ্ধের বিবরণই দেননি, তাঁরা সমাজের রীতি-নীতি, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং রাষ্ট্রপরিচালনার নানা দিকও নথিবদ্ধ করেছেন। এই ধারার উত্তরসূরি হিসেবেই আবু রায়হান আল বেরুনী মধ্যযুগীয় ভারতীয় বাস্তবতাকে লিপিবদ্ধ করেছেন।
৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ইরানের উত্তরাঞ্চলের খারিজম রাজ্যে জন্মগ্রহণকারী আল বেরুনী শৈশব থেকেই অদ্ভুত মেধা ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দেন। তাঁর শিক্ষাজীবনের বড় একটি অংশ কেটেছে খিরাম অঞ্চলে। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি চলে আসেন তাবারিস্তানে, যা তখন শাসন করতেন জ্ঞানপৃষ্ঠপোষক শামসুল মাআলি কাবুম। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় তাবারিস্তান হয়ে ওঠে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এখানে আল বেরুনীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক, চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী ইবনে সিনা।
মধ্যযুগীয় শাসকরা জ্ঞানী পণ্ডিতদের গুরুত্ব উপলব্ধি করলেও তাঁদের প্রভাবকে শঙ্কার চোখে দেখতেন, কারণ এঁরা প্রায়ই শাসকের উপদেষ্টা হয়ে নীতিনির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করতেন। গজনীর সুলতান মাহমুদ তাবারিস্তানের বহু পণ্ডিতকে তাঁর দরবারে নিয়ে আসেন। ইবনে সিনা এই আহ্বান এড়িয়ে গেলেও আল বেরুনী গজনীতে আসেন এবং সুলতান মাহমুদের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী হন। মাহমুদের ধারাবাহিক ভারত অভিযানে তিনি সহযাত্রী হয়ে বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শনের সুযোগ পান। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁকে ভারতীয় ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন এবং সমাজব্যবস্থার গভীর অন্তর্দৃষ্টি দেয়।
সুলতান মাহমুদের নির্দেশে আল বেরুনী ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থা, সামাজিক প্রথা, ধর্মীয় বিশ্বাস, সাহিত্য, শিল্প, জ্ঞানচর্চা এবং জনগণের দৈনন্দিন জীবনের নিখুঁত বিবরণ সংগ্রহ করেন। প্রায় দুই দশকের নিরবচ্ছিন্ন গবেষণার ফলস্বরূপ ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে, মাহমুদের মৃত্যুর কিছু পরেই, তিনি কিতাব-উল-হিন্দ সম্পন্ন করেন। অধিকাংশ গবেষকের মতে, আল বেরুনীর মৃত্যু হয় ১০৫০ খ্রিস্টাব্দে, যদিও কিছু সূত্র ১০৪৮ খ্রিস্টাব্দকেও সম্ভাব্য মৃত্যুসাল হিসেবে উল্লেখ করেছে। আবু মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহর নির্ধারিত ১০৫০ খ্রিস্টাব্দের তারিখটিই বর্তমানে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য। এই গ্রন্থটি শুধু তথ্যবহুল নয়, এতে তাঁর গভীর জ্ঞান, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি এবং বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। আল বেরুনী আবেগের অতিরঞ্জন বা পক্ষপাত এড়িয়ে একজন অনুসন্ধানী পর্যবেক্ষকের নিরপেক্ষতায় ভারতকে উপস্থাপন করেছেন—যা তাঁর সময়ে বিরল গুণ। তাঁর রচনার ভঙ্গি এবং বিশ্লেষণক্ষমতা তাঁকে কেবল মুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যেই নয়, বিশ্ব ইতিহাসচর্চার ধারাতেও অনন্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে।
মধ্যযুগীয় শাসকদের মনে পণ্ডিতদের প্রতি একধরনের দ্বৈত অনুভূতি কাজ করত—একদিকে তাঁদের জ্ঞানের জন্য শ্রদ্ধা, অন্যদিকে রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে ভীতি। কারণ, রাজ্য জয় ও শাসন পরিচালনার সূক্ষ্ম কূটনীতি প্রণয়নে এই পণ্ডিতরাই প্রায়শই প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। গজনীর সুলতান মাহমুদের শাসনকালে এই প্রবণতা সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। তিনি তাবারিস্তানের সব পণ্ডিতকে গজনীতে নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। অনেকে, যেমন ইবনে সিনা, রাজনৈতিক কারণে বা স্বাধীন চেতনার প্রেরণায় এই আহ্বান এড়িয়ে যান; কিন্তু আবু রায়হান আল বেরুনী আহ্বান গ্রহণ করে গজনীতে উপস্থিত হন।
সুলতান মাহমুদ তখন ধারাবাহিকভাবে ভারত অভিযানে ব্যস্ত। তিনি আল বেরুনীকে কেবল একজন সভাসদ হিসেবেই নয়, বরং এক বিশেষ গবেষক হিসেবে সঙ্গী করেন। তাঁর নির্দেশ ছিল—ভারতবর্ষের মানুষ, সমাজ, জীবনধারা, জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা, দর্শন ও ধর্মীয় রীতি, ভাষা ও সাহিত্য বিকাশ, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সম্পর্কে যতদূর সম্ভব বিস্তৃত ও প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহ করা এবং সেসব লিখিত আকারে তাঁর নিকট পেশ করা। আল বেরুনী এই দায়িত্ব গ্রহণ করে বছরের পর বছর গভীর মনোযোগে গবেষণায় নিমগ্ন থাকেন। তাঁর জ্ঞানের তৃষ্ণা তাঁকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল, মন্দির, পুঁথিশালা, এবং পণ্ডিতসমাজে নিয়ে যায়।
১০৩০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর প্রায় পাঁচ মাস পর, আল বেরুনী তাঁর মহাগ্রন্থ কিতাব-উল-হিন্দ সম্পন্ন করেন। তখন গজনীর সিংহাসনে বসেছেন মাহমুদের পুত্র মাসউদ। নতুন শাসনকালেও আল বেরুনী তাঁর গবেষণাকর্ম চালিয়ে যান। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়, তাঁর মৃত্যু হয় ১০৪৮ খ্রিস্টাব্দে; যদিও কিছু মতামতে ১০৫০ খ্রিস্টাব্দকে সম্ভাব্য মৃত্যুসাল বলা হয়েছে। এ বিষয়ে আবু মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহর নির্ধারিত ১০৫০ সালের তারিখটিই অধিকাংশ গবেষকের কাছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য।
কিতাব-উল-হিন্দ কেবল একটি ইতিহাসগ্রন্থ নয়, বরং মধ্যযুগীয় ভারতের সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্মীয় জীবন, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানুষের চিন্তাজগতের এক নিরপেক্ষ ও সুগভীর প্রতিচ্ছবি। আল বেরুনীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অনুসন্ধিৎসু ও সংবেদনশীল, এবং তাঁর ভাষ্য ছিল তথ্যনিষ্ঠ, আবেগমুক্ত। যে পরিপক্ব জ্ঞান, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও বিস্ময়কর বিশ্লেষণ তিনি এই গ্রন্থে তুলে ধরেছেন, তা আজও ইতিহাসচর্চায় এক অনন্য নজির।
আল বেরুনীর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় জুরজানে অতিবাহিত হয়, যেখানে তিনি প্রায় এক দশক ধরে অধ্যয়ন ও রচনায় মনোনিবেশ করেন। তবে গজনীতে আগমন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজগুলো সম্পন্ন করার সুযোগ এনে দেয়। সেই সময় গজনী ছিল আফগানিস্তানে অবস্থিত এক সুবৃহৎ ও সমৃদ্ধ নগরী, যার প্রভাব বিস্তৃত ছিল ইরান, পাকিস্তান এবং ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। এই শক্তিশালী সাম্রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতায় আল বেরুনী তাঁর গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সব উপকরণ ও সুযোগ পান। তদুপরি, সুলতান মাহমুদের অভ্যাস ছিল হিন্দুস্তানে সামরিক অভিযানের সময় আল বেরুনীকে সঙ্গে নেওয়া—যা তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম এবং সমাজব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার অনন্য সুযোগ দেয়।
সুলতানি যুগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল হলো তবকাত-ই-নাসিরী। এর রচয়িতা মিনহাজ-ই-সিরাজীর পূর্ণ নাম আবু উমর মিনহাজ-উদ-দীন বিন সিরাজ-উদ-দীন আল-জুজ্জানী। ভারতে এসে তিনি প্রথমে মুলতানের শাসক সুলতান নাসিরউদ্দীন কুবাচার অধীনে কাজীর পদে নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে সুলতান ইলতুৎমিশের আমলে দিল্লীতে আসেন এবং সেখানেও কাজীর দায়িত্ব পালন করেন—প্রথমে ইলতুৎমিশের শাসনকালে, পরে তাঁর উত্তরাধিকারীদের আমলে। মিনহাজ-ই-সিরাজী তাঁর তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থটি সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদের (১২৪৬–১২৬৬ খ্রিঃ) নামে উৎসর্গ করেন। এই গ্রন্থে ভারতের মুসলিম শাসনের সূচনাপর্ব সম্পর্কিত অসংখ্য মূল্যবান তথ্য সন্নিবেশিত রয়েছে, এবং এতে ১২৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের ঘটনাপ্রবাহ ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ আছে। এর মাধ্যমে দিল্লি সুলতানতের প্রারম্ভিক রাজনৈতিক, সামরিক ও প্রশাসনিক ইতিহাসের এক নির্ভরযোগ্য ভিত্তি গড়ে ওঠে, যা আজও গবেষকদের জন্য অপরিহার্য উৎস হিসেবে বিবেচিত।
‘তবকাত-ই-নাসিরী’-এর পরবর্তী ধারাকে যেন অনায়াসে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যান মধ্যযুগের আরেক বিশিষ্ট ইতিহাসলেখক জিয়া-উদ-দীন বারণী, তাঁর সুবিখ্যাত তারিখ-ই-ফিরুজশাহী গ্রন্থের মধ্য দিয়ে। মিনহাজ-ই-সিরাজীর বর্ণনা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকেই যেন বারণীর আখ্যানের সূচনা। তবে তিনি তবকাত-ই-নাসিরী-এর মতো কেবলমাত্র ঘটনা লিপিবদ্ধ করার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং সমকালীন রাজনীতি, প্রশাসনিক কৌশল, নৈতিকতা, এবং সুলতানদের ব্যক্তিগত চরিত্র—সবকিছুর একটি সুসংহত বিশ্লেষণ তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে।
বারাণীর তারিখ-ই-ফিরুজশাহী ১২৬১ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী ঘটনাপঞ্জি থেকে শুরু হয়। প্রকৃত অর্থে, তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের সিংহাসনে আরোহণের সময়—১২৬৬ খ্রিস্টাব্দ—থেকে আখ্যান শুরু করেন এবং সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসনকালের প্রথম ছয় বছর পর্যন্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। এই সময়কাল দিল্লি সুলতানতের রাজনৈতিক উত্তরণ ও প্রশাসনিক পুনর্গঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ যুগ, যা বারাণীর লেখায় গভীর ও বিশদভাবে ফুটে উঠেছে।
বারাণীর পারিবারিক পটভূমি তাঁকে রাজদরবারের অভ্যন্তরীণ পরিমণ্ডলের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত করেছিল। তাঁর পূর্বপুরুষেরা দিল্লির সুলতানদের অধীনে নানা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনিও নিজে সুলতানি দরবারে মর্যাদাপূর্ণ আসন লাভ করেছিলেন। বলবনের রাজত্বকালে তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়, ফলে এই সুলতানের প্রশাসনিক ধরন, সামরিক সংস্কার, এবং দরবারি আচার-আচরণের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষ পরিচিত ছিলেন। তাঁর আখ্যানের প্রথমাংশে বলবনের যুগের বিবরণ তাই কেবল শোনা কথা নয়, বরং শৈশবস্মৃতির সঙ্গে যুক্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারও ফসল।
তবে ১২৬৬ থেকে ১২৯০-এর মধ্যে কয়েকজন খলজি সুলতান এবং পরে তুঘলক রাজবংশের প্রারম্ভিক শাসকদের বিষয়ে তিনি যে তথ্য দেন, তার অনেকটাই প্রত্যক্ষদর্শী অভিজ্ঞতা ও সমসাময়িক যোগাযোগের ভিত্তিতে সংগৃহীত। বিশেষত সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকালীন ঘটনাবলি তিনি নিজচক্ষে দেখা ঘটনার মতোই বিশদ ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই কারণেই তারিখ-ই-ফিরুজশাহী কেবল খলজি ও তুঘলক যুগের ইতিহাসের একটি মৌলিক উৎস নয়, বরং সেই সময়কার সামাজিক মনস্তত্ত্ব, রাজকীয় নীতি এবং প্রশাসনিক দর্শনেরও এক অনন্য দলিল।
বারাণীর লেখনীতে কেবল ঘটনাপঞ্জির নিরপেক্ষ বর্ণনা নয়, বরং নৈতিক বিচারও বিদ্যমান। তিনি সমকালীন সুলতানদের চরিত্র, নীতি ও কর্মদক্ষতা সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করেছেন। রাজ্যের স্থায়িত্ব রক্ষায় ন্যায়পরায়ণতার গুরুত্ব, শাসকশ্রেণির মধ্যে নৈতিক শৃঙ্খলা, এবং রাজনৈতিক কৌশলের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তাঁর মতামত আজও রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।
একই শিরোনামে—তারিখ-ই-ফিরুজশাহী—আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন শামস-ই-সিরাজ আফীফ, যা প্রায়শই বারাণীর গ্রন্থের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়, কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক থেকে এটি আলাদা। আফীফের জন্ম ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে এবং তিনি সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের সান্নিধ্য ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তাঁর আখ্যানের পরিসর একান্তভাবে ফিরোজ শাহের শাসনকালকে ঘিরে। আফীফ কেবল রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ নয়, বরং ফিরোজ শাহের সাংস্কৃতিক নীতি, স্থাপত্য-উদ্যোগ, জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি, এবং শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার বিবরণ বিশেষ যত্নে সংরক্ষণ করেছেন।
গবেষকরা ধারণা করেন, আফীফ তাঁর এই গ্রন্থটি তৈমুর লঙের ধ্বংসযজ্ঞের পরবর্তী সময়ে, সম্ভবত পঞ্চদশ শতকের প্রথম দশকে রচনা করেন। এর ফলে তাঁর লেখনীতে এক ধরনের নস্টালজিয়া—অতীতের তুলনামূলক শান্তি ও সমৃদ্ধির স্মৃতিচারণ—দেখা যায়। যদিও তিনি আরও বহু রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়, আজ সেগুলোর কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না।
ফিরোজ শাহ তুঘলকের সময়কাল সম্পর্কিত একটি অনন্য উৎস হলো সুলতানের নিজের লেখা ফুতুহাত-ই-ফিরুজশাহী। মাত্র বত্রিশ পৃষ্ঠার এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থটির শিরোনামের আক্ষরিক অর্থ—“ফিরোজ শাহের বিজয়সমূহ”—তাঁর সামরিক অভিযানগুলির সারসংক্ষেপ নির্দেশ করলেও, এর অন্তর্নিহিত গুরুত্ব এর চেয়ে অনেক বেশি। এখানে সুলতান নিজের ভাষায় তাঁর শাসননীতির মূল ভাবনা, জনকল্যাণমূলক প্রকল্প, এবং ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। ফলে এটি শুধু রাজনৈতিক ইতিহাস নয়, বরং সুলতানের মানসিকতা ও শাসনদর্শনেরও সরাসরি প্রতিফলন।
এর পাশাপাশি, ১৩৭০ খ্রিস্টাব্দে রচিত সীরাত-ই-ফিরুজশাহী নামের আরেকটি গ্রন্থ ফিরোজ শাহের যুগের মূল্যবান দলিল। যদিও লেখকের নাম জানা যায় না, অনুমান করা হয় যে এটি সুলতানের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত। কিছু গবেষকের মতে, সুলতান নিজেই হয়তো গ্রন্থটির রচনায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছিলেন। এর বিষয়বস্তুতে ফুতুহাত-ই-ফিরুজশাহী-এর সঙ্গে অনেক মিল থাকলেও, পরিসরে এটি বড় এবং বিস্তারিত। সুলতানের কার্যাবলী, দান-ধ্যান, ধর্মীয় সংস্কার, এবং ব্যক্তিগত গুণাবলীর ভূয়সী প্রশংসা এই রচনার মূল সুর।
সুলতানি যুগের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো ফুতুহ-উস-সালাতীন, যা ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন খাজা আব্দুল মালিক ইসামী। তাঁর জীবনের সঙ্গে মুহম্মদ বিন তুঘলকের নীতির সংঘাতের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। যখন তুঘলক দিল্লি থেকে দেবগিরি (নাম পরিবর্তিত হয়ে দৌলতাবাদ) রাজধানী স্থাপন করেন, তখন তিনি প্রধান অমাত্যদের পুরনো রাজধানী ছেড়ে নতুন রাজধানীতে আসতে বাধ্য করেন। তরুণ ইসামী তাঁর পিতামহের সঙ্গে দেবগিরি পাড়ি জমান।
দৌলতাবাদে অবস্থানকালে, প্রথম বাহমনী সুলতান আলাউদ্দিন হাসান বাহমন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায়, ইসামী তাঁর ফুতুহ-উস-সালাতীন রচনা করেন। গ্রন্থটিতে গজনীর ইয়ামিনী শাসকদের উত্থান থেকে শুরু করে মুহম্মদ বিন তুঘলকের যুগ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন শতাব্দীর ইতিহাস কাব্যিক ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। ইসামীই একমাত্র ঐতিহাসিক যিনি তুঘলক আমলের ইতিহাস এমন স্বাধীন মনোভাবে লিখেছিলেন যে তাতে রাজসুলভ ভয় বা সেন্সরের প্রভাব অনুপস্থিত।
তবে এ স্বাধীনতা সবসময় তাঁর নিরপেক্ষতাকে নিশ্চিত করেনি। অনেকের মতে, মুহম্মদ বিন তুঘলকের ব্যক্তিগত রোষানলে পড়ে দৌলতাবাদে নির্বাসিত হওয়ায়, ইসামী তাঁর লেখনীতে সুলতানের প্রতি অতটা সহানুভূতিশীল ছিলেন না। এর ফলে তাঁর বর্ণনায় সমালোচনার সুর প্রকট হয়েছে। আবার, যেহেতু ফুতুহ-উস-সালাতীন কাব্য আকারে রচিত, তাই তাতে অতিরঞ্জন ও অলঙ্কারপ্রধানতার অভিযোগও রয়েছে।
তবু এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ইসামীর রচনা মধ্যযুগীয় ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি অপরিহার্য দলিল। কারণ, তিনি কেবল যুদ্ধ-বিজয়ের কাহিনি নয়, বরং সামাজিক অবস্থা, দরবারি রাজনীতি, আঞ্চলিক শক্তির উত্থান, এবং শাসক-অধীনস্থ সম্পর্কের সূক্ষ্ম পরিবর্তনও তাঁর আখ্যানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।
এইভাবে, বারাণী থেকে আফীফ, সুলতান ফিরোজ শাহের স্বলিখিত দলিল থেকে অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার, এবং ইসামী পর্যন্ত—সুলতানি যুগের এই ইতিহাসগ্রন্থসমূহ শুধু ঘটনাপঞ্জির ধারাবাহিকতা নয়, বরং রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি ও শাসনদর্শনের বহুমাত্রিক প্রতিচ্ছবি। এগুলোর প্রতিটি পাঠ আমাদের সামনে মধ্যযুগীয় ভারতের এক জটিল, বৈচিত্র্যময়, এবং ক্রমবিকাশমান সভ্যতার চিত্র তুলে ধরে, যেখানে সুলতানদের সামরিক অভিযান যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি তাঁদের সাংস্কৃতিক নীতি, প্রশাসনিক সংস্কার, এবং ব্যক্তিগত জীবনদর্শনও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।
তৈমুর লং-এর আত্মজীবনীমূলক দলিল মাহফুজাত-ই-তিমুরী মধ্যযুগীয় ভারতীয় ইতিহাস, বিশেষত সুলতানি আমলের শেষ অধ্যায় বোঝার ক্ষেত্রে এক অনন্য উৎস। ইতিহাসবিদদের দৃষ্টিতে এটি কেবল একজন বিজেতার ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা নয়, বরং রাজনৈতিক ক্ষমতার রূপান্তরের একটি প্রত্যক্ষ দলিলও বটে। কারণ, তৈমুর লং-এর বিধ্বংসী বিজয়াভিযানের পরেই ভারতে তুঘলক শাসনের পতন ঘটে এবং নতুন রাজনৈতিক বিন্যাসের সূত্রপাত হয়।
মূল গ্রন্থটি তুর্কি ভাষায় রচিত হলেও, পরবর্তী কালে আবু তালিব হুসাইনী একে ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন এবং তা সম্রাট শাহজাহানের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। এ অনুবাদের মাধ্যমে মধ্যযুগীয় ভারতীয় দরবারে তৈমুরের বিজয় ও শাসনদর্শন নতুন করে আলোচনায় আসে। যদিও কিছু গবেষক গ্রন্থটির বস্তুনিষ্ঠতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন—কারণ এটি এক বিজেতার নিজের বক্তব্য, যেখানে আত্মপ্রশস্তি এবং বিজয়ের ন্যায়সঙ্গতীকরণ অনিবার্যভাবে মিশে আছে—তবু পণ্ডিতসমাজের একটি বড় অংশের মতে, মাহফুজাত-ই-তিমুরী তৈমুরের ব্যক্তিত্ব, সামরিক নীতি, প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বহু মৌলিক তথ্য প্রদান করেছে।
তৈমুরের মৃত্যুর প্রায় তিন দশক পর, তাঁর পৌত্রের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায়, আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হয়—জাফরনামা। এর রচয়িতা শরাফউদ্দিন আলি ইয়াজদি, যিনি কেবল ঐতিহাসিক নয়, বরং এক বিশিষ্ট গদ্যশিল্পীও ছিলেন। এই গ্রন্থটির ভাষা অলঙ্কারময় ও কাব্যমিশ্রিত, যেখানে ঘটনা-বিবরণের পাশাপাশি রয়েছে এক প্রকার সাহিত্যিক আভিজাত্য। জাফরনামা তৈমুরি যুগের ফারসি সাহিত্যের শীর্ষস্থানে অবস্থান করে, এবং এটিকে প্রায়শই শাহরুখ মীর্জা ও উলুগ বেগের সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষকতার নিদর্শন হিসেবে দেখা হয়।
ইয়াজদির এই জাফরনামা মূলত তৈমুরের জীবদ্দশায় তাঁর দাপ্তরিক জীবনীলেখক নিজামউদ্দিন শামির রচিত জাফরনামা-এর ভিত্তিতে রচিত। তবে ইয়াজদি কেবল পূর্বসূরির তথ্য অনুলিখন করেননি, বরং ভাষা, বর্ণনাশৈলী এবং ঘটনার বিন্যাসে নতুনত্ব এনেছেন। শাহরুখ মীর্জা ও উলুগ বেগ—দু’জনেই পার্সিয়ান সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এবং তাঁদের দরবারেই এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। এই সময়ে পার্সি সাহিত্য যেমন সমৃদ্ধ হয়, তেমনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অগ্রগতি ঘটে। উলুগ বেগ নিজেও ছিলেন একজন খ্যাতিমান জ্যোতির্বিজ্ঞানী, যার বহু রচনা ফারসিতে নয়, বরং আরবিতে রচিত হয়েছিল।
তৈমুরি আমলের সাংস্কৃতিক নীতির আরেকটি প্রতীক হলো বাইসুনকুরের নির্দেশে শাহনামা-এর নতুন সংস্করণ প্রস্তুতকরণ। এই “বাইসুনকুরের শাহনামা” কেবল সাহিত্যের নয়, মধ্যযুগীয় চিত্রশিল্প ও ক্যালিগ্রাফিরও এক অনন্য নিদর্শন।
তবে তৈমুরিরা শুধু ফারসি সাহিত্যেই অবদান রাখেননি; তাঁরা তুর্কি ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। বিশেষত চাগাতাই ভাষায় এই সময়ে শক্তিশালী সাহিত্যধারা গড়ে ওঠে। মীর আলি শের নাওয়াই, হুসাইন বাইকারা, এমনকি পরবর্তীকালে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর—তাঁরা সকলেই চাগাতাই ভাষাকে সাহিত্যভাষা হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন। চাগাতাই ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হলো বাবরের আত্মজীবনী বাবরনামা, যা কেবল ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা নয়, বরং মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক, সামরিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের এক সমৃদ্ধ দলিল।
ভারতের সুলতানি আমলের ইতিহাসচর্চায় তারিখ-ই-মুবারকশাহী বিশেষ গুরুত্ববাহী। ইয়াহিয়া বিন আহমদ বিন আবদুল্লাহ সরহিন্দি রচিত এই গ্রন্থে বর্ণনা শুরু হয়েছে মুইজউদ্দিন মুহম্মদ বিন সাম বা মুহম্মদ ঘোরীর শাসনকাল থেকে, এবং হঠাৎ করে তা সমাপ্ত হয়েছে ১৪৩৪ খ্রিস্টাব্দে। গ্রন্থটির পরিসর মূলত দিল্লির সাধারণ রাজনৈতিক ইতিহাস হলেও, ১৩৮৮ থেকে ১৪৩৪—এই ৪৬ বছরের জন্য এটি একমাত্র প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য উৎস। বিশেষত ১৪১৪ থেকে ১৪৩৪ সাল পর্যন্ত দিল্লির সৈয়দ বংশের প্রথম দুই সুলতানের রাজত্বকালীন ঘটনাবলির ক্ষেত্রে এটি একমাত্র প্রত্যক্ষ বর্ণনা প্রদান করে।
ইয়াহিয়া বিন আহমদের বিশেষ সুবিধা ছিল যে, তিনি সুলতান মুবারক শাহের রাজত্বকালে সরকারি দপ্তরে অবাধ যাতায়াত ও দলিল-দস্তাবেজ ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছিলেন। এর ফলে তাঁর প্রদত্ত তথ্যগুলি উচ্চমাত্রার নির্ভরযোগ্যতা লাভ করেছে। পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ—যেমন নিজামউদ্দিন আহমদ বখশী, আব্দুল কাদের বদায়উনী, ও ফিরিশতা—তাঁকে নির্ভরযোগ্য ইতিহাসলেখক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।
খিজির খানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুবারক শাহ দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। সমসাময়িকদের মতে, তিনি একজন দক্ষ ও বিদ্যোৎসাহী শাসক ছিলেন। তাঁর সময়ে দিল্লি সাম্রাজ্যে তুলনামূলক স্থিতি ফিরে আসে, কিন্তু রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র থেকে তিনি মুক্তি পাননি। ১৪৩৪ খ্রিস্টাব্দে সারওয়ার উল-মুলক নামের এক অভিজাতের হাতে তিনি নিহত হন। ইয়াহিয়া-বিন-আহমদ তাঁর তারিখ-ই-মুবারকশাহী এই সুলতানের প্রতি উৎসর্গ করেছিলেন।
মুবারক শাহের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মুহম্মদ শাহ, যিনি অল্পকালের মধ্যেই পিতৃব্যের হত্যার প্রতিশোধ নেন—সারওয়ার উল-মুলক সুলতানের সৈন্যদের হাতে নিহত হন। মুহম্মদ শাহ মোট এগার বছর রাজত্ব করেন। তাঁর পরবর্তী শাসক আলাউদ্দিন আলম শাহ ছিলেন সৈয়দ বংশের শেষ এবং সবচেয়ে দুর্বল সুলতান। ১৪৫১ সালে তিনি স্বেচ্ছায় বাহলুল লোদীর কাছে সিংহাসন ত্যাগ করেন, ফলে সৈয়দ বংশের অবসান এবং লোদী বংশের প্রতিষ্ঠা ঘটে। ১৪৭৮ সালে আলম শাহের মৃত্যু হয়। উল্লেখযোগ্য যে, দিল্লির ইতিহাসে লোদী সুলতানরা একমাত্র পাঠান বংশোদ্ভূত শাসক; অন্য সব সুলতান ছিলেন খাঁটি বা মিশ্র তুর্কি বংশোদ্ভূত।
ইয়াহিয়া বিন আহমদের লেখায় বাংলার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেখা যায় না। কেবল তখনই তিনি বাংলার উল্লেখ করেন, যখন তা দিল্লির সুলতানদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। এ জন্যই তাঁর বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে সৈয়দ বংশের সময়ে বাংলা কার্যত স্বাধীন ছিল এবং দিল্লির সঙ্গে এর সম্পর্ক ছিল অতি সীমিত। তা সত্ত্বেও, পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের রচনা—যেমন মিনহাজ-ই-সিরাজীর তবকাত-ই-নাসিরী, বারাণীর তারিখ-ই-ফিরুজশাহী, ও আফীফের তারিখ-ই-ফিরুজশাহী—ব্যবহার করে তিনি প্রয়োজনীয় পটভূমি সংযোজন করেছেন। কালপঞ্জি ও ঘটনাক্রম যাচাইয়ের ক্ষেত্রে তাঁর তারিখ-ই-মুবারকশাহী এখনো অমূল্য সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হয়।
এইভাবে, মাহফুজাত-ই-তিমুরী, জাফরনামা, এবং তারিখ-ই-মুবারকশাহী—তিনটি গ্রন্থই সুলতানি আমল ও তৎপরবর্তী রাজনৈতিক পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা বোঝার ক্ষেত্রে একে অপরের পরিপূরক। প্রথমটি বিজেতার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও আত্মপ্রশস্তি, দ্বিতীয়টি সাহিত্যিক ভাষায় রচিত বিজয়ের কাব্যময় ইতিহাস, আর তৃতীয়টি এক আমলাতান্ত্রিক ইতিহাসবিদের নিরপেক্ষ দলিল। এদের সম্মিলিত পাঠ আমাদেরকে কেবল যুদ্ধ ও ক্ষমতার পালাবদল নয়, বরং মধ্যযুগীয় ভারতের রাজনীতি, সংস্কৃতি, প্রশাসন ও আঞ্চলিক সম্পর্কের বহুমাত্রিক ছবি উপস্থাপন করে।
ফারসি ভাষায় রচিত মধ্যযুগীয় ইতিহাস-গ্রন্থ তারিখ-ই-শাহী ভারতবর্ষের বিশেষত দিল্লি ও বাংলার আফগান সুলতানদের ইতিহাস অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এর পূর্ণ শিরোনাম তারিখ-ই-সালাতীন-ই-আফগানা—অর্থাৎ “আফগান সুলতানদের ইতিহাস”। এই গ্রন্থে আফগান রাজাদের সম্পর্কে এমন বহু তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে যা অন্য কোনো সমসাময়িক বা পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক উৎসে পাওয়া যায় না। বিশেষ করে বাংলা ও উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে আফগান শাসনের প্রকৃতি, তাদের সামরিক সংঘর্ষ, প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং দিল্লির সঙ্গে সম্পর্কের যে বিবরণ এখানে আছে, তা অন্যত্র দুর্লভ।
আফগান শাসক দাউদ কররানীর প্রত্যক্ষ নির্দেশে ১৫৭২ থেকে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আফগান বংশোদ্ভূত ইতিহাসলেখক আহমেদ ইয়াদগার এই গ্রন্থ রচনা করেন। দাউদ কররানী, যিনি বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান, মুগল সম্রাট আকবরের সঙ্গে একাধিক সামরিক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁর আমলে রাজনৈতিক উত্তেজনা ও সাম্রাজ্যিক চ্যালেঞ্জ চরমে পৌঁছেছিল। এই পটভূমিতেই ইয়াদগারের রচিত তারিখ-ই-শাহী কেবল শাসকদের জীবনী নয়, বরং আফগান ক্ষমতার পতনের প্রাক্কালে একটি রাজনৈতিক দলিল হিসেবেও মূল্যবান। পরবর্তীকালে এটি “তারিখ-ই-শাহী” শিরোনামে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল থেকে প্রকাশিত হয়, যার ফলে আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণায় এর ব্যবহার আরও বিস্তৃত হয়।
মুগল যুগের ইতিহাসচর্চায় আকবরনামা নিঃসন্দেহে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। সম্রাট আকবরের দরবারের প্রধান ইতিহাসলেখক আবুল ফজল আল্লামী রচিত এই মহাগ্রন্থ কেবল সম্রাটের জীবনীই নয়, বরং ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাসের এক সুবিশাল ভাণ্ডার। আবুল ফজল, যিনি সম্রাট আকবরের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ও নীতি-পরামর্শদাতা ছিলেন, ১৫৫৬ থেকে ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দের রাজত্বকালীন ঘটনাপ্রবাহ নিজের কলমে লিপিবদ্ধ করেন এমনভাবে, যাতে সম্রাটের প্রতিচ্ছবি এক আদর্শ, প্রজ্ঞাবান, ও ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে ফুটে ওঠে।
আকবরনামা তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে রয়েছে তিমুর বংশের উৎস ও বিকাশ, বাবর ও হুমায়ুনের রাজত্বকাল, এবং দিল্লির শূর বংশীয় সুলতানদের বিবরণ। দ্বিতীয় খণ্ডে আকবরের শাসনের প্রথম ছেচল্লিশ বছর পর্যন্ত রাজনৈতিক, সামরিক ও কূটনৈতিক ঘটনাবলির ধারাবাহিক বিবরণ রয়েছে—যা তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার ও সংহতির ইতিহাস বোঝার জন্য অপরিহার্য। তৃতীয় খণ্ডটি আলাদা নামেও পরিচিত—আইন-ই-আকবরী—যেখানে আকবরের আমলে প্রচলিত আইন-কানুন, রাজস্বনীতি, সামরিক ও প্রশাসনিক কাঠামো, এবং সাংস্কৃতিক-পারিবেশিক বিষয়াবলি সুবিন্যস্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই শেষ খণ্ড ভারতীয় সমাজ-অর্থনীতির এক বিশদ নথি, যা সমসাময়িক রাষ্ট্রব্যবস্থার এক অনন্য প্রতিচ্ছবি।
মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসগ্রন্থগুলির মধ্যে নিজামউদ্দীন আহমদ রচিত তবকাত-ই-আকবরী বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। গ্রন্থকারের পিতা মুকিম হারভী ছিলেন সম্রাট আকবরের আমলের প্রথম বখশী—অর্থাৎ উচ্চপদস্থ সামরিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা। নিজামউদ্দীনের রচিত এই গ্রন্থকে তারিখ-ই-নিজামী নামেও অভিহিত করা হয়। ১০০১ হিজরি (১৫৯২-৯৩ খ্রিস্টাব্দ) সালে রচনা শুরু হলেও এর বিবরণ ১০০২ হিজরি (১৫৯৩-৯৪ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত বিস্তৃত। সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী মুসলিম শাসনের ইতিহাস এখানে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে।
নিজামউদ্দীন আহমদ সহজ-সরল ভাষায় এই ইতিহাস রচনা করেছিলেন, যা মূলত একটি প্রাতিষ্ঠানিক রিপোর্টের মতো গাম্ভীর্যপূর্ণ হলেও তাতে ব্যক্তিগত মূল্যায়নের ছাপ প্রায় নেই। পূর্ববর্তী সময়ের বর্ণনায় তিনি পুরনো ঐতিহাসিকদের রচনা ব্যবহার করেছেন, কিন্তু আকবর-যুগের ঘটনাবলির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী। আকবরের রাজদরবারের একজন বিশ্বস্ত সভাসদ হওয়ায় তাঁর দেওয়া তথ্য উচ্চমাত্রায় নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। তবুও লক্ষ্যণীয় যে, সম্রাটের ধর্মীয় উদ্ভাবন—বিশেষত তাঁর নয়া মতবাদ প্রবর্তনের প্রসঙ্গ—তিনি সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন। কোনো সমালোচনা বা ভিন্নমত প্রকাশের ইঙ্গিতও তাঁর লেখায় নেই, যা হয়তো সম্রাটের আনুকূল্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সচেতনভাবে বর্জিত হয়েছে।
বাংলার সুলতানি আমলের ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে তবকাত-ই-আকবরী বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রাক-মুগল যুগে বাংলার উপর সমসাময়িক কোনো পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হয়নি, ফলে পরবর্তী কালের গ্রন্থগুলি ইতিহাসচর্চায় সহায়ক হয়ে ওঠে। এই গ্রন্থে প্রথমবারের মতো বাংলার ইতিহাস একটি পৃথক অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে, যেখানে বখতিয়ার খলজী থেকে মুগল শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বপর্যন্ত শাসকদের ধারাবাহিক তালিকা পাওয়া যায়। যদিও সময়-উল্লেখে ভুল আছে, অনেক সুলতানের নাম বাদ পড়েছে, তবুও এটি প্রথম প্রায়-সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া গ্রন্থ হিসেবে ঐতিহাসিকভাবে মূল্যবান। একই ধরনের তথ্য আরেকটি গ্রন্থ তারিখ-ই-ফিরিশতা-তেও পাওয়া যায়, তবে তবকাতে তা অধিক সংক্ষিপ্ত আকারে রয়েছে।
আবদুল কাদির বদাউনী রচিত মুন্তখব-উত-তাওয়ারিখ মধ্যযুগীয় ভারতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ, তবে আংশিকভাবে বিতর্কিত, ঐতিহাসিক দলিল। এর রচয়িতা বদাউনের অধিবাসী, হিজরি ৯৪৮ (১৫৪১-৪২ খ্রিস্টাব্দ) সালে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হন। ১৫৭৩ সালে সম্রাট আকবরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং পরে তিনি রাজদরবারের পণ্ডিতদের অন্তর্ভুক্ত হন। বদাউনী ছিলেন নিজামউদ্দীন আহমদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বন্ধুর মৃত্যুর পর তিনি নিজ হাতে ভারতের সামগ্রিক ইতিহাস লেখার দায়িত্ব নেন এবং ১০০৪ হিজরির ২৩ জমাদি-উস-সানি (ফেব্রুয়ারি ১৫৯৬) তাঁর রচনা সম্পন্ন করেন। সম্ভবত এর অল্পদিন পরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
মুন্তখব-উত-তাওয়ারিখ-এর বিশেষত্ব হলো, এতে সম্রাট আকবরের ধর্মীয় মতবাদের প্রতি প্রকাশ্য সমালোচনা পাওয়া যায়। বদাউনী তাঁর লেখায় আকবরের প্রবর্তিত নতুন মতবাদ, দীন-ই-ইলাহী, এবং তার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সমালোচনায় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ভাষা ব্যবহার করেছেন। এই কারণে গ্রন্থটি আকবরের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি; তা গোপন রাখা হয় এবং অবশেষে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে প্রকাশিত হয়। জাহাঙ্গীর নিজে গ্রন্থটির বিষয়বস্তু নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। এমনকি বদাউনী-পরিবারের দাবি যে তাঁরা বইটির অস্তিত্বই জানতেন না, তা জাহাঙ্গীর প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।
তবে বাংলার ইতিহাসচর্চায় মুন্তখব-উত-তাওয়ারিখ বিশেষ অবদান রাখেনি। বদাউনী বাংলার জন্য কোনো পৃথক অধ্যায় রাখেননি; সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের মধ্যে তিনি কেবল প্রাসঙ্গিক হলে বাংলার উল্লেখ করেছেন। এর ফলে বাংলা-সংক্রান্ত তথ্য এখানে বিচ্ছিন্ন ও সীমিত।
এই চারটি গ্রন্থ—তারিখ-ই-শাহী, আকবরনামা, তবকাত-ই-আকবরী, এবং মুন্তখব-উত-তাওয়ারিখ—সমষ্টিগতভাবে মধ্যযুগীয় ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে অমূল্য উৎস। প্রথমটি আফগান সুলতানদের ইতিহাসের বিশেষ দালিলিক প্রমাণ, দ্বিতীয়টি এক সাম্রাজ্যবাদী শাসকের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক আদর্শের মহাগ্রন্থ, তৃতীয়টি সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী মুসলিম শাসনের ধারাবাহিক বিবরণ, এবং চতুর্থটি এক সমালোচনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে মুগল সম্রাটের ধর্মীয় নীতি পর্যবেক্ষণ।
ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসগ্রন্থের মধ্যে তারিখ-ই-ফিরিশতা এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। মুহাম্মদ কাসিম হিন্দু শাহ, যিনি ফিরিশতা নামে সমধিক পরিচিত, ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে এই গ্রন্থ রচনা করেন। এর পূর্ণ নাম গুলশান-ই-ইবরাহিমী, কারণ এটি তিনি বিজাপুরের ইবরাহিম আদিল শাহের নামে উৎসর্গ করেছিলেন। শিরোনামের আভিজাত্যই বোঝায়, এটি কেবল তথ্যসংকলন নয়, বরং সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাসের এক সুপরিকল্পিত উপস্থাপন। ফিরিশতা মূলত দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন রাজ্যের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে আলোচনা করলেও এর পরিধি সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে বিস্তৃত; আকবরের রাজত্বকালের শেষ পর্যায় পর্যন্ত ঘটনার ধারাবাহিকতা এখানে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে।
ফিরিশতা তাঁর রচনায় পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে গভীরভাবে প্রভাবিত হন। বিশেষত নিজামউদ্দীন আহমদের তবকাত-ই-আকবরী ও আবদুল কাদির বদাউনীর মুন্তখব-উত-তাওয়ারিখ—এই দুই গ্রন্থ ছিল তাঁর অন্যতম ভিত্তি। তবে তিনি কেবল পূর্বসূরিদের তথ্য হুবহু গ্রহণ করেননি; বরং প্রামাণ্য দলিল যাচাই ও স্থানীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য স্বচক্ষে বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করেন। এই পর্যবেক্ষণ ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ তাঁর বর্ণনাকে এক বিশেষ বিশ্বাসযোগ্যতা দিয়েছে। সমসাময়িক ঐতিহাসিক সাহিত্যের প্রচলিত ধারা অনুযায়ী তিনি ঘটনাপঞ্জি আকারে রচনা সাজিয়েছেন, কিন্তু তাতে ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ ও প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যার ছাপও সুস্পষ্ট।
বাংলার সুলতানি আমলের ইতিহাস পুনর্গঠনের জন্য তারিখ-ই-ফিরিশতা অমূল্য। বাংলাদেশের মাটিতে সুলতানি যুগে কোনো পূর্ণাঙ্গ সমসাময়িক ইতিহাসলেখা আজ অবধি আবিষ্কৃত হয়নি। ফলে এই সময়ের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অনেকাংশই পুনর্গঠিত হয়েছে দিল্লি ও অন্যান্য কেন্দ্রে রচিত ইতিহাসগ্রন্থের উপর নির্ভর করে। যেখানে দিল্লিভিত্তিক লেখকদের গ্রন্থে বাংলার সুলতানদের তথ্য অনুপস্থিত, সেখানে ঐ সময়ের ঘটনাপঞ্জি কার্যত শূন্য রয়ে গেছে। এই প্রেক্ষাপটে ফিরিশতার অবদান অনস্বীকার্য—তিনি দ্বিতীয় ঐতিহাসিক যিনি সুলতানি বাংলার জন্য একটি পৃথক অধ্যায় রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। প্রথম প্রচেষ্টা করেছিলেন নিজামউদ্দীন আহমদ বখশী, যার রচনার উপর ফিরিশতা গভীরভাবে ঋণী। তবে ফিরিশতা কেবল পূর্বসূরির তথ্য পুনর্লিখন করেননি; তিনি কিছু অতিরিক্ত তথ্যও সরবরাহ করেছেন, যা তাঁর ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের ফল। তিনি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আরিফ কান্দাহারির একটি গ্রন্থের উল্লেখ করেন, যদিও আজ সেই গ্রন্থ হারিয়ে গেছে।
ফিরিশতার ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি সমকালীন রাজনৈতিক জটিলতা বোঝার জন্য বিশেষভাবে সহায়ক। দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির পাশাপাশি তিনি বাংলার ইতিহাসকে ভারতের বৃহত্তর সাম্রাজ্যিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেছেন। এর ফলে পাঠক বুঝতে পারেন, কীভাবে বাংলা একদিকে স্বাধীন সুলতানি রাজ্য হিসেবে বিকশিত হয়েছে, আবার অপরদিকে দিল্লি ও মুগল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে ক্রমাগত মিথস্ক্রিয়ায় যুক্ত থেকেছে।
দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যযুগীয় ইতিহাসচর্চায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হলো তারিখ-ই-রশিদী—যা রচনা করেন মির্জা হায়দার দুগলত। মির্জা হায়দার ছিলেন মধ্য এশিয়ার প্রখ্যাত দুগলত তুর্কি বংশের সন্তান এবং বাবুরের চাচাত ভাই। ৯০৫ হিজরি (১৪৯৯-১৫০০ খ্রিস্টাব্দে) তাসখন্দে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন সেখানকার গভর্নর, কিন্তু মাত্র নয় বছর বয়সে পিতৃহারা হন মির্জা। এরপর বাবুর তাঁকে নিজের তত্ত্বাবধানে লালনপালন করেন, যা পরবর্তীকালে তাঁর রাজনৈতিক ও সামরিক জীবনের ভিত্তি গঠন করে।
মির্জা হায়দার একজন সফল জেনারেল হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন এবং ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ কনৌজের যুদ্ধে তিনি প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেন। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীরের কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির আমন্ত্রণে তিনি কাশ্মীর উপত্যকা জয় করেন ও সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তবে তাঁর জীবনের অবসান ঘটে করুণ পরিণতিতে—১৫৫১ খ্রিস্টাব্দে ভিরবলে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গেলে স্থানীয় অধিবাসীদের হাতে তিনি নিহত হন।
তারিখ-ই-রশিদী মূলত দুটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্ব লেখা হয় ৯৫১ ও ৯৫২ হিজরিতে (১৫৪৪-১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে), আর দ্বিতীয় পর্ব লেখা হয় ৯৪৮ হিজরিতে (১৫৪১ খ্রিস্টাব্দে)। সময়ক্রম অনুসারে দ্বিতীয় পর্ব আগে রচিত হলেও এতে লেখকের সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। গ্রন্থটি সম্পন্ন হওয়ার পর এটি উৎসর্গ করা হয় কাশগড়ের শাসক আবদুল ফতেহ সুলতান সায়ীদের পুত্র আব্দুর রশিদ খানের নামে, যার নাম থেকেই গ্রন্থটির শিরোনাম তারিখ-ই-রশিদী।
এই গ্রন্থের সূচনা হয় মুগল খাকান তুগলক তিমারের বিবরণ দিয়ে—যিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বৃহৎ অংশজুড়ে রয়েছে মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাস, যার মধ্যে রয়েছে বাবুর ও হুমায়ুনের জীবন ও কর্মকাণ্ডের বিশদ বিবরণ। বাবুরের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র সম্পর্কে মির্জা হায়দার গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, এবং হুমায়ুনের প্রতি তাঁর অবিচল আনুগত্যও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি হুমায়ুনের ভারতীয় অভিযানের ঘটনাপ্রবাহ এত বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, অন্য কোনো সমসাময়িক বা পরবর্তী ঐতিহাসিক ততটা করেননি। কনৌজের যুদ্ধে কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনীর একটি অংশ তিনি নিজে পরিচালনা করায় যুদ্ধের বিবরণও এসেছে প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষায়, যা এটিকে আরও মূল্যবান করে তোলে।
ভারতের বাইরে কাশ্মীরের ইতিহাসচর্চার প্রসঙ্গ এলে সংস্কৃত ভাষায় রচিত রাজতরঙ্গিণী অপরিহার্যভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাশ্মীরি পণ্ডিত কলহন এই ইতিহাসগ্রন্থ রচনা শুরু করেন। পরে অন্যান্য লেখকেরা তা পরিসমাপ্ত করেন। রাজতরঙ্গিণী মূলত কাশ্মীরের রাজাদের বংশানুক্রমিক ইতিহাস, যা সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডারে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক রচনা হিসেবে বিবেচিত। মির্জা হায়দারের তারিখ-ই-রশিদী ও কলহনের রাজতরঙ্গিণী উভয়ই কাশ্মীরের রাজনৈতিক ইতিহাসের জন্য অপরিহার্য দলিল, যদিও একটির ভাষা ফারসি এবং অপরটির ভাষা সংস্কৃত।
সব মিলিয়ে, তারিখ-ই-ফিরিশতা ও তারিখ-ই-রশিদী—দুটি গ্রন্থই মধ্যযুগীয় ভারত ও মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। প্রথমটি সমগ্র ভারতবর্ষ, বিশেষত দাক্ষিণাত্য ও বাংলার ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রামাণ্য দলিল; দ্বিতীয়টি মধ্য এশিয়া ও কাশ্মীরের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে মুগল সাম্রাজ্যের প্রাথমিক যুগের ঘটনাপঞ্জি উপস্থাপন করেছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে। এই দুই গ্রন্থ একত্রে পাঠ করলে বোঝা যায়, কীভাবে আঞ্চলিক ইতিহাস বৃহত্তর সাম্রাজ্যিক প্রেক্ষাপটে মিশে যায়, এবং কীভাবে ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা ও দলিলভিত্তিক ইতিহাস মিলিত হয়ে এক সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক আখ্যান রচনা করে।
বাংলার মুসলিম শাসনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসরচনার ক্ষেত্রে রিয়াজ-উস-সালাতীন এক অনন্য মাইলফলক। ফারসি ভাষায় রচিত এই গ্রন্থই ছিল বাংলার ইতিহাসে প্রথম সুসংহত ও ধারাবাহিক প্রচেষ্টা, যেখানে ১২০৪–০৫ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজীর নদীয়া বিজয় থেকে শুরু করে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ শতাব্দীর ঘটনাপ্রবাহ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। গ্রন্থের কোথাও কোথাও বর্ণনার ফাঁক থাকলেও এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এটি শুধু একটি রাজনৈতিক ইতিহাস নয়, বরং বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরেরও একটি দলিল।
গ্রন্থকার গোলাম হোসেন সলিম ছিলেন জায়েদপুরের সন্তান। জীবনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে তিনি বাংলার মালদহ জেলায় এসে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন এবং এখানেই মুনশি হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তাঁর প্রশাসনিক কর্মজীবনের সূচনা হয় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ‘কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট’ জর্জ উডনীর অধীনে ডাক-মুনশি বা পোস্টমাস্টারের পদে নিযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে। ইতিহাসচর্চায় তাঁর দক্ষতা ও আগ্রহের প্রতি আস্থা রেখে উডনী ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে বাংলার মুসলিম শাসনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্য উৎসাহিত করেন। সেই উৎসাহ ও অনুরোধেই সলিম রিয়াজ-উস-সালাতীন রচনায় হাত দেন এবং ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে এর কাজ সমাপ্ত করেন। গ্রন্থের শিরোনাম ‘রিয়াজ-উস-সালাতীন’ সংখ্যাসূচক; এটি ১৭৮৮ সালকে নির্দেশ করে, যা এর সমাপ্তি-সনের প্রতীকও বটে।
গোলাম হোসেন সলিম ছিলেন ইতিহাসের এক নিবেদিত প্রাণ ছাত্র। তিনি সমকালীন ইতিহাসচর্চার পদ্ধতি, উৎসসংগ্রহের নিয়ম এবং আখ্যান রচনার রীতি সম্পর্কে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর গ্রন্থের মুখবন্ধ চারটি পৃথক শাখায় বিভক্ত—প্রথম শাখায় রয়েছে বাংলার সীমানা, ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জনসংখ্যা সম্পর্কে বিবরণ; দ্বিতীয় শাখায় তিনি বাংলার জনগণের উৎপত্তি, জীবনযাত্রা ও আচার-অনুষ্ঠানের কিছু চিত্র অঙ্কন করেছেন; তৃতীয় শাখায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন প্রধান শহরসমূহের বিবরণ; আর চতুর্থ শাখায় সংক্ষেপে বাংলায় হিন্দু শাসনের ইতিহাস উপস্থাপন করেছেন।
গ্রন্থের মূল অংশ তিনি চারটি বড় অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেন। প্রথম তিন অধ্যায়ে ক্রমান্বয়ে বর্ণিত হয়েছে—(১) দিল্লির সুলতান ও তাঁদের নিযুক্ত গভর্নরগণ, (২) বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ এবং (৩) বাংলায় মুগল শাসন। চতুর্থ অধ্যায়কে তিনি দুই খণ্ডে বিভক্ত করেছেন—প্রথম খণ্ডে রয়েছে বাংলায় আগত বিদেশি শক্তিসমূহের বিবরণ, যেমন পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসি প্রভৃতি; আর দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে ইংরেজদের আগমন, বাণিজ্য বিস্তার এবং বাংলায় তাদের শাসন প্রতিষ্ঠার কাহিনী।
গোলাম হোসেন তাঁর ব্যবহৃত উৎসগুলির পূর্ণাঙ্গ তালিকা দেননি, তবে অভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকে জানা যায় যে তিনি ফারসি ভাষায় রচিত বহু সমসাময়িক মানসম্মত ইতিহাসগ্রন্থের সহায়তা নিয়েছিলেন। সুলতানি যুগের ইতিহাস নির্মাণে তিনি ভরসা করেছেন মিনহাজ-ই-সিরাজের তবকাত-ই-নাসিরী, জিয়াউদ্দীন বরনী ও শামস-ই-সিরাজ আফীফের তারিখ-ই-ফিরুজশাহী, এবং ইয়াহিয়া বিন আহমদের তারিখ-ই-মুবারকশাহী প্রভৃতির উপর। আফগান ও মুগল আমলের ইতিহাস নির্মাণে তিনি ব্যবহার করেছেন আব্বাস শেরওয়ানির তারিখ-ই-শাহী, আবুল ফজলের আকবরনামা ও আইন-ই-আকবরী, বদাউনীর মুন্তখব-উত-তাওয়ারিখ, নিজামউদ্দীন বখশীর তবকাত-ই-আকবরী এবং বিজাপুর দরবারে রচিত ফিরিশতার তারিখ-ই-ফিরিশতা। পাশাপাশি তিনি গ্রহণ করেছেন তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী, পাদশাহনামা এবং আলমগীরনামা। নওয়াবি আমলের ইতিহাস রচনায় তিনি সলিমুল্লাহর তারিখ-ই-বাঙ্গালা এবং সৈয়দ গোলাম হোসেন তাবাতাবাইয়ের সিয়ার-উল-মুতাখেরীন ব্যবহার করেছেন। এ ছাড়াও তিনি স্বীকার করেছেন যে, একটি ‘ছোট বই’ এবং হাজী মুহাম্মদ আরিফ কান্দাহারির রচিত আরেকটি গ্রন্থ তাঁর কাজে লেগেছিল—যা দুর্ভাগ্যক্রমে আজ আর পাওয়া যায় না।
গোলাম হোসেন সলিম শুধু গ্রন্থপাঠে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। তিনি স্থাপত্যনিদর্শন ও শিলালিপি থেকেও তথ্য সংগ্রহ করেছেন। গৌড় ও পান্ডুয়া—সুলতানি আমলের বাংলার দুই রাজধানী—তিনি নিজে পরিদর্শন করেন। সেখানে মসজিদ, সমাধি ও অন্যান্য স্থাপত্যে সংরক্ষিত শিলালিপির পাঠোদ্ধার করে তা ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত করেন। এই শিলালিপিভিত্তিক তথ্যগ্রহণ তাঁর রচনাকে শুধু ঐতিহাসিকভাবে নয়, প্রত্নতাত্ত্বিকভাবেও সমৃদ্ধ করেছে।
তাঁর এই অনন্য উৎসসংগ্রহ সত্ত্বেও তিনি কিছু সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত ছিলেন না। বিশেষ করে কালানুক্রম নির্দেশনায় তিনি বেশ কিছু ভুল করেছেন। কোনো কোনো মুগল সুবাহদারের শাসনকাল তাঁর বর্ণনায় স্থান পায়নি। আশ্চর্যের বিষয়, বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়—আমীর-উল-উমারাহ শায়েস্তা খানের শাসনকাল এবং তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব, বিশেষত ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম বিজয়ের কাহিনী—সলিমের বর্ণনায় প্রায় অনুল্লেখিত রয়ে গেছে। তবে এই ধরনের ত্রুটি সত্ত্বেও রিয়াজ-উস-সালাতীন-এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ। কারণ এটি ছিল বাংলায় মুসলিম শাসনের সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনার প্রথম স্থানীয় প্রচেষ্টা।
গোলাম হোসেন সলিমের এই গ্রন্থ থেকে পরবর্তী ইউরোপীয় ও ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা বিপুলভাবে উপকৃত হয়েছেন। বাংলার প্রথম আধুনিক ঐতিহাসিক হিসেবে পরিচিত ক্যাপ্টেন চার্লস স্টুয়ার্ট তাঁর History of Bengal (১৮১৩) রচনার সময় রিয়াজ-উস-সালাতীন–কে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এর ঘটনাপ্রবাহকে ভিত্তি করেই নিজের আখ্যান সাজান।
১৭৮৮ সালে রিয়াজ-উস-সালাতীন–এর সমাপ্তির প্রায় তিন দশক পর, ১৮১৭ সালে মালদহ শহরে গোলাম হোসেন সলিমের মৃত্যু হয়। তাঁকে মালদহের চক কোরবান আলী এলাকায় সমাহিত করা হয়। তাঁর সমাধি আজও ইতিহাসপ্রেমীদের জন্য স্মৃতিচিহ্ন।
বাংলার ইতিহাসে এই গ্রন্থের স্থান ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গেলে বুঝতে হয় যে, সলিম ছিলেন কেবল একজন ইতিহাসলেখক নন—তিনি ছিলেন ঐতিহাসিক, গবেষক, পর্যটক, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং আংশিক নৃতত্ত্ববিদ। তাঁর রচনায় রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের পাশাপাশি প্রাকৃতিক ভূগোল, সামাজিক আচরণ, নগরজীবন, বিদেশি আগমন, বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও স্থাপত্যকলার বিবরণ মিলিত হয়েছে এক সুসংবদ্ধ ঐতিহাসিক গাঁথায়।
বাংলার ইতিহাসচর্চার ধারায় রিয়াজ-উস-সালাতীন–এর পরে স্থান পায় দক্ষিণ ভারতের বাহমনী বংশ ও আহমদনগরের নিজাম শাহী বংশের ইতিহাস, যা সাইয়েদ আলী তাবাতাবা রচিত বুরহান-ই-মাসীহ্–এ সংরক্ষিত। যদিও এটি মূলত দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ইতিহাস, তবুও এর মধ্যে সুলতানি যুগের শেষ পর্যায়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা বাংলা ও দাক্ষিণাত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝার জন্য সহায়ক।
সবশেষে বলা যায়, রিয়াজ-উস-সালাতীন ছাড়া বাংলায় মুসলিম শাসনের ইতিহাস পুনর্গঠন আধুনিক ঐতিহাসিকদের জন্য অনেক কঠিন হয়ে পড়ত। এর সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেও একে উপেক্ষা করা যায় না, কারণ এটি শুধু তথ্যসংগ্রহ নয়—এটি ছিল বাংলার নিজস্ব ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতা থেকে নির্মিত এক সুবিন্যস্ত ইতিহাসের প্রথম প্রয়াস। এর মধ্য দিয়ে গোলাম হোসেন সলিম কেবল নিজের সময়ের নয়, পরবর্তী প্রজন্মেরও কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।
২। সমসাময়িক সাহিত্য
বাংলার মুসলিম শাসনকালীন ইতিহাস অনুধাবনের ক্ষেত্রে সমসাময়িক সাহিত্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রামাণ্য উৎস। এ সময়ের বহু সাহিত্যকর্মে, প্রত্যক্ষভাবে নয়তো প্রচ্ছন্নভাবে, সমকালীন ইতিহাসের অমূল্য সূত্র সংরক্ষিত আছে। এই সাহিত্যকে সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—ঐতিহাসিক সাহিত্য ও সুফি সাহিত্য। অধিকাংশ রচনাই আরবি ও ফারসি ভাষায় রচিত হলেও, কিছু সংস্কৃত গ্রন্থও এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা যায়, যেগুলিতে মুসলিম শাসনামলের উল্লেখযোগ্য সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা প্রতিফলিত হয়েছে।
ঐতিহাসিক সাহিত্যের ধারায় প্রথমেই উল্লেখযোগ্য আল-সাখাভী রচিত আল-জাউ-উল-লামী গ্রন্থ। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর বিশিষ্ট মুসলিম কবি, পণ্ডিত ও সুলতানদের সম্পর্কে এতে বিশদ বিবরণ রয়েছে। বিশেষত বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ এবং জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ কর্তৃক মক্কা ও মদিনায় প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা, জনহিতকর কর্মকাণ্ড ও দানশীলতার যে চিত্র এখানে অঙ্কিত হয়েছে, তা সমকালীন বাংলার ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের জন্য অমূল্য দলিল। এ ধরনের রচনায় কেবল রাজনৈতিক ঘটনা নয়, মুসলিম শাসকদের মানবিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের প্রতিফলনও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।
ঐতিহাসিক সাহিত্যের আলোচনায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নাম আমীর খসরু। তাঁর সাহিত্যকীর্তি মূলত সুফি আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে যুক্ত হলেও, এর মধ্যে রয়েছে সমকালীন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বহু ইঙ্গিত। আবুল হাসান ইয়ামিন উদ্দিন খসরু (১২৫৩–১৩২৫) ছিলেন মধ্যযুগীয় ভারতের এক বিরল প্রতিভা—একাধারে কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, ভাষা-স্রষ্টা ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের কারিগর। তিনি ছিলেন খ্যাতনামা সুফি সাধক হজরত নিজামুদ্দিন আউলিয়ার আধ্যাত্মিক শিষ্য, এবং আধ্যাত্মিক জগতের পাশাপাশি রাজদরবারেও সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত।
আমীর খসরুর জন্ম হয়েছিল উত্তর ভারতের পাটিয়ালায়। তাঁর পিতা আমীর সাইফ উদ্দিন মাহমুদ ছিলেন তুর্কি বংশোদ্ভূত, আর মাতা ছিলেন রাজপুত কন্যা—এই দুই ভিন্ন সংস্কৃতির মেলবন্ধন তাঁর ব্যক্তিত্ব ও শিল্পরুচিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। অল্প বয়সেই তিনি কবিতার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন; মাত্র আট বছর বয়সে তাঁর প্রথম কবিতা রচিত হয়। শৈশবে তিনি ব্যক্তিগত জীবনে একাধিক গভীর আঘাত সহ্য করেন—দিদার মৃত্যুর পরপরই (যার বয়স ছিল ১১৩ বছর) ১২৯৮ সালে মা ও ভাইয়ের মৃত্যু তাঁকে গভীর শোকে নিমজ্জিত করে। এই সময় সঙ্গীতই ছিল তাঁর প্রধান আশ্রয় ও মানসিক পুনর্জাগরণের পথ।
রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয় সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবানের সেনাবাহিনীতে যোগদানের মাধ্যমে। শীঘ্রই তাঁর কাব্য ও সঙ্গীত প্রতিভা দিল্লি দরবারে প্রশংসিত হয়। বলবানের পুত্র বুঘরা খান তাঁর গান শুনে এতটাই মুগ্ধ হন যে, তাঁকে বিপুল স্বর্ণমুদ্রায় পুরস্কৃত করেন এবং বাংলার শাসনভার অর্পণ করেন। যদিও খসরু শাসক হিসেবে বাংলায় স্থায়ী হননি, তবুও এই অভিজ্ঞতা তাঁর রচনায় বাংলা ও তৎকালীন পূর্ব ভারতের সাংস্কৃতিক প্রভাব সঞ্চারিত করে।
দিল্লিতে প্রত্যাবর্তনের পর জালালউদ্দিন খিলজি তাঁকে “আমারত” উপাধিতে ভূষিত করেন, এবং তখন থেকেই তিনি ‘আমীর খসরু’ নামে পরিচিতি লাভ করেন। পরবর্তীতে আলাউদ্দিন খিলজি ও তাঁর পুত্রের জন্য তিনি একাধিক কাব্য ও সঙ্গীত রচনা করেন। তাঁর রচনায় কেবল রাজকীয় প্রশস্তিই নয়, যুদ্ধ, প্রেম, আধ্যাত্মিকতা ও মানবজীবনের নানা দিক উঠে এসেছে।
দিল্লির সুলতানরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য একটি নতুন ভাষার প্রয়োজন অনুভব করলে, সেই প্রয়াসে খসরুই মূল কারিগরের ভূমিকা পালন করেন। ফারসি, আরবি, তুর্কি ও সংস্কৃতের সঙ্গে স্থানীয় খারিবলি ভাষাকে মিলিয়ে তিনি যে ভাষা নির্মাণ করেন, সেটিই ক্রমে উর্দু নামে পরিচিত হয়। এর ফলে প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক নতুন ভাষাগত সেতুবন্ধন গড়ে ওঠে।
আমীর খসরু কেবল কবি ও ভাষা-স্রষ্টাই নন—তিনি ছিলেন এক সঙ্গীত উদ্ভাবক। তবলা ও সেতার—হিন্দুস্থানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের দুটি অপরিহার্য বাদ্যযন্ত্র—তাঁর সৃষ্ট বলে প্রচলিত আছে। আরবি ভাষায় “তার” অর্থ ‘ঢোল’ বা ‘ড্রাম’, সেখান থেকে তবলাশব্দের ব্যুৎপত্তি; আর সেতার শব্দটি ফারসি, যার অর্থ ‘তিন তার’। এই দুটি যন্ত্র মধ্যযুগে হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের সুর ও ছন্দকে নতুন মাত্রা দেয়। খসরু কাওয়ালির জনক হিসেবে সুপরিচিত; তাঁর রচিত সুর ও গানের ধারা আজও ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে বহমান। তিনি দক্ষিণ এশিয়ায় গজল সঙ্গীতেরও প্রথম প্রবর্তক, যা পরবর্তীতে এক স্বতন্ত্র শিল্পরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।
আমীর খসরুর সাহিত্য ও সঙ্গীতকীর্তি শুধু নান্দনিকতায় নয়, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর রচনায় তৎকালীন দিল্লি সুলতানদের শাসননীতি, রাজসভা সংস্কৃতি, যুদ্ধ ও কূটনীতি, এবং সমাজজীবনের বহু দিক অঙ্কিত হয়েছে। তাঁর প্রশস্তিমূলক কবিতার মধ্যেও রাজ্যের রাজনৈতিক ভাবধারা ও সমকালীন ইতিহাসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যা ঐতিহাসিক সাহিত্যের অপরিহার্য অংশ।
বাংলার মুসলিম শাসনকালীন সাহিত্য-ইতিহাসে এ ধরনের রচনার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। যেমন, আল-জাউ-উল-লামী কেবল তথ্যভাণ্ডার নয়—এটি মুসলিম শাসকদের জনকল্যাণমূলক ভূমিকার দলিল; আর আমীর খসরুর রচনা মধ্যযুগীয় ভারতীয় সংস্কৃতির বহুস্বরিক প্রতিচ্ছবি। এসব সাহিত্যকর্ম ঐতিহাসিক তথ্যের পাশাপাশি যুগের মানসিকতা, সংস্কৃতির গতিপ্রকৃতি ও ভাষাগত বিবর্তন বোঝার জন্য অপরিহার্য উৎস।
এভাবে সমসাময়িক ঐতিহাসিক সাহিত্য একদিকে আমাদের প্রামাণ্য দলিল সরবরাহ করে, অন্যদিকে যুগের সাহিত্যিক রুচি, আধ্যাত্মিকতা ও নান্দনিক চেতনার প্রতিফলন ঘটায়। এই সূত্রগুলো ছাড়া বাংলার ও উপমহাদেশের মধ্যযুগীয় ইতিহাসের বহু দিকই আজ আমাদের অজানা থেকে যেত।
আমীর খসরুর জীবন ও কর্ম মধ্যযুগীয় ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায়। তাঁর জীবনকে কালানুক্রমিকভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, প্রতিটি পর্যায়ে তিনি নতুন মাত্রা যোগ করেছেন সাহিত্য, সঙ্গীত ও ভাষার বিকাশে, পাশাপাশি প্রত্যক্ষদর্শীর দৃষ্টিতে সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করেছেন।
তিনি ১২৫৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আমীর সাইফ উদ্দিন মাহমুদ ছিলেন তুর্কি বংশোদ্ভূত সেনানায়ক এবং মা ছিলেন রাজপুত বংশের কন্যা। এই পারিবারিক মিশ্র ঐতিহ্যই তাঁকে শৈশব থেকেই এক বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছিল। ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে পিতার মৃত্যু হলে মাত্র সাত বছরের খসরু মায়ের সঙ্গে দিল্লি পাড়ি জমান। এই সময় থেকেই তিনি দিল্লির রাজসভা, সামরিক শিবির ও সুফি খানকারের সংস্পর্শে আসতে থাকেন।
১২৭২ খ্রিস্টাব্দে তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবানের ভাতিজা মালিক ছাজ্জুর সভাকবি হিসেবে নিয়োজিত হন। এখানেই তাঁর কবিতার প্রথম রাজদরবারীয় স্বীকৃতি মেলে। চার বছর পর, ১২৭৬ খ্রিস্টাব্দে, তিনি বলবানের পুত্র বুঘরা খানের সভাকবি হন। এই সময়েই তাঁর রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তীক্ষ্ণ হতে থাকে। ১২৭৯ সালে তিনি বাসতুল-হায়াত নামক গ্রন্থ রচনা শুরু করেন এবং বাংলায় প্রথম যাত্রা করেন, যা পরবর্তীতে তাঁর রচনায় পূর্ব ভারতের চিত্র অঙ্কনে সহায়ক হয়।
১২৮১ সালে তিনি সুলতান মুহাম্মদের সঙ্গে মুলতান অভিযানে অংশ নেন। পরের বছর, ১২৮৫ খ্রিস্টাব্দে, মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন এবং বন্দি হলেও অলৌকিকভাবে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। এই অভিজ্ঞতা তাঁর কাব্যে যুদ্ধক্ষেত্রের প্রত্যক্ষ বর্ণনা সমৃদ্ধ করে। ১২৮৭ সালে তিনি আমীর আলি হাতিমের সঙ্গে আওধ সফর করেন।
১২৮৮ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ কিরান-উস-সাদাইন রচনা সম্পন্ন হয়, যেখানে তিনি বুঘরা খান ও কায়কোবাদের পিতা-পুত্র মিলনকে “দুই তারকার মিলন” হিসেবে রূপকভাবে বর্ণনা করেছেন। ১২৯০ সালে তিনি মিফতাহুল ফুতুহ শেষ করেন, যা মূলত আলাউদ্দিন খিলজির শাসনকালে বিজয় ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের কাব্যিক দলিল। ১২৯৪ সালে ঘিরাতুল কামাল এবং ১২৯৮ সালে খামসা-ই-নিজামী রচনা সম্পন্ন করেন, যা মধ্যযুগীয় ফারসি কাব্যের উচ্চতম শিখরে তাঁর অবস্থান নিশ্চিত করে।
১৩১০ সালে তিনি খাজাইন-উল-ফুতুহ শেষ করেন—এটি আলাউদ্দিন খিলজির সাম্রাজ্য বিস্তার ও সামরিক সাফল্যের কাব্যিক দলিল। ১৩১৫ সালে রচিত দুয়াল রানি খিজার খান তাঁর অন্যতম রোমান্টিক রচনা, যেখানে রাজনীতি ও প্রেমের মেলবন্ধন দেখা যায়। জীবনের শেষ পর্যায়ে, ১৩২১ সালে, তিনি তুঘলকনামা লেখা শুরু করেন, যা গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের শাসনকালের এক মূল্যবান ইতিহাস। ১৩২৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়, কিন্তু তিনি রেখে যান ভাষা, সাহিত্য ও সঙ্গীতের এমন এক উত্তরাধিকার যা আজও প্রাসঙ্গিক।
এই প্রেক্ষাপটে, আমীর খসরুর রাজনৈতিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিলেন বুঘরা খান—বলবনের কনিষ্ঠ পুত্র ও বাংলার স্বাধীন সুলতানি যুগের প্রবর্তক। ১২৮১ থেকে ১২৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি লখনৌতির গভর্নর এবং পরে (১২৮৭–১২৯১) স্বাধীন সুলতান ছিলেন। প্রাথমিকভাবে সামানা ও সোনমের গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত থাকলেও, তুগরল খানের বিদ্রোহ দমনের অভিযানে পিতার সঙ্গে লখনৌতি আসেন। বিদ্রোহ দমনে প্রায় তিন বছর সময় লাগে; তুগরল নিহত হন এবং তাঁর সহযোগীদের ফাঁসি দেওয়া হয়। বিদ্রোহ দমনের পর বলবন তাঁকে লখনৌতির শাসনভার অর্পণ করেন।
যখন মোঙ্গলদের সঙ্গে যুদ্ধে যুবরাজ মুহাম্মদ নিহত হন, তখন বলবন বুঘরা খানকে দিল্লিতে ডেকে এনে সুলতানি দায়িত্ব নিতে বলেন। কিন্তু বুঘরা খান দিল্লির সিংহাসনের পরিবর্তে বাংলার স্বায়ত্তশাসিত শাসনকে বেশি পছন্দ করেন। গোপনে দিল্লি ত্যাগ করে লখনৌতিতে ফিরে যান—যা ছিল তাঁর স্বাধীন নীতি গ্রহণের সূচনা। এদিকে সিংহাসনে কায়খসরু বসেন, এবং তাঁর মৃত্যুর পর ক্ষমতাহীন কায়কোবাদের শাসন শুরু হয়, কার্যত যা নিয়ন্ত্রণ করতেন প্রধানমন্ত্রী নিজামউদ্দিন।
এই সময় পিতা-পুত্র বিরোধ মেটাতে বুঘরা খান দিল্লির পথে যাত্রা করেন। কায়কোবাদও পিতাকে আটকাতে সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। সরযূ নদীর দুই তীরে দুই শিবির স্থাপন হলেও বিনা রক্তপাতেই পিতা-পুত্রের পুনর্মিলন ঘটে। বুঘরা খান পুত্রকে রাজকার্যে সতর্ক ও বিচক্ষণ হতে উপদেশ দেন। এই ঘটনাই খসরুর কিরান-উস-সাদাইন এ কাব্যময় বর্ণনায় অমর হয়ে আছে।
বুগরা খান পরবর্তীতে লখনৌতিতে ফিরে স্বাধীনভাবে শাসন চালান। ১২৯০ সালে দিল্লিতে কায়কোবাদের পতনের পর বলবন বংশ নিশ্চিহ্ন হয়, এবং মর্মাহত বুঘরা খান পুত্র রুকনুদ্দিন কায়কাউসকে সিংহাসন দিয়ে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময় থেকেই বাংলা কার্যত স্বাধীন নীতি গ্রহণ করে, যা সুলতানি আমলের ভিত্তি স্থাপন করে। সম্ভবত তিনি দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বাংলার সীমানা সম্প্রসারণ শুরু করেন, যা তাঁর উত্তরসূরিদের আমলেও অব্যাহত থাকে। কায়কাউস তাঁর মুদ্রা ও লিপিতে নিজেকে ‘সুলতান-বিন-সুলতান’ হিসেবে অভিহিত করেন, যা প্রমাণ করে যে বুঘরা খান কেবল গভর্নর নন—তিনি কার্যত একজন স্বাধীন শাসক ছিলেন।
আমীর খসরুর জীবন ও বুঘরা খানের রাজনীতি—দুটোই আমাদের মধ্যযুগীয় ভারত ও বাংলার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। খসরুর রচনায় যেমন পিতা-পুত্রের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও পুনর্মিলনের বর্ণনা আছে, তেমনই আছে সুলতানি শাসনের নীতি, যুদ্ধ ও কূটনীতির চিত্র। ফলে তাঁর সাহিত্য শুধু নান্দনিকতায় নয়, ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রেও অমূল্য।
বাংলার মধ্যযুগীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বাহর-উল-হায়াত এক অনন্য দলিল, যা শুধু একটি যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থের অনুবাদ নয়—বরং তা ভারতীয় ও ইসলামি আধ্যাত্মিক ধারার এক বিরল মিলনক্ষেত্র। মূলত সংস্কৃত ভাষায় রচিত অমৃতকুণ্ড নামে পরিচিত এই গ্রন্থটি ছিল এক যোগতত্ত্বভিত্তিক আধ্যাত্মিক সাধনার সারসংকলন। বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার কিছু সময় পর, কামরূপের একজন খ্যাতিমান যোগী—যিনি ভোজর ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত—লখনৌতির রাজধানীতে আগমন করেন। উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম শাসক ও আলেম-উলামার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করা এবং তাঁদের জ্ঞানভান্ডার ও আধ্যাত্মিক ভাবধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হওয়া।
তখন লখনৌতির সুলতান ছিলেন আলী মর্দান খলজী, এবং তাঁর অধীনে কাজীর পদে নিযুক্ত ছিলেন রুকনুদ্দীন সমরকন্দি—যিনি ফারসি ভাষা ও ইসলামি আইনশাস্ত্রে পারদর্শী, একইসঙ্গে সুফি সাধনার সঙ্গেও যুক্ত। ভোজর ব্রাহ্মণ ও কাজীর মধ্যে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল বিস্তৃত—ইসলামের নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর জীবন, তাঁর শিক্ষার মূল দর্শন, তাওহিদ, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন দিক। এই বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক সংলাপ যোগীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। শেষপর্যন্ত ভোজর ব্রাহ্মণ ইসলাম গ্রহণ করেন।
ইসলাম গ্রহণের পরও তাঁর জ্ঞানপিপাসা থেমে থাকেনি। ইসলামি ফিকহ, হাদিস ও তাফসিরসহ শাস্ত্রসমূহ তিনি এমন দক্ষতায় আয়ত্ত করেন যে, তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে ফতোয়া প্রদানের অনুমতি দেওয়া হয়—যা ছিল এক বিরল সম্মান। এই সময় তিনি কাজী রুকনুদ্দীন সমরকন্দিকে উপহার দেন তাঁর প্রিয় সংস্কৃত গ্রন্থ অমৃতকুণ্ড। গ্রন্থটি পড়ে কাজী বিস্মিত হন এবং উপলব্ধি করেন, যোগশাস্ত্রের এই তত্ত্ব ও অনুশীলন মানুষের আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উন্নতিতে কতটা কার্যকর হতে পারে।
কাজী স্বয়ং যোগশাস্ত্রের অনুশীলনে গভীরভাবে নিমগ্ন হন এবং এমন পর্যায়ে পৌঁছান যে, সমসাময়িকরা তাঁকে যোগীদের পর্যায়ে স্থান দিতে শুরু করে। তিনি অমৃতকুণ্ড প্রথমে ফারসিতে অনুবাদ করেন—যার নাম দেন বাহর-উল-হায়াত (“জীবনের সমুদ্র”)। পরবর্তীতে সেই ফারসি পাঠ থেকে একটি আরবি অনুবাদও প্রস্তুত হয়, যার নাম হাউজ-উল-হায়াত (“জীবনের সরোবর”)। আশ্চর্যের বিষয়, উভয় অনুবাদই আজও মুদ্রিত অবস্থায় বিদ্যমান, যা মধ্যযুগীয় ভারত-ইসলামি সাংস্কৃতিক বিনিময়ের এক জীবন্ত নিদর্শন।
এই ক্ষুদ্র অথচ গভীরতাসম্পন্ন গ্রন্থটি মোট দশটি অধ্যায় ও পঞ্চাশটি শ্লোকে বিভক্ত। এর আলোচ্য বিষয় যোগশাস্ত্রের আধ্যাত্মিক পদ্ধতি, শারীরিক আসন, প্রণায়াম ও মনঃসংযোগের কলা। এখানে কেবল দর্শন নয়—বাস্তব অনুশীলনের দিকগুলিও ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যাতে একজন সাধক ধাপে ধাপে তাঁর আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেন। ইসলামের জ্ঞানতত্ত্ব ও সুফি সাধনার সঙ্গে এই যোগশাস্ত্রীয় দর্শনের মেলবন্ধন এক অভিনব দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়ায়।
সুলতান বারবক শাহ (শাসনকাল ১৪৫৯–১৪৭৪ খ্রি.) ছিলেন এমন এক শাসক, যিনি হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের পণ্ডিতদের সমানভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁর আমলে মুসলিম কবি-লেখকদের পাশাপাশি হিন্দু পণ্ডিতরাও অসাধারণ অবদান রাখেন। এই সময় জয়নুদ্দীন রচনা করেন রাসুল বিজয়, যা নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর জীবনীকেন্দ্রিক বাংলা কাব্যের অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন। একই সময়ে ইবরাহিম কাওয়াম ফারসি ভাষায় রচনা করেন ফারহাং-ই-ইব্রাহিম, যা শরফনামা নামেও পরিচিত।
বারবক শাহের আমলে হিন্দু পণ্ডিতদের মধ্যে রায় মুকুল, ব্রহ্মপতি মিশ্র, মালাধর বসু, কৃত্তিবাস ও কুলাধর ছিলেন বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। কৃত্তিবাস রামায়ণ বঙ্গানুবাদে জনমানসে যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। মালাধর বসু রচনা করেন শ্রীকৃষ্ণবিজয়, যা বৈষ্ণব ভক্তিকাব্যের অন্যতম প্রাচীন উদাহরণ। এর ফলে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে বহুধর্মীয় সাংস্কৃতিক সংলাপের এক সৃজনশীল পরিসর গড়ে ওঠে।
এই সময়কাল থেকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি আইনশাস্ত্রগ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে—মুনসাৎ-ই-মাহরু। লেখক আইনুল মুলক এই গ্রন্থে সুলতান ফিরুজ শাহ তুঘলকের শাসনকাল সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানে শুধু রাজনীতিই নয়, প্রশাসনিক কাঠামো, অর্থনৈতিক নীতি, সামরিক কৌশল, এমনকি তুঘলকের সমাজকল্যাণমূলক উদ্যোগগুলিও প্রতিফলিত হয়েছে। ফলে এটি কেবল একটি ফিকহগ্রন্থ নয়—বরং তা রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক দলিল হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ।
ভারতীয় ঐতিহাসিক সাহিত্যের প্রাচীনতম এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ রাজতরঙ্গিণী রচনা করেন কাশ্মীরের মহাকবি কলহন (Kalhana)। তাঁর পিতা চম্পক ছিলেন কাশ্মীরের রাজা হর্ষের অনুগত অমাত্য। কলহন জন্মসূত্রে শৈব ছিলেন, কিন্তু তাঁর রচনায় স্পষ্ট দেখা যায় যে, তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সমসাময়িক অনেক পণ্ডিতের ধারণা, তাঁর গুরু অলকদত্তের পরামর্শেই তিনি এই বিশাল কর্মযজ্ঞে হাত দেন।
কলহন ছিলেন প্রাচীন সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকদের রচনার গভীর পাঠক, এবং সেখান থেকে তথ্য গ্রহণে দ্বিধা করেননি। তবে তিনি কেবল পুরোনো দলিলের পুনরাবৃত্তি করেননি—নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও নতুন তথ্যও সন্নিবেশ করেছেন। রাজতরঙ্গিণীর বিশেষত্ব এই যে, কলহন তাঁর স্বদেশবাসীদের দোষত্রুটি ও অন্যায়-অত্যাচারও অকপটে নিন্দা করেছেন, যা মধ্যযুগীয় অনেক ঐতিহাসিকের ক্ষেত্রে বিরল।
এই গ্রন্থে কাশ্মীরের রাজাদের ধারাবাহিক শাসনকাল, রাজনৈতিক চক্রান্ত, সামরিক সংঘর্ষ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ধর্মীয় অনুশাসন ও সামাজিক প্রথার এক বিস্তৃত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কলহন জ্যোতির্বিজ্ঞানেও পারদর্শী ছিলেন, এবং তাঁর রচনায় গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি সম্পর্কিত বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর নিরপেক্ষতা ও প্রমাণভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি রাজতরঙ্গিণীকে কেবল সাহিত্য নয়, ইতিহাসেরও এক প্রামাণ্য দলিল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
এইভাবে, বাহর-উল-হায়াত থেকে শুরু করে বারবক শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা বহু ভাষিক সাহিত্যধারা, মুনসাৎ-ই-মাহরুর মতো প্রশাসনিক-ঐতিহাসিক দলিল, এবং রাজতরঙ্গিণীর মতো প্রাচীন রাজবংশীয় ইতিহাস—সবই প্রমাণ করে যে, মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে জ্ঞানচর্চা কখনও একক ধর্মীয় বা ভাষাগত সীমানায় আবদ্ধ ছিল না। বরং, পারস্পরিক বিনিময়, অনুবাদ ও সংলাপের মধ্য দিয়ে এখানে এক সমৃদ্ধ, বহুস্তরীয় ও বহুমাত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল।
সুফি সাহিত্য বাংলা সংস্কৃতির ইতিহাসে এক অনন্য ধারা, যা শুধু আধ্যাত্মিক সাধনার ভাষাই নয়, মধ্যযুগীয় সমাজ-মনস্তত্ত্ব, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের দলিল হিসেবেও বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। যদিও সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাস নির্মাণে সুফি সাহিত্য প্রধানতম উৎস নয়, তবে আঞ্চলিক ইতিহাস, বিশেষত বাংলার মুসলিম সমাজের আত্মিক জীবন ও ভাবজগত বোঝার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অপরিসীম।
মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে সুফি প্রভাবিত সৃষ্টির সূত্রপাত মূলত সুফিতত্ত্বকে অবলম্বন করে। এর প্রেরণা এসেছিল বহিরাগত সুফি সাধক, দরবেশ ও পীরদের কাছ থেকে, যারা ইসলামি সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, মানবপ্রেম ও সেবার আদর্শ নিয়ে বাংলায় আগমন করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, মুসলিম বিজয়ের পূর্বেই আরব, ইরান ও মধ্য এশিয়ার সুফি সাধকেরা বঙ্গদেশে প্রবেশ করেছিলেন, তবে ত্রয়োদশ শতকে তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজীর বঙ্গবিজয়ের পর তাঁদের আগমন আরও বৃদ্ধি পায়। রাজপুরুষ, বণিক, সৈন্য ও সাধারণ মানুষের পাশাপাশি আলেম, ধর্মপ্রচারক ও পীরদরবেশরা রাজধানী লখনৌতি ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।
ইসলামের মূল বার্তা—সমতা, ন্যায়, সহিষ্ণুতা ও সর্বজনীন প্রেম—বাংলার সামাজিক কাঠামোয় নতুন চেতনার সঞ্চার ঘটায়। বিশেষত সুফিদের জীবনযাপন ও আচার-আচরণ ছিল এতটাই উদার ও মানবিক যে, সমাজের অবহেলিত, নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষ দ্রুত তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ফলে, একদিকে বহিরাগত মুসলিম শাসক ও ধর্মজ্ঞানী আলেমদের প্রভাব, অন্যদিকে ধর্মান্তরিত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণে একটি নবীন মুসলিম সমাজ গড়ে ওঠে। এই নতুন সমাজের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণের জন্য সুফি কবিরা বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা শুরু করেন, যা পরবর্তীকালে “সুফি সাহিত্য” নামে স্বীকৃতি পায়।
ফারসি ও আরবি প্রভাব
সুফিতত্ত্ব-ভিত্তিক সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম বৃহৎ ধারা দেখা যায় ইরানে। সেখানে আবদুর রহমান জামী, নিজামী গঞ্জভী, ওমর খইয়াম, হাফিজ, রুমির মতো কবিরা ফারসি ভাষায় দিওয়ান, মসনভি, গজল, রুবাইয়াৎ, খমসা ইত্যাদি আঙ্গিকে অনন্য সব রচনা করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে আমির খসরুর মতো কবিরাও একই ধারায় সৃষ্টিকর্ম করেন। বাংলার সুফি কবিরা মূলত এই ফারসি সাহিত্য ও আধ্যাত্মিক কবিতারই প্রভাবে অনুপ্রাণিত হন।
ফারসি ও আরবি সাহিত্যের প্রভাব বাংলায় আসার অন্যতম মাধ্যম ছিল অনুবাদ। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার অল্পকাল পরেই রাজধানী লখনৌতিতে সংস্কৃত ভাষায় রচিত অমৃতকুণ্ড নামক যোগতত্ত্বমূলক গ্রন্থটি প্রথম ফারসিতে (বাহর-উল-হায়াত) এবং পরে আরবিতে (হাওয-উল-হায়াত) অনূদিত হয়। এটি সুফি মহলে জনপ্রিয় হয়, কারণ হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের কাছে যোগতত্ত্ব ও ইসলামি আধ্যাত্মিক দর্শনের সংমিশ্রণ সহজবোধ্য ও গ্রহণযোগ্য ছিল। এই মিশ্রধারার প্রভাবেই বাংলা সুফি সাহিত্য তার প্রথম রূপলাভ করে।
বাংলা সুফি কাব্যের রূপ ও ধারা
বাংলা সুফি সাহিত্যের দুই প্রধান রূপ—শাস্ত্রকাব্য ও পদাবলি।
শাস্ত্রকাব্যে সুফি সাধনার তত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক পথের বিবরণ পাওয়া যায়। পদাবলিতে সুফি সাধকের অন্তর্মুখী ভাবনা, প্রেমানুভূতি, আল্লাহপ্রেমের রূপকল্প এবং ভক্তি-আবেগের প্রকাশ দেখা যায়।
শাস্ত্রকাব্য
বাংলা সুফি শাস্ত্রকাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—শেখ জাহিদের আদ্য পরিচয় (১৪৯৮), সৈয়দ সুলতানের জ্ঞানপ্রদীপ ও জ্ঞানচৌতিশা, যোগকলন্দর (সম্ভবত সৈয়দ মর্তুজার রচনা), শেখ চাঁদের হরগৌরী-সম্বাদ ও তালিবনামা, আবদুল হাকিমের চারি-মাকাম-ভেদ, হাজী মহম্মদের সুরতনামা, মীর মহম্মদ শফির নূরনামা, শেখ মনসুরের সিনামা, এবং আলী রজার আগম ও জ্ঞানসাগর।
এগুলোতে শরিয়ত, তরিকত, হকিকত ও মারিফতের সুফি চার মঞ্জিল, যোগ-চক্র, নাসুত-মলকুত-জবরুত-লাহুতের দেহতত্ত্ব, সৃষ্টির আদি রহস্য, আত্মোপলব্ধি, গুরুতত্ত্ব, এবং হিন্দু যোগসাধনার প্রভাবিত ধ্যানপদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। যেমন—যোগকলন্দর-এ শাহ বু-আলি কলন্দরের উদ্ভাবিত ইরানীয়-ভারতীয় মিশ্র সাধনপদ্ধতির ব্যাখ্যা রয়েছে, যেখানে মূলাধার থেকে শক্তি জাগরণ, মণিপুরে বায়ু নিয়ন্ত্রণ, কলিজায় জ্যোতির মিলন এবং অনাহত চক্রে আল্লাহর জ্যোতির উপলব্ধি—এই ধাপগুলি সুফি সাধনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।
শেখ চাঁদের কাব্যে হিন্দু পুরাণের চরিত্র, যেমন হর ও গৌরী, রূপক-প্রতীকের মাধ্যমে সুফি তত্ত্ব ব্যাখ্যা পেয়েছে। হাজী মহম্মদের সুরতনামা-তে যোগভিত্তিক দেহতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব ও নৈতিক উপদেশ পাশাপাশি এসেছে। আলী রজার কাব্যে সুফি সাধনার পথে ফকিরিপন্থার মাহাত্ম্য বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে—“ফকির হলেই আল্লাহকে পাওয়া যায়” এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁর রচনায়।
সুফি পদাবলি
পদাবলি ধারায় সুফি কবিরা মূলত গীতপদ বা গজলিয়াৎ রচনা করেছেন, যা সুর ও ছন্দে গাওয়ার উপযোগী। এখানে আল্লাহকে চিরন্তন প্রেমিক ও সর্বোচ্চ সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়েছে। মানুষের আত্মা প্রেম ও ভক্তির মাধ্যমে তাঁর সান্নিধ্যে পৌঁছায়—এই ভাবই পদাবলির মূল সুর।
সুফি গুরুর বা মুর্শিদের ভূমিকা এখানে অপরিহার্য—তিনি সাধককে আল্লাহর পথে পরিচালিত করেন। ইন্দ্রিয়নিয়ন্ত্রণ, চিত্তশুদ্ধি, জাগতিক মোহ থেকে মুক্তি, এবং আল্লাহর নিকট নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ—এই ধাপগুলো পদাবলিতে কবিত্বময় ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে।
রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে সুফি কবিরা রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন, যেখানে রাধা প্রতীক আত্মার, কৃষ্ণ প্রতীক আল্লাহর। এই প্রতীকী বিন্যাস এতটাই ব্যাপক যে, অনেক সাহিত্যসমালোচক তাঁদের “মুসলমান বৈষ্ণব কবি” বলে অভিহিত করেছেন।
পদাবলিতে ব্যক্তিগত আবেগ, ঈশ্বরানুসন্ধান, সাধনার সাফল্য-ব্যর্থতা, এবং আধ্যাত্মিক পথের সংগ্রাম—সবই এসেছে। প্রায় শতাধিক সুফি পদকর্তার নাম জানা গেছে, যেমন—আইনুদ্দীন, আফজল, আলাওল, আলী রজা, নাসির মাহমুদ, মীর ফয়জুল্লাহ, শেখ কবির, শেখ চাঁদ, সৈয়দ মর্তুজা, সৈয়দ সুলতান প্রমুখ। অনেকেই শাস্ত্রকাব্যেরও রচয়িতা ছিলেন। সৈয়দ মর্তুজার ষাটের অধিক সুফি পদ পাওয়া গেছে, যেগুলির শীর্ষে রাগতাল উল্লেখ আছে, যা প্রমাণ করে এগুলি গীতউপযোগী ছিল।
সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব
সুফি সাহিত্য বাংলার মধ্যযুগীয় মুসলিম সমাজের অন্তর্মুখী ভাবনার প্রতিচ্ছবি। শাস্ত্রকাব্যে যেমন তত্ত্ব ও সাধনার প্রক্রিয়া লিপিবদ্ধ হয়েছে, তেমনি পদাবলিতে সেই তত্ত্বের আবেগঘন কাব্যিক রূপ ফুটে উঠেছে। এই সাহিত্যধারা কেবল আধ্যাত্মিক সাধনার দলিল নয়, বরং ভাষার বিবর্তন, সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ, এবং ধর্মীয় সহাবস্থানেরও প্রমাণ বহন করে।
সুফি সাহিত্যই প্রথম বাংলায় ইসলামি আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে দেশজ রূপক, প্রতীক, কাহিনি ও ছন্দের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। এভাবে সুফি কবিরা একদিকে ইসলামের গভীর আধ্যাত্মিক দিকটি রক্ষা করেছেন, অন্যদিকে হিন্দু-বৌদ্ধ প্রভাবিত বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে তাকে সমন্বিত করেছেন।
সমরকন্দের সুপ্রসিদ্ধ হানাফি ফিক্হশাস্ত্রবিদ, সুফি চিন্তাবিদ ও বহুগ্রন্থকার কাজী রুকনউদ্দীন আবু হামিদ মোহাম্মদ বিন মোহাম্মদ আল-অমিদী মধ্যযুগীয় বাংলা-ইসলামি সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত যোগতত্ত্বমূলক গ্রন্থ অমৃতকুণ্ড—যা মূলত এক যোগীর আধ্যাত্মিক সাধনা ও জীবনদর্শনের সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর ব্যাখ্যা—তিনি ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন। ইতিহাসের বিচারে এটিই ছিল বঙ্গদেশে ফারসি ভাষায় অনূদিত প্রথম সাহিত্যকর্ম। মাত্র দশটি অধ্যায় ও পঞ্চাশটি শ্লোক নিয়ে গঠিত এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে যোগশাস্ত্রের মূল পথনির্দেশ, ধ্যানপদ্ধতি, শরীর ও মননশীলতার সম্পর্ক, এবং আধ্যাত্মিক লক্ষ্য অর্জনের ধাপসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। আল-অমিদীর এই অনুবাদ কেবল ভাষান্তর নয়; এটি ছিল দুই ভিন্ন আধ্যাত্মিক জগতের—ভারতীয় যোগশাস্ত্র ও ইসলামি তাসাউফের—এক অনন্য সেতুবন্ধন।
গৌড়ের গভর্নর নাসিরউদ্দীন মাহমুদ বগরা খান (শাসনকাল ১২৮৩–১২৯১) ছিলেন শিল্প, সাহিত্য ও বিদ্যার এক উদার পৃষ্ঠপোষক। তাঁর রাজসভা ছিল তৎকালীন ভারতের অন্যতম প্রাণবন্ত সাহিত্যকেন্দ্র, যেখানে কবি ও পণ্ডিতদের মিলন ঘটত অবাধে। দিল্লি থেকে শামসুদ্দীন দবীর, কাজী আছীর প্রমুখ প্রতিভাবান সাহিত্যিক তাঁর আহ্বানে গৌড়ে আসেন। তাঁদের সাহিত্যচর্চা ও ফারসি রচনায় পাণ্ডিত্য এই অঞ্চলে ফারসি ভাষার বিকাশে বিরাট ভূমিকা রাখে। বগরা খানের শাসনামলকে তাই বাংলা অঞ্চলে ফারসি সাহিত্যের এক উন্মেষপর্ব বলা চলে।
একই সময়ে বিহারের খ্যাতনামা সুফি সাধক শেখ শরফুদ্দীন ইয়াহিয়া মুনইয়ারীর শ্বশুর ও আধ্যাত্মিক গুরু, সুবিখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ শেখ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা প্রায় ১২৮২–৮৭ সালের মধ্যে সোনারগাঁওয়ে আগমন করেন। তৎকালীন বাংলার রাজধানী সোনারগাঁও তাঁর আগমনে এক নবজাগরণের আলোকচ্ছটায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এখানে তিনি একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, যা শিক্ষার্থীদের জন্য ছিল এক আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্র, এবং পাশাপাশি খানকাহ স্থাপন করেন, যা সুফি শিষ্যদের আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মাকামাত, যা আধ্যাত্মিক দর্শন ও সাধনাপদ্ধতির এক অনন্য সংকলন, জীবদ্দশাতেই বিপুল খ্যাতি অর্জন করে।
নাসিরউদ্দীন বগরা খানের পুত্র রুকনুদ্দীন কায়কাউস (শাসনকাল ১২৯১–১৩০১) তাঁর পিতার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে অব্যাহত রাখেন। তাঁর সময়েই সোনারগাঁওয়ে ফিক্হশাস্ত্র বিষয়ক নামে-এ-হক নামে এক ফারসি গ্রন্থ রচিত হয়। দশ খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থে প্রায় ১৮০টি কাব্যাংশ সংযোজিত ছিল। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী এটি শেখ আবু তাওয়ামার রচনা, তবে গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক নিজেই উল্লেখ করেছেন যে, মূলত এটি তাঁর এক শিষ্য আবু তাওয়ামার বক্তৃতা ও শিক্ষামূলক আলাপ থেকে সংকলন করেছেন। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, সোনারগাঁও কেবল রাজনৈতিক রাজধানীই ছিল না, বরং ফারসি ভাষা ও ইসলামি আইনচর্চার এক প্রধান কেন্দ্র হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের (১৩৯০–১৪০৯) শাসনামলকে অনেক ঐতিহাসিকই বাংলায় ফারসি সাহিত্যের ‘স্বর্ণযুগ’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ সময়ে ফারসি গদ্য ও পদ্যচর্চার এমন বিস্তার ঘটে যা এর আগে দেখা যায়নি। তাঁর সাহিত্যপ্রীতি ও পাণ্ডিত্যের অন্যতম প্রমাণ মেলে সুফি কবি হাফিজ শিরাজীর সঙ্গে তাঁর পত্রালাপে। জানা যায়, একবার সুলতান গিয়াসউদ্দীন একটি গজল রচনা করতে গিয়ে প্রথম শ্লোকের অর্ধাংশ লিখে বাকিটা সম্পূর্ণ করতে না পেরে তা হাফিজের কাছে পাঠান, এবং তাঁকে বাংলায় আসার নিমন্ত্রণ জানান। হাফিজের জবাবে রচিত শ্লোক—‘সাগ্বি হাদিছে সার্ভ ও গুল ও লালেহ্ মি রাভাদ/ ভীন বাহাছ বা সালাসা গ্বাচছালা মি রাভাদ/ শেকার শেকান শাভান্দ হামে তোতিয়ানে হিন্দ/ যীন কন্দে পারেছি বেহ্ বাংগালেহ্ মি রাভাদ’—সে যুগে বাংলায় ফারসি কাব্যের খ্যাতি ও প্রভাবের এক জীবন্ত দলিল।
পরবর্তী সুলতান জালালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহ (১৪১৫–১৪৩২) ছিলেন ইসলামি জ্ঞানচর্চা ও পাণ্ডিত্যের নিবেদিত পৃষ্ঠপোষক। তাঁর অন্যতম মহৎ কর্ম ছিল মক্কায় একটি মাদ্রাসার অর্থব্যয় বহন, যা সে সময়ে অসাধারণ উদারতা ও ধর্মনিষ্ঠার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হতো।
সুলতান রুকনুদ্দীন বরবক শাহের (১৪৫৯–১৪৭৪) দরবার ছিল জ্ঞানানুরাগী ও সৃজনশীল প্রতিভাদের এক সমৃদ্ধ মিলনক্ষেত্র। এখানে কবি আমির জয়নুদ্দীন হারাবী, খ্যাতনামা চিকিৎসক ও ফারসি অভিধানসম্পাদক আমির শিহাবউদ্দীন হাকিম কিরমানী, কবি মনসুর শিরাজী, মালিক ইউসুফ বিন হামিদ, সাইয়্যেদ জালাল ও সাইয়্যেদ মোহাম্মদ রুকন প্রমুখ তাঁদের বিদ্যাচর্চা ও সাহিত্যসাধনার মাধ্যমে সমৃদ্ধি আনেন। এ সময়েই মাওলানা ইব্রাহিম কাওয়াম ফারুকী প্রাচীনতম ও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফারসি অভিধান ফারহাঙ্গে ইব্রাহিমী সম্পাদনা করেন, যা বিহারের সুফি মখদুম শরফুদ্দীন ইয়াহিয়া মুনইয়ারীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে ‘শরফনামা’ নামেও পরিচিত। অভিধানটি শুধু ভাষাবিদ্যায় নয়, ফারসি সাহিত্যচর্চার ধারাবাহিক বিকাশেও বিশেষ ভূমিকা রাখে।
হুসেন শাহী আমলে, বিশেষত আলাউদ্দীন হুসেন শাহের (১৪৯৩–১৫১৯) শাসনামলে, ফারসি ও আরবি চর্চা বাংলায় ব্যাপক প্রসার লাভ করে। এই সময়ের খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের মধ্যে মোহাম্মদ বুদাই বা সাইয়্যেদ মীর আলাভী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর হিদায়াত-উর-রুমী গ্রন্থ সুফি তত্ত্ব ও নৈতিক শিক্ষার সমন্বয়ে রচিত, যা এ সময়ের আধ্যাত্মিক সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।
বাংলার সুলতানি যুগে (১২০৩–১৫৭৬) জনহিতৈষী ও সংস্কৃতিমনা সুলতানগণ সাহিত্য ও বিদ্যার চর্চাকে সর্বতোভাবে উৎসাহিত করেছেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় ফারসি সাহিত্য এক দৃঢ় ভিত্তি পায়, যা পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে সুফি সাহিত্য ও স্থানীয় কাব্যধারার সঙ্গে মিশে এক নতুন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে তোলে।
সুফি দরবেশ ও সাধকেরা ইসলামের আধ্যাত্মিক বার্তা প্রচারে যেমন মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন, তেমনি বাংলার সাহিত্যের এক বড় অংশ সুফি ভাবধারার প্রভাবে গড়ে উঠেছে। সুফি সাহিত্যের দুটি প্রধান রূপ ছিল—একটি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও তার দার্শনিক ব্যাখ্যা, অপরটি ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীত, যা প্রধানত পদাবলি আকারে প্রচলিত ছিল। বাউল ও মুর্শিদি গানের মাধ্যমে এই ধারা সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছায়। এই গানগুলিতে শিষ্যের আত্মবিনাশ, পরিশুদ্ধি, এবং ঈশ্বরপ্রাপ্তির নানা ধাপের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।
হাজী মোহাম্মদ ও সৈয়দ সুলতান এই ধারার গুরুত্বপূর্ণ লেখক। হাজী মোহাম্মদের নূর জামাল কাব্য দার্শনিক গভীরতার দিক থেকে সৈয়দ সুলতানের জনন প্রদীপ অপেক্ষা সমৃদ্ধতর। তাঁর রচনায় পাঠককে প্রথমে শরিয়তের শিক্ষায় প্রবেশ করিয়ে ধীরে ধীরে ওহাদাতুল ওজুদ, সর্বেশ্বরবাদ, এবং ইবনুল আরাবী ও মুজাদ্দিদে আলফে সানির মতবাদে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। মুর্শিদি ও বাউল গানগুলির গভীরে নিহিত তত্ত্বে ইরানি সুফি কবি মাওলানা জালালউদ্দীন রুমীর মাসনাভী ও শেখ ফরিদউদ্দীন আত্তারের মানতিক উত-তাইর এর সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষণীয়।
এছাড়া সুফি সাধকেরা তাঁদের রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডে চিঠিপত্রেরও ব্যাপক ব্যবহার করেছেন। এই পত্রাবলীর সংকলন সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসের পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করে। এসব চিঠি থেকে তৎকালীন বাংলার দরবারি পরিবেশ, ধর্মীয় সহাবস্থান, শিক্ষাকেন্দ্রের কর্মকাণ্ড, এবং গ্রামীণ-নগরজীবনের নানা দিকের জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায়—যা মধ্যযুগীয় বাংলা-ইসলামি সংস্কৃতির একটি সমৃদ্ধ আর্কাইভ রচনা করে।
৩। বিদেশী পর্যটকদের বিবরণঃ
সুলতানি যুগের ইতিহাসচর্চায় কেবল স্থানীয় ও রাজকীয় দলিলপত্র কিংবা দেশীয় কবি-ইতিহাসবিদদের রচনাই প্রধান উৎস হয়ে ওঠেনি; সমকালীন বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্তও এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কারণ, এ সময় ভারতবর্ষে আগমনকারী পর্যটকদের অনেকে নিছক কৌতূহলী পর্যটক ছিলেন, আবার অনেকে কূটনৈতিক, বাণিজ্যিক কিংবা ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে এই উপমহাদেশে পদার্পণ করেছিলেন। তাঁরা যেসব অঞ্চল ভ্রমণ করেছেন, সেসব অঞ্চলের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবন, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। এই সব বিবরণ, স্থানীয় তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে, ঐ সময়ের বাংলার ইতিহাস ও ভূগোল আরও সমৃদ্ধভাবে প্রতিফলিত হয়।
এই বিদেশি ভ্রমণকারীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং ইতিহাসবিদদের কাছে বিশেষভাবে মূল্যবান নামটি নিঃসন্দেহে ইবনে বতুতা। জন্মসূত্রে মরক্কোর তাঞ্জিয়ের নগরীর অধিবাসী এই অভিযাত্রী ১৩০৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং অল্প বয়সেই বিস্ময়কর এক জীবনযাত্রা শুরু করেন। তাঁর পূর্ণ নাম ছিল শেখ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-লাওয়াতি আল-তাঞ্জি, তবে ইতিহাসে তিনি ‘ইবনে বতুতা’ নামেই অমর হয়েছেন। মাত্র একুশ বছর বয়সে, ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে, তিনি তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন, কিন্তু সেই যাত্রাই পরিণত হয়েছিল এক দীর্ঘ বিশ্বভ্রমণের সূচনায়। পরবর্তী প্রায় তিন দশক তিনি সমগ্র উত্তর আফ্রিকা, আরব উপদ্বীপ, পারস্য, আনাতোলিয়া, মধ্য এশিয়া, পূর্ব আফ্রিকা, ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং চীনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন।
ভারতবর্ষে তাঁর আগমন ঘটে ১৩৩৪ খ্রিস্টাব্দে, যখন দিল্লির সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক তাঁকে দিল্লির প্রধান কাজী হিসেবে নিয়োগ দেন। প্রায় আট বছর তিনি এই পদে বহাল থেকে নানান প্রশাসনিক ও বিচারিক দায়িত্ব পালন করেন। ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে সুলতান তাঁকে চীনে রাষ্ট্রদূত হিসেবে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু পথে জাহাজডুবির শিকার হয়ে তাঁর চীনযাত্রা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পরে তিনি মালয় দ্বীপপুঞ্জে প্রায় এক বছর বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দে সিংহল (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) সফর শেষে তিনি দক্ষিণ ভারতের মাদুরায় কিছুদিন অবস্থান করেন। এখান থেকেই শুরু হয় তাঁর বাংলাভ্রমণ।
ইবনে বতুতার বাংলায় আগমনের উদ্দেশ্য ছিল একান্তই আধ্যাত্মিক—তৎকালীন কামরূপ পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থানরত প্রখ্যাত সুফি সাধক হযরত শাহজালাল মুজারদ-ই-ইয়েমেনীর (শেখ জালালউদ্দীন) সাক্ষাৎ লাভ। ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ জুলাই তিনি প্রথম বাংলায় পদার্পণ করেন, এবং তাঁর বর্ণনায় যে শহরের নাম এসেছে ‘সাদকাঁও’—যা স্পষ্টতই বর্তমান চট্টগ্রামের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এখান থেকে তিনি সরাসরি কামারু (কামরূপ) অভিমুখে রওনা হন, যা তাঁর ভাষ্যমতে এক মাসের পদযাত্রার দূরত্বে অবস্থিত। কামরূপের ভূপ্রকৃতিকে তিনি বিস্তৃত পার্বত্যাঞ্চল হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা চীন সীমান্ত থেকে তিব্বতের অন্তঃপ্রদেশ পর্যন্ত প্রসারিত। আধুনিক গবেষকেরা অনুমান করেন, ইবনে বতুতার ‘কামারু’ আসলে আসামের অন্তর্গত শ্রীহট্ট অঞ্চল, যা খাসিয়া, জৈন্তিয়া ও ত্রিপুরা পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত ছিল।
কামরূপ সফরে ইবনে বতুতা তিন দিন অবস্থান করেন শাহজালালের খানকায়। তাঁর বর্ণনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সুফি সাধকের খানকা শুধু আধ্যাত্মিক সাধনার কেন্দ্রই নয়, দূরদূরান্ত থেকে আগত মুসলিম ও অমুসলিম ভক্তদের মিলনস্থলও ছিল। এখানকার আতিথেয়তা, আধ্যাত্মিক পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁকে গভীরভাবে মুগ্ধ করেছিল।
কামরূপ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি যাত্রা করেন আন-নহর উল-আয্রাক (অর্থাৎ নীল নদী) নামক নদীর তীরে অবস্থিত হবঙ্ক নগরীর উদ্দেশ্যে। পনের দিনের নৌযাত্রায় তিনি পৌঁছান এই সমৃদ্ধ ও সুন্দর নগরে, যা ইতিহাসবিদদের মতে সিলেটের পূর্বদিকে অবস্থিত ভাঙ্গা অঞ্চলের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ইবনে বতুতার বর্ণিত হবঙ্ক নগরের ধ্বংসাবশেষ আজ আর দৃশ্যমান নয়, তবে তাঁর বর্ণনা থেকে ধারণা মেলে যে এটি ছিল বাণিজ্য, কৃষি ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ এক জনপদ।
১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট, হবঙ্ক থেকে নদীপথে যাত্রা করে ইবনে বতুতা পৌঁছান বাংলার রাজধানী সুনুরকাঁও (সোনারগাঁ)-এ। তাঁর চোখে সোনারগাঁও ছিল এক সুরক্ষিত, দুর্ভেদ্য ও সমৃদ্ধ নগর, যা বাণিজ্য ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিল। এখান থেকে তিনি এক চীনা জাহাজে জাভার উদ্দেশ্যে রওনা হন। বাংলায় তাঁর অবস্থানকাল ছিল মাত্র দুই মাসেরও কম, কিন্তু এই স্বল্পসময়ের মধ্যেই তিনি যে স্থানগুলো ভ্রমণ করেছেন এবং যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তা তাঁর ‘রেহলা’ গ্রন্থে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে।
‘রেহলা’র পূর্ণ আরবি নাম তুহফাতুন-নুজ্জার ফি গারাইবিল আমসার ওয়া আজাইবিল আস্ফার। মরক্কোর সুলতান আবু ইনান মারিনির নির্দেশে ইবনে বতুতা তাঁর সমগ্র ভ্রমণকাহিনী সুলতানের সচিব আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ ওরফে ইবনে জুয়াইনের কাছে বর্ণনা করেন। ইবনে জুয়াইন তা লিখিত আকারে সংকলন করেন। এই রচনায় বাংলার সাদকাঁও, কামারু, হবঙ্ক ও সুনুরকাঁও নগরীর সঙ্গে গঙ্গা, যুন এবং আন-নহর উল-আয্রাক নদীর ভৌগোলিক বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁর উল্লেখ অনুযায়ী, সাদকাঁও ছিল সমুদ্র উপকূলবর্তী এক বৃহৎ নগর, যার নিকটে গঙ্গা ও যুন (যমুনা) নদীর মিলনস্থল অবস্থিত। এই নদীগুলোর মিলনস্থল আজকের পদ্মা-যমুনা সংযোগস্থলের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।
আন-নহর উল-আয্রাক, যার অর্থ ‘নীল নদী’, সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, এটি আধুনিক সুরমা নদী। এই নদীপথ ব্যবহার করে যেমন লক্ষ্ণৌতি রাজ্যে পৌঁছানো যেত, তেমনি সহজেই পৌঁছানো যেত সোনারগাঁয়। নদীপথের এই সহজগম্যতা তৎকালীন বাংলার বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডকে সমৃদ্ধ করেছিল।
ইবনে বতুতা বাংলার জলবায়ু ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনায়ও অনন্য। তাঁর ভাষায়, “আমরা পনের দিন নদীর দুপাশে সবুজ গ্রাম ও ফলফলাদির বাগানের মধ্য দিয়ে নৌকায় পাল তুলে চলেছি, মনে হয়েছে যেন আমরা কোনো পণ্যসমৃদ্ধ বাজারের মধ্য দিয়ে চলছি। নদীর দুই কূলে জমিতে জলসেচের পানি কল, সুদৃশ্য গ্রাম ও ফলের বাগান, যেমনটি রয়েছে মিশরের নীলনদের দুই তীরে।” বাংলার প্রাকৃতিক শোভা, শস্যপ্রাচুর্য ও গ্রামীণ জীবনের সচ্ছলতা তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করলেও, এখানকার আর্দ্র ও গুমোট আবহাওয়া—বিশেষত গ্রীষ্মকালে নদীপাড়ের দাবদাহ—তাঁর কাছে অতিশয় পীড়াদায়ক মনে হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেছেন, খোরাসানি ভ্রমণকারীরা এ দেশকে ‘দোজখ-ই-পুর নিয়ামত’—অর্থাৎ ‘প্রাচুর্যে ভরা নরক’—বলে আখ্যায়িত করত, এবং ইবনে বতুতা নিজেও সেই উপমাকে যথাযথ মনে করেছেন।
ইবনে বতুতার বাংলাভ্রমণ যতটা সংক্ষিপ্ত ছিল, ততটাই তা ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর বর্ণনায় শুধু নগর, নদী ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিবরণ নয়; বরং বাংলার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, সুফি প্রভাব, নদীনির্ভর অর্থনীতি এবং নগরজীবনের এক জীবন্ত ছবি ফুটে উঠেছে। তাঁর রচনার ফলে আমরা তৎকালীন বাংলার রাজনৈতিক ভৌগোলিক বিস্তৃতি, বাণিজ্যপথ, আধ্যাত্মিক কেন্দ্র এবং প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে স্পষ্ট ধারণা পাই, তা সমসাময়িক দেশীয় কোনো উৎসে এতটা সুসংহতভাবে প্রতিফলিত হয়নি। তাই সুলতানি যুগের ইতিহাস গবেষণায় ইবনে বতুতার ‘রেহ্লা’ শুধু একটি ভ্রমণবৃত্তান্ত নয়, বরং এক অমূল্য দলিল হিসেবে স্থান পেয়েছে।
ইবনে বতুতার বাংলাসফরের বর্ণনা কেবল ভ্রমণকাহিনী নয়, বরং তা মধ্যযুগীয় বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের এক বিরল দলিল হিসেবে মূল্যবান। তাঁর বিবরণে আমরা সে সময়কার বাংলার রাজনীতি সম্পর্কে এক সুস্পষ্ট ধারণা পাই। তিনি সুলতান ফখরুদ্দিন মুবারক শাহকে অত্যন্ত সম্মান ও প্রশংসার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন—একজন খ্যাতিমান, প্রাজ্ঞ এবং উদার নরপতি হিসেবে, যিনি বহিরাগত বিশেষত ফকির ও সুফি দরবেশদের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ পোষণ করতেন। ইবনে বতুতার লেখনীতে সোনারগাঁয়ের সুলতান ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ এবং লক্ষ্ণৌতির সুলতান আলাউদ্দিন আলী শাহের মধ্যে চলমান তীব্র রাজনৈতিক সংঘাতের চিত্র অত্যন্ত জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে।
তিনি সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদের শাসনকাল থেকে শুরু করে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ ও আলাউদ্দিন আলী শাহের ক্ষমতা লাভ পর্যন্ত বাংলার রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ধারাবাহিক বিবরণ দিয়েছেন। এ বিবরণে সবচেয়ে লক্ষণীয় দিক হলো—ইবনে বতুতা নিজে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাষ্ট্রদূত হয়েও ফখরুদ্দিনকে দিল্লির সুলতানের ‘বিদ্রোহী’ হিসেবে হেয় করার মনোভাব দেখাননি। বরং তিনি তাঁর চারিত্রিক গুণাবলি, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল প্রশংসা করেছেন।
তাঁর বর্ণনায় বাংলার সামাজিক পরিস্থিতিরও এক উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ সুফি দরবেশদের প্রভাবের অধীনে ছিল। বিশেষ করে হযরত শেখ জালালউদ্দিনের খানকা ছিল এক মিলনক্ষেত্র, যেখানে মুসলিম ও অমুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ সমবেত হতো, তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করত, এবং নানা ধরনের উপহার—‘নজর-নেওয়াজ’—অর্পণ করত। এই উপহার সামগ্রী দিয়েই খানকার আগন্তুক ফকির ও মুসাফিরদের জীবিকা নির্বাহ হতো।
তৎকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থায় সুফি-দরবেশদের জন্য বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা ছিল। সুলতানের ফরমান অনুসারে নদী পারাপারের জন্য সাধক বা ফকিরদের কোনো অর্থ প্রদান করতে হতো না, এবং স্থানীয় অধিবাসীদের কর্তব্য ছিল তাঁদের বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ করা। এমনকি রাষ্ট্রীয় নিয়মে নির্ধারিত ছিল যে, কোনো ফকির দরবেশ কোনো শহরে পৌঁছালে তাকে অর্ধ দীনার ভাতা প্রদান করতে হবে। এসব দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়, সে সময়কার সমাজে ধর্মীয় সাধক ও আধ্যাত্মিক নেতাদের জন্য কতটা মর্যাদা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ছিল।
ইবনে বতুতা শেখ জালালউদ্দিনের ব্যক্তিগত জীবন ও কর্মধারার এক মনোমুগ্ধকর চিত্র এঁকেছেন। তাঁর বিবরণে পাওয়া যায় দরবেশের দৈহিক গঠন, বয়স, দৈনন্দিন আহার ও পরিধান, কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন, আধ্যাত্মিক শক্তি ও কেরামতের নিদর্শন, অতিথি অভ্যর্থনার আন্তরিকতা, জনসাধারণের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা, এবং খানকার চারপাশের পরিবেশের বিস্তারিত বর্ণনা।
ইবনে বতুতার লেখনী থেকে বাংলায় তৎকালীন দাসপ্রথার প্রচলন সম্পর্কেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, খোলাবাজারে দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় হতো এবং এর মূল্য নির্ধারণ ছিল তুলনামূলকভাবে কম। উদাহরণ হিসেবে তিনি লিখেছেন, তাঁর চোখের সামনেই এক সুন্দরী তরুণী, যিনি উপপত্নী হিসেবে ব্যবহারের উপযুক্ত বলে বিবেচিত, মাত্র এক স্বর্ণমুদ্রায় বিক্রি হয়েছেন। এমনকি তিনি নিজেও ‘আশুরা’ নামের এক যুবতী দাসী প্রায় অনুরূপ মূল্যে ক্রয় করেছিলেন, যাকে তিনি ‘পরমা সুন্দরী’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর এক সঙ্গী ‘লুলু’ নামে এক সুদর্শন দাস বালককে দুই স্বর্ণ দীনারে কিনেছিলেন।
বাংলার নদীনির্ভর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রেক্ষিতে ইবনে বতুতা গঙ্গা নদীর বিশেষ উল্লেখ করেছেন। তিনি গঙ্গাকে একটি পবিত্র নদী হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, এখানকার হিন্দুরা তীর্থস্নান করে ধর্মীয় আচার পালন করে। পাশাপাশি কামরূপের অধিবাসীদের সম্পর্কে তিনি প্রথমবারের মতো লিখেছেন, তারা যাদুবিদ্যা ও সম্মোহনী মন্ত্রতন্ত্রের চর্চায় সিদ্ধহস্ত এবং এ বিদ্যায় গভীরভাবে অনুরক্ত।
অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে ইবনে বতুতার বিবরণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর মতে, বাংলায় খাদ্যশস্যের বিপুল প্রাচুর্য ছিল এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম এতটাই সস্তা ছিল যে, পৃথিবীর অন্য কোথাও তিনি এমন প্রাচুর্য ও সুলভমূল্য দেখেননি। তিনি শুধু দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসা নয়, বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার সম্পর্কেও লিখেছেন। নদী পথে অসংখ্য নৌকা চলাচল করত—মানুষ ও পণ্য উভয় পরিবহনের জন্য। নদীর তীরে বাজার গড়ে উঠেছিল, এবং সোনারগাঁ বন্দরে জাভা অভিমুখে যাত্রার অপেক্ষায় একটি বিশাল চীনা জাহাজ নোঙর করে ছিল—যা বাণিজ্যের আন্তর্জাতিক চরিত্রের প্রমাণ বহন করে।
তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, বাংলার ধানচালের রপ্তানি মালয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। নদীপথে চলাচলকারী প্রতিটি পণ্যবাহী নৌকায় একটি করে ঢাক রাখা হতো। রাতের বেলায় যখন দুটি নৌকা কাছাকাছি আসত, তখন মাঝিমাল্লারা ঢাক বাজিয়ে পরস্পরের প্রতি শুভেচ্ছা জানাত। এটি শুধু সামাজিক যোগাযোগের প্রকাশ নয়, বরং সম্ভবত একটি বাণিজ্যিক সংকেত—যা নৌকার পরিচয় নিশ্চিত করা ও সম্ভাব্য জলদস্যুতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হতো।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, ইবনে বতুতা বাজারে গিয়ে নিজ চোখে দ্রব্যমূল্য পর্যবেক্ষণ করে একটি তালিকা তৈরি করেছিলেন। তিনি পণ্যের দাম উল্লেখ করেছেন দীনার ও দিরহামে, এবং ওজন নির্ধারণ করেছেন দিল্লির ‘রতল’ পরিমাপ অনুযায়ী। আজকের মুদ্রা ও ওজনের মানে রূপান্তর না করলে এই দামগুলো ঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। গবেষকদের মতে, এক রৌপ্য দীনারকে আনুমানিক আধুনিক এক টাকার সমান ধরা যেতে পারে, এবং এক দিল্লি রতল প্রায় ১৪ সেরের সমান। এই হিসাব অনুযায়ী ইবনে বতুতার প্রদত্ত পণ্যমূল্যের তালিকাকে আধুনিক মানে রূপান্তর করলে দেখা যায়, সে সময় বাংলার দ্রব্যমূল্য বিশ্বের অন্যতম সস্তা ছিল।
ইবনে বতুতার এ বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়, তৎকালীন বাংলায় রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি—সব কিছুই ছিল বহুমাত্রিক এবং বৈশ্বিক বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর পর্যবেক্ষণ শুধু ঐতিহাসিক নয়, নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকেও অমূল্য। বাংলার ভৌগোলিক সৌন্দর্য, সামাজিক রীতি, অর্থনৈতিক প্রাচুর্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রাণচাঞ্চল্য—সব মিলিয়ে তিনি এক সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত বাংলার ছবি এঁকেছেন, যা আজও ইতিহাসের পাতায় জীবন্ত হয়ে আছে।
চৌদ্দ শতকের ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে মূল্যবান কিছু তথ্য আমরা পাই আল-ক্বাল কাসুন্দির সুব-উল-আ’শা গ্রন্থে। উল্লেখযোগ্য যে, এই গ্রন্থের রচয়িতা কখনো নিজে ভারত ভ্রমণ করেননি। তবু তাঁর বর্ণনা প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, কারণ তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গমনকারী পর্যটক, ভূগোলবিদ ও বণিকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত, স্মৃতিকথা ও মৌখিক তথ্যের উপর নির্ভর করে তাঁর বিবরণ রচনা করেছেন। সেই সূত্রে এই গ্রন্থ ভারত-সংক্রান্ত মধ্যযুগীয় আরবি সাহিত্যের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। তাঁর লেখনীতে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি বাণিজ্য, ধর্মীয় জীবন ও সামাজিক রীতিনীতির ছায়াও দেখা যায়।
পরবর্তী যুগে, পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, আরেকজন বিদেশি দূত আব্দুর রাজ্জাক তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তের মাধ্যমে ভারতবর্ষের ইতিহাসে অমূল্য সংযোজন করেন। ১৪৪২ খ্রিস্টাব্দে তিনি পারস্যের শাহ রুখের প্রেরিত দূত হিসেবে কালিকটের শাসক জামিরনের দরবারে উপস্থিত হন। পরবর্তীতে তিনি দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগর সাম্রাজ্য ভ্রমণ করেন এবং এই রাজ্যের সমাজজীবন, প্রশাসনিক কাঠামো, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, রাজকীয় আচার-অনুষ্ঠান ও জনগণের জীবনযাত্রা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর বর্ণনায় বিজয়নগরের সমৃদ্ধি, রাজকীয় শোভাযাত্রা, সুবিশাল নগর-প্রাচীর, বাজারের ঐশ্বর্য, মন্দিরের স্থাপত্যশিল্প ও ধর্মীয় আচার-বিশ্বাসের নিখুঁত চিত্র ফুটে ওঠে। উত্তরকালে বিজয়নগরের ইতিহাস রচনায় তাঁর বিবরণ একটি অপরিহার্য প্রামাণ্য দলিল হয়ে দাঁড়ায়, বিশেষত সুলতানি যুগের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বুঝতে।
সুলতানি যুগে ইউরোপীয় পর্যটক ও বণিকদের আগমনও ভারতের ইতিহাস চর্চায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করে। এ সময় দক্ষিণ ভারতের মধ্যযুগীয় শক্তিধর সাম্রাজ্য বিজয়নগর ইউরোপীয় বণিকদের চোখে “বিসনাগা” নামে পরিচিত ছিল। ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম হরিহর ও তাঁর ভ্রাতা বুক্কা রায় এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে দক্ষিণ ভারতে ইসলামি অভিযানের মোকাবিলা করে তারা নিজেদের ভূখণ্ড সুরক্ষিত করেন এবং ক্রমে আশপাশের অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। ১৬৪৬ সাল পর্যন্ত বিজয়নগর সাম্রাজ্যের আনুষ্ঠানিক অস্তিত্ব বজায় থাকলেও ১৫৬৫ সালের তালিকোট যুদ্ধ দাক্ষিণাত্য সুলতানিদের হাতে তাদের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এর পতনের সূচনা ঘটে। সাম্রাজ্যের রাজধানী বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান কর্ণাটক রাজ্যের হাম্পিতে অবস্থিত, যা আজ ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থল।
ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের মধ্যে ডোমিনগো পেজ, ফার্নাও নানস ও নিকোলো দ্য কন্টি প্রমুখ তাঁদের রচনায় বিজয়নগরের বর্ণনা দিয়েছেন, যেখানে স্থানীয় সাহিত্য ও লোককথার ছাপও রয়েছে। পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও খননকার্যের মাধ্যমে যে নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা তাঁদের বর্ণনাকে দৃঢ় প্রমাণ দিয়েছে—বৃহৎ মন্দির, সুবিশাল প্রাসাদ, সড়ক ব্যবস্থা, জলাধার ও বাজার স্থাপনা সবই সে সময়ের শিল্পোন্নতি ও সমৃদ্ধির নিদর্শন। এর মধ্যে হাম্পির স্থাপত্যসম্ভার নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।
পর্তুগিজদের আগমন সুলতানি যুগের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় উন্মোচন করে। এই সময় বহু পর্তুগিজ বণিক, নাবিক ও ভ্রমণকারী ভারত ভ্রমণ করেন, যাঁদের ভ্রমণকাহিনী শুধু ইতিহাসের দলিল নয়, বরং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যোগাযোগের সাক্ষ্য। ১৪৯৮ সালের ২০ মে, সমুদ্রপথে প্রথম ইউরোপীয় অভিযাত্রী হিসেবে ভাস্কো দা গামা তাঁর নৌবহর নিয়ে মালাবারের উপকূলে, কালিকটের নিকটবর্তী কাপ্পাডুতে এসে পৌঁছান। সেই সময় কালিকটের রাজা সামুদিরি (জামরিণ) তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী পোন্নানিতে অবস্থান করছিলেন। বিদেশি নৌবহরের আগমনের সংবাদ পেয়ে তিনি কালিকটে ফিরে আসেন।
ভাস্কো দা গামা ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য রাজদরবারে ঐতিহ্যবাহী আড়ম্বরপূর্ণ অভ্যর্থনার আয়োজন করা হয়, যেখানে তিন হাজারেরও বেশি সশস্ত্র নায়রের শোভাযাত্রা ছিল। কিন্তু এই সৌজন্য বিনিময়ের পরও জামরিণ ও দা গামার মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। ‘দা গামা’ পর্তুগালের রাজা ডোম ম্যানুয়েলের পক্ষ থেকে চারটি উজ্জ্বল লাল কাপড়ের জোব্বা, ছয়টি টুপি, চার প্রকার প্রবাল, বারোটি আলমাসার, সাতটি পিতলের পাত্র, এক বাক্স চিনি, দুটি তেলের পিপা এবং এক পিপা মধু উপহার দেন। স্থানীয় প্রজারা উপহার তালিকায় সোনা বা রূপা না দেখে বিস্মিত হয়, এবং সম্রাটও তাতে বিশেষ আগ্রহ দেখাননি। একজন মুসলিম বণিক দা গামাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে সতর্ক করেন যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে কোনো রাজদূত নন, বরং একজন জলদস্যু।
ভাস্কো দা গামা ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য করার অনুমতি চাইলে জামরিণ তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং জানিয়ে দেন যে অন্যান্য বিদেশি ব্যবসায়ীদের মতো কর হিসেবে সোনা দিতে হবে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে দা গামা কয়েকজন নায়র ও ষোলো জন জেলেকে জোরপূর্বক বন্দি করে নিয়ে যান। তবু নানা বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তাঁর প্রথম সমুদ্রযাত্রা বাণিজ্যিকভাবে সফল হয়—ফেরার পথে নৌবহরের মালামালের মূল্য অভিযানের খরচের প্রায় ষাট গুণ হয়ে দাঁড়ায়।
১৫০০ সালে দ্বিতীয় পর্তুগিজ নৌবহরের নেতৃত্বে ভারত আসেন পেড্রো আলভারেস কেব্রেল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জামরিণের সঙ্গে শান্তি ও বাণিজ্যচুক্তি করে কালিকটে একটি পর্তুগিজ কারখানা স্থাপন। কিন্তু আরব বণিকদের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, এবং এক ঘটনায় কারখানার সত্তর জন পর্তুগিজ নিহত হয়। ক্ষুব্ধ কেব্রেল প্রতিশোধস্বরূপ কালিকট শহরে গোলাবর্ষণ করেন, ফলে পর্তুগাল ও কালিকটের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়।
১৫০২ সালে চতুর্থ পর্তুগিজ নৌবহরের নেতৃত্বে আবারও ভারতে আসেন ভাস্কো দা গামা। এবার তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জামরিণকে পর্তুগিজ শর্তে বাণিজ্যে বাধ্য করা এবং আগের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া। তিনি ১৫টি অস্ত্রসজ্জিত জাহাজ ও ৮০০ জন নাবিক নিয়ে ফেব্রুয়ারি মাসে লিসবন ত্যাগ করেন। কিছুদিন পর তাঁর চাচাতো ভাই এস্তেভাও দা গামা আরও পাঁচটি জাহাজ নিয়ে অভিযানে যোগ দেন এবং ভারত মহাসাগরে এসে মূল বহরের সঙ্গে মিলিত হন। এই নৌবহরে তাঁর দুই চাচা ভিসেন্তে সভ্রে ও ব্রাস সোদ্রে ভারত মহাসাগরে নৌ-নজরদারির দায়িত্বে ছিলেন, আর তাঁর শালা আলভারো দা আটাইদে ও বোনের স্বামী লোপো মেন্দেস দা ভাসকন্সেলস প্রধান জাহাজের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
এভাবে পর্তুগিজদের সঙ্গে ভারতের উপকূলীয় রাজ্যগুলোর সম্পর্ক শুরু থেকেই ছিল জটিল—একদিকে বাণিজ্যের আকর্ষণ, অন্যদিকে সামরিক সংঘাত ও আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা। তাঁদের ভ্রমণবৃত্তান্ত শুধু সুলতানি যুগের অর্থনৈতিক কাঠামো বোঝার সহায়ক নয়, বরং সমুদ্রপথে ইউরোপ-ভারত সংযোগের প্রথম যুগের রাজনৈতিক উত্তেজনার দলিল হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ।
১৫০২ সালের অক্টোবরে ভাস্কো দা গামার নেতৃত্বে বিশালাকায় পর্তুগিজ নৌবহর ভারত উপকূলে এসে নোঙর করল। সেই সময় মক্কামুখী মিরি নামের এক জাহাজ, যা তীর্থযাত্রীতে পূর্ণ ছিল, সমুদ্রপথে চলাচল করছিল। দা গামা নির্দ্বিধায় সেই জাহাজে আক্রমণ চালিয়ে সমস্ত যাত্রীকে মুক্ত সমুদ্রে হত্যা করলেন। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এই নৃশংসতা এক ভয়াবহ দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। হত্যাযজ্ঞের পর তিনি কালিকটে এসে পেড্রো আলভারেস কেব্রেলের করা বাণিজ্যচুক্তির সংশোধন প্রস্তাব করলেন। জামরিণ যখন নতুন চুক্তিতে সই করতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন, দা গামা তার আগে এক অদ্ভুত শর্ত জুড়ে দিলেন—কালিকট শহর থেকে সমস্ত মুসলমানকে বিতাড়িত করতে হবে। ন্যায়পরায়ণ হিন্দু শাসক জামরিণ এই প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। এর ফলেই ভাস্কো দা গামা সমুদ্রতীরবর্তী দুর্গম স্থান থেকে প্রায় দুই দিন ধরে কালিকট নগরীতে নিরবচ্ছিন্ন গোলাবর্ষণ চালাতে থাকে। শহরের ঘরবাড়ি, বাজার, গুদাম, এমনকি মসজিদ-মন্দির—কোনো কিছুরই রেহাই মেলেনি। ক্ষয়ক্ষতি ছিল বিপুল, নিহত ও আহতের সংখ্যা অগণিত।
এখানেই থেমে থাকেননি দা গামা। কিছু ভারতীয় জাহাজ আটক করে তিনি সেই জাহাজের নাবিকদের হাত, নাক, কান কেটে দেন এবং তাদেরকে অপমানের চিহ্নস্বরূপ জামরিণের কাছে পাঠিয়ে দেন। এভাবে কেবল শারীরিক আঘাত নয়, মানসিক অপমানও চূড়ান্তভাবে প্রদর্শন করা হয়। এই নিষ্ঠুরতা তার দ্বিতীয় সমুদ্রযাত্রার কুখ্যাতিকে ভারত মহাসাগরীয় উপকূলে ছড়িয়ে দেয়।
এই যাত্রাপথে মাদায়ি অঞ্চলে দা গামা কালিকট থেকে মক্কাগামী এক জাহাজ আটক করেন। তাতে প্রায় চার শতাধিক যাত্রী ছিল, যার মধ্যে পঞ্চাশ জন ছিলেন নারী, এবং এক মিশরীয় রাষ্ট্রদূতও যাত্রী ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী থম লোপেজ এবং ইতিহাসলেখক গ্যাস্পার করিয়া বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন কিভাবে দা গামা জাহাজটি লুট করেন, যাত্রীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ দাবি করেন, এবং সেই মুক্তিপণ দিয়ে “ফেজ রাজ্যের সকল খ্রিস্টান দাস মুক্ত করা সম্ভব”—এই যুক্তি সত্ত্বেও, কাউকেই ছেড়ে দেননি। নারী-শিশুরা স্বর্ণালংকার হাতে প্রাণভিক্ষা চাইছিল, কিন্তু দা গামার নিষ্ঠুর মন গলল না। জাহাজটি অবশেষে অগ্নিসংযোগে পুড়িয়ে যাত্রীদের জীবন্ত দগ্ধ করে হত্যা করা হয়।
কালিকট থেকে মুসলমানদের বিতাড়নের দাবির পর জামরিণ তার উচ্চপদস্থ ব্রাহ্মণ উপদেষ্টা তালাপ্পানা নাম্বুথিরিকে আলোচনার জন্য পাঠান। কিন্তু দা গামা ব্রাহ্মণটিকে গুপ্তচর সন্দেহে ধরে তার ঠোঁট ও কান কেটে ফেলে, এবং সেই ক্ষতস্থানে কুকুরের কান জুড়ে দেওয়ার আদেশ দেন—যা ছিল একপ্রকার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অপমানের ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত।
এর বহু আগে, ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দে, পর্তুগালের রাজা ইমানুয়েলের পৃষ্ঠপোষকতায় দা গামা সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে পৌঁছানোর অভিযানে যাত্রা করেছিলেন। যদিও আরব নাবিকরা শত শত বছর আগে থেকেই এই নৌপথে বাণিজ্য করছিল, দা গামা উত্তমাশা অন্তরীপ পেরোনোর পর পথ হারিয়ে আরব নাবিকদের সাহায্য নিতে বাধ্য হন। অবশেষে তাদের সহায়তায় তিনি ১৪৯৮ সালের ২০ মে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে কালিকটে পৌঁছান।
পর্তুগিজরা ইতিপূর্বেই ইউরোপ ও আফ্রিকার সমুদ্রতটে জলদস্যুতার জন্য কুখ্যাত ছিল। ভারতবর্ষে দা গামার আগমনের আসল উদ্দেশ্যও বাণিজ্যের আড়ালে লুটপাট ও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার। এজন্য তিনি গোলমরিচ ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন। কালিকটের রাজা নতুন ক্রেতা ভেবে তাকে স্বাগত জানান। প্রথমে মনে হয়েছিল এরা মুসলমান বণিকদের মতোই বাণিজ্যে যুক্ত হবে। কিন্তু স্থানীয় অভিজ্ঞ মুসলমান বণিকরা দ্রুত বুঝতে পারেন, এই ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের উদ্দেশ্য কেবল বাণিজ্য নয়, বরং সামরিক প্রভাব বিস্তার ও উপনিবেশ স্থাপন। তাদের পরামর্শে রাজা সতর্ক হন।
দা গামা ১৪৯৮ সালের ২৯ আগস্ট ভারতের মানচিত্র, সংবাদ ও বাণিজ্যসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে দেশে ফেরেন। তবে এই ফেরার পথে এক উচ্চপদস্থ ব্রাহ্মণ কর্মকর্তার সাহায্য পান, যিনি হয়তো পুরস্কারের আশায় তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। পরে দা গামা তাকে জাহাজে ডেকে এনে তার দুই হাত ও দুই কান কেটে একটি বাক্সে ভরে জামরিণকে একটি চিঠির সঙ্গে পাঠিয়ে দেন, যেখানে লিখেছিলেন—রাজা যেন এই মাংস রান্না করে খান (ভারতবর্ষ ও ইসলাম – শ্রীদাসগুপ্ত, পৃ. ২১)।
মাত্র দুই বছর পর, ১৫০০ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর, পেড্রো আলভারেজ কাব্রাল তেরোটি জাহাজের নৌবহর নিয়ে ভারতে আসেন এবং কালিকটে একটি সামরিক কুঠি স্থাপন করেন। এসেই মুসলিম বণিকদের মালামাল বোঝাই জাহাজ দখল করতে শুরু করলে মুসলমানরা পাল্টা আক্রমণ চালায় এবং কুঠির প্রধান আইরস কোরিয়াকে হত্যা করে। বহু মানুষ নিহত হয়। এরপর কাব্রাল কোচিনে গিয়ে স্থানীয় রাজাকে কালিকটের রাজা বানানোর প্রলোভন দেখান।
১৫০২ সালে দা গামা পুনরায় বিশাল নৌবহর নিয়ে ভারতে আসেন। কালিকটে এসে আবারও জামরিণকে মুসলমানদের বিতাড়নের দাবি জানান। রাজা প্রত্যাখ্যান করলে শহরে গোলাবর্ষণ চালান। নিরপরাধ বহু মানুষ প্রাণ হারায়। এরপর মক্কাগামী হজযাত্রীদের জাহাজ লুট করে গোটা শহরটিকে প্রায় শ্মশানে পরিণত করেন।
এরপর কাব্রাল কোচিনে গিয়ে দুর্গ ও গির্জা স্থাপন করেন, যা ছিল “এক হাতে অস্ত্র, অন্য হাতে শাস্ত্র” নীতির সুস্পষ্ট উদাহরণ। পর্তুগিজরা গুপ্তচরবৃত্তি চালাতে থাকে, রাজা জামরিণের অনুপস্থিতিতে কালিকটে হামলার পরিকল্পনা করে। অবশেষে ১৫১০ সালের ৩ জানুয়ারি তারা আক্রমণ চালায়, কিন্তু শহরবাসী, বিশেষত মুসলিম বণিক ও মোপলারা, প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং পর্তুগিজদের পিছু হটতে বাধ্য করে।
পরে ইউরোপীয় বর্ণনায় এই ঘটনাকে বিকৃত করে বলা হয়, “ধর্মান্ধ মুসলমান মোপলাদের নিষ্ঠুর আক্রমণে” তারা পরাস্ত হয়েছিল, এবং এর কারণ নাকি ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। অথচ ঐতিহাসিক শ্রীদাসগুপ্ত স্পষ্টভাবে লিখেছেন—”(ইউরোপীয়রা) নিজেদের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখার জন্য ভারতীয় ও আরবদের এই ঐক্যকে ধর্মান্ধতার ভিত্তিতে দাঁড় করিয়েছে, যার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের ইউরোপীয় সাধুতা প্রমাণ করা”।
কালিকট থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর পর্তুগিজরা বুঝতে পারে, মুসলমানদের না সরালে তাদের ব্যবসা বা প্রভাব বিস্তার সম্ভব নয়। তাই ধীরে ধীরে তারা মুসলমানদের সঙ্গে মধুর ব্যবহার শুরু করে এবং ভারতীয়দের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করে।
অবশেষে ১৫২৪ সালে ভাস্কো দা গামার মৃত্যু ঘটে। তার জীবদ্দশার বহু ভয়ঙ্কর কাণ্ড প্রায় গোপনই থেকে যায়। ইউরোপীয় ইতিহাসলেখকরা তার বর্বরতার কথা এড়িয়ে যান, কারণ এতে ইউরোপীয় “সভ্যতার মুখোশ” ক্ষুণ্ণ হতে পারত। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের চরিত্র কলঙ্কিত করে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর রচনা, যাতে ভারতবর্ষকে দীর্ঘদিন ধরে শাসন ও শোষণ করা যায়।
পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতবর্ষের সমৃদ্ধ জনপদগুলির প্রতি ইউরোপীয় বণিক ও অভিযাত্রীদের কৌতূহল দ্রুত বাড়ছিল। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বাজারে ভারতীয় মসলা, বস্ত্র ও রত্নের কদর তখন চরমে; কিন্তু সরাসরি সমুদ্রপথ তখনও ইউরোপীয়দের জন্য উন্মুক্ত হয়নি। এই সময় রাশিয়ার বণিক ও অভিযাত্রী এথানাসিয়াস নিকিতিন প্রায় ১৪৭০ খ্রিস্টাব্দের দিকে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা শেষে এসে পৌঁছান দক্ষিণ ভারতের বাহমনী রাজ্যে। নিকিতিনের ভ্রমণবৃত্তান্ত “A Journey Beyond the Three Seas” আজও ভারত-সংক্রান্ত প্রাচীনতম ইউরোপীয় প্রত্যক্ষ সূত্রগুলির একটি হিসেবে মূল্যবান। তিনি শুধু রাজপ্রাসাদ ও শাসনব্যবস্থার বিবরণই দেননি, বরং ভারতীয় জনজীবনের সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক দিকও লিপিবদ্ধ করেছিলেন। বিশেষত দক্ষিণ ভারতের বাণিজ্য, মুসলিম শাসকদের দরবারের আড়ম্বর, সৈন্যবাহিনীর শক্তি এবং সোনার, রূপোর মুদ্রা প্রচলনের বিবরণ তার লেখায় স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। নিকিতিনের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, সে সময় ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ বাজার যেমন প্রাণবন্ত ছিল, তেমনি সমুদ্রপথে বিদেশি বণিকদের আনাগোনা ছিল নিয়মিত।
এর অর্ধশতাব্দী পরে, ষোড়শ শতাব্দীর সূচনালগ্নে, ভারতীয় উপমহাদেশে আসেন ইতালীয় পরিব্রাজক লুডোভিকো দ্য ভারথেমা। তিনি কেবল দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের বন্দরই নয়, বাংলার ঐশ্বর্য সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। ভারথেমা বিস্ময়ভরা ভাষায় উল্লেখ করেন—এখানে খাদ্যের অভাব নেই, বরং “অপর্যাপ্ত শস্য ও সর্বপ্রকার মাংস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়”। এছাড়া বাংলার চিনির প্রাচুর্য, উৎকৃষ্ট মানের আদা এবং তুলো তার দৃষ্টি কাড়ে। তার ভাষ্যমতে, পৃথিবীর অন্য কোথাও এই সব দ্রব্য এমন অধিক পরিমাণে পাওয়া যেত না। তিনি বাংলার ধনশালী বণিকদের সমৃদ্ধির কথাও তুলে ধরেন এবং জানান যে, প্রতি বছর প্রায় পঞ্চাশটি জাহাজ সূতী ও রেশমি বস্ত্র বোঝাই করে বঙ্গদেশ থেকে বিভিন্ন দেশে যাত্রা করত। ভারথেমা এই বস্ত্রের নানা প্রকারভেদ ও নামও নথিভুক্ত করেন। এসব বস্ত্র তুরস্ক, সিরিয়া, আরবসহ সমগ্র ভারতে বিপুল চাহিদাসম্পন্ন ছিল।
বাংলা শুধু বস্ত্রশিল্পেই নয়, রত্ন ব্যবসাতেও প্রসিদ্ধ ছিল। সে সময় বহু জহরত ব্যবসায়ী দূরদেশ থেকে এখানে আসত। বঙ্গদেশের নদীবন্দরগুলো জাহাজে জাহাজে ভরে থাকত, আর গুদামগুলো ছিল রঙিন কাপড়, মসলা, চিনি ও রত্নে সজ্জিত।
ষোড়শ শতকের প্রথমভাগ থেকে পর্তুগিজ নাবিক ও বণিকরা বঙ্গদেশে বাণিজ্যিকভাবে প্রবেশ করতে শুরু করে। প্রথমদিকে তারা বঙ্গদেশের অধিবাসীদের সঙ্গে তুলনামূলক শান্তিপূর্ণ বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করে। সেই সময় বঙ্গের সর্বাধিক ব্যস্ত বন্দর ছিল সপ্তগ্রাম। এটি ছিল গোদাই নদীর তীরে অবস্থিত এক প্রাচীন নগরী, যেখান থেকে বাংলার অভ্যন্তর ও সমুদ্রগামী বাণিজ্যের সংযোগ ঘটত। কিন্তু ক্রমে নদীপথের পলি জমে নাব্যতা নষ্ট হতে শুরু করলে সপ্তগ্রামের বন্দরব্যবস্থা ধীরে ধীরে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ে।
এরপর পর্তুগিজরা তাদের বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেয় চট্টগ্রামকে। বঙ্গোপসাগরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই বন্দরকে তারা পোর্টো গ্রান্ডি বা ‘বৃহৎ বন্দর’ নামে আখ্যা দেয়। সপ্তগ্রামকে তারা তুলনামূলকভাবে পোর্টো পেকিনো বা ‘ক্ষুদ্র বন্দর’ বলত। পরবর্তীতে সপ্তগ্রামের পরিবর্তে হুগলী প্রধান বন্দরে পরিণত হয়। পর্তুগিজরা যেখানে স্থায়ীভাবে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করত, তাকে তারা ব্যান্ডেল নামে ডাকত। আজও হুগলী ও চট্টগ্রামের কাছে ব্যান্ডেল নামের স্থানগুলির অস্তিত্ব এই ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে।
পর্তুগিজ শাসন ও বাণিজ্যের সময়ে বঙ্গদেশের মানচিত্র প্রথমবারের মতো ইউরোপে প্রচারিত হয়। খ্যাতনামা পর্তুগিজ মানচিত্রকার ডি ব্যারো বঙ্গের ভৌগোলিক ও বাণিজ্যিক বিবরণসহ একটি বিস্তৃত মানচিত্র প্রকাশ করেন। সেখানে এশিয়ার বহু প্রদেশের উল্লেখ থাকলেও বঙ্গদেশকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রামের বর্ণনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে বঙ্গের সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক ঐতিহ্য। সময়ে সময়ে হুগলী ও পিপলী বন্দরকেও ‘পোর্টো পেকিনো’ নামে উল্লেখ করা হতো।
১৫৭০ খ্রিস্টাব্দে ফ্রেড্রিক নামে এক ইউরোপীয় বঙ্গদেশে এসে সপ্তগ্রামের বাণিজ্যের বিস্তার ও পণ্যের প্রাচুর্যের কথা লিপিবদ্ধ করেন। এর কিছু পরে, ষোড়শ শতকের অন্তিমভাগে, ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় আগমন করেন প্রথম ইংরেজ ভ্রমণকারী রালফ ফিচ। তিনি বাংলার বহু অঞ্চলে ভ্রমণ করেন এবং কার্পাস, কার্পাসবস্ত্র ও রেশমি বস্ত্রের বিপুল উৎপাদন ও বাণিজ্যের কথা বিস্তারিতভাবে লেখেন।
ফিচ টাঁড়া, কুচবিহার, হিজলী, বাকলা, শ্রীপুর প্রভৃতি স্থানের বিশেষত্ব তুলে ধরেন। তার বিবরণে উল্লেখ আছে, সোনারগাঁও-এর সূক্ষ্ম মসলিন আন্তর্জাতিক বাজারে এক অনন্য স্থান অধিকার করেছিল। হিজলীতে একপ্রকার তৃণ জন্মাত, যার আঁশ দিয়ে রেশমের মতো ঝকঝকে ও কোমল বস্ত্র তৈরি হতো—এই বিস্ময়কর তথ্যও তার লেখায় পাওয়া যায়। তিনি ধান ও চালের বিপুল উৎপাদনের কথাও উল্লেখ করেন।
ফিচের বর্ণিত সপ্তগ্রামসহ বিভিন্ন বাজারের চিত্র থেকে বোঝা যায়, এগুলো কেবল আঞ্চলিক বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল না—এগুলি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গেও যুক্ত ছিল। এখানে নানা দেশের ব্যবসায়ীরা আসত, পণ্য আমদানি ও রপ্তানি হতো, আর বাজারে ভিনদেশি ভাষা ও পোশাকের বর্ণিল সমাবেশ দেখা যেত।
এই সমস্ত বিবরণ থেকে একদিকে যেমন জানা যায় যে, ষোড়শ শতাব্দীর বঙ্গদেশ ছিল এক অর্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্র, তেমনি স্পষ্ট হয় যে, ইউরোপীয় বণিকদের প্রাথমিক আগমন মূলত বাণিজ্যিক কৌতূহল ও মুনাফার স্বার্থে হলেও, তা ধীরে ধীরে উপনিবেশ বিস্তারের প্রস্ত্ততি পর্যায়ে রূপ নেয়। রুশ বণিক নিকিতিন থেকে শুরু করে ইতালীয় ভারথেমা, আর পরবর্তী ইংরেজ রালফ ফিচ—তাদের প্রত্যেকের চোখে বঙ্গ ছিল এক সমৃদ্ধশালী, প্রাণবন্ত ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র, যেখানে প্রাচুর্যের সঙ্গে মিশে ছিল প্রাচীন ঐতিহ্যের সৌরভ।
চৈনিক বিবরণঃ
পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে ভারত মহাসাগর—যা তৎকালীন চীনা ভৌগোলিক জ্ঞানে পশ্চিম সাগর নামে পরিচিত—ছিল পূর্ব ও পশ্চিমের বাণিজ্য ও কূটনৈতিক যোগাযোগের এক বিশাল সেতুবন্ধন। এই সময় চীনা মিং সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এক অসাধারণ অধ্যায় রচনা করেন অ্যাডমিরাল জেং হি (চীনা উচ্চারণে চেং হো), যিনি ১৪০৫ থেকে ১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মোট সাতবার সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়ে পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া, পারস্য উপসাগর ও আফ্রিকার উপকূল পর্যন্ত নৌ-বহর পরিচালনা করেন। এই বিরাট নৌবহর কেবল বাণিজ্য নয়, কূটনীতি, সাংস্কৃতিক বিনিময় ও রাজনৈতিক বার্তা বহনের জন্যও ব্যবহৃত হতো।
জেং হি-র এই দীর্ঘ অভিযাত্রার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন চারজন প্রধান কর্মকর্তা, যাঁরা প্রত্যেকে ছিলেন অভিজ্ঞ, শিক্ষিত এবং দূরদর্শী। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মা হুয়ান—যিনি কেবল একজন নাবিক বা অনুবাদকই নন, বরং ছিলেন এক অনুসন্ধিৎসু ভ্রমণলেখক, যার বিবরণ আজও পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যযুগীয় ইতিহাসের অন্যতম প্রামাণ্য উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়।
মা হুয়ানের সৌজন্য পদবি ছিল জংদাউ। তিনি চীনের উপকূলীয় প্রদেশ জেজিয়াং-এর শাওজিং জেলার গুইজি নগরের বাসিন্দা ছিলেন। জন্মসূত্রে মুসলমান, মা হুয়ানের পারিবারিক পদবি “মা”—যা চীনে প্রচলিতভাবে মুহাম্মদ (সঃ) নামের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। একইভাবে তার সহযাত্রী গুয়ো চংলী-ও মুসলমান ছিলেন, যদিও “গুয়ো” পদবিটি মুসলিম উৎসজাত কি না, তা নিশ্চিত নয়। চীনা মুসলিমদের আরেকটি প্রচলিত পদবি ছিল ‘পু’, যা আরবি “আবু”, “আবদুল” বা “আবুল”-এর সমার্থক।
এই মুসলিম উত্তরাধিকারের সূত্র জেং হি-র সঙ্গেও মিলে যায়। অ্যাডমিরাল জেং হি নিজেও ছিলেন মুসলমান; তার পারিবারিক নামও ছিল “মা” (পুরো নাম মা হি)। তিনি মধ্য ইউনান প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর দাদা ও পিতা সম্ভবত মঙ্গোল বা আরব বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং দু’জনেই পবিত্র হজ্জ পালন করেছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে, মিং বাহিনী যখন ইউনানের শাসকের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালায়, তখন মা হি ধৃত হন। তাঁকে খোজায় পরিণত করে মিং রাজবংশের তৃতীয় সম্রাট ইয়ংলের হারেমে প্রহরী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। সম্রাটের মায়েরও পদবি ছিল “মা”; রাজকীয় শালীনতার জন্য সম্রাট তাঁর পারিবারিক নাম পরিবর্তন করে দেন “জেং”।
এই পরিবর্তনের পরেও জেং হি ধীরে ধীরে সম্রাট ইয়ংলের আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন। সম্রাট যখনই বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক যোগাযোগ বা বাণিজ্য স্থাপনের উদ্যোগ নিতেন, তখনই জেং হি-কে নেতৃত্বে রাখতেন। বিদেশযাত্রার ক্ষেত্রে খোজাদের নিয়োগ করা ছিল চীনা সম্রাটদের এক প্রথাগত নীতি—কারণ তাঁদের পারিবারিক বা বংশগত স্বার্থসংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ছিল না, এবং তাঁদের বিশ্বস্ততা ছিল প্রায় প্রশ্নাতীত।
মা হুয়ান প্রায় ১৩৮০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন বলে অনুমান করা হয়। মৃত্যুর সঠিক সাল জানা না গেলেও ধারণা করা হয়, ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর গ্রন্থ প্রকাশের কিছু পরেই তিনি প্রয়াত হন। শৈশবে ও যৌবনে তিনি ভালো শিক্ষালাভের সুযোগ পান, এবং আরবি ও ফারসি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন—যা তাঁকে পরবর্তীতে এক অসাধারণ দোভাষীতে পরিণত করে। লেখনভঙ্গিতে ধ্রুপদী চীনা সাহিত্যিক শৈলী ও বৌদ্ধ গ্রন্থের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যদিও তাঁর কবিতা ছিল সহজসরল, তবুও গদ্যে ছিল ভ্রমণবৃত্তান্তের প্রাণবন্ততা ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি।
তিনি প্রথম জেং হি-র নৌবহরে যোগ দেন চতুর্থ অভিযানে (১৪১৩–১৪১৫), যেখানে তিনি সহদোভাষী গুয়ো চংলীর সঙ্গে পারস্য উপসাগরের গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হরমুজ পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। পরবর্তীতে ১৪২১–১৪২৩ খ্রিস্টাব্দে ও ১৪৩১–১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দে আরও দুটি অভিযানে যোগ দেন। শেষ অভিযানে তাঁর সফরের অন্যতম বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল মক্কা পরিদর্শন—যা ছিল তাঁর জীবনের প্রথম ও শেষ হজ্জযাত্রা।
এই তিনটি অভিযানের প্রতিটিতেই চীনা নৌবহর বাংলায় আসে, এবং মা হুয়ান প্রত্যক্ষভাবে এই দেশের ভৌগোলিক অবস্থা, জনজীবন, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভের সুযোগ পান। ১৪১৬ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে তিনি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তের প্রথম খসড়া রচনা করেন, যার নাম দেন ইয়াংয়াই সেংলান (The Overall Survey of the Ocean’s Shores)। ১৪৩৪–১৪৩৬ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে, এবং ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সহযাত্রী গুয়ো চংলী এটি প্রকাশ করেন। রাজকীয় লেখক গু পো প্রদত্ত মুখবন্ধে এই প্রকাশনার সত্যতা নিশ্চিত হয়।
চার সহকারীর মধ্যে ফেই সিন (The Overall Survey of the Star Raft, ১৪৩৬), গং জেন (Records of Foreign Countries in the Western Ocean, ১৪৩৪) এবং মা হুয়ানের বর্ণনা মিলিয়ে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমৃদ্ধ বিবরণ পাওয়া যায়। গং জেনের বিবরণ প্রায় মা হুয়ানের লেখার অনুরূপ হলেও, বিশদ ও গভীরতায় মা হুয়ানের রচনা শ্রেষ্ঠ। তাঁর লেখায় ২০টি দেশের বর্ণনা রয়েছে, যেখানে ইবনে বতুতা মাত্র ১০টি দেশের এবং ফেই সিন ১৮টি দেশের বিবরণ দিয়েছেন—তাও সংক্ষিপ্তভাবে। তুলনায় মা হুয়ানের বিশ্লেষণ অধিক পূর্ণাঙ্গ ও তথ্যবহুল।
বাংলা সম্পর্কে মা হুয়ানের বিবরণ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি “বাং-গে-লা” নামে এই অঞ্চলকে উল্লেখ করেন এবং এখানে আসার জলপথ, নদীপথ, বিভিন্ন শহর ও বন্দর, তাদের পারস্পরিক দূরত্ব ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের বিস্তারিত বর্ণনা দেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এখানকার বস্ত্রশিল্প, বিশেষত সূক্ষ্ম মসলিন, রেশম ও রেশমগুটি উৎপাদন, বিভিন্ন প্রকার শস্য, পানীয় ও মাদক দ্রব্য, লোকের পোশাক-আশাক, অলঙ্কার, মুদ্রা, নৃত্যশিল্পী, বাঘ শিকারি, এমনকি বিবাহ ও শেষকৃত্যের আচার পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ থেকে বোঝা যায়, তিনি বাংলায় অবস্থানকালে কিছুটা বাংলা ভাষাও রপ্ত করেছিলেন।
মা হুয়ান ছিলেন সহিংসতার ঘোর বিরোধী। জাভায় মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপক প্রয়োগ দেখে তিনি গভীরভাবে বিচলিত হন। তার লেখায় কেবল রাজনৈতিক বা বাণিজ্যিক তথ্য নয়, বরং স্থানীয় লোককাহিনী, ধর্মীয় উপাখ্যান ও অজানা জীবজন্তুর বর্ণনাও পাওয়া যায়—যেমন কালিকটে প্রচলিত মোজেস ও স্বর্ণগোবৎসের কাহিনী, এবং চীনে বিরল ফল কাঁঠাল, গন্ডার, জেব্রা, জিরাফ ইত্যাদির চিত্রময় বর্ণনা।
এভাবে, ১৪শ শতকের প্রথম দিক থেকে ১৫শ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় দেড়শো বছরের মধ্যে যাঁরা ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কে মূল্যবান বিবরণ দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ইবনে বতুতা, ওয়াং দাইউয়ান, ফেই সিন, মা হুয়ান, গং জেন ও নিকোলো ডি কন্টি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু চৈনিক পর্যটকদের মধ্যে মা হুয়ানের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, ভাষাগত দক্ষতা ও অনুসন্ধিৎসা তাঁকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। বিজয়নগর ব্যতীত দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় প্রতিটি অঞ্চল, শ্রীলঙ্কা, কুইলোন ও মালদ্বীপ থেকে শুরু করে বাংলার নদীবন্দর পর্যন্ত তাঁর বিবরণে এক উজ্জ্বল বাস্তবতা ও পক্ষপাতহীনতা প্রতিফলিত হয়—যা মধ্যযুগীয় ভ্রমণসাহিত্যে দুর্লভ।
দুয়ার্তে বারবোসা (?-১৫২১) ছিলেন ষোড়শ শতকের শুরুর দিকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্তুগিজ পর্যটক, যিনি কেবল একজন বাণিজ্যিক কর্মকর্তা হিসেবেই নন, বরং একজন গভীর পর্যবেক্ষণশীল ভ্রমণলেখক হিসেবেও ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন। ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রায় ১৫১৭ পর্যন্ত তিনি কানানোর ও কোচিনে পর্তুগিজ ফ্যাক্টর বা বাণিজ্য প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর রচনায় আমরা শুধু বাংলার নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তৃত ভূখণ্ডের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও জনজীবনের এক জীবন্ত চিত্র দেখতে পাই।
বারবোসার পারিবারিক পটভূমি ছিল সম্ভ্রান্ত। তাঁর বাবা দিয়োগো বারবোসা ব্রাগাংকার ডিউকের অধীনে কর্মরত ছিলেন। ১৫০১ সালে তিনি ভারতের উদ্দেশে যাত্রা করেন। বারবোসার চাচা, গোঙ্কালো গিল বারবোসা, ১৫০৩ সালে পেদ্রো আলভারেজ ক্যাবরেলের নেতৃত্বাধীন পর্তুগিজ নৌবহরের সঙ্গে ভারতে আসেন এবং কোচিনে স্থায়ীভাবে থেকে যান। ধারণা করা হয়, দুয়ার্তে নিজেও একই বহরের সঙ্গেই ভারতে পৌঁছান এবং চাচার সঙ্গেই কোচিনে অবস্থান করতে থাকেন। সেই সময়ের মধ্যে তিনি দ্রুত স্থানীয় ভাষা মালয়ালাম আয়ত্ত করে ফেলেন এবং ফ্রান্সিসকো ডি আলবুকার্ক ও কানানোর রাজার মধ্যে কূটনৈতিক আলাপচারিতায় দ্বিভাষী দোভাষীর ভূমিকা পালন করেন।
তাঁর দক্ষতা ও বহুমুখী অভিজ্ঞতার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৫১৩ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে পর্তুগালের রাজার কাছে পাঠানো এক চিঠিতে। তাতে তিনি উল্লেখ করেন যে, কাঙ্ক্ষিত প্রধান লিপিকারকের পদটি তিনি পাননি এবং গভর্নর দিয়োগো কোরেরার বিরুদ্ধে স্থানীয় জনগণের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। ১৫১৫ সালের পরে তিনি পর্তুগালে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৫১৮ সালের মধ্যে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থটি সম্পন্ন করেন। এই গ্রন্থই তাঁকে ইউরোপীয় ভ্রমণসাহিত্যে স্থায়ী খ্যাতি এনে দেয়।
১৫১৯ সালে বারবোসা তাঁর শ্যালক, বিখ্যাত অভিযাত্রী ফারনাও ডি ম্যাগেলানের সঙ্গে ফিলিপাইনের উদ্দেশে যাত্রা করেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে ১৫২১ সালের ২১ এপ্রিল সেবুর দ্বীপের নিকটে ম্যাগেলান নিহত হন এবং একই বছরের ১ মে স্থানীয় রাজার হাতে নির্বিচারে নিহতদের মধ্যে বারবোসাও ছিলেন। এভাবেই এক অসাধারণ জীবন ও দুঃসাহসিক অভিযাত্রা হঠাৎ করেই সমাপ্ত হয়।
বারবোসার বিবরণ প্রথম সংকলিত হয় ১৫৬৩ সালে, ভেনিস থেকে প্রকাশিত রামুসিওর ইতালীয় ভাষার গ্রন্থে। পরবর্তীকালে লিসবনে সংরক্ষিত একটি পর্তুগিজ পাণ্ডুলিপি ১৮১৩ সালে প্রকাশিত হয়। এর স্পেনীয় ভাষার সংস্করণ বার্সেলোনা ও মিউনিখে সংরক্ষিত রয়েছে। প্রথম ইংরেজি অনুবাদ করেন লর্ড স্ট্যানলি (হ্যাকল্যুত সোসাইটি, ১৮৬৫) এবং দ্বিতীয় অনুবাদ, An Account of the Countries Bordering on the Indian Ocean and Their Inhabitants, সম্পন্ন করেন এম.এল. ডেমস (১৯১৮)। এই অনুবাদসমূহ আজও ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক গবেষণার অন্যতম মূল্যবান উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়।
তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে আফ্রিকা, আরব, পারস্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা দেশের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁর বর্ণিত আবিসিনিয়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন, যা আজও অনন্য রূপে মূল্যায়িত হয়। ভারত ও পশ্চিম এশিয়ার মধ্যে প্রাচীন বাণিজ্যিক সম্পর্কের বিষয়ে যাঁরা প্রথম স্পষ্ট ধারণা দেন, বারবোসা তাঁদের অন্যতম। তাঁর লেখায় দেখা যায় কীভাবে পর্তুগিজরা নতুন সমুদ্রপথ — উত্তমাশা অন্তরীপের আবিষ্কার — কাজে লাগিয়ে এই প্রাচীন বাণিজ্যপথকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনে, যার ফলে তুর্কি সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক শক্তি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
লোহিত সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলবর্তী উপজাতিদের মধ্যে কন্যাশিশুর ওপর শল্যচিকিৎসার প্রচলন সম্পর্কেও তিনি প্রমাণযোগ্য বর্ণনা দেন, যা পরবর্তীকালে নৃতত্ত্ববিদেরা নিশ্চিত করেছেন। তিনি এডেন বন্দরের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন কীভাবে লোহিত সাগরের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে এটি ছিল মূল চাবিকাঠি, এবং আলবুকার্কের ব্যর্থতার ফলে তা পর্তুগিজদের দখলে আসেনি। অন্যদিকে হরমুজ প্রণালীর ওপর পর্তুগিজদের কর্তৃত্ব লোহিত সাগর অঞ্চলের সঙ্গে ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল, যা তুর্কিদের রাজস্ব আয় কমিয়ে দেয়।
আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে সমৃদ্ধ ঘোড়া ব্যবসার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পর্তুগিজরা দাক্ষিণাত্যের মুসলিম রাজ্যসমূহ এবং বিজয়নগরে তাদের প্রভাব বিস্তার করে। বারবোসা গুজরাট ভ্রমণকালে সেখানকার মানুষের জীবনধারা, ধর্মীয় প্রথা, ভাষা ও বাণিজ্যের একটি বিস্তৃত চিত্র এঁকেছেন। তাঁর বিবরণে মুসলমানদের সাধারণত “মুর” বলা হলেও, তিনি প্রয়োজনমতো তুর্কি, আরব, পারস্যদেশীয়, খোরাসানি প্রভৃতি জাতিগত পরিচয়ও উল্লেখ করেছেন। হিন্দুদের ক্ষেত্রে তিনি বিশেষত রাজপুত ও ব্রাহ্মণদের আলাদা করে বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ করেছেন জৈন বানিয়াদের, যারা চরম অহিংসা নীতি মেনে চলে—মাংস তো দূরের কথা, জীবন্ত পোকামাকড়ের জীবন রক্ষার্থেও মুসলমানদের অর্থ প্রদান করত।
ক্যাম্বের মুসলমানদের মধ্যে ভাষাগত বৈচিত্র্যের কথাও তিনি বলেছেন—কেউ ছিলেন অভিবাসী, কেউবা নবধর্মান্তরিত। তাঁদের জীবনযাপনে ছিল আড়ম্বর ও অবাধ ভোগের ছাপ। ক্যাম্বের সুতি ও রেশম শিল্প, দক্ষ কারিগরের সুনাম এবং ঘোড়াচালিত গাড়ির প্রাচীনতম ব্যবহার সম্পর্কেও তাঁর বিবরণ অমূল্য ঐতিহাসিক দলিল।
ভারতের পশ্চিম উপকূলের বন্দরনগরীগুলির প্রসঙ্গে বারবোসার বক্তব্য প্রমাণ করে যে, পর্তুগিজ আগমনের প্রাক্কালে ভারতের বাণিজ্য কতটা সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত ছিল। বিশেষ করে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি, রাজধানীর জৌলুস এবং রাজার উদারতার প্রসঙ্গ তাঁর লেখায় গভীর প্রভাব ফেলে। যদিও বাংলা সম্পর্কে তিনি সরাসরি ভ্রমণ করে তথ্য সংগ্রহ করেননি, বরং অন্য উৎস থেকে নির্ভর করেছেন, তথাপি তাঁর “বেঙ্গলা” শহরের উল্লেখ ইতিহাসবিদদের মধ্যে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। কেউ একে সপ্তগ্রাম বলে চিহ্নিত করেছেন।
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, বাংলার বহির্বাণিজ্যে হিন্দু বণিকদের অনুপস্থিতি এবং মুসলিম বণিকদের পূর্ণ আধিপত্য—যা তাঁর বিবরণে স্পষ্ট প্রতীয়মান। মুসলমান বণিকদের হাতে ছিল একাধিক বড় জাহাজের মালিকানা, এবং তাঁরা সুতি কাপড়, চিনি ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলির সঙ্গে সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। খোজার ব্যবসাও মুসলমান বণিকদের নিয়ন্ত্রণে ছিল, যা সে সময়ের বাণিজ্যের একটি বিতর্কিত অথচ গুরুত্বপূর্ণ দিক।
বারবোসার রচনা শুধু বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ হিসেবেই নয়, সমকালীন জাতিতাত্ত্বিক বিবরণ হিসেবেও অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। যদিও তিনি অনেক তথ্যই পরোক্ষভাবে সংগ্রহ করেছিলেন, তবু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তুলনামূলকভাবে নিরপেক্ষ ও অনুসন্ধিৎসু। তাঁর লেখায় মেলে একটি যুগসন্ধিক্ষণের আভাস—যেখানে মধ্যযুগীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যপথ পর্তুগিজ শক্তির বিস্তারে নতুন ভৌগোলিক বাস্তবতায় রূপ নিচ্ছিল, এবং ভারত মহাসাগরীয় বিশ্বের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভারসাম্য বদলে যাচ্ছিল চিরতরে।
৪। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানঃ
সুলতানি যুগের ইতিহাসচর্চায় প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্রের গুরুত্ব অকাট্য। এই যুগের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় চিত্র পুনর্গঠনের জন্য সমকালীন বা পরবর্তী কালের লিখিত ইতিহাস যতটুকু তথ্য দেয়, তার পরিপূরক ও নির্ভরযোগ্য দলিল হিসেবে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণই হয়ে ওঠে সবচেয়ে শক্তিশালী উপাদান। এই প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্রকে মূলত তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—মুদ্রা, শিলালিপি ও স্থাপত্য। এর মধ্যে মুদ্রা শুধু অর্থনৈতিক ইতিহাস অনুধাবনের জন্য নয়, সমগ্র রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো বোঝার ক্ষেত্রেও অমূল্য।
মুদ্রা বলতে এমন এক ধাতবখণ্ডকে বোঝায়, যা নির্দিষ্ট ধাতব বিশুদ্ধি ও নির্ধারিত তৌলরীতি অনুসারে প্রস্তুত এবং সমাজে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই ধাতবখণ্ডে রাষ্ট্র বা শাসকের পক্ষ থেকে উৎকীর্ণ করা হতো নানা প্রতীক, নকশা ও লিপি—যা মুদ্রার প্রামাণ্যতা ও রাষ্ট্র-অনুমোদন নিশ্চিত করত। দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসচর্চার বড় অন্তরায় হলো সমকালীন পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক দলিলের স্বল্পতা। ফলে, প্রাচীন যুগের ইতিহাস কেবল গ্রন্থ বা কাহিনি নির্ভর করলে তা অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ থেকে যেত। এই শূন্যতা পূরণে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ, বিশেষত মুদ্রা, এক অনন্য ভূমিকা পালন করে।
মুদ্রার মুখ্য দিক বা অবভার্সে সাধারণত শাসকের নাম, উপাধি বা প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ থাকত; অপর দিক বা রিভার্সে থাকত ধর্মীয় প্রতীক, দেবদেবীর প্রতিচিত্র, বা কখনও শুধুই লিপি। এই দুই দিকের মিলিত তথ্য আমাদের দেয় শাসকের রাজনৈতিক পরিচয়, ধর্মীয় ঝোঁক, সাম্রাজ্যের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল এবং বহির্বাণিজ্যের ইঙ্গিত। মুদ্রা কেবল লেনদেনের হাতিয়ার নয়—এটি সমকালীন সমাজের অর্থনৈতিক গতিশীলতা, প্রযুক্তিগত উন্নতি, ও রাষ্ট্রশক্তির প্রতিফলন। যদিও বিনিময়ের জন্য কড়িও প্রচলিত ছিল, বিশেষ করে ক্ষুদ্র লেনদেনে, তবু বৃহৎ বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক লেনদেনে রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রাই ছিল অপরিহার্য।
বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দশকে, বখতিয়ার খলজীর গৌড় বিজয়ের মধ্য দিয়ে। পরবর্তী প্রায় একশ ত্রিশ বছরে সমগ্র বাংলায় মুসলিম শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩৩৪ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপী স্বাধীন সুলতানি যুগ। এই সময়ের রৌপ্যমুদ্রা সুলতানদের পরিচয়ের অন্যতম প্রধান প্রমাণ। মুদ্রালিপি থেকে জানা যায় সুলতানদের ধর্মীয় অনুরাগ কতটা গভীর ছিল। অনেকেই তাঁদের ইসলামের প্রতি ভালোবাসা থেকে মুদ্রায় উৎকীর্ণ করিয়েছেন কালেমায়ে তাইয়্যেবা—“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ”। আলী মর্দান খলজীর (১২১০–১৩ খ্রি.) মুদ্রায় প্রথমবার কালেমার উপস্থিতি পাওয়া যায়। পরবর্তীতে শিহাবুদ্দিন বায়জিদ শাহ (১৪১২–১৪ খ্রি.), জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ (১৪১৮–৩৫ খ্রি.), নাসিরুদ্দিন মাহমুদ (১৪৩৪–৫৯ খ্রি.), রুকনুদ্দিন বারবাক শাহ (১৪৫৯–৭৪ খ্রি.), শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪–৮১ খ্রি.), নুরুদ্দিন সিকান্দার (১৪৮১ খ্রি.), জালালুদ্দিন ফতেহ শাহ (১৪৮১–৮৭ খ্রি.), সাইফুদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৪৮৮–৯০ খ্রি.), কুতুবুদ্দিন মাহমুদ (১৪৯০ খ্রি.), শামসুদ্দিন মুজাফফর (১৪৯০–৯৩ খ্রি.) এবং আলাউদ্দিন হোসেন শাহের (১৪৯৩–১৫১৯ খ্রি.) মুদ্রায়ও এই কালেমা উৎকীর্ণ ছিল।
বাংলার বহু সুলতান ইসলামের প্রথম চার খলিফা—হজরত আবু বকর, হজরত ওমর, হজরত ওসমান ও হজরত আলী (রা.)—এর নামও তাঁদের মুদ্রায় খোদাই করিয়েছিলেন। সিকান্দার শাহ (১৩৫৭–৮৯ খ্রি.), গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ (১৩৮৯–১৪১০ খ্রি.), শিহাবুদ্দিন বায়জিদ শাহ, শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ ও শামসুদ্দিন মুজাফফর শাহের মুদ্রায় ‘খোলাফায়ে রাশেদিন’-এর নাম উৎকীর্ণ রয়েছে। এতে স্পষ্ট প্রতিফলিত হয় সুলতানদের ধর্মীয় আনুগত্য ও রাজনৈতিক পরিচয়।
সুলতানরা প্রায়ই নিজেদের মুদ্রায় উপাধি গ্রহণ করতেন, যা কেবল ব্যক্তিগত মর্যাদা নয়, ইসলামের সেবায় তাঁদের অবস্থানও প্রকাশ করত। “গাউসুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন” (ইসলাম ও মুসলিমদের ত্রাণকর্তা) বা “নাসির-উল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন” (ইসলাম ও মুসলিমদের সাহায্যকারী) এই ধরনের উপাধি বহু মুদ্রায় দেখা যায়। কেউ কেউ নিজেদের সরাসরি আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। যেমন কুতুবুদ্দিন মাহমুদ শাহ তাঁর মুদ্রায় ঘোষণা করেছেন—“আল মুয়িদ বিতাইদ আল রহমান, খলিফাতুল্লাহ বিল হুজ্জাত ওয়াল বুরহান”।
রাজ্যবিস্তার বা বিজয়কে আল্লাহর অনুগ্রহ হিসেবে স্বীকার করাও মুদ্রালিপিতে প্রতিফলিত হয়। সিকান্দার শাহের বহু মুদ্রায় উৎকীর্ণ আছে—“নাসির আল দ্বীন, আল্লাহ, আল-কাহির, অলি আল্লাহ”—যা রাজনৈতিক শক্তি ও ধর্মীয় বিশ্বাসের মিশ্রণ।
সুলতানি শাসনে মুদ্রা জারি ছিল সার্বভৌমত্বের প্রতীক। ক্ষমতা গ্রহণ, স্বাধীনতা ঘোষণা কিংবা বিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে নতুন মুদ্রা প্রচলন একপ্রকার রাষ্ট্রীয় ঘোষণা ছিল। ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে গৌড় বিজয়ের পর বখতিয়ার খলজী সুলতান মুহাম্মদ বিন সাম-এর নামে গৌড় থেকে মুদ্রা জারি করেন—যা বাংলায় প্রথম মুসলিম মুদ্রা হিসেবে পরিচিত। স্বাধীন সুলতানি প্রতিষ্ঠার (১৩৩৮ খ্রি.) আগে প্রায় একশ ত্রিশ বছর বাংলা দিল্লি সালতানাতের একটি প্রদেশ ছিল এবং এখানকার মুদ্রা দিল্লির সুলতানদের নামে জারি হতো। কিছু গভর্নর স্বীয় প্রভুর নামে মুদ্রায় নিজের নামও যুক্ত করার অনুমতি পেতেন। আবার কেউ কেউ বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করতেন।
স্বাধীন সুলতানদের প্রায় প্রত্যেকের স্বনামে উৎকীর্ণ মুদ্রা আজও পাওয়া গেছে। যাঁরা দীর্ঘকাল ক্ষমতায় ছিলেন, তাঁদের প্রচুর সংখ্যক রৌপ্যমুদ্রা নানা নকশা ও আকারে আবিষ্কৃত হয়েছে। বাংলায় এই আমলে মূলত তিন ধাতুর মুদ্রা প্রচলিত ছিল—স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র। বহু সুলতানের স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হলেও রৌপ্যমুদ্রাই ছিল সবচেয়ে প্রচলিত। তাম্রমুদ্রার প্রাপ্তি বিরল, কারণ দৈনন্দিন ক্ষুদ্র লেনদেনে কড়ির ব্যবহার তখনও ব্যাপক ছিল।
এই সব মুদ্রা শুধু অর্থনৈতিক লেনদেনের মাধ্যম নয়; এগুলো সুলতানি বাংলার ধর্মীয় জীবন, শিল্পকলার ধারা, রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ইতিহাসের অমূল্য দলিল। প্রতিটি মুদ্রা যেন এক একটি সময়ের নীরব সাক্ষী, যা শতাব্দী পেরিয়েও ইতিহাসের ভান্ডারে অক্ষয় দলিল হিসেবে টিকে আছে।
সুলতানি বাংলার মুদ্রা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ে এর নকশা, শৈলী, লিপি ও প্রতীকের বহুমাত্রিক বৈচিত্র্য—যা একদিকে রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতিফলন, অন্যদিকে বাংলার সংস্কৃতি ও ধর্মীয় মেলবন্ধনের এক অনন্য দলিল। মধ্যযুগীয় মুসলিম মুদ্রা ভারতে প্রবেশ করে আরব বণিক ও শাসকদের হাত ধরে। প্রথম পর্যায়ে এটি মূলত সিন্ধু অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকলেও ধীরে ধীরে উত্তর ভারত ও বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। সপ্তম ও অষ্টম শতকে সিন্ধুর প্রাদেশিক আরব গভর্নররা যে মুদ্রা জারি করতেন, তা ছিল উমাইয়া খিলাফতের মুদ্রার প্রায় হুবহু প্রতিলিপি। এগারো শতকে এসে ভারতীয় ভূখণ্ডে মুসলিম মুদ্রা একটি স্বতন্ত্র রূপ পায়। এ সময়ে দুটি স্পষ্ট ধারা দেখা যায়—
প্রথমত, গজনী সুলতানদের মুদ্রার অনুকৃতি, যা সম্পূর্ণভাবে আরবি লিপিতে উৎকীর্ণ হতো এবং ধর্মীয় দিক থেকে খলিফার কর্তৃত্বের স্বীকৃতি বহন করত। দ্বিতীয়ত, উত্তর ভারতে জারিকৃত এমন কিছু মুদ্রা, যেখানে আরবি ও সংস্কৃত লিপির মিশ্রণ দেখা যেত। এই মিশ্রলিপি কেবল ভাষাগত সমন্বয় নয়, বরং হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির পারস্পরিক প্রভাবের একটি স্পষ্ট নিদর্শন।
বাংলার মুদ্রায়ও হিন্দু সংস্কৃতির ছাপ স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, বখতিয়ার খলজীর মুদ্রায় দেখা যায় ঘোড়সওয়ারের প্রতিকৃতি এবং নাগরী লিপিতে উৎকীর্ণ “গৌড় বিজয়”। আলী মর্দান খলজীর স্বর্ণমুদ্রায় ঘোড়সওয়ার প্রতিকৃতি একইভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ ও জালালুদ্দীন মাহমুদ শাহ তাঁদের মুদ্রায় সিংহ প্রতীক ব্যবহার করেছেন, আর জালালুদ্দীন ফতেহ শাহের মুদ্রায় রয়েছে সাতরশ্মি বিশিষ্ট সূর্যের প্রতীক। এসব চিত্র উপাদান সমকালীন সমাজে প্রতীকের অর্থবহ ভূমিকা ও ধর্মীয় সহনশীলতার ইঙ্গিত বহন করে।
দিল্লির প্রদেশ হিসেবে বাংলায় প্রায় একশ ত্রিশ বছরের শাসনামলে (১২০৫–১৩৩৮ খ্রি.) দুটি ধরনের মুদ্রা চালু ছিল—প্রথমত, দিল্লি সুলতানদের নামে জারিকৃত মুদ্রা, এবং দ্বিতীয়ত, বাংলায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠাকারী গভর্নরদের মুদ্রা। প্রথম বিভাগের মুদ্রাগুলো আবার দুটি উপবিভাগে বিভক্ত: (ক) একমাত্র দিল্লি সুলতানের নামাঙ্কিত মুদ্রা এবং (খ) দিল্লি সুলতান ও বাংলার গভর্নরের যৌথ নামাঙ্কিত মুদ্রা।
বাংলার টাকশাল থেকে আজ পর্যন্ত যে সব মুদ্রা পাওয়া গেছে, তার মধ্যে ঘোরের একজন এবং দিল্লির ছয়জন সুলতানের নামাঙ্কিত মুদ্রা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা হলেন—মুইজউদ্দীন মুহাম্মদ বিন সাম (১২০৩–১২০৬ খ্রি.), শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশ (১২১০–১২৩৬ খ্রি.), জালালুদ্দীন রাজিয়া (১২৩৬–১২৪০ খ্রি.), নাসিরুদ্দীন মাহমুদ (১২৪৬–১২৬৬ খ্রি.), গিয়াসউদ্দীন বালবান (১২৬৬–১২৮৭ খ্রি.), গিয়াসউদ্দীন তুগলক (১৩২০–১৩২৫ খ্রি.) এবং মুহাম্মদ বিন তুগলক (১৩২৫–১৩৫১ খ্রি.)। মুইজউদ্দীন মুহাম্মদ বিন সাম ও ইলতুৎমিশ স্বর্ণ ও রৌপ্য—দুই ধরনের মুদ্রাই প্রচলন করেছিলেন, বাকি সুলতানদের কাছ থেকে কেবল রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গেছে। একমাত্র মুহাম্মদ বিন তুগলকের স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা—তিন প্রকারই প্রচলিত ছিল।
বাংলা বিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে ৬০১ হিজরিতে (১২০৫ খ্রি.) বখতিয়ার খলজী গৌড় থেকে মুহাম্মদ বিন সামের নামে স্বর্ণমুদ্রা জারি করেন। এই মুদ্রার মুখ্য দিকে আরবিতে উপাধিসহ সুলতানের নাম উৎকীর্ণ, আর গৌণ দিকে দণ্ডধারী ঘোড়সওয়ারের প্রতিকৃতি, চারপাশে তারিখ এবং নাগরী লিপিতে “গৌড় বিজয়” লেখা। আশ্চর্যের বিষয়, এখানে বখতিয়ার খলজীর নিজ নাম অনুপস্থিত। একই সময়ে কিছু রৌপ্যমুদ্রাও পাওয়া গেছে, যা ‘ঘোড়সওয়ার’ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।
ইলতুৎমিশও অনুরূপ ঘোড়সওয়ার প্রতিকৃতিসমৃদ্ধ স্বর্ণমুদ্রা জারি করেছিলেন। দিল্লি সুলতানদের রৌপ্যমুদ্রার বৈশিষ্ট্য ছিল মুখ্য দিকে উপাধিসহ সুলতানের নাম উৎকীর্ণ করা এবং অপর দিকে কালেমা বা খলিফার সঙ্গে সম্পর্কসূচক বাক্য—যেমন “নাসির আমিরুল মুমিনিন” বা “ফী আহদে ইমাম আল মুস্তাসিম”। প্রান্তলিপিতে সাধারণত টাকশাল ও সাল উল্লেখ থাকত, অনেক সময় মাসের নামও যুক্ত হতো। সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদের মুদ্রায় প্রথমবার ‘তানকাহ’ শব্দটি দেখা যায়, যা সংস্কৃত ‘টঙ্কা’ থেকে আগত এবং মুদ্রার নাম ও মূল্যমান বোঝাতে ব্যবহৃত। এই সময়ের প্রায় সব রৌপ্যমুদ্রাই পূর্ণ টাকা, ওজনে প্রায় এক ভরি, কারণ অর্ধ বা সিকি মুদ্রা প্রচলিত ছিল না—ক্ষুদ্র লেনদেনের জন্য কড়ি ব্যবহৃত হতো।
যৌথ নামাঙ্কিত মুদ্রার উদাহরণও কম নয়। দিল্লির চারজন সুলতান ও বাংলার চারজন গভর্নরের নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গেছে—(১) গভর্নর দৌলত শাহ বিন মওদুদ, সুলতান ইলতুৎমিশের সঙ্গে, (২) গভর্নর ইখতিয়ারুদ্দীন ইউযবক তুগরল, সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদের সঙ্গে, (৩) গভর্নর নাসিরুদ্দীন ইবরাহিম, সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুগলক ও মুহাম্মদ বিন তুগলকের সঙ্গে, এবং (৪) গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর, সুলতান মুহাম্মদ বিন তুগলকের সঙ্গে। অধিকাংশই রৌপ্যমুদ্রা, তবে গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর ও মুহাম্মদ বিন তুগলকের যৌথ স্বর্ণমুদ্রাও আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব মুদ্রায় কখনও খলিফা ও সুলতানের নামের পাশাপাশি গভর্নরের নামও উৎকীর্ণ, আবার কখনও একপাশে দিল্লি সুলতানের নাম, অন্যপাশে গভর্নরের নাম—প্রান্তে সবসময় টাকশাল ও সাল।
স্বাধীন সুলতানি যুগের সূচনার আগে (১২০৫–১৩৩৮ খ্রি.) বাংলায় যেসব গভর্নর স্বাধীনতা ঘোষণা করে নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চারজন হলেন—আলী মর্দান খলজী, মুগিসউদ্দীন ইউযবক, মুইজউদ্দীন তুগরল ও নাসিরুদ্দীন মাহমুদ (বুগরা খান)। এঁদের পাশাপাশি কয়েকজন সরাসরি স্বাধীন সুলতানও ছিলেন, যারা কোনওদিন দিল্লির গভর্নর ছিলেন না—যেমন গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজী, রুকনুদ্দীন কায়কাউস, শামসুদ্দীন ফিরুজ ও গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর। শামসুদ্দীনের জীবদ্দশাতেই তাঁর তিন পুত্র নিজস্ব মুদ্রা প্রচলনের অধিকার পেয়েছিলেন এবং তাঁদের মুদ্রায় ‘সুলতান বিন সুলতান’ বাক্য যুক্ত করে বংশীয় মর্যাদা প্রদর্শন করা হতো।
১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ সোনারগাঁওয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে মুদ্রা জারি করেন। তাঁর মুদ্রার সময়কাল ১৩৩৮ (৭৩৯ হি.) থেকে ১৩৪৯ (৭৫০ হি.) পর্যন্ত বিস্তৃত। পুত্র ইখতিয়ারউদ্দীন গাজী শাহ ১৩৫২ (৭৫৩ হি.) পর্যন্ত রৌপ্যমুদ্রা প্রচলন করেন। ফখরুদ্দীনের স্বর্ণমুদ্রা অল্পসংখ্যক হলেও, প্রতিবছরের রৌপ্যমুদ্রা বিপুল পরিমাণে পাওয়া গেছে। গাজী শাহের কাছ থেকে কেবল রৌপ্যমুদ্রাই পাওয়া গেছে।
পরে ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁও দখল করে সমগ্র বাংলাকে একীভূত করেন এবং বিভিন্ন টাকশাল থেকে মুদ্রা জারি করেন। প্রাথমিক ইলিয়াসশাহী বংশের চারজন শাসকের (ইলিয়াস শাহ, সিকান্দার শাহ, গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ, সাইফুদ্দীন হামজা শাহ) সকলেরই প্রচুর রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং হামজা শাহ ছাড়া বাকিদের স্বর্ণমুদ্রাও বিদ্যমান।
হামজা শাহের দাস বায়েজীদ ও তাঁর পুত্র আলাউদ্দীন ফিরুজ মাত্র তিন বছর বাংলার সুলতানি ক্ষমতায় ছিলেন এবং স্ব স্ব নামে রৌপ্যমুদ্রা জারি করেছিলেন। ইতিহাসে আলাউদ্দীন ফিরুজের একমাত্র পরিচয় এই মুদ্রাই—যা না থাকলে তাঁর নাম হয়তো বিস্মৃত ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে যেত।
এই ধারাবাহিক মুদ্রা-প্রচলনের ইতিহাস শুধু সুলতানি বাংলার রাজনৈতিক বিবর্তনই নয়, ধর্মীয় মনোভাব, সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জটিল কাঠামোরও এক অমূল্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রতিটি মুদ্রাই যেন এক একটি জীবন্ত সাক্ষী, যা সময়ের ধূলিকণায় আচ্ছাদিত হলেও এখনও স্পষ্টভাবে বলে যায়—কেমন ছিল মধ্যযুগীয় বাংলার রাজনীতি, ধর্ম, শিল্প ও অর্থনীতির চিত্র।
বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে সুলতানি যুগের মুদ্রা কেবল অর্থনৈতিক বিনিময়ের মাধ্যম ছিল না, বরং তা ছিল সম্রাটের ক্ষমতা, ধর্মীয় অভিমুখ, রাজনৈতিক অবস্থান এবং সাংস্কৃতিক রুচিরও প্রতীক। এই মুদ্রাগুলোয় উৎকীর্ণ লিপি, প্রতীক, ভাষা এবং তারিখের ধরন থেকে শাসকের রাজনৈতিক মনোভাব, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও সাংস্কৃতিক প্রভাব সহজেই নির্ণয় করা যায়। এই ধারাবাহিক বিবরণে রাজা গণেশ থেকে শুরু করে হোসেনশাহী আমল পর্যন্ত মুদ্রার বিবর্তন ও বৈশিষ্ট্য ধাপে ধাপে ফুটে ওঠে।
রাজা গণেশ বাংলায় ক্ষমতা গ্রহণের পর মুদ্রা জারি করেন এমন এক বিশেষ রূপে, যা আগে সুলতানি বাংলায় দেখা যায়নি। তাঁর মুদ্রার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল—আরবি বা ফার্সি লিপির পরিবর্তে শুদ্ধ বাংলা লিপির ব্যবহার। হিজরি সনের বদলে তিনি শকাব্দ অনুসারে তারিখ উৎকীর্ণ করান। এর ফলে মুদ্রা বাংলার আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার এক অনন্য স্বাক্ষর হয়ে ওঠে। তাঁর জারিকৃত মুদ্রা পান্ডুনগর, চাটিগ্রাম ও সুবর্ণগ্রাম টাকশাল থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রচেষ্টা ছিল একধরনের সাংস্কৃতিক ঘোষণাপত্র, যা বাংলার নিজস্বতা ও স্থানীয় ভাষার মর্যাদা তুলে ধরেছিল।
রাজা গণেশের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মহেন্দ্রও পিতার অনুকরণে বাংলা লিপিতে মুদ্রা চালু করেন। কিন্তু রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে রাজপরিবারের অন্য পুত্র যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ উপাধি ধারণ করেন। তাঁর শাসনামলে আবার মুদ্রায় আরবি লিপি ও হিজরি সাল ব্যবহারের প্রচলন শুরু হয়। দীর্ঘ বিরতির পর তিনি বাংলার মুদ্রায় কলেমা পুনঃপ্রবর্তন করেন, যা প্রায় দুই শতাব্দী ধরে অনুপস্থিত ছিল। এই কলেমার পুনরাবির্ভাব কেবল ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, রাজনৈতিক বৈধতার ক্ষেত্রেও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, কারণ ইসলামী বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতার প্রতীক হিসেবেই এর ব্যবহার দেখা যায়। তিনি প্রথম পর্যায়ে ১৪১৫ থেকে ১৪১৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এবং পুনরায় ১৪১৮ থেকে ১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার সুলতান হিসেবে ক্ষমতা ধরে রাখেন। তাঁর পুত্র শামসুদ্দীন আহমদ শাহও নিজস্ব মুদ্রা প্রচলন করেন। জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহের স্বর্ণমুদ্রা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পাশাপাশি মর্যাদার প্রতীক হিসেবেও বিবেচিত।
মুদ্রাবিদ্যার গবেষণায় একটি চমকপ্রদ তথ্য এসেছে সাম্প্রতিক আবিষ্কারে—১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দ (৮৩৭ হিজরি) তারিখসম্বলিত গিয়াসুদ্দীন নুসরত শাহ নামে এক অজানা সুলতানের মুদ্রা পাওয়া গেছে, যার উল্লেখ প্রচলিত ইতিহাসে অনুপস্থিত। এটি সুলতানি বাংলার ইতিহাসে এখনো এক রহস্য।
১৪৩৪ খ্রিস্টাব্দ (৮৩৮ হিজরি) থেকে ইলিয়াসশাহী বংশের দ্বিতীয় পর্যায়ে মোট পাঁচজন সুলতান বাংলার মুদ্রা জারি করেন—(১) নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ (১৪৩৫–১৪৫৯), (২) রুকনুদ্দীন বারবক শাহ (১৪৫৯–১৪৭৪), (৩) শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪–১৪৮১), (৪) নূরুদ্দীন সিকান্দার শাহ (১৪৮১) এবং (৫) জালালউদ্দীন ফতেহ শাহ (১৪৮১–১৪৮৭)। এঁদের মধ্যে নূরুদ্দীন সিকান্দারের মুদ্রা দীর্ঘদিন অজানা ছিল; কেবল মুদ্রার মাধ্যমেই তাঁর পরিচয় পাওয়া গেছে। ইতিহাসবিদেরা মুদ্রা বিশ্লেষণ করে জানতে পেরেছেন, তিনি ছিলেন নাসিরুদ্দীন মাহমুদের পুত্র এবং বারবক ও ফতেহ শাহের ভাই। তাঁর শাসনকাল ছিল অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী।
ইলিয়াসশাহীদের পতনের পর ক্ষমতা আসে হাবশী বংশের হাতে। এই বংশের চারজন শাসক—শাহজাদা বারবক (১৪৮৭–১৪৮৮), সাইফুদ্দীন ফিরুজ (১৪৮৮–১৪৯০), কুতুবউদ্দীন মাহমুদ (১৪৯০) এবং শামসুদ্দীন মুজাফফর (১৪৯০–১৪৯৩)—বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। শাহজাদা বারবক ও কুতুবউদ্দীনের মুদ্রা দুর্লভ, তবে মুজাফফর শাহের কামতা বিজয়ের স্মারক মুদ্রা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মুদ্রায় উৎকীর্ণ ‘কামতামরদান ৮৯৮’ বাক্যটি সমকালীন সামরিক সাফল্যের গৌরব বহন করে।
হাবশীদের পর হোসেনশাহী বংশ বাংলার মুদ্রা জারির ইতিহাসে সমৃদ্ধ অধ্যায় রচনা করে। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৪–১৫১৯), নাসিরুদ্দীন নুসরত শাহ (১৫১৯–১৫৩২), আলাউদ্দীন ফিরুজ (১৫৩২) এবং গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ (১৫৩৩–১৫৩৮) স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় প্রকার মুদ্রা প্রচলন করেন। নুসরত শাহের কিছু তাম্রমুদ্রাও আবিষ্কৃত হয়েছে, যা বাংলায় তাম্রমুদ্রা প্রচলনের বিরল প্রমাণ। হোসেন শাহের ‘কামরূপ–কামতা–জাজনগর ও উড়িষ্যা বিজয়ী’ লিপি উৎকীর্ণ স্মারক মুদ্রা বিশেষভাবে ঐতিহাসিক, যা তাঁর সামরিক সাফল্যের দলিল। হোসেনশাহী মুদ্রার প্রাচুর্য থেকে বোঝা যায় যে, এই সময়ে বাংলার অর্থনীতি, বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল।
বাংলার সুলতানি মুদ্রা সাধারণত গোলাকার হলেও জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহের একটি ষড়ভুজাকার ব্যতিক্রমী মুদ্রা ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ওজনের নিরিখে প্রথমদিকে দিল্লির মুদ্রার অনুকরণে ১৭৭ গ্রেইন বা ১১.৬ গ্রাম মান গৃহীত হলেও পরবর্তী কালে তা কমে দাঁড়ায় ১৬৬ গ্রেইন বা ১০.৮ গ্রামে। স্বর্ণমুদ্রা ছিল তুলনামূলকভাবে বিরল, যা প্রধানত বড় লেনদেন, রাজকীয় অনুদান, অথবা স্মারকচিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হতো; অপরদিকে রৌপ্যমুদ্রাই ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান বিনিময় মাধ্যম।
ইসলামী বিশ্বের মুদ্রায় উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক প্রথম কলেমার ব্যবহার চালু করেন। বাংলার সুলতানদের মধ্যেও বহুজন মুদ্রায় কলেমা উৎকীর্ণ করিয়েছেন, যদিও স্বাধীনতার প্রথম যুগে (জালালউদ্দীন মুহম্মদের পূর্ববর্তী সময়ে) অধিকাংশ মুদ্রায় কলেমার পরিবর্তে খিলাফতের প্রতি আনুগত্য প্রকাশক বাক্য ব্যবহৃত হতো। জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ দীর্ঘ ব্যবধানে পুনরায় কলেমা প্রবর্তন করে এই ধারা পুনঃস্থাপন করেন।
খিলাফতের প্রতি মুসলিম শাসকদের মনোভাবও মুদ্রায় প্রতিফলিত হয়। বাংলার স্বাধীন সুলতানরা যেমন, তেমনি দিল্লি-নিযুক্ত গভর্নরদের জারিকৃত মুদ্রাতেও খিলাফতের প্রতি আনুগত্য বা সংযোগের ইঙ্গিত দেখা যায়। এর ধরন চার প্রকারে বিভক্ত—
১. খলিফার নাম সরাসরি উৎকীর্ণ করা—যেমন গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজীর ৬১৯ বা ৬১৭ হিজরি (১২২২ বা ১২২০) এবং ৬২১ হিজরি (১২২৪) সালের মুদ্রায় কলেমার পর বাগদাদের খলিফার উদ্দেশ্যে ‘আল নাসির আমির আল মুমিনিন’ উৎকীর্ণ রয়েছে।
২. খলিফার নাম ছাড়া আনুগত্য প্রকাশ—যেমন সুলতান সিকান্দর শাহের (১৩৫৮–১৩৯০) ৭৮১ হিজরি (১৩৭৯) সালের মুদ্রায় উৎকীর্ণ ‘ইয়ামিন খলিফাতুল্লাহ নাসির আমির আল মুমিনিন শাসসুল ইসলাম ওয়াল মুসলেমিন খুল্লিদাত খিলাফাতে’।
৩. কলেমা ও নবীর প্রতি সম্পর্কসূচক লিপি—যেমন আলাউদ্দীন হোসেন শাহের ৮৯৯ হিজরি (১৪৯৩) সালের মুদ্রায় একপাশে কলেমা, অপর পাশে উৎকীর্ণ ‘আস সুলতান আল আদীল আল বাযিল ওয়ালাদ-ই সাইয়িদ উল মুরসালিন’।
৪. নিজেকে খলিফা ঘোষণা—যেমন জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহের ৮৩১ হিজরি (১৪২৭) সালের মুদ্রায় বৃত্তের মধ্যে উৎকীর্ণ ‘খলিফাতুল্লাহ নাসির আল ইসলাম ওয়াল মুসলেমিন’।
এভাবে সুলতানি বাংলার মুদ্রা ইতিহাস শুধু অর্থনৈতিক লেনদেনের দলিল নয়, বরং রাজনৈতিক ক্ষমতার বৈধতা, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি, সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। প্রতিটি মুদ্রা যেন একটি ক্ষুদ্র ধাতব দলিল, যা সমকালীন বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক চিত্রকে আজও নীরবে বহন করে চলেছে।
বাংলার সুলতানি যুগে মুদ্রা কেবল অর্থনৈতিক বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবেই নয়, বরং রাজনৈতিক ক্ষমতা, প্রশাসনিক কাঠামো এবং সাংস্কৃতিক রুচিরও প্রতীক ছিল। সেই সময়কার শাসকেরা মুদ্রা ব্যবস্থাকে জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য ও কার্যকর করার লক্ষ্যে বিশেষ নীতি গ্রহণ করেছিলেন। রাজধানী-নির্ভর কেন্দ্রীভূত টাকশাল পদ্ধতির পরিবর্তে তাঁরা টাকশাল বিকেন্দ্রীকরণের পথে অগ্রসর হন। এর ফলে রাজধানী ছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে টাকশাল স্থাপন করা হয়, যেখান থেকে স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী মুদ্রা জারি করা সম্ভব হতো। ঐতিহাসিক দলিল ও প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে সুলতানি বাংলার ২৭টিরও বেশি টাকশালের নাম পাওয়া যায়, যদিও এদের সবগুলির ভৌগোলিক অবস্থান এবং পৃথক সত্তা সবসময় নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।
এই টাকশালগুলির নামকরণেও নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। কখনও শাসকেরা রাজধানীর নাম মুদ্রায় উৎকীর্ণ করেছেন, কখনও পিতার নামে শহরের নামকরণ হয়েছে। নামের পূর্বে ‘হজরত জালাল’, ‘ইকলিম’, ‘খিত্তা’, ‘আরসাহ’ প্রভৃতি বিশেষণ ব্যবহারের প্রথাও চালু ছিল। তৎকালীন মুদ্রায় সাল-তারিখ উৎকীর্ণ করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে সংখ্যার পরিবর্তে শব্দ ব্যবহার করা হতো। তবে সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের শাসনামলে প্রথমবারের মতো সাল-তারিখে সংখ্যার ব্যবহার শুরু হয়। সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ পরবর্তীতে মুদ্রার নকশায় বড় পরিবর্তন আনেন—প্রান্তে লিপি উৎকীর্ণ করার রীতি তিনি পরিত্যাগ করেন এবং টাকশালের নাম ও তারিখ সংখ্যায় উৎকীর্ণ করে মুদ্রার বৃত্তাকার মধ্যস্থলে স্থাপন করেন। এই সময় থেকেই টাকশালের নামের পূর্ববর্তী বিশেষণ ব্যবহারের ধারা বিলুপ্ত হয় এবং প্রান্তে অলংকরণমূলক মোটিফ ব্যবহারের মাধ্যমে মুদ্রার নান্দনিকতা বৃদ্ধি পায়।
ঐতিহাসিক সূত্র অনুযায়ী, সুলতানি বাংলার টাকশালগুলির তালিকায় রয়েছে—লাখনৌতি, ফিরুজাবাদ, সাতগাঁও, সোনারগাঁও, মুয়াজ্জমাবাদ, শহর-ই-নও, গিয়াসপুর, ফতেহাবাদ, খলিফাতাবাদ, হোসেনাবাদ, মুজাফফরাবাদ, মাহমুদাবাদ, মুহম্মদাবাদ, আরাকান, তান্ডা, রোটাসপুর, জান্নাতাবাদ, নুসরাতাবাদ, চাওয়ালিস্তান (কামরু), বারবকাবাদ, পান্ডুনগর, সুবর্ণগ্রাম, চাটিগ্রাম, চন্দ্রাবাদ, খলিফাতাবাদ বদরপুর, বঙ্গ এবং শরিফাতাবাদ। তবে এই নামগুলির সবক’টি যে স্বতন্ত্র টাকশাল শহর ছিল তা নয়। রাজনৈতিক প্রয়োজন ও ক্ষমতার রদবদলের ফলে রাজধানী বা টাকশাল শহরের নাম পরিবর্তনের ঘটনা প্রায়ই ঘটত। যেমন—রোটাসপুরের পাঠ আজও নিশ্চিত নয়; জান্নাতাবাদ আসলে গৌড়েরই আরেক নাম; শহর-ই-নও, হোসেনাবাদ, নুসরাতাবাদ, মাহমুদাবাদ—সবই গৌড়ের রূপভেদ। আরাকান কোনো নগর নয়, বরং সীমান্ত অঞ্চল; পান্ডুনগর হলো পান্ডুয়া; চাটিগ্রাম চট্টগ্রামের সমার্থক। এভাবে নাম মিলিয়ে দেখলে প্রকৃত টাকশাল শহরের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১৬।
মুদ্রায় কখনও কখনও ‘খাজানা’ ও ‘দার-উয-যারব’ শব্দও টাকশালের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমটি সম্ভবত রাজধানীর কোষাগার নির্দেশ করত, যা থেকে মুদ্রা জারি হত—এতে কেন্দ্রীভূত রাজকোষব্যবস্থার প্রতিফলন পাওয়া যায়। আর ‘দার-উয-যারব’ ছিল মূলত ‘টাকশাল’ শব্দেরই পারিভাষিক রূপ, যা শহর নয়, প্রতিষ্ঠানকে বোঝাত।
সুলতানি যুগে মুদ্রার লিপিশৈলীর মানও সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে। ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের শাসনকাল পর্যন্ত মুদ্রার লিপি ছিল সুস্পষ্ট ও শিল্পগুণসম্পন্ন—প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ভট্টশালী তাঁর মুদ্রাগুলিকে বাংলার সুলতানি মুদ্রাশিল্পের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলে অভিহিত করেছেন। পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও টাকশাল কারিগরির মান হ্রাসের কারণে লিপির মানেও অবনতি ঘটে।
ঐতিহাসিক তথ্যের ঘাটতি পূরণে মুদ্রা আজও এক অমূল্য উৎস। বাংলার ইতিহাসে এমন বহু সুলতানের নাম কেবল তাঁদের জারিকৃত মুদ্রার মাধ্যমেই জানা গেছে, যাঁদের সম্পর্কে অন্য কোনো সমসাময়িক সূত্রে উল্লেখ নেই। ফলে, সুলতানি বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস রচনায় মুদ্রা এক প্রামাণ্য নথি। শুধু রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসেরও বহু উপাদান আমরা মুদ্রার মাধ্যমেই পাই—মুদ্রায় উৎকীর্ণ টাকশালের নাম, সাল-তারিখ থেকে শাসনামলের ভৌগোলিক বিস্তৃতি, বাণিজ্যকেন্দ্র, প্রশাসনিক গুরুত্ব এমনকি ধর্মীয় প্রভাব পর্যন্ত নির্ধারণ সম্ভব হয়।
হোসেনশাহী বংশের পতনের পর ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় আফগান (পাঠান) শাসনের সূচনা হয়, যা ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে মুগল সম্রাট আকবরের অধীনে আসা পর্যন্ত প্রায় চার দশক স্থায়ী হয়। এই সময়টি মূলত আফগান আমিরদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ক্ষমতার লড়াইয়ের ইতিহাস। প্রথম পর্যায়ে (১৫৩৮–১৫৫৩ খ্রি.) শেরশাহ সূরি ও তাঁর পুত্র ইসলাম শাহ বাংলা দিল্লির অধীন প্রদেশ হিসেবে শাসন করেন। ১৫৩৮ সালের বাংলা থেকে জারিকৃত শেরশাহের রৌপ্যমুদ্রা আজও পাওয়া যায়। ওই বছর হুমায়ুন সাময়িকভাবে বাংলা দখল করে নয় মাস গৌড়ে অবস্থান করেন এবং নিজের নামে মুদ্রা জারি করেন।
শেরশাহ ক্ষমতায় ফিরে এসে মুদ্রা ব্যবস্থায় যুগান্তকারী সংস্কার করেন—তিনি রৌপ্যমুদ্রার মান ৯৬ রতি (এক ভরি) ওজনে নির্ধারণ করেন, যা পরবর্তীতে মুগলরাও অনুসরণ করে। তিনি হোসেনশাহী আমলের ধর্মনিরপেক্ষ শিলালিপির পরিবর্তে মুদ্রায় পুনরায় কলেমা উৎকীর্ণের প্রথা চালু করেন এবং প্রথমবারের মতো দেবনাগরী লিপিতে নিজের নাম অঙ্কন করান—‘শ্রী শেরশাহী’। তাঁর মুদ্রায় একপাশে কলেমা, চার খলিফার নাম ও উপাধি ‘আসসুলতান আল আদিল’, অন্যপাশে নিজের নাম, টাকশালের নাম ও দেবনাগরী লিপি উৎকীর্ণ থাকত।
ইসলাম শাহ পিতার ধারা অব্যাহত রাখেন, যদিও বাংলায় তাঁর স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়নি। তিনি ফতেহাবাদ, সাতগাঁও, শরীফাবাদ ও শেরগড় টাকশাল থেকে রৌপ্যমুদ্রা জারি করেন এবং দেবনাগরীতে ‘শ্রী ইসলাম শাহী’ লিখতেন। মুহম্মদ আদীল শাহও শেরশাহের নকশা অনুসরণ করেন; তাঁর নাম ছিল ‘মুবারিজদ্দুনিয়া ওয়াদ্দীন আবুল মুজাফফর সুলতান মুহম্মদ আদীল’।
মুহম্মদ শাহ গাজী (১৫৫৩–৫৫) মুদ্রায় দেবনাগরী লিপি বাদ দেন—তাঁর মুদ্রা ‘রিকাব’ (সম্ভবত যুদ্ধক্ষেত্রের ভ্রাম্যমাণ টাকশাল) থেকে মুদ্রিত হয়েছিল। বাহাদুর শাহ গাজী ও জালাল শাহ গাজী পুনরায় দেবনাগরী ব্যবহার শুরু করেন। কররানী বংশের দাউদ খান কররানী (১৫৭২–৭৬) পাটনা, সাতগাঁও ও তান্ডা টাকশাল থেকে মুদ্রা জারি করেন, শেরশাহের ধারা অনুসরণ করে। তাঁর মৃত্যুর পরই বাংলা মুগল সাম্রাজ্যের প্রদেশে পরিণত হয়, আর সুলতানি শাসনের সমাপ্তি ঘটে।
এই মুদ্রাগুলির সুবিন্যস্ত সংকলন করেন এডওয়ার্ড টমাস তাঁর The Chronicles of the Pathan Kings of Delhi গ্রন্থে। পাশাপাশি বিজয়নগরের রাজা, মাদুরা ও বাহমনী সুলতানদের বিপুলসংখ্যক মুদ্রা আবিষ্কার ইতিহাস রচনায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। সুলতানি যুগের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো পুনর্গঠনে এই সব মুদ্রা এক অমূল্য দলিল।
শিলালিপিঃ
সুলতানি আমলে বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে শিলালিপি এক অমূল্য প্রাথমিক উৎস। এগুলি কেবল শাসকদের পরিচয় বা স্থাপত্য নির্মাণের তারিখের সাক্ষ্যই দেয় না, বরং তৎকালীন সমাজের ধর্মীয় জীবন, প্রশাসনিক কাঠামো, শিল্পরুচি এবং আঞ্চলিক ভূগোল সম্পর্কেও বিস্তারিত ধারণা প্রদান করে। সাধারণত আরবি ও ফারসি ভাষায় উৎকীর্ণ এই শিলালিপিগুলিতে কোরআনের আয়াত, হাদিস, সুলতানের নাম ও উপাধি, উৎকীর্ণকারী কর্মকর্তার পরিচয় এবং স্থাপনা নির্মাণের সাল অঙ্কিত থাকত। প্রেক্ষাপট অনুসারে কখনও সেগুলি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দিত, কখনও বা স্থানীয় অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং সুফি সাধকদের কর্মক্ষেত্রকে দৃশ্যমান করে তুলত।
শিলালিপি মূলত মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের অংশ হিসেবেই টিকে আছে—মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, সমাধি, প্রাসাদ, সেতু, ঈদগাহ, ফটক, এমনকি কখনও পুকুর বা কূপের শিলালিপি। সুলতানি বাংলায় (১২০৪–১৫৩৮ খ্রি.) প্রাপ্ত শিলালিপির অধিকাংশই আরবিতে উৎকীর্ণ, ফারসি ভাষার শিলালিপির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। মুগল যুগে এসে ফারসির ব্যবহার কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও সুলতানি যুগে ধর্মীয় অনুষঙ্গ ও ইসলামী ক্যালিগ্রাফির প্রতি অনুরাগই মুখ্য ছিল।
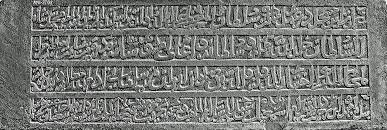
ইসলামী শিল্পরীতিতে প্রাণীর অবয়ব অঙ্কনের নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে লিপি অলংকরণই শিল্পীদের সৃজনশীলতার প্রধান ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। শিলালিপি উৎকীর্ণকারীরা আরবি বর্ণমালার কুফিক, নাসখ, তালিক ও নাস্তালিক প্রভৃতি শৈলীতে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। বাংলার শিলালিপিতে এই ধারার ক্রমবিকাশ আরব ও পারস্যের ধারা অনুসরণ করলেও স্থানীয় শিল্পবোধও তাতে মিশে যায়। কুফিক শৈলীতে অক্ষরের সরলতা ও দৃঢ়তা, নাসখে মসৃণতা, তালিক ও নাস্তালিকে বাঁকানো ও তির্যক রেখার সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। এর বাইরেও ‘তোঘরা’ নামের এক অলংকরণধর্মী ধারা দেখা যায়—এটি কোনও স্বতন্ত্র লিপিপদ্ধতি নয়, বরং প্রচলিত অক্ষরের নান্দনিক রূপান্তর, যেখানে বর্ণের আকারকে লম্ব বা সমান্তরাল কিংবা বক্রভাবে সম্প্রসারিত-সংকুচিত করে শৈল্পিক রূপ দেওয়া হতো। এই পদ্ধতিতে কখনও অক্ষর ফুল-পত্র-বৃক্ষের মতো নকশায় রূপ নিত, ফলে শিলালিপি একধরনের দৃশ্যশিল্পে পরিণত হতো।
সুলতানি বাংলার শিলালিপির বক্তব্য প্রকাশের দিক থেকেও কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথমত, সুলতানদের নাম সর্বদা উপাধিসহ উৎকীর্ণ হতো—এটি কেবল ক্ষমতার ঘোষণা নয়, রাজনৈতিক বৈধতারও প্রতীক। লখনৌতির গভর্নর বা রাজধানী-নিয়োগকৃত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নামও কিছু শিলালিপিতে উল্লেখ থাকত, যা প্রশাসনিক কাঠামো বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক। দ্বিতীয়ত, নির্দিষ্ট পদবি ছাড়াও বহু শিলালিপিতে গুণবাচক বা প্রশংসাবাচক উপাধি ব্যবহৃত হতো। দাপ্তরিক পদবিগুলির মধ্যে ছিল—শাহজাদা, উজির, শর-ই-লস্কর, মুনসিফ, দেওয়ান, কোতয়াল, বাকআলি, মাহলিয়ান, নওবাদ আলী, জমাদার বইরমাহলি, মরাবদার, ঘইরমাহলী, মীনবক, শিকদার, জংদার, মীর বহর, শের-ই-খেল, কারা-ই-ফরমান, কাজীদস্তর, শের-ই-গুমস্তাহ ইত্যাদি। প্রশংসাবাচক উপাধির মধ্যে দেখা যায়—গাউস উল ইসলাম ওয়াল মুসলেমিন, মুগিস আল মুলক ওয়াল সালাতিন, মুঈন আল মুলক ওয়াল সালাতিন, নাসের আল মুলক ওয়াল সালাতিন, সাহিব আল আদল ওয়াল বাফাত, সাহিব আল সঈফ ওয়াল কালাম ইত্যাদি। এসব উপাধি শাসকের ধর্মীয়, সামরিক ও ন্যায়বিচারমূলক গুণাবলি তুলে ধরত।
তৃতীয়ত, কিছু শিলালিপিতে তোঘরা রীতির সঙ্গে শৈল্পিক অলংকরণের মিশ্রণ দেখা যায়, যেখানে লিপির মাঝখান বা প্রান্তে জটিল জ্যামিতিক ও ফুলেল নকশা করা হতো। চতুর্থত, সুফি সাধকদের নামের উল্লেখও পাওয়া যায়—এগুলি থেকে সুফিদের কার্যক্ষেত্র, পৃষ্ঠপোষকতা ও সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে তথ্য মেলে। পঞ্চমত, মুসলিম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিলালিপির শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ হির রাহমানির রাহিম’ লেখার প্রচলন ছিল, যা স্থাপনার ধর্মীয় উদ্দেশ্য ও পবিত্রতার ইঙ্গিত বহন করত। ষষ্ঠত, বহু শিলালিপি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা শহরের নাম উল্লেখ করে, যেমন—আরসাহ সাজলা মকনাহবাদ, শহর বা থানা লাওবলা, শহর সিমলাবাদ, আরসা ও মহল বা শহর হাদিগড়, শহর মশহুর হুসাইনাবাদ, ইকলিম মুবারকাবাদ, ইকলিম মুয়াজ্জমাবাদ, আরসা শ্রীহট, মাহমুদাবাদ ইত্যাদি—যা আঞ্চলিক ভূগোল নির্ধারণে সহায়ক।
বাংলার মুসলিম শাসকদের মধ্যে সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজির (১২১৩–১২২৭ খ্রি.) নামাঙ্কিত শিলালিপি সবচেয়ে প্রাচীন বলে ধরা হয়। ১২২১ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ এই শিলালিপিটি পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার মখদুম শাহের দরগাহে সংযুক্ত ছিল। এটি কেবল ধর্মীয় স্থাপনার নয়, বরং সুলতানি বাংলায় ইসলামী ক্যালিগ্রাফির প্রাথমিক ধাপেরও এক মূল্যবান নিদর্শন। প্রথম দিককার কিছু শিলালিপি বিহার অঞ্চলেও পাওয়া গেছে, যা বাংলার রাজনৈতিক প্রভাববলয়ের বিস্তার নির্দেশ করে।
স্বাধীন সুলতানি যুগে প্রথম ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনকালে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিলালিপি উৎকীর্ণ হয়। ইলিয়াস শাহী বংশের তৃতীয় সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের পর বাংলার শাসন কাঠামো কিছু সময়ের জন্য দুর্বল হয়ে পড়ে এবং রাজঅমাত্য গণেশ সীমিত সময়ের জন্য হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর শাসনকালে কোনও শিলালিপি পাওয়া যায়নি, তবে তাঁর পুত্র যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সুলতান জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ (১৪১৫–১৪৩৩ খ্রি.) নামে সিংহাসনে বসেন। তাঁর আমলে রাজশাহী ও ঢাকায় দুটি শিলালিপি উৎকীর্ণ হয়।
পরবর্তী ইলিয়াস শাহী সুলতানদের শাসনকালে শিলালিপির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৪৩৬–১৪৫৯) আমলে ১৭টি, সুলতান রুকনউদ্দিন বারবক শাহ (১৪৫৯–১৪৭৪) আমলে ১৮টি, সুলতান শামসউদ্দিন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪–১৪৮১) আমলে ১১টি এবং সুলতান জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ (১৪৮১–১৪৮৭) আমলে ১০টি শিলালিপি আজও সংরক্ষিত আছে। এসব শিলালিপির মাধ্যমে আমরা শুধু স্থাপত্য ইতিহাসই নয়, রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা, প্রশাসনিক নীতি, শিল্পরীতি ও ধর্মীয় সংস্কৃতির রূপও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারি।
এভাবে সুলতানি বাংলার শিলালিপি একদিকে যেমন স্থাপত্য ও শিল্পকলার নিদর্শন, তেমনি অপরদিকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দলিল। এগুলির মাধ্যমে মধ্যযুগীয় বাংলার ক্ষমতার কাঠামো, আঞ্চলিক রাজনীতি, ধর্মীয় জীবন, শিল্পরুচি ও ভাষার বিবর্তন সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র নির্মাণ করা সম্ভব হয়—যা কেবল গ্রন্থিত ইতিহাসে নয়, বাংলার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারে এক অমোচনীয় অবদান রেখে গেছে।
বাংলার স্বাধীন সুলতানি আমলের শেষভাগে ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন হাবশি সুলতানরা। এই স্বল্পকালীন শাসনপর্বেও শিলালিপি-সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন সংরক্ষিত হয়েছে, যা থেকে সে সময়ের রাজনৈতিক ও স্থাপত্য ইতিহাস সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। সুলতান সাইফউদ্দিন ফিরুজ শাহের (১৪৮৭–১৪৯০ খ্রি.) শাসনামলে উৎকীর্ণ পাঁচটি শিলালিপি এবং সুলতান শামসউদ্দিন মোজাফফর শাহের (১৪৯০–১৪৯৩ খ্রি.) আমলের আরও পাঁচটি শিলালিপি এ সময়ের দলিলস্বরূপ বিদ্যমান। এসব শিলালিপি কেবল স্থাপত্যের উদ্বোধনী দলিল নয়, বরং সুলতানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা, ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও শিল্প-রুচির প্রতিফলনও বহন করে।
বাংলার স্বাধীন সুলতানি আমলে স্থাপত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির দিক থেকে সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও দীর্ঘস্থায়ী সময়টি অতিবাহিত হয়েছিল হোসেনশাহী যুগে। এই আমলে বাংলার প্রাদেশিক রাজধানী গৌড়, সোনারগাঁও ও পাণ্ডুয়া সহ নানা অঞ্চলে ব্যাপক হারে স্থাপত্য নির্মাণ হয়েছে, যার ফলে শিলালিপির প্রাপ্তিও অসামান্যভাবে বৃদ্ধি পায়। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের (১৪৯৩–১৫১৯ খ্রি.) সময়কালের ৭৭টি শিলালিপি আজও সংরক্ষিত, যা সংখ্যার দিক থেকে বাংলার যে কোনো সুলতানের আমলে সর্বাধিক। তাঁর পুত্র সুলতান নাসিরউদ্দিন নুসরত শাহের (১৫১৯–১৫৩২ খ্রি.) আমলে পাওয়া গেছে ২৩টি শিলালিপি; সুলতান আলাউদ্দিন ফিরুজ শাহের (১৫৩২–১৫৩৩ খ্রি.) শাসনকাল থেকে পাওয়া গেছে একটি এবং সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের (১৫৩৩–১৫৩৮ খ্রি.) সময়কালের ৮টি শিলালিপি। এই বিপুল সংখ্যক শিলালিপি কেবল নির্মাণ-কার্যের নথি নয়, বরং সে যুগের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও শিল্প-সংস্কৃতির অমূল্য প্রতিফলন।
১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন সুলতানি শাসনের অবসান ঘটে এবং বাংলা অল্প সময়ের জন্য মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের অধিকারে আসে। তবে শিগগিরই ক্ষমতার পালা ঘুরে যায় এবং বাংলা চলে যায় আফগান সুলতানদের অধীনে। ১৫৪১ থেকে ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই আফগান আমলেও শিলালিপির ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, সুলতান শেরশাহ সূরির (১৫৩৮–১৫৪৫ খ্রি.) নামে উৎকীর্ণ চারটি শিলালিপি আসলে কামানের গায়ে খোদিত, যা ‘কামান-লিপি’ নামে পরিচিত। এর বাইরে সুলতান শামসউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ গাজীর (১৫৫৪–১৫৫৫ খ্রি.) একটি, সুলতান গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ সূরির (১৫৫৬–১৫৬০ খ্রি.) পাঁচটি, সুলতান গিয়াসউদ্দিন জালাল শাহের (১৫৬০–১৫৬৩ খ্রি.) তিনটি এবং সুলায়মান কররানির (১৫৬৪–১৫৭২ খ্রি.) আমলের পাঁচটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব লিপি আফগান শাসনকালের সামরিক শক্তি, স্থাপত্যে তাঁদের আগ্রহ এবং ধর্মীয় ভাবাদর্শের স্পষ্ট প্রতিফলন বহন করে।
স্থাপত্য-নিদর্শনের দিকে তাকালে দেখা যায়, সুলতানি যুগের স্থাপত্য কেবল বাংলার ইতিহাস নয়, সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের শিল্প-ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ভারতীয় স্থাপত্যের শিকড় সুপ্রাচীন; তা দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ব্যবস্থার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই স্থাপত্য বিকশিত হয়েছে, গ্রহণ করেছে বিশ্বের নানা প্রান্তের প্রভাব—কখনো পারস্য, তুর্কি ও আরবের সংস্পর্শে, কখনো ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার সাংস্কৃতিক বিনিময়ে। মুসলিম শাসনের সূচনালগ্নে দিল্লির কুতুব মিনার এ ঐতিহাসিক মেলবন্ধনের এক অসামান্য নিদর্শন। সুফি সাধক কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকির স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত এই মিনারের কাজ শুরু করেছিলেন কুতুবউদ্দিন আইবক এবং তা সম্পূর্ণ হয়েছিল ইলতুৎমিশের আমলে। এ স্থাপত্যের ভিত্তিতে দৃশ্যমান হিন্দু-জৈন মন্দিরের খোদাই করা স্তম্ভ ও অলংকরণ প্রমাণ করে, কীভাবে মুসলিম স্থাপত্য ভারতীয় কারুশিল্পের উপাদানকে গ্রহণ করে নতুন রূপ দিয়েছে।
খলজি যুগে নির্মিত আলাউদ্দিন খলজির জামাতখানা মসজিদ ও আলাই দরওয়াজা হিন্দু শিল্পরীতির সঙ্গে মুসলিম নকশার সংমিশ্রণের চমৎকার উদাহরণ। তুঘলক আমলে স্থাপত্যে সরলতা, দৃঢ়তা ও কার্যকারিতা গুরুত্ব পেলেও পূর্ববর্তী যুগের সূক্ষ্ম অলংকরণের অভাব লক্ষ করা যায়। লোদি ও সৈয়দ আমলে উন্নতির কিছু প্রচেষ্টা দেখা গেলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তবে সুলতানি আমলের শেষভাগে আফগান শাসক শেরশাহ সূরির সমাধি (সাসারাম) মধ্যযুগীয় ভারতীয় স্থাপত্যের এক মহিমান্বিত নিদর্শন।
দিল্লি, গুজরাট, মালওয়া, দাক্ষিণাত্য—সব প্রাদেশিক স্থাপত্যেই স্থানীয় শিল্পরীতি ও ইসলামি স্থাপত্যের সমন্বয় ঘটে। বাংলার ক্ষেত্রে, পাথরের পরিবর্তে ইট প্রধান নির্মাণসামগ্রী হওয়ায় স্থাপনাগুলি তুলনামূলক ছোট হলেও শৈল্পিক সৌন্দর্যে অনন্য। ১৩৬৮ খ্রিস্টাব্দে সিকান্দার শাহের নির্মিত পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ তার বিশাল আয়তন, দৃষ্টিনন্দন খিলান ও সমৃদ্ধ অলংকরণের জন্য বিশেষভাবে খ্যাত। হোসেন শাহের আমলে ওয়ালি মুহাম্মদ নির্মিত ছোট সোনা মসজিদ, নুসরত শাহের সময়ের বড় সোনা মসজিদ এবং তাঁরই আমলে নির্মিত কদম রসুল মসজিদ মুসলিম স্থাপত্যে সূক্ষ্মতা ও আভিজাত্যের নিদর্শন হয়ে আছে।
উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও এ সময় স্বতন্ত্র শিল্পধারা বিকশিত হয়েছিল। জৌনপুরের অটালদেবী মসজিদে হিন্দু স্থাপত্যশৈলীর প্রভাব সুস্পষ্ট। গুজরাটের আহমেদাবাদের মসজিদ ও প্রাসাদসমূহে ভারতীয় অলংকরণশৈলী ও মুসলিম নকশার মেলবন্ধন দেখা যায়। মালওয়ার মান্ডু অঞ্চলের জাহাজ মহল, হিন্দোলা মহল ও জামি মসজিদে মুসলিম স্থাপত্যের সরল অথচ মর্যাদাবান সৌন্দর্য প্রতিফলিত হয়েছে। দাক্ষিণাত্যের বাহমনি স্থাপত্যে ভারতীয়, তুর্কি, মিশরীয় ও পারস্য রীতির সম্মিলন ঘটে—গুলবর্গার জামি মসজিদ, দৌলতাবাদের চাঁদ মিনার ও বিদরের মামুদ গাওয়ান কলেজে পারস্যি প্রভাব সুস্পষ্ট হলেও স্থানীয় হিন্দু অলংকরণের ছাপও রয়েছে। আদিল শাহি আমলের মসজিদগুলোতে দাক্ষিণাত্যের আঞ্চলিক রীতি দ্যাখা যায়।
অন্যদিকে, বিজয়নগর সাম্রাজ্যে হিন্দু স্থাপত্যের মহিমা নতুন উচ্চতায় পৌঁছায়। রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের নির্মিত বিট্টলনাথ মন্দির, কর্ণাটকের গ্রানাইট পাথরে নির্মিত রাজপ্রাসাদ, বিশাল গোপুরম ও স্তম্ভমণ্ডপ এক অনন্য শৈল্পিক ধারার জন্ম দেয়। ফার্গুসনের মতো শিল্পসমালোচকেরা এই স্থাপত্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। পুরীর জগন্নাথ মন্দির ও কোনারকের সূর্য মন্দিরও এ সময়ের হিন্দু স্থাপত্যের গৌরবোজ্জ্বল নিদর্শন। বিজয়নগরের রাজকীয় স্থাপত্যে উত্তর ও দক্ষিণ দাক্ষিণাত্যের প্রভাব যেমন রয়েছে, তেমনি এর পৃষ্ঠপোষকতায় কন্নড়, তেলুগু, তামিল ও সংস্কৃত সাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা ঘটে। কর্ণাটকী সংগীতও এই যুগেই তার পরিণত রূপ লাভ করে।
অতএব, হাবশি সুলতানদের স্বল্পকালীন শাসন থেকে শুরু করে হোসেনশাহী আমলের ঐশ্বর্যমণ্ডিত স্থাপত্য, আফগান সুলতানদের কামান-লিপি, কিংবা উপমহাদেশব্যাপী প্রাদেশিক শিল্পরীতির বিকাশ—সবই এক বৃহৎ ঐতিহাসিক ধারার অংশ। শিলালিপি ও স্থাপত্য কেবল শিল্পের নিদর্শন নয়, বরং এগুলো রাজনৈতিক ক্ষমতা, ধর্মীয় জীবন, সামাজিক কাঠামো ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের যুগপৎ সাক্ষ্য বহন করে, যা মধ্যযুগীয় বাংলার ইতিহাস পুনর্গঠনে অমূল্য ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।
ভারতবর্ষের ইতিহাসে মধ্যযুগের সংজ্ঞা ও কালবিন্যাস ইউরোপের ইতিহাসচর্চা থেকে স্বভাবতই ভিন্ন। ইউরোপীয় ইতিহাসে মধ্যযুগ নির্ধারণে প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের পতন ও রেনেসাঁর সূচনা দুটি প্রধান মাপকাঠি হলেও, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সময়সীমারেখা টানা হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। সাধারণভাবে মনে করা হয়, আফগানিস্তানের ঘোরী বংশীয় সুলতানদের দিল্লি অধিগ্রহণ (বারো শতকের শেষ দশক) এবং তার পরপরই উত্তরভারতে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষে মধ্যযুগের সূচনা ঘটে। দিল্লি অধিকারের অল্প কিছু বছরের মধ্যেই মুসলমানদের বাংলায় প্রবেশ ও কর্তৃত্ব বিস্তারের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১২০৪-০৫ খ্রিস্টাব্দে মুহম্মদ বখতিয়ার খলজীর বঙ্গবিজয় ছিল এই নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের সূচনাবিন্দু—যা বাংলার ইতিহাসে মধ্যযুগের দ্বার উন্মোচন করেছিল।
বাংলায় মুসলিম শাসনের আগমন কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; এটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শিল্পকলার ক্ষেত্রেও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এতদিন পর্যন্ত বাংলা সমাজ ও সংস্কৃতির ভিত রচিত ছিল প্রধানত হিন্দু ও বৌদ্ধ উপাদানের সমন্বয়ে। মুসলিম বিজয়ের পর সেই অবিমিশ্র ভারতীয়-হিন্দু সংস্কৃতিতে নতুনভাবে যুক্ত হয় মধ্যপ্রাচ্য, পারস্য, তুর্কি ও আফগান উপাদান। ফলত, জীবনের প্রায় সবক্ষেত্রে গড়ে ওঠে এক নতুন ধারা—যা ইতিহাসবিদেরা ‘ভারতীয় ইসলামি’ বা ‘ভারতীয় মুসলিম’ সংস্কৃতিরূপে আখ্যায়িত করেছেন। এই ধারায় যেমন মুসলমানেরা এনেছিলেন তাদের নিজস্ব ধর্মীয় চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্থাপত্য ও গঠনশৈলী, তেমনি স্থানীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ নির্মাণশিল্পীরা যোগ করেছিলেন নিজেদের প্রাচীন দক্ষতা, অলঙ্করণপ্রবণতা এবং টেকনিকের সূক্ষ্মতা। ফলে গড়ে ওঠে এক স্বতন্ত্র শিল্পধারা, যা ছিল না কেবল বাইরের অনুকরণ, আবার কেবল স্থানীয় ধারারও পুনরাবৃত্তি নয়—বরং উভয়ের মেলবন্ধনে সৃষ্ট এক নতুন সত্তা।
মুসলমান শাসকগণ ভারতবর্ষে এমন কিছু স্থাপত্য প্রযুক্তি প্রবর্তন করেছিলেন যার সঙ্গে ভারতীয়দের পূর্বপরিচয় ছিল না। যেমন—স্থাপনার বহির্ভাগে খিলান (arch) ও স্তম্ভ (pillar) ব্যবহার, গম্বুজ (dome) ধারণের জন্য পেন্ডেন্টিভ (pendentive) ও স্কুইঞ্চ (squinch) প্রয়োগ ইত্যাদি। যদিও এগুলির উৎপত্তি মূলত প্রাচীন রোমান-বাইজেন্টীয় এবং পারসিক স্থাপত্য থেকে, মুসলমানরা সেগুলিকে ইসলামি বিশ্বজুড়ে প্রায় অপরিহার্য উপাদান হিসেবে রূপান্তরিত করেন। অপরদিকে, স্থানীয় হিন্দু-বৌদ্ধ স্থাপত্য থেকে তারা গ্রহণ করেন ছাদ বহনের জন্য পাথর বা কাঠের স্তম্ভ ও সদল (lintel), কড়ি-বরগা, এবং কোণ ভরাটের জন্য কর্বেল পদ্ধতি—যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতীয় মন্দির ও বিহারের অলঙ্কৃত স্থাপত্যে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল।
বখতিয়ার খলজীর বঙ্গবিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলায় মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের সূচনা ঘটে। সমসাময়িক ঐতিহাসিক মিনহাজ উদ্দিন সিরাজ, তাঁর তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, বখতিয়ার খলজী ‘‘মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ’’ নির্মাণ করেছিলেন। যদিও সেসময়ের এসব স্থাপনার সুনির্দিষ্ট নিদর্শন আজ আর অবশিষ্ট নেই, তবুও অন্যান্য দেশের সমসাময়িক স্থাপত্য এবং বাংলার পরবর্তী সময়ের নিদর্শন থেকে অনুমান করা যায়, এসব স্থাপনা মূলত স্থানীয় উপাদান ও স্থানীয় কারিগরদের সহায়তায় গড়ে উঠেছিল। সম্ভবত যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের পরিত্যক্ত ইমারত বা উপকরণও ব্যবহৃত হতো। তবে বাংলায় মন্দিরের গঠন ও দিক-নির্দেশনার কারণে সেগুলিকে সরাসরি মসজিদে রূপান্তর করা প্রায় অসম্ভব ছিল; এজন্য মুসলিম শাসকরা নকশা ঠিক রেখে নতুন উপকরণ দিয়ে ইসলামী ধর্মীয় রীতি অনুসারে স্থাপনা গড়ে তোলার পথকেই বেছে নেন।
বঙ্গবিজয়ের পরবর্তী এক শতকেরও বেশি সময় জুড়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অস্থিতিশীল। দিল্লি সুলতানি ও স্থানীয় গভর্নরদের ক্ষমতার লড়াই, আঞ্চলিক বিদ্রোহ এবং বহিরাগত আক্রমণের ফলে এই দীর্ঘ সময়ে বিশাল আকারের স্থাপত্যনির্মাণ তেমন হয়নি বলেই অনুমান করা যায়। তবুও কিছু নিদর্শন আজও টিকে আছে, যা সেই প্রাথমিক মুসলিম স্থাপত্যচর্চার আভাস দেয়। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার তমলুকের কাছে জাফর খান গাজীর মসজিদ ও সমাধি, এবং হুগলি জেলার ত্রিবেণীতে অবস্থিত বরী মসজিদ ও সংলগ্ন মিনার—এগুলিই মধ্যযুগীয় বাংলায় মুসলিম স্থাপত্যের প্রাচীনতম জীবিত নিদর্শন হিসেবে পরিচিত।
যদিও প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী জাফর খান গাজীর মসজিদ ত্রয়োদশ শতকের শেষদিকে নির্মিত, স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এর সম্মুখভাগের স্তম্ভ ও অভ্যন্তরের মিহরাবের অলঙ্করণ গৌড়ের কদম রসুল মসজিদ বা রাজশাহীর বাঘা মসজিদের সঙ্গে গভীর সাদৃশ্যপূর্ণ—যা মূলত হোসেন শাহী আমলের বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ, প্রাথমিক নির্মাণ হয়তো আগে হলেও পরবর্তী সময়ে, বিশেষত পঞ্চদশ শতকে, এই মসজিদ পুনর্গঠন বা সংস্কার হয়েছে। একইভাবে বরী মসজিদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, এর স্তম্ভ, খিলান ও পেন্ডেন্টিভের গঠন গৌড়ের দরসবাড়ি বা ধুনিচক মসজিদের সঙ্গে এমন মিল রয়েছে যে, এর নির্মাণকালও সম্ভবত পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ, অর্থাৎ পরবর্তী ইলিয়াস শাহী শাসনামল।
এই প্রাথমিক উদাহরণগুলিতে একটি বিষয় সুস্পষ্ট—বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে শুরু থেকেই স্থানীয় নির্মাণশৈলী ও উপাদানের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান ছিল। এখানে মূল নির্মাণসামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে পোড়ামাটির ইট, কারণ বাংলায় প্রাকৃতিকভাবে বড় আকারের নির্মাণযোগ্য পাথরের প্রাচুর্য ছিল না। এই ইটের উপর সূক্ষ্ম খোদাই, টেরাকোটা প্যানেল, এবং কোরানিক লিপি উৎকীর্ণ করে অলঙ্করণ করা হতো, যা বাংলার নিজস্ব স্থাপত্যরীতিকে স্বতন্ত্র পরিচয় দান করেছে।
তাছাড়া, প্রাথমিক মুসলিম স্থাপত্যে কাঠামোগত সরলতার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় ধর্মীয় আবহকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা। মসজিদের নকশায় প্রশস্ত প্রার্থনাকক্ষ, কিবলামুখী মিহরাব, এবং মিনারের পরিবর্তে ছাদের কোণে ছোট গম্বুজ-সদৃশ টাওয়ার স্থাপন করা হতো। গম্বুজ নির্মাণে স্কুইঞ্চ ও পেন্ডেন্টিভের ব্যবহার, খিলানবিশিষ্ট প্রবেশপথ এবং অভ্যন্তরে মসৃণ প্লাস্টার ফিনিশ—এসবই মুসলিম স্থাপত্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে।
বাংলায় মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের এই প্রাথমিক ধাপ পরবর্তী শতকে, বিশেষত স্বাধীন সুলতানি আমলে, আরও পরিণত ও সমৃদ্ধ রূপ পায়। কিন্তু বখতিয়ার খলজীর পরবর্তী সময়ে যে কয়েকটি নিদর্শন টিকে আছে, সেগুলি কেবল স্থাপত্য ইতিহাস নয়, বরং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস বোঝার ক্ষেত্রেও অনন্য দলিল হিসেবে বিবেচিত। এগুলির মাধ্যমে বোঝা যায়, কীভাবে মুসলিম শাসন বাংলায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয় শিল্পী ও কারিগরদের অংশগ্রহণে এক নতুন গঠনশৈলীর সূচনা করেছিল—যা ছিল না নিছক বিদেশি আমদানি, আবার নিছক স্থানীয় ঐতিহ্যের পুনরাবৃত্তিও নয়, বরং দুই ধারার সম্মিলনে সৃষ্ট এক অভিনব ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি।
ইলিয়াসশাহী বংশ ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হওয়ার মধ্য দিয়ে এক নতুন যুগের সূচনা করে। এর আগে বাংলার শাসনভার মূলত দিল্লির সুলতানের মনোনীত গভর্নর বা অধীনস্থ শাসকদের হাতে ছিল, যারা কখনো কখনো দিল্লির শাসন থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেও তাদের ক্ষমতা ছিল অস্থায়ী ও অনিশ্চিত। কিন্তু হাজী ইলিয়াস শাহের ক্ষমতায় আরোহণ ছিল এক ভিন্নতর ঘটনা—তিনি শুধু বাংলার সর্বত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন না, বরং স্থানীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সার্বভৌম শাসনের প্রতীক হিসেবে “শাহ-ই-বাঙ্গালা” উপাধি গ্রহণ করলেন, যা পরবর্তী কালে বাংলার রাজনৈতিক পরিচয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। ইলিয়াসশাহী বংশ প্রায় দেড় শতাব্দীর বেশি সময় ধরে—মধ্যবর্তী তেইশ বছরের ব্যতিক্রম ছাড়া—বাংলার শাসনভার ধরে রাখে। এই তেইশ বছর (১৪১৩-১৪৩৫) ক্ষমতায় ছিলেন শিহাবউদ্দীন বায়েজীদ শাহ, রাজা গণেশ এবং তাঁর বংশধরগণ। পরবর্তীতে ১৪৮৭ থেকে ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় আসেন হাবশী শাসকগণ; তাঁদের স্বল্পস্থায়ী শাসনের পর হোসেনশাহী বংশ ১৪৯৪ থেকে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশ শাসন করেন। এর পরে শূর বংশ (১৫৩৮–১৫৬৩) এবং কররানী বংশ (১৫৬৩–১৫৭৬) মঞ্চে আসে, যতক্ষণ না মুঘলরা ১৫৭৬ সালে বাংলাকে তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে।
১৩৪২ থেকে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়কালে বাংলায় মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের স্বর্ণযুগ পরিলক্ষিত হয়। এ সময়ের স্থাপত্যকলা শুধু দিল্লির সুলতানি রীতির অনুসরণ নয়, বরং স্থানীয় ঐতিহ্য ও কৌশলের সঙ্গে ইসলামী স্থাপত্য উপাদানের মেলবন্ধনে এক স্বকীয় রূপ লাভ করে, যা পরবর্তীতে “বাংলা রীতি” নামে খ্যাত হয়। এর স্বাতন্ত্র্য ভারতের অন্যান্য আঞ্চলিক রীতি বা দিল্লির সুলতানি ধরন থেকে স্পষ্টত আলাদা। ইলিয়াসশাহী ও হোসেনশাহী সুলতানরা এই রীতির বিকাশে নির্দিষ্ট অবদান রাখেন, যা আজও স্থাপত্য ইতিহাসের গবেষণায় অনন্য উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়।
স্বাধীন যুগে নির্মিত স্থাপত্যগুলির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো—এসব স্থাপনা মূলত রাজধানী বা গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। এটি প্রমাণ করে যে স্থাপত্যকলা ছিল মূলত রাজশক্তি ও ক্ষমতাশালী পৃষ্ঠপোষকদের উদ্যোগে গড়ে ওঠা একটি শিল্প। রাজধানী গৌড়-লখনৌতি, পান্ডুয়া-ফিরুজাবাদ, মাহমুদাবাদ (অথবা মুহম্মদাবাদ), খলিফাতাবাদ, সোনারগাঁও এবং বাঘা—এসব স্থান ছিল প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল। পাশাপাশি সুরা, কুসুম্বা, শৈলকুপা, নবগ্রাম, মসজিদবাড়ি, রামপাল প্রভৃতি অঞ্চলে নির্মিত ছোট মসজিদসমূহ ইঙ্গিত দেয় যে এসব অঞ্চলও একসময় ছিল ক্ষুদ্র প্রশাসনিক সদর বা বাণিজ্যকেন্দ্র।
আজ যে সব স্থাপত্য নিদর্শন টিকে আছে, তার অধিকাংশই ধর্মীয় প্রকৃতির। এর প্রধান কারণ, ধর্মীয় স্থাপনা পরিত্যক্ত হলেও সেগুলির নির্মাণসামগ্রী সাধারণত লুণ্ঠিত বা অপহৃত হয়নি; অথচ সেক্যুলার বা প্রাসাদোপম ভবনগুলো ব্যক্তিগত নির্মাণের জন্য ধ্বংস করে উপকরণ সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। গৌড়-লখনৌতি ও পান্ডুয়া-ফিরুজাবাদের ধ্বংসাবশেষই এই লুণ্ঠনের বাস্তব প্রমাণ বহন করে।
ধর্মীয় স্থাপনার মধ্যে মসজিদের প্রাধান্য সর্বাধিক। এগুলি মূলত দুই প্রকার—শুক্রবারের জামাতের জন্য জামে মসজিদ এবং প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য ওয়াক্তিয়া বা “পাঞ্জেগানা” মসজিদ। জামে মসজিদ আকারে বড়, এবং উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রায়ই শাহী গ্যালারি বা “মাকসুরা” যুক্ত থাকে, যা শাসক বা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিরাপত্তার জন্য ব্যবহৃত হতো। মাকসুরা অনেকটা দোতলার মতো উঁচু অংশ, যেখান থেকে শাসক নামাজে অংশ নিতেন। তবে সব জামে মসজিদে মাকসুরা থাকত না—যেমন, খলিফাতাবাদের জামে মসজিদে (বর্তমান বাগেরহাট জামে মসজিদ) এ ধরনের গ্যালারি নেই, বরং মিহরাবের উত্তর পাশে গোপন একটি পথ রাখা হয়েছিল, যা দিয়ে শাসক নিরাপদে প্রবেশ করতে পারতেন।
জামে মসজিদ সাধারণত আয়তাকার এবং বহুগম্বুজবিশিষ্ট হয়। এর মধ্যভাগে লম্বালম্বিভাবে বিস্তৃত খিলানযুক্ত প্রশস্ত “নেভ” থাকে। দিল্লি বা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের জামে মসজিদের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, বাংলার জামে মসজিদে সাধারণত “রিওয়াক” বেষ্টিত খোলা “সাহান” নেই, যা ভারতের বাইরে বা দিল্লিতেও প্রচলিত ছিল। এই পার্থক্যের কারণ স্থানীয় জলবায়ু—বর্ষাকালীন অতিবৃষ্টি ও আর্দ্র আবহাওয়ায় খোলা প্রাঙ্গণ ব্যবহার অনুপযোগী ছিল।
বাংলার সুলতানি যুগের প্রতিনিধিত্বকারী উল্লেখযোগ্য জামে মসজিদের মধ্যে রয়েছে—পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদ (১৩৭৩), খলিফাতাবাদের জামে মসজিদ (পনেরো শতকের মধ্যভাগ), গুণমন্ত মসজিদ (পনেরো শতকের মাঝামাঝি), তাঁতীপাড়া মসজিদ (আনুমানিক ১৪৮০), দরসবাড়ি মসজিদ (১৪৭৯), গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ (১৪৯৪–১৫১৯) ও বড় সোনা মসজিদ (১৫২৬), রাজশাহীর বাঘা মসজিদ (১৫২২), কুসুম্বা মসজিদ (১৫৫৮), এবং সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে আবিষ্কৃত যশোরের বারো বাজার এলাকার সাতগাছিয়া ও মনোহর দিঘির জামে মসজিদ (পনেরো শতকের শেষভাগ বা ষোল শতকের প্রথম ভাগ)। এক ব্যতিক্রমী উদাহরণ হলো মুন্সিগঞ্জ জেলার রামপালের মসজিদ, যা শিলালিপিতে জামে মসজিদ বলে উল্লেখ থাকলেও এতে শাহী গ্যালারি নেই। এটি নির্মাণ করেছিলেন পরবর্তী ইলিয়াসশাহী বংশের শেষ সুলতান জালালউদ্দীন ফতেহ শাহ, ৮৮৮ হিজরি (১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে)।
অন্যদিকে, ওয়াক্তিয়া মসজিদ আকারে ছোট এবং সাধারণত স্থানীয় মহল্লা বা বাজারে নির্মিত হতো। এগুলি শুধু নামাজের জন্য নয়, বরং সামাজিক বৈঠক, ধর্মীয় আলোচনা, এবং শিশুদের প্রাথমিক ইসলামী শিক্ষাদানের স্থান হিসেবেও ব্যবহৃত হতো। অধিকাংশ ওয়াক্তিয়া মসজিদ এক গম্বুজবিশিষ্ট, এবং কিছু ক্ষেত্রে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে খিলানযুক্ত বারান্দা যুক্ত থাকত।
বাংলার মসজিদ স্থাপত্যের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো এর খিলান ও গম্বুজ নির্মাণের ধরন। জামে হোক বা ওয়াক্তিয়া—উভয় ধরনের মসজিদের খিলান প্রায়ই বাংলার ঐতিহ্যবাহী কুটিরের অনুকরণে চৌচালা আকৃতির হতো। এ রূপটি স্থানীয় স্থাপত্য নান্দনিকতার সাথে ইসলামী স্থাপত্যশৈলীর সৃজনশীল মেলবন্ধনের ফল। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় গৌড়-লখনৌতির চামকাটি মসজিদ (১৪৭৫), খনিয়াদিঘি ও লট্টন মসজিদ (পনেরো শতকের শেষ ভাগ), বাগেরহাটের রণবিজয়পুর ও বিবি বেগনি মসজিদ (পনেরো শতকের মধ্যভাগ), বারো বাজারের জোড় বাংলা ও গোড়ার মসজিদ (পনেরো শতকের শেষ ভাগ বা ষোলো শতকের প্রথম ভাগ), সোনারগাঁয়ের গোয়ালদি মসজিদ, এবং দিনাজপুরের সুরা মসজিদে।
এইভাবে, ইলিয়াসশাহী থেকে কররানী আমল পর্যন্ত প্রায় আড়াই শতাব্দীর মুসলিম শাসন বাংলার স্থাপত্যকলাকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। এটি ছিল এমন এক সময়, যখন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, শাসকদের শিল্পপ্রীতি, এবং স্থানীয় কারিগরদের দক্ষতা মিলিত হয়ে স্থাপত্যে এক স্বতন্ত্র বাংলা রীতির জন্ম দেয়—যা শুধু ইসলামী জগতেই নয়, সমগ্র দক্ষিণ এশীয় শিল্প ঐতিহ্যে অনন্য মর্যাদা লাভ করেছে।
বাংলার সুলতানি যুগের স্থাপত্য ও শিল্পকলার পর্যালোচনায় দেখা যায়, টিকে থাকা ধর্মীয় স্থাপত্যের মধ্যে মসজিদের পাশাপাশি সমাধিসৌধও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিদ্যমান। এই সমাধিসৌধ দুটি প্রধান ধরনে বিভক্ত—প্রথমত, সুদৃঢ় ইমারত আকারে নির্মিত সমাধি, এবং দ্বিতীয়ত, পাথরে বাঁধানো কবর। স্থায়িত্বের দিক থেকে ইমারত-আকৃতির সমাধিগুলি তুলনামূলকভাবে দৃঢ় হলেও, পাথরে বাঁধানো কবরগুলো প্রাকৃতিক ক্ষয় এবং মানবসৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞের কাছে অধিকতর অরক্ষিত ছিল। এরই মধ্যে কয়েকটি নিদর্শন আজও বাংলার স্থাপত্য ঐতিহ্যের উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করছে।
এই শ্রেণির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হিসেবে গণ্য হয় পান্ডুয়া-ফিরুজাবাদে অবস্থিত সুলতান জালালউদ্দীন মুহাম্মদ শাহের (১৪১৫–১৪৩২) সমাধি এবং বাগেরহাটে খান জাহান আলীর (মৃত্যু ১৪৫৯) সমাধি। উভয়ই বর্গাকার পরিকল্পনার উপর একগম্বুজ বিশিষ্ট সৌধ, যা নকশায় দিল্লির সুলতানি স্থাপত্যের প্রভাব বহন করলেও, শৈলীতে বাঙালি রীতির স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট। ইতিহাসবিদেরা মনে করেন, এই ধরনের সমাধি নির্মাণে অনুপ্রেরণা এসেছিল দিল্লির প্রাচীনতম বর্গাকার সমাধি—সুলতান ইলতুৎমিশের সমাধি—থেকে, যার স্থাপত্য উৎস প্রাক-ইসলামি সাসানীয় যুগের চাহারতক্ রীতিতে নিহিত। তবে মুগল যুগে যেমন সমাধি নির্মাণ একটি ব্যাপক প্রচলিত স্থাপত্যধারা হয়ে ওঠে, সুলতানি যুগে তেমন ঘন ঘন সমাধি নির্মাণ হয়নি—এটি একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য।
পাথরে নির্মিত সমাধির মধ্যে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে সোনারগাঁওয়ের সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের সমাধি। নিখুঁত খোদাই করা পাথরের গায়ে এর সূক্ষ্ম অলংকরণ মধ্যযুগীয় বাংলার পাথরশিল্পের পরিপক্বতা নির্দেশ করে। এর বিপরীতে, গৌড়-লখনৌতিতে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ এবং তাঁর পরিবারের সমাধি, কিংবা পান্ডুয়া-ফিরুজাবাদের সুফি সাধক শেখ জালালউদ্দীন তাবরিজি (মৃত্যু ১২২৬/১২৪৪) এবং নূর কুতুব আলমের (মৃত্যু ১৪১৫) সমাধিগুলি নকশা ও কারিগরিতে তুলনামূলকভাবে সংযত হলেও ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মর্যাদায় অনন্য। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, পাথরে বাঁধানো এই সমাধিগুলি, বিশেষত যেগুলি সুফি-পীর বা পুণ্যাত্মাদের নয়, সেগুলি শতাব্দীব্যাপী প্রাকৃতিক ক্ষয় ও মানবসৃষ্ট ধ্বংসের শিকার হয়ে আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে।
সুলতানি যুগের শিক্ষা ও ধর্মীয় সংস্কৃতির স্মারক হিসেবে গৌড়-লখনৌতির দুটি মাদ্রাসার উল্লেখ পাওয়া যায়। এর মধ্যে দরসবাড়ি মাদ্রাসা (১৫০৪) ছিল এক বিশাল আয়তাকার স্থাপনা, যার কেন্দ্রে উন্মুক্ত চত্বর এবং চত্বর ঘিরে ধারাবাহিক কক্ষ। পশ্চিম দিকের বৃহৎ কক্ষটি ছিল মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত, যার প্রমাণস্বরূপ এখনও তিনটি মিহরাব বিদ্যমান। এই নকশা থেকে বোঝা যায়, মাদ্রাসাটি ছিল শিক্ষার্থীদের আবাসন ও পাঠদান, পাশাপাশি ধর্মীয় অনুশীলনের কেন্দ্র। অপরদিকে বেলবাড়ি মাদ্রাসা (১৫০২) এখনও সম্পূর্ণরূপে উৎখনন হয়নি, ফলে এর পূর্ণাঙ্গ চিত্র অজানা রয়ে গেছে।
গৌড়-লখনৌতির কদম রসুল (১৫৩১) একটি স্বতন্ত্র প্রকৃতির ধর্মীয় স্থাপনা, যা সুলতানি যুগে সচরাচর দেখা যায়নি। হোসেনশাহী বংশের নাসিরউদ্দীন নুসরত শাহ এটি মসজিদের অবয়বে নির্মাণ করালেও এর মূল আকর্ষণ ছিল কেন্দ্রস্থলের উঁচু মঞ্চে মহানবী (সঃ)-এর পদচিহ্নের প্রতীকী স্মারক সংরক্ষণ। এই রীতি মুগল যুগে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে, কিন্তু সুলতানি যুগে এটি ছিল বিরল।
ধর্মীয় স্থাপত্যের তুলনায় সেক্যুলার স্থাপত্য আজ অতি বিরল। যে অল্প কয়েকটি টিকে আছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গৌড়-লখনৌতির দাখিল দরওয়াজা, গুমতি গেট এবং চিকা ভবন—শেষোক্তটি সম্ভবত প্রশাসনিক কার্যালয় ছিল। এছাড়াও রয়েছে পনেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত কয়েকটি সেতুর অবশেষ এবং গৌড়-লখনৌতি ও পান্ডুয়া-ফিরুজাবাদের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ।
গৌড়-লখনৌতির প্রাসাদ থেকে আজও দেখা যায় বাইশগজী নামে পরিচিত চৌহদ্দি প্রাচীরের কিছু অংশ এবং নকশাদার মোজাইক করা পাকা মেঝের ভগ্নাংশ। পান্ডুয়া-ফিরুজাবাদের প্রাসাদ, যা চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত, এখন প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত ও জঙ্গলে ঢাকা। অবশিষ্টাংশের মধ্যে রয়েছে একটি হাম্মামের ধ্বংসাবশেষ এবং একটি ভগ্ন বুরুজ, যা সম্ভবত মিনার নামে পরিচিত নগরপ্রবেশ ফটকের অংশ ছিল। এই প্রাসাদগুলির গৌরবময় বিবরণ আমরা পাই সমসাময়িক চীনা ও পর্তুগিজ পর্যটকদের রচনায়, যেখানে বর্ণিত হয়েছে মধ্যযুগীয় বাংলার নগর-পরিকল্পনা, প্রাচীর-সুরক্ষা, সজ্জিত প্রাসাদকক্ষ ও সভাগৃহের জাঁকজমক।
বাংলার সুলতানি স্থাপত্যে ব্যবহৃত উপকরণ ও নকশার ধরণ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের থেকে যথেষ্ট ভিন্ন। অধিকাংশ স্থাপনা ইটের তৈরি, যার দেয়াল ছিল ১.৫ থেকে ৪ মিটার পুরু। বহির্ভাগে প্রায়ই পাথরের সরদল সংযোজন করা হতো। ইমারতের কোণে সংযুক্ত বুরুজগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে অষ্টভুজাকৃতি, কখনও গোলাকার, এবং ছাদের শীর্ষভাগ ছিল সমতল, চূড়াবিহীন। ছাদের গঠন ছিল ধনুকাকৃতিতে বাঁকা, যা বাংলার ঐতিহ্যবাহী চৌচালা কুঁড়েঘরের অনুকরণে তৈরি, এবং তার উপর বসানো হতো উল্টানো পাত্র আকৃতির গম্বুজ। এই গম্বুজ স্থাপনের জন্য ত্রিকোণী পেন্ডেন্টিভ অথবা স্কুইঞ্চ—দুটি বহিরাগত কৌশল—ব্যবহৃত হতো। বৃহৎ ইমারতের অভ্যন্তরে দ্বিকেন্দ্রিক সূচ্যগ্র খিলান বহনের জন্য গ্রানাইট পাথরের শক্ত স্তম্ভ সারিবদ্ধভাবে বসানো হতো, ফলে ভেতরের স্থান হয়ে উঠত খোলামেলা ও আড়ম্বরপূর্ণ।
স্থাপত্য অলঙ্করণের ক্ষেত্রে পোড়ামাটির ফলক ও খোদাইকৃত পাথরের সমন্বয় ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মন্দিরশিল্প থেকে ধার করা শিকল ও ঘণ্টার মোটিফ, লতাপাতা খচিত ফ্রেম, জটিল জ্যামিতিক নকশা—সবই সুলতানি মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মীয় স্থাপত্যে শোভিত হতো। মসজিদের পূর্বপ্রান্তের প্রবেশপথ বরাবর মিহরাবসমূহে প্রায়ই খিলানযুক্ত গ্রিল সংযোজন করা হতো, যাতে আলো ও বাতাস চলাচল করলেও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা বজায় থাকে।
এইসব বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে বাংলার সুলতানি স্থাপত্য ভারতীয় মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের ধারায় এক স্বতন্ত্র বাঙালি রীতি গড়ে তোলে, যা চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল এবং মুগল প্রভাব বিস্তার লাভের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল। পরবর্তী সময়ে এই রীতির কিছু উপাদান মন্দির স্থাপত্যেও দেখা যায়, যদিও সপ্তদশ শতক থেকে মুগল রীতিই প্রধান ধারায় পরিণত হয়।
স্থাপত্যের পাশাপাশি সুলতানি যুগে চিত্রকলার অবস্থাও বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। একসময় মনে করা হতো, ইসলামের বিধিনিষেধের কারণে এ যুগে চিত্রকলার কোনো চর্চা ছিল না। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় এই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। আসলে মুসলিম শাসন ও হিন্দু সংস্কৃতির মেলবন্ধনের ফলে একটি সমন্বয়ী শিল্পধারা গড়ে ওঠে, যেখানে পারস্যীয় শিল্পরীতি এবং ভারতীয় আঞ্চলিক রীতি পরস্পরের প্রভাব গ্রহণ করেছিল। এ যুগের কিছু সুলতান ও হিন্দু রাজপুরুষ শিল্প ও সংস্কৃতির সক্রিয় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, যার ফলে আঞ্চলিক চিত্ররীতির বিকাশ ঘটে।
যদিও বাংলার সুলতানি যুগের চিত্রকলার উদাহরণ আজ হাতে অতি সামান্য, অন্যান্য অঞ্চলে এর কিছু প্রতিফলন পাওয়া যায়। বিশেষত গুজরাট, রাজস্থান ও সৌরাষ্ট্রে জৈন শিল্পীরা এই সময়ে অসাধারণ পাণ্ডুলিপি অলংকরণ ও চিত্রাঙ্কনে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। তাঁদের আঁকা ক্ষুদ্রচিত্রে পারস্যীয় সূক্ষ্মরীতি ও ভারতীয় উজ্জ্বল রঙের সংমিশ্রণ স্পষ্ট। এই যুগের চিত্রকলার উত্তরাধিকার থেকেই পরবর্তীকালে তিনটি স্বতন্ত্র ধারার জন্ম হয়—মুগল, রাজস্থানি এবং দক্ষিণী রীতি—যা ভারতের শিল্পকলার ইতিহাসে এক স্বর্ণযুগের সূচনা করে।
সুলতানি আমলের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিচার করতে গেলে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান উৎস, যদিও সমগ্র ভারতবর্ষের পরিসরে এ উৎসের ভূমিকা তুলনামূলকভাবে সীমিত। তবুও কিছু অঞ্চল—বিশেষত বাংলা, বাহমনি, গুজরাট ইত্যাদি—এর ইতিহাস রচনায় প্রত্নতত্ত্ব ও শিলালিপি গবেষণা এক অমূল্য সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। দিল্লি সালতানাতের প্রাথমিক যুগ থেকেই মুদ্রা ও লিপি রাজবংশের ক্রমবিকাশ, শাসকদের নীতি, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য দিয়েছে। ইলতুৎমিশ, গিয়াসউদ্দীন বলবন, আলাউদ্দিন খলজি, এবং বিশেষভাবে মুহাম্মদ-বিন-তুঘলকের শাসনামলে প্রচলিত মুদ্রা তাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও প্রশাসনিক কৌশলের এক প্রমাণ বহন করে। এই মুদ্রা শুধু অর্থনৈতিক লেনদেনের মাধ্যমই ছিল না, বরং শাসকগণের ক্ষমতার প্রতীক এবং রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক নীতি ঘোষণার মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহৃত হতো। স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং চিত্রকলার সমন্বিত বিকাশ সুলতানি যুগের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতার দৃশ্যমান নিদর্শন।
ইতিহাসের বিচারে সুলতানি আমল ১১৮৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত—প্রায় সাড়ে তিন শতকেরও বেশি সময়জুড়ে। এই দীর্ঘকালীন সময়ে দিল্লি সালতানাত একদিকে যেমন শক্তিশালী রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তেমনি সময়ের আবর্তে তা ভেঙে গিয়ে বিভিন্ন আঞ্চলিক স্বাধীন সালতানাতের জন্ম দেয়। এর মধ্যে বাংলার সালতানাত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ এটি শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতাই অর্জন করেনি, বরং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিতেও শীর্ষস্থান দখল করেছিল। ১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিস্তৃত বাংলার সুলতানি আমল এক সমৃদ্ধ যুগ হিসেবে পরিচিত। সমসাময়িক বিদেশি পর্যটক ও বণিকদের বিবরণে প্রতীয়মান হয়, বাংলার পণ্য, বিশেষত কৃষি ও বস্ত্রশিল্পের খ্যাতি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। রেশম, সূক্ষ্ম সুতির কাপড়, চিনি, গুড়, এবং বড় বড় সমুদ্রগামী কাঠের জাহাজ ছিল এর প্রধান রপ্তানি সামগ্রী। বঙ্গোপসাগরপারের সমুদ্রপথে বাংলার বণিকেরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আরব উপকূল, এমনকি পূর্ব আফ্রিকার বন্দরনগরীগুলোতেও পণ্য রপ্তানি করতেন।
বাংলার এই অর্থনৈতিক বিকাশ কেবল প্রাকৃতিক সম্পদ ও উর্বর ভূমির কারণে নয়, বরং সুসংগঠিত প্রশাসন, শান্তিপূর্ণ সামাজিক পরিবেশ, এবং দক্ষ কারিগরি ও বাণিজ্যিক অবকাঠামোর ফলেও সম্ভব হয়েছিল। সুলতানি যুগে ধান ছিল প্রধান খাদ্যশস্য, যা সহজেই উৎপাদন করা যেত এবং প্রচুর পরিমাণে উদ্বৃত্ত থাকত। সেইসঙ্গে ইক্ষু চাষও ছিল বিস্তৃত, যার গুড় ও চিনি শুধু অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাত না, বিদেশেও রপ্তানি হতো। ঐ সময়কার চীনা পর্যটক মা হুয়াং তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে উল্লেখ করেছেন, বাংলার বাজারে চিনি, রেশম, সূক্ষ্ম বস্ত্র ও জাহাজ নির্মাণশিল্পের ব্যাপক চাহিদা ছিল।
বাংলার রাজনৈতিক কাঠামোও ছিল যথেষ্ট সুসংহত। রাজ্যশাসনের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসন লাভ ছিল একটি প্রচলিত রীতি, অর্থাৎ সুলতানের পুত্রই সাধারণত পরবর্তী সুলতান হতেন। তবে কেবল রক্তসম্পর্কই যথেষ্ট ছিল না—আমির, উমরাহ এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সমর্থন ব্যতীত কেউ সিংহাসনে আরোহণ করতে পারতেন না। ইতিহাসে দেখা যায়, সুলতানের পুত্র না হয়েও ক্ষমতায় আরোহনের নজির রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলার অন্যতম প্রভাবশালী শাসক আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৮) কোনো রাজবংশীয় উত্তরাধিকারী ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের নির্বাচিত প্রার্থী। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র নাসিরউদ্দীন নুসরাত শাহ (১৫১৮-১৫৩২) সুলতান হন, তবে এখানেও রাজকর্মচারীদের সাধারণ অনুমোদন অপরিহার্য ছিল। এই প্রক্রিয়া একদিকে রাজতন্ত্রকে উত্তরাধিকারের কাঠামোয় বেঁধে রাখলেও, অন্যদিকে অভিজাত শ্রেণির ক্ষমতাকেও সুদৃঢ় করেছিল।
সামরিক শক্তি ছিল সুলতানি আমলের আরেকটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান। বাংলার সেনাবাহিনী চারটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত ছিল—অশ্বারোহী বাহিনী, গজারোহী বাহিনী, পদাতিক বাহিনী এবং নৌবাহিনী। পদাতিক সৈন্যদের ‘পাইক’ বলা হতো এবং দশজন অশ্বারোহী মিলিয়ে গঠিত হতো একটি ‘খেল’। নৌবাহিনীকে বলা হতো ‘খেল-ই-সর’, যার সর্বোচ্চ কর্মকর্তাকে বলা হতো ‘মীর-বহর’। বাংলার গজারোহী বাহিনী উপমহাদেশে সুপরিচিত ছিল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করত। সেনাবাহিনীর বেতন ও রসদ সরবরাহের দায়িত্বে থাকতেন ‘উজির-ই-লস্কর’। প্রযুক্তিগতভাবে বাংলা সেনারা সময়ের তুলনায় অগ্রসর ছিল—তারা পর্তুগিজদের কাছ থেকে কামান ব্যবহারের কৌশল শিখেছিল এবং বাবরের সাথে যুদ্ধে এই কামানের ব্যবহার করে। যদিও বাবর বাংলাকে জয় করতে পারেননি, তিনি নুসরাত শাহের সাথে সম্মানজনক সন্ধি করেছিলেন এবং তাঁর আত্মজীবনী ‘তুজুক-ই-বাবুরি’-তে নুসরাত শাহের শাসনপ্রজ্ঞা, সৌজন্য ও ভ্রাতৃস্নেহের বিশেষ প্রশংসা করেছেন। বাবরের ভাষায়, “এ রকম ভ্রাতৃপ্রেম রাজাদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না।” তিনি প্রথম কোনো সুলতানের নামের সাথে ‘বাঙালি’ উপাধি যুক্ত করেন, যা বাংলা পরিচয়ের ইতিহাসে এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।
প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ‘মহল’ ছিল কর আদায়ের মৌলিক একক, যা কয়েকটি ‘শিক’-এ বিভক্ত থাকত। শিকের দায়িত্বে থাকতেন ‘শিকদার’, যা পরে একটি প্রচলিত উপাধিতে রূপান্তরিত হয় এবং আজও বাংলার গ্রামীণ সমাজে এই নাম দেখা যায়। এই করব্যবস্থা রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে কার্যকর ভূমিকা রাখত।
বাংলার সুলতানি আমল কেবল রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেই নয়, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এক নবজাগরণের সূচনা করেছিল। সেই সময়ে বাংলায় একটি স্বতন্ত্র স্থাপত্যশৈলী বিকাশ লাভ করে, যা স্থানীয় হিন্দু-বৌদ্ধ রীতির সাথে মুসলিম গঠনশৈলীর এক চমৎকার সংমিশ্রণ। একই সময়ে বাংলা সাহিত্যেরও নব অধ্যায়ের সূচনা হয়। যদিও এই সময়ে রচিত অধিকাংশ সাহিত্য সংস্কৃত ভাষায়, তথাপি সুলতান রোকন-উদ-দীন বারবাক শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় কীর্তিবাস ওঝা প্রথমবারের মতো সংস্কৃত রামায়ণ বাংলায় অনুবাদ করেন (১৪৫৫–১৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ)। এই অনুবাদ কেবল ভাষাগত দিক থেকে নয়, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও যুগান্তকারী ছিল, কারণ এটি বাঙালি সাধারণ মানুষের কাছে রামায়ণের কাহিনি সহজবোধ্য ভাষায় পৌঁছে দেয়।
শাসনব্যবস্থার দৃঢ়তা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সামরিক শক্তি, এবং সাংস্কৃতিক বিকাশ—এই সব মিলিয়ে সুলতানি আমল বাংলার ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই সময়ে বাংলার পরিচিতি উপমহাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মানচিত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচ্যের সোনার বাংলার ধারণা বহির্বিশ্বে প্রথম সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা পায় এই যুগেই। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি একে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল, যেখানে শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য, এমনকি কৃষি ও বাণিজ্যও সমান তালে বিকাশ লাভ করেছিল। সেই দিক থেকে দেখলে, সুলতানি আমল বাংলার ইতিহাসে শুধু একটি রাজনৈতিক যুগ নয়, বরং এক পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক রেনেসাঁর যুগ।
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি
- ১. ইরফান হাবিব (সম্পা.), মধ্যকালীন ভারত, প্রথম খণ্ড, কে.পি. বাগচী এন্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৯০।
- ২. আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস (সুলতানি আমল), ২য় প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১৫৫।৩. সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৮, চিত্র ৪।
- ৪. অনিরুদ্ধ রায়, সুলতানি আমলের অর্থনৈতিক ইতিহাস: একটি সমীক্ষা, কলকাতা: ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭।
- ৫. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড ও চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৫।
- ৬. খন্দকার ফজলে রাব্বী, বাংলার মুসলমান, অনুবাদ: আব্দুর রাজ্জাক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৬।
- ৭. এ. কে. এম. শাহনাওয়াজ, ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ: সুলতানি পর্ব, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০২।
- ৮. এ. কে. এম. শাহনাওয়াজ, দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস: ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৩।৯. Muhammad Mohar Ali, History of the Muslims of Bengal, Vol. B।
- ১০. Muhammad Mohar Ali, History of the Muslims of Bengal, Vol. A, Riyadh: Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, 1985।
- ১১. L. P. Sarma, History of Medieval India (1000–1740 A.D.), Kornak Publishers, 1987।১২. V. A. Smith, The Oxford History of India, Oxford University Press, 1981।
- ১৩. R. P. Tripathi, Some Aspects of Muslim Administration।
- ১৪. Irfan Habib, The Economic History of Medieval India: A Survey, Tulika Books, 2001।

 নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা
নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা