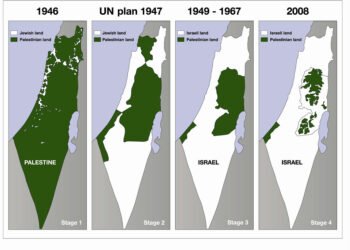লিখেছেনঃ মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম
ইসরায়েল —পশ্চিম এশিয়ার একটি রাষ্ট্র, যার ইতিহাস, রাজনীতি, এবং বর্তমান বাস্তবতা মধ্যপ্রাচ্যের জটিল ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। হিব্রু ভাষায় ‘মেদিনাত ইসরায়েল’ এবং আরবি ভাষায় ‘দাউলাত ইস্রা’ঈল’ নামে পরিচিত এই রাষ্ট্রটি ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি এমন এক ভূখণ্ডে অবস্থিত, যাকে ঘিরে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে ধর্মীয়, জাতিগত ও রাজনৈতিক সংঘাত, বিশেষত ইহুদি এবং ফিলিস্তিনিদের মধ্যে।
ভৌগোলিকভাবে ইসরায়েল ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে এবং লোহিত সাগরের উত্তরে বিস্তৃত। উত্তর সীমান্তে লেবানন, উত্তর-পূর্বে সিরিয়া, পূর্বদিকে জর্দান ও ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর, পশ্চিমে গাজা ভূখণ্ড এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে মিশরের সঙ্গে এর স্থলসীমান্ত রয়েছে। তেল আবিব, যদিও আনুষ্ঠানিক রাজধানী নয়, ইসরায়েলের অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও বাণিজ্যিক প্রাণকেন্দ্র। দেশটির প্রধান সরকারি দপ্তর, আদালত ও সংসদ অবস্থিত জেরুসালেম শহরে—যেটিকে ইসরায়েল তার “অভেদ্য ও একক রাজধানী” হিসেবে দাবি করে। কিন্তু এই দাবিকে আন্তর্জাতিক মহলের অধিকাংশ দেশ স্বীকৃতি দেয় না এবং তাদের দূতাবাসসমূহ এখনো তেল আবিবেই অবস্থান করছে, যদিও যুক্তরাষ্ট্র, গুয়াতেমালা এবং ইতালির মতো কয়েকটি দেশ এই দাবিকে সমর্থন জানিয়েছে।

রাজনৈতিকভাবে ইসরায়েল একটি সংসদীয় গণতন্ত্র, যার কেন্দ্রে রয়েছে এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা—ক্নেসেত। প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন সরকারের কার্যকর প্রধান। ইসরায়েল নিজেকে একটি “ইহুদিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র” হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে, যা একদিকে ধর্মীয় পরিচয়ের উপর দাঁড়িয়ে, অপরদিকে গণতন্ত্রের সাংবিধানিক কাঠামো বজায় রাখার চেষ্টা করে—এই দ্বৈত বৈশিষ্ট্য নিয়ে দেশটির অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নানা বিতর্ক দেখা দেয়।
আধুনিক ইসরায়েল বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে এক বিশ্বনেতা রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রতি বছর দেশটি তার জিডিপির প্রায় ৫ শতাংশ গবেষণা ও উন্নয়নে ব্যয় করে, যা বিশ্বের সর্বোচ্চ। প্রতি দশ লক্ষ মানুষের অনুপাতে ইসরায়েলে ৮,৩৪১ জন বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী ও গবেষক রয়েছেন, যা একটি ব্যতিক্রমী পরিসংখ্যান। তথ্য ও প্রযুক্তি রপ্তানি, উচ্চশিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রযুক্তিনির্ভর স্টার্টআপের ঘনত্বের দিক থেকেও ইসরায়েল বিশ্বে অন্যতম শীর্ষে। ব্লুমবার্গ এবং গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্স-এর মতো সূচকে একাধিকবার শীর্ষ দশে স্থান পাওয়া দেশটি জ্ঞানের বিকাশেও ব্যতিক্রমী—উইকিপিডিয়ায় প্রতি দশ লক্ষ নাগরিকের অনুপাতে ইসরায়েলিদের সম্পাদনার সংখ্যা বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ।
বর্তমানে ইসরায়েলে আনুমানিক ৯৩ লক্ষ মানুষের বসবাস, যার মধ্যে প্রায় ৬৭ লক্ষ ইহুদি ও ১৯ লক্ষ আরব, যাঁদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান। এই বৈচিত্র্য সত্ত্বেও, ইসরায়েল হলো বিশ্বের একমাত্র রাষ্ট্র যেখানে ইহুদিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং এই জাতিগোষ্ঠীর জন্য একটি স্বতন্ত্র জাতীয় আবাসভূমি গঠনের লক্ষ্যে এই রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এখানকার জনসংখ্যার শিক্ষাগত মানও উচ্চ; ২৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী জনগণের মধ্যে প্রায় অর্ধেকেরই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ডিগ্রি রয়েছে, যা বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ।
তবে এই উন্নয়নের ছবি যেমন উজ্জ্বল, তেমনি এর ছায়াপাতও গভীর। ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধের পর থেকে ইসরায়েল ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড—বিশেষ করে পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকার উপর সামরিক দখল বজায় রেখেছে। এই দখল দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিকভাবে নিন্দিত হয়ে আসছে এবং এটি বর্তমান বিশ্বে দীর্ঘতম সামরিক দখলের একটি উদাহরণ হিসেবে পরিগণিত। এই দখলদারিত্বের ফলশ্রুতিতে ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘন, ভূমি দখল, বসতি স্থাপন এবং জাতিসংঘের একাধিক প্রস্তাব লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে।
জাতিসংঘের ১৯২টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ১৬৪টি ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিলেও ২৮টি রাষ্ট্র, যাদের অধিকাংশই মুসলিমপ্রধান, এখনও ইসরায়েলকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নেয়নি। এসব দেশের মতে, ইসরায়েল একটি অবৈধ রাষ্ট্র যা ফিলিস্তিনের মূল ভূখণ্ড দখল করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবু, মিশর (১৯৭৯) ও জর্দান (১৯৯৪) ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে সম্পর্ক স্বাভাবিক করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, মরক্কো ও সুদানের সঙ্গে “আব্রাহাম চুক্তি”-এর মাধ্যমে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ফলে মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতি নতুন মোড় নিচ্ছে।
ইসরায়েলকে নিয়ে বিতর্ক কেবল তার ভূখণ্ড বা ইতিহাসেই সীমাবদ্ধ নয়; এর জাতীয় পরিচয়, রাষ্ট্রের চরিত্র এবং মানুষের ন্যায্য অধিকার নিয়েও প্রশ্ন উঠে আসে। ইহুদিদের জন্য একটি নিরাপদ আবাসভূমির প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রটির প্রেক্ষাপটে ফিলিস্তিনিদের বিতাড়ন, নিপীড়ন এবং রাষ্ট্রহীনতা একটি মানবিক সংকট হিসেবে আজও বিদ্যমান। এই দ্বন্দ্ব ও বিভাজনের ইতিহাস একদিকে যেমন ধর্মীয় আবেগে ঘেরা, অন্যদিকে তেমনি জটিল রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বাস্তবতায় আবদ্ধ।
ইসরায়েল তাই এক অদ্ভুত দ্বৈততার প্রতীক—একদিকে প্রযুক্তি, জ্ঞান, উদ্ভাবন ও উন্নয়নের এক চূড়ান্ত রূপ; অন্যদিকে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, দখল ও মানবিক সংকটের নিত্য সহচর। এই রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে কেবল তার নিজস্ব বিজ্ঞান ও সামরিক কৌশলের উপর নয়, বরং আরও নির্ভর করছে আঞ্চলিক ন্যায়বিচার, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং মানবিকতার ভিত্তিতে টেকসই রাজনৈতিক সমাধান খোঁজার উপর।
ইসরায়েলের শাসনব্যবস্থা ও ফিলিস্তিনিদের ওপর তার দীর্ঘমেয়াদী নীতি নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরে বহুদিন ধরেই বিতর্ক, সমালোচনা ও উদ্বেগ বিদ্যমান। তবে ২০২১ সালের এপ্রিলে মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ যে রিপোর্টটি প্রকাশ করে, তা এই বিতর্কে এক গভীর ও জোরালো বাঁক নিয়ে আসে। সংস্থাটি তাদের বিশ্লেষণে দাবি করে যে, ইসরায়েল সরকার শুধুমাত্র ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে নিপীড়নমূলক আচরণ করছে না, বরং একটি প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকল্পিত ও কাঠামোগত বৈষম্যের মাধ্যমে ইহুদি জনগোষ্ঠীর জন্য রাষ্ট্রটিকে ‘অগ্রাধিকারভিত্তিক’ করে তুলেছে। এই বৈষম্য আইন, রাষ্ট্রীয় নীতি ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ঘোষণায় এতটাই প্রোথিত যে, তা এককথায় একটি পূর্ণাঙ্গ শাসনতান্ত্রিক দর্শনকেই ধারণ করে।
রিপোর্টে উত্থাপিত প্রধান অভিযোগ হল, ইসরায়েলের রাষ্ট্রনীতির মূলে রয়েছে—“ইহুদিদের কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন রাখা”। জনসংখ্যার অনুপাত, রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ—এই তিনটি স্তম্ভে ইসরায়েলি শাসনযন্ত্র পরিকল্পিতভাবে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যার মাধ্যমে ফিলিস্তিনিরা দমন ও নিঃশেষিত হয়ে পড়ছে। দখলকৃত পশ্চিম তীর ও গাজা ভূখণ্ডে এই বৈষম্য আরও নগ্ন ও নির্মম। ফিলিস্তিনি বসতি উচ্ছেদ, তাদের ভূমি কেড়ে নিয়ে সেখানে ইহুদি বসতি নির্মাণ, সুউচ্চ সুরক্ষা প্রাচীর নির্মাণ এবং এইভাবে ফিলিস্তিনিদের ছিন্নভিন্ন ছিটমহলে রূপান্তর করে তাদের চলাচল, জীবনধারা ও আত্মপরিচয়কেই সংকুচিত করে দেওয়া হয়েছে। অনেক এলাকায় এমনকি তাদের নাগরিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত রাখা হয়েছে, আর এইসব কার্যকলাপ এমন এক মাত্রায় পৌঁছেছে যেখানে তা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ—বিশেষত জাতিগত বিচ্ছিন্নতাবাদ বা অ্যাপারথেইড-এর স্বরূপ ধারণ করছে।
হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তাদের পর্যবেক্ষণে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে, কীভাবে এই বৈষম্য কেবল ঘটনাচক্রে ঘটে চলেছে এমন নয়, বরং ইসরায়েলি রাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসরায়েলের দখলকৃত অঞ্চলে রাষ্ট্রযন্ত্রের সক্রিয় মদতে আইনত এবং প্রশাসনিকভাবে জারি রয়েছে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে এক পদ্ধতিগত বিভাজন। বসতির অনুমোদন, জমির মালিকানা, চলাচলের স্বাধীনতা, নাগরিক সেবা থেকে শুরু করে নির্বাচনী অধিকার—সবখানেই এই বৈষম্য বিদ্যমান।
এমন অভিযোগ নতুন নয়। ২০১৭ সালেই অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল তাদের এক বিবৃতিতে জানায়, ইসরায়েল ফিলিস্তিনিদের উপরে যে ব্যবস্থা চালু রেখেছে, তা “দীর্ঘস্থায়ী নিপীড়নের এক আধুনিক রূপ।” সেই বিবৃতিতে সংস্থাটি জানায়, পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ইসরায়েল পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুসালেমের হাজার হাজার একর ভূমি দখল করে, সেখানে প্রায় ছয় লক্ষ ইহুদি বসতি স্থাপন করেছে—যা আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে অবৈধ। এইসব বসতি নির্মাণের পাশাপাশি ফিলিস্তিনিদের নিজস্ব ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, জমি দখল করা হয়েছে, এমনকি তাদের জল ও বিদ্যুৎ ব্যবহারের অধিকারও সীমিত করে রাখা হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ফিলিস্তিনিদের জন্য কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও ধর্মীয় বা পারিবারিক কারণে চলাচল—সবকিছুই হয়ে উঠেছে সীমাহীন কঠিন ও অবরুদ্ধ।
বিশ্লেষকদের মতে, এই অবস্থা কেবলমাত্র একটি রাজনৈতিক সংঘাত নয়, বরং একটি কাঠামোগত বৈষম্যের নিষ্ঠুর রূপ, যা যুগপৎ জাতিগত ও রাষ্ট্রনৈতিক দিক থেকে ফিলিস্তিনিদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক তো বটেই, অনেক ক্ষেত্রেই অধিকারহীন প্রজা করে তোলে। এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাপনার পেছনে আছে এক ঐতিহাসিক ও মতাদর্শগত ধারা—যা ইসরায়েলকে কেবল ইহুদি জনগোষ্ঠীর নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াসে, অন্য জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব, অধিকার ও পরিচয়কে অস্বীকার করেছে।
এইসব বাস্তবতা আজ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে। বিশ্বের নানা প্রান্তে আন্দোলনকারী সংগঠন, বুদ্ধিজীবী, গবেষক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি ক্রমাগত প্রশ্ন তুলছে—একটি রাষ্ট্র যদি ধর্মীয় বা জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে অপর একটি জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করে, তবে সেই রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক পরিচয় বা মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার দাবিটি আদৌ টেকসই থাকে কি না?
ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিন প্রশ্ন তাই কেবল একটি আঞ্চলিক বিরোধ নয়, বরং এটি একটি বৃহত্তর নৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যবস্থার সামনে দাঁড় করানো এক কঠিন পরীক্ষা। যেখানে একদিকে প্রযুক্তি, উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের সাফল্য, অন্যদিকে জবরদখল, নিপীড়ন ও জাতিগত বৈষম্যের অভিযোগ—এই দুই বিপরীত স্রোত একসঙ্গে প্রবাহিত হচ্ছে। এই সংঘাতের নিষ্পত্তি কেবল শান্তিচুক্তির মাধ্যমে নয়, বরং ন্যায়বিচারভিত্তিক মানবিক বিবেচনার মাধ্যমেই সম্ভব—এমন প্রত্যাশাই ক্রমবর্ধমান বিশ্বজনমত থেকে উঠে আসছে।
ব্যুৎপত্তি
ইসরায়েল নামটির পেছনে রয়েছে এক দীর্ঘ ও বহুস্তরীয় ইতিহাস, যা ধর্মীয় আখ্যান, ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে এক গভীর পরিচয়ের সন্ধান দেয়। এই নামটির উৎপত্তি, প্রচলন এবং ইতিহাসের প্রাচীনতম সাক্ষ্যগুলি শুধু ধর্মীয় জগতেই নয়, বরং প্রাচীন নিকটপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতাকেও স্পর্শ করে।
হিব্রু বাইবেল অনুযায়ী, ইসরায়েল নামটি প্রথম দেয়া হয় পিতৃপুরুষ জ্যাকবকে—এক গভীর প্রতীকী মুহূর্তে। বলা হয়, তিনি ঈশ্বরের এক দূতের সঙ্গে সারারাত কুস্তি করেন এবং শেষপর্যন্ত বিজয়ী হন। এই ‘সংগ্রাম’ এবং তার মধ্য দিয়ে আত্মপরিচয়ের এক নবতর রূপ পাওয়ার ফলে ঈশ্বর তাঁকে নাম দেন “יִשְׂרָאֵל” (Yisra’el), যার অর্থ ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে ভিন্ন হতে পারে—‘ঈশ্বর শাসন করেন’, ‘ঈশ্বর রক্ষা করেন’ অথবা সর্বাধিক জনপ্রিয় ব্যাখ্যায়, ‘যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন’। এই নামটি শুধু একটি ব্যক্তির নয়, একটি জনগোষ্ঠীর পরিচয়ে পরিণত হয়—জ্যাকবের সন্তানেরাই পরবর্তীতে ‘ইসরায়েলের সন্তান’ নামে পরিচিতি লাভ করে এবং ইতিহাসে একটি জাতির রূপ পায়।
ধর্মগ্রন্থের বাইরেও, এই নামের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব ১৩ শতকের মিশরীয় মারনেপ্টাহ স্তম্ভে। এটি হল এক রাজকীয় স্মারক পাথর বা স্টেল, যাতে রাজা মারনেপ্টাহের (ফারাও রামেসেস II-এর পুত্র) সামরিক জয়গাথা উৎকীর্ণ হয়েছে। এই স্তম্ভে ‘ইসরায়েল’ নামটি একটি জাতিগত বা গোষ্ঠীগত সমষ্টি হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে, এবং এটি প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে ইসরায়েল শব্দটির প্রথম পরিচিত ব্যবহার হিসেবে চিহ্নিত। এই উল্লেখটি স্বল্প হলেও তা প্রমাণ করে যে ইসরায়েল নামধারী জনগোষ্ঠী তখনকার সময়ে ইতোমধ্যে প্রাচীন কনান বা লেভান্ট অঞ্চলে পরিচিত একটি বাস্তব অস্তিত্ব হিসেবে বিবেচিত ছিল—যা কেবল ধর্মীয় কল্পনা নয়, বরং ইতিহাসের পাতায়ও ছাপ ফেলেছিল।
গবেষকরা এই স্তম্ভে ব্যবহৃত হায়ারোগ্লিফিক রচনার ব্যাকরণ ও গঠন বিশ্লেষণ করে বলেন, ‘ইসরায়েল’ নামটি এখানে একটি জাতি বা জনগোষ্ঠী বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে, কোনও নগর বা শহরের নাম হিসেবে নয়—যা সেই সময়কার মিশরীয় রীতি অনুযায়ী এক অর্থবহ তথ্য। নামটির পাশে যে চিহ্নগুলি ব্যবহৃত হয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট হয়, এটি একটি বসতি-নির্ভর রাষ্ট্র ছিল না বরং একটি বিচ্ছিন্ন, আদিবাসী গোত্রের গোষ্ঠী—যাদের সঙ্গে রাজা মারনেপ্টাহের মিশরীয় বাহিনীর সংঘর্ষ হয়েছিল।
ইসরায়েল নামটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শুধু একটি জনগোষ্ঠী বা জাতির পরিচয় হয়ে ওঠেনি, বরং এটি একটি রাষ্ট্র, এক ধর্মীয় ঐতিহ্য, এমনকি রাজনৈতিক মতাদর্শেরও কেন্দ্রীয় প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। হিব্রু বাইবেলের কাহিনিগুলিতে ইসরায়েল একদিকে যেমন ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত ভূমিতে একটি ধার্মিক জীবনের প্রতীক, অন্যদিকে তেমনই এটি বিপর্যয়, নির্বাসন ও প্রত্যাবর্তনের এক দীর্ঘগল্পও। পরবর্তীকালে ইসরায়েল ও জুডার দুটি পৃথক রাজ্য এই নামের ধারাবাহিক ঐতিহ্য বহন করে, যা আবার ধ্বংস, বিজয় এবং প্রজারূপে পরিবর্তিত হতে হতে দীর্ঘশতক ধরে ইহুদি পরিচয়ের মূল ভিত্তি গঠন করে।
এছাড়াও, হিব্রু নাম “Yisra’el” থেকে গ্রীক ভাষায় এর অনুবাদ করা হয়েছিল সেপ্টুয়াজিন্টে (Septuagint)—যা বাইবেল অনুবাদের প্রথম দিকের গ্রীক প্রচেষ্টা। এই অনুবাদে নামটি “Ισραήλ” (Israēl) রূপে প্রতিস্থাপিত হয়, যা পরবর্তীতে খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বেও প্রবেশ করে এবং আজও বিশ্বজুড়ে এক ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে।
এইভাবে, ইসরায়েল নামটির মধ্যে নিহিত রয়েছে ধর্মীয় তাত্পর্য, প্রত্নতাত্ত্বিক সত্যতা এবং রাজনৈতিক বাস্তবতার এক আন্তঃসম্পর্ক। মারনেপ্টাহ স্তম্ভের একটিমাত্র হায়ারোগ্লিফিক উল্লেখ আমাদের নিয়ে যায় সেই প্রাচীন কালে, যেখানে ইতিহাস, মিথ, বিশ্বাস এবং পরিচয়ের বীজ একসঙ্গে গাঁথা ছিল। এই নামটি কেবল এক পুরাতন শব্দ নয়, বরং এক ধারাবাহিক সভ্যতার বহমান প্রতিচ্ছবি—যা আজও রাজনীতি, ধর্ম এবং ইতিহাসের পরিসরে তর্ক-বিতর্ক ও প্রজ্ঞার কেন্দ্রে বিরাজ করছে।
ইসরায়েলের ইতিহাস
ইসরায়েলের ইতিহাস বলতে আমরা মূলত যে ভৌগোলিক অঞ্চলকে বুঝি, তা আজকের আধুনিক ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের পরিসীমার মধ্যেই অবস্থিত। এই অঞ্চলটি বহু প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দক্ষিণাংশে অবস্থিত এই ভূমিটি প্রাচীন কালে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল—কেনান, ফিলিস্তিন, পবিত্র ভূমি বা হোলি ল্যান্ড ইত্যাদি। ইতিহাসের নানা বাঁকে এই ভূমি শুধু রাজনৈতিক দখল ও শাসনের পট পরিবর্তনের সাক্ষীই নয়, বরং বহু ধর্মীয় বিশ্বাস ও জাতিসত্তার উৎপত্তি ও সংঘাতের কাহিনির নীরব ধারকও বটে।
মানব সভ্যতার বিবর্তনের এক প্রাচীন করিডোর হিসেবে এই অঞ্চলটি আফ্রিকা থেকে মানব সম্প্রসারণের এক গুরুত্বপূর্ণ সেতু ছিল। আনুমানিক ১০ হাজার খ্রিস্টপূর্বে নটুফীয় সংস্কৃতির আবির্ভাব এখানকার প্রাগৈতিহাসিক সাংস্কৃতিক বিকাশের অন্যতম সাক্ষ্য। পরে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে ক্যানানীয় সভ্যতার উত্থানের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চল ব্রোঞ্জ যুগে প্রবেশ করে। এরপর থেকে ব্রোঞ্জ যুগের শেষদিকে এটি মিশরের প্রভাবাধীন অঞ্চলে পরিণত হয়। লৌহ যুগে এখানেই গড়ে ওঠে প্রাচীন ইসরায়েল ও যিহূদা রাজ্য—যা কেবল রাজনৈতিক পরিসরই নয়, বরং ইহুদি জাতিসত্তার এবং ইব্রাহিমীয় ধর্মীয় ঐতিহ্যের এক গঠনতান্ত্রিক সূচনা ঘটায়।
ইহুদি ধর্মের পাশাপাশি এই ভূমি ছিল শমরীয় ধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম, ইসলাম, দ্রুজ, বাহাই এবং আরও অনেক ক্ষুদ্র ধর্মীয় গোষ্ঠীর জন্মস্থান ও বিকাশের ক্ষেত্র। এই ধর্মীয় বৈচিত্র্য একদিকে যেমন সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যের প্রতীক, অন্যদিকে তেমনই বহুবিধ দখল, নির্যাতন ও পালাবদলের কারণেও পরিণত হয়।
খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই অঞ্চলকে ঘিরে বারবার ক্ষমতার পালাবদল ঘটে। প্রথমে আসে আসিরীয় সাম্রাজ্য, পরে ব্যাবিলনীয়রা। ব্যাবিলনীয়দের হাতে যিহূদা রাজ্যের পতনের মাধ্যমে প্রথম ইহুদি নির্বাসনের সূচনা হয়। এরপর হাখমানেশি পার্সিয়ান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এই অঞ্চল, যেখানে পার্সীয়রা ইহুদিদের জেরুসালেমে ফিরে গিয়ে মন্দির পুনর্নির্মাণের অনুমতি দেয়। এই ঘটনা ইহুদি ইতিহাসে দ্বিতীয় মন্দির যুগের সূচনা হিসেবে চিহ্নিত।
হেলেনিস্টিক যুগে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট-এর মৃত্যুর পরে টলেমীয় এবং সেলেউসিড বংশ এই অঞ্চলের ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে। এই সময় ইহুদিদের উপর গ্রিকীকরণের চাপ বাড়ে, যার প্রতিক্রিয়ায় গড়ে ওঠে মাকাবীয় বিদ্রোহ এবং এর ফলশ্রুতিতে হাসমোনীয় রাজবংশের সূচনা ঘটে। শতবর্ষের কিছু কম সময় এই রাজ্য স্বাধীনতা ভোগ করলেও পরবর্তীতে রোমান প্রজাতন্ত্র অঞ্চলটি দখল করে নেয় এবং ধীরে ধীরে এটি রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।
রোমান শাসনকালেই ইহুদি-রোমান যুদ্ধসমূহ সংঘটিত হয় (৬৬-১৩৫ খ্রিস্টাব্দ), যার ফলে বিপুলসংখ্যক ইহুদি নিহত, নির্বাসিত বা দাসত্বে বিক্রীত হন। দ্বিতীয় মন্দির ধ্বংস হয় ৭০ খ্রিস্টাব্দে এবং ইহুদি পরিচয় এক ভিন্ন পর্বে প্রবেশ করে—বিচ্ছিন্ন ও প্রবাসী জাতি হিসেবে। এই ধ্বংসের পরিণতিতে ইহুদিরা কেবল ভূখণ্ড হারায়নি, হারিয়েছে আত্মপরিচয়ের একটি নিগূঢ় ভরকেন্দ্রও।
চতুর্থ শতকের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলে জেরুসালেম ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল খ্রিস্টীয় তীর্থভূমিতে পরিণত হয়। যদিও এই পরিবর্তন ইহুদিদের জন্য এক নতুন রূপে নিপীড়নের সূচনা করে, যেখানে তারা রাজনৈতিক ও ধর্মীয়ভাবে প্রান্তিক হয়ে পড়ে। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে আরবদের উত্থানের ফলে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল বাইজেন্টাইনদের হাতছাড়া হয়ে যায়। ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম সেনাপতি খালিদ ইবনে ওয়ালিদের নেতৃত্বে জেরুসালেম বিজিত হয় এবং ইসলামি শাসনের সূচনা ঘটে। এই সময় পবিত্র ভূমির চেহারা আবারও পাল্টে যায়। জেরুসালেমে গড়ে ওঠে আল-আকসা মসজিদ ও কুব্বাত আস-সাখরা, যা পরবর্তীতে মুসলিমদের তৃতীয় সর্বোচ্চ পবিত্র স্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
১১ থেকে ১৩ শতকের মধ্যকার সময় ছিল ক্রুসেডের যুগ। ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের নেতৃত্বে ক্রুসেডার বাহিনী একাধিকবার জেরুসালেম দখল করে এবং মুসলিমদের সাথে রক্তক্ষয়ী সংঘাতে লিপ্ত হয়। পাল্টাপাল্টি দখলের এই সংঘর্ষ অনেক সময় স্থানীয় জনসাধারণের ওপর চূড়ান্ত নিপীড়ন ডেকে আনে। পরে সালাহউদ্দিন আইয়ুবি এই অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেন। ১৩ শতকে যখন মঙ্গোল আক্রমণ সংঘটিত হয়, তখন মিশরের মামলুক সালতানাত প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং এই অঞ্চল রক্ষা পায়। এরপর প্রায় আড়াই শতাব্দী ধরে এই ভূমি মামলুক শাসনের অধীনে ছিল, যতক্ষণ না অটোমান তুর্কিরা ১৬শ শতকে পুরো লেভান্ট দখল করে নেয়।
১৬ থেকে ২০ শতকের শুরু পর্যন্ত এই অঞ্চল অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে একটি প্রাদেশিক ইউনিট হিসেবে পরিচালিত হয়। যদিও রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীলতা ছিল, তবে এই সময়ে ইহুদিদের সংখ্যা এই অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে ছিল কম। তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল ইউরোপ, মধ্য এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার নানা প্রান্তে।
১৯শ শতকের শেষভাগে ইউরোপীয় প্রেক্ষাপটে ইহুদি জাতীয়তাবাদ, তথা জায়নবাদ, এক নতুন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ক্রমবর্ধমান ইহুদি-বিদ্বেষ, রাশিয়ায় পোগ্রোম এবং ইউরোপজুড়ে জাতীয়তাবাদী জোয়ারের প্রেক্ষাপটে জায়নবাদ দাবি তোলে—ইহুদিদের জন্য একটি স্বতন্ত্র, নিরাপদ জাতীয় আবাসভূমির। এই দাবির কেন্দ্রে ছিল প্যালেস্টাইন। হিব্রু ভাষায় এই প্রত্যাবর্তনকে বলা হয় ‘আলিয়াহ’—যার অর্থ, স্বর্গের দিকে আরোহণ, কিংবা আধ্যাত্মিক ও জাতীয় পুনরুত্থান।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ব্রিটেন ফিলিস্তিন অঞ্চলকে ‘ম্যান্ডেট’ শাসনাধীন করে তোলে। ১৯১৭ সালে জারি করা হয় ‘ব্যালফোর ঘোষণা’, যেখানে ব্রিটিশ সরকার প্রথমবারের মতো ইহুদি জাতির জন্য একটি ‘জাতীয় আবাসভূমি’ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই ঘোষণার মধ্য দিয়েই আরবদের সঙ্গে ইউরোপীয় শক্তির বিরোধ গড়ে উঠতে থাকে। আরব জাতীয়তাবাদীরা মনে করে, ব্রিটিশরা তাদের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এবং ইহুদি অভিবাসনের মাধ্যমে আরব ভূখণ্ডকে ধীরে ধীরে দখল করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে।
ম্যান্ডেট শাসনকাল জুড়ে ইহুদি অভিবাসনের হার বাড়তে থাকে, বিশেষ করে নাৎসি জার্মানির উত্থানের পর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ও পরে লক্ষ লক্ষ ইহুদি ইউরোপ থেকে পালিয়ে ফিলিস্তিনে আশ্রয় নিতে থাকে। এর ফলে আরব-ইহুদি বিরোধ আরও তীব্র হয় এবং উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ, দাঙ্গা ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ব্যাপক আকার ধারণ করে। ব্রিটিশরা এই উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয় এবং ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘ ফিলিস্তিনকে দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করার প্রস্তাব দেয়—একটি ইহুদি রাষ্ট্র ও একটি আরব রাষ্ট্র। ইহুদিরা এই পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও আরবরা প্রত্যাখ্যান করে।
১৯৪৮ সালের ১৪ মে ইসরায়েল রাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হয়। তার পরদিনই মিশর, সিরিয়া, জর্দান, লেবানন ও ইরাকের সামরিক বাহিনী ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। এই আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের ফলে প্রায় সাত লক্ষ ফিলিস্তিনি তাদের ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হন—এক ঐতিহাসিক মানবিক সংকট, যা ‘নাকবা’ (বিপর্যয়) নামে পরিচিত। একদিকে যেমন ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠিত হয়, অন্যদিকে তেমনই একটি জাতি নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদিত হয়ে উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে।
পরবর্তী কয়েক দশকে মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র বহুবার রক্তাক্ত সংঘর্ষের মাধ্যমে পাল্টে যায়। ১৯৫৬, ১৯৬৭, ১৯৭৩—প্রতিটি যুদ্ধে ইসরায়েল একেকবার করে জয়লাভ করে এবং আরও ভূখণ্ড দখল করে ফেলে—বিশেষ করে পশ্চিম তীর, গাজা, পূর্ব জেরুসালেম ও গোলান মালভূমি। ১৯৭৯ সালে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির মাধ্যমে মিশর ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেয় এবং সীমানা সংক্রান্ত একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এরপর ১৯৯৩ সালে ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা (পিএলও)-র সাথে ওসলো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার মাধ্যমে ফিলিস্তিনি জাতীয় কর্তৃপক্ষ গঠিত হয় এবং পশ্চিম তীর ও গাজার কিছু অংশে স্বশাসনের সূচনা ঘটে। ১৯৯৪ সালে জর্ডানের সঙ্গে দ্বিতীয় শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
তবে এই শান্তির প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত একটি স্থায়ী নিষ্পত্তি এনে দিতে পারেনি। একদিকে ইসরায়েলের বসতি সম্প্রসারণ, অন্যদিকে ফিলিস্তিনের ভেতরে রাজনৈতিক বিভাজন, হামাসের উত্থান, গাজা অবরোধ, রকেট হামলা ও সামরিক অভিযানের সমান্তরালে, বহু অসামরিক মানুষ প্রতিনিয়ত সহিংসতার বলি হয়ে চলেছে। ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু সমস্যা আজও অনিশ্চিত, এবং অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ ক্রমশ আরও গভীর হয়ে উঠছে।
ইসরায়েলের ইতিহাস তাই কেবল একটি রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাস নয়; এটি আত্মপরিচয়, ধর্মীয় উত্তরাধিকার, জাতিগত অধিকার ও ভূরাজনৈতিক কৌশলের এক জটিল কাহিনি। এখানে বারবার ঘুরে ফিরে আসে একটিই প্রশ্ন—কোন ভূমিকে কারা নিজের বলে দাবি করবে, কোন ইতিহাস হবে বৈধ, আর কোন স্মৃতি চাপা পড়বে অস্ত্রের জোরে। আজকের দিনে দাঁড়িয়েও এই প্রশ্নগুলির জবাব অসম্পূর্ণ, অথচ এই অসম্পূর্ণতাই সম্ভবত ইতিহাসের সবচেয়ে স্থায়ী উত্তর।
প্রাগৈতিহাসিক কাল
ইসরায়েলের ইতিহাসের সূচনা কেবল লিখিত রেকর্ড কিংবা ধর্মীয় কাহিনিতে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এই অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আমাদের মানবজাতির আদিযুগের কথাও বলে। আধুনিক ইসরায়েলের উত্তরাংশ, বিশেষ করে গালীল সাগরের সন্নিকটে অবস্থিত উবেদিয়া নামক স্থানে আজ থেকে প্রায় ১৫ লক্ষ বছর আগে প্রাচীন মানুষের বসবাসের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এই আবিষ্কারটি পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য সংযোজন, কারণ এটি আফ্রিকার বাইরের অঞ্চলে মানুষের প্রাচীনতম অস্তিত্বের অন্যতম প্রমাণ বহন করে। এখানকার আবিষ্কৃত ফ্লিন্ট টুল বা পাথরের তৈরি হস্তনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র আদিম প্রযুক্তির এক সুস্পষ্ট চিহ্ন, যাকে একিলীয় প্রযুক্তি নামে অভিহিত করা হয়। এই প্রযুক্তি প্রায় ১৪ লক্ষ বছর পূর্বে ব্যবহৃত হতো এবং ধারণা করা হয়, বাইজাত রুহামা গ্রুপ এবং গেসের নোট ইয়াকভ গ্রুপ নামক প্রাচীন মানবগোষ্ঠী এই পদ্ধতির ব্যবহার করত।
প্রাক-মানব ইতিহাসের যে স্তরগুলি এতদিন পর্যন্ত মূলত আফ্রিকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল বলে ভাবা হতো, আজ প্রত্নতত্ত্ব সেই ধারণায় প্রশ্ন তুলছে। ইসরায়েলের ভূখণ্ড আজ সেইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সাহায্য করছে। কার্মেল পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত এল-তাবুন ও এস-স্খুল গুহায় নিয়ান্ডারথাল ও আধুনিক মানবজাতির দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এইসব গুহার স্তরে স্তরে পাথর, হাড় এবং নানা জৈব উপাদান বিশ্লেষণ করে গবেষকরা অনুমান করেন যে এই অঞ্চলটি প্রায় ছয় লক্ষ বছরের মানব-চিহ্ন ধারণ করে আছে। এই স্ট্রেটিগ্রাফি রেকর্ডগুলি আমাদের জানায় কীভাবে এক ধাপে ধাপে মানব বিবর্তন, পরিবেশ পরিবর্তন ও সাংস্কৃতিক অভিযোজন ঘটেছে।
এই এলাকা কেবল প্রাণীবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রেই নয়, বরং মানব সভ্যতার বিকাশের গতিপথ অনুধাবনের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেসেম ও ম্যানট গুহা এই পর্বতশ্রেণির অন্তর্গত আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকা। এখানে যে ধরনের পাথর-প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে, তা আমাদের জানায় মানুষের চিন্তাশক্তির ক্রমোন্নয়ন, পশুশিকার কৌশল, খাদ্য সংরক্ষণ এবং সামাজিক বিন্যাস সম্পর্কে।
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, আফ্রিকার বাইরে সবচেয়ে প্রাচীন শারীরিকভাবে আধুনিক মানুষের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে ইসরায়েলের উত্তর অংশে স্খুল ও কাফেজ অঞ্চলে। এই হোমিনিডস জাতির অস্তিত্ব প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার বছর আগেকার। এরা তথাকথিত ‘আধুনিক মানুষ’-এর শারীরিক গঠন ও আচরণে অনেকাংশে অনুরূপ ছিল। এই নিদর্শনগুলি একদিকে যেমন আমাদের ‘আউট অফ আফ্রিকা’ থিওরির একটি বিকল্প পথ নির্দেশ করে, তেমনি মধ্যপ্রাচ্যের এই অঞ্চলটির একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট হিসেবেও চিহ্নিত করে।
মানব ইতিহাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক হলো আনুমানিক ১০ হাজার খ্রিস্টপূর্বে নটিফীয় সংস্কৃতির উত্থান। এই সংস্কৃতি কৃষির প্রাথমিক রূপ, প্রাণীর আংশিক গৃহপালন এবং স্থায়ী বসবাসের সূচনা ঘটায়। শিকারজীবী গোষ্ঠী থেকে একটি আধা-নগরায়িত জীবনের দিকে মানুষের অভিসার শুরু হয় এই সময়েই। নটিফীয়রা প্রথমবারের মতো মৃতদেহ কবর দেওয়ার নিয়ম প্রবর্তন করে, যা সামাজিক ও ধর্মীয় আচরণবিধির প্রাথমিক গঠন নির্দেশ করে। এদের বাসগৃহ, শস্য সংরক্ষণের কৌশল এবং খাদ্য সংগ্রহের পদ্ধতি আমাদের জানায় কৃষির পূর্ববর্তী সাংস্কৃতিক অভিযোজন সম্পর্কে।
এইসমস্ত নিদর্শন একত্রে বিবেচনা করলে বোঝা যায়, আজকের ইসরায়েল রাষ্ট্র যে ভূমিতে অবস্থিত, তা শুধু ধর্মীয় ইতিহাসের নয়, মানব সভ্যতার আদিম উত্তরণের ইতিহাসেরও এক মৌলিক প্রেক্ষাপট। এই অঞ্চলটি যুগ যুগ ধরে মানুষের অভিযোজন, সংগ্রাম ও সংস্কৃতির লালনভূমি ছিল। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ব, জীবাশ্মবিদ্যা, এবং স্ট্রেটিগ্রাফিক বিশ্লেষণ একযোগে আমাদের নিয়ে যায় এক মহাকালের দরজায়—যেখানে ইসরায়েল নামক ভৌগোলিক পরিসীমা শুধুমাত্র একটি জাতির রাজনৈতিক আত্মপরিচয়ের ভিত্তি নয়, বরং মানব জাতির বহু সহস্র বছরের বিবর্তনের অমলিন উপাখ্যান।
ক্যানান
প্রাচীন লেভান্ত অঞ্চলের ইতিহাসে ক্যানানীয় সভ্যতা এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে এসেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা যায়, মধ্য ব্রোঞ্জ যুগে (আনুমানিক ২১০০ থেকে ১৫৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) ক্যানানীয়রা বর্তমান ইসরায়েল, পশ্চিম তীর এবং দক্ষিণ লেবাননের বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে বসবাস করত। তাদের বসতি ছিল শহরকেন্দ্রিক, এবং এই শহরগুলি ছিল নিজ নিজ স্বাধীন অথবা আধা-স্বাধীন রাজ্য কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত। এই নগররাষ্ট্রগুলোতে স্থানীয় রাজা অথবা শাসকগণ শাসন করতেন এবং প্রাচীন লিপিতে পাওয়া কিছু মিশরীয়, হিট্টিত এবং আকাদীয় চিঠিপত্র থেকে এই ধরণের প্রশাসনিক কাঠামোর অস্তিত্বের তথ্য মেলে।
শহরগুলোর চারপাশে প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে নির্মিত হত পাথরের শক্ত প্রাচীর। কালক্রমে এইসব শহরের ধ্বংসাবশেষ ও পরবর্তী নির্মাণের স্তরাবলি একত্রিত হয়ে ঢিবিতে পরিণত হয়, যাকে আধুনিক প্রত্নতত্ত্বে বলা হয় ‘টেল’ (Tell)। টেল হাজর, টেল মেগিদো, টেল বেইত শান ইত্যাদি স্থানে খননকার্যে আবিষ্কৃত হয়েছে ক্যানানীয়দের এই প্রতিরক্ষা কাঠামো, বাসগৃহ, মন্দির, সমাধি ও দৈনন্দিন ব্যবহারের বহু বস্তু। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল বহুদেবতাবাদী, এবং তারা স্থানীয় দেবদেবী যেমন এল, আসিরা, বাল এবং আনাতের উপাসনা করত। এই দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া ও উৎসব পালন ছিল ক্যানানীয় সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
মধ্য লৌহ যুগের শেষদিকে ক্যানানীয়দের একাংশ মিশরের নীল বদ্বীপ এলাকায় বসতি স্থাপন করে। এই অভিবাসনের সূত্রে ক্যানান এবং মিশরের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিশেষ করে হাইকসোস নামক একটি গোষ্ঠী, যাদের ক্যানানীয় অথবা এশীয় উৎসের বলে মনে করা হয়, তারা খ্রিষ্টপূর্ব ১৬ শতকের দিকে মিশরের উত্তরাংশে (নিচ মিশর) শাসনক্ষমতা অর্জন করে এবং দীর্ঘ সময় ধরে মিশরের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। হাইকসোসরা ঘোড়ার গাড়ি, নতুন ধরণের অস্ত্র ও সামরিক কৌশল মিশরে নিয়ে আসে, যা পরবর্তী মিশরীয় সামরিক কৌশলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে এই বিদেশী শাসকদের প্রতি স্থানীয় মিশরীয়দের অসন্তোষ জন্মায় এবং অবশেষে ফারাও কামোস ও তার পুত্র আহমোস-এর নেতৃত্বে মিশরীয়রা হাইকসোসদের পরাজিত করে এবং তাদের বিতাড়িত করে।
এরপর শুরু হয় মিশরের নব্য সাম্রাজ্য যুগ, যা খ্রিষ্টপূর্ব ১৫৫০ থেকে ১২০০ অব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সময় মিশরীয় সাম্রাজ্য ক্যানানের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং অঞ্চলটিকে একটি উপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসে। গাজা শহরকে প্রশাসনিক কেন্দ্র করে মিশর ক্যানান অঞ্চল শাসন করত এবং স্থানীয় রাজারা মিশরীয় ফারাওদের প্রভুত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ক্যানানে স্থাপিত মিশরীয় দুর্গ ও প্রশাসনিক কার্যালয় সেই মিশরীয় কর্তৃত্বের প্রতিচ্ছবি। খ্রিষ্টপূর্ব ১৪৫৭ অব্দে, মিশরীয় ফারাও থুতমোস তৃতীয় ক্যানানের মেগিদো শহরে অনুষ্ঠিত বিখ্যাত যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন। কাদেশের রাজা সহ একাধিক ক্যানানীয় শাসক বিদ্রোহ করে বসেছিল; এই বিদ্রোহ থামিয়ে থুতমোস তৃতীয় মিশরীয় কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। মেগিদোর যুদ্ধকে প্রাচীন ইতিহাসের অন্যতম প্রামাণ্য সামরিক অভিযান হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
তবে শেষ ব্রোঞ্জ যুগে (খ্রিষ্টপূর্ব ১৩০০–১২০০) মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে এক গভীর রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটের সূচনা ঘটে। বহু সভ্যতা—বিশেষত মিশরীয়, হিট্টিত, মাইসেনীয়—এই সময়ে দুর্বল হয়ে পড়ে বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এর অন্যতম কারণ হিসেবে আবহাওয়া পরিবর্তন, দুর্ভিক্ষ, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, পরস্পরবিরোধী যুদ্ধ এবং সমুদ্র থেকে আগত অভিবাসীদের আগমনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ক্যানানের শহরগুলিও এই সংকট থেকে মুক্ত ছিল না। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা যায়, হাজর, মেগিদো, বেইত শান, এক্রন, ইসদুদ এবং আস্কালনের মতো ক্যানানীয় নগরগুলি হয় সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে অথবা তাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। আগুনে পোড়া স্থাপত্যাবশেষ, ভাঙা মূর্তি এবং ধ্বংসস্তূপের স্তর থেকে বোঝা যায় এক মারাত্মক রাজনৈতিক বিপর্যয় এই অঞ্চলজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল।
এই সময়ই উদিত হয় দুইটি নতুন জনসমষ্টি—যারা ক্যানান ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এক নতুন যুগের সূচনা ঘটায়। এদের মধ্যে একটি দলকে বলা হয় ‘সমুদ্রজাত মানুষ’ বা ‘সী পিপলস’—যাদের মধ্যে পলেষ্টীয়রা (Philistines) অন্যতম। তারা সম্ভবত এজিয়ান দ্বীপপুঞ্জ কিংবা মাইসেনীয় সভ্যতার উত্তরাধিকারী ছিল এবং ব্রোঞ্জ যুগের শেষ পর্যায়ে পূর্ব ভূমধ্যসাগরের উপকূলে এসে বসতি স্থাপন করে। পলেষ্টীয়রা ক্যানানের দক্ষিণাঞ্চলে আশদোদ, আশকেলন, গাজা, গাথ এবং এক্রন শহরগুলি গড়ে তোলে—যা পরে পঞ্চনগর রাষ্ট্র (Pentapolis) হিসেবে পরিচিত হয়। তাদের সমাজে ছিল উন্নত ধাতুবিদ্যা, বৃহৎ স্থাপত্য এবং ক্রীড়ার ঐতিহ্য।
অন্যদিকে আরেকটি দল ধীরে ধীরে ক্যানানের পার্বত্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে—যাদের প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ধর্মীয় পরিচিতি থেকে ‘ইস্রায়েলীয়’ নামে অভিহিত করা হয়। এই জনগোষ্ঠী ক্যানানীয় সভ্যতার পরবর্তী উত্তরসূরী হলেও তারা ভিন্ন একটি ধর্মীয় ও সামাজিক পরিচয় গঠন করে। পাহাড়ি এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছোট ছোট কৃষিভিত্তিক গ্রামে বসবাস শুরু করে তারা। এদের সমাজ কাঠামো ছিল অপেক্ষাকৃত সরল এবং কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা তখনও গড়ে ওঠেনি। প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়, এই সমাজ ধাপে ধাপে পশুপালন, কৃষিকাজ ও সাম্প্রদায়িক উপাসনার মধ্য দিয়ে একটি পৃথক সংস্কৃতি গঠন করতে থাকে।
এইভাবে ব্রোঞ্জ যুগের পতনের মাধ্যমে একটি নতুন লৌহ যুগের সূচনা ঘটে—যেখানে ক্যানানীয়, মিশরীয়, পলেষ্টীয় এবং ইস্রায়েলীয়দের সংঘর্ষ, সহাবস্থান ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মধ্য দিয়ে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ইতিহাস এক নতুন গতিপথে প্রবেশ করে। ক্যানানের ভূখণ্ড, যা এতদিন ধরে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের করায়ত্ত ছিল, এখন একাধিক জাতিগোষ্ঠীর বাস্তুভূমিতে পরিণত হয়। তাদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা, ধর্মীয় বিশ্বাস, বর্ণমালা ও প্রশাসনিক অভ্যাস আগামী শতকগুলিতে পশ্চিম এশিয়ার রাজনীতি, ধর্ম এবং সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে।
এই ইতিহাস কেবল একটি অঞ্চলভিত্তিক বিবরণ নয়, বরং মানব সভ্যতার ধারাবাহিক বিবর্তনের একটি শক্তিশালী পাঠ। ক্যানানীয় সভ্যতার উত্থান, মিশরীয় সাম্রাজ্যের আধিপত্য, হাইকসোসদের শাসন, পলেষ্টীয় আগমন এবং ইস্রায়েলীয় সম্প্রদায়ের বিকাশ—সবকিছু মিলিয়ে এটি এক জটিল অথচ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ প্রেক্ষাপট, যা আমাদের আজকের বিশ্ব ইতিহাস বুঝতে অনন্যভাবে সাহায্য করে।
প্রাচীন ইসরায়েল ও যিহুদা
প্রাচীন ইসরায়েলীয়দের ইতিহাস প্রথম লৌহ যুগে গড়ে ওঠা এক বিস্তৃত সামাজিক ও ধর্মীয় রূপান্তরের কাহিনি, যা মূলত ইসরায়েলের পার্বত্য অঞ্চলে কেনানীয় সমাজের অভ্যন্তর থেকে গড়ে উঠেছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ১৩ শতকের শেষভাগে মিশরের ফারাও মেরনেপ্তাহ একটি স্মারক স্তম্ভ নির্মাণ করেন, যাতে ‘ইসরায়েল’ শব্দটি প্রথমবারের মতো লিখিত ইতিহাসে স্থান পায়। এই হায়ারোগ্লিফিক শিলালিপি, যেটি মেরনেপ্তাহ স্তম্ভ নামে পরিচিত, তাতে ঘোষণা করা হয়েছিল—”ইসরায়েল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে; তার বংশধরেরা আর বেঁচে নেই।” এটি মূলধারার প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে ইসরায়েল জাতির অস্তিত্বের সর্বপ্রাচীন লিখিত প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত।
প্রথম লৌহ যুগে, আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ১২০০ থেকে ১০০০ সালের মধ্যে, জর্ডান নদীর দুই তীর ধরে এবং সামারিয়ার পাহাড়ি এলাকায় শতাধিক ছোট ছোট জনপদ গড়ে ওঠে, যেগুলিকে প্রাচীন ইসরায়েলীয় বসতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এইসব গ্রামে সাধারণত গড়ে চারশত জনসংখ্যা ছিল এবং তারা সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভরশীল জীবনযাপন করত। কৃষিকাজ, পশুপালন, জলপাই ও আঙুরচাষ ছিল তাদের জীবিকার মূল উৎস। এছাড়াও তারা স্থানীয় পর্যায়ে কিছু হস্তশিল্প ও লেনদেনের চর্চাও করত। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে পাওয়া মাটির পাত্র এবং সরঞ্জামাদির সরলতা প্রমাণ করে যে এই সমাজটি ছিল অত্যন্ত মিতব্যয়ী এবং ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী।
মৃৎশিল্পে ছিল না কোনো অলঙ্করণ বা উচ্চমানের কারুকাজ, বরং দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোই ছিল মুখ্য। যদিও লিপি ও লেখার ব্যবহার সীমিত ছিল, তথাপি প্রাথমিক পর্যায়ের কিছু শিলালিপি, গৃহাভ্যন্তরের লিখনচিহ্ন ও খণ্ড খণ্ড লেখ্যনির্দেশ মিলেছে, যা ইঙ্গিত দেয় যে তথ্য সংরক্ষণের এক ক্ষুদ্রতর ব্যবস্থা তাদের সমাজে বিদ্যমান ছিল। উইলিয়াম জি. ডিভার এই সময়ের ইসরায়েল সম্পর্কে মন্তব্য করেন—“ইহারা কেবল একটি জাতিগোষ্ঠী ছিল না; বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক গঠন কাঠামোতে ইসরায়েল একটি বিকাশমান রাষ্ট্রের রূপ নিচ্ছিল।”
আধুনিক গবেষণায় অধিকাংশ পণ্ডিত একমত যে ইসরায়েলীয়রা সম্পূর্ণরূপে বাইরের জাতি ছিল না বরং তারা কেনানীয়দের মধ্য থেকেই একটি স্বতন্ত্র সমাজ হিসেবে গড়ে ওঠে। এই পরিবর্তনের মূলে ছিল ধর্মীয় ও সামাজিক রূপান্তর। প্রাচীন কেনানীয়দের বহু ঈশ্বরবিশ্বাস থেকে ধীরে ধীরে ইসরায়েলীয়রা এক গৃহদেবতার পূজা শুরু করে এবং সেই গৃহদেবতা পরে পরিণত হয় জাতীয় দেবতা ইয়াহওয়েহ-এ। এই রূপান্তরের ফলে ইসরায়েলীয়দের মধ্যে একপ্রকার একেশ্বরবাদের বীজ বপিত হয়, যা পরবর্তীতে ইহুদী ধর্মের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে।
এই সামাজিক স্বাতন্ত্র্যবোধের চিহ্ন হিসেবে ইসরায়েলীয় সমাজে কড়াকড়ি জাতিগত ও পারিবারিক নিয়ম চালু হয়। বিয়ে ও বংশের শুদ্ধতা সংরক্ষণে কেনানীয়দের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ হয়। নিজস্ব পূর্বপুরুষের পরিচয় ও গোষ্ঠী ইতিহাসকে গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয়। এই নতুন পরিচয়বোধ নির্মাণের প্রক্রিয়াতেই গঠিত হয় ‘ইসরায়েল’ জাতিসত্তার ভিত্তি। এম.সি. নাটের মতে, এই প্রথম লৌহ যুগেই সেই স্বাতন্ত্র্যচেতনার উন্মেষ ঘটে যার মধ্য দিয়ে ইসরায়েলীয়রা নিজেদের কেনানীয়দের থেকে পৃথক করে দেখতে শুরু করে।
এদিকে, একই সময়ে উপকূলীয় এলাকায় বসবাসকারী পলেষ্টীয়দের আগমন ঘটে, যারা সম্ভবত এজিয়ান অঞ্চল থেকে আগত এক অভিবাসী জাতি। প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যে তাদের রান্নার পাত্র, খাদ্যাভ্যাসে শূকরের মাংসের ব্যবহার, এবং মাইসিনীয় নকশায় তৈরি কুমার শিল্প প্রমাণ করে যে তারা স্থানীয় কেনানীয়দের থেকে সাংস্কৃতিকভাবে ভিন্ন। তাদের দ্বারা নির্মিত নগরগুলো ছিল বড় এবং সুসজ্জিত, যা সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস এবং এক জটিল প্রশাসনিক কাঠামোর উপস্থিতির ইঙ্গিত বহন করে। এদের শহরগুলো—যেমন গাজা, গাথ, এক্রন প্রভৃতি—ছিল পল্লবিত কেল্লা ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র। পলেষ্টীয়রা ছিল যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষ, এবং পরবর্তী সময়ে তারা ইসরায়েলীয়দের অন্যতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে।
তুলনামূলকভাবে ইসরায়েলীয় সমাজ ছিল কৃষিভিত্তিক ও অপেক্ষাকৃত সরল। তবে এই সরলতাই তাদের সামাজিক সংহতি ও সাংগঠনিক স্থায়িত্বে সাহায্য করেছিল। তারা পার্বত্য এলাকায় গ্রাম গঠন করে এবং ফিলিস্তিন উপত্যকার তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও বিচ্ছিন্ন পরিবেশে নিজেদের বিকাশ ঘটায়। এই বিকাশই ধীরে ধীরে ইসরায়েলের রাজতন্ত্র, ধর্মীয় ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভিত্তি স্থাপন করে।
অন্যদিকে, পলেষ্টীয়দের জটিল শহর এবং আক্রমণাত্মক নীতি ইসরায়েলীয়দের সামরিক ও সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় গঠনে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। বাইবেলীয় বিবরণে ফিলিস্তীয়দের বিরুদ্ধে লড়াই, যেমন—গোলিয়াথের সঙ্গে দাভিদের যুদ্ধ, এই দ্বন্দ্বের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়।
এই প্রথম লৌহ যুগে ইসরায়েলীয়দের মধ্যে যে ধর্মীয় ধারণা, সামাজিক শৃঙ্খলা এবং জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে, তা-ই পরবর্তী সময়ে ইহুদি জাতীয়তাবাদের এবং একেশ্বরবাদী ধর্মমতের ভিত্তি স্থাপন করে। সেইসঙ্গে এই সময়ই ইসরায়েলীয় সমাজ বাইবেলীয় বিচারকদের যুগে প্রবেশ করে, যাঁরা স্থানীয়ভাবে নেতৃত্ব প্রদান করতেন এবং প্রয়োজনে সামরিক প্রতিরক্ষা বা সামাজিক শৃঙ্খলার রক্ষাকর্তা হিসেবে কাজ করতেন। বিচারক যুগ থেকেই ইসরায়েলের রাজতন্ত্রের দিকে ধাবমান রাজনীতি ও সমাজের সূচনা হয়।
এইভাবে প্রথম লৌহ যুগের ইসরায়েলীয়রা কেবল একটি জনগোষ্ঠী হিসেবেই নয়, বরং একটি রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ঐক্যের রূপে আত্মপ্রকাশ করে, যার শিকড় কেনানীয় সমাজে থাকলেও যা ক্রমশ ধর্ম, সমাজ ও ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এক স্বতন্ত্র জাতিসত্তায় রূপান্তরিত হয়।
ইসরায়েল এবং যিহূদা (দ্বিতীয় লৌহ যুগ)
১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৯০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে প্রাচীন ইস্রায়েলের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিন্যাসের সূচনা হয়—যেখানে ইস্রায়েল এবং যিহূদা নামে দুটি পৃথক রাজ্যের বিকাশ ঘটে। হিব্রু বাইবেলের বর্ণনায় এই দুটি রাজ্য এককালে একটি একীভূত রাজ্য ছিল বলে দাবি করা হয়, যা প্রথমে রাজা শৌল, পরে রাজা দাভিদ এবং সর্বশেষে তাঁর পুত্র সলোমনের অধীনে শাসিত হত। বলা হয়ে থাকে, রাজা সলোমনের শাসনামলেই প্রাচীন জেরুজালেমে প্রথম পবিত্র মন্দির নির্মিত হয়, যেটি ইহুদী ধর্মে ‘সোলোমনের মন্দির’ নামে পরিচিত।
তবে, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বাইবেলের এই বিবরণ নিয়ে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। একটি পক্ষ মনে করে, বাইবেল যেমনটা বর্ণনা করে, তেমন একটি একীভূত ও সুসংগঠিত রাজ্য ইতিহাসে বাস্তবেই বিদ্যমান ছিল। অপর পক্ষের দাবি, যদি এমন কোনও যুক্তরাজ্য থেকেও থাকে, তবে তার বিস্তার ও সাংগঠনিক কাঠামো বাইবেলের বর্ণনার তুলনায় অনেক ছোট ও সীমিত ছিল। ফলে, ‘যুক্তরাজ্য’ ধারণাটিই একটি ধর্মীয় বা কাহিনিরূপ কাঠামো বলে অনেকে মত দেন।
যদিও ঐতিহাসিকভাবে বাইবেলের সমস্ত বিবরণ সমর্থিত নয়, তথাপি অধিকাংশ প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক একমত যে, আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে উত্তরভাগে ইস্রায়েল নামক একটি রাজ্য এবং দক্ষিণভাগে যিহূদা নামে অন্য একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উত্তরাঞ্চলের ইস্রায়েল রাজ্য তুলনামূলকভাবে বৃহৎ ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ছিল। অমরিড বংশের অধীনে এ রাজ্য আঞ্চলিক রাজশক্তিতে পরিণত হয়। তারা সামারিয়া, গ্যালিলী, জর্ডান উপত্যকা, শারন এবং ট্রান্সজর্ডানের বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করত। রাজ্যটির রাজধানী ছিল সামারিয়া (শোমরোন), যেখানে প্রাচীন লৌহ যুগের অন্যতম বৃহৎ স্থাপত্য নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এর আগে ইস্রায়েল রাজ্যের রাজধানী একাধিকবার স্থানান্তরিত হয়েছিল—শেখেম, পেনুয়েল এবং তিরজাহ ছিল পূর্ববর্তী রাজধানী শহরগুলি।
উল্লেখযোগ্য যে, ইস্রায়েল রাজ্যে ক্ষমতার হস্তান্তর প্রায়ই সহিংস অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সংঘটিত হত, যার ফলে রাজনীতিতে অস্থিরতা ছিল প্রবল। এর বিপরীতে দক্ষিণের যিহূদা রাজ্য ছিল তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র, কিন্তু অধিকতর স্থিতিশীল। যিহূদা রাজ্যের শাসনক্ষমতা মূলত দাভিদিক বংশের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল এবং প্রায় চার শতাব্দী ধরে একটানা এই বংশ রাজত্ব করে। রাজ্যটির রাজধানী ছিল জেরুজালেম, যা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দিক থেকে কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে।
ভৌগোলিকভাবে যিহূদা রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করত জুডিয় পর্বতমালার একটি বিশাল অংশ, যার মধ্যে ছিল নাগেভের উত্তরাংশ, শেফেলার অধিকাংশ এলাকা এবং বীরশেবা উপত্যকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রাপ্ত নিদর্শন থেকে অনুমান করা যায়, এই সময়কালে জেরুজালেম একটি নগররাষ্ট্রের মতো গঠন অর্জন করেছিল এবং প্রাসাদ, প্রশাসনিক ভবন ও ধর্মীয় কাঠামোর উপস্থিতি সেখানে রাজনৈতিক পরিপক্বতার ইঙ্গিত দেয়।
যদিও উভয় রাজ্যই হিব্রু জাতির অংশ হিসেবে বিবেচিত হত, তাদের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, ধর্মীয় পার্থক্য ও সংস্কৃতি চর্চার ভিন্নতা বিদ্যমান ছিল। ইস্রায়েল রাজ্যের ধর্মচর্চা তুলনামূলকভাবে বহুদেবতাবাদী প্রবণতা প্রকাশ করত, যেখানে যিহূদা ধীরে ধীরে একেশ্বরবাদ বা ইয়াহওয়াহ পূজাকে প্রধান ধর্মীয় আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। পরবর্তী সময়ে এই একেশ্বরবাদী ধর্মীয় ধারা ইহুদী ধর্মের ভিত্তি রচনা করে এবং জেরুজালেমের মন্দির তার কেন্দ্রে পরিণত হয়।
এই পর্বে রাজনৈতিক বিভাজনের মধ্যেও ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর চলমান ছিল, যা ইসরায়েল ও যিহূদার ভবিষ্যৎ ইতিহাস, নির্বাসন এবং ধর্মীয় ঐতিহ্যের বিকাশে গভীর ছাপ রেখে যায়।
আসিরীয় আক্রমণ
আধুনিক ইসরায়েলের ভূখণ্ড ও প্রাচীন লেভান্ট অঞ্চলের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় আসে খ্রিস্টপূর্ব ৮ম শতকে, যখন শক্তিশালী আসিরীয় সাম্রাজ্য ইসরায়েলীয় রাজ্যগুলির উপর দখল প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে। ফারাত ও টাইগ্রিস নদী উপত্যকা থেকে উত্থান ঘটানো আসিরীয় সাম্রাজ্য ধাপে ধাপে তার সামরিক শক্তি ও প্রশাসনিক পরিকাঠামো দিয়ে প্রাচীন লেভান্ট অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করে। এই ধারার এক চূড়ান্ত পরিণতি দেখা যায় খ্রিস্টপূর্ব ৭৩২ সালে, যখন আসিরীয় রাজা তৃতীয় তিগলাথ পাইলেসার ইসরায়েলীয় রাজ্যের উত্তরাংশে প্রবেশ করে ব্যাপক দমন অভিযানে নেতৃত্ব দেন। সামারিয়া শহরসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল তারা কব্জা করে নেয়।
তবে সামারিয়ার পতনের ঘটনাটি ঘটে প্রায় এক দশক পরে, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৭২০-৭২১ সালের দিকে। আসিরীয় বর্ণনার ভিত্তিতে ধারণা করা হয়, দ্বিতীয় সারগন সেই সময় সামারিয়া দখল করেন এবং প্রায় ২৭ হাজার অধিবাসীকে বন্দী করে মেসোপটেমিয়ার বিভিন্ন অংশে নির্বাসনে পাঠান। এই জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি ও পুনর্বাসন নীতি ছিল আসিরীয় শাসকদের একটি চিহ্নিত রণনীতি—উদ্দেশ্য ছিল দখলকৃত অঞ্চলগুলিতে স্থানীয় জনসংখ্যার সাংস্কৃতিক-জাতিগত কাঠামো ভেঙে দেওয়া এবং প্রশাসনিকভাবে আনুগত্যশীল এক নতুন সমাজ গঠন করা।
হিব্রু বাইবেলের বিবরণ কিছুটা ভিন্নরকম। সেখানে বলা হয়েছে, সালমানাসার নামক এক রাজা এই আক্রমণ ও পতনের মূল নেতৃত্বে ছিলেন, যদিও বাইবেল ও আসিরীয় নথির মধ্যেকার এই পার্থক্য নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। যাহোক, এইসব বিবরণ এবং এর সঙ্গে যুক্ত জনশ্রুতি ও ধর্মীয় বিশ্বাস মিলে ‘নিখোঁজ দশ গোত্র’ ধারণার জন্ম দেয়—যা পরবর্তীতে ইহুদি, খ্রিস্টান ও কিছু ইসলামি পরম্পরার মধ্যে এক ধরনের ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় কল্পনাকেই উদ্বুদ্ধ করে।
এই নির্বাসনের ফলে শমরিয়ার স্থানীয় বাসিন্দাদের একটি অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও, শমরীয়রা (Samaritans) বিশ্বাস করে, তারা সেই প্রাচীন ইসরায়েলীয় জনগোষ্ঠীরই উত্তরসূরি যারা নির্বাসনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল এবং মূল শহরে থেকেই গিয়েছিল। পরবর্তী কালে শমরীয়দের ধর্মীয় ঐতিহ্য ও হিব্রু বাইবেলের একটি বিকল্প সংস্করণ তাদের পরিচয়কে স্বতন্ত্র রূপ দেয়।
ইসরায়েল রাজ্যের পতনের পর দক্ষিণের যিহূদা রাজ্যে শরণার্থীদের আগমন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এই প্রবাহের ফলে জেরুজালেম ও তার পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, শহর সম্প্রসারিত হয় এবং বসবাসের জন্য নতুন পরিকাঠামোর প্রয়োজন দেখা দেয়। একমাত্র সুরক্ষিত ও দীর্ঘস্থায়ী জলের উৎস নিশ্চিত করতে তৎকালীন যিহূদা রাজা হেজিকিয়াহ খনন করান বিখ্যাত সিলোম টানেল। বাইবেলেও এই টানেলের উল্লেখ আছে এবং ১৮৮০ সালে আবিষ্কৃত একটি অভিলিখনে এই টানেল নির্মাণের বিবরণ হিব্রু লিপিতে উৎকীর্ণ রয়েছে। এই ফলকটিই ইতিহাসে প্রথম দীর্ঘ হিব্রু গদ্যলিপি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বর্তমানে এটি ইস্তাম্বুলের প্রত্নতত্ত্ব জাদুঘরে সংরক্ষিত।
হেজিকিয়ার রাজত্বে সাময়িক স্থিতি এলেও আসিরীয় হুমকি থেমে থাকেনি। সারগনের পুত্র সেনাচেরিব নতুন করে যিহূদা আক্রমণ করেন এবং দাবি করেন যে, তিনি ৪৬টি দুর্গবেষ্টিত শহর ধ্বংস করেছেন। যদিও জেরুজালেম অবরুদ্ধ হয়, তবে ঐতিহাসিকভাবে এটি দখল করা সম্ভব হয়নি। অনেকে মনে করেন যে উপঢৌকন ও কূটনৈতিক কৌশলে জেরুজালেমকে রক্ষা করা হয়েছিল। সেনাচেরিব তাঁর রাজধানী নিনেভেতে জয়ের স্মারক হিসেবে ল্যাচিশ শহরে বিজয় উৎকীর্ণ করান, যার নিদর্শন আজও পাওয়া যায়।
এই রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই ধর্মীয় ও সামাজিক ভাবনা জোরদার হতে থাকে। এই সময় চারজন গুরুত্বপূর্ণ নবীর আবির্ভাব হয়—যাদের মধ্যে হোসেয়া ও আমোস ইসরায়েল অঞ্চলে এবং ইসাইয়া ও মিকাহ যিহূদাতে সক্রিয় ছিলেন। এঁরা শুধুমাত্র ধর্মীয় প্রচারক ছিলেন না, বরং তাঁদের বক্তব্যে রাজনৈতিক সমালোচনা, নৈতিক চেতনার জোরালো আহ্বান এবং সমসাময়িক দুর্নীতির বিরুদ্ধচারণ ছিল স্পষ্ট। তাদের বার্তা ছিল স্পষ্ট—জনগণের অসদাচরণ ও ধর্মচ্যুতি ঈশ্বরের ক্রোধ আহ্বান করছে, এবং শত্রুদের হাতে পতন তারই প্রতিক্রিয়া। এই বার্তাগুলি শুধু ধর্মীয় সাহিত্য নয়, বরং প্রাচীন ইসরায়েলীয় সমাজে নৈতিক আত্মসমালোচনার একটি সাংস্কৃতিক রূপও গঠন করেছিল।
পরবর্তী কালে, জোসিয়া নামক এক তরুণ রাজা যিহূদার ক্ষমতায় আসেন। খ্রিস্টপূর্ব ৭ম শতকের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর রাজত্বকালে জেরুজালেমের মন্দিরে আবিষ্কৃত হয় একটি ধর্মীয় পুস্তক, যা ‘দ্বিতীয় বিবরণী’ (Deuteronomy) নামে পরিচিত। কেউ কেউ মনে করেন এটি ছিল পূর্ববর্তী সময়ের কোন গ্রন্থের পুনরাবিষ্কার; আবার অনেক গবেষক মনে করেন, জোসিয়ার শাসনামলে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে নতুন ধর্মীয় সংস্কারের অংশ হিসেবে। এই বইয়ের মূল বার্তা ছিল একেশ্বরবাদ, কেন্দ্রীভূত উপাসনা এবং নৈতিকতার প্রতি আনুগত্য। জোসিয়ার উদ্যোগে একধরনের ধর্মীয় পুনর্জাগরণ সূচিত হয় এবং তাঁর শাসনকালকেই প্রায়শই হিব্রু বাইবেলের সংস্কারমূলক যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
এই ধর্মীয় পটভূমিতেই গঠিত হয় হিব্রু বাইবেলের কিছু প্রাথমিক অংশ, যেখানে ইতিহাস, ধর্ম, নৈতিকতা এবং জাতীয় পরিচয় মিলেমিশে যায়। দ্বিতীয় বিবরণীর ধাঁচে রচিত গল্পসমূহ যেমন যশুয়া, বিচারক, স্যামুয়েল ইত্যাদি বইতে আমরা দেখতে পাই ইসরায়েলীয়দের ঐতিহাসিক যাত্রার মধ্যে দিয়ে এক জাতি-রাষ্ট্র নির্মাণ ও তার ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হচ্ছে।
এই সময়ের ধর্মীয় ভাবনায় একমাত্র ঈশ্বর ইয়াহওয়েহর পূজা, ইসরায়েলীয়দের অনন্য পরিচয়, এবং ‘নির্বাচিত জাতি’ হিসেবে আত্মবোধ ধীরে ধীরে এক গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাসে রূপান্তরিত হতে থাকে। আসিরীয় সাম্রাজ্যের অধোগতি এবং নবউদিত ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের উত্থান এই ধর্মীয় ও রাজনৈতিক রূপান্তরকে আরেক দিক থেকে ত্বরান্বিত করে। ইতিহাসের পরবর্তী পর্বে আমরা দেখব কিভাবে ব্যাবিলনীয়রা যিহূদা দখল করে, জেরুজালেম ধ্বংস করে এবং ইহুদিদের বন্দীত্বের মাধ্যমে ‘বাবিলীয় নির্বাসন’ সূচিত করে। কিন্তু তার আগেই, জোসিয়ার শাসন এবং ধর্মীয় সংস্কার ছিল এক অন্তর্বর্তী অধ্যায়—যেখানে জাতীয় পুনরুদ্ধার এবং ধর্মীয় আত্মনির্মাণের প্রচেষ্টা একসাথে গাঁথা হয়ে যায়।
ব্যবিলনীয় সময়কাল (৫৮৭-৫৩৮ খ্রিষ্টপূর্ব)
খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শুরুটা ছিল প্রাচীন যিহূদা রাজ্যের জন্য গভীর রাজনৈতিক সংকট, পরাধীনতা ও চরম রূপান্তরের এক সন্ধিক্ষণ। ৬৩০ থেকে ৬০১ খ্রিষ্টপূর্বের মধ্যবর্তী সময়ে যিহূদা, একদিকে নব্য-আসিরীয় সাম্রাজ্যের পতনের ফলে শূন্যতা, অন্যদিকে মিশর ও নবউদীয়মান নব্য ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝখানে পড়ে ক্রমে একটি উপনিবেশিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এই সময়ে যিহূদা রাজ্যের শাসকরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে কখনও মিশরের সাথে, আবার কখনও ব্যাবিলনের সঙ্গে মিত্রতা গড়ে তুলতে থাকে।
৬০১ খ্রিষ্টপূর্বে যিহূদার রাজা জেহোইয়াকিম এক কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেন—তিনি ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মিশরের সঙ্গে জোট বাঁধেন। এই সিদ্ধান্ত প্রাচীন ইসরায়েলি সমাজে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। যিহূদার এক প্রখ্যাত নবী, জেরেমিয়াহ, এই জোটকে আত্মঘাতী এবং ঈশ্বরবিরুদ্ধ বলে তীব্র আপত্তি জানান। তাঁর মতে, যিহূদার শত্রুদের বিরুদ্ধে ঈশ্বর নিজেই প্রতিশোধ নেবেন, কোনো বিদেশি সামরিক জোটে ভরসা করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু রাজা নবীর সতর্কবাণী উপেক্ষা করেন এবং এর ফলস্বরূপ যিহূদার ভাগ্য অনিবার্যভাবে এক চরম বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যায়।
জেহোইয়াকিমের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জেহোইয়াচিন সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু এর অল্প কিছুদিন পরেই, ৫৯৭ খ্রিষ্টপূর্বে, ব্যাবিলনীয়রা যিহূদা রাজ্যের রাজধানী জেরুজালেম ঘিরে ফেলে এবং শহরটি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। নেবুচান্দেজার নেতৃত্বাধীন ব্যাবিলনীয় বাহিনী রাজপরিবার, বিশিষ্ট বংশীয় অভিজাত, পুরোহিত, কারিগর ও সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বন্দী করে ব্যাবিলনে নিয়ে যায়। এই ঘটনাকে বাইবেলীয় ইতিহাসে প্রথম বন্দীত্ব (First Deportation) বলা হয়। সমকালীন ব্যাবিলনীয় দলিলপত্র এবং মাটির ফলকে উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায় যে এই অভিযান এবং বন্দিত্ব ছিল পরিকল্পিত ও প্রণালীবদ্ধ।
এরপর নেবুচান্দেজার জেহোইয়াচিনের চাচা জেদেকিয়াহকে পুতুল রাজা হিসেবে যিহূদার সিংহাসনে বসান। যদিও তিনি বাইরের দৃষ্টিতে ব্যাবিলনের আনুগত্য বজায় রাখছিলেন, অন্তরে অন্তরে তিনি একটি স্বাধীন যিহূদা রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতেন এবং বিদেশি শক্তির প্রভাব থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন। এই আবেগ থেকেই কিছু বছর পর তিনি ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, যার পরিণতি আবারও হয় বিপর্যয়কর।
৫৮৭ বা ৫৮৬ খ্রিষ্টপূর্বে নেবুচান্দেজার জেরুজালেম দখল করেন। এই সময় প্রথম মন্দির—যেটিকে ইহুদি ধর্ম ও জাতিসত্তার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করা হত—সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। শহরের প্রতিরক্ষা প্রাচীর ভেঙে ফেলা হয়, রাজপ্রাসাদ ও গৃহস্থালি ধ্বংস করে পুরো নগরীকে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এটি ছিল এক সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও জাতীয় দুর্যোগ। যিহূদা রাজ্যকে ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত করে নাম দেওয়া হয় ইয়েহুদ। তার প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপন করা হয় মিযপাহ নামক একটি শহরে, যা ধ্বংসপ্রাপ্ত জেরুজালেমের উত্তরে অবস্থিত।
এই বন্দিত্বকালীন সময়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ পাওয়া যায় ব্যাবিলন শহরের ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধারকৃত দলিল বা কাদামাটির ট্যাবলেট থেকে, যেগুলোতে রাজা জেহোইয়াচিন ও তাঁর সঙ্গীদের খাবার, বাসস্থান ও রেশন ব্যবস্থার বিবরণ রয়েছে। এই দলিলগুলি থেকে জানা যায়, বন্দী হলেও জেহোইয়াচিন ও তাঁর পরিবার ব্যাবিলনে একটি সম্মানজনক অবস্থান পেয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে তাকে কারামুক্তও করা হয়।
এই সময়ে গঠিত হয় “রস গালুত” বা “নির্বাসিতদের নেতা” পদবীধারী এক ধারাবাহিক বংশ, যারা ধর্মীয় নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হয়ে ইহুদি জাতিকে নির্বাসনে ঐক্যবদ্ধ রাখার চেষ্টা করেন। ঐতিহাসিক ও তালমুদীয় সূত্র অনুযায়ী, এই বংশটি পরবর্তী ১৫০০ বছর ধরে আধুনিক ইরাকের ভূখণ্ডে ইহুদি সমাজের নেতৃত্ব দিয়ে যায়। একাদশ শতকে এই ধারার সমাপ্তি ঘটে, তবে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ থেকে যায়।
এই সময়ে যিহূদা জাতির অভ্যন্তরে এক গভীর নৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পুনর্গঠন শুরু হয়। হিব্রু বাইবেলের বিভিন্ন গ্রন্থ এই সময়েই সম্পাদিত ও সংগৃহীত হয় বলে অনেক পণ্ডিত বিশ্বাস করেন। বিশেষত, দ্বিতীয় বিবরণী এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক বইগুলির মাধ্যমে একেশ্বরবাদ, জাতীয়তা ও নৈতিকতার এক নতুন ভিত্তি রচিত হয়, যা পরবর্তীতে ইহুদি ধর্মের ভিত্তিস্বরূপে স্থায়ী রূপ পায়। নির্বাসনকালে যে আঘাত জাতি হিসেবে যিহূদীদের উপর নেমে আসে, সেটাই এক অদ্ভুতভাবে তাদের আত্মপরিচয়ের গভীরে অনুপ্রবেশ করে এবং একটি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া কিন্তু ধর্ম ও সংস্কৃতিতে সংহত জাতিসত্তা গঠনে ভূমিকা রাখে।
এই পর্বটিকে কেবল একটি পরাজয়ের ইতিহাস হিসেবে দেখা ভুল হবে। বরং, এটি ছিল আত্মসমীক্ষা, সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন এবং ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতির বীজ বপনের একটি যুগ। এই সংকটকালেই জন্ম নেয় নতুনধারার নবী-কথা, যেগুলি রাজনৈতিক বিদ্রোহ নয়, বরং নৈতিক ও ধর্মীয় জাগরণের আহ্বান জানাত। এবং সেই আহ্বানই পরবর্তী শতকে ইহুদিদের আবার সংগঠিত হতে, ফিরে আসতে এবং তাদের জাতীয় অস্তিত্বকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে সাহায্য করে।
পারস্যের সময়কাল (৫৩৮-৩৩২ খ্রিষ্টপূর্ব)
৫৩৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবদলের মুহূর্তে পারস্যের হাখমানেশী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কুরুশ মহান ব্যাবিলন বিজয় করেন। এই বিজয় কেবল সাম্রাজ্য বিস্তারের ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং মানব ইতিহাসে ধর্মীয় সহনশীলতা ও নির্বাসিত জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষার একটি যুগান্তকারী দৃষ্টান্তও স্থাপন করে। ব্যাবিলনের দরজা খুলে যাওয়ার সাথে সাথেই কুরুশ একটি বিখ্যাত ঘোষণা জারি করেন, যা আজ “সাইরাস সিলিন্ডার” নামে খ্যাত। এই ঘোষণায় কুরুশ ঘোষণা দেন যে, ব্যাবিলনে বন্দিত্বে থাকা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং তারা তাদের নিজ নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে গিয়ে নিজেরা নিজেদের ধর্মীয় রীতি অনুসরণে স্বাধীন থাকবে। ইহুদীদের ক্ষেত্রেও এই নীতিরই বাস্তবায়ন ঘটে।
হিব্রু বাইবেলের বিবরণ অনুসারে, এই সময়ে ব্যাবিলনে নির্বাসিত প্রায় পঞ্চাশ হাজার ইহুদী, জেরুবাবেলের নেতৃত্বে ফেরত আসেন যিহুদার ভূমিতে। এই প্রত্যাবর্তনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল জেরুজালেমে একটি নতুন মন্দির গঠন করা—যেটিকে পরবর্তীকালে “দ্বিতীয় মন্দির” বলা হয়। দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও প্রচেষ্টার পর খ্রিষ্টপূর্ব ৫১৫ সালে এই মন্দিরের নির্মাণ সম্পন্ন হয়। এই মন্দির ছিল প্রাচীন ইহুদী জাতির আত্মপরিচয়, ধর্মীয় সংস্কৃতি ও আচারবিধির একটি প্রতীক।
পরবর্তীতে খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫৬ সালে ইষ্রা ও নেহেমিয়ার নেতৃত্বে আরও প্রায় পাঁচ হাজার ইহুদীর একটি দল যিহুদায় ফিরে আসে। এই সময় পারস্য সম্রাট ইষ্রাকে ধর্মীয় অনুশাসনের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করেন এবং নেহেমিয়ার হাতে প্রশাসনিক কার্যভার অর্পণ করেন। তাঁদের নেতৃত্বে জেরুজালেম শহরের পরিত্যক্ত ও ভাঙা প্রতিরক্ষা প্রাচীরগুলো পুনরায় নির্মাণ করা শুরু হয়। এই নির্মাণ কাজ রাজনৈতিক প্রতিরোধের মুখোমুখি হলেও, ধর্মীয় আবেগ ও জাতীয় ঐক্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ইহুদীরা আবারও নিজেদের শহরকে পুনর্গঠনে সক্ষম হন।
হাখমানেশী শাসনামলে যিহুদা পারস্য সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যার নাম ছিল ‘ইয়েহুদ’। এই সময়ে একটি প্রশাসনিক কাঠামো গঠিত হয় যার শীর্ষে থাকতেন পারস্য নিযুক্ত গভর্নর, যিনি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে থাকতেন এবং পারস্যের আইন অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। তবে ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃত্ব ছিল প্রধান পুরোহিতের হাতে। এই দ্বৈত শাসনব্যবস্থায় ধর্ম ও প্রশাসন দুটি আলাদা কিন্তু পরস্পর-সম্পৃক্ত স্তম্ভ হিসেবে কাজ করত। বেশিরভাগ সময় এই প্রশাসনিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব ইহুদীদের হাতেই থাকত, ফলে পারস্যের অধীন থেকেও ইহুদীরা নিজেদের জাতীয় পরিচয় ও ধর্মীয় সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল।
এই সময়কালেই অনুমান করা হয় যে, তোরাহ—অর্থাৎ হিব্রু বাইবেলের প্রথম পাঁচটি গ্রন্থ—চূড়ান্তভাবে সংকলিত এবং সম্পাদিত হয়। এই সংকলন সম্ভবত খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০ থেকে ৩৫০ সালের মধ্যে সম্পন্ন হয় এবং এর ভাষা হিসেবে আরামীয় বর্ণমালার ব্যবহার শুরু হয়, যাকে ‘আসুরী লিপি’ বলা হয়। ইহুদীরা এই লিপির ধারণা ব্যাবিলনীয় নির্বাসনের সময় অর্জন করে এবং ধীরে ধীরে ক্যানানীয় লিপির ব্যবহার বিলুপ্ত হয়ে যায়। আধুনিক হিব্রু লিপি আসলে এই আরামীয় লিপিরই একটি বিবর্তিত রূপ। এছাড়াও, হিব্রু বর্ষপঞ্জি ও ধর্মীয় রীতি-নীতি ব্যাবিলনীয় সংস্কৃতির প্রভাব বহন করে, যা এই দুই সংস্কৃতির পারস্পরিক সংযোগের প্রমাণ বহন করে।
এই সময়েই একটি বিশিষ্ট সামাজিক টানাপোড়েন দেখা যায়। একদিকে ছিল ব্যাবিলন থেকে ফিরে আসা অভিজাত ইহুদীরা, যারা পারস্যের শাসকের আনুকূল্য লাভ করেছিল, এবং অন্যদিকে ছিল স্থানীয়ভাবে বসবাসরত সাধারণ মানুষজন, যারা পূর্ব থেকেই যিহুদার ভূমিতে বসবাস করে আসছিল। এই স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকেই আশঙ্কা করত যে, ফিরে আসা অভিজাতরা তাঁদের জমি ও সামাজিক প্রাধান্য কেড়ে নেবে। এই বিরোধ কখনো কখনো মন্দির নির্মাণের কাজে প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করেছিল। বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে এ বিরোধের চিত্র স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।
পারস্য শাসনের অধীনে যিহুদার সমাজে একটি বৈশিষ্ট্যমূলক ধর্মরাষ্ট্র কাঠামো গড়ে ওঠে। ধর্মীয় নেতৃত্ব প্রধান পুরোহিতের হাতে কেন্দ্রীভূত হয় এবং ধর্মীয় আইনই হয়ে ওঠে সমাজের নৈতিক ও সামাজিক নির্দেশিকা। প্রশাসনিকভাবে যদিও পারস্যের আইন মেনে চলতে হত, তবুও অনেক সময়ই স্থানীয় ধর্মীয় বিধিবিধানই মানুষের জীবনচর্চায় প্রধান হয়ে ওঠে। এই সময়ে পুরোহিত বংশধরদের মধ্যে সমাজে এক ধরনের শ্রেণিবিভাজন দেখা দেয়, যা ভবিষ্যতের ধর্মীয় রাজনীতির সূচনা করে।
পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনস্থ অন্যান্য অঞ্চলের মতো, যিহুদাও সাম্রাজ্যিক পরিকাঠামোর অংশে পরিণত হয়। পারস্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ইহুদী সম্প্রদায়ের ছড়িয়ে পড়ার কারণে পারস্য শাসকেরা ইহুদীদের সামরিক ও প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত রাখে। এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে, মিশরের আসওয়ান অঞ্চলে এলিফেন্টাইন দ্বীপে বসবাসরত ইহুদী সৈন্যদল। পারস্য সরকার সেখানে একটি ইহুদী গার্ড রেজিমেন্ট গঠন করেছিল, যারা এলিফেন্টাইন দুর্গের রক্ষী হিসেবে কাজ করত। এই সম্প্রদায়ের বহু প্রশাসনিক ও ধর্মীয় দলিলপত্র প্যাপিরাসে লেখা হত। ২০ শতকের শুরুতে আবিষ্কৃত ১৭৫টি এলিফেন্টাইন প্যাপিরাস দলিল থেকে জানা যায়, এই ইহুদীরা পাসওভারের মতো ধর্মীয় উৎসব পালন করত এবং পারস্যের প্রশাসনিক নিয়মকানুন মেনে চলার পাশাপাশি নিজেদের ধর্মীয় রীতিও পালন করত। প্যাপিরাসগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য দলিল, “পাসওভার প্যাপিরাস”, যেখানে ঈশ্বরের সম্মানে উৎসব পালনের জন্য সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। এই দলিলগুলো ইতিহাসবিদদের কাছে এক অনন্য দলিল হিসেবে বিবেচিত, কারণ এর মাধ্যমে পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে ইহুদী ধর্মীয় সংস্কৃতি, অভিব্যক্তি ও রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়।
এই সমগ্র সময়কাল, যেটিকে প্রায়শই “দ্বিতীয় মন্দির যুগের সূচনা” বলা হয়, ইহুদী ধর্মীয় চিন্তাধারা, জাতীয় পরিচয় এবং সমাজ কাঠামোর দিক থেকে গভীর রূপান্তরের সময়কাল হিসেবে বিবেচিত হয়। এ সময়েই ইহুদী ধর্ম একাধারে ঐতিহ্য ও আধুনিক বাস্তবতার সম্মিলনে একটি টেকসই সাংস্কৃতিক কাঠামো নির্মাণ করতে সক্ষম হয়, যার প্রভাব পরবর্তীতে খ্রিষ্টীয় যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।
হেলেনীয় সময়কাল (৩৩৩-৬৪ খ্রিষ্টপূর্ব)
খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষভাগে পারস্য সাম্রাজ্য যখন একের পর এক আঘাতে ক্ষতবিক্ষত, তখন ম্যাসিডোনিয়ার তরুণ সম্রাট আলেক্সান্ডার মহান ইতিহাসের মঞ্চে প্রবেশ করেন। ৩৩২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে পারস্যের ওপর তার দুর্ধর্ষ আক্রমণের সময় যিহূদার ভূমিও তার নিয়ন্ত্রণে আসে। এই অঞ্চলের ভাগ্য এরপর দীর্ঘ সময়জুড়ে রাজ্যাভ্যন্তর ও সাম্রাজ্যিক রাজনীতির নানা ঢেউয়ে ভেসে বেড়ায়। আলেক্সান্ডারের অকাল মৃত্যুর পর তার বিশাল সাম্রাজ্য সেনাপতিদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ যিহূদা একপ্রকার সীমান্তবর্তী অঞ্চল হয়ে পড়ে সেলেউসিড সাম্রাজ্য ও মিশরের টলেমীয় রাজ্যের মাঝে। শুরু হয় এক দীর্ঘ অস্থির সময়ের যাত্রা।

প্রথমে যিহূদা টলেমীয় শাসনের অধীনে আসে। এই শাসকেরা সাধারণত ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ইহুদী প্রতিষ্ঠানের প্রতি সহনশীল মনোভাব বজায় রাখে। কিন্তু খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ সালে পানিয়াম যুদ্ধে টলেমীয়দের পরাজয়ের পর যিহূদা সেলেউসিড শাসনের অধীন আসে। এই নতুন শাসনামলেও প্রাথমিকভাবে ধর্মীয় ও সামাজিক স্বাধীনতা বজায় থাকে। ইসরায়েলের প্রধান পুরোহিত, যিনি বংশানুক্রমে নিযুক্ত হতেন, রাজ্যের প্রশাসনিক ও ধর্মীয় নেতৃত্ব বহন করতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে হেলেনীয় সংস্কৃতির ছায়া পড়ে ইহুদীদের উপর। গ্রিক ভাষা, পোশাক, ক্রীড়া ও জীবনচর্চা ইহুদী সমাজে অনুপ্রবেশ করতে থাকে, যা একদিকে কিছু প্রগতিশীল ইহুদী যুবকদের আকৃষ্ট করে, অন্যদিকে ধর্মীয় রক্ষণশীলদের উদ্বিগ্ন করে তোলে। এভাবেই শুরু হয় অভ্যন্তরীণ সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব—যেখানে একদিকে ছিল হেলেনীয়তা গ্রহণকারী দল এবং অন্যদিকে কট্টর ইহুদী সম্প্রদায়।
এই দ্বন্দ্ব আরও ঘনীভূত হয় যখন সেলেউসিড সম্রাট চতুর্থ এন্টিওকাস এপিফানেস যিহূদার ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিসর সংকুচিত করে তোলেন। তিনি জেরুজালেমের মন্দিরকে গ্রিক দেবতা জিউসের পূজার স্থান হিসেবে ব্যবহার করার আদেশ দেন। ইহুদীদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করা হয়, এমনকি শিশুদের খৎনা, কাশরুৎ রীতি বা শব্বত পালনের মত ধর্মীয় রীতিও অপরাধ গণ্য হতে থাকে। এই নিষেধাজ্ঞা ও জুলুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনা ঘটে খ্রিষ্টপূর্ব ১৬৭ সালে মোদিন শহরে। সেখানকার এক ইহুদী ধর্মযাজক ম্যাথিয়াস সেলেউসিড কর্মকর্তা এবং একজন হেলেনীয় অনুগত ইহুদী পুরোহিতকে হত্যা করেন, যা ছিল বিদ্রোহের আগুনে প্রথম স্ফুলিঙ্গ। এই ঘটনার মধ্য দিয়েই সূচনা হয় “মাকাবীয় বিদ্রোহ”—একটি ধর্ম ও জাতীয় স্বাধীনতার জন্য লড়াই।
বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ম্যাথিয়াসের পুত্র, জুদা মাকাবী। তিনি সেলেউসিড সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে একাধিক সফল অভিযান পরিচালনা করেন এবং শেষ পর্যন্ত খ্রিষ্টপূর্ব ১৬৪ সালে জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। তিনি দ্বিতীয় মন্দিরে ইহুদী ধর্মীয় প্রথার পুনঃপ্রবর্তন করেন এবং মন্দিরকে শুদ্ধ করে তোলেন। এই ঘটনাকে স্মরণ করেই আজও ইহুদীরা “হানুক্কাহ” নামে একটি আলোকোৎসব পালন করে থাকে, যা মন্দিরের প্রদীপে অলৌকিকভাবে আটদিন ধরে তেলের জ্বলে থাকার স্মৃতি বহন করে।
পরবর্তী কয়েক দশকে জুদা মাকাবীর ভাইরা—জোনাথান ও সাইমন—হাসমোনীয় রাজবংশের ভিত্তি স্থাপন করেন। যদিও এই রাজ্য শুরুতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল না, তবে সেলেউসিড সাম্রাজ্যের অব্যাহত দুর্বলতা, পার্থিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ, ও রোমান প্রজাতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে হাসমোনীয়রা নিজেদের আধিপত্যকে ক্রমে শক্তিশালী করে তোলে। জন হাইরক্যানাস, সাইমনের পুত্র, এই বংশের অন্যতম ক্ষমতাধর নেতা ছিলেন। তিনি শুধু যিহূদার স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন না, বরং রাজ্যের আয়তন দ্বিগুণ করে ফেলেন। তিনি ইদোম, স্কাইথোপোলিস, ও শমরিয়ার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং শমরীয়দের ধর্মীয় কেন্দ্রীয় মন্দির ধ্বংস করেন। ইদোমীয়দের ইহুদী ধর্মে দীক্ষিত করা ছিল হাসমোনীয় রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা ইহুদী জাতীয়তাবাদের একটি রূপ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়।
জন হাইরক্যানাস প্রথম হাসমোনীয় নেতা যিনি নিজস্ব মুদ্রা চালু করেন, যা তার রাজনৈতিক স্বকীয়তা ও আর্থিক স্বাধীনতার প্রতীক ছিল। পরবর্তীকালে তাঁর পুত্ররা—প্রথম আরিস্টোবুলাস ও আলেক্সান্ডার জানিয়াস—রাজ্যকে একাধিক দিকে সম্প্রসারিত করেন এবং ইহুদাকে একটি পূর্ণাঙ্গ রাজ্যে পরিণত করেন। এই সময়ে রাজ্য বিস্তৃত হয় উপকূলীয় অঞ্চল, গালীল এবং ট্রান্সজর্দানের কিছু অংশজুড়ে। এই সময়কালেই ধর্ম, রাজনীতি এবং সামাজিক জীবনের ভেতর গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।
হাসমোনীয় শাসনের সময় ইহুদী সমাজে নানা সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের সূচনা ঘটে। ফারিসি, সাদুসি এবং এসিন নামক তিনটি প্রধান ধর্মীয় আন্দোলনের উদ্ভব হয়। ফারিসিরা ছিলেন ধর্মীয় আইন ও মৌখিক ঐতিহ্যের অনুগামী; তাঁরা সাধারন মানুষের সাথে ধর্মীয় চর্চার সংযোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। সেমিয়ন বেন শিটাচ-এর নেতৃত্বে ফারিসিরা সিনাগগ ও ধর্মশিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলেন, যা পরবর্তীকালে রাব্বানিক ইহুদীবাদের ভিত্তি গঠন করে। সাদুসিরা মূলত পুরোহিত সম্প্রদায় ও উচ্চবিত্ত গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করত এবং শুধুমাত্র লিখিত তোরাহকে গ্রহণ করত। আর এসিন গোষ্ঠী ছিল এক রহস্যময়, অন্তর্মুখী গোষ্ঠী, যাদের নিয়ে পরবর্তীকালে কুমরান নথিপত্রের (Dead Sea Scrolls) সূত্রে আরও বিশদ গবেষণা হয়।
হাসমোনীয় রাজবংশের অন্তিম পর্বে এসে আবারও জাতীয় ঐক্যে চিড় ধরে। আলেক্সান্ডার জানিয়াসের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী রাণী সালোম আলেক্সান্দ্রা কিছুদিন শাসন করেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে দুই পুত্র—দ্বিতীয় হাইরক্যানাস ও দ্বিতীয় আরিস্টোবুলাস—সিংহাসন দখলের জন্য সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। এই গৃহযুদ্ধে উভয় পক্ষই রোমান জেনারেল পম্পির সাহায্য কামনা করে, ফলে একপ্রকার রোমানদের সামনে দরজা খুলে যায়। পম্পে নিজে জেরুজালেমে প্রবেশ করে মন্দির চত্বরে উপস্থিত হন এবং কার্যত হাসমোনীয় রাজবংশের উপর রোমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।
এইভাবে এক শক্তিশালী, আত্মনির্ভরশীল ইহুদী রাজ্য যা ধর্মীয় এবং সামরিক উভয় দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, ধীরে ধীরে নিজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির চাপে আত্মসমর্পণ করে বৃহত্তর সাম্রাজ্যিক শক্তির সামনে। তথাপি, হাসমোনীয় যুগের ধর্মীয় চেতনা, রাজনৈতিক সচেতনতা এবং জাতীয়তাবাদী আবেগ পরবর্তী যুগে ইহুদী ইতিহাসের বহু গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের উৎস হয়ে থাকে।
আদি রোমান যুগ (৬৪ খ্রিষ্টপূর্ব-২য় শতক (খ্রিষ্টাব্দ))
৬৪ খ্রিস্টপূর্বে রোমান প্রজাতন্ত্রের অন্যতম প্রভাবশালী সেনানায়ক এবং রাজনীতিবিদ পম্পে, সিরিয়া জয় করার পরপরই যিহূদিয়ার অভ্যন্তরীণ সংঘাতে হস্তক্ষেপ করেন। হাসমোনীয় গৃহযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে, যেখানে দ্বিতীয় হাইরক্যানাস এবং তার ভাই দ্বিতীয় আরিস্ট্রোবুলাস সিংহাসনের জন্য একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন, পম্পে দ্বিতীয় হাইরক্যানাসের অনুকূলে অবস্থান নেন। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তিনি কেবল হাইরক্যানাসকে প্রধান পুরোহিত হিসেবে পুনঃস্থাপনই করেন না, বরং যিহূদিয়া রাজ্যটিকে রোমান সাম্রাজ্যের অধীন একটি সামন্ত রাজ্যে পরিণত করেন।
এই রাজনীতিক পরিবর্তনের পর, যিহূদিয়ার রাজনীতি ক্রমশ রোমান প্রশাসনের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে। ৪৭ খ্রিষ্টপূর্বে আলেক্সান্দ্রিয়া অবরোধের সময় দ্বিতীয় হাইরক্যানাসের পাঠানো প্রায় তিন হাজার ইহুদি সৈন্য ইডোমীয় বংশোদ্ভূত অ্যান্টিপেটার-এর নেতৃত্বে রোমের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি জুলিয়াস সিজার ও মিশরের রানী ক্লিওপেট্রার জীবন রক্ষা করে। এই কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ জুলিয়াস সিজার অ্যান্টিপেটারের বংশধরদের রোমান সমর্থিত রাজশক্তির মালিক করে তোলে। এই ঘটনার মধ্য দিয়েই ইহুদি রাজনীতিতে ইডোমীয় বংশের প্রবেশ এবং প্রভাবশালী হয়ে ওঠার সূচনা ঘটে।

৩৭ খ্রিষ্টপূর্ব থেকে ৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইডোম বংশীয় হেরোড বংশ, বিশেষত হেরোড দ্য গ্রেট, যিহূদিয়া শাসন করেন। রোমানদের আশীর্বাদপুষ্ট এই রাজা তার নির্মাণকৌশল ও রাজকীয় উচ্চাভিলাষের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। দ্বিতীয় মন্দিরকে পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করে তিনি একে প্রাচীন বিশ্বের অন্যতম বিস্ময়কর ধর্মীয় স্থাপনার রূপ দেন, যা পরে “হেরোডের মন্দির” নামে পরিচিত হয়। এ সময় যিহূদার জনগণ ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললেও, রাজসভার রাজনীতি ও সামাজিক বিভাজন প্রচণ্ড রূপ নিতে থাকে।
হেরোডের রাজত্বে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকলেও তার পরবর্তী প্রজন্মের অযোগ্যতা ও বিভাজন রোমান প্রশাসনকে আরও সক্রিয় করে তোলে। ৬ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আগস্তুস যিহূদীয়াকে সরাসরি রোমান প্রদেশে পরিণত করেন। তখনকার শেষ ইহুদি রাজা হেরড আর্কিলাসকে অপসারণ করে তাঁর জায়গায় একজন রোমান প্রশাসক, অর্থাৎ “প্রোকিউরেটর” নিযুক্ত করা হয়। এর ফলে যিহূদার ওপর সরাসরি রোমান শাসনের সূচনা ঘটে এবং রোমান করব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, যা দ্রুত জনরোষ তৈরি করে।
রোমানদের আরোপিত কর এবং ধর্মীয় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিক্রিয়া আসে “জুদাস অব গালীল” নামক এক ধর্মীয় নেতার নেতৃত্বে। তিনি কর না দেওয়ার ডাক দেন এবং ছোট আকারে সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটিত করেন। যদিও বিদ্রোহ দ্রুত দমন করা হয়, এই ঘটনাটি ইঙ্গিত দেয় যে, রোমান আধিপত্য যিহূদার জনগণের মধ্যে গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল।
এই সময় ইহুদি সমাজ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দিক থেকে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি বড় অংশ ছিল রোমপ্রেমী এবং হেলেনীয় সংস্কৃতিতে আকৃষ্ট, অপরদিকে রক্ষণশীল এবং জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী দিন দিন আরও চরমপন্থী হয়ে ওঠে। ইহুদিদের ভেতরে বিভিন্ন ধর্মীয় দল, যেমন ফারিসী, সাদুসী, এবং এসেনীরা আলাদা আলাদা মতবাদে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এসেনীরা মূলত কিউমরানে বসবাস করে এবং নিজস্ব ধর্মীয় জীবনচর্চার মাধ্যমে একটি ধ্রুপদী ও শুদ্ধ জীবনধারার অনুসারী হয়ে ওঠেন। অন্যদিকে, ফারিসীরা ধর্মীয় আইনকে জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চায় এবং সাদুসীরা মন্দিরের পূজার আচারে কেন্দ্রীভূত থাকেন।
৬৪ খ্রিষ্টাব্দে, দ্বিতীয় মন্দিরের তৎকালীন প্রধান পুরোহিত যসুয়া বেন গ্যামলা একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করেন—তিনি ঘোষণা দেন, প্রত্যেক ইহুদি ছেলেশিশুকে ছয় বছর বয়স থেকে শিক্ষার আওতায় আনতে হবে। এই শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল এবং ধীরে ধীরে ইহুদি সমাজে বিদ্যালয় এবং শিক্ষাব্যবস্থা একটি সাংস্কৃতিক অবলম্বনে পরিণত হয়। পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে এটি রাব্বিনিক ইহুদিবাদের ভিত্তি নির্মাণে অবদান রাখে।
তবে সামাজিক ও ধর্মীয় অস্থিরতা ক্রমাগত বেড়ে চলে। ইহুদিরা অপেক্ষা করতে থাকে এক মহামুক্তিদাতার জন্য, যিনি আসবেন এবং ইসরায়েলকে আবার স্বাধীন ও মহিমান্বিত করবেন। এই মুক্তিদাতাকে বলা হতো “মাসিয়াহ”। তার আগমনের আশায় জনমনে তৈরি হতে থাকে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও প্রতীক্ষা। ধর্মীয় ভবিষ্যদ্বাণী, সাহিত্যে মাসিয়াহের আগমনের পূর্বাভাস প্রতিফলিত হতে শুরু করে। এই প্রেক্ষাপটেই যিশু নাসারেথের মত ব্যক্তিত্ব আবির্ভূত হন, যিনি নিজেকে বা যাঁকে তাঁর অনুসারীরা মাসিয়াহ বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেন।
রোমান কর্তৃপক্ষ এই ধরনের আন্দোলনের বিপজ্জনক সম্ভাবনা দেখে রক্ষার নীতি গ্রহণ করে এবং অনেক ধর্মীয় নেতার উপর নজরদারি চালায়। তবে একবিংশ শতাব্দীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, এই সময়টিকে রাজনৈতিক চাপ, ধর্মীয় দ্বন্দ্ব এবং সামাজিক রূপান্তরের যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ইহুদি সমাজে ধর্মীয় অনুশাসনের অনুশীলন যেমন অব্যাহত ছিল, তেমনই বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভও পুঞ্জীভূত হতে থাকে।
এই সময়েই শুরু হয় এক নতুন যুগের প্রস্তুতি—যেখানে রোমান সাম্রাজ্য ও ইহুদি সমাজের সংঘর্ষ ধীরে ধীরে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়, যা শেষ পর্যন্ত ৭০ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় মন্দির ধ্বংসের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের এক যুগের অবসান ঘটায়।
ইহুদি-রোমান যুদ্ধ
৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ইহুদিয়ার ভূখণ্ডে যে মহাসংঘর্ষের সূচনা হয়েছিল, তাকে শুধু একটি যুদ্ধ বললে যথেষ্ট হয় না—এ ছিল এক বিস্ময়কর সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিপর্যয়ের সূচনা। এই প্রথম ইহুদি-রোমান যুদ্ধ, যা ৬৬ খ্রিষ্টাব্দে শুরু হয়ে ৭৩ খ্রিষ্টাব্দে শেষ হয়, ইহুদি ইতিহাসের গতি ও কাঠামো সম্পূর্ণরূপে বদলে দেয়।
এই যুদ্ধের পেছনে যে অগ্নিসংযোগকারী উপাদানগুলো জমা হচ্ছিল, তা ছিল বহুস্তরীয়। একদিকে রোমান শাসকদের কর নির্যাতন, বৈষম্যমূলক শাসনব্যবস্থা এবং উপনিবেশিক দমননীতি, অপরদিকে ছিল ইহুদি সমাজের অভ্যন্তরীণ বিভাজন, দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা। বিশেষ করে অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট হয়ে উঠেছিল। সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণি রোমান শাসকদের সঙ্গে আঁতাত করে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল, অথচ অধিকাংশ সাধারণ মানুষ চরম দারিদ্র্য আর নিপীড়নের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। এই অসাম্য ইহুদি সমাজে গভীর ক্ষোভ জন্ম দেয়। পাশাপাশি, জেরুজালেমের মতো এক ধর্মীয় শহরে বসবাসরত ইহুদি ও প্যাগানদের মধ্যে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব ক্রমাগত বেড়ে উঠছিল। এই উত্তপ্ত পরিবেশে সামান্য উসকানিই পর্যাপ্ত ছিল বিস্ফোরণের জন্য।
যুদ্ধ শুরু হলে ইহুদিরা রোমানদের বিরুদ্ধে প্রথম দিকে কিছু সাফল্য অর্জন করলেও, শীঘ্রই বিভক্তি ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল তাদের দুর্বল করে তোলে। ঐতিহাসিক যোসেফাস ফ্লাভিয়াসের বর্ণনায় আমরা দেখি, ইহুদি বিদ্রোহীরা নিজেদের মধ্যেই দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল—সিকারি, জিলট, এসেনস, এবং ফারেসিদের মধ্যে মতবিরোধ এবং পরস্পর সন্দেহ এতটাই প্রকট হয়ে ওঠে যে, রোমানদের মোকাবিলার চেয়ে নিজেদের দমন করতেই অধিক সময় ব্যয় হয়। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রোমান সেনাপতি ভেসপাসিয়ান এবং পরবর্তীতে তার পুত্র টাইটাস ধারাবাহিকভাবে একের পর এক ইহুদি দুর্গ, শহর এবং খাদ্যাগার ধ্বংস করে দেন।
৭০ খ্রিষ্টাব্দে টাইটাসের নেতৃত্বে রোমান বাহিনী জেরুজালেম অবরোধ করে এবং পাঁচ মাসের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শেষে শহরটি দখল করে। ধ্বংস করা হয় দ্বিতীয় মন্দির—যা ছিল ইহুদি জাতির ধর্মীয় পরিচয়ের মূল স্তম্ভ। এই ধ্বংস কেবল একটি স্থাপত্যের পতন নয়, বরং একটি ধর্মীয় সাংস্কৃতিক মহাবিপর্যয়। হাজার হাজার ইহুদি নিহত হন, অনেকে বন্দী হন এবং বহু পরিবার দেশান্তরে বাধ্য হন। যুদ্ধের ফলাফল হিসেবে ইহুদি সমাজে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়, তা কেবল জনসংখ্যাগত নয়—এই শূন্যতা ছিল আধ্যাত্মিক ও সাংগঠনিক।
এই ধ্বংসযজ্ঞের সবচেয়ে বড় প্রতীক ছিল দ্বিতীয় মন্দিরের বিলুপ্তি। মন্দির ছিল ইহুদিদের পূজার কেন্দ্রে, তাদের জাতীয় ঐক্য এবং ধর্মীয় জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। মন্দিরধর্মী ফেরকা যেমন সাজুসেইদের অস্তিত্বই নির্ভর করত মন্দিরের অস্তিত্বের উপর। ফলে, মন্দির ধ্বংসের পর তাদের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়। অপরদিকে, ফারেসিরা—যারা তোরাহ ও মৌখিক শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব দিত—তারা সময়ের দাবি মেনে নিজেদের ধর্মীয় চর্চা ও কাঠামো পুনর্গঠনে এগিয়ে আসে। এই পুনর্গঠনের পথপ্রদর্শক হন যোহানান বেন জাক্কাই।
যোহানান রোমান শাসকদের কাছ থেকে ইয়াভনে একটি বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি পান, যা হয়ে ওঠে ইহুদিদের নতুন আধ্যাত্মিক ঘাঁটি। এই প্রতিষ্ঠান রাব্বিনিক ইহুদিবাদের ভিত্তি স্থাপন করে—যেখানে তোরাহ পাঠ, মৌখিক আইন ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা ধর্মচর্চার কেন্দ্রে আসে। এই নতুন কাঠামোই পরবর্তীতে ইহুদিবাদের মূলধারায় রূপান্তরিত হয়।
এই সংঘাতের রেশ রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ১১৫ থেকে ১১৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চলে আরেক দফা বিদ্রোহ, যা ইতিহাসে কিটোস বিদ্রোহ নামে পরিচিত। লিবিয়া, মিশর, সাইপ্রাস এবং মেসোপটেমিয়ার ইহুদিরা রোমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে। কিন্তু এই বিদ্রোহ নিছক সামরিক সংঘর্ষে সীমাবদ্ধ ছিল না—এটি রূপ নেয় জাতিগত সহিংসতা ও নির্বিচার গণহত্যায়। হাজার হাজার মানুষ নিহত হন, বসতি ধ্বংস হয়, এমনকি সাইপ্রাসের মতো এলাকায় ইহুদিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। অনেক জায়গায় ইহুদি অস্তিত্ব মুছে ফেলা হয় এবং নতুন ঔপনিবেশিকরা এনে বসানো হয়।
এই সমস্ত ঘটনাবলি রোমানদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও কঠোর করে তোলে। ইহুদিদের উপর নজরদারি, ধর্মীয় চর্চার উপর নিষেধাজ্ঞা, তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাধা দেওয়া—এসব নীতির মাধ্যমে ইহুদি পরিচয়কে রুদ্ধ করার চেষ্টা চলে। তবুও, এই দমনপীড়নের মধ্য দিয়েই এক নতুন ইহুদি চেতনার জন্ম হয়। রোমানদের অত্যাচার ইহুদিদের মধ্যে একপ্রকার প্রতিরোধমূলক আত্মপরিচয়ের বোধ তৈরি করে। ধর্মীয় বিশ্বাস আরও ঘনীভূত হয় এবং ভবিষ্যতের জন্য এক ‘মেসিয়াহ’ আগমনের প্রত্যাশা সমাজে ক্রমশ প্রবল হয়ে ওঠে। এই প্রত্যাশা থেকেই পরবর্তী যুগে বহু নবী ও নেতার আবির্ভাব ঘটে, যারা সমাজকে নতুন করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখাতেন।
এই দুঃসময়ের মধ্যে রাব্বিনিক ইহুদিবাদ একটি শক্ত ভিত গড়ে তোলে, যা পরে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। তোরাহ-ভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতি, হালাখাহ আইন, এবং সিনাগগ কেন্দ্রিক ধর্মচর্চা ইহুদি সংস্কৃতির মৌলিক উপাদানে রূপ নেয়। মন্দির-নির্ভর ধর্মচর্চা থেকে শিক্ষা ও স্মৃতি নির্ভর ধর্মীয় জীবনে রূপান্তর ঘটে। এই রূপান্তর ইহুদি জাতির অস্তিত্ব রক্ষার এক কৌশলী পথ হিসেবে কাজ করে।
ইতিহাসের এই অধ্যায় শুধু ইহুদিদের জন্য নয়, গোটা মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মানচিত্রকেও প্রভাবিত করে। এই সময় থেকেই এক দীর্ঘ প্রবাস জীবনের যাত্রা শুরু হয়, যা পরবর্তী দুই হাজার বছর ধরে ইহুদিদের পরিচয়, সংগ্রাম ও স্বপ্নকে নির্ধারণ করে দেয়।
প্রাগৈতিহাসিক
ইসরায়েলের লেভান্ট অঞ্চলে মানুষের উপস্থিতি এক কথায় এক বিশাল মানবিক ইতিহাসের সাক্ষী, যা প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু যুগ অতিক্রম করে আধুনিক মানব সভ্যতার ভিত্তি গড়ে তোলে।
এই অঞ্চলের আলোচনামূলক শুরুটা হয় উবেদিয়া থেকে, যেখানে প্রায় পনের লক্ষ (১৫ লাখ) বছর আগের মানুষের অস্তিত্ব প্রমাণ পাওয়া গেছে। তখনকার প্রাগৈতিহাসিক সমাজে মানুষ পাথরের সরঞ্জাম তৈরি করতো এবং সামাজিকভাবে গ্রুপ হয়ে বসবাস করতো—স্বল্প পরিসরের হলেও তারা বাস বাছিয়েছিল একটি নিরাপদ ও উপযোগী প্রাকৃতিক আশ্রয়ে।
প্রায় ১,২০,০০০ বছর আগে বর্তমান স্কুল এবং কফজেহ এলাকার হোমিনিন (মানবীয়) জীবাশ্ম আবিষ্কার মানব বিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় লিখে—এদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য আধুনিক মানুষের মতো বিবর্তিত হলেও, জীবনধারার নিদর্শন দেখায় তারা প্রায় সম্পূর্ণ মানব জাতির আদিভূমিরই উত্তরসূরি।
এরপরে আনুমানিক ১০,০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে নাতুফিয়ান সংস্কৃতি আবির্ভূত হয়, যাকে বৈজ্ঞানিকরা প্রাচীন আফ্রো-এশীয় ভাষা ধারণার সাথে যুক্ত করেন। এরা প্রথম মানুষেরা যিনি শিকার ও সংগ্রহ নির্বাহ করেই ধাপে ধাপে কৃষি সংস্কৃতির দিকে অগ্রসর হন—প্রোটো-অগ্রিকালচারি তালিকাভুক্ত হয় তাঁদের জীবনধারা। স্থায়ী বা আধা-স্থায়ী বসতি স্থাপন, শস্যসংরক্ষণ, পশুপালন এবং সামাজিক রীতি-নীতি গড়ে তোলার সূচনা এই সময় থেকেই ঘটে।
এরপরে খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০০–৪০০০ সাল নাগাদ ঘাসুলিয়ান সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করে, যেখানে মানুষ এখন সরাসরি গৃহায়ণ, কুঠুরি নির্মাণ, কৃষি সম্প্রসারণ ও জমিতে নিয়ন্ত্রিত চাষাবাদ শুরু করে। এখানেই শুরু হয় প্রথম শহরতলী গঠন, যেখানে সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও প্রযুক্তির বিকাশ গতিশীলতা পায়—এই ধাপলাইন পার্রিতির এক দূরদৃষ্টিকোণিক রূপান্তর।
এই প্রবাহ ইতিহাসের ধারায় যে ধারাবাহিকতা তৈরি হয়, তা ইসরায়েলের ভূমিকে শুধু ধর্মীয় বা রাজনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত করে না—যেখান থেকে আধুনিক মানব জাতির নিজস্বতা, সামাজিক যোগসূত্র ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি প্রসারিত হয়। এখানেই আমরা ঐতিহাসিক মানুষের সংগ্রাম, অভিযোজন ও সৃজনশীলতার প্রাথমিক স্পন্দন খুঁজে পাই যা বিশ্বসভ্যতার পরবর্তী বিকাশের ভিত্তি স্থাপন করে।
ব্রোঞ্জ এবং লৌহ যুগ
প্রাচীন লেভান্তের ইতিহাস এক দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের কাহিনি, যার গভীরে নিহিত রয়েছে কানানীয় সভ্যতার উত্থান, ইসরায়েল ও যিহূদার রাজ্য গঠনের পটভূমি এবং ব্রোঞ্জ যুগ থেকে শুরু করে লৌহ যুগ পর্যন্ত এক জটিল ঐতিহাসিক ধারা। এই অঞ্চলটি — যা আধুনিক লেবানন, ইসরায়েল, ফিলিস্তিন, জর্ডান ও সিরিয়ার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত — হাজার হাজার বছর ধরে এক গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতাকেন্দ্র ছিল। এরই ভিতর থেকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে হিব্রু জনগোষ্ঠী এবং পরবর্তীকালে ইহুদি ধর্মীয় ঐতিহ্যের ভিত্তি।
প্রথমেই বলা দরকার, “কানান” ও “কানানাইটস” শব্দ দুটি মূলত বহুবিধ ভাষায় পাওয়া যায় এবং এগুলোর উৎস ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ বা তারও আগে। মিশরীয়, আক্কাদীয়, ওগারিতীয় ও হিত্তি দলিলপত্রে এই নামগুলি নানা প্রেক্ষিতে ব্যবহার হয়েছে। “কানান” বলতে বোঝানো হত একটি ভূগোলিক অঞ্চলকে, যার পরিধি সময় ও রাজনীতির প্রেক্ষিতে বদলে গিয়েছে। এটি কখনো কখনো উপকূলীয় অঞ্চলকেই নির্দেশ করেছে, কখনো বা সমগ্র লেভান্তকেই। এ অঞ্চলটির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল এর নগর-রাষ্ট্রভিত্তিক রাজনৈতিক গঠন। যেমন বাইবেলের বর্ণনায় আমরা দেখি, ইয়েরিখো, হাৎছোর, গেবেল বা বাইব্লোস, মেগিদ্দো ইত্যাদি শক্তিশালী কানানীয় নগর-রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত ছিল।
এই নগর-রাষ্ট্রগুলি কোনো কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শাসনাধীন ছিল না, বরং স্বতন্ত্র শাসক দ্বারা পরিচালিত হত এবং মাঝে মাঝে একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষেও জড়িয়ে পড়ত। এই সময়কার কানানীয় সংস্কৃতি একটি উঁচুমানের লিপি ও সাহিত্য ধারণ করত — বিশেষ করে উগারিত শহর থেকে পাওয়া অগণিত মাটির ফলকে তার নিদর্শন রয়েছে। এই ভাষা সেমিটিক পরিবারের একটি শাখা এবং প্রাচীন হিব্রু, ফিনিশীয় ও আরামীয় ভাষার পূর্বসূরী বলেই ধরা হয়।
প্রায় ১৫৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ সময়কালকে পরবর্তী ব্রোঞ্জ যুগ (Late Bronze Age) বলা হয়। এই সময়ে কানানের বড় একটি অংশ মিশরের নব রাজ্যের অধীনে পড়ে যায়। মিশরীয় শাসক থুতমোসিস III থেকে শুরু করে রামেসেস II পর্যন্ত একাধিক ফিরাউন এই অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করতেন। “আমার্না পত্রপত্রিকা” — যা কূটনৈতিক ও প্রশাসনিক চিঠিপত্রের এক বিরল সংকলন — থেকে আমরা জানতে পারি, কানানের বহু শহরের শাসকরা ফিরাউনের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়মিত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতেন এবং স্থানীয় বিদ্রোহ দমনে মিশরীয় সহায়তা প্রার্থনা করতেন।
কিন্তু পরবর্তী ব্রোঞ্জ যুগের অবসানে (প্রায় ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) গোটা পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এক বৃহৎ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয় নেমে আসে, যা “ব্রোঞ্জ যুগের পতন” নামে পরিচিত। মাইসেনীয় গ্রিস, হিত্তি সাম্রাজ্য, এবং মিশরের প্রভাবিত অঞ্চলসমূহে এই সময়কালে ধ্বংস, জনবসতির পরিত্যাগ, এবং শাসন কাঠামোর ভাঙন লক্ষ্য করা যায়। এর পিছনে কারণ হিসেবে জলবায়ুর পরিবর্তন, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, তথাকথিত ‘সামুদ্রিক জাতিগোষ্ঠীর’ আগমন ও বাণিজ্য পথের পতনকে দায়ী করা হয়।
এই দোলাচলে কানানও নিস্তার পায়নি। বহু নগর-রাষ্ট্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, মিশরের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে যায়, এবং এক নতুন শক্তির উত্থান দেখা দেয়। এই প্রেক্ষাপটে প্রাচীন মিশরের মেরনেপতাহ স্তম্ভ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে প্রথমবার “ইসরায়েল” নামটি ঐতিহাসিকভাবে উল্লেখিত হয়েছে। স্তম্ভটি খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ১২০০ সালের, এবং এতে লেখা আছে: “ইসরায়েল ধ্বংস হয়েছে; তার বীজ আর নেই।” এই বাক্যাংশ প্রমাণ করে যে তখনকার সময়ে, কানানের অভ্যন্তরে একটি জনগোষ্ঠী ইতিমধ্যেই “ইসরায়েল” নামে পরিচিত ছিল এবং তাদের সামাজিক উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য ছিল।
তবে তারা কোনো শহর-রাষ্ট্র ছিল না; বরং ইতিহাসবিদদের মতে, তারা ছিল একটি সম্প্রদায়, যারা পাহাড়ি অঞ্চলে গবাদিপশু পালন ও কৃষিনির্ভর জীবিকা গড়ে তুলেছিল। আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা এবং সামাজিক-ইতিহাস বিশ্লেষণ এই ধারণা প্রতিষ্ঠা করেছে যে ইসরায়েলীয়রা কানানের মধ্য থেকেই বিকশিত হয়েছিল — বাইরের আগন্তুক নয়, বরং অভ্যন্তরীণ বিকাশের ফল।
তাদের ধর্মীয় বিবর্তনও ধাপে ধাপে হয়েছে। কানানীয় ধর্ম বহুঈশ্বরবাদী ছিল, যেখানে এল, বাল, আশেরাহ প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজা চলত। ইসরায়েলীয়রা প্রথমদিকে এই ধর্মীয় কাঠামোর মধ্যে থেকেই উপাসনা করত, কিন্তু ধীরে ধীরে ইয়াহওয়ে উপাসনাকে কেন্দ্র করে এক স্বতন্ত্র একেশ্বরবাদী ধ্যান গড়ে ওঠে। এটি ছিল একটি দীর্ঘমেয়াদী ধর্মীয় রূপান্তর, যার চূড়ান্ত রূপ গৃহীত হয় বহু শতাব্দী পরে।
ইসরায়েলীয়রা যে ভাষায় কথা বলত তা ছিল প্রাচীন হিব্রু, যা সেমিটিক ভাষাগুলির একটি শাখা। এই ভাষাতেই বাইবেলের তোরাহ, নবী-লেখা ও অন্যান্য গ্রন্থ রচিত হয়। একই সময়ে, উপকূলীয় অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে এক নতুন জাতিগোষ্ঠী — ফিলিস্তীয়রা — যাদের সম্পর্কে ধারণা করা হয়, তারা সম্ভবত দক্ষিণ ইউরোপ থেকে আগত নাবিক ও সামরিক সম্প্রদায় ছিল। গাজা, অশকেলন, অশদোদ প্রভৃতি শহরে তারা একটি শক্তিশালী ফিলিস্তীয় পঞ্চনগর রাষ্ট্র গঠন করে।
এখানে স্মরণযোগ্য যে, হিব্রু বাইবেলে বর্ণিত “এক্সোডাস” — অর্থাৎ মিশর থেকে মোশির (মুসা) নেতৃত্বে ইসরায়েলীয়দের নির্গমন ও চূড়ান্তভাবে কানানে প্রবেশ — এই কাহিনির ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে এখনকার অধিকাংশ গবেষক সন্দিহান। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বা মিশরীয় ইতিহাসে এর সরাসরি প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং অনেকে মনে করেন, এই কাহিনি ইহুদি জাতিসত্ত্বার নির্মাণে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মিথ, যার মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র জাতীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
ইতিহাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল ইসরায়েল ও যিহূদার রাজ্য গঠনের প্রক্রিয়া। প্রায় ৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ উত্তর কানানে ইসরায়েলের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যার রাজধানী ছিল সামারিয়া। এটি ছিল অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ, জনবহুল ও রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় এক রাষ্ট্র, যা ওম্রিদ রাজবংশের অধীনে গালিলি, জর্দান উপত্যকা, শ্যারন সমভূমি ও ট্রান্সজর্ডান অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।
দক্ষিণে যিহূদার রাজ্য গঠিত হয় কিছুটা পরে — অনুমানিক ৮৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে — যার রাজধানী ছিল জেরুজালেম এবং যেটি ছিল একটি অপেক্ষাকৃত ছোট ও দুর্বল রাজ্য। এই রাজ্য শাসিত হত দায়ূদের (ডেভিড) বংশধরদের দ্বারা। ধর্মীয়ভাবে যিহূদা ছিল অপেক্ষাকৃত একনিষ্ঠ ইয়াহওয়ে উপাসক এবং এখানেই স্থাপিত হয় সোলোমনের মন্দির, যা পরবর্তীতে ইহুদি জাতির ধর্মীয় কেন্দ্র হয়ে ওঠে।
৭২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইসরায়েলের রাজ্য নব-অসিরীয় সাম্রাজ্যের আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বহু অধিবাসী নির্বাসিত হন, যাদের অনেকে ইতিহাসে “হারিয়ে যাওয়া দশ গোত্র” নামে পরিচিত। যিহূদা রাজ্য কিছুদিন অসিরীয় অধীনস্থ রাজারূপে টিকে থাকলেও পরে নব-বেবিলনীয় সাম্রাজ্যের অধীন পড়ে। ৫৮৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, নবূখদনেজার II জেরুজালেম দখল করেন, শহর ধ্বংস করেন এবং সোলোমনের মন্দির ভেঙে ফেলেন। এই ঘটনার ফলে শুরু হয় “বাবিলনীয় নির্বাসন” — ইহুদি জাতির ইতিহাসে এক গভীর অভিঘাতময় অধ্যায়।
এই নির্বাসনকালেই ইহুদিদের ধর্মীয় পরিচয় এবং ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তার গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটে। মন্দির-কেন্দ্রিক পূজা ব্যবস্থার পরিবর্তে শাস্ত্রপাঠ, উপাসনা ও ধর্মীয় অনুশীলনের এক নতুন ধারা গড়ে ওঠে, যার ভিত্তিতে পরবর্তী কালে ইহুদি ধর্মের রূপ পরিপূর্ণতা লাভ করে।
প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, লিপিপত্র, বাইবেল ও মিশরীয় দলিলপত্র একসঙ্গে পাঠ করলে বোঝা যায় যে, ইসরায়েল ও যিহূদা নামক দুটি রাষ্ট্র মূলত কানানের অভ্যন্তরে বসবাসকারী সেমিটিক জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকেই গড়ে উঠেছিল। তাদের রাজনৈতিক ইতিহাস, ধর্মীয় চেতনার বিবর্তন এবং সাংস্কৃতিক রূপান্তর এক বৃহৎ লেভান্তীয় প্রেক্ষাপটের অন্তর্গত ছিল।
এই ইতিহাস শুধুমাত্র ইহুদি জাতির নয়, এটি প্রাচীন লেভান্তের জাতিগুলির যৌথ উত্তরাধিকার। কানানের সেই বহু রঙিন নগর-রাষ্ট্র, ফিনিশীয়দের বাণিজ্যিক সাফল্য, ফিলিস্তীয়দের সামরিক উপস্থিতি, এবং মিশরীয়দের প্রশাসনিক প্রভাব সব মিলিয়ে এক বহুরৈখিক ইতিহাস তৈরি করে — যার প্রতিটি স্তর আজও প্রত্নতত্ত্বের মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে, আবার কোনোটির ছাপ রয়ে গেছে বাইবেলের পাতায়, মিশরীয় স্তম্ভে কিংবা উগারিতের লিপিতে। এই ইতিহাস চর্চার মধ্য দিয়ে আমরা শুধু অতীত নয়, সমসাময়িক ধর্মীয় ও জাতীয় পরিচয়ের উৎপত্তির গভীরতাকেও অনুধাবন করতে পারি।
শাস্ত্রীয় প্রাচীনত্ব
বাবিলনীয় সাম্রাজ্যের পতন এবং আকেমেনিড যুগের সূচনা প্রাচীন নিকটপ্রাচ্যের ইতিহাসে এক মৌলিক পালাবদলের সূচনা করে। খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৯ সালে, পারস্যের আকেমেনিড শাসক সাইরাস দ্য গ্রেট তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে বাবিলন দখল করেন এবং প্রাচীন বিশ্বের বৃহত্তম এক সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। কিন্তু সাম্রাজ্য গঠনের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি কেবল রাজনৈতিক শক্তি বিস্তারের দিক থেকেই নয়, বরং সংস্কৃতি, ধর্ম এবং মানবাধিকারবিষয়ক এক মৌলিক ঘোষণার মাধ্যমেও স্মরণীয় হয়ে থাকে।
সাইরাস, যিনি ‘মহান’ অভিধায় ভূষিত, শুধু একজন বিজয়ী সেনাপতি ছিলেন না, তিনি ছিলেন ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদের এক প্রাথমিক প্রচারক। তাঁর সর্বাধিক পরিচিত নীতিগত উদাহরণ হল বাবিলনের অধিবাসীদের, বিশেষ করে নির্বাসিত যিহূদিদের নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান। সাইরাস সিলিন্ডার — যা অনেকেই মানবাধিকার ঘোষণার প্রাচীনতম দলিল বলে বিবেচনা করেন — এই মানবিক রাজনীতির সাক্ষ্য বহন করে। ইহুদি ঐতিহ্যেও সাইরাসকে ঈশ্বরনির্ধারিত মুক্তিদাতা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, যেমনটি আমরা ইসায়া গ্রন্থে পাই।
যিহূদিদের একটি বড় অংশ, যারা নবূখদনেজারের হাত ধরে বাবিলনীয় নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল, পারস্যের এই নয়া নীতির ফলে আবারও তাদের প্রাচীন ভূমি — যিহূদা প্রদেশ — এ ফিরে আসে। এই প্রত্যাবর্তনের ধারাবাহিকতায় খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৫২০ সালের মধ্যে দ্বিতীয় মন্দির নির্মিত হয়। প্রথম সোলোমনিক মন্দির ধ্বংসের প্রায় ৭০ বছর পর এই মন্দির নির্মাণ ইহুদি জাতিগত পরিচয়ের পুনর্গঠনে এক কেন্দ্রীয় ভূমিকা রাখে। একে কেন্দ্র করে পুনরায় গঠিত হয় যিহূদিদের ধর্মীয় জীবন, এবং এটি পরবর্তী এক সহস্রাব্দ ধরে ইহুদি উপাসনার কেন্দ্রে অবস্থান করে।
আকেমেনিড প্রশাসন এই অঞ্চলের শাসনব্যবস্থাকে “ইয়েহুদ মেদিনাতা” নামে একটি আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশে রূপান্তরিত করে, যার নেতৃত্বে থাকত স্থানীয় প্রশাসক ও পুরোহিতগণ, যাঁরা পারস্যের সর্বোচ্চ প্রশাসনের অধীন থাকলেও অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে প্রচুর স্বাধীনতা ভোগ করতেন। এই সময়েই এজরা ও নেহেমিয়ার মতো ধর্মীয় নেতারা হিব্রু আইনকানুন পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, যার ফলে ধর্মীয় আইনের সামাজিক রূপ আরও শক্তিশালী হয়।
তবে শান্তির এই যুগ চিরস্থায়ী হয়নি। খ্রিস্টপূর্ব ৩৩২ সালে, গ্রিক যোদ্ধা আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট এক দুর্বার অভিযানে এই অঞ্চল দখল করেন। আকেমেনিড সাম্রাজ্যের পতনের পরে আলেকজান্ডারের তৈরি সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হলে, তাঁর সেনাপতিরা একাধিক রাজ্য গড়ে তোলে। এর ফলে যিহূদা অঞ্চল টলেমীয় ও পরে সেলেউসিড শাসনের অধীনে চলে যায়। এই নতুন গ্রিক-ভিত্তিক রাজনৈতিক পরিকাঠামো শুধু প্রশাসনিক কাঠামো নয়, ধর্ম ও সংস্কৃতিতেও এক রকমের ‘হেলেনাইজেশন’ প্রক্রিয়া চালু করে।
হেলেনিজম, যা গ্রিক ভাষা, ধর্ম ও রীতিনীতি গ্রহণের এক বিস্তৃত সংস্কারপ্রক্রিয়া, যিহূদা অঞ্চলের রক্ষণশীল ধর্মীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে গুরুতর সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ে — একদিকে গ্রিক সংস্কৃতি অনুসরণকারী ধনী ও প্রভাবশালী শ্রেণি, অপরদিকে ধর্মীয় আইনকে আঁকড়ে ধরা সাধারণ ইহুদি জনগণ। এই উত্তেজনার চূড়ান্ত রূপ দেখা যায় আনতিওকাস চতুর্থ এপিফানিসের শাসনামলে, যিনি যিরূশালেম মন্দিরে গ্রিক দেবতার প্রতিমা স্থাপন করেন এবং ইহুদি ধর্মীয় চর্চা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।
এই ধর্মীয় নিপীড়নের জবাবে শুরু হয় ম্যাকাবীয় বিদ্রোহ — এক সশস্ত্র জনআন্দোলন, যা খ্রিস্টপূর্ব ১৬৭ সালে সূচিত হয়। যিহূদা ম্যাকাবি ও তাঁর পরিবার সেলেউসিড বাহিনীর বিরুদ্ধে এক কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। পরবর্তী দুই দশকের সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে সেলেউসিড কর্তৃত্ব ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং ম্যাকাবীয়রা হাশমোনীয় বংশ নামে এক নতুন রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। হাশমোনীয় রাজ্য ছিল ইহুদি স্বায়ত্তশাসনের একটি বিরল অধ্যায়, যা প্রায় এক শতাব্দী ধরে টিকে ছিল এবং তার আওতায় আশপাশের অঞ্চল যেমন ইদোমিয়া, গালিলি, পেরেয়া ও সামারিয়ার কিছু অংশ জুড়ে এক ধরণের আঞ্চলিক সম্প্রসারণ ঘটে।
তবে হাশমোনীয় শাসনও রাজনৈতিক সংকট থেকে মুক্ত ছিল না। অভ্যন্তরীণ বিরোধ, বিশেষ করে শাসনক্ষমতার জন্য ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ, যিহূদা রাজনীতিকে দুর্বল করে তোলে এবং বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি করে। এই পটভূমিতে, খ্রিস্টপূর্ব ৬৩ সালে রোমান প্রজাতন্ত্রের জেনারেল পম্পেই এক অভিযানের মাধ্যমে সিরিয়া দখল করেন এবং পরে যিরূশালেমে প্রবেশ করে হাশমোনীয়দের অভ্যন্তরীণ বিরোধকে কাজে লাগিয়ে অঞ্চলটিকে রোমের আওতাভুক্ত করেন।
এই সময়কাল থেকেই যিহূদা এক স্পষ্ট রোমান উপনিবেশে পরিণত হয়, যার শাসনভাগ একদিকে রোমান গভর্নরের হাতে আর অন্যদিকে স্থানীয় এডোমীয় বংশোদ্ভূত হেরোদ দ্য গ্রেটের হাতে অর্পিত হয়। হেরোদ ছিলেন একদিকে রোমানপন্থী রাজা, অন্যদিকে এক নির্মম ও চতুর কূটনীতিক। তিনি ব্যাপক নির্মাণকাজের জন্য পরিচিত ছিলেন — হেরোদিয়ান মন্দিরের পুনঃনির্মাণ ছিল তাঁর সর্ববৃহৎ অবদান — তবে একই সঙ্গে তিনি তাঁর প্রতিপক্ষদের নির্মূল করার জন্যও berühmtheit লাভ করেন।
খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে এই ভূখণ্ড সরাসরি রোমান প্রদেশ “জুদেয়া”র অংশ হয়ে যায় এবং এই নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতা ইহুদি জনগণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে। উচ্চ কর, ধর্মীয় অবমাননা, এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা — এই তিনের সংমিশ্রণে ৬৬ খ্রিস্টাব্দে ইহুদি-রোমান যুদ্ধের সূচনা ঘটে, যা ঐতিহাসিকভাবে “প্রথম ইহুদি-রোমান যুদ্ধ” নামে পরিচিত।
এই যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী। জিউসেফাস ফ্ল্যাভিয়াস, একজন ইহুদি ইতিহাসবিদ যিনি পরবর্তীতে রোমানদের পক্ষে কাজ করেছিলেন, এই যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেন। যিরূশালেম অবরুদ্ধ হয়, দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে, এবং অবশেষে ৭০ খ্রিস্টাব্দে রোমান সেনাপতি টাইটাস শহরে প্রবেশ করে দ্বিতীয় মন্দির ধ্বংস করেন। এই ধ্বংস কেবল একটি ধর্মীয় কেন্দ্রের পতন ছিল না; এটি ইহুদি জাতিগত আত্মপরিচয়ের কেন্দ্রচ্যুতি ঘটায়।
রোমান নিপীড়নের শেষ অধ্যায় শুরু হয় বার কখবা বিদ্রোহ (১৩২–১৩৬ খ্রিস্টাব্দ), যা হাদ্রিয়ানের শাসনামলে সংঘটিত হয়। এই বিদ্রোহ ছিল এক চূড়ান্ত প্রয়াস, যার নেতৃত্ব দেন শিমন বার কখবা। ইহুদিরা সাময়িকভাবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেও, রোমানরা শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত নির্মমভাবে এই বিদ্রোহ দমন করে। লক্ষ লক্ষ ইহুদি নিহত হন, বহু গ্রাম ও শহর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এবং যিরূশালেম পুনর্নির্মাণ করে এক রোমান উপনিবেশ ‘এলিয়া ক্যাপিটোলিনা’ হিসেবে গড়ে তোলা হয়।
এই দমননীতির অংশ হিসেবে যিহূদা প্রদেশের নাম পরিবর্তন করে “সিরিয়া প্যালেস্টিনা” রাখা হয় — অনেক গবেষকের মতে, ইহুদি ইতিহাস ও স্মৃতি মুছে ফেলার জন্য এটি একটি কৌশলগত পদক্ষেপ। ইহুদিদের যিরূশালেমে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়, ধর্মীয় স্বাধীনতা চরমভাবে খর্ব হয়, এবং জাতিগত উপস্থিতির কেন্দ্র সরে যায় গালিলির মতো অঞ্চলে।
তবুও, ইহুদি চেতনার অবসান ঘটেনি। গালিলি হয়ে ওঠে এক নতুন ধর্মীয় কেন্দ্র, যেখানে তান্নাঈম ও পরবর্তী যুগের রাব্বিদের নেতৃত্বে মিশনা ও তালমুদের প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই সময় থেকেই ইহুদি পরিচয় ভৌগোলিক না হয়ে মূলত ধর্মীয় ও আইনি কাঠামোর ভিত্তিতে গঠিত হতে থাকে।
এই দীর্ঘ ইতিহাস প্রমাণ করে, যে যিহূদা ও যিরূশালেম শুধু একটি ভূগোলিক পরিসর নয়, বরং এক চলমান জাতিগত, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রতীক। এখানেই বিনির্মিত হয়েছে মুক্তির আখ্যান, জন্ম নিয়েছে নির্যাতনের স্মৃতি, এবং এই ইতিহাস এখনও আধুনিক রাজনৈতিক বাস্তবতা পর্যন্ত প্রসারিত। তাই এই প্রাচীন কাহিনি শুধুই অতীত নয়; এটি একটি চলমান মানবিক ইতিহাস, যার অনুরণন আমরা আজও টের পাই।
পরবর্তী প্রাচীনত্ব এবং মধ্যযুগ
চতুর্থ শতকে রোমান সাম্রাজ্যের ধর্মীয় ইতিহাসে এক মৌলিক ও স্থায়ী রূপান্তর ঘটে। বহুদেবতার পূজাভিত্তিক পৈত্তলিক ধর্ম, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রোমান সমাজের মূল সাংস্কৃতিক অভ্যাস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা ধীরে ধীরে হারিয়ে যায় খ্রিস্টধর্মের বিজয়ী উত্থানে। এই রূপান্তরের সূচনাপর্বের কেন্দ্রীয় চরিত্র ছিলেন সম্রাট কনস্ট্যানটাইন — এক রাজনৈতিক কৌশলী ও ধর্মীয় যুগদ্রষ্টা যিনি নিজের শাসনকে শক্তিশালী করার জন্য খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে এক গভীর সম্পর্ক স্থাপন করেন। ৩১৩ খ্রিস্টাব্দে কনস্ট্যানটাইন ও তাঁর সহশাসক লিসিনিয়াস “মিলান চুক্তি” ঘোষণার মাধ্যমে খ্রিস্টধর্মসহ সমস্ত ধর্মের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেন। তবে শুধু ধর্মীয় সহনশীলতা নয়, কনস্ট্যানটাইন খ্রিস্টধর্মকে সাম্রাজ্যিক রাজনীতির অন্যতম স্তম্ভে পরিণত করেন। তাঁর নেতৃত্বে খ্রিস্টান গির্জার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বাড়তে থাকে, এবং যিরূশালেমের মতো শহরগুলোতে গির্জা নির্মাণ শুরু হয় — যেমন খ্রিস্টান বিশ্বাস অনুযায়ী যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার স্থান ‘গলগোথা’র ওপর নির্মিত হয় ‘চার্চ অব দ্য হলি সেপালখর’।
খ্রিস্টধর্মের এই উত্থানকে পূর্ণতা দেন সম্রাট থিওডোসিয়াস প্রথম, যিনি ৩৮০ খ্রিস্টাব্দে “এডিক্ট অব থেসালোনিকা” জারি করে খ্রিস্টধর্মকে রোমান সাম্রাজ্যের একমাত্র বৈধ রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেন। এর মাধ্যমে পৈত্তলিক ধর্মগুলোকে আইনত নিষিদ্ধ করা হয় এবং খ্রিস্টধর্মই সাম্রাজ্যের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চেতনার কেন্দ্রে চলে আসে। এই নতুন বাস্তবতা শুধু রোমান রাজনৈতিক কাঠামোর উপরেই নয়, বরং সাম্রাজ্যের সকল ধর্মীয় সংখ্যালঘুর ওপরও গভীর প্রভাব ফেলে। ইহুদি সম্প্রদায়, যারা দীর্ঘকাল ধরে লেভান্ট ও অন্যান্য অঞ্চলে স্থিত ও সংগঠিত ছিল, তারা ক্রমশ এক নিপীড়িত ও বৈষম্যের শিকার জনসমষ্টিতে পরিণত হয়।
চতুর্থ শতক থেকে শুরু করে রোমান আইনে একাধিক বিধিনিষেধ আরোপিত হতে থাকে ইহুদিদের বিরুদ্ধে। তাদের ধর্মীয় অধিকার সংকুচিত করা হয়, নতুন গির্জা নির্মাণের জন্য তাদের জমি অধিগ্রহণ করা হয়, এবং কখনও কখনও জোরপূর্বক ধর্মান্তর বা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়। একই সঙ্গে রোমান ক্যাথলিক গির্জা এক তাত্ত্বিক অবস্থান গ্রহণ করে, যেখানে ইহুদিদের ‘ঈশ্বর হত্যাকারী’ (deicide) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় — এই অভিযোগের ভিত্তিতে ভবিষ্যতের শতাব্দীতে বহু ইহুদি নিপীড়নের শিকার হবেন।
যিহূদা ও গালিলির অনেক ইহুদি এই পরিবর্তিত অবস্থায় নিজ নিজ জন্মভূমি ছেড়ে প্রবাসে পাড়ি জমান — মিশর, পারস্য, ব্যাবিলন ও পরবর্তীতে ইউরোপের বিভিন্ন অংশে। অন্যদিকে, স্থানীয়ভাবে ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরের একটি উল্লেখযোগ্য প্রবণতা দেখা যায়, যা রোমান প্রশাসনের চাপ, সামাজিক সুবিধা লাভের প্রত্যাশা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার আকাঙ্ক্ষা থেকে উৎসারিত হয়। এর ফলে যিরূশালেমসহ অন্যান্য শহরে খ্রিস্টান জনসংখ্যা বাড়তে থাকে, এবং পঞ্চম শতকের মধ্যে খ্রিস্টানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ওঠে।
এই সময়েই এক ভিন্ন জনগোষ্ঠী — সামারিটানদের — উপর নতুন করে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চাপ সৃষ্টি হতে থাকে। সামারিটানরা ছিল একটি স্বতন্ত্র ধর্মীয় সম্প্রদায়, যারা মূসার আইন মানত বটে, তবে যিরূশালেমের মন্দিরকে স্বীকৃতি দিত না; তারা শিখেম ও গেরিজিম পর্বতমালাকে পবিত্র স্থান বলে গণ্য করত। খ্রিস্টান প্রশাসনের দৃষ্টিতে এই ভিন্নধর্মী অবস্থান ছিল সন্দেহজনক ও বিভ্রান্তিকর। পঞ্চম শতকের শেষ দিকে শুরু হয় সামারিটান বিদ্রোহ, যা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং ৬ষ্ঠ শতকের শেষ পর্যন্ত চলতে থাকে। বাইজেন্টাইন কর্তৃপক্ষ এই বিদ্রোহ নৃশংসভাবে দমন করে। লক্ষাধিক সামারিটান নিহত হন, বহু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এবং এই ঘটনার ফলে সামারিটান সম্প্রদায়ের সংখ্যা চরমভাবে হ্রাস পায়।
এই শাসনকাঠামোর আরেকটি পরিবর্তন আসে ৬১৪ খ্রিস্টাব্দে, যখন পারস্যের সাসানীয় সাম্রাজ্য বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এক সফল সামরিক অভিযানে যিরূশালেম দখল করে। এই সময় ইহুদি সম্প্রদায় পারস্য বাহিনীর পক্ষে অবস্থান নেয়, বাইজেন্টাইন নিপীড়নের প্রতিশোধ নিতে। তারা সাময়িকভাবে যিরূশালেমে একধরনের স্বশাসন প্রতিষ্ঠা করে এবং বাইজেন্টাইনদের নির্মিত চার্চ ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু এই বিজয় স্থায়ী হয় না। ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট হেরাক্লিয়াস পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জিতে পুনরায় যিরূশালেমের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এরপর ইহুদিদের ওপর প্রতিশোধ নেয়া হয় — হাজার হাজার ইহুদি হত্যা করা হয়, বহুজন নির্বাসিত হন, এবং এই অঞ্চলে তাদের অস্তিত্ব আরও সংকুচিত হয়।
এই জটিল ও অনিরাপদ রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে এক নতুন শক্তি আত্মপ্রকাশ করে — ইসলাম। হিজরি ১৩/খ্রিস্টীয় ৬৩৪ সালে রাশিদুন খিলাফতের সেনারা লেভান্ট অঞ্চলে অভিযান শুরু করেন। খলিফা আবু বকর ও পরবর্তীতে উমর ইবন আল-খাত্তাবের নেতৃত্বে সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও মিশর একে একে ইসলামী শাসনের আওতায় আসে। খ্রিস্টীয় ৬৪১ সালের মধ্যেই বাইজেন্টাইনরা এই অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত হয়। মুসলিমদের শাসনপদ্ধতি ছিল তুলনামূলকভাবে সহনশীল। “আহলুল কিতাব” (গ্রন্থধারী সম্প্রদায়) হিসেবে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের উপাসনা, ধর্মীয় আইন ও বিচারব্যবস্থা বজায় রাখার অনুমতি দেওয়া হয় — যদিও তাদের উপর জিযিয়া নামক একটি কর আরোপিত ছিল।
এরপরের ছয় শতাব্দীতে লেভান্টের শাসনক্ষমতা একাধিক মুসলিম শাসকবর্গের মধ্যে পরিবর্তিত হতে থাকে — প্রথমে উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফত, তারপর ফাতিমীয় ও সেলজুকদের শাসন এবং শেষপর্যন্ত আইয়ুবীয় বংশের উত্থান। এই সময়ে আরবিয়করণ ও ইসলামীকরণের ধারা তীব্রতর হয়। পূর্বে গ্রিক, আরামীয় ও হিব্রু ভাষার প্রচলন থাকলেও এখন আরবি প্রধান ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। ধর্মীয় ক্ষেত্রেও ইসলামিক আইন, শিক্ষা ও সাহিত্য ছড়িয়ে পড়ে।
তবে এই দীর্ঘকালীন পরিবর্তনের মধ্যেও ইহুদি সম্প্রদায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। তারা গালিলি, তিবেরিয়াস ও সাফেদ-এর মতো অঞ্চলে সংগঠিত হয়ে ছোট ছোট জনপদে বসবাস করতে থাকে। সেখানে গড়ে ওঠে তান্নাঈম ও আমোরাঈমদের নেতৃত্বে একটি বৌদ্ধিক পরিবেশ, যার ফসল হল প্যালেস্টাইনীয় তালমুদ ও মিদ্রাশ।
অন্যদিকে, ইসলামী যুগেও এক গুরুতর গণসংকট দেখা দেয় — জনসংখ্যা ব্যাপক হারে হ্রাস পেতে থাকে। রোমান ও বাইজেন্টাইন যুগে যেখানে লেভান্ট অঞ্চলে প্রায় ১০ লাখ জনসংখ্যা ছিল বলে অনুমান করা হয়, সেখানে ইসলামী মধ্যযুগের শেষে, ওসমানীয় শাসনের প্রারম্ভে, এই সংখ্যা তিন লাখে নেমে আসে। এই পতনের পেছনে ছিল যুদ্ধ, মহামারী, শাসনযন্ত্রের শিথিলতা এবং পরিবেশগত অবক্ষয়।
এতদসত্ত্বেও, এই অঞ্চলের গুরুত্ব কখনোই হ্রাস পায়নি। বিশেষ করে যিরূশালেম — যা মুসলিমদের কাছে আল-উক্সা মসজিদের জন্য তৃতীয় পবিত্রতম শহর — ক্রমাগত ধর্মীয় ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই পবিত্র শহর ও এর আশপাশের অঞ্চল পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে এক নতুন শক্তি আত্মপ্রকাশ করে ইউরোপে — ক্রুসেড আন্দোলন।
১১শ শতকের শেষে পোপ আরবান II-এর ডাকে শুরু হয় ‘প্রথম ক্রুসেড’। এর পিছনে ছিল ধর্মীয় উন্মাদনা, রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং অর্থনৈতিক প্রেরণা। ইউরোপীয় খ্রিস্টান ক্রুসেডাররা লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে লেভান্টে অভিযান চালায় এবং অবশেষে ১০৯৯ সালে যিরূশালেম দখল করে ‘ক্রুসেডার রাজ্য’ প্রতিষ্ঠা করে। শহর দখলের সময় হাজার হাজার মুসলমান ও ইহুদি হত্যার শিকার হন — এটি ছিল ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ গণহত্যাগুলির একটি।
এই ক্রুসেডার শাসন স্থায়ী হয় প্রায় ২০০ বছর, যদিও বিভিন্ন সময়ে মুসলিম সেনাপতিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। সালাহউদ্দিন আইয়ুবি ছিলেন সেই প্রতিরোধের সবচেয়ে স্মরণীয় মুখ। ১১৮৭ সালে তিনি হট্টিনের যুদ্ধে ক্রুসেডারদের পরাজিত করে যিরূশালেম পুনরুদ্ধার করেন, এবং বিপরীতভাবে, যেভাবে খ্রিস্টানরা শহর দখল করেছিল, তা থেকে ভিন্নভাবে — অতি মানবিক ও সংযত আচরণ প্রদর্শন করেন।
শেষ পর্যন্ত, ১২৯১ সালে মিশরের মামলুক সুলতানদের হাতে একে একে ক্রুসেডারদের সব দুর্গ পতন ঘটে, এবং এই অঞ্চল আবারও পুরোপুরি মুসলিম শাসনে ফিরে আসে। ক্রুসেড-পরবর্তী এই সময়ে লেভান্ট অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, যদিও সাম্রাজ্যিক প্রতিযোগিতা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব কখনো পুরোপুরি থেমে যায়নি।
এই দীর্ঘ ইতিহাস, spanning এক সহস্রাধিক বছর, প্রমাণ করে — লেভান্ট ও বিশেষ করে প্যালেস্টাইন অঞ্চল ছিল এক বহুধর্মীয়, বহুজাতিগত ও রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল ভূখণ্ড। এখানে ইতিহাস কখনোই সরলরেখায় প্রবাহিত হয়নি। বরং প্রতিটি শাসক, ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠী এই ভূমির সঙ্গে তাদের পরিচয়, স্মৃতি ও দাবির এক জটিল সম্পর্ক গড়ে তুলেছে, যার প্রতিধ্বনি আমরা আজও টের পাই আধুনিক রাজনীতি, ধর্মীয় বিতর্ক ও ইতিহাসচর্চার পরতে পরতে।
আধুনিক যুগ এবং জায়নবাদের উত্থান
১৫১৬ সালে ওসমানী সাম্রাজ্য লেভান্ট অঞ্চল দখল করে নিলে প্যালেস্টাইন তাদের সিরিয়ার অঙ্গরাজ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই দখলদারির পটভূমিতে ছিল সাম্রাজ্য বিস্তারের কৌশল এবং মামলুকদের দুর্বলতা। ১৫১৭ সালে, ওসমানী বাহিনী মিশরের মামলুক সুলতানদের পরাজিত করলে, ফিলিস্তিনীয় অঞ্চলও তাদের নিয়ন্ত্রণে আসে। যদিও এই দখল রক্তপাতবিহীন ছিল না। ঐ বছরেই দুটি সহিংস আক্রমণ ঘটে—সাফেদ এবং হেবরনে—যাতে ইহুদি সম্প্রদায় নিপীড়নের শিকার হয়। এই ঘটনাগুলি ইঙ্গিত দেয় যে ওসমানী সাম্রাজ্যের প্রাথমিক শাসনধারা সবক্ষেত্রে সহনশীল ছিল না, বিশেষ করে সমাজের সংখ্যালঘুদের জন্য।
তবে, সামগ্রিকভাবে ওসমানী শাসন প্যালেস্টিনে এক ধরণের স্থিতিশীলতা এবং শাসন কাঠামোর সরলীকরণ নিয়ে আসে। সাম্রাজ্য তাদের বিখ্যাত “মিলেট সিস্টেম” প্রয়োগ করে, যেখানে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী—বিশেষ করে খ্রিস্টান এবং ইহুদি সম্প্রদায়—”ধিম্মি” অর্থাৎ সুরক্ষিত জনসত্তা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এর বিনিময়ে, তারা বিশেষ কর প্রদান করত, যা জিযিয়া নামে পরিচিত। এই ব্যবস্থায় তারা নিজস্ব ধর্মীয়, সামাজিক ও বিচার ব্যবস্থা বজায় রাখতে পারত, যদিও তাদের উপর কিছু ভৌগোলিক ও নাগরিক সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হতো। এই সীমাবদ্ধতাগুলি কাগজে কঠোর হলেও বাস্তবে বহু ক্ষেত্রেই তা নমনীয়ভাবে প্রয়োগ করা হত।
১৬শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, স্পেনের ইনকুইজিশনের তাণ্ডব থেকে পালিয়ে আসা সেফারদী ইহুদিদের জন্য প্যালেস্টাইন আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। ১৫৬১ সালে সুলতান সুলেইমান এই ইহুদিদের তিবেরিয়াসে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেন। তিবেরিয়াসকে সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করে একটি ইহুদি সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। একই সময়ে, ইহুদি সম্প্রদায়গুলি চার পবিত্র শহর—জেরুজালেম, তিবেরিয়াস, হেবরন ও সাফেদ—জুড়ে নিজেদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচিতি গড়ে তোলে।
এই সময়েই ইহুদি ধর্মীয় পুণর্জাগরণ ও তালমুদ চর্চা ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়, বিশেষত সাফেদ শহরে। এখানে কাব্বালাহ তথা ইহুদি মিস্টিসিজমের এক নতুন ধারা গড়ে ওঠে, যার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন ইসাক লুরিয়া ও তাঁর শিষ্যরা। সাফেদ ক্রমে একটি ধর্মীয় তীর্থে রূপান্তরিত হয়, যেখানে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইহুদি পণ্ডিতেরা আসতে থাকেন। তবে ১৬৬০ সালে দ্রুজ বিদ্রোহের সময় এই অঞ্চল আবার অস্থির হয়ে পড়ে। সাফেদ ও তিবেরিয়াস তখন ব্যাপক ধ্বংসের শিকার হয় এবং অনেক ইহুদি বসতি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।
১৮শ শতকে ফিলিস্তিনীয় অঞ্চল ওসমানী নিয়ন্ত্রণে থাকলেও কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতা এবং স্থানীয় ক্ষমতাকেন্দ্রের উত্থান দেখা যায়। স্থানীয় আরব নেতা যাহির আল-উমর গালিলিতে কার্যত একটি স্বায়ত্তশাসিত আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একাধারে প্রশাসক, সামরিক নেতা ও কূটনীতিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর আমলে বাণিজ্য, কৃষি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত হয়। যদিও ওসমানীরা তাঁকে হটাতে একাধিক প্রচেষ্টা চালায়, কিন্তু জীবিতাবস্থায় তা ব্যর্থ হয়। তাঁর মৃত্যুর পর কেন্দ্রীয় শাসন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৭৯৯ সালে, ফরাসি সেনাপতি নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সিরিয়া অভিযান শুরু করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল মিসর থেকে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে ব্রিটিশ উপনিবেশের পথ রুদ্ধ করা। একর শহরে ওসমানী গভর্নর জায্জার পাসা তাঁর অভিযান রুখে দেন। ফরাসি বাহিনী এক দীর্ঘ অবরোধের পর ব্যর্থ হয়ে পিছু হটে। এই ব্যর্থতা প্যালেস্টিনে ইউরোপীয় হস্তক্ষেপের এক প্রাথমিক অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়।
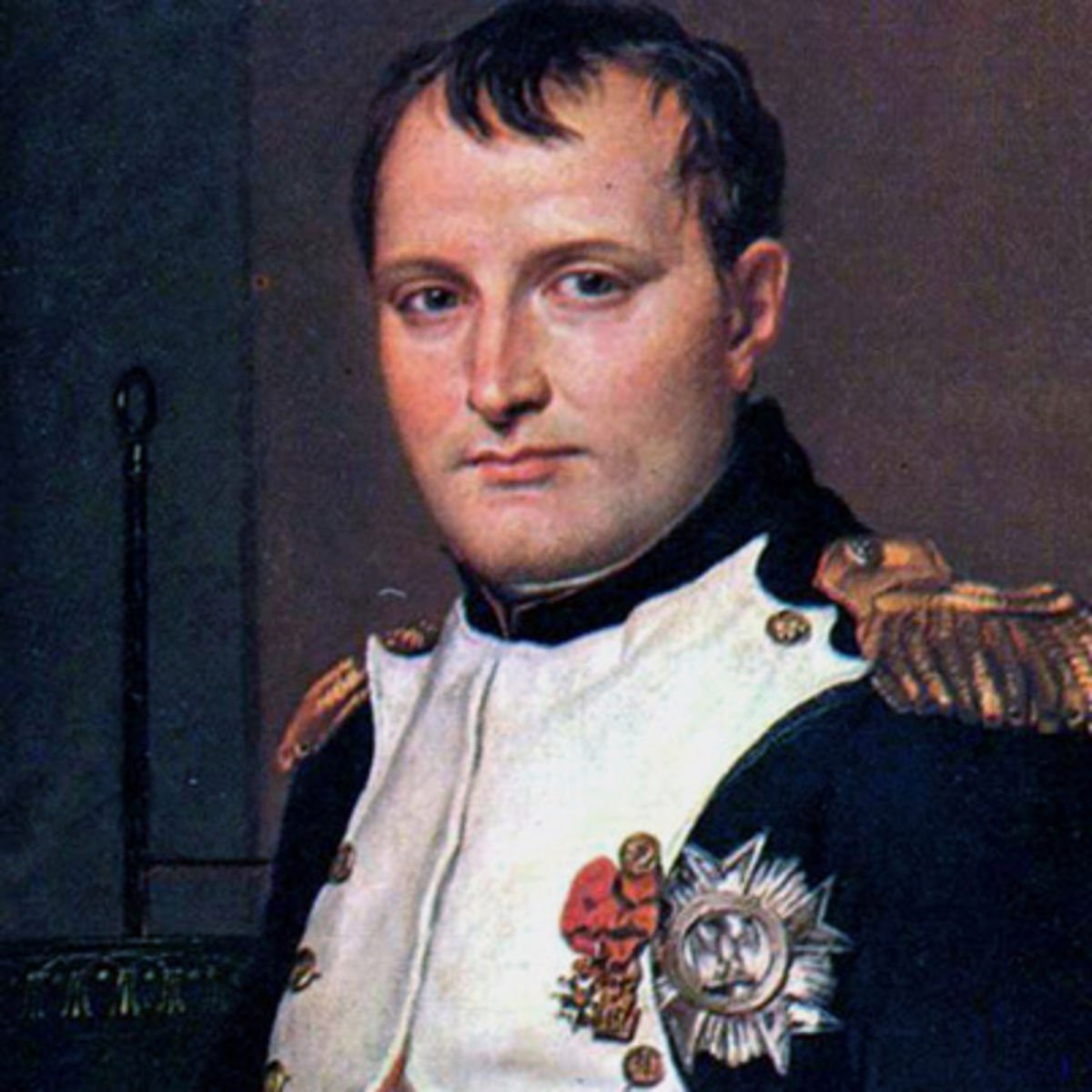
১৯ শতকের শুরুতে, বিশেষ করে ১৮৩৪ সালে, স্থানীয় আরব কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহ মূলত মিশরের খেদিভ মোহাম্মদ আলীর কর নীতি ও নিয়োগ প্রথার বিরুদ্ধে ছিল। যদিও প্রথমদিকে বিদ্রোহকারীরা কিছু অঞ্চল নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়, পরবর্তীতে মিশরীয় বাহিনী বিদ্রোহ কঠোরভাবে দমন করে। এই বিদ্রোহ ও দমনের প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ হস্তক্ষেপ ঘটে এবং ১৮৪০ সালে মিশরীয় প্রভাব কমে গিয়ে ওসমানী শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এর পরে তানজিমাত নামে পরিচিত প্রশাসনিক সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হয়, যা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে নতুন আইনি ও সামাজিক ব্যবস্থা চালু করে।
এই সময়ে ইউরোপীয় শক্তিগুলির প্রভাব ক্রমশ বাড়তে থাকে, এবং একই সঙ্গে ইহুদি জাতীয়তাবাদ বা সায়নিজমের বীজও রোপিত হতে থাকে। ১৮৮১ সালে পূর্ব ইউরোপে ইহুদিদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও পোগ্রামের ফলে শুরু হয় প্রথম আলিয়াহ—ইহুদি অভিবাসনের প্রথম ঢেউ। এই অভিবাসীরা মূলত রাশিয়া ও রোমানিয়ার মতো দেশ থেকে আগত, যারা প্যালেস্টিনে নতুন কৃষি বসতি স্থাপন করতে থাকে। এই বসতিগুলিকে বলা হতো “মোশাভ” বা “কিবুত্জ”। যদিও এই অভিবাসন সংখ্যা ছিল সীমিত, তবে তাদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।
১৮৮২ সালের মেয় আইন ইহুদিদের জন্য নতুন অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিধিনিষেধ আরোপ করে, যার ফলে রাশিয়ায় ইহুদি জীবন আরও কঠিন হয়ে পড়ে। এর ফলে ইউরোপীয় ইহুদি সমাজে সায়নিজম নামক একটি নতুন রাজনৈতিক আন্দোলনের বিকাশ ঘটে। এই আন্দোলনের মূল প্রেরণা ছিল—ইহুদি জাতির আত্মনির্ধারণের অধিকার এবং ফিলিস্তিনে একটি স্বতন্ত্র ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।
১৮৯৭ সালে সুইজারল্যান্ডের বাসেলে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম আন্তর্জাতিক সায়নিজ কংগ্রেস, যার প্রধান সংগঠক ছিলেন থিওডর হার্জল। এই সম্মেলনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একটি সুসংগঠিত কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এ সময় ফিলিস্তিনে ইহুদি জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার খুব সামান্য অংশ। যারা তখন সেখানে বাস করতেন, তাদেরকে বলা হতো “পুরাতন ইয়িশুভ” — তারা মূলত ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সেখানে ছিলেন এবং অনেকেই স্থানীয় আরব সমাজের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে অভ্যস্ত ছিলেন।
তবে নতুন ইহুদি অভিবাসীরা এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আগমন করেন। তারা আত্মনির্ভরতা, নিজস্ব শ্রম এবং জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে ফিলিস্তিনে পা রাখেন। ১৯০৪ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে শুরু হয় দ্বিতীয় আলিয়াহ, যার মাধ্যমে প্রায় ৪০,০০০ ইহুদি ফিলিস্তিনে আগমন করেন। তাদের অনেকেই ছিলেন সমাজতন্ত্রী এবং তারা কিবুত্জ আন্দোলনের সূচনা করেন — একটি সমবায় কৃষি ব্যবস্থা, যেখানে সম্পত্তি ও শ্রম ছিল যৌথভাবে ব্যবস্থাপিত।
এই নতুন অভিবাসীরা আরব কৃষকদের শ্রমের উপর নির্ভর না করে কেবলমাত্র ইহুদি শ্রমের উপর নির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এতে আরব সম্প্রদায়ের সঙ্গে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। আরবদের মনে এই ধারণা জন্ম নিতে থাকে যে নতুন অভিবাসীরা শুধুমাত্র বসতি স্থাপন করতে নয়, বরং তাদের জমি, সংস্কৃতি ও সমাজের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে এসেছে। এই জাতীয়তাবাদী উত্তেজনা পরবর্তীতে ইহুদি-আরব দ্বন্দ্বের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়।
এই সময়ে ইহুদি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একাধিক সশস্ত্র সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৯০৭ সালে বার-গিওরা এবং ১৯০৯ সালে হাশোমের প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা ইহুদি বসতিগুলির পাহারা দিত এবং স্থানীয় সংঘাতের সময় প্রতিরোধ গড়ে তুলত। একই সময়ে ১৯০৯ সালেই তেল আভিভ প্রতিষ্ঠিত হয় — এটি ছিল প্রথম পরিকল্পিত ইহুদি শহর।
এইভাবে ওসমানী শাসনের শেষ দিকে প্যালেস্টিন এক পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়ায়। একদিকে ছিল বহুবর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার, অন্যদিকে ছিল ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের অভিঘাতে বিকশিত একটি নতুন চেতনা — যা পরবর্তীতে মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক মানচিত্রকে আমূল বদলে দেবে।
ইসরায়েল রাষ্ট্র
১৯৪৮ সালের ১৪ মে, যখন ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগের দিন ছিল, তৎকালীন ইহুদি এজেন্সির প্রধান ডেভিড বেন-গুরিয়ন ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন—প্রাচীন “এরেথ ইসরায়েল” বা ঐতিহাসিক ইসরায়েলের ভূমিতে একটি স্বাধীন ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ইহুদি জনগণের বহু শতাব্দীর স্বপ্ন ও সংগ্রামের বাস্তব রূপ ছিল এই ঘোষণা। এর ফলে পরদিনই, অর্থাৎ ১৫ মে, আরব বিশ্ব থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া আসে। মিশর, সিরিয়া, ট্রান্সজর্ডান এবং ইরাকের সেনাবাহিনী একযোগে আক্রমণ চালিয়ে সদ্যঘোষিত ইহুদি রাষ্ট্রে প্রবেশ করে। পরে ইয়েমেন, মরক্কো, সৌদি আরব এবং সুদান থেকেও সৈন্য পাঠানো হয়। এই সম্মিলিত আগ্রাসনের উদ্দেশ্য নিয়ে বিতর্ক রয়েছে—ইহুদি পক্ষের দাবি ছিল, এই আক্রমণ ছিল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে, আরবদের একটি অংশ সরাসরি ঘোষণা করে বসে—”ইহুদিদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করাই উদ্দেশ্য।”
তবে আরব লীগের ব্যাখ্যা ছিল কিছুটা আলাদা। তারা দাবি করে, ম্যান্ডেটের ভাঙনের পর যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে, তা নিয়ন্ত্রণ করা এবং শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই তাদের মূল লক্ষ্য। কিন্তু বাস্তবে এই যুদ্ধে ব্যাপক রক্তপাত ঘটে, এবং এর পরিণতিতে প্রায় এক বছর ধরে সংঘর্ষ চলতে থাকে। শেষে, একটি যুদ্ধবিরতির মধ্য দিয়ে অস্থায়ী সীমান্ত নির্ধারিত হয়—যা পরে “গ্রিন লাইন” নামে পরিচিতি পায়। এই সীমারেখার মধ্যেই ইসরায়েল রাষ্ট্র কার্যত তার প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করে। যুদ্ধের ফলস্বরূপ জর্ডান পশ্চিম তীর এবং পূর্ব জেরুজালেম অধিকার করে, এবং মিশর গাজা উপত্যকার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে।
সবচেয়ে গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী মানবিক পরিণতি দেখা যায় প্যালেস্টিনীয় জনগণের ক্ষেত্রে। আনুমানিক ৭ লক্ষেরও বেশি প্যালেস্টিনীয় এই সময়ে নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন বা জোরপূর্বক বিতাড়িত হন—এই ঘটনাকে প্যালেস্টিনীয়রা ‘নাকবা’ নামে স্মরণ করে, যার অর্থ বিপর্যয় বা দুর্যোগ। বহু শতাব্দী ধরে চলে আসা প্যালেস্টিনীয় আরব সমাজ এই বিচ্ছিন্নতার ফলে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। জাতীয় পরিচয়, ঐতিহ্য এবং সামাজিক কাঠামো ভেঙে পড়ে। তবুও, প্রায় ১ লক্ষ ৫৬ হাজার প্যালেস্টিনীয় আরব ইসরায়েলের সীমানার মধ্যে থেকে যান এবং পরবর্তীতে তারা ইসরায়েলের নাগরিকত্ব লাভ করেন—যদিও তাদের অবস্থান বহু দশক ধরে আইনি ও সামাজিকভাবে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত হয়নি।
এই যুদ্ধোত্তর সময়ে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের পথ সহজ হয়। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের রেজুলেশন ২৭৩-এর মাধ্যমে, ১৯৪৯ সালের ১১ মে, ইসরায়েল রাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। নতুন রাষ্ট্রের রাজনীতি ও প্রশাসনিক কাঠামো নির্মাণের নেতৃত্বে ছিলেন লেবার সায়নিজমের প্রধান প্রতিনিধি ও প্রধানমন্ত্রী বেন-গুরিয়ন। তাঁর প্রশাসন মূলত একটি সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন শুরু করে, যার অন্যতম অগ্রাধিকার ছিল বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা ইহুদি জনগণকে একত্রিত করে ইসরায়েলে পুনর্বাসন করা।
এই উদ্দেশ্যেই গড়ে ওঠে অভিবাসন সংক্রান্ত একটি সুসংগঠিত নীতি, যার অন্তর্গত ছিল “এক মিলিয়ন পরিকল্পনা”। মোসাদ লে আলিয়া বেট নামক একটি গোপন সংস্থা বিশেষভাবে কাজ করত এমনসব দেশে, যেখানে ইহুদিদের ওপর নিপীড়ন চলছিল—যেমন মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা, পূর্ব ইউরোপ। এই সংস্থাটি গোপন অপারেশনের মাধ্যমে ইহুদিদের ইসরায়েলে নিয়ে আসত। ১৯৫৩ সালে এই সংস্থা বিলুপ্ত হলেও, এর অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই।
ইসরায়েলের প্রথম তিন বছরে, অভিবাসনের ঢেউ ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। হোলোকাস্ট থেকে বেঁচে যাওয়া ইউরোপীয় ইহুদি, পূর্ব ইউরোপে স্টালিনীয় দমন-পীড়ন, এবং আরব ও মুসলিম দেশগুলোতে রাষ্ট্রীয় বৈষম্যের মুখে পড়া ইহুদিরা দলে দলে ইসরায়েলে পাড়ি জমান। ফলস্বরূপ, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময় যেখানে ইহুদি জনসংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ, তা দ্রুত বেড়ে ১৪ লক্ষে পৌঁছায়। ১৯৫৮ সালের মধ্যে এই সংখ্যা দুই মিলিয়নে পরিণত হয়। ১৯৪৮ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে আনুমানিক ১১.৫ লক্ষ ইহুদি ইসরায়েলে পুনর্বাসিত হন।
তবে এই বিশাল অভিবাসী জনগোষ্ঠীকে অবকাঠামোগত, সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে স্থাপন করা ছিল এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। অস্থায়ীভাবে তাদের রাখা হয়েছিল “মাআবরত” নামের তাঁবুর শহরে। ১৯৫২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এমন তাঁবুতে প্রায় ২ লক্ষেরও বেশি মানুষ বাস করছিলেন। এই অভিবাসীদের মধ্যে ইউরোপীয় ইহুদিরা তুলনামূলকভাবে বেশি সুবিধা পেতেন। আরব দেশগুলো থেকে আগত মিজরাহি ও সেফারদী ইহুদিদের জন্য বরাদ্দ আবাসন ইউনিটগুলো অনেক সময় ইউরোপীয়দের হাতে চলে যেত, যার ফলে আরব দেশীয় ইহুদিরা অনেক দিন ধরে অস্থায়ী শিবিরেই কাটিয়ে দিতেন। এতে ইসরায়েলের অভ্যন্তরে শ্রেণিভেদ ও জাতিগত বৈষম্যের ভিত্তি তৈরি হতে থাকে।
এই সময়ে দেশজুড়ে দেখা যায় চরম অর্থনৈতিক সংকট। খাদ্য, বস্ত্র, জ্বালানি—সবকিছুতেই কড়া নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। এই সময়টিকে বলা হয় “অষ্টেরিটি পিরিয়ড” বা সংকোচনের যুগ। প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান করতে গিয়ে বেন-গুরিয়ন সরকার এক কঠিন সিদ্ধান্ত নেন—পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে একটি পুনঃক্ষতিপূরণ চুক্তি স্বাক্ষর করেন। হোলোকাস্টের জন্য এই অর্থনৈতিক ক্ষতিপূরণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত ইসরায়েলের অভ্যন্তরে গভীর বিতর্কের জন্ম দেয়। বহু ইহুদি নাগরিক এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে রাস্তায় প্রতিবাদে নামে। তাদের বক্তব্য ছিল, জার্মানি থেকে নেওয়া অর্থ রক্ত দিয়ে রঞ্জিত। তবে রাষ্ট্রের আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার স্বার্থে বেন-গুরিয়ন নিজের অবস্থানে অনড় থাকেন।
এই গোটা সময়কালটি ছিল ইসরায়েলের জাতীয় পরিচয় নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্য সামলানো, এবং বহিঃশক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার এক জটিল অধ্যায়। এটি শুধুমাত্র একটি রাষ্ট্র গঠনের গল্প নয়—এটি বহু ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং বেদনার সংঘাতে দাঁড়িয়ে একটি জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস।
ভূগোল
পশ্চিম এশিয়ার মানচিত্রে একটুকরো অনন্য ভূখণ্ড হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে ইসরায়েল—ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত এই দেশটির আয়তন তুলনামূলকভাবে ছোট হলেও, ভৌগোলিক বৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্রের দিক থেকে এর গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য চমকপ্রদ। রাষ্ট্রটি এমন এক ভূখণ্ডে অবস্থিত যেখানে একদিকে মরুভূমির রুক্ষতা, অন্যদিকে সমুদ্রঘেরা উর্বর সমভূমি, আবার উত্তরে শীতপ্রধান পর্বতমালা—সব মিলিয়ে যেন এক প্রকৃতির ক্ষুদ্র বিশ্ব।
ইসরায়েলের পশ্চিমে আছে ভূমধ্যসাগর—একটি পুরাতন সভ্যতার আঁতুড়ঘর—যার পূর্ব উপকূলে ছড়িয়ে আছে ইসরায়েলি উপকূলীয় সমভূমি। এই সমভূমি অঞ্চলেই গড়ে উঠেছে দেশের বৃহত্তর জনবসতি অঞ্চল এবং এখানেই বাস করে অধিকাংশ ইসরায়েলি নাগরিক। উপকূলবর্তী এই অঞ্চল তুলনামূলকভাবে উর্বর, যার মাটি কৃষিকাজের উপযোগী এবং আবহাওয়া ভূমধ্যসাগরীয় ধরনের—শীতকালে মৃদু ও কিছুটা আর্দ্র, গ্রীষ্মে শুষ্ক ও উষ্ণ। ফলে এই অঞ্চল কৃষিকাজ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও নগরায়নের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত।
দেশটির দক্ষিণভাগ জুড়ে বিস্তৃত নেগেভ মরুভূমি—প্রায় ১৩,০০০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই অঞ্চলটি দেশের অর্ধেকেরও বেশি এলাকা দখল করে আছে। এখানকার মাটি শুষ্ক ও শিলাময়, বর্ষণ অতি অল্প। তবে আশ্চর্যজনকভাবে, ইসরায়েল এই মরুভূমিতেও জীবন ও চাষাবাদের স্পন্দন ফিরিয়ে আনতে পেরেছে। অত্যাধুনিক জলসেচ প্রযুক্তি, ড্রিপ ইরিগেশন ও মরুভূমি কৃষি গবেষণার মাধ্যমে এখানেও ফলানো হচ্ছে খেজুর, ড্রাগন ফ্রুট, বাদাম ও নানা রকম শাকসবজি। এ যেন মরুতে ফোটানো এক সবুজ বিপ্লব।
ইসরায়েলের উত্তরে আছে গালিলি, কারমেল এবং গোলান মালভূমির পাহাড়ি অঞ্চল। এইসব এলাকা তুলনামূলকভাবে শীতল এবং বরফাবৃতও হয় শীতকালে। এখানে হিমবাহ নেই ঠিকই, তবে হেরমোন পর্বতশ্রেণিতে শীতকালে তুষারপাত ঘটে। এই পর্বতমালা ইসরায়েল, লেবানন ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী সীমান্তে অবস্থিত। উত্তরাঞ্চলীয় এই ভূপ্রকৃতি পাহাড়, বনভূমি, খাল, হ্রদ এবং নদী দ্বারা সমৃদ্ধ। বিশেষত হুলা উপত্যকা ও গ্যালিলি সাগর এলাকা অত্যন্ত সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যে।
উল্লেখযোগ্য একটি নদী হল জর্দান নদী—যা হুলা উপত্যকা থেকে উৎপন্ন হয়ে গ্যালিলি সাগর পেরিয়ে মৃত সাগরে গিয়ে শেষ হয়েছে। এই নদী প্রবাহিত হয়েছে এক গভীর রিফট উপত্যকা দিয়ে, যেটি গ্রেট রিফট ভ্যালির একটি অংশ। এই রিফট উপত্যকা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অত্যন্ত নিচুতে অবস্থিত, আর মৃত সাগর হল পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের সর্বনিম্ন বিন্দু—সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪৩০ মিটার নিচে। মৃত সাগরের লবণাক্ততা এত বেশি যে, এখানে কোনও জীবজন্তু টিকে থাকতে পারে না, তবে পর্যটন এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে এর বিপুল ব্যবহার রয়েছে।
দক্ষিণদিকে আরাভা উপত্যকা নেগেভ মরুভূমিকে বিভক্ত করে রেখেছে এবং এটি ইসরায়েলকে লোহিত সাগরের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। এখানেই অবস্থিত এলাত বন্দর—ইসরায়েলের একমাত্র সমুদ্রবন্দর যেটি ভারত মহাসাগরীয় রুটে পৌঁছাতে সক্ষম। বাণিজ্যিক ও কৌশলগত দিক থেকে এলাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
ভৌগোলিক গঠনের দিক থেকে ইসরায়েলের মরু ও উপত্যকায় ‘মাখতেশ’ নামের এক ধরনের বিরল ভূ-প্রকৃতির দেখা মেলে। এই মাখতেশ এক ধরনের ক্ষয়প্রাপ্ত গিরিখাত বা চক্রাকৃতি গর্ত, যা শুধুমাত্র নেগেভ ও সিনাই উপদ্বীপে দেখা যায়। এর মধ্যে ‘মাখতেশ রামন’ সবচেয়ে বড়—এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৮ কিলোমিটার। একে পৃথিবীর বৃহত্তম ইরোশান ক্রেটার হিসেবে গণ্য করা হয়, যা ভূতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
ইসরায়েলের মোট ভূখণ্ডের আয়তন বিভিন্নভাবে নির্ধারিত। ১৯৪৯ সালের যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুযায়ী, ইসরায়েলের সার্বভৌম ভূখণ্ডের আয়তন প্রায় ২০,৭৭০ বর্গকিলোমিটার। তবে ইসরায়েলি আইন অনুসারে পূর্ব জেরুজালেম ও গোলান মালভূমি যুক্ত করলে এই আয়তন হয় ২২,০৭২ বর্গকিলোমিটার। এর বাইরে ইসরায়েল পশ্চিম তীরের একটি বড় অংশ সামরিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেই এলাকা যোগ করলে ইসরায়েলি নিয়ন্ত্রণাধীন মোট ভূখণ্ডের আয়তন দাঁড়ায় প্রায় ২৭,৭৯৯ বর্গকিলোমিটার।
আয়তনের দিক থেকে দেশটি সরু এবং দীর্ঘ—উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার লম্বা হলেও প্রস্থে সর্বাধিক ১০০ কিলোমিটার। ফলে এর উপকূলীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল বা ‘ইইজেড’ স্থলভাগের দ্বিগুণেরও বেশি বিস্তৃত, এবং মৎস্য, খনিজ ও শক্তি সম্পদের ব্যবহার এই সামুদ্রিক অঞ্চলকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে।
দেশটির এই ছোট ভূখণ্ডে চমৎকার পরিবেশগত বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। এখানে চারটি প্রধান স্থলজ বাস্তুসংস্থান বিদ্যমান—(১) পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় শঙ্কুযুক্ত-স্ক্লেরোফিলাস-বিস্তৃত পাতাবিশিষ্ট বন, (২) দক্ষিণ আনাতোলীয় পার্বত্য শঙ্কুযুক্ত ও পর্ণমোচী বনাঞ্চল, (৩) আরব মরুভূমি, এবং (৪) মেসোপটেমিয়ান ঝোপঝাড় মরু অঞ্চল। এই বৈচিত্র্য দেশের উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতে প্রতিফলিত হয়েছে—ইসরায়েল হল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মধ্যে প্রতি বর্গমিটারে সর্বাধিক উদ্ভিদ প্রজাতির বাসস্থানের দেশ। উদাহরণস্বরূপ, এখানে প্রায় ২,৮০০-এর বেশি দেশীয় উদ্ভিদ প্রজাতির অস্তিত্ব রয়েছে, যার মধ্যে শতাধিক স্থানীয়ভাবে বিপন্ন বা দুর্লভ।
অন্যদিকে, বনায়নের দিক থেকেও ইসরায়েল একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ১৯৪৮ সালে যখন ইসরায়েল রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, তখন দেশের মাত্র ২ শতাংশ অঞ্চল বনভূমি হিসেবে চিহ্নিত ছিল। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, পরিবেশ সচেতনতা এবং ইহুদি জাতীয় তহবিল (Jewish National Fund) দ্বারা পরিচালিত বিপুল বনায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে এই হার ২০১৬ সালের মধ্যে বেড়ে দাঁড়ায় ৮.৫ শতাংশে। বনায়নের মাধ্যমে কেবল জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নয়, বরং কার্বন নিঃসরণ হ্রাস ও আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও কার্যকর প্রভাব পড়েছে।
ইসরায়েলের ভূপ্রকৃতি কেবলমাত্র প্রাকৃতিক পরিবেশই নয়, দেশটির রাজনীতি, কূটনীতি, অর্থনীতি এবং সামরিক কৌশলের দিক থেকেও গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। গোলান মালভূমির মতো ভূখণ্ড কৌশলগতভাবে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সিরিয়ার সঙ্গে এর মালিকানা নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী বিরোধ চলছে। একইভাবে জর্দান উপত্যকা বা পশ্চিম তীর অঞ্চল জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক মহলে বিতর্কিত ও আলোচিত।
এই সমস্ত ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল ইসরায়েলের পানি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার আধুনিকতা। একদিকে এটি মরুভূমির দেশ, অন্যদিকে এর জল ব্যবস্থাপনা এমন উচ্চমানের যে, তা বিশ্বের বহু দেশ অনুসরণ করে। ডেসালিনেশন প্ল্যান্টের মাধ্যমে সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে ব্যবহারোপযোগী করা, পুনর্ব্যবহারযোগ্য জলের পরিমাণ ৮০% ছাড়িয়ে যাওয়া এবং ‘ড্রিপ ইরিগেশন’ প্রযুক্তির আবিষ্কার ইসরায়েলকে জল ব্যবস্থাপনায় বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশে পরিণত করেছে।
ইসরায়েলের ভৌগোলিক অবস্থান একদিকে যেমন তাকে বহু ঐতিহাসিক সংঘর্ষ ও ধর্মীয় রাজনীতির কেন্দ্রে এনে দাঁড় করিয়েছে, অন্যদিকে এ দেশের ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু ও পরিবেশ তাকে এক বৈচিত্র্যপূর্ণ, বহুস্তরীয় রাষ্ট্ররূপে গড়ে তুলেছে। ছোট আয়তনের মধ্যে এত বেশি বৈচিত্র্য, পরিবেশ সচেতনতা এবং বিজ্ঞাননির্ভর অবকাঠামো গড়ে তোলার দৃষ্টান্ত বিশ্বে বিরল।
সবশেষে বলা যায়, ইসরায়েল শুধু একটি রাজনৈতিক সত্তা নয়, বরং এক জৈব-ভৌগোলিক পরীক্ষাগারও বটে, যেখানে সহাবস্থান করে মরু ও জঙ্গল, সমুদ্র ও পাহাড়, কৃষি ও প্রযুক্তি, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং আধুনিক রাষ্ট্রচালনার জটিল প্রক্রিয়া। এই রাষ্ট্র আমাদের শেখায় কীভাবে সীমিত ভূখণ্ড ও বৈরী প্রকৃতি সত্ত্বেও টেকসই উন্নয়ন ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সম্ভব।
টেকটোনিক্স এবং ভূমিকম্প
ভূ-পৃষ্ঠের গঠন ও পরিবর্তনের নিখুঁত নাটকীয়তা মাঝে মাঝেই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমরা এক ক্রমাগত গতিশীল, অস্থির ও বিস্ময়কর গ্রহে বসবাস করছি। সেই নাট্যপ্রবাহের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ইসরায়েল ও জর্ডান উপত্যকা অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস। এই অঞ্চলের একটি বিশাল টেকটোনিক বৈশিষ্ট্য হল জর্ডান রিফট ভ্যালি, যার মধ্যে দিয়ে বইছে বিখ্যাত জর্দান নদী এবং যার মধ্যে লুকিয়ে আছে ভূমিকম্পের এক গভীর, প্রাচীন স্মৃতি। প্রাকৃতিক এই ভূ-রেখাটি শুধুমাত্র মধ্যপ্রাচ্যের নয়, গোটা বিশ্বের অন্যতম সক্রিয় ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলগুলোর একটি, যা প্রতিনিয়ত আমাদের মনে করিয়ে দেয় ভূগোল কেবল মানচিত্রে আঁকা রেখা নয়—তা এক জীবন্ত প্রক্রিয়া।
জর্ডান রিফট ভ্যালি কোনও সাধারণ উপত্যকা নয়, এটি ‘গ্রেট রিফট ভ্যালি’ নামে পরিচিত একটি সুবিশাল ভূ-গঠনিক ব্যবস্থার অংশ, যা পূর্ব আফ্রিকার মোজাম্বিক থেকে শুরু হয়ে লেভান্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই রিফট ভ্যালি গঠিত হয়েছে মূলত টেকটোনিক প্লেটের বিচ্ছিন্নতা ও সেগুলোর অনবরত নড়াচড়ার ফলস্বরূপ। ইসরায়েল ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির ভূতাত্ত্বিক বিন্যাসে এ রকম একটি বড় ধরনের বিচ্ছেদ রেখা বিদ্যমান, যাকে ভূতত্ত্ববিদেরা “ডেড সি ট্রান্সফর্ম” বা DST নামে চিহ্নিত করেছেন।
এই ডিএসটি অঞ্চল আসলে একটি সক্রিয় ট্রান্সফর্ম ফল্ট সিস্টেম, যেখানে আফ্রিকান ও আরব টেকটোনিক প্লেট পরস্পরের পাশ দিয়ে ঘর্ষণের মাধ্যমে সরে যাচ্ছে। এই দুটি প্লেট মুখোমুখি সংঘর্ষে না গিয়ে একে অপরের পাশ দিয়ে সরে যাওয়ার যে প্রবণতা, তা ভূমিকম্প সৃষ্টির জন্য অত্যন্ত অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করে। আফ্রিকান প্লেটটি অবস্থান করছে পশ্চিমে, যার অন্তর্গত অঞ্চলগুলির মধ্যে পড়ে গ্যালিলি, পশ্চিম তীর, উপকূলীয় সমভূমি ও নেগেভ মরুভূমি। অপরদিকে, গোলান হাইটস ও জর্ডান অঞ্চল আরব প্লেটের অংশ। প্লেটগুলির এই ঘর্ষণ, চাপ ও সঞ্চিত শক্তি ভূগর্ভে ক্রমাগত তৈরি করে চলেছে অপূর্ব এক বিপদের ছায়া—এক সম্ভাব্য বড় মাত্রার ভূমিকম্পের আশঙ্কা।
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এই অঞ্চলে বহুবার ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্প ঘটেছে। প্রাচীন যুগ থেকেই ইসরায়েল ও আশেপাশের ভূখণ্ড কম্পনের ভয়াল অভিঘাতে প্রকম্পিত হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ৩১ সালে, এক ভয়াবহ ভূমিকম্পে ইউরোপ-এশিয়ার সংযোগস্থল হিসেবে পরিচিত লেভান্ত অঞ্চলের একাংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এর পরে ৩৬৩ খ্রিস্টাব্দে আরও একটি ভূমিকম্প হয়, যা খ্রিস্টান ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ ওই ভূমিকম্পে জেরুজালেমের পুনর্গঠন প্রকল্প মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।
৭৪৯ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্প ছিল অন্যতম ভয়ংকর। প্রায় ৭.৪ মাত্রার এই ভূকম্পনে জর্দান উপত্যকা জুড়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিধ্বস্ত হয়, বহু শহর ধ্বংস হয়ে যায় এবং হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। বিশেষত তিবেরিয়াস, বেইসান (বর্তমান বেইত শিয়ান), এবং জেরাশ শহর এই ভূমিকম্পে বিপর্যস্ত হয়। ভূতাত্ত্বিক গবেষণায় উঠে এসেছে যে, এই ভূমিকম্প এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, মাটির গঠন কাঠামো পরিবর্তিত হয়ে যায়, নদীর গতিপথ বাঁক নেয়, এমনকি মৃত সাগরের প্রান্তভাগে ভূমির উচ্চতা সাময়িকভাবে পরিবর্তিত হয়।
পরবর্তী এক বড় ভূমিকম্প হয় ১০৩৩ খ্রিস্টাব্দে, যা প্রায় সমানমাত্রার ছিল। এই ভূমিকম্পেরও বিস্তৃত প্রভাব পড়ে গোটা লেভান্ত অঞ্চলে। এত বড় ভূমিকম্প গড়ে প্রতি ৪০০ বছর পরপর এই রিফট অঞ্চলে ঘটে এসেছে বলে পর্যবেক্ষকগণ ধারণা করেন। কিন্তু ছোট ও মাঝারি মানের কম্পন আরও ঘন ঘন ঘটে—গড়ে প্রতি ৮০ বছর অন্তর ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্প আঘাত হানে, যা জনজীবনকে ভয়াবহভাবে প্রভাবিত করে।
আধুনিক ভূতত্ত্বের আলোকে এ অঞ্চলের ভূমিকম্প ঝুঁকি নিছক অনুমান নয়, বরং এক বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা। ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব না হলেও, টেকটোনিক স্ট্রেসের পরিমাণ পরিমাপ করে বিশেষজ্ঞরা বলেন, ইসরায়েল এবং এর আশপাশের ভূগর্ভে ইতিমধ্যেই একটি প্রায় ৭.৪ মাত্রার ভূমিকম্প ঘটানোর মতো শক্তি সঞ্চিত হয়ে আছে। এবং এটি ঘটতে পারে আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই। ভূগর্ভস্থ ফল্ট লাইনে এই সঞ্চিত শক্তি অনিয়মিতভাবে মুক্তি পায়—এটাই ভূমিকম্প। আর যখন এই শক্তি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে, তখন ভূপৃষ্ঠ কেঁপে ওঠে, গগনচুম্বী অট্টালিকা মুহূর্তেই ভেঙে পড়ে, আর জীবন থমকে দাঁড়ায় ধ্বংসস্তূপের নিচে।
ইসরায়েল সরকার এবং বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা দীর্ঘদিন ধরেই ভূমিকম্প প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সচেতন। কঠোর বিল্ডিং কোড চালু করা হয়েছে, নতুন নির্মাণগুলিকে ভূমিকম্প প্রতিরোধী মানদণ্ড পূরণ করতে বাধ্য করা হয়েছে। বিশেষ করে ১৯৮০ সালের পর যেসব ভবন নির্মিত হয়েছে, সেগুলিকে ভূমিকম্প সহনশীল করে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে বাস্তবতা হল, এ পর্যন্ত ইসরায়েলের প্রায় ৫০,০০০ আবাসিক ভবন এবং বহু সরকারি স্থাপনা এখনো এই মানদণ্ড পূরণ করেনি।
২০০৭ সালের এক সমীক্ষা অনুযায়ী, এই পুরনো ভবনগুলোর বেশিরভাগই একমাত্রিক ইট বা কংক্রিট কাঠামোর ওপর নির্ভর করে নির্মিত, যেগুলোর ভিত্তি শক্তিশালী ভূমিকম্প সহ্য করতে সক্ষম নয়। একদিকে যেমন বহু প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থাপনা, তেমনি অন্যদিকে বিভিন্ন হাসপাতাল, স্কুল, প্রশাসনিক ভবন এবং ঘনবসতিপূর্ণ আবাসন প্রকল্প রয়ে গেছে ঝুঁকির মধ্যে। ফলত, একটি মাত্র বড় ভূমিকম্প বহু জীবনহানির পাশাপাশি বিপুল অবকাঠামোগত ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে।
ইসরায়েলের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকার এই ঝুঁকি মোকাবিলায় ‘তামা ৩৮’ নামের একটি প্রকল্প চালু করেছে, যার আওতায় পুরনো ভবনগুলোকে সংস্কার করে ভূমিকম্প প্রতিরোধযোগ্য করে তোলা হচ্ছে। তবুও, কাজের অগ্রগতি ধীর, এবং অনেক এলাকায় বাসিন্দাদের আর্থিক অক্ষমতা কিংবা প্রশাসনিক জটিলতার কারণে সংস্কারকাজ থমকে আছে।
এই সংকটকে আরও গভীর করে তোলে রাজনৈতিক ও সামরিক বাস্তবতা। উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিম তীর ও গোলান হাইটসের অনেক এলাকায় ভূমিকম্প প্রতিরোধী নির্মাণ পরিকল্পনা কার্যকর করা কঠিন, কারণ এই অঞ্চলগুলোর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বিতর্কিত এবং প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান বিচ্ছিন্ন। ফলে এই ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলের জনগণ দ্বিগুণ ঝুঁকিতে বসবাস করছেন—একদিকে রাজনৈতিক সংঘাত, অন্যদিকে ভূপ্রকৃতির অতল শক্তি।
অন্যদিকে, এই ভূ-গঠনের কারণে কিছু উপকারী দিকও রয়েছে। যেমন, জর্ডান রিফট ভ্যালি অঞ্চলে ভূ-তাপীয় শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ ভূগর্ভে উষ্ণ পাথর ও তরল পদার্থের উপস্থিতি এখানে বেশি। যদিও এখনো বাণিজ্যিকভাবে বড় পরিসরে ভূ-তাপীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়নি, গবেষণা ও পরীক্ষামূলক প্রকল্প ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে।
ভূমিকম্প শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, এটি এক সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ও বটে। মধ্যপ্রাচ্যের বহু ঐতিহাসিক শহর, প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান এবং ধর্মীয় নিদর্শন এই ভূমিকম্প ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। একটি বড় ভূমিকম্প মুহূর্তেই বিলীন করে দিতে পারে হাজার হাজার বছরের পুরনো ইতিহাসের নিদর্শন, যা কেবল জাতীয় গর্ব নয়, বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ। ফলে ভূমিকম্প প্রতিরোধ পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এক নতুন মাত্রা—ইতিহাস ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ।
সব মিলিয়ে, জর্ডান রিফট ভ্যালি একটি ভূ-প্রাকৃতিক বিস্ময়, যা একদিকে যেমন মধ্যপ্রাচ্যের ভূমির গঠনকে নির্ধারণ করে, অন্যদিকে সভ্যতার ধারাকেও নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে নিরব জ্যোতিষ্কের মতো। এটি শুধু একটি ভূগর্ভস্থ ফল্ট লাইন নয়, বরং একটি চলমান জৈবভূতাত্ত্বিক প্রবাহ, যা প্রমাণ করে যে, পৃথিবীর ভূগর্ভে আজও সেই আদিম জ্বালাময়ী শক্তি তৎপর রয়েছে, যা গড়ে তোলে পর্বত, সৃষ্টি করে উপত্যকা, আর ধ্বংস করে নগর।
একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে আমরা ভূমিকম্প প্রতিরোধের প্রযুক্তি যতই উন্নত করি না কেন, এই শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তবে প্রস্তুতি, সচেতনতা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা কমাতে পারি ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা এবং ভবিষ্যতের জন্য গড়ে তুলতে পারি এক সুরক্ষিত ও টেকসই বাসযোগ্য বিশ্ব।
জলবায়ু
ইসরায়েলের ভৌগোলিক বৈচিত্র্য যেমন বিস্ময়কর, তেমনি তার জলবায়ুগত অবস্থানও এক অদ্ভুত ভারসাম্যের ইঙ্গিত দেয়। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত এই দেশটি আকারে ছোট হলেও, জলবায়ুর দিক থেকে তা নানা বৈচিত্র্যে পূর্ণ। একই মৌসুমে, মাত্র কয়েক ঘণ্টার দূরত্বে, একপ্রান্তে যখন মরুভূমির দাবদাহ, অন্যপ্রান্তে তখন পর্বতের শীতল হাওয়া ও তুষারের পরশ—এ যেন প্রকৃতির চিত্রপটের এক অভিনব রূপান্তর।
ইসরায়েলের জলবায়ু নির্ধারিত হয়েছে মূলত তার ভৌগোলিক অবস্থানের দ্বারা। দেশটি একদিকে যেমন উষ্ণমণ্ডলীয় বেল্টের অন্তর্গত, অন্যদিকে তা ভূমধ্যসাগরীয় ও মাপান্দ্র অঞ্চলের মাঝামাঝি অবস্থানে। এই মধ্যবর্তী অবস্থান একাধারে চারটি স্বতন্ত্র ফাইটোজিওগ্রাফিক অঞ্চল সৃষ্টি করেছে—যা উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের গঠন ও বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ফলে খুব ছোট এক ভূখণ্ডের মধ্যেও নানা পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য ও বাস্তুসংস্থান গড়ে উঠেছে, যা বিশ্বের আর কোনো দেশের ক্ষেত্রে এত ঘনভাবে বিরল।
উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে যেমন টেল আবিভ, নেতানিয়া ও হাইফা, জলবায়ু প্রধানত ভূমধ্যসাগরীয়। এখানে গ্রীষ্মকাল দীর্ঘ, উষ্ণ ও শুষ্ক হয়—মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টি প্রায় অনুপস্থিত থাকে। শীতকাল তুলনামূলকভাবে মৃদু ও আর্দ্র, এবং এই সময়ে মূলত বর্ষা মৌসুম দেখা যায়। বছরে গড়ে ৫০ থেকে ৬০ দিনের মতো বৃষ্টিপাত হয়, যার বেশিরভাগই হয় অক্টোবর থেকে মার্চের মধ্যে। এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত জলভাণ্ডার ও কৃষিকাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও, মোট পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম—প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ মিমি। তবে উপকূলীয় বাতাস ও সমুদ্রের কাছাকাছি থাকার সুবাদে এখানকার তাপমাত্রা অন্যত্রের তুলনায় কিছুটা নিয়ন্ত্রিত থাকে।
এর বিপরীতে, দক্ষিণের বেয়ারশেবা ও উত্তর নেগেভ অঞ্চলে অর্ধ-মরু জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়। এখানে গ্রীষ্ম অত্যন্ত গরম এবং শুষ্ক, যেখানে দিনের তাপমাত্রা প্রায়শই ৩৫–৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁয়ে যায়। শীতকাল তুলনামূলকভাবে ঠান্ডা ও শুষ্ক এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আরও কম—গড়ে ২০০ থেকে ২৫০ মিমি বার্ষিক। বেয়ারশেবা, যা নেগেভের প্রবেশদ্বার বলা হয়, সেখানে মরুভূমি ও মানববসতির সহাবস্থান এক বিশেষ ভূ-রাজনৈতিক এবং পরিবেশগত নজির।
আরও দক্ষিণে, নেগেভ মরুভূমির গভীর অংশ ও আরাবাহ উপত্যকা (যা লোহিত সাগরের দিকে প্রসারিত) প্রকৃত মরুভূমির জলবায়ু নিয়ে গঠিত। এ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে দিনের তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠতে পারে এবং বাতাস শুষ্ক, ধুলিভরা ও উত্তপ্ত। রাতের তাপমাত্রা দ্রুত নেমে যেতে পারে, যা মরু অঞ্চলের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। শীতকালে এই অঞ্চলে তাপমাত্রা মৃদু থাকে, দিনের বেলায় ১৫–২০ ডিগ্রি এবং রাতে কখনও কখনও ৫ ডিগ্রির নিচে নেমে আসে।
এক সময় বিশ্বের অন্যতম সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ডও গড়েছিল ইসরায়েল। ১৯৪২ সালে, দেশটির উত্তরাঞ্চলের তীরাত জ্ভি কিবুতজে রেকর্ড করা হয়েছিল ৫৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস (১২৯ ডিগ্রি ফারেনহাইট)। যদিও এই রেকর্ডের বৈজ্ঞানিক সত্যতা নিয়ে পরবর্তীতে বিতর্ক হয়েছে, তবুও এটি স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় এই অঞ্চলের চরম জলবায়ু বৈচিত্র্যের প্রতি।
জলবায়ুর একদম বিপরীত ধারা দেখা যায় পর্বতশ্রেণিগুলিতে—বিশেষ করে জেরুজালেম, হেব্রন এবং গালিলির পার্বত্য অঞ্চলে। এই এলাকাগুলির উচ্চতা প্রায়ই ৭৫০ মিটার (২,৪৬০ ফুট) বা তার বেশি। শীতকালে এখানে বাতাস ঠান্ডা ও শুষ্ক হয় এবং প্রতিবছর অন্তত একবার তুষারপাত ঘটে থাকে—বিশেষ করে জেরুজালেম শহরে, যা ধর্ম, ইতিহাস ও আধুনিক নগর উন্নয়নের এক অসাধারণ মিশ্রণ। তুষারপাত, যদিও স্বল্পমেয়াদি, তবুও তার দৃষ্টিনন্দনতা ও আবহাওয়াগত গুরুত্ব দেশটির জলবায়ু বৈচিত্র্যকে আরও গভীর করে তোলে।
জলবায়ু বৈচিত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইসরায়েলের প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎও যথেষ্ট বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধ। এখানে প্রায় ২,৮৬৭ প্রজাতির উদ্ভিদ চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে ২৫৩টি প্রজাতি স্থানীয় নয়, বরং আনা হয়েছে বিদেশ থেকে। এই উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের জন্যই ইসরায়েলকে ‘বায়োডাইভারসিটি হটস্পট’ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এছাড়াও দেশে ৩৮০টিরও বেশি প্রকৃতি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে, যেখানে নানা প্রজাতির পাখি, স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ ও উদ্ভিদ প্রাকৃতিকভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে। এই সংরক্ষণের আওতায় আছে যেমন হুলা ভ্যালির পাখির অভয়ারণ্য, তেমনি গোলান মালভূমির হ্রদ ও জলাভূমি অঞ্চল।
উষ্ণ ও শুষ্ক অঞ্চলে পানির সংকট একটি স্থায়ী বাস্তবতা। এই সমস্যা মোকাবিলায় ইসরায়েল এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন হলো ‘ড্রিপ ইরিগেশন’ বা বিন্দু সেচ পদ্ধতি, যা ১৯৬০-এর দশকে ইসরায়েলেই উদ্ভাবিত হয়েছিল। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে গাছের গোড়ায় সরাসরি সুনির্দিষ্ট পরিমাণে জল পৌঁছে দেওয়া হয়, যাতে জল অপচয় রোধ হয় এবং শুষ্ক মাটিতে ফসল ফলানো সম্ভব হয়। এই প্রযুক্তির ব্যবহারে ইসরায়েল এখন মরুভূমিতেও সবজি, ফল ও ফুল চাষে সক্ষম।
জল সংরক্ষণে আরও একটি বড় বিপ্লব এসেছে সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে ব্যবহারোপযোগী করার মধ্য দিয়ে। দেশটিতে এখন একাধিক ‘ডেসালিনেশন প্লান্ট’ বা লবণমুক্ত জল পরিশোধন কেন্দ্র চালু আছে, যেগুলি দৈনিক লক্ষ লক্ষ কিউবিক মিটার জল উৎপাদন করে। এর ফলে দেশটি তার নগরজীবনের প্রায় ৭০% জল সরবরাহ এই প্রযুক্তির মাধ্যমে মেটাতে সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি, দেশের পুনর্ব্যবহৃত জলের হার ৮০% ছাড়িয়ে গেছে—যা বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ।
এছাড়াও, ইসরায়েল সৌর শক্তির ব্যবহারে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দেশটির অধিকাংশ বাড়িতেই সৌর প্যানেল ব্যবহৃত হয়, বিশেষ করে গরম জল সরবরাহের জন্য। সরকারি নীতিমালার বাধ্যবাধকতায় বহু বছর আগেই সৌর গরম জল সিস্টেম চালু হয়েছে, যার ফলে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে এবং পরিবেশ দূষণও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এর ফলে ইসরায়েল সৌর শক্তির গৃহস্থালী ব্যবহারে বিশ্বে শীর্ষস্থানীয় দেশের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে।
তবে এতসব উন্নয়ন সত্ত্বেও জলবায়ু পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব নিয়ে ইসরায়েল সরকার ও পরিবেশবাদীরা গভীরভাবে চিন্তিত। দেশটির পরিবেশ সুরক্ষা মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে জানিয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সমাজের প্রতিটি স্তরে অনুভূত হবে—বিশেষ করে দরিদ্র ও সংবেদনশীল জনগোষ্ঠীর উপর। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টিপাতের মৌসুমি প্যাটার্ন বদলে যাচ্ছে, গ্রীষ্ম আরও দীর্ঘায়িত হচ্ছে, শীত আরও খরাপ্রবণ হয়ে উঠছে। এসব পরিবর্তনের ফলে জল সরবরাহ, কৃষিকাজ, বনভূমি ও জীববৈচিত্র্য মারাত্মক চাপে পড়ছে।
পরিবেশগত টেকসইতা ও জলবায়ু সহনশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে, ইসরায়েল সরকার বৈজ্ঞানিক গবেষণা, প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। বিশ্বব্যাপী জল সংকটের মোকাবিলায় ইসরায়েলের উদ্ভাবন ও সফলতা আজ অনন্য উদাহরণ হয়ে উঠেছে—মরুভূমিকে চাষযোগ্য করা, সৌর শক্তিকে দৈনন্দিন জীবনে যুক্ত করা এবং জল অপচয় রোধের প্রযুক্তিকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরা একদিকে যেমন বিজ্ঞানপ্রিয়তার প্রমাণ, তেমনি দেশের ভবিষ্যতের জন্য একটি সচেতনতা নির্ভর পথচলার নির্দেশনা।
সব মিলিয়ে, ইসরায়েলের জলবায়ু শুধু তার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ নয়, বরং একটি রাষ্ট্রের পরিবেশ-সচেতন পরিকল্পনা, প্রযুক্তিনির্ভর সমাধান এবং ভবিষ্যতের প্রতিকূলতার মুখোমুখি হওয়ার প্রস্তুতির বহিঃপ্রকাশ। যেখানে অধিকাংশ দেশ আজও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে নীতিগত দ্বিধায়, ইসরায়েল সেখানেই বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ নিয়ে বিশ্বে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।
সরকার এবং রাজনীতি
ইসরায়েল নামক রাষ্ট্রটি, যা মধ্যপ্রাচ্যের কৌশলগত এক কেন্দ্রে অবস্থিত, একদিকে যেমন আধুনিক গণতন্ত্রের রূপকে ধারণ করে, তেমনি তার রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক কাঠামোয় নিহিত রয়েছে একাধিক জটিলতা ও বৈসাদৃশ্য। ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর থেকে ইসরায়েল তার রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে এমন এক অনন্য পথে গড়ে তুলেছে, যা একাধারে ইউরোপীয় সংসদীয় ঐতিহ্য অনুসরণ করে, আবার জাতীয় পরিচয় ও ধর্মীয় চেতনার এক ঘনিষ্ঠ মেলবন্ধনও বহন করে।
ইসরায়েলের শাসনব্যবস্থা একটি সংসদীয় গণতন্ত্র, যেখানে সরকারের প্রধান হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপ্রধান হচ্ছেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতির ভূমিকাটি মূলত আনুষ্ঠানিক এবং তিনি প্রজাতন্ত্রের প্রতীকমাত্র, বাস্তব নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে কেন্দ্রীভূত। প্রতিটি জাতীয় নির্বাচনেই এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যেখানে প্রধান রাজনৈতিক দল বা জোট সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, এবং সেই জোটের নেতা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত হয় মন্ত্রিসভা, যা কার্যত দেশ শাসনের প্রধান যন্ত্র।
ইসরায়েলি সংসদ, ‘কনেসেট’ নামে পরিচিত, এতে ১২০টি আসন রয়েছে। এই কনেসেট সদস্যরা নির্বাচিত হন সম্পূর্ণভাবে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে, যেখানে সমগ্র দেশকে একটিমাত্র নির্বাচনী এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই ব্যবস্থা এমন এক রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যেখানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন কার্যত অসম্ভব এবং জোট সরকার গঠন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ন্যূনতম সীমা বর্তমানে ৩.২৫% ভোট। এই তুলনামূলকভাবে কম সীমা বহু ক্ষুদ্র ও স্বল্পপ্রচলিত দলকে জাতীয় রাজনীতিতে প্রবেশাধিকার দেয়, যার ফলে কনেসেটে রাজনৈতিক বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। তবে একইসঙ্গে, এই বৈচিত্র্য প্রায়শই সরকার গঠনে জটিলতা তৈরি করে এবং সরকারের স্থায়িত্বহীনতা দীর্ঘদিন ধরেই ইসরায়েলি রাজনীতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।
ইসরায়েলের নির্বাচন সাধারণত প্রতি চার বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সরকার পতন কিংবা অনাস্থা ভোটের কারণে অনেক সময় তা নির্ধারিত সময়ের আগেই অনুষ্ঠিত হয়। ফলত গত দুই দশকে ইসরায়েলে গড়ে প্রায় প্রতি দুই থেকে তিন বছরে একবার করে জাতীয় নির্বাচন হয়েছে, যা দেশটির নীতিনির্ধারণে এক ধরনের অনিশ্চয়তা ও বিরতিহীন পরিবর্তনের আবহ তৈরি করেছে।
ইসরায়েলে সংসদীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামোটি একদিকে যেমন গণতান্ত্রিক, অন্যদিকে তা জাতীয় ও ধর্মীয় পরিচয়ের বিশেষ ভার বহন করে। ২০১৮ সালে কনেসেটে পাস হওয়া ‘নেশন-স্টেট ল’ এই দ্বৈত চরিত্রের একটি প্রতীকী প্রকাশ। এই বেসিক ল অনুসারে ইসরায়েল নিজেকে “ইহুদি জনগণের জাতি-রাষ্ট্র” হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে, যেখানে কেবলমাত্র ইহুদিদের জাতীয় আত্মনির্ধারণের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এই আইনে হিব্রু ভাষাকে রাষ্ট্রের একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষিত হয়েছে, যেখানে আরবি ভাষাকে “বিশেষ মর্যাদা” প্রদান করা হয়েছে—যা পূর্বে আরবিকে সমান সরকারি ভাষার মর্যাদা প্রদানকারী আইনকে কার্যত বিলুপ্ত করে দেয়।
‘নেশন-স্টেট ল’-এর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল—ইসরায়েলি ভূখণ্ডে ইহুদি বসতি স্থাপনকে “জাতীয় স্বার্থ” হিসেবে চিহ্নিত করা এবং সরকারকে এই বসতি স্থাপন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য ক্ষমতায়িত করা। এই পদক্ষেপটি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে, বিশেষ করে ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার ও ভূমি দখলের প্রসঙ্গে।
ইসরায়েলের আরেকটি মৌলিক রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য হল তার সংবিধানের অনুপস্থিতি। দেশটিতে আজ পর্যন্ত একটি পূর্ণাঙ্গ লিখিত সংবিধান নেই। এর পরিবর্তে ‘বেসিক ল’ নামের কিছু আইন সংবিধানস্বরূপ কাজ করে। প্রথম ‘বেসিক ল’ গৃহীত হয় ১৯৫৮ সালে, যার পর ধাপে ধাপে একাধিক ‘বেসিক ল’ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইনে রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামো, নাগরিক অধিকার, বিচারব্যবস্থা ও প্রশাসনিক শাখার কার্যাবলি নির্ধারিত হয়েছে। ২০০৩ সালে কনেসেট একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান রচনার কাজ শুরু করলেও রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে এই প্রক্রিয়া আজও অসমাপ্ত রয়েছে। ফলে ‘বেসিক ল’-ই কার্যত দেশের সাংবিধানিক ভিত্তি।
রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েলের প্রকৃত চরিত্র—‘ইহুদি ও গণতান্ত্রিক’—এই দুই শব্দের পারস্পরিক টানাপড়েনে গড়ে উঠেছে এক ধরণের দ্বৈততা, যার ফলে দেশে নাগরিক অধিকারের প্রশ্নটি প্রায়ই বিতর্কের কেন্দ্রে চলে আসে। রাষ্ট্রটি নিজেকে কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা না করলেও, এর ধর্মীয় পরিচয় ও আইনকানুনে ইহুদিধর্মের এক স্পষ্ট প্রতিফলন রয়েছে। নাগরিক বিবাহ ও তালাক, খাদ্য সংক্রান্ত আইন, শাসন ব্যবস্থায় রাব্বিনিক আদালতের উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয় ধর্মীয় বিধানের ওপর নির্ভরশীল। ফলে ধর্মীয় সংখ্যালঘু, বিশেষত মুসলিম ও খ্রিস্টান নাগরিকদের ক্ষেত্রে এই কাঠামো কখনও কখনও বৈষম্যমূলক হয়ে ওঠে।
আরব নাগরিকরা, যারা ইসরায়েলের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০% অংশ, তারা কনেসেট নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার রাখে এবং বহু আরব নেতৃত্বাধীন দল কনেসেটে প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। ১৯৮৮ সালে প্রথম আরব-নেতৃত্বাধীন দল গঠিত হয়। ২০২২ সাল পর্যন্ত আরব দলেরা কনেসেটের প্রায় ১০% আসনে উপস্থিত ছিল, যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার গঠনে এই দলগুলোর ভূমিকা প্রথাগতভাবে সীমিতই থেকে গেছে। তবে ২০২১ সালের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মধ্যে দিয়ে ইসরায়েলের রাজনীতিতে নতুন এক দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়—ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একটি আরব দল সরকার গঠনে জোট অংশীদার হয়, যা ইসরায়েলের বহুত্ববাদী চরিত্রের সম্ভাবনার দিকটি তুলে ধরে।
তবে রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির এই দিকটি সম্পূর্ণ নয়। ইসরায়েলের নির্বাচনী আইনের আওতায়, কোনো দল কনেসেট নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না যদি তার লক্ষ্য বা কার্যক্রম ইসরায়েলকে “ইহুদি জনগণের রাষ্ট্র” হিসেবে স্বীকৃতি না দেয়। এই ধারা কার্যত এমন কিছু দলকে প্রান্তিক করে দেয়, যারা ধর্মনিরপেক্ষ বা জাতিগতভাবে সমতা-ভিত্তিক রাষ্ট্র কাঠামোর পক্ষে। এর ফলে নির্বাচনব্যবস্থার মধ্যেই এক ধরনের আদর্শিক সীমাবদ্ধতা আরোপিত হয়।
রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই ইসরায়েলি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি ও গোষ্ঠীর বৈপরীত্য প্রতিফলিত হয়। যেমন, বসতি স্থাপনকারী ইহুদি জনগণ, যারা পশ্চিম তীরের বিতর্কিত এলাকায় বসবাস করেন, তাঁরাও কনেসেট নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন এবং নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ২০১৫ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, কনেসেটে বসতি স্থাপনকারী প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ১০ জন—যা মোট সদস্যসংখ্যার ৮%। এই প্রতিনিধিরা প্রায়শই রাজনৈতিকভাবে কট্টর দক্ষিণপন্থী এবং পশ্চিম তীর দখল বজায় রাখার পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন, যা ফিলিস্তিনি-ইসরায়েলি দ্বন্দ্বের এক গভীর মাত্রা।
এই রাজনৈতিক কাঠামোর আরও একটি চ্যালেঞ্জ হল—নিয়মিত জোট সরকার গঠন এবং তার ভঙ্গুরতা। ইসরায়েলে রাজনৈতিক দলগুলোর পরস্পরবিরোধী আদর্শ ও ধর্মনিরপেক্ষ বনাম ধর্মীয় মতাদর্শের সংঘাত প্রায়শই জোট সরকার গঠনে জটিলতা তৈরি করে। একেকটি সরকার টিকতে টিকতে হোঁচট খায়, মন্ত্রীসভা ভাঙে, আর পরবর্তী নির্বাচনের সঙ্কেত এসে হাজির হয়। এই ধারা ইসরায়েলের রাজনৈতিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী হলেও, তা গণতন্ত্রের এক অতিশয় সজাগ রূপকেই প্রকাশ করে—যেখানে একনায়কত্বের অবকাশ নেই, তবে স্থায়িত্বও অনেক সময়ে প্রশ্নবিদ্ধ।
এই সবকিছুর মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে এক বহুমাত্রিক, জটিল এবং প্রায়শই বিতর্কিত রাজনৈতিক বাস্তবতা—যেখানে ইসরায়েল একাধারে একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, আবার ধর্মীয় রাষ্ট্রতত্ত্বে নিবদ্ধ জাতিগত জাতিরাষ্ট্রের ধারণাতেও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। এই দ্বৈত পরিচয় তার রাজনীতি, আইন, সমাজ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রতিটি স্তরে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।
ইসরায়েলের জেলা
ইসরায়েলের প্রশাসনিক কাঠামো একটি সুসংবদ্ধ ও বহুস্তরীয় পদ্ধতির অনুসরণে গঠিত, যেখানে প্রাথমিক স্তরে ছয়টি প্রধান জেলা বা “মেহজোত” (מְחוֹזוֹת; একবচন: מָחוֹז) রয়েছে। এই হিব্রু পরিভাষা আরবি ভাষায় পরিচিত “মিনতাকাহ” নামে। প্রতিটি জেলা ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি মৌলিক কাঠামো হিসেবে কাজ করে। কিন্তু শুধু জেলাগুলির মধ্যেই থেমে থাকে না এই বিভাজন—এই ছয়টি জেলার অধীনে রয়েছে আরও পনেরোটি উপজেলা, যেগুলোকে বলা হয় “নাফোত” (נָפוֹת; একবচন: נָפָה)। এই উপ-জেলাগুলি আবার শহর, পৌরসভা এবং আঞ্চলিক কাউন্সিলের ভিত্তিতে ভাগ করা হয়েছে, ফলে একটি বহুস্তরীয় স্থানিক প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে উঠেছে।
ইসরায়েলের এই প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের জনসংখ্যার ঘনত্ব, সামাজিক বৈশিষ্ট্য এবং রাজনৈতিক সংবেদনশীলতা লক্ষণীয়। যদিও পরিসংখ্যানের সূত্র হিসেবে ইসরায়েলের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো নির্ভরযোগ্য ও নিরীক্ষিত তথ্য সরবরাহ করে থাকে, তথাপি এই পরিসংখ্যানগুলোকে পুরোপুরি রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ বলা যায় না, কারণ ইসরায়েল অধিকৃত কিছু অঞ্চলকেও এই পরিসংখ্যানে অন্তর্ভুক্ত করে, যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নয়। যেমন, গোলান মালভূমির গোলান উপজেলা এবং এর চারটি প্রাকৃতিক অঞ্চল ইসরায়েলের বেসামরিক শাসনের আওতাভুক্ত থাকলেও জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তা ইসরায়েলের ভূখণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। তবু, ইসরায়েলি প্রশাসনিক কাঠামোতে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে এবং নিয়মিত পরিসংখ্যান প্রদান করা হয়।
একইভাবে, জেরুসালেম জেলা নিয়ে একটি জটিলতা রয়েছে। এই জেলার পরিসংখ্যানে পূর্ব জেরুসালেমকেও ধরা হয়েছে, যা ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধের পর ইসরায়েল দখল করে নেয়। জাতিসংঘ এবং অধিকাংশ আন্তর্জাতিক সংগঠন ও রাষ্ট্র পূর্ব জেরুসালেমকে দখলকৃত এলাকা হিসেবে বিবেচনা করে, এবং সেখানে ইসরায়েলি সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দেয় না। তবে ইসরায়েল রাষ্ট্র তার রাজধানী হিসেবে পুরো জেরুসালেমকে বিবেচনা করে, ফলে প্রশাসনিক কাঠামোর অংশ হিসেবেও পূর্ব জেরুসালেম সেখানে স্থান পেয়েছে।
জুডেয়া ও সামেরিয়া অঞ্চল (অর্থাৎ পশ্চিম তীরের একটি অংশ) ইসরায়েলি প্রশাসনিক বিভাজনের একটি ব্যতিক্রম। যদিও এই অঞ্চল ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর থেকে কার্যত ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, তবু এখানে সরাসরি বেসামরিক প্রশাসনিক শাসন প্রয়োগ করা হয়নি। তাই জেলা ও উপজেলার পরিসংখ্যানে এই অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। ফলে একে একধরনের প্রশাসনিক সীমানার বাইরে রাখা হয়েছে। তা সত্ত্বেও, কিছু কিছু পৌর এলাকা ও ইহুদি বসতি, যেগুলো ইসরায়েল দ্বারা স্থাপিত, সেগুলো আংশিকভাবে ইসরায়েলি শাসনের আওতায় থেকে যায়।
এই বিস্তৃত প্রশাসনিক কাঠামো ইসরায়েলের জনসংখ্যার বৈচিত্র্য ও ভৌগোলিক জটিলতাকে প্রতিফলিত করে। উপকূলবর্তী তেল আভিভ এবং হাইফা জেলার ঘনবসতিপূর্ণ আরব ও ইহুদি জনবসতির পাশাপাশি, দক্ষিণে বিস্তৃত নেগেভ মরুভূমির বিশাল এলাকা অপেক্ষাকৃত কম জনবসতির হলেও প্রশাসনিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত। আবার, জেরুসালেম জেলার মতো সংবেদনশীল এলাকায় ইহুদি ও আরব জনসংখ্যার অনুপাত রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।
অতএব, ইসরায়েলের জেলা ও উপজেলা কাঠামো শুধুমাত্র প্রশাসনিক কার্যকারিতা নয়, বরং রাজনৈতিক বাস্তবতা, জনসংখ্যাগত রূপান্তর এবং আঞ্চলিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যের প্রতিফলন হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে। এই কাঠামোর মধ্যে নিহিত রয়েছে এমন এক বাস্তবতা, যেখানে ভূগোল, জনসংখ্যা এবং রাজনীতি একে অপরকে আচ্ছন্ন করে থাকে।
জেরুসালেম জেলা ইসরায়েলের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল প্রশাসনিক অঞ্চল, যার তাৎপর্য শুধু প্রশাসনিক পর্যায়েই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা জাতীয় পরিচয়, ধর্মীয় প্রতীকীতা ও আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক টানাপোড়েনের প্রতীকও বটে। হিব্রু ভাষায় এই জেলাকে বলা হয় “মেহোয ইয়েরুশালাইম” (מְחוֹז יְרוּשָׁלַיִם)। প্রাচীন ইতিহাস, ধর্মীয় স্থাপত্য এবং আধুনিক নগর জীবনের মেলবন্ধনে এই জেলা আজ বৈশ্বিকভাবে আলোচিত এক ভূখণ্ড।
এই জেলার সর্ববৃহৎ ও প্রশাসনিক কেন্দ্র জেরুসালেম শহর, যা ইসরায়েল রাষ্ট্রের ঘোষণা অনুযায়ী রাজধানী হলেও, আন্তর্জাতিকভাবে এই দাবির স্বীকৃতি বিভাজিত। জেরুসালেম শহর পূর্ব ও পশ্চিম অংশে বিভক্ত। পশ্চিম জেরুসালেম ১৯৪৮ সাল থেকেই ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু পূর্ব জেরুসালেম ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধের পরে ইসরায়েল দখল করে এবং একতরফাভাবে তা নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করে। এই অন্তর্ভুক্তিকে অধিকাংশ আন্তর্জাতিক সংস্থা ও রাষ্ট্র এখনও স্বীকৃতি দেয়নি।
জনসংখ্যার বিচারে, এই জেলায় বসবাসকারী মানুষের মধ্যে প্রায় ৬৫.৫ শতাংশ ইহুদি এবং ৩২.৮ শতাংশ আরব, যার মধ্যে অধিকাংশ ফিলিস্তিনি মুসলমান ও খ্রিস্টান। এই অনুপাত ইসরায়েলের অন্যান্য জেলার তুলনায় অনন্য। শুধু সংখ্যার দিক থেকে নয়, এই জনসংখ্যাগত বৈচিত্র্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে গভীর প্রভাব ফেলে। গোটা ইসরায়েলের আরব জনগোষ্ঠীর প্রায় ২১ শতাংশ এই জেলা কেন্দ্রীভূত—যা এই অঞ্চলকে ধর্মীয়, জাতিগত ও ভাষাগত বৈচিত্র্যের এক দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরে।
২০১৬ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, জেলাটির জনসংখ্যা ছিল আনুমানিক ১০ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩০০ জন। এর পরিসরও অন্যান্য অনেক জেলার তুলনায় তুলনামূলকভাবে কম—মোট আয়তন প্রায় ৬৫৩ বর্গ কিলোমিটার বা ২৫২ বর্গমাইল। এই ছোট ভূখণ্ডে গঠিত হয়েছে অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ ও রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর এক পরিবেশ, যেখানে ইতিহাস ও আধুনিকতা একসঙ্গে সহাবস্থান করে।
জেলার প্রশাসনিক কাঠামো অনুযায়ী, এখানে রয়েছে ২টি স্বীকৃত শহর, ৩টি স্থানীয় কাউন্সিল এবং একটি আঞ্চলিক কাউন্সিল। এই কাঠামোর মধ্য দিয়ে প্রশাসনিক দায়িত্বগুলি ভাগ করা হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করা হয়। বিশেষ করে পূর্ব জেরুসালেমে বসবাসকারী ফিলিস্তিনি বাসিন্দাদের সামাজিক সেবা, নাগরিক অধিকার এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রশ্নে নানা বিতর্ক ও অসংগতি দেখা যায়।
জেরুসালেম জেলা শুধুমাত্র প্রশাসনিক শ্রেণিবিভাগে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা ইসরায়েল-ফিলিস্তিন দ্বন্দ্বের কেন্দ্রস্থল। এখানে প্রতিটি এলাকাই বহুস্তরীয় ইতিহাসের বাহক—চwhether তা ওল্ড সিটির প্রাচীরঘেরা প্রাচীন মসজিদ, চার্চ ও সিনাগগ, কিংবা আধুনিক পশ্চিম জেরুসালেমের ব্যবসায়িক ভবন ও হাই-টেক অফিস। এই জেলার প্রতিটি ইঞ্চি ভূমি ধর্মীয় আবেগ, রাজনৈতিক দাবি ও কূটনৈতিক কৌশলের জটিল সংমিশ্রণ।
বিশ্বজুড়ে ইহুদি, মুসলিম ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের কাছে পবিত্র নগরী হিসেবে পরিচিত জেরুসালেম শহরের অবস্থান এই জেলাকেই ইসরায়েলের অন্যান্য জেলার চেয়ে একধরনের ভিন্নতর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। এখানেই অবস্থিত আল-আকসা মসজিদ, পশ্চিম প্রাচীর (ওয়েস্টার্ন ওয়াল), গির্জা অফ দ্য হোলি সেপালকার ইত্যাদি ধর্মীয় গুরুত্বসম্পন্ন স্থান, যা হাজার হাজার বছর ধরে তীর্থযাত্রা ও রাজনৈতিক সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু।
জেলাটির ভৌগোলিক বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। পর্বতবেষ্টিত এই অঞ্চল গ্রীষ্মে গরম ও শীতে ঠান্ডা জলবায়ুর অভিজ্ঞতা দেয়। শীতকালে এখানে মাঝে মাঝে তুষারপাতও হয়, বিশেষত উচ্চভূমির অংশে। যদিও এর আয়তন ছোট, তথাপি জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং ভূমির ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় গুরুত্বের কারণে এটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।
জেনেরালি বিল্ডিং, যা ঐতিহাসিকভাবে ব্রিটিশ শাসনামলে গড়ে উঠেছিল, দীর্ঘদিন জেরুসালেম জেলা প্রশাসনের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি শহরের প্রশাসনিক ইতিহাসের অংশ হয়ে উঠেছে।
অতএব, জেরুসালেম জেলা কেবলমাত্র সংখ্যাগত বা ভৌগোলিক বিবরণে ধরা যায় না; এটি একটি জীবন্ত ও রাজনৈতিকভাবে পরিপুষ্ট অঞ্চল, যার প্রতিটি উপাদান বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়। এখানকার জনসংখ্যা, ভূপ্রকৃতি, প্রশাসনিক গঠন ও রাজনৈতিক পরিবেশের প্রতিটি উপাদান ইসরায়েল রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এক জটিল প্রেক্ষাপট নির্মাণ করে। ফলে, জেরুসালেম জেলা হলো সেই স্পর্শকাতর কেন্দ্র, যেখান থেকে বারবার ইতিহাস রচিত হয়েছে, এবং সম্ভবত ভবিষ্যতের অনেক সংঘর্ষ ও সমঝোতার বীজও এখানেই নিহিত।
উত্তর জেলা
উত্তর ইসরায়েল, যা হিব্রু ভাষায় মেহোয হাতসাফোন (מְחוֹז הַצָּפוּן) নামে পরিচিত, ভূগোল, জনসংখ্যা এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের এক অনন্য সংমিশ্রণ। এই জেলা শুধুমাত্র ভৌগোলিক বিস্তৃতির দিক থেকেই বৃহৎ নয়, বরং সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এটি বহুমাত্রিক। গালিল এলাকার বিস্তৃত উপত্যকা, গ্রীষ্মে সবুজে ছেয়ে যাওয়া পাহাড়, আর ঐতিহাসিক প্রাচীন শহরগুলির সহাবস্থান এই জেলাকে অন্য জেলাগুলোর তুলনায় এক স্বতন্ত্র চরিত্র দিয়েছে।
জেলার প্রশাসনিক রাজধানী নফ হাগালিল, যা পূর্বে “নাজারেথ ইলিট” নামে পরিচিত ছিল, ইসরায়েলের একটি পরিকল্পিত শহর। এটি নাজারেথ শহরের উত্তরে অবস্থিত। এই রাজধানী শহরটি আধুনিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে গড়ে উঠলেও, তার প্রতিবেশী নাজারেথ হচ্ছে একটি অত্যন্ত প্রাচীন শহর, খ্রিস্টধর্মের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এখানে খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী যিশুখ্রিস্ট তাঁর শৈশবকাল কাটিয়েছিলেন।
এই জেলার একটি বৈশিষ্ট্য হল তার জনসংখ্যাগত বৈচিত্র্য। ২০১৮ সালের তথ্য অনুযায়ী, এখানে আনুমানিক ১৪ লক্ষ ৪৮ হাজারেরও বেশি মানুষ বসবাস করেন। এর মধ্যে ৫৩.৭ শতাংশ আরব এবং প্রায় ৪৩.১ শতাংশ ইহুদি। এই অনুপাত ইসরায়েলের অন্যান্য জেলার তুলনায় একটি ব্যতিক্রমী বৈচিত্র্য তুলে ধরে। আরব জনগোষ্ঠীর মধ্যে মুসলিম, খ্রিস্টান এবং দ্রুজ সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছেন, যারা যুগ যুগ ধরে এই অঞ্চলে সহাবস্থান করে আসছেন।
উত্তর জেলায় মোট ১৭টি শহর, ৬১টি স্থানীয় কাউন্সিল এবং ১৫টি আঞ্চলিক কাউন্সিল রয়েছে। এই বিস্তৃত প্রশাসনিক কাঠামো এখানকার জনগণের নাগরিক পরিষেবা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই শহরগুলির মধ্যে কিছু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ তারা শুধু আধুনিক জনবসতি নয়, বরং ইতিহাস, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক সম্পদের আধার।
উপজেলা পর্যায়ে কয়েকটি এলাকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:
ত্সফাত (সাফেদ): প্রায় ১ লক্ষ ২১ হাজারেরও বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট এই শহরটি কাব্বালাহ বা ইহুদি গূঢ়তত্ত্ব চর্চার এক ঐতিহাসিক কেন্দ্র। এখানকার সংকীর্ণ গলি, নীল রঙে রাঙানো বাড়ি এবং ঐতিহাসিক সিনাগগগুলো আজও বহু দর্শনার্থী ও তীর্থযাত্রীকে আকর্ষণ করে।
কিনারেত: এই অঞ্চলের জনসংখ্যা ১ লক্ষ ১২ হাজারের কাছাকাছি। এটি তিবেরিয়াস ও গ্যালিলি সাগরের আশেপাশের এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা বাইবেলীয় ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। গ্যালিলি হ্রদ কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য নয়, খ্রিস্টান ধর্মের প্রেক্ষাপটেও এক ঐতিহাসিক মর্যাদা রাখে।
ইজরেএল উপত্যকা: এখানে জনসংখ্যা ৫ লক্ষ ২০ হাজারেরও বেশি। ইজরেএল উপত্যকা ইসরায়েলের অন্যতম উর্বর অঞ্চল হিসেবে পরিচিত এবং বহু প্রাচীন যুদ্ধ ও সভ্যতার কেন্দ্র। আজও এই অঞ্চল কৃষিকাজ এবং আঞ্চলিক উৎপাদনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
আক (অক্রা): এই শহরের জনসংখ্যা ৬ লক্ষ ৪৩ হাজারের মতো এবং এটি প্রাচীন রোমান, ক্রুসেডার ও উসমানীয় স্থাপত্যের সমৃদ্ধ এক শহর। ইউনেস্কো ঘোষিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট এই শহরের পুরনো অংশ আজও ইতিহাসপ্রেমীদের এক বিশেষ গন্তব্য।
গোলান অঞ্চল: প্রায় ৫০ হাজার ৬০০ জনসংখ্যা বিশিষ্ট এই অঞ্চল রাজনৈতিক দিক থেকেও বিতর্কিত। ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধের পর ইসরায়েল সিরিয়া থেকে এই অঞ্চলটি দখল করে। যদিও আন্তর্জাতিকভাবে এটির ইসরায়েলি অধিভুক্তি স্বীকৃত নয়, তবুও এটি ইসরায়েলি প্রশাসনিক কাঠামোর অন্তর্গত।
উত্তর জেলা শুধু শহর ও জনসংখ্যার সংখ্যা দিয়ে বিচার করা যায় না। এটি একটি সাংস্কৃতিক মোজাইক যেখানে আরব এবং ইহুদি সম্প্রদায় একে অপরের প্রতিবেশী হয়ে বেঁচে আছে—কখনও বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান, আবার কখনও উত্তেজনার ইতিহাস নিয়ে। ভাষা, ধর্ম, উৎসব, পোশাক ও খাদ্যাভ্যাসে এখানে যে বৈচিত্র্য দেখা যায়, তা শুধু ইসরায়েল নয়, গোটা পশ্চিম এশিয়ার বৃহত্তর সাংস্কৃতিক প্রবাহের অংশ।
জেলাটির ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যও এর প্রাণবন্ত বৈচিত্র্যকে প্রতিফলিত করে। গ্যালিলি পাহাড় থেকে শুরু করে হুলা উপত্যকা এবং গলান মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে রয়েছে উপত্যকা, বনাঞ্চল, কৃষিভূমি এবং জলাশয়। এখানকার জলবায়ু ভূমধ্যসাগরীয়, যার ফলে শীতকাল তুলনামূলকভাবে মৃদু এবং বৃষ্টিপূর্ণ, আর গ্রীষ্মকাল গরম ও শুষ্ক।
এই জেলার কৌশলগত গুরুত্বও কম নয়। লেবাননের সীমান্তের কাছাকাছি হওয়ায় এই অঞ্চল প্রায়শই নিরাপত্তাজনিত উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এখানকার অবকাঠামো উন্নয়ন, পর্যটন এবং কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার ইসরায়েলি অর্থনীতিতে এ জেলার ভূমিকা আরও দৃঢ় করেছে।
অতএব, উত্তর জেলা শুধুমাত্র একটি প্রশাসনিক একক নয়, বরং তা ইসরায়েলের মধ্যে একটি মিনি-ইসরায়েল—যেখানে ইতিহাস, ধর্ম, ভূগোল এবং জনসমাজের বিচিত্র পরতগুলি একসূত্রে গাঁথা। এই জেলার ভবিষ্যৎ যে শুধু কাগজে আঁকা প্রশাসনিক সীমানায় নয়, বরং আন্তঃসম্পর্ক, বোঝাপড়া এবং ঐতিহাসিক সচেতনতার ওপর নির্ভর করছে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।
হাইফা জেলা
হাইফা জেলা, হিব্রু ভাষায় যাকে বলা হয় “মেহোজ হেইফা” (מְחוֹז חֵיפָה), ইসরায়েলের প্রশাসনিক মানচিত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ও স্বতন্ত্র অঞ্চল। ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত এই জেলার ভূপ্রকৃতি যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনি জনসংখ্যা ও সংস্কৃতির দিক থেকেও এটি অনেক রঙে রঙিন। ইহুদি সংখ্যাগরিষ্ঠতার পাশাপাশি এখানে আরব সম্প্রদায়ের একটি দৃশ্যমান ও সক্রিয় উপস্থিতি রয়েছে, যা জেলার সামাজিক কাঠামোকে বহুমাত্রিক ও সমন্বিত করে তুলেছে।
২০১৬ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, হাইফা জেলার প্রায় ৬৯.৭ শতাংশ বাসিন্দা ইহুদি এবং ২৫.১ শতাংশ আরব। এই অনুপাত শুধু সংখ্যার দিক থেকে নয়, বরং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও সামাজিক বাস্তবতার একটি চিত্রও তুলে ধরে। এখানকার ইহুদি জনগোষ্ঠীর মধ্যে যেমন ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মপরায়ণ উভয় ধরনের লোক রয়েছে, তেমনি আরব সম্প্রদায়ের মধ্যে মুসলমান, খ্রিস্টান ও দ্রুজদের বাস রয়েছে, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই উপকূলীয় ভূমিতে সহাবস্থান করে এসেছে।
জেলার মোট জনসংখ্যা ২০১৮ সালের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ১০ লক্ষ ৩২ হাজার ৮০০ জন। তুলনামূলকভাবে ছোট—মোট মাত্র ৮৬৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে গঠিত এই জেলা, ঘনবসতির এক চমৎকার উদাহরণ। এখানে নগর উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অনন্য মেলবন্ধন দেখা যায়, বিশেষ করে হাইফা শহরের পাহাড়ি ভূপ্রকৃতি, সমুদ্রতীরবর্তী উপসাগর ও শিল্পাঞ্চলের যুগলবন্দীতে।
হাইফা জেলার প্রশাসনিক রাজধানী হল হাইফা শহর নিজেই। প্রায় ৫ লক্ষ ৮৩ হাজার ৪০০ জন মানুষ এই শহরে বসবাস করে, যা এই জেলায় জনসংখ্যার একটি বড় অংশ জুড়ে। হাইফা শহর শুধু একটি প্রশাসনিক কেন্দ্রই নয়, বরং ইসরায়েলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বন্দরনগরী, শিল্প ও প্রযুক্তির কেন্দ্র এবং একাডেমিক চর্চার এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। টেকনিয়ন – ইসরায়েল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি এবং হাইফা বিশ্ববিদ্যালয়, এই শহরের বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হিসেবে বিশ্বজুড়ে খ্যাতি অর্জন করেছে।
এছাড়াও, হাইফার উল্লেখযোগ্য একটি বৈশিষ্ট্য হল এখানকার বহুধর্মীয় সহাবস্থান। হাইফা শহরকে প্রায়শই “সহাবস্থানের প্রতীক” বলে অভিহিত করা হয়, কারণ এখানে ইহুদি, মুসলমান, খ্রিস্টান ও বাহাই ধর্মাবলম্বীরা যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি বসবাস করে এসেছে। বাহাই ধর্মের প্রধান উপাসনালয় ও আন্তর্জাতিক কেন্দ্র, “বাহাই গার্ডেনস”, এই শহরের গর্ব ও বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ।
দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর হল হাদেরা, যার জনসংখ্যা ৪ লক্ষ ৪৯ হাজার ৩০০ জনের কাছাকাছি। এটি একদিকে কৃষিকাজনির্ভর অঞ্চল হিসেবে পরিচিত ছিল, কিন্তু সাম্প্রতিক দশকে এখানে শিল্প, প্রযুক্তি এবং আবাসিক উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যাপক রূপান্তর হয়েছে। হাদেরা শহরের উল্লেখযোগ্য দিক হল এখানকার পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং শহরের কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক এলাকা, যা আশপাশের উপশহরগুলির জন্যও একটি কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে।
জেলাটির প্রশাসনিক কাঠামো মোট ১১টি শহর, ১৪টি স্থানীয় কাউন্সিল এবং ৪টি আঞ্চলিক কাউন্সিলে বিভক্ত। এই বিন্যাসটি জেলা জুড়ে বসবাসরত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নাগরিক পরিষেবা, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ও পরিবহন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
ভূগোলগতভাবে, হাইফা জেলা পাহাড়, উপকূল ও সমতলের সম্মিলন। কারমেল পর্বতমালা এখানকার একটি প্রভাবশালী ভূপ্রকৃতি, যা সমুদ্র থেকে উঠে এসে শহরের ওপর ছায়া ফেলে। এই পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়ে উঠেছে আবাসিক এলাকা, বাণিজ্যিক কেন্দ্র এবং ধর্মীয় স্থাপনা। হাইফা বন্দর ও ইসরায়েলের জাতীয় নৌপরিবহণের একটি মূল কেন্দ্র এই জেলার অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।
জেলাটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, এখানে বহু আরব গ্রাম ও শহরও রয়েছে যেগুলিতে বহু শতাব্দী ধরে আরব পরিবারগুলি বসবাস করে আসছে। এই গ্রামগুলিতে স্থানীয় আরবি ভাষা, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য এখনও সক্রিয় ও জীবন্ত। তবে, এই আরব জনগোষ্ঠী ইসরায়েলের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে অসাম্য নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করে আসছে।
হাইফা জেলার অর্থনীতিতে শিল্প ও পরিষেবা খাত ছাড়াও উচ্চপ্রযুক্তি খাতের অবদান ক্রমাগত বাড়ছে। এখানে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি কোম্পানির অফিস রয়েছে, এবং ইসরায়েলের “সিলিকন উপত্যকা” খ্যাত হাই-টেক করিডোরের অংশ হিসেবেও হাইফা শহর পরিচিত হয়ে উঠেছে। তেল ও রাসায়নিক শিল্পেও এই জেলায় বড় কারখানা রয়েছে, বিশেষ করে হাইফা বে অঞ্চলে, যদিও তা পরিবেশগত প্রশ্ন ও স্বাস্থ্যগত উদ্বেগও তৈরি করে।
পরিবেশ সচেতনতা এই জেলায় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। হাইফা অঞ্চলে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও শিল্প-নগরীর পরিবেশ বান্ধব রূপান্তরের জন্য নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রশাসন, নাগরিক সমাজ ও পরিবেশবাদী সংগঠনগুলোর সক্রিয়তায় জেলাটি পরিবেশ-সহিষ্ণু নগর গঠনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।
এই জেলায় ধর্মীয় উৎসব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও শিল্পচর্চাও সমানভাবে সক্রিয়। হাইফা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, বাহাই ওয়াল্ড সেন্টার-কে কেন্দ্র করে বহু আন্তর্জাতিক পর্যটকের আগমন, এবং শহরের নাট্য, সঙ্গীত ও সাহিত্যচর্চার ঐতিহ্য জেলার সাংস্কৃতিক পরিচিতিকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।
এইভাবে হাইফা জেলা ইসরায়েলের প্রশাসনিক মানচিত্রে শুধু একটি নামমাত্র অঞ্চল নয়, বরং তা একটি চলমান জীবন্ত উদাহরণ—যেখানে ইতিহাস ও আধুনিকতা, ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতা, প্রযুক্তি ও পরিবেশ-সচেতনতা, আরব ও ইহুদি সমাজের সহাবস্থান একসঙ্গে মিশে একটি জটিল অথচ গতিশীল বাস্তবতা সৃষ্টি করেছে। এই জেলার ভবিষ্যৎ কেবল অবকাঠামোর উন্নয়ন বা জনসংখ্যার পরিসংখ্যানে নয়, বরং সামাজিক ন্যায়, বহুসাংস্কৃতিক বোঝাপড়া এবং সমন্বিত উন্নয়ননীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নে নিহিত।
মধ্য জেলা
মধ্য ইসরায়েল, হিব্রু ভাষায় যার নাম “মেহোজ হামেরকায” (מְחוֹז הַמֶּרְכָּז), দেশের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক অঞ্চল। রাজধানী রামলাকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত এই জেলা বিভিন্ন দিক থেকে ইসরায়েলের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও জনতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যের এক সমৃদ্ধ প্রতিচ্ছবি।
২০১৮ সালের ইসরায়েলি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২১ লক্ষ ৯৬ হাজার ১০০ জন। প্রায় ১,২৯৪ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত এই এলাকা ইসরায়েলের অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ অংশগুলোর একটি। জনসংখ্যার গঠনে একটি চমকপ্রদ বৈসাদৃশ্য দেখা যায়—প্রায় ৮৮ শতাংশ বাসিন্দা আরব এবং মাত্র ৮.২ শতাংশ ইহুদি। এই সংখ্যা ইঙ্গিত দেয় যে, জাতিগত-ধর্মীয় বৈচিত্র্য ও সামাজিক সহাবস্থান এই জেলার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।
প্রশাসনিক কাঠামোর দিক থেকে মধ্য জেলা যথেষ্ট জটিল ও বিস্তৃত। এখানে মোট ১৮টি শহর, ২২টি স্থানীয় কাউন্সিল এবং ১২টি আঞ্চলিক কাউন্সিল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রতিটি স্তরেই রয়েছে পৃথক প্রশাসনিক কার্যপরিধি, যা স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন, নাগরিক পরিষেবা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
জেলার প্রশাসনিক কেন্দ্র রামলা একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক শহর, যার শিকড় খ্রিস্টপূর্ব যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। রামলা শুধুমাত্র একটি সরকারি প্রশাসনিক কেন্দ্র নয়, বরং একটি সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবেও পরিচিত। এখানে বহু ঐতিহাসিক মসজিদ, গির্জা এবং পুরাতন বাজার এখনো সংরক্ষিত অবস্থায় আছে, যা শহরটির ঐতিহাসিক গৌরব বহন করে চলেছে।
এই জেলার মধ্যে “পেতা তিকভা” একটি আধুনিক ও ঘনবসতিপূর্ণ শহর, যা “ইসরায়েলের মাতৃনগরী” বলেও পরিচিত। কৃষিনির্ভর বসতি হিসেবে এর সূচনা হলেও আজ এটি একটি শিল্প, প্রযুক্তি ও স্বাস্থ্যসেবার কেন্দ্র। বহু নামকরা হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রযুক্তি কোম্পানি এই শহরের গর্ব। জনসংখ্যায় এটি জেলার বৃহত্তম শহরগুলোর মধ্যে পড়ে, যদিও সুনির্দিষ্ট সংখ্যাটি সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে থাকে।
“রেহোভত” শহরটি ইসরায়েলের বৈজ্ঞানিক গবেষণার এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এখানেই অবস্থিত বিখ্যাত “ওয়েইজমান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স”, যা ইসরায়েল তো বটেই, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে খ্যাত। এই শহরের সাংস্কৃতিক আবহও জোরালো এবং স্থানীয় আরব ও ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে শৈল্পিক ও সামাজিক আদান-প্রদান এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বাস্তবতা।
“শারন” নামটি আসলে একটি প্রাকৃতিক অঞ্চলকেও নির্দেশ করে, যেখানে বেশ কয়েকটি ছোট ও মাঝারি শহর, কৃষি অঞ্চল এবং আধুনিক বসতি গড়ে উঠেছে। এই এলাকা কৃষি, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং আবাসন খাতে গত দুই দশকে বিস্তর উন্নয়ন দেখেছে। এখানে সবুজ খোলা মাঠ, অরেঞ্জ গ্রোভ এবং ছোট নদী উপত্যকার প্রাচুর্য রয়েছে, যা অঞ্চলটির ভূপ্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বাসযোগ্যতা বাড়িয়ে দিয়েছে।
মধ্য জেলার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এর অবকাঠামোগত সংযুক্তি। দেশের গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক ও রেলপথ এই জেলার মধ্য দিয়ে গেছে, যার ফলে এটি শুধু ভৌগোলিক নয়, পরিবহন ও বাণিজ্যের দিক থেকেও একটি কেন্দ্রীয় অবস্থানে রয়েছে। তেল আবিব, জেরুসালেম ও দক্ষিণ ইসরায়েলের অন্যান্য জেলার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে এই জেলার সড়কপথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
জনসংখ্যাগত বৈচিত্র্য ছাড়াও, এই জেলায় আরব ও ইহুদি জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কও একটি স্পর্শকাতর বিষয়। আরব সম্প্রদায় বহু বছর ধরে তাদের সামাজিক মর্যাদা, উন্নয়নের সুযোগ এবং নাগরিক অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলে আসছে। যদিও বিভিন্ন প্রশাসনিক প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে, তথাপি ন্যায্যতা ও সমতা অর্জনে এখনো অনেক দূর যেতে হবে।
এই জেলায় শিক্ষার হার তুলনামূলকভাবে বেশি, এবং এখানকার বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল ও পলিটেকনিক কলেজ জাতিগতভাবে মিশ্র শিক্ষার্থী নিয়ে গড়ে উঠেছে। এটি সামাজিক মেলবন্ধন ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবেও কাজ করে।
মধ্য জেলার শিল্প ও বাণিজ্য খাতও যথেষ্ট উন্নত। বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল, বাণিজ্যিক কেন্দ্র, বিপণিবিতান এবং আন্তর্জাতিক কোম্পানির শাখা এই জেলায় অবস্থিত। কৃষিখাত, বিশেষ করে সাইট্রাস ফল, ফুল এবং ডেইরি শিল্প এখানকার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তবে, শিল্পায়নের কারণে পরিবেশ দূষণ এবং আবাসন সমস্যাও ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছে।
মধ্য জেলা তার বহুমাত্রিক চরিত্রের জন্য ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রশাসনিক মানচিত্রে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। একদিকে যেমন এখানে জাতিগত ও ধর্মীয় বিভাজন, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে আন্তঃসম্প্রদায়িক সহাবস্থান এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার বাস্তব রূপরেখা। সামাজিক ও রাজনৈতিক টানাপোড়েন থাকা সত্ত্বেও, এই জেলাটি আজকের দিনে ইসরায়েলের অন্যতম জটিল অথচ কার্যকরী এক প্রশাসনিক বাস্তবতা হিসেবে বিবেচিত।
এইভাবে রামলা থেকে পেতা তিকভা, রেহোভত থেকে শারনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে ছড়িয়ে থাকা এই জেলার জীবনযাত্রা, প্রশাসনিক গঠন এবং সাংস্কৃতিক বহুত্ব ইসরায়েলের কেন্দ্রীয় সত্তার এক বহুবর্ণ চিত্রপট তৈরি করে রেখেছে—যেখানে রাষ্ট্রের আধুনিকতা, ঐতিহ্য এবং বিবিধ জাতিগত পরিচয় পরস্পরের সঙ্গে মিশে গেছে।
তেল আবিব জেলা
তেল আভিভ জেলা, হিব্রুতে “মেহোয তেল আভিভ” (מְחוֹז תֵּל־אָבִיב) নামে পরিচিত, ইসরায়েলের প্রশাসনিক মানচিত্রে এক ব্যতিক্রমী ভূখণ্ড। যদিও এটি আয়তনের বিচারে সবচেয়ে ছোট জেলা—মাত্র ১৭২ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত—তবু এর গুরুত্ব দেশটির সামগ্রিক অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিপুল। রাজধানী তেল আভিভ শহর কেবল জেলার নয়, ইসরায়েলের আধুনিকতার প্রতীক। প্রযুক্তি, গণমাধ্যম, ফ্যাশন, সমুদ্রতট ও মুক্তচিন্তার এক তুরীয় সম্মেলন এখানে নিত্যদিন ঘনিয়ে ওঠে।
২০১৮ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, তেল আভিভ জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১৪ লক্ষ ২৭ হাজার ২০০ জন। এই সংখ্যা জেলার তুলনায় অত্যন্ত বেশি—এটি ইঙ্গিত দেয় যে, এই ঘনবসতিপূর্ণ নগরায়িত এলাকা ইসরায়েলের নাগরিক জীবনের এক কেন্দ্রীয় ক্ষেত্র। জনসংখ্যার প্রায় ৯৮.৯ শতাংশ ইহুদি, আর মাত্র ১.১০ শতাংশ আরব সম্প্রদায়ের। এটি ইসরায়েলের অন্যান্য জেলার তুলনায় একটি অপেক্ষাকৃত একজাতিক সামাজিক বিন্যাস তুলে ধরে।
প্রশাসনিক কাঠামোর দিক থেকে এই জেলায় মোট ১০টি স্বীকৃত শহর এবং ২টি স্থানীয় কাউন্সিল রয়েছে, তবে কোনও আঞ্চলিক কাউন্সিল নেই। কারণ এই জেলা মূলত একটি সম্পূর্ণ নগরভিত্তিক অঞ্চল, যেখানে গ্রামীণ জনপদ বা বসতির পরিসর প্রায় নেই বললেই চলে। বস্তুত, এখানকার জনবসতির কাঠামো পুরোপুরি শহুরে—উচ্চ দালান, আধুনিক আবাসন প্রকল্প, সুশৃঙ্খল রাস্তাঘাট, বিস্তৃত পরিবহন নেটওয়ার্ক, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং ব্যস্ত বাজারঘেঁষা জীবনযাপন।
তেল আভিভ শহর নিজে শুধুমাত্র এই জেলার প্রশাসনিক কেন্দ্র নয়, বরং এটি ইসরায়েলের “আর্থিক রাজধানী” হিসেবেও বিবেচিত হয়। বহু বহুজাতিক কোম্পানির সদর দপ্তর এখানে অবস্থিত। এখানে আছে পৃথিবীখ্যাত হাই-টেক শিল্পাঞ্চল “সিলিকন উপত্যকার” আদলে গড়ে ওঠা অঞ্চলের আদর্শ উদাহরণ—যা “সিলিকন ওয়াদি” নামে পরিচিত। নানা ধরনের স্টার্টআপ, সাইবার নিরাপত্তা সংস্থা ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান এই শহরকে বিশ্বের হাই-টেক মানচিত্রে স্থাপন করেছে।
শুধু অর্থনীতি নয়, তেল আভিভ সাংস্কৃতিকভাবেও দেশের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। শহরটির বাসিন্দারা মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী, এবং এখানকার জীবনে ধর্মীয় অনুশাসনের বদলে উদারনৈতিক জীবনধারা বেশি স্পষ্ট। সাংস্কৃতিক উৎসব, সমুদ্রতীরবর্তী বিনোদন, সমকামী অধিকারের বিস্তার ও রাত্রিজীবনের বৈচিত্র্যে এটি ইউরোপীয় শহরের সঙ্গে তুলনীয় হয়ে উঠেছে।
তেল আভিভ জেলার আরেকটি অনন্য দিক হল এর নাগরিক পরিকাঠামো। শহরটির অভ্যন্তরে আধুনিক ট্রেন ব্যবস্থা, বিস্তৃত বাস নেটওয়ার্ক এবং এখন সম্প্রসারিত মেট্রোরেল প্রকল্প—সব মিলিয়ে এক কার্যকর নগর পরিবহন ব্যবস্থার রূপরেখা নির্মাণ করেছে। শহরজুড়ে বাইক-লেন, হেঁটে চলার উপযোগী ফুটপাথ ও উদ্যানসমূহ নাগরিকদের জন্য আরও আরামদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। শহরটির বেশ কয়েকটি এলাকা যেমন নেভে তেজেদেক, সারোনা মার্কেট ও রোথচাইল্ড বুলেভার্ড—প্রতিদিন দেশি-বিদেশি পর্যটকের ভিড়ে সরগরম থাকে।
তেল আভিভ জেলা সামাজিকভাবে অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও সচেতন। নারীর অধিকার, পরিবেশ আন্দোলন, ভোক্তা অধিকার এবং নাগরিক স্বচ্ছতার দাবিতে নানা সময়ে আন্দোলন হয়েছে এই শহরের রাস্তায়। এখানকার গণমাধ্যম এবং সমাজকর্মী সম্প্রদায় প্রায়শই ইসরায়েলি নীতিনির্ধারণে একটি বিকল্প কণ্ঠস্বর হিসেবে উঠে এসেছে।
তবে সব ইতিবাচক দিকের মাঝেও এই জেলার কিছু চ্যালেঞ্জও বিদ্যমান। অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ, উচ্চ হাউজিং মূল্য, যানজট এবং পর্যাপ্ত সবুজ পরিসরের অভাব দিন দিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে অনেকেই আর্থিক কারণে শহরের কেন্দ্রীয় অংশ থেকে প্রান্তে সরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। স্থানীয় প্রশাসন এই সমস্যা মোকাবিলায় বহু প্রকল্প হাতে নিয়েছে—যেমন উন্নত গণপরিবহন, ভর্তুকিযুক্ত আবাসন, এবং পরিবেশবান্ধব শহর পরিকল্পনা।
অন্যদিকে, তেল আভিভ জেলার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, এটি জাতিগতভাবে তুলনামূলকভাবে একজাতিক হলেও বিদেশি অভিবাসীদের একটি বৃহৎ অংশ এখানে বসবাস করে—বিশেষ করে ফিলিপিনো, থাই, আফ্রিকান ও পূর্ব ইউরোপীয় অভিবাসী শ্রমিকরা। তাঁরা মূলত স্বাস্থ্যসেবা, গৃহপরিচর্যা, নির্মাণ এবং আতিথেয়তা খাতে কাজ করেন। এই অভিবাসী জনগোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থান এবং অধিকার ইসরায়েলের নাগরিক সমাজে একটি চলমান আলোচনার বিষয়।
তেল আভিভ জেলাকে তাই শুধুমাত্র একটি প্রশাসনিক বিভাগ বলে সীমিত করা যায় না। এটি ইসরায়েলের আধুনিক, মুক্তমনস্ক, প্রযুক্তিনির্ভর এবং বৈচিত্র্যপ্রীতিশীল রাষ্ট্রসমাজের প্রতীক। এখানে জাতীয়তাবাদ ও বৈশ্বিকতা, ঐতিহ্য ও আধুনিকতা, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা—সব কিছুরই মেলবন্ধন ঘটেছে, একধরনের উত্তেজক সহাবস্থানের ভেতর দিয়ে।
সব মিলিয়ে, তেল আভিভ জেলা ইসরায়েলের হৃদস্পন্দন। এটি এমন এক জায়গা যেখানে রাষ্ট্রের অর্থনীতি গতি পায়, সমাজ সংস্কৃতির নতুন ভাষা খুঁজে পায়, আর নাগরিক জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে একধরনের মুক্তির স্বাদ যুক্ত হয়—যা ইসরায়েল রাষ্ট্রকে মধ্যপ্রাচ্যে একটি অনন্য পরিচয় দেয়।
দক্ষিণ জেলা
দক্ষিণ ইসরায়েল, প্রশাসনিকভাবে যা “মেহোয হাদারোম” নামে পরিচিত, আয়তনের বিচারে গোটা দেশের বৃহত্তম জেলা। ১৪,১৮৫ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত এই বিশাল এলাকা ইসরায়েলের মোট ভূখণ্ডের প্রায় ৬০ শতাংশ নিয়ে গঠিত, অথচ জনসংখ্যা বণ্টনের দিক থেকে এটি অপেক্ষাকৃত কম ঘনবসতিপূর্ণ। ২০১৮ সালের হিসাব অনুযায়ী, এই জেলায় প্রায় ১৩ লক্ষ ২ হাজার মানুষ বসবাস করে, যার মধ্যে প্রায় ৭৯.৬৬ শতাংশ ইহুদি এবং ১২.৭২ শতাংশ আরব।
দক্ষিণ জেলার রাজধানী বিরশেবা—যা কখনও কখনও “নেগেভের রাজধানী” বলেও পরিচিত—ইতিহাস, সামরিক কৌশল ও আধুনিক শহরায়নের এক চমৎকার সংমিশ্রণ। এই শহরকে কেন্দ্র করে সারা জেলার প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। এটি শুধু একটি প্রশাসনিক শহরই নয়, বরং নেগেভ মরুভূমিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এক সম্ভাবনাময় নগরী, যেখানে চরম আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতার মাঝেও টিকে থাকার ইতিহাস আছে।
এই জেলার অধিকাংশ এলাকা জুড়ে রয়েছে নেগেভ মরুভূমি—এক বিশাল শুষ্ক অঞ্চল, যার মধ্যে বিস্তীর্ণ পাথুরে উপত্যকা, পাহাড়ি গিরিখাত এবং অগভীর বালুর সমতল দেখা যায়। তাপমাত্রা গ্রীষ্মে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যেতে পারে, আবার শীতে হঠাৎ ঠান্ডা ও রাতের বেলা হিমেল হাওয়ার প্রকোপ দেখা যায়। এই প্রতিকূল ভূপ্রকৃতি সত্ত্বেও দক্ষিণ ইসরায়েল বহু কৃষি-প্রযুক্তি নির্ভর প্রকল্প, বিশেষত ড্রিপ ইরিগেশন ও সবুজায়ন কৌশলের জন্ম দিয়েছে, যা বিশ্বজুড়ে ইসরায়েলের খ্যাতি এনে দিয়েছে।
প্রশাসনিক পরিকাঠামোর দিক থেকে, দক্ষিণ জেলায় ১২টি শহর, ১১টি স্থানীয় কাউন্সিল এবং ১৫টি আঞ্চলিক কাউন্সিল রয়েছে। এই কাউন্সিলগুলোর কার্যক্রম নেগেভের ছড়ানো ছিটানো বসতি ও উন্নয়নমূলক অঞ্চলগুলিকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। জেলার মধ্যে বিখ্যাত শহরগুলোর মধ্যে আশকেলন ও বি’এর শেভার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আশকেলন, যার জনসংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ ৫১ হাজার ২০০, একটি উপকূলীয় শহর, যেখানে উন্নত আবাসন, উচ্চশিক্ষা ও পর্যটন শিল্প গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে, বি’এর শেভা—যার জনসংখ্যা ৭ লক্ষ ৫০ হাজার ৭০০ জন—একটি দ্রুত উন্নয়নশীল শহর, যেখানে উচ্চপ্রযুক্তি অঞ্চল, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল এবং আধুনিক নগরায়নের চিহ্ন স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান।
দক্ষিণ জেলার সামাজিক ও জনমিতিক বৈচিত্র্যও উল্লেখযোগ্য। এখানে রয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বেদুইন আরব সম্প্রদায়, যারা মূলত মরু অঞ্চলজুড়ে ছড়িয়ে থাকা নগর ও আধা-নগর সম্প্রদায়ে বাস করেন। ইসরায়েলি রাষ্ট্র ও বেদুইনদের মধ্যে জমির মালিকানা, নগর উন্নয়ন এবং নাগরিক অধিকার নিয়ে বহু দশক ধরেই টানাপড়েন চলছে। এই বেদুইন সম্প্রদায়দের উন্নয়নে নানা সরকারি কর্মসূচি নেওয়া হলেও, তাদের বাস্তব পরিস্থিতি অনেক ক্ষেত্রেই অনগ্রসর।
গাজার সীমানা সংলগ্ন এলাকাগুলো—যেমন হফ আযা—দক্ষিণ জেলার রাজনৈতিক বাস্তবতা ও নিরাপত্তাজনিত চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৫ সালে ইসরায়েল সরকার ‘ডিসএনগেজমেন্ট প্ল্যান’ বা গাজা থেকে প্রত্যাহার নীতি কার্যকর করে, যার ফলে প্রায় ১০,০০০ ইসরায়েলি নাগরিককে হফ আযার আঞ্চলিক কাউন্সিল এলাকা থেকে সরে যেতে বাধ্য করা হয়। বর্তমানে, এই এলাকাগুলিতে কোনো বসতি নেই, তবে সামরিক ও প্রশাসনিক পর্যবেক্ষণ অব্যাহত আছে, এবং সেখানে “সমন্বয় ও যোগাযোগ প্রশাসন” বা Coordination and Liaison Administration (CLA) কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।
বিরাট ভৌগোলিক বিস্তৃতি থাকা সত্ত্বেও, দক্ষিণ ইসরায়েলের জনসংখ্যার ঘনত্ব তুলনামূলকভাবে কম। তবে সরকারের বিভিন্ন নীতি, যেমন নেগেভের উন্নয়ন পরিকল্পনা, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ এবং নতুন শহর গড়ে তোলা—এই অঞ্চলটিকে ধীরে ধীরে একটি নতুন সম্ভাবনার কেন্দ্র হিসেবে রূপ দিচ্ছে। “নাহাল বেসোর”, “রামাত হানেগেভ”, এবং “আরাদ” এর মতো স্থানের নতুন পরিকল্পনামাফিক উন্নয়ন ইতিমধ্যেই দৃশ্যমান।
পরিবহন ব্যবস্থার দিক থেকেও দক্ষিণ জেলা ক্রমশ উন্নত হচ্ছে। নতুন হাইওয়ে, বিস্তৃত রেলপথ, বিমানঘাঁটি এবং শিল্প পার্কের ফলে রাজধানী তেল আভিভ বা জেরুসালেমের সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের যোগাযোগ আরও সহজতর হয়েছে। এর ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিধিও বাড়ছে এবং কর্মসংস্থানের নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি হচ্ছে।
পরিশেষে বলা যায়, দক্ষিণ জেলা শুধু আয়তনের দিক থেকেই বৃহৎ নয়, বরং এর মধ্যে নিহিত রয়েছে ইসরায়েলের প্রযুক্তি, পরিবেশ-অভিযোজন, নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ এবং সমাজ-উন্নয়নের এক জটিল অথচ শক্তিশালী প্রতিচ্ছবি। বেদুইন গ্রাম থেকে শুরু করে হাই-টেক শহর, মরু ভূমি থেকে সবুজ কৃষিজমি, উপকূল থেকে সীমান্তবর্তী গ্রাম—সব মিলিয়ে দক্ষিণ ইসরায়েল এক প্রতিকূলতাকে সুযোগে রূপান্তরের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।
জুডেয়া ও সামেরিয়া অঞ্চল
ইসরায়েলের প্রশাসনিক মানচিত্রে এক বিশেষ অবস্থান নিয়ে অবস্থান করছে জুডেয়া ও সামেরিয়া অঞ্চল—যা পশ্চিম তীরের (West Bank) একটি বিস্তৃত অংশজুড়ে অবস্থিত এবং হিব্রু ভাষায় যাকে বলা হয় ‘এযোর ইয়েহুদা ভেশোমরন’। যদিও এটি রাষ্ট্রের ছয়টি মূল প্রশাসনিক জেলার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়, তবু এটি প্রশাসনিকভাবে এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসরায়েলের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির কেন্দ্রীয় বিতর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
এই অঞ্চলটির বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামো অনুযায়ী, এখানে রয়েছে ৪টি শহর, ১৩টি স্থানীয় কাউন্সিল এবং ৬টি আঞ্চলিক কাউন্সিল। যদিও আন্তর্জাতিকভাবে এই অঞ্চলকে অধিকৃত (occupied) পশ্চিম তীরের অংশ হিসেবে দেখা হয়, তবু ইসরায়েল এই অঞ্চলজুড়ে নানা ধরণের বসতি নির্মাণ করেছে এবং এখানকার কিছু এলাকায় কার্যত বেসামরিক শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। ২০১৮ সালের হিসাব অনুযায়ী, ইসরায়েলি বসতির জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৪ লক্ষ ২৭ হাজার ৮০ জন। তবে এই পরিসংখ্যানে আরব ও বেদুইন জনসংখ্যাকে (Area A ও B বাদে) আলাদাভাবে গণ্য করা হয়, যার আনুমানিক সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার।
জুডেয়া ও সামেরিয়া অঞ্চল নামটি হিব্রু বাইবেল ও প্রাচীন ইহুদি ঐতিহ্যের অনুসরণে গঠিত। ‘জুডেয়া’ নামটি ইহুদি রাজ্যের ঐতিহাসিক ভূমি ইঙ্গিত করে, আর ‘সামেরিয়া’ হলো ইসরায়েলের প্রাচীন উত্তরাঞ্চল। এই নামকরণ ও ব্যবহার কেবলমাত্র এক প্রশাসনিক চিহ্নই নয়, বরং একটি রাজনৈতিক অবস্থানও, যা গোটা মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার অন্তর্গত এক আবেগঘন অধ্যায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইসরায়েলের ডানপন্থী রাজনৈতিক শক্তিগুলি এই অঞ্চলকে ‘ঐতিহাসিক ইসরায়েল’ এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সেখানে বসতি নির্মাণকে একটি জাতীয় কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করে থাকে।
তবে আন্তর্জাতিক আইন ও কূটনৈতিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, এই অঞ্চলকে অধিকৃত ভূমি হিসেবেই গণ্য করা হয়। জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অধিকাংশ রাষ্ট্র এই বসতিগুলিকে অবৈধ হিসেবে ঘোষণা করেছে। আর এখানেই শুরু হয় বিতর্কের দোলাচল—একদিকে ইসরায়েলি সরকার ও বসতি-বাসিন্দাদের ‘ঐতিহাসিক অধিকার’ এর দাবি, অন্যদিকে ফিলিস্তিনি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ভূখণ্ডগত স্বীকৃতির সংগ্রাম।
জুডেয়া ও সামেরিয়া অঞ্চলের বৃহত্তম শহর হচ্ছে মোদি’ইন ইলিট (Modi’in Illit), একটি মূলত হারে-দী (অতি-অর্থোডক্স) ইহুদি জনসংখ্যা অধ্যুষিত বসতি। এছাড়াও এরিয়েল, মালে আদুমিম এবং বেইত এল’র মতো গুরুত্বপূর্ণ বসতিগুলি এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ভূচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ নাম। এখানকার বসতিরা নিজেদের আধুনিক নগর পরিকল্পনার মডেল হিসেবে উপস্থাপন করলেও, সমান্তরালভাবে চলছে এই বসতিগুলির কারণে ফিলিস্তিনি বসতি ও চলাচলের সীমাবদ্ধতা।
উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই অঞ্চলটি প্রশাসনিকভাবে ইসরায়েলের “মেহোজ” বা জেলা বিভাগভুক্ত নয়। যদিও এটি হিব্রু প্রশাসনিক পরিভাষায় একটি “এযোর” বা অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত হয়, বাস্তবে এটি একটি সামরিক প্রশাসনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এখানে “সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফর জুডেয়া অ্যান্ড সামারিয়া” নামক একটি প্রশাসনিক দপ্তর কার্যকর, যা ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ।
এই ভূখণ্ডে থাকা বসতির আইনি মর্যাদা নিয়েও বহু মতপার্থক্য বিদ্যমান। ইসরায়েলি আইনে এগুলি কিছুটা স্বাধীনভাবে পরিচালিত হলেও, আন্তর্জাতিক আইনে এই এলাকাগুলিকে দখলদার ভূখণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ কারণে বহুবার আন্তর্জাতিক মহলে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, এবং এই ইস্যুটি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আলোচনার কেন্দ্রে থেকেছে।
একই সঙ্গে, জুডেয়া ও সামেরিয়া অঞ্চল জুড়ে ইহুদি ও আরব জনসংখ্যার মধ্যকার সামাজিক বিভাজনও দিনে দিনে প্রকট হচ্ছে। আলাদা সড়কপথ, আলাদা নিরাপত্তা বেষ্টনী, সামরিক চেকপয়েন্ট ইত্যাদি এক ধরনের দখল ও বিচ্ছিন্নতার মানচিত্র নির্মাণ করেছে। যদিও বসতি স্থাপনকারী ইসরায়েলি নাগরিকরা উন্নত পরিকাঠামো ও নাগরিক সেবার সুযোগ পাচ্ছেন, ফিলিস্তিনি অধিবাসীরা তা থেকে বহুলাংশে বঞ্চিত। এই অসাম্য ও বৈষম্যের চিত্র গোটা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে।
জুডেয়া ও সামেরিয়া অঞ্চল ছাড়াও জেরুজালেম ও উত্তর জেলার কিছু অংশ আন্তর্জাতিকভাবে ইসরায়েলের অংশ হিসেবে স্বীকৃত নয়। ইসরায়েল এই এলাকাগুলিকে তার একক রাষ্ট্র হিসেবে দেখলেও, বাস্তবে এটি এক জটিল ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি করেছে। এমনকি ২০২১ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, এই অঞ্চলে মোট জনসংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষ ৬৫ হাজার ৪০০ জন, যার ৯৮% ইহুদি এবং প্রায় ০% আরব (অর্থাৎ আরবরা সংখ্যাগতভাবে এখানে তেমন কোনো দৃষ্টিগোচর নয়)। তবে এই পরিসংখ্যান শুধুমাত্র ইসরায়েলি নাগরিকদের অন্তর্ভুক্ত করে, ফিলিস্তিনি বা আরব বাসিন্দাদের নয়।
অবশ্য এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ‘এরিয়া এ’, ‘এরিয়া বি’ এবং ‘এরিয়া সি’ এর জটিল বিভাজন। অসলো চুক্তির ভিত্তিতে এই শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছিল, যার ফলে কিছু এলাকা ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও, ‘এরিয়া সি’-তে (যেখানে অধিকাংশ ইহুদি বসতি অবস্থিত) ইসরায়েলি প্রশাসন পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। এই নিয়ন্ত্রণের ফলে উন্নয়ন, নির্মাণ, জমির মালিকানা এমনকি জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহও তীব্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।
এই অঞ্চল নিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। বিশ্ব সম্প্রদায় দ্ব্যর্থহীনভাবে বলছে—এই ভূখণ্ড একদিন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে। কিন্তু মাটির উপর বাস্তবতা বলছে ভিন্ন কথা। প্রতিদিন নতুন বসতির অনুমোদন, ফিলিস্তিনি ঘরবাড়ি ধ্বংস, রাস্তাঘাটের নির্মাণ—সবকিছুই এই অঞ্চলে এক অদৃশ্য কিন্তু অনিবার্য রাষ্ট্রায়নের পথে এগোচ্ছে। এই প্রবণতা ভবিষ্যতের মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ার জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে।
সার্বিকভাবে বলা যায়, জুডেয়া ও সামেরিয়া অঞ্চল শুধু ইসরায়েলের এক ভৌগোলিক প্রসারণ নয়—এটি একটি ইতিহাস, এক বিশ্বাস, এক রাজনৈতিক প্রকল্প এবং এক বিরোধপূর্ণ বাস্তবতা। এর মধ্যে নিহিত আছে সংঘাত ও সহাবস্থানের যুগপৎ চিত্র, যা মধ্যপ্রাচ্যের জটিল ধাঁধাটির একটি অপরিহার্য খণ্ড।
ইসরায়েলের নাগরিকত্ব আইন
ইসরায়েলি নাগরিকত্ব সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালা কেবল একটি রাষ্ট্রের প্রশাসনিক নিয়মবিধির প্রশ্ন নয়—এটি ইসরায়েলের অস্তিত্ব, তার পরিচিতি এবং ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রগঠনের দর্শনের গভীরে গিয়ে প্রোথিত। ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই যে দুটি আইন এই জাতিগঠনের ধারণাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল, তা হল ১৯৫০ সালের ‘প্রত্যাবর্তন আইন’ (Law of Return) এবং ১৯৫২ সালের ‘নাগরিকত্ব আইন’ (Israeli Citizenship Law)। এ দুটি আইন শুধু অভিবাসন বা নাগরিকত্বপ্রাপ্তির প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে না—বরং রাষ্ট্রকে কাদের জন্য, কিভাবে এবং কোন নৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড় করানো হয়েছে, সেই প্রশ্নগুলোকেই বৈধতা দেয়।
প্রত্যাবর্তন আইন কার্যত একটি মৌলিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত: “প্রত্যেক ইহুদি বিশ্বের যে কোনও প্রান্ত থেকে ইসরায়েলে ফিরে আসতে পারে এবং এই রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে পারে।” এই আইনের মাধ্যমে ধর্মীয় পরিচয়—বিশেষত ইহুদি ধর্মীয় পরিচয়—একটি রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করে। এই আইনের আওতায়, কেবল ইহুদিদের নয়, তাঁদের সন্তান, নাতি-নাতনিদেরও এই রাষ্ট্রে অভিবাসনের অধিকার দেওয়া হয়েছে, যদিও এই সুযোগ শুধু ইহুদিদের জন্যই বরাদ্দ। অর্থাৎ এই আইন কার্যকরভাবে ধর্মীয় ও জাতিগত একচেটিয়াতা প্রতিষ্ঠা করে, যা আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থার আদর্শ থেকে অনেকটাই দূরে।
অন্যদিকে ১৯৫২ সালের নাগরিকত্ব আইন একটি তুলনামূলকভাবে প্রশাসনিক কাঠামো প্রদান করে। এতে বলা হয়েছে, যে সব ব্যক্তি ইসরায়েলে জন্মগ্রহণ করেছে এবং যাঁদের অন্তত একজন অভিভাবক ইসরায়েলের নাগরিক, তাঁরা জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব পেতে পারেন। পাশাপাশি, নির্দিষ্ট শর্তে বসবাস, বৈবাহিক সম্পর্ক বা সরকারি অনুমোদনের ভিত্তিতে ইসরায়েলি নাগরিকত্ব লাভ সম্ভব। তবে বাস্তবে, এই আইনের নানা ধারা এমনভাবে বিন্যস্ত হয়েছে, যাতে ফিলিস্তিনি ও অন্যান্য অ-ইহুদি নাগরিকদের নাগরিকত্ব প্রাপ্তির পথ অধিকতর জটিল, এমনকি অনেক সময় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।
ইসরায়েলি আইনের আরেকটি জটিল ও বহুচর্চিত দিক হলো ‘জাতীয়তা’ এবং ‘নাগরিকত্ব’ শব্দদুটোর বিভাজন। অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই দুই ধারণা প্রায় সমার্থক। কিন্তু ইসরায়েলের ক্ষেত্রে এটি একেবারে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে “ইসরায়েলি নাগরিকত্ব” বৈধ প্রশাসনিক পরিচয় হলেও, “ইসরায়েলি জাতীয়তা” নামে কোনও সত্ত্বা রাষ্ট্র স্বীকার করে না। ১৯৭০ এবং ২০০০ দশকে একাধিক মামলা হওয়ার পরও ইসরায়েলের সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয় যে “ইসরায়েলি জাতীয়তা” বলে কোনও স্বীকৃত আইনি বা সাংবিধানিক পরিচয় নেই। এই অবস্থান কার্যত ইসরায়েলি সমাজে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠা করে।
যাঁরা ইহুদি, তাঁরা “ইহুদি জাতীয়তা”-র সদস্য হিসেবে বিবেচিত হন এবং তাঁদের ধর্মীয় পরিচয়ই রাষ্ট্র কর্তৃক জাতীয় পরিচয় হিসেবে স্বীকৃত। ফলে একজন মুসলিম, খ্রিস্টান বা দ্রুজ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি, যিনি ইসরায়েলের নাগরিকত্ব পেয়ে থাকলেও, কখনোই “ইসরায়েলি” জাতীয়তায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন না। এক্ষেত্রে জাতীয়তা বিষয়টি হয়ে ওঠে একটি একচেটিয়া ধর্মীয় পরিচয়ের গালচিত্র, যার মাধ্যমে রাষ্ট্র ‘কে এই ভূমির প্রকৃত মালিক’—এই প্রশ্নে একমাত্রিক উত্তর প্রতিষ্ঠা করে।
২০১৮ সালে এই জটিল ও বিতর্কিত কাঠামো আরও গভীরতর আইনগত ভিত্তি পায় যখন ইসরায়েলি ক্নেসেট (সংসদ) একটি বিশেষ ‘জাতিরাষ্ট্র আইন’ (Nation-State Law) পাস করে। এই আইন অনুযায়ী, ইসরায়েলকে স্পষ্টভাবে “ইহুদি জনগণের জাতিরাষ্ট্র” হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এটি নির্ধারণ করে যে, ইহুদি জনগণই এই রাষ্ট্র গঠনের একমাত্র মালিক, এবং রাষ্ট্রটি কেবলমাত্র ইহুদি জনগণের স্বজাতিক উন্নয়নের জন্যই প্রতিষ্ঠিত। এই আইনে হিব্রু ভাষাকে একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং আরবি ভাষার পূর্বের মর্যাদা হ্রাস পায়। এছাড়াও এই আইনে ‘ইহুদি বসতি নির্মাণ’ কে রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে—যা ফিলিস্তিনিদের উদ্বেগ আরও ঘনীভূত করে।
সমালোচকদের মতে, এই আইন কার্যত একটি প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য সৃষ্টি করে, যা সংখ্যালঘু আরবদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে বিবেচনার পথে ঠেলে দেয়। এই আইনের বিরুদ্ধে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ফিলিস্তিনি নাগরিকরা একে তাঁদের মৌলিক অধিকার হরণের আইন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, যেখানে তাঁদের ভাষা, ইতিহাস এবং সংস্কৃতিকে রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে প্রায় অদৃশ্য করে ফেলা হয়েছে।
ইসরায়েলের এই নাগরিকত্ব কাঠামোর মধ্যে দিয়ে স্পষ্টতই প্রতিফলিত হয় একটি বিশেষ ধরণের জাতিগঠনের প্রচেষ্টা, যেখানে “রাষ্ট্র” এক ধরনের ঐতিহাসিক-ধর্মীয় পরিচয়ের উপর দাঁড় করানো হয়েছে। এই কাঠামোতে নাগরিকত্ব পাওয়া কেবল প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নয়—তা হয়ে দাঁড়ায় রাষ্ট্রের আদর্শ নাগরিক কে হবে, সেই প্রশ্নের একটি ধর্মীয়-জাতিগত উত্তর। ফলে, জাতিগত ভিন্নতা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বা ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিসরে অপ্রত্যাশিত বলেই বিবেচিত হয়।
এই প্রেক্ষাপটে ইসরায়েলি আরব, দ্রুজ, বেদুইন, আফ্রিকান অভিবাসী বা এমনকি ধর্মান্তরিত ইহুদিদের অবস্থান হয়ে ওঠে বিশেষভাবে সংকটাপন্ন। তাঁদের নাগরিকত্ব প্রাপ্তি আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে সম্ভব হলেও, প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে তাঁদের স্থান ক্রমাগত সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে। অনেক সময় এই শ্রেণির মানুষের পক্ষে সরকারি চাকরি, আবাসিক সুবিধা, জমির মালিকানা বা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ফলে ‘আইনি নাগরিক’ হলেও তাঁরা ‘রাষ্ট্রের মানুষ’ হয়ে উঠতে পারেন না।
তবে এর বিপরীতে, ইসরায়েলি সমাজের একটি অংশ, বিশেষত বামপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠী এই নাগরিকত্ব ও জাতীয়তার মধ্যেকার বৈষম্যের সমালোচনা করে থাকেন। তাঁদের মতে, একটি আধুনিক, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই ধরনের ধর্মনির্ভর নাগরিকত্ব কাঠামো কেবলমাত্র ভেদাভেদ সৃষ্টি করে না, বরং রাষ্ট্রকে একটি কুয়াশাচ্ছন্ন জাতিবাদী প্রকল্পে পরিণত করে। তাঁদের দাবি, ইসরায়েলি জাতীয়তা নামে একটি অবিসংবাদিত পরিচয় গড়ে তোলা দরকার, যার মধ্যে সকল নাগরিক—ধর্ম, জাতি, বা ভাষা নির্বিশেষে—অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন।
সার্বিকভাবে ইসরায়েলের নাগরিকত্ব আইন ও তার প্রয়োগ দেশটির পরিচয় ও রাষ্ট্রচিন্তার কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে। এটি একদিকে যেমন বিশ্বজুড়ে ইহুদি জনগণের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয় গড়ে তোলে, অন্যদিকে একইভাবে অন্য জাতিগোষ্ঠীর জন্য রাষ্ট্রের দ্বার আংশিকভাবে বা একেবারেই রুদ্ধ করে। ফলে প্রশ্নটি কেবল কাকে নাগরিক হিসেবে গ্রহণ করা হবে তা নয়, বরং কে এই রাষ্ট্রের অন্তর্গত এবং কে নয়—এই মৌলিক প্রশ্নটি আজও ইসরায়েলি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্যতম তীব্র বিতর্কের বিষয় হয়ে রয়ে গেছে।
বৈদেশিক সম্পর্ক
নিরাপত্তা, কৌশল এবং ধর্মীয় জাতিসত্তার প্রশ্নে ইসরায়েলের কূটনৈতিক সম্পর্ক ও বৈদেশিক নীতি একটি জটিল, বহুস্তরীয় এবং প্রায়শই বিতর্কিত অধ্যায়। রাষ্ট্রটির প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বৈশ্বিক রাজনীতির মানচিত্রে তার অবস্থান কখনো সম্মানের, কখনো ঘৃণার, আবার কখনো দ্বৈত সম্পর্কের নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েলের জন্মের পর থেকেই এটি আন্তর্জাতিকভাবে বৈচিত্রময় কূটনৈতিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছে, যদিও সেই সম্পর্কের বিস্তার আজও বৈষম্যপূর্ণ এবং অঞ্চলভেদে নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত।
বর্তমানে ইসরায়েল ১৬৫টি জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্রের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে, যার বাইরে হলি সি (ভ্যাটিকান), কসোভো, কুক দ্বীপপুঞ্জ ও নিয়ুর মতো রাষ্ট্র ও অঞ্চলও পড়ে। দেশটির বিদেশ মন্ত্রণালয় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ১০৭টি কূটনৈতিক মিশন পরিচালনা করছে, যা ইসরায়েলি পররাষ্ট্রনীতির সক্রিয়তার ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু এই বিস্তৃত কূটনৈতিক উপস্থিতির আড়ালে এক গভীর বিভাজনও স্পষ্ট—বিশেষত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ক আজও বহু ক্ষেত্রে অনুপস্থিত বা ভঙ্গুর।
বিশ্ব রাজনীতিতে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে মাত্র ছয়টি—সংখ্যায় আরব লীগের ২২টির মধ্যে—ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করেছে। এর মধ্যে আছে মিশর ও জর্ডানের মতো রাষ্ট্র, যারা অনেক আগে থেকেই চুক্তির মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, এবং সাম্প্রতিকতর আরব-ইসরায়েল স্বীকৃতির ঢেউ, যার ফলস্বরূপ সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, মরক্কো ও সুদান ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই চুক্তিগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মার্কিন মধ্যস্থতায় স্বাক্ষরিত হয়, বিশেষ করে “আব্রাহাম অ্যাকর্ডস”-এর পরিপ্রেক্ষিতে। তবে এই স্বীকৃতির রাজনীতির সঙ্গে বহু আরব রাষ্ট্রের জনগণের মানসিকতা মেলে না। মিশরের সঙ্গে দীর্ঘকালীন শান্তিচুক্তি থাকা সত্ত্বেও মিশরের জনমানসে ইসরায়েলকে এখনো বহুলাংশে শত্রু রাষ্ট্র হিসেবে দেখা হয়।
আরও কিছু মুসলিম দেশ ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেও সেই সম্পর্ক কখনোই স্থায়ী বা সুগভীর হয়ে ওঠেনি। ২০০৮–০৯ সালের গাজা যুদ্ধের পর মৌরিতানিয়া, কাতার, বলিভিয়া ও ভেনেজুয়েলা ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। বলিভিয়া পরবর্তীতে ২০১৯ সালে আবারও সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করে, যা ইসরায়েলের বৈদেশিক সম্পর্কের অবস্থা কতটা প্রেক্ষাপটনির্ভর তা বুঝতে সাহায্য করে।
মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সিরিয়া ও লেবাননের নাম উঠে আসে প্রথমেই। সিরিয়ার সঙ্গে ১৯৪৮ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর থেকেই কোনো আনুষ্ঠানিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি এবং যুদ্ধাবস্থা এখনো অমীমাংসিত। লেবাননের সঙ্গেও একই রকম পরিস্থিতি বিদ্যমান, যেখানে সীমান্তবিরোধ, হিজবুল্লাহর কার্যক্রম এবং পানিসম্পদ নিয়ে দ্বন্দ্ব পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। ইসরায়েল-লেবানন সীমান্ত আজও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোনো চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারিত নয়, ফলে সেখানে প্রায়শই সামরিক উত্তেজনা দেখা যায়।
ইরান প্রসঙ্গে ইসরায়েলের অবস্থান সবচেয়ে তীব্র। ১৯৭৯ সালে ইসলামিক বিপ্লবের পর ইরান ইসরায়েলকে স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে এবং পরবর্তীতে পারমাণবিক কর্মসূচি, হিজবুল্লাহ ও হামাসের প্রতি সমর্থনের কারণে ইসরায়েল ইরানকে ‘প্রধান হুমকি’ হিসেবে গণ্য করে আসছে। পারস্পরিক শত্রুতা কেবল নীতিগত নয়—তা একাধিকবার সাইবার আক্রমণ, গুপ্তচরবৃত্তি ও সরাসরি সামরিক হামলার পর্যায়েও পৌঁছেছে।
ইসরায়েলের জন্য এক নিঃসন্দেহে সবচেয়ে দৃঢ় এবং অবিচল মিত্র হলো যুক্তরাষ্ট্র। রাষ্ট্রটির প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন একসঙ্গে স্বীকৃতি দিলেও, পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় এবং তা পুনঃস্থাপিত হয় ১৯৯১ সালে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল সম্পর্ক এক অনন্য দৃষ্টান্ত। যুক্তরাষ্ট্র বারবার ঘোষণা করেছে, ইসরায়েলই মধ্যপ্রাচ্যে তাদের “সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অংশীদার”—যা কৌশলগত, সামরিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে নির্মিত। ১৯৬৭ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে প্রায় $৬৮ বিলিয়ন সামরিক সাহায্য এবং $৩২ বিলিয়ন অনুদান প্রদান করেছে, যা বিশ্বের অন্য কোনো দেশের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব। আমেরিকান জনমানসেও ইসরায়েলের প্রতি একটি শক্তিশালী সমর্থন দেখা যায়।
ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স ও ইতালির সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ক মোটামুটি স্থিতিশীল। বিশেষ করে জার্মানি—হলোকাস্ট-পরবর্তী প্রেক্ষাপটে ইসরায়েলের কাছে তাদের দায়বদ্ধতা উপলব্ধি করে—যথেষ্ট আর্থিক ও রাজনৈতিক সহায়তা প্রদান করেছে। ২০০৭ সাল পর্যন্ত তারা ইসরায়েল ও ইহুদি জনগণের জন্য ২৫ বিলিয়ন ইউরোরও বেশি ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের “ইউরোপীয় প্রতিবেশী নীতিতে” ইসরায়েলের অংশগ্রহণ ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার প্রতীক।
ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলজুড়ে তুরস্ক ও গ্রিসের সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ক দুই বিপরীত মেরুর উদাহরণ। ১৯৪৯ সালেই তুরস্ক ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিলেও রাজনৈতিক দোলাচলের কারণে বহুবার সম্পর্ক উত্থান-পতনের মুখে পড়ে। গাজা ফ্লোটিলা ইস্যু এবং ফিলিস্তিনি সহিংসতা নিয়েও সম্পর্ক খারাপ হয়েছে। অন্যদিকে, গ্রিসের সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ক তুলনামূলকভাবে উষ্ণতর। লেভিয়াথান গ্যাসক্ষেত্র এবং ইউরোএশিয়া ইন্টারকানেক্টর প্রকল্প দু’দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও শক্তি-সুরক্ষা সহযোগিতা বাড়িয়েছে।
এশিয়া ও আফ্রিকার বেশ কয়েকটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র যেমন আজারবাইজান, কাজাখস্তান ও ইথিওপিয়ার সঙ্গে ইসরায়েল দৃঢ় কৌশলগত ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। আজারবাইজানের সঙ্গে ইসরায়েলের সামরিক ও জ্বালানি সহযোগিতা, বিশেষত ইরান সংলগ্ন ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে, কৌশলগত গুরুত্ব বহন করে। ভারত ও ইসরায়েলের সম্পর্কও ১৯৯০-এর দশক থেকে ধারাবাহিকভাবে উন্নত হয়েছে। ১৯৯২ সালে পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর, দুই দেশ অস্ত্র, প্রযুক্তি, কৃষি ও সাইবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। বর্তমানে ভারত ইসরায়েলি অস্ত্রের অন্যতম প্রধান ক্রেতা এবং এই সম্পর্ক দুই দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিতে প্রভাব ফেলছে।
ইসরায়েলের বৈদেশিক সম্পর্কের এই জটিল চিত্র একদিকে যেমন কৌশলগত সক্ষমতা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ, অন্যদিকে তা রাষ্ট্রটির নীতিগত ও নৈতিক সংকটকেও তুলে ধরে। কূটনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্নতা এবং আঞ্চলিক বৈরিতা এড়াতে ইসরায়েল নতুন নতুন মিত্রতার দিকে ঝুঁকছে, কিন্তু এই সম্পর্কের অনেকগুলোই ভঙ্গুর ও সময়নির্ভর। ফলে ইসরায়েলের আন্তর্জাতিক কূটনীতি কেবল মৈত্রীর গল্প নয়, বরং প্রতিরোধ, প্রতিক্রিয়া ও অস্তিত্ব রক্ষার একটি কাহিনি—যেখানে স্বীকৃতি কেবল একটি রাজনৈতিক অর্জন নয়, বরং অনেকাংশেই একটি অস্তিত্বগত প্রশ্ন।
সামরিক শক্তি
ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা কাঠামো শুধুমাত্র একটি সামরিক বাহিনীর উপস্থিতিতে সীমাবদ্ধ নয়—এটি দেশটির অস্তিত্ব, রাষ্ট্রনীতি এবং পরিচয়ের গভীরে প্রোথিত একটি বাস্তবতা। রাষ্ট্রটি জন্মলগ্ন থেকেই এক ক্রমাগত হুমকির পরিবেশে বেড়ে উঠেছে, এবং সেই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সেস বা আইডিএফ (IDF) গঠিত হয়েছে একটি অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও বৈদেশিক প্রতিরক্ষার শক্ত প্রতীক হিসেবে।
আইডিএফ মূলত সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনী নিয়ে গঠিত একটি একক ও সংহত সশস্ত্র বাহিনী, যা এক ছাতার নিচে সমস্ত প্রতিরক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই বাহিনী ইসরায়েলি মন্ত্রিসভার অধীনে পরিচালিত হয় এবং একটি শক্তিশালী জেনারেল স্টাফের চিফ—রামাতকাল—এর অধীন থাকে। আইডিএফের গোড়াপত্তন ঘটে ১৯৪৮ সালে, যখন হেগানাহ নামক ইহুদি প্যারামিলিটারি গোষ্ঠী এবং অন্যান্য মিলিশিয়া গোষ্ঠীগুলোকে একত্র করে একটি রাষ্ট্রীয় বাহিনী গড়ে তোলা হয়।
IDF-এর ইতিহাস মূলত যুদ্ধ, সংঘর্ষ ও আত্মরক্ষার কাহিনিতে পূর্ণ। ১৯৪৮ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ থেকে শুরু করে ছয় দিনের যুদ্ধ, ইয়ম কিপুর যুদ্ধ এবং একবিংশ শতকের গাজা সংঘাত—সব ক্ষেত্রেই আইডিএফ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং প্রতি সংঘর্ষেই তাদের অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা এবং কৌশলগত উদ্ভাবনের মাধ্যমে তারা এক অনন্য পরিচয় তৈরি করেছে।
ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সর্বজনীন সামরিক সেবা বাধ্যতামূলক করা। ১৮ বছর পূর্ণ হলেই পুরুষ ও নারীদের সামরিক প্রশিক্ষণে অংশ নিতে হয়—যদিও পুরুষদের জন্য সময়সীমা সাধারণত দুই বছর আট মাস এবং নারীদের জন্য প্রায় দুই বছর। এরপর পুরুষদের বাধ্যতামূলক রিজার্ভ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যেখানে প্রায় প্রতি বছর কিছু নির্দিষ্ট সময়ে তাদের পুনঃপ্রশিক্ষণের জন্য ডাকা হয়। এই রিজার্ভ সেবা চলতে পারে চল্লিশোর্ধ্ব বয়স পর্যন্ত। আরব নাগরিকদের (ড্রুজ গোষ্ঠী ব্যতিক্রম) বাধ্যতামূলক সেবা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলেও, তাদের মধ্যে কেউ কেউ স্বেচ্ছায় আইডিএফে যোগ দিয়ে থাকেন।
অন্যদিকে, যাঁরা ধর্মীয় কারণে বা অন্যান্য সামাজিক কারণে সামরিক সেবায় অব্যাহতি পান, তাঁদের জন্য একটি বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে—‘শেরুত লেউমি’ বা জাতীয় সেবা, যেখানে তারা সমাজকল্যাণ, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেন।
বর্তমানে আইডিএফের সক্রিয় সদস্য সংখ্যা আনুমানিক ১ লক্ষ ৭৬ হাজার, এবং রিজার্ভিস্ট সংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষ ৬৫ হাজার। এই বিপুল বাহিনী এবং জনসংখ্যার উচ্চ প্রশিক্ষিত অংশীদারিত্ব ইসরায়েলকে এমন একটি রাষ্ট্রে পরিণত করেছে, যেখানে নাগরিক এবং সৈন্যের পার্থক্য প্রায়ই ঘুচে যায়।
প্রযুক্তি ও অস্ত্র ব্যবস্থার দিক থেকে ইসরায়েল নিজেকে এক যুগান্তকারী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। দেশটি স্থানীয়ভাবে ডিজাইন করা উন্নত সামরিক প্রযুক্তির ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ‘আয়রন ডোম’—একটি রকেট প্রতিরোধ ব্যবস্থা যা গাজা থেকে ছোঁড়া হাজার হাজার রকেটকে মাঝপথে ধ্বংস করে প্রতিরক্ষা গড়ে তোলে। ‘অ্যারো মিসাইল’, ‘স্পাইক’ অ্যান্টি-ট্যাংক গাইডেড মিসাইল এবং ‘পাইথন’ এয়ার-টু-এয়ার মিসাইল ইসরায়েলের নিজস্ব অস্ত্রশক্তির মূল স্তম্ভ।
ইসরায়েলের গোয়েন্দা প্রযুক্তি ক্ষেত্রেও উল্লখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। ইয়ম কিপুর যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশটি উন্নত উপগ্রহ গোয়েন্দা প্রযুক্তি তৈরি করেছে। ‘অফেক’ প্রোগ্রামের মাধ্যমে উপগ্রহ উৎক্ষেপণে সক্ষম ইসরায়েল বিশ্বের হাতে গোনা কয়েকটি দেশের মধ্যে পড়ে।
সবচেয়ে বিতর্কিত ও আলোচিত বিষয়ে আসে পারমাণবিক অস্ত্রধারণ। ইসরায়েল কখনোই সরাসরি তার পারমাণবিক ক্ষমতা স্বীকার করেনি, তবে আন্তর্জাতিক পরিসরে এটি পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জিত রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হয়। নিউক্লিয়ার নন-প্রোলিফারেশন চুক্তিতে স্বাক্ষর না করেও দেশটি ‘পারমাণবিক অস্পষ্টতা’-এর নীতি মেনে চলেছে, যা একধরনের কৌশলগত নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে। ইসরায়েলের ডলফিন সাবমেরিনগুলিকে এই পারমাণবিক নীতির ‘দ্বিতীয় আক্রমণ’ ক্ষমতার অংশ বলে ধারণা করা হয়।
ইসরায়েলে প্রতিটি নবনির্মিত বাড়িতে এখন একটি ‘মেরখাভ মুগান’ বা প্রতিরক্ষা কক্ষ বাধ্যতামূলক, যা রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্রের আক্রমণ ঠেকানোর জন্য প্রস্তুত। এটি সশস্ত্র ও নিরাপত্তা সংস্কৃতির প্রাত্যহিক বাস্তবতা কতটা নাগরিক জীবনে প্রোথিত, তার একটি দৃষ্টান্ত।
অর্থনৈতিক পরিসরে ইসরায়েলের সামরিক ব্যয় জিডিপির একটি বড় অংশ দখল করে থাকে। ১৯৭৫ সালে এটি ছিল সর্বোচ্চ ৩০.৩ শতাংশ। ২০২১ সালে ইসরায়েল প্রতিরক্ষা খাতে প্রায় ২৪.৩ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে, যা তাকে বিশ্বের সামরিক ব্যয়ে শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর তালিকায় ১৫তম স্থানে রেখেছে এবং জিডিপির অনুপাতে ষষ্ঠ স্থানে। ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাক্ষরিত এক ঐতিহাসিক চুক্তির আওতায় দেশটি ২০১৮ থেকে ২০২৮ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ৩.৮ বিলিয়ন ডলার মার্কিন সামরিক সহায়তা পাবে—যা ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাজেটের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ।
বিশ্ববাজারে অস্ত্র রপ্তানিকারক দেশ হিসেবেও ইসরায়েল আজ উল্লেখযোগ্য। ২০২২ সালে তারা ছিল ৯ম অবস্থানে, যদিও রপ্তানির বিশদ তথ্যের অধিকাংশই নিরাপত্তাজনিত কারণে গোপন রাখা হয়।
তবে এই শক্তির বিপরীতপটে আছে একটি আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক প্রশ্ন। ইসরায়েল গ্লোবাল পিস ইনডেক্সে বরাবরই নিচের দিকে অবস্থান করে এসেছে—২০২২ সালে তার স্থান ছিল ১৬৩টি দেশের মধ্যে ১৩৪তম। এই সূচক শুধুমাত্র সামরিক ক্ষমতা নয়, বরং নিরাপত্তা, মানবাধিকার ও সামগ্রিক শান্তির মানদণ্ডে একটি রাষ্ট্র কতটা এগিয়ে তা তুলে ধরে।
সুতরাং, ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী কেবল অস্ত্র ও প্রশিক্ষণের সমাহার নয়—এটি এক সমগ্র নিরাপত্তা-রাষ্ট্র কাঠামোর প্রতিচ্ছবি, যা আত্মরক্ষার ছদ্মাবরণে প্রায়ই আগ্রাসনের রূপ নেয়, এবং বিশ্ব-রাজনীতির মানচিত্রে এক গভীর বিভাজন তৈরি করে চলে।
আইনি ব্যবস্থা
ইসরায়েলের বিচারব্যবস্থা একটি ত্রিস্তরীয় কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, যার প্রতিটি স্তর একে অপরের পরিপূরক হলেও নিজস্ব ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পরিসর নিয়ে কাজ করে। এই বিচারব্যবস্থা একদিকে যেমন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার বহন করে, তেমনি ইহুদি ধর্মীয় আইন ও আধুনিক গণতান্ত্রিক আইনের সমন্বয়ও এতে প্রতিফলিত হয়েছে।
সর্বনিম্ন স্তরে আছে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট বা নিম্ন আদালত, যা প্রায় প্রতিটি শহরে অবস্থিত এবং সাধারণ নাগরিক মামলা-মোকদ্দমার প্রাথমিক পর্ব এখান থেকেই শুরু হয়। ছোটখাটো ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলা, প্রাথমিক তদন্ত এবং সীমিত আর্থিক পরিমাণের মামলাগুলি এখানেই নিষ্পত্তি হয়। এই স্তরের আদালত প্রতিদিনকার বিচারপ্রক্রিয়ার সর্বাধিক বোঝা বহন করে থাকে।
ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ওপরে অবস্থান করছে জেলা আদালত, যা মধ্যম স্তরের বিচারিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। এটি দ্বৈত ভূমিকা পালন করে—একদিকে এটি উচ্চতর ফৌজদারি এবং দেওয়ানি মামলার প্রথম স্তরের আদালত, অন্যদিকে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল আদালত হিসেবেও এটি ব্যবহৃত হয়। ইসরায়েলের ছয়টি প্রধান প্রশাসনিক জেলার মধ্যে পাঁচটিতে এই জেলা আদালত স্থাপিত হয়েছে। এই স্তরের আদালতগুলির বিচারিক পরিধি অনেক বিস্তৃত এবং এসব আদালতেই মূলত জটিল, বৃহৎ পরিসরের মামলা ওঠে।
বিচারব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তর, এবং এককথায় রাষ্ট্রের বিচারিক স্তম্ভ, হল সুপ্রিম কোর্ট। এটি জেরুজালেমে অবস্থিত এবং এর ভূমিকাও দ্বিমুখী—একদিকে এটি আপিলের সর্বশেষ আদালত, আবার হাই কোর্ট অফ জাস্টিস হিসেবে এটি সংবিধান ও মৌলিক অধিকারের প্রশ্নে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারে। হাই কোর্ট অফ জাস্টিস রূপে এই আদালত প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, আইনগত বৈধতা বা রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধেও সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে বিদেশি পর্যন্ত সবাইকে প্রতিকার পাওয়ার অধিকার দেয়। এই সরাসরি আবেদনের সুযোগ ইসরায়েলি বিচারব্যবস্থাকে একটি বিশেষ মাত্রা দিয়েছে।
ইসরায়েলের আইনপদ্ধতি মূলত তিনটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—ইংরেজ কমন ল, ইউরোপীয় সিভিল ল এবং ইহুদি হালাখা আইন। এই তিন ধারার সমন্বয়ে একটি অনন্য আইনতাত্ত্বিক কাঠামো গঠিত হয়েছে, যেখানে ‘স্টারে ডেসিসিস’ অর্থাৎ বিচারিক নজির অনুসরণের নীতিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। মামলাগুলি পেশাদার বিচারকদের দ্বারা পরিচালিত হয়; জুরির কোনো ভূমিকা এখানে নেই, যা অনেক পশ্চিমা দেশের বিচারব্যবস্থার তুলনায় এক ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য।
যেহেতু ইসরায়েল একটি ধর্মভিত্তিক সমাজ কাঠামোর মধ্যে গড়ে উঠেছে, তাই পারিবারিক আইন—বিশেষ করে বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ—ধর্মীয় আদালতের অধীন। ইহুদি, মুসলিম, দ্রুজ এবং খ্রিস্টান প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় আদালত রয়েছে, যারা শুধুমাত্র ধর্মীয় আইনের ভিত্তিতে এই বিষয়গুলো নিষ্পত্তি করে। ফলে, বেসামরিক বিবাহ বা আন্তঃধর্মীয় বিবাহ ইসরায়েলে এখনো আইনত স্বীকৃত নয়, যা ইহুদি গণতন্ত্র হিসেবে পরিচিত রাষ্ট্রটির একটি অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব।
বিচারকদের নিয়োগ একটি নির্দিষ্ট বিচারপতি নির্বাচন কমিটির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, যার নেতৃত্ব দেন ন্যায়বিচার মন্ত্রী। এই কমিটিতে সংসদ সদস্য, আইনজীবী এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারকরাও অন্তর্ভুক্ত থাকেন, যা একদিকে বিচারব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করলেও, সমালোচকরা মাঝে মাঝে এর রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।
ইসরায়েলের মৌলিক আইন: মানব মর্যাদা ও স্বাধীনতা ১৯৯২ সালে গৃহীত হয় এবং এটি মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য নথি হিসেবে বিবেচিত হলেও, তাতে “সমতা” বা “বৈষম্যহীনতা”-এর কোনো সুস্পষ্ট ধারা নেই। এই সীমাবদ্ধতা জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল এবং একাধিক স্বাধীন সংস্থা প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। এটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন প্রশ্ন আসে ইসরায়েলি আরব বা সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রসঙ্গে।
অধিকৃত অঞ্চলের ক্ষেত্রে, এনক্লেভ আইন অনুসারে, পশ্চিম তীর বা জুডিয়া-সামারিয়ার কিছু এলাকায় বসবাসকারী ইসরায়েলি নাগরিকদের উপরও ইসরায়েলের দেওয়ানি আইন প্রযোজ্য। ফলে এই অঞ্চলগুলো একধরনের দ্বৈত আইনি বাস্তবতা সৃষ্টি করে—একদিকে ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য সামরিক প্রশাসন, অন্যদিকে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের জন্য দেওয়ানি আদালতের অধিকার। এই ব্যবস্থাটি আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে, কারণ এটি আইনগত বৈষম্যের জন্ম দেয়।
সার্বিকভাবে, ইসরায়েলের বিচারব্যবস্থা একটি জটিল, বহুস্তরীয় ও বহু উৎস নির্ভর কাঠামো—যা একদিকে ধর্মীয় ঐতিহ্যকে ধারণ করে, আবার অন্যদিকে আধুনিক গণতান্ত্রিক আইনের বিভিন্ন রূপকে আত্মস্থ করে। তবে এই ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত আছে কিছু মৌলিক প্রশ্ন, যেগুলো রাষ্ট্র ও জনগণের মাঝে সমতার ভিত্তিতে ন্যায়বিচারের সম্পর্ককে বারবার চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়।
অর্থনীতি
বিশ্বের নানা প্রান্তে যখন অর্থনৈতিক অস্থিরতা, রাজস্ব ঘাটতি কিংবা বিনিয়োগে আস্থার অভাব লক্ষ্য করা যায়, তখন পশ্চিম এশিয়ার মধ্যেই দাঁড়িয়ে এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ইসরায়েল। দেশটির সামান্য ভূখণ্ড এবং সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও, ইসরায়েল বর্তমানে এই অঞ্চলের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও শিল্পোন্নত অর্থনীতির অধিকারী। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইসরায়েলের মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) দাঁড়ায় ৫২১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, এবং মাথাপিছু উৎপাদন ৫৩,২০০ ডলার ছাড়িয়ে যায়—যা একে বিশ্বের ১৩তম ধনী অর্থনীতির কাতারে নিয়ে আসে।
এশিয়া মহাদেশে নামমাত্র মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে ইসরায়েল জাপান ও সিঙ্গাপুরের পর তৃতীয় অবস্থানে অবস্থান করছে। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর তুলনায়, ইসরায়েল শুধুমাত্র মাথাপিছু আয় নয়, সম্পদের বৈষম্য এবং গড় সম্পদের পরিমাণেও শীর্ষস্থানীয়। দ্য ইকোনমিস্ট ২০২২ সালে উন্নত দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক সফলতার বিচারে ইসরায়েলকে চতুর্থ স্থানে রেখেছে, যা এর টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং উদ্ভাবনী সক্ষমতার প্রমাণ বহন করে।
বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে সবচেয়ে বেশি বিলিয়নিয়ার ইসরায়েলেই বাস করেন, যা এ অঞ্চলে এর অর্থনৈতিক আধিপত্যকে আরও জোরালোভাবে তুলে ধরে। বিশ্বের স্কেলেও এদিক থেকে এটি ১৮তম স্থানে রয়েছে। এমন এক সময়ে যখন অনেক উন্নত দেশের প্রবৃদ্ধি স্থবিরতায় ভুগছে, তখন ইসরায়েল ধারাবাহিকভাবে উচ্চ প্রবৃদ্ধির হার বজায় রেখেছে। ২০১০ সালে ইসরায়েল অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা (OECD)-তে যোগ দেয়, যা উন্নত অর্থনীতিগুলোর একটি অভিজাত সংস্থা হিসেবে বিবেচিত।
বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেস রিপোর্টে ইসরায়েলের অবস্থান ২০তম এবং বিশ্ব ব্যাংকের ‘Ease of Doing Business’ সূচকে ৩৫তম। তবে এই পরিসংখ্যানগুলো প্রায়শই গোলান মালভূমি, পূর্ব জেরুজালেম এবং পশ্চিম তীরের ইসরায়েলি বসতি অন্তর্ভুক্ত করে, যা আন্তর্জাতিকভাবে বিতর্কিত।
স্বল্প প্রাকৃতিক সম্পদের দেশ হয়েও ইসরায়েল কৃষি ও শিল্প খাতে চমৎকার সাফল্য অর্জন করেছে। খাদ্য উৎপাদনে দেশটি স্বনির্ভর হলেও কিছু নির্দিষ্ট খাদ্যপণ্য, বিশেষত শস্য ও গরুর মাংস, আমদানির উপর নির্ভর করে। ২০২০ সালে ইসরায়েলের আমদানির পরিমাণ ছিল ৯৬.৫ বিলিয়ন ডলার, যেখানে কাঁচামাল, সামরিক সরঞ্জাম, জ্বালানি ও ভোগ্যপণ্য প্রধান ভূমিকা পালন করে। একই বছরে রপ্তানির অঙ্ক দাঁড়ায় ১১৪ বিলিয়ন ডলার, যার মধ্যে প্রযুক্তি সরঞ্জাম, হীরা, রাসায়নিক দ্রব্য, কৃষিপণ্য ও সফটওয়্যার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
ইসরায়েলের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ বর্তমানে ২০১ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা বিশ্বের মধ্যে ১৭তম বৃহৎ রিজার্ভ। ১৯৭০-এর দশক থেকে ইসরায়েল মার্কিন সামরিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা পেয়ে আসছে, যার ফলে বৈদেশিক ঋণের চাপ তুলনামূলকভাবে সীমিত থেকেছে। ২০১৫ সালে দেশটি নেট বৈদেশিক ঋণে ৬৯ বিলিয়ন ডলারের উদ্বৃত্ত সহ ঋণদাতা দেশের তালিকায় উঠে আসে।
উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ইসরায়েলকে প্রায়শই “স্টার্টআপ নেশন” নামে ডাকা হয়। এটি যুক্তরাষ্ট্রের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক স্টার্টআপের দেশ, এবং NASDAQ-এ তালিকাভুক্ত বিদেশি কোম্পানির সংখ্যায় তৃতীয়। মাথাপিছু স্টার্টআপের হিসেবে ইসরায়েল বিশ্বে এক নম্বরে। ইন্টেল ও মাইক্রোসফট তাদের প্রথম বিদেশি গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র ইসরায়েলেই স্থাপন করেছিল। আজকের দিনে গুগল, অ্যাপল, আইবিএম সহ অসংখ্য বহুজাতিক প্রযুক্তি কোম্পানি ইসরায়েলের মাটিতে তাদের গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র গড়ে তুলেছে।
কর্মদিবসের নিয়মেও ইসরায়েল একটু ব্যতিক্রমী। দেশের অফিস আদালত ও শিল্প খাতে কাজের সপ্তাহ রবিবার থেকে শুরু হয়ে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চলে। কিছু এলাকায় শুক্রবার অর্ধদিবস কর্মদিবস হিসেবে গণ্য হয়, কারণ শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে শনি সন্ধ্যা পর্যন্ত ‘শাব্বাত’ বা ইহুদি ধর্মীয় বিশ্রামের দিন পালিত হয়। বিশ্বব্যাপী মানানসই কর্মসপ্তাহের সঙ্গে সাযুজ্য বজায় রাখতে এই নিয়মে পরিবর্তনের প্রস্তাবও মাঝেমধ্যে তোলা হয়।
সবমিলিয়ে, ইসরায়েলের অর্থনীতি আজ এক জটিল কিন্তু গতিশীল কাঠামো—যেখানে প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, কৃষি এবং বৈদেশিক সহযোগিতা এক অভূতপূর্ব ভারসাম্য তৈরি করেছে। চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও, দেশটি যে গতিতে এগোচ্ছে, তা আগামী দিনের পশ্চিম এশিয়ার অর্থনৈতিক মানচিত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে—এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনের জগতে ইসরায়েল নিজেকে একটি ব্যতিক্রমী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে—যেখানে সীমিত ভূপ্রকৃতি কিংবা প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্পতা কখনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। আজকের দিনে দেশটি যেভাবে প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, গবেষণা, এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বিশ্ব নেতৃত্ব দিচ্ছে, তা এক কথায় অভূতপূর্ব। সফটওয়্যার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, এবং জীবনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসরায়েল বহুদিন ধরেই বিশ্বদরবারে ‘মধ্যপ্রাচ্যের সিলিকন ভ্যালি’ হিসেবে স্বীকৃত।
বিশ্বের যে ক’টি দেশ GDP-র সর্বোচ্চ শতাংশ গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করে, ইসরায়েল তাদের মধ্যে প্রথম সারিতে—প্রকৃতপক্ষে, এটি বিশ্বে এক নম্বরে। এরই স্বীকৃতি হিসেবে ২০২৪ সালের গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্সে দেশটি ১৫তম এবং ব্লুমবার্গ ইনোভেশন ইনডেক্সে ৫ম অবস্থানে পৌঁছেছে। প্রতি ১০,০০০ কর্মচারীর মধ্যে ১৪০ জন বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী বা প্রযুক্তিবিদ—এই অনুপাত বিশ্বে আর কোথাও দেখা যায় না। প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে এই ‘মানবসম্পদ’ ইসরায়েলের প্রকৃত শক্তি।
বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ইসরায়েল বিশেষ করে রসায়নবিদ্যায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছে। ২০০৪ সাল থেকে দেশটি ছয়জন নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী তৈরি করেছে। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশের অনুপাতে ইসরায়েল একাধিকবার শীর্ষে থেকেছে। উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোর দিক থেকেও দেশটির অবস্থান ঈর্ষণীয়—বিশ্বের সেরা ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় টেকনিয়ন, তেল আবিব বিশ্ববিদ্যালয়, হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় ও ওয়েইজম্যান ইনস্টিটিউট বিভিন্ন বিভাগে স্থান করে নিয়েছে।
মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রেও ইসরায়েল নিজেদের সক্ষমতা প্রমাণ করেছে। ১৯৮৮ সালে শাভিত উৎক্ষেপণযানের মাধ্যমে নিজস্ব স্যাটেলাইট মহাকাশে প্রেরণ করে, ইসরায়েল হয়ে ওঠে বিশ্বের অষ্টম উৎক্ষেপণক্ষম দেশ। মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক, গবেষণা এবং গোয়েন্দা উপগ্রহ তৈরি ও পরিচালনায় দেশটির পদচারণা উল্লেখযোগ্য। ইলান রামন, কলম্বিয়া স্পেস শাটলে ইসরায়েলের প্রথম মহাকাশচারী হিসেবে মিশনে অংশ নিয়ে দেশের গর্ব বহুগুণে বাড়িয়ে তোলেন।
অন্যদিকে, মরুপ্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায়, ইসরায়েলকে বরাবরই পানি সংকটের মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিন্তু সীমাবদ্ধতাই সেখানে উদ্ভাবনের জন্ম দিয়েছে। আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় ব্যবহৃত ড্রিপ সেচ পদ্ধতির উদ্ভবই হয়েছে এই দেশে। এছাড়া লবণাক্ত পানি শোধন ও পুনর্ব্যবহারের প্রযুক্তিতে ইসরায়েল এখন বিশ্বের অগ্রগণ্য। ২০১৫ সালের মধ্যে গৃহস্থালি ও শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রায় ৫০ শতাংশ জল কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন হয়েছে। বিশ্বের বৃহত্তম সমুদ্রজলের শোধনাগার ‘সোরেক’ আজ ইসরায়েলের এই প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। আশাবাদী পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০৫০ সালের মধ্যে শোধিত জল দেশটির প্রায় ৭০% পানীয় জলের চাহিদা পূরণ করবে।
জল ব্যবস্থাপনার এই সাফল্য ইসরায়েলকে প্রযুক্তি-নির্ভর পানির রপ্তানিকারক দেশে পরিণত করেছে। শুধু তাই নয়, রিভার্স অসমোসিস প্রযুক্তিতে উদ্ভাবনী অগ্রগতির ফলে ২০১১ সালেই পানিসংশ্লিষ্ট শিল্পের বার্ষিক বাজারমূল্য ২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছিল।
পরিবেশ ও নবায়নযোগ্য শক্তির প্রশ্নেও দেশটি পিছিয়ে নেই। সৌরশক্তির ব্যবহারকে প্রাত্যহিক জীবনের অংশ করে তোলার ক্ষেত্রে ইসরায়েল একটি আদর্শ দেশ। আজ দেশটির প্রায় ৯০ শতাংশ বাড়ি গরম জলের জন্য সৌরশক্তি ব্যবহার করে—যা বৈশ্বিক তুলনায় সর্বোচ্চ। এছাড়া নেগেভ মরুভূমির বিশাল সৌর বিকিরণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে গড়ে উঠেছে এক উন্নত সৌর গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র, যা আন্তর্জাতিক প্রকল্পেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।
সৌরশক্তির ব্যবহার ইসরায়েলের বিদ্যুৎ চাহিদার ৮ শতাংশ হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে। যদিও বৈদ্যুতিক যানবাহনের প্রাথমিক উদ্যোক্তা ‘Better Place’ কোম্পানিটি ২০১৩ সালে বন্ধ হয়ে যায়, তবুও দেশটির চার্জিং স্টেশনের অবকাঠামো এবং বৈদ্যুতিক পরিবহনের স্বপ্ন এখনও ততটা ক্ষীণ হয়ে যায়নি।
সবমিলিয়ে ইসরায়েল কেবল প্রযুক্তি-নির্ভর উন্নয়নের এক রূপরেখা নয়, বরং তা হয়ে উঠেছে অনুপ্রেরণার এক প্রতিচ্ছবি। বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনের হাত ধরে সীমাবদ্ধতাকে সম্ভাবনায় রূপান্তর করার এই উদাহরণটি বিশ্বে আর খুব বেশি দেখা যায় না।
শক্তি
শক্তি নির্ভরতার ইতিহাসে ইসরায়েল এক অনন্য অধ্যায় রচনা করেছে—একটি দেশ, যার নিজের তেল বা প্রাকৃতিক গ্যাসের জোরালো ভাণ্ডার একসময় ছিল না, সেই দেশই আজ শক্তি নিরাপত্তা এবং রপ্তানির প্রশ্নে নিজস্ব অবস্থান গড়ে তুলতে পেরেছে। বিগত দুই দশকে, দেশটির উপকূলীয় গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার ও উৎপাদন কার্যক্রমের মাধ্যমে শক্তির অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রেও ইসরায়েল এক বিশাল অগ্রগতি অর্জন করেছে।
২০০৪ সালে ইসরায়েল তার উপকূলীয় গ্যাসক্ষেত্র থেকে প্রথম প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন শুরু করে। এরপর ২০০৯ সালে আবিষ্কৃত হয় তামার (Tamar) গ্যাসক্ষেত্র এবং ২০১০ সালে লেভিয়াথান (Leviathan) নামের আরও বৃহৎ গ্যাসক্ষেত্রের সন্ধান মেলে। তামার গ্যাসক্ষেত্রের উৎপাদন বাণিজ্যিকভাবে শুরু হয় ২০১৩ সালে, যেখানে বার্ষিক উৎপাদন ৭.৫ বিলিয়ন ঘন মিটার (BCM) ছাড়িয়ে যায়। লেভিয়াথান থেকে গ্যাস উত্তোলন শুরু হয় ২০১৯ সালে, এবং এই গ্যাসক্ষেত্রটির সম্ভাবনা আরও বিস্তৃত—যা শুধু অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণেই নয়, বরং আঞ্চলিক রপ্তানি বাজারেও ইসরায়েলকে শক্তিশালী ভূমিকা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।
২০১৬ সালের তথ্য অনুযায়ী, ইসরায়েলের নিশ্চিত গ্যাস রিজার্ভ প্রায় ১৯৯ বিলিয়ন ঘন মিটার, যা বর্তমান চাহিদা ও রপ্তানির গতি বজায় থাকলে অন্তত ৫০ বছর পর্যন্ত গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারে। এই গ্যাসক্ষেত্রগুলোর মাধ্যমে জ্বালানির ক্ষেত্রে দেশের নির্ভরতা আমদানির উপর থেকে কমেছে, যা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য এক যুগান্তকারী পরিবর্তন।
শুধু প্রাকৃতিক গ্যাস নয়, নবায়নযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রেও ইসরায়েল সাহসী ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০১১ সালে অ্যারাভা পাওয়ার কোম্পানির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ‘কেতুরা সান’ ছিল দেশের প্রথম বাণিজ্যিক সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র। এই সৌর প্রকল্পে ব্যবহৃত হয়েছে সানটেক নির্মিত প্রায় ১৮,৫০০টি ফটোভোলটাইক (PV) প্যানেল, যা প্রতি বছর আনুমানিক ৯ গিগাওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম।
এই সৌর ক্ষেত্রের সর্বাধিক তাৎপর্য, শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদনে নয়, বরং এর পরিবেশগত প্রভাবেও নিহিত। পরবর্তী দুই দশকে এই প্রকল্প একাই প্রায় ১,২৫,০০০ মেট্রিক টন কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন প্রতিরোধে সাহায্য করবে বলে ধারণা করা হয়েছে—যা একটি শক্তিশালী জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বিবেচ্য।
উপকূলীয় গ্যাসক্ষেত্র ও সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের সমন্বয়ে ইসরায়েল এখন এমন এক শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছেছে, যেখানে জ্বালানি নিরাপত্তা, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক লাভ—তিনটিই পরস্পরকে শক্তিশালী করছে। একসময় আমদানি-নির্ভর দেশ আজ নিজের শক্তিতে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে চলেছে, একটি টেকসই ও উদ্ভাবনী শক্তি অর্থনীতির দৃষ্টান্ত হয়ে।
পরিবহন
ইসরায়েলের পরিবহন অবকাঠামো মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম উন্নত ও সংগঠিত বলে বিবেচিত হয়, যদিও এর ভৌগোলিক পরিসর তুলনামূলকভাবে ছোট। সড়ক, রেল, বিমান ও সমুদ্র—চারটি প্রধান ক্ষেত্রেই দেশটি ধারাবাহিকভাবে বিনিয়োগ ও আধুনিকীকরণের মাধ্যমে নিজেদের গতিশীল ও টেকসই যোগাযোগ ব্যবস্থায় রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম হয়েছে।
দেশটির মোট ১৯,২২৪ কিলোমিটার পেভড সড়ক রয়েছে, যার মাধ্যমে বিভিন্ন শহর, গ্রাম এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলো সংযুক্ত। ইসরায়েলে বর্তমানে প্রায় ৩ মিলিয়ন মোটরযান চলাচল করে, কিন্তু মাথাপিছু মোটরযানের অনুপাত এখনো তুলনামূলকভাবে কম—প্রতি ১,০০০ জন মানুষের জন্য মাত্র ৩৬৫টি মোটরযান। এই পরিসংখ্যান উন্নত বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় পিছিয়ে থাকলেও, একে পরিবেশবান্ধব যাতায়াত ও ভিড় কমানোর দিক থেকে ইতিবাচক নজির হিসেবে দেখা যায়।
সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের রাস্তায় চলাচলকারী গাড়ির ৩০ শতাংশকে বৈদ্যুতিক যানবাহনে রূপান্তরের লক্ষ্য স্থির করেছে। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য সরকার ইলেকট্রিক গাড়ির চার্জিং স্টেশন স্থাপন, ট্যাক্স ছাড়, ও অবকাঠামো উন্নয়নের উপর জোর দিয়েছে। একইসঙ্গে, ইসরায়েল শহরাঞ্চলে গণপরিবহন ব্যবস্থাকে আরও বিস্তৃত ও আধুনিক করে তুলতে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে।
ইসরায়েলের গণপরিবহন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো বাস পরিষেবা। দেশটিতে ৫,৭১৫টি বাস নিয়মিতভাবে নির্ধারিত রুটে যাত্রী পরিবহন করে, যার বেশিরভাগই পরিচালনা করে ‘এগেড’ নামে পরিচিত বৃহত্তম পরিবহন সংস্থা। এই কোম্পানিটি ইসরায়েলের প্রায় প্রতিটি শহর এবং নগরাঞ্চলে নিয়মিত ও নির্ভরযোগ্য সেবা প্রদান করে আসছে। এছাড়াও অন্যান্য ছোট পরিবহন সংস্থাগুলোও অঞ্চলভেদে তাদের সেবা দিয়ে থাকে।
রেল যোগাযোগের দিক থেকেও ইসরায়েল উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। দেশটির রেলপথ বর্তমানে ১,২৭৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং এগুলির পরিচালনা করে রাষ্ট্রায়ত্ত ইসরায়েল রেলওয়ে। নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে এই খাতে সরকার বড় পরিমাণে বিনিয়োগ করেছে, যার ফলস্বরূপ রেলপথে যাত্রী চলাচলের সংখ্যা ১৯৯০ সালে ২৫ লাখ থেকে বেড়ে ২০১৫ সালে ৫৩ মিলিয়নে পৌঁছায়। এছাড়াও, প্রতি বছর গড়ে ৭.৫ মিলিয়ন টন পণ্য রেলপথে পরিবহন করা হয়, যা দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপে এক বিশাল ভূমিকা রাখে। নতুন ট্রেন লাইন, আধুনিক রেল স্টেশন এবং দ্রুতগামী ট্রেন চালুর মাধ্যমে এই খাতকে আরও কর্মক্ষম ও লাভজনক করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
আকাশপথে যাতায়াতের প্রধান কেন্দ্র হলো তেল আবিবের নিকটে অবস্থিত বেন গুরিয়ন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, যা আকারে এবং যাত্রীসংখ্যার দিক থেকে দেশের সর্ববৃহৎ বিমানবন্দর। ২০২৩ সালে এই বিমানবন্দরটি ২১.১ মিলিয়নেরও বেশি যাত্রীর সেবা প্রদান করেছে। এ ছাড়াও, দক্ষিণের রামন বিমানবন্দর এবং উত্তরাঞ্চলের হাইফা বিমানবন্দর স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক উড়ানে অবদান রাখে। ইসরায়েলের বিমানবন্দরগুলো নিরাপত্তা ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার জন্য আন্তর্জাতিক মহলে প্রশংসিত।
সমুদ্রপথে বাণিজ্য ও পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে দেশের তিনটি প্রধান বন্দর—হাইফা, আশদোদ এবং এইলাত—গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হাইফা বন্দর, যেটি সবচেয়ে পুরোনো এবং বৃহৎ, দেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত এবং এটি ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। আশদোদ বন্দর তুলনামূলকভাবে নতুন হলেও উচ্চ কার্যক্ষমতা ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দেশীয় বাণিজ্যে অনন্য। লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত এইলাত বন্দর দক্ষিণে অবস্থিত হওয়ায় তা এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের জন্য কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ।
সড়ক, রেল, বিমান ও সমুদ্র—এই চারটি স্তম্ভকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ইসরায়েলের সমন্বিত যোগাযোগব্যবস্থা দেশটির অভ্যন্তরীণ গতি, বৈদেশিক বাণিজ্য ও কৌশলগত প্রস্তুতির একটি মজবুত ভিত্তি তৈরি করেছে। দেশের উন্নয়ন নীতিমালার সঙ্গে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির সমন্বয়, নিরাপত্তা এবং উদ্ভাবনী দৃষ্টিভঙ্গি মিলিয়ে ইসরায়েল যোগাযোগ খাতেও মধ্যপ্রাচ্যে এক ব্যতিক্রমী উদাহরণ হয়ে উঠেছে।
পর্যটন
ইসরায়েলে পর্যটন শিল্প শুধু অর্থনৈতিক সঞ্চালন নয়, বরং ইতিহাস, ধর্ম এবং ভূরাজনীতির এক অনন্য সংমিশ্রণ হিসেবে গুরুত্ব বহন করে। নানা সময়ে যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক চাপ সত্ত্বেও ইসরায়েল প্রতিনিয়ত বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আসা ভ্রমণপ্রেমী এবং তীর্থযাত্রীদের স্বাগত জানিয়ে এসেছে। এখানে পর্যটনের প্রধান আকর্ষণ ধর্মীয় তীর্থস্থান হলেও এর বাইরেও সমুদ্রতট, মরুভূমি, প্রাকৃতিক সংরক্ষণাগার, প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মানুষকে আকৃষ্ট করে।
তেল আবিবের সমুদ্রসৈকত ও আধুনিক নগরজীবন, হাইফার পাহাড়ি দৃশ্য, নাজারেথের খ্রিস্টীয় ঐতিহ্য, বেথলেহেম ও হিব্রনের বাইবেলসংশ্লিষ্ট স্থান, আর সর্বোপরি জেরুজালেমের পুরোনো শহর—এই সব মিলিয়ে ইসরায়েল এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার দেশ। জেরুজালেম শহরেই আছে তিনটি প্রধান আব্রাহামিক ধর্ম—ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম—এর পবিত্র স্থান। এখানে পশ্চিম প্রাচীর (ওয়েস্টার্ন ওয়াল), চার্চ অফ দ্য হলি সেপালখর, এবং আল-আকসা মসজিদ একই শহরের বুকে যুগপৎ অবস্থান করছে—যা বিশ্বে বিরল।
২০১৭ সালে প্রায় ৩৬ লক্ষ আন্তর্জাতিক পর্যটক ইসরায়েল সফর করেছিলেন, যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ২৫ শতাংশ বেশি। এই বৃদ্ধির ফলে সরকার ও বেসরকারি পর্যটন খাত প্রায় ২০ বিলিয়ন শেকেল রাজস্ব অর্জন করে। ইসরায়েলি সরকার পর্যটনকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচনা করে এবং এই খাতে প্রচুর বিনিয়োগ ও আন্তর্জাতিক প্রচারণা চালিয়ে থাকে। বিমান চলাচল সহজতর করা, অন-অ্যারাইভাল ভিসা সুবিধা, এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার মাধ্যমে পর্যটকদের আকৃষ্ট করা হয়েছে।
ইসরায়েল পর্যটকদের জন্য সারা বছরজুড়ে উপযোগী এক গন্তব্য। শীতকালে ডেড সি এবং দক্ষিণাঞ্চলের এইলাত শহরে উষ্ণ আবহাওয়া মানুষকে টানে, আবার গ্রীষ্মকালে ভূমধ্যসাগরের সৈকত ও পাহাড়ি অঞ্চলগুলো ভ্রমণকারীদের স্বর্গ হয়ে ওঠে। দেশটির ঐতিহাসিক শহরগুলোর অলিগলিতে ঘুরে বেড়ানো মানে হাজার বছরের ইতিহাসকে নিজের চোখে দেখা।
ইসরায়েলের পর্যটন খাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল চিকিৎসা পর্যটনের বিকাশ। বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে মানুষ উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, বিশেষত রেডিওথেরাপি ও পুনর্বাসন চিকিৎসার জন্য ইসরায়েলে আসে। ডেড সি অঞ্চলের খনিজ-সমৃদ্ধ জলের জন্য চর্মরোগসহ নানা স্বাস্থ্য সমস্যার চিকিৎসায় এখানে আসা পর্যটকদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও সোশ্যাল মিডিয়ার প্রচারের মাধ্যমে ইসরায়েল তার পর্যটন গন্তব্যগুলোকে নতুন করে তুলে ধরছে। ‘হোলি ল্যান্ড’ শুধু ধর্মপ্রাণ মানুষের গন্তব্য নয়, বরং ইতিহাস, প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও আধুনিক জীবনের এক আশ্চর্য মেলবন্ধন, যা ইসরায়েলকে পর্যটনের মানচিত্রে আরও দৃঢ়ভাবে স্থাপন করছে।
ভূসম্পত্তি
ইসরায়েল আজ শুধু পশ্চিম এশিয়ার নয়, বরং বিশ্বের অন্যতম ব্যয়বহুল আবাসন বাজারের একটি মুখ। একটি সাধারণ অ্যাপার্টমেন্ট কেনার জন্য ইসরায়েলি নাগরিককে গড়ে প্রায় ১৫০ মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়—যা বিশ্বে আবাসন ব্যয়বহুলতার দিক থেকে তৃতীয় অবস্থানে দাঁড় করায় দেশটিকে। ২০২২ সালের হিসাব অনুযায়ী, ইসরায়েলে প্রায় ২৭ লক্ষ আবাসন সম্পত্তি নিবন্ধিত, এবং প্রতিবছর নতুন করে প্রায় ৫০ হাজার আবাসন প্রকল্প যুক্ত হলেও, বাজারে চাহিদার তুলনায় সরবরাহের ঘাটতি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ২০২১ সালে এই ঘাটতির পরিমাণ ছিল আনুমানিক ২ লক্ষ অ্যাপার্টমেন্ট। এই ঘাটতির প্রেক্ষিতে, একই বছরে গৃহমূল্য বেড়েছে গড়ে ৫.৬ শতাংশ।
চাহিদার এই উর্ধ্বগতি কেবল বাজারে মূল্যের চাপই বাড়ায়নি, বরং মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে গৃহস্বপ্নকে অনেকাংশেই দূরের করে দিয়েছে। ২০২১ সালে ইসরায়েলিরা ১১৬.১ বিলিয়ন শেকেলেরও বেশি পরিমাণ ঋণ নিয়ে মর্টগেজ গ্রহণ করে, যা আগের বছরের তুলনায় ৫০ শতাংশ বেশি। এই ঋণের প্রবণতা ইঙ্গিত দেয় যে, নাগরিকদের স্বপ্নের বাড়ি ক্রয় করতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বড় ঋণের দ্বারস্থ হতে হয়।
অন্যদিকে, জনসংখ্যাগত দিক থেকে ইসরায়েল বিশ্বের একমাত্র রাষ্ট্র, যেখানে ইহুদিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ২০২৪ সালের মে মাসে দেশটির জনসংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৯৯ লক্ষের কাছাকাছি। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, এদের মধ্যে ৭৩.৬ শতাংশ ইহুদি, ২১.১ শতাংশ আরব এবং বাকি ৫.৩ শতাংশ অন্যান্য—যাদের মধ্যে কেউ কেউ ধর্মনিরপেক্ষ, কেউ আরব নন-খ্রিস্টান। নানা প্রেক্ষাপটে, এই জনসংখ্যাগত বিন্যাস ইসরায়েলি রাজনীতির কেন্দ্রীয় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।
বিভিন্ন সময়ে ইসরায়েলে অভিবাসনের ঢেউ এসেছে, যার মধ্যে ১৯৪৯ এবং ১৯৯০ সালের সোভিয়েত পতনের পরবর্তী সময় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপ, রাশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, থাইল্যান্ড, চীন থেকে আগত অভিবাসী কর্মীরা বর্তমানে শহরাঞ্চলের নানা খাতে কাজ করছেন। তাদের সংখ্যা আনুমানিক ১.৬ থেকে ২ লক্ষের মধ্যে বলে ধারণা করা হয়, যদিও এদের একটি বড় অংশ সরকারি নথিতে নেই। ২০১২ সালের জুন পর্যন্ত শুধু আফ্রিকান অভিবাসীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০,০০০।
ইসরায়েলের জনসংখ্যার প্রায় ৯৩ শতাংশ শহরাঞ্চলে বাস করে, যা দেশটির উচ্চ নগরায়নের পরিচয় বহন করে। আরব-ইসরায়েলিরা মূলত গ্যালিলি, ট্রায়াঙ্গেল এবং নেগেভ অঞ্চলের ১৩৯টি আরব প্রধান শহর ও গ্রামে বসবাস করে; মাত্র ১০ শতাংশ মিশ্র অঞ্চল বা শহরে বসবাস করে। গড় আয়ু ইসরায়েলে তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ—৮২.৫ বছর, যা OECD-এর মধ্যে ষষ্ঠ সর্বোচ্চ। যদিও আরব জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এই গড় তিন থেকে চার বছর কম, তবুও মুসলিম দেশগুলোর তুলনায় এটি অনেক বেশি। জন্মহার দিক থেকেও ইসরায়েল OECD-এর মধ্যে সর্বোচ্চ, এবং একমাত্র দেশ যেখানে এই হার প্রতিস্থাপন হারের (২.১) চেয়ে বেশি।
দেশের জনসংখ্যা গঠনের পেছনে আশকেনাজি ও সেফারদি বংশের ইহুদি অভিবাসীদের ভূমিকা বিশাল। আশকেনাজিরা মূলত ইউরোপ ও প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আগত, আর সেফারদি ও মিজরাহিরা আরব ও মুসলিম দেশ থেকে এসেছেন। বর্তমান স্কুলপড়ুয়া শিশুদের মধ্যে প্রায় এক চতুর্থাংশেরই দুই বংশের অভিন্ন উত্তরাধিকার রয়েছে। ধর্মীয় আইনের পরিপ্রেক্ষিতে যাঁরা ইহুদি হিসেবে গণ্য না হলেও, ল অফ রিটার্ন অনুযায়ী নাগরিকত্ব পেয়েছেন—এমন মানুষের সংখ্যাও কম নয়। এঁদের একটি বড় অংশ রুশ বংশোদ্ভূত।
সবুজ রেখার বাইরে, অর্থাৎ অধিকৃত পশ্চিম তীর, পূর্ব জেরুজালেম এবং গোলান মালভূমির বসতিগুলোতেও বসতি স্থাপনকারী ইহুদিদের সংখ্যা অনেক। ২০১৬ সালের তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ৪ লক্ষ ইসরায়েলি পশ্চিম তীরের বসতিতে বাস করত, পূর্ব জেরুজালেমে প্রায় ২ লক্ষ এবং গোলান মালভূমিতে ২২ হাজারের বেশি। গাজা উপত্যকার গুশ কাটিফে একসময় ৭,৮০০ ইসরায়েলি বাস করলেও, ২০০৫ সালের বিতর্কিত বিচ্ছিন্নকরণ পরিকল্পনার মাধ্যমে তাদের অপসারণ করা হয়।
আরব নাগরিকদের মধ্যেও আত্মপরিচয় নিয়ে বিভাজন রয়েছে। ২০১৭ সালের এক জরিপে দেখা যায়, ৪০ শতাংশ আরব নাগরিক নিজেকে “ইসরায়েলের আরব” বা “আরব নাগরিক” বলে পরিচিত করেন, ১৫ শতাংশ শুধুমাত্র “ফিলিস্তিনি”, ৮.৯ শতাংশ “ইসরায়েলি ফিলিস্তিনি” এবং ৮.৭ শতাংশ নিজেকে শুধু “আরব” বলেন। এই বিবিধ পরিচয়ের রাজনীতির পেছনে ইতিহাস, অভিজ্ঞতা এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের জটিলতা কাজ করে। তবুও, জরিপ অনুযায়ী, প্রায় ৬০ শতাংশ আরব নাগরিক ইসরায়েল রাষ্ট্র সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা পোষণ করেন—যা সমসাময়িক মধ্যপ্রাচ্যের বাস্তবতায় এক গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান।
ইসরায়েল রাষ্ট্র আজ শুধু সামরিক ও প্রযুক্তি নয়, বরং জনসংখ্যা, আবাসন ও অভিবাসনের দিক থেকেও বৈচিত্র্যে ভরপুর এক জটিল সমাজের নাম। এই সমাজের ভেতরকার সমীকরণ যেমন স্পষ্ট নয়, তেমনি তা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। এখানেই ইসরায়েলের রাষ্ট্র-চরিত্র ও ভবিষ্যৎ রাজনীতির প্রাসঙ্গিকতা নিহিত।
প্রধান শহুরে এলাকা
ইসরায়েলের জনবসতির মানচিত্রে চারটি প্রধান মহানগর এলাকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, যেগুলি দেশের অর্থনীতি, প্রশাসন ও সংস্কৃতির চালিকাশক্তি হিসেবেই বিবেচিত। এর মধ্যে সর্ববৃহৎ মহানগর হলো গুশ দান, যা মূলত তেল আভিভ কেন্দ্রিক একটি বিস্তৃত নগরায়ন অঞ্চল। এই মহানগর এলাকায় প্রায় ৩৮.৫ লক্ষ মানুষ বাস করে, যা দেশের সামগ্রিক শহুরে জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশকে ধারণ করে। গুশ দান শুধু জনসংখ্যার ঘনত্ব নয়, বরং ইসরায়েলের বাণিজ্য, প্রযুক্তি এবং সাংস্কৃতিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র হিসেবেও পরিচিত।
দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর অঞ্চল হলো জেরুজালেম, যার নগর সীমার ভেতর বাস করে প্রায় ১২.৫ লক্ষ মানুষ। এটি শুধু ইসরায়েলের রাজধানী নয়, বরং ধর্মীয়, ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকেও এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। জেরুজালেমের জনসংখ্যা ও ভূখণ্ডের হিসাবের মধ্যে পূর্ব জেরুজালেম অন্তর্ভুক্ত, যা আন্তর্জাতিকভাবে বিতর্কিত এলাকা হিসেবে স্বীকৃত। বহু দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এখনো পূর্ব জেরুজালেমকে অধিকৃত অঞ্চল হিসেবেই বিবেচনা করে থাকে।
হাইফা, তৃতীয় বৃহত্তম শহর, ইসরায়েলের অন্যতম প্রধান বন্দরনগরী, যেখানে প্রায় ৯ লক্ষের কাছাকাছি মানুষ বাস করেন। এটি দেশের উত্তরাঞ্চলের প্রধান অর্থনৈতিক কেন্দ্র, পাশাপাশি ইসরায়েলের অন্যতম শিল্পাঞ্চল ও উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। কার্মেল পর্বতের ঢালে অবস্থিত এই শহরটি তার অনন্য ভূপ্রকৃতি, সমুদ্রতট ও মিলিত আরব–ইহুদি বসতির জন্যও আলাদা পরিচিতি পেয়েছে।
চতুর্থ মহানগর হলো বেয়ারশেবা, যা নেগেভ মরুভূমির দরজায় অবস্থিত। এখানে বাস করে প্রায় ৩.৭ লক্ষ মানুষ। দক্ষিণ ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে খ্যাত বেয়ারশেবা এখন প্রযুক্তি ও গবেষণার একটি উঠতি কেন্দ্র, যেখানে ইসরায়েলের অন্যতম বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়—বেন-গুরিয়ন ইউনিভার্সিটি অব দ্য নেগেভ অবস্থিত।
পৌর প্রশাসনের বিচারে, জেরুজালেম ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় পৌরসভা, যার জনসংখ্যা প্রায় ৯.৮ লক্ষ এবং এলাকা ১২৫ বর্গ কিলোমিটার। তার পরে রয়েছে তেল আভিভ, যেখানে প্রায় ৪.৭ লক্ষ মানুষ বাস করেন। হাইফা শহরের জনসংখ্যা ২.৯ লক্ষের কিছু বেশি।
একটি ব্যতিক্রমী শহর হলো বনী ব্রাক, যা দেশের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ শহর এবং বিশ্বে শীর্ষ দশে থাকা নগরগুলোর একটি। এই শহরটি মূলত হারেদি (আল্ট্রা-অর্থোডক্স ইহুদি) জনসংখ্যার জন্য পরিচিত, যেখানে ধর্মীয় জীবন অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং নাগরিক জীবনধারা ধর্মানুবর্তিতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।
ইসরায়েলে মোট ১৬টি শহর আছে যেগুলোর জনসংখ্যা এক লক্ষের বেশি, এবং ২০১৮ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ৭৭টি নগর অঞ্চল বা পৌরসভা সরকারিভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এর মধ্যে চারটি শহর পশ্চিম তীর অঞ্চলে অবস্থিত, যা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে স্পর্শকাতর এবং বিতর্কিত।
এই পৌর কাঠামো ও নগরায়নের গতিপ্রকৃতি ইসরায়েলের সমসাময়িক রাষ্ট্রচরিত্র, অভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিচ্ছবি। এখানে প্রথাগত ধর্মীয় সম্প্রদায়, আধুনিক প্রযুক্তি নগর, পুরাতন ঐতিহ্য এবং নতুন উচ্চাকাঙ্ক্ষা—all একসঙ্গে সহাবস্থান করে, তৈরি করে এক জটিল কিন্তু আকর্ষণীয় নগর-সমাজের রূপরেখা।
ভাষা
ইসরায়েলের ভাষাগত পরিসর তার ইতিহাস, অভিবাসন প্রবাহ এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের একটি জীবন্ত প্রতিফলন। এই রাষ্ট্রের সংবিধানগত ভাষা হিব্রু, যা শুধু প্রশাসনিক বা আনুষ্ঠানিক কার্যকলাপেই নয়, বরং দৈনন্দিন জীবনে জনসাধারণের কথোপকথনেও সবচেয়ে প্রচলিত ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হিব্রুর আধুনিকীকরণ এবং রাষ্ট্রভাষা হিসেবে তার পুনর্জাগরণ ছিল সায়োনিস্ট আন্দোলনের একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প—বিশেষত ‘ইয়িশুভ’ নামক ইহুদি উপনিবেশ গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে, যারা ব্রিটিশ ম্যান্ডেট যুগে প্যালেস্টাইনে বসতি স্থাপন করে।
হিব্রুর উত্থানের বিপরীতে দাঁড়িয়ে ছিল ইয়িদ্দিশ, যা আশকেনাজি ইহুদিদের ঐতিহ্যবাহী ভাষা। কিন্তু হিব্রুকে “নতুন জাতীয় আত্মপরিচয়ের বাহক” হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসে, ইয়িদ্দিশ ভাষা ও সংস্কৃতিকে একধরনের প্রতিক্রিয়াশীল অতীত হিসেবে দেখা হয়। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম দশকে ইয়িদ্দিশ থিয়েটার, প্রকাশনা এমনকি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উপর অনেকাংশে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। এই মনোভাব সায়োনিস্ট আদর্শবাদীদের মধ্যে এতটাই প্রবল ছিল যে, তারা হিব্রুর বিকল্প কোনো ভাষার প্রতি সহনশীল ছিলেন না।
আরবি, যা একসময়ে হিব্রুর পাশাপাশি সরকারিভাবে স্বীকৃত ছিল, ২০১৮ সালে পাস হওয়া “নেশন-স্টেট ল” অনুযায়ী “বিশেষ মর্যাদা” নামক একটি নতুন সাংবিধানিক অবস্থানে নামিয়ে আনা হয়। যদিও আরবি ভাষায় এখনো ইসরায়েলের আরব নাগরিকদের মধ্যে শিক্ষা, গণমাধ্যম এবং বিচারব্যবস্থায় ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে, এই পদক্ষেপটি ইসরায়েলি আরবদের মধ্যে গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং আন্তর্জাতিক মহলেও সমালোচিত হয়। অনেক আরব বিদ্যালয়ে আরবি এবং হিব্রু উভয় ভাষাই শেখানো হয়, এবং কিছু ক্ষেত্রে হিব্রু শেখা বাধ্যতামূলকও।
ভাষার এই বৈচিত্র্য শুধুমাত্র মধ্যপ্রাচ্যীয় সমাজ কাঠামোর ফল নয়, বরং বহিরাগত অভিবাসন প্রবাহের কারণেও সৃষ্ট। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বিপুল সংখ্যক অভিবাসীর আগমন (বিশেষত ১৯৯০-এর দশকে) রাশিয়ান ভাষাকে আজকের ইসরায়েলে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভাষায় পরিণত করেছে। আনুমানিক এক মিলিয়নেরও বেশি রাশিয়ানভাষী আজ দেশটিতে বসবাস করছেন। একইভাবে, ইথিওপিয়া থেকে আগত ইহুদি অভিবাসীদের (ফালাশা বা বেটা ইসরায়েল নামে পরিচিত) কারণে আমহারীয় ভাষার ব্যবহার কিছু এলাকায় ব্যাপক। এই দুই অভিবাসী গোষ্ঠীর জন্য সরকার আলাদা শিক্ষানীতি এবং সমাজসেবার উদ্যোগ নিয়েছে।
ফ্রেঞ্চ ভাষার প্রচলন মূলত ফ্রান্স এবং উত্তর আফ্রিকার মাগরেব অঞ্চলের ইহুদি অভিবাসীদের দ্বারা ঘটেছে। ইসরায়েলের আনুমানিক সাত লাখ মানুষ ফরাসি ভাষায় কথা বলেন বা অন্তত বোঝেন। এই সংখ্যাটি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশেষ করে ২০১০-এর পর থেকে ফ্রান্স থেকে ইহুদি অভিবাসনের হার বেড়ে যাওয়ায়।
ইংরেজি ভাষারও ইসরায়েলি সমাজে একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, যদিও এটি আর সরকারিভাবে স্বীকৃত ভাষা নয়। ব্রিটিশ ম্যান্ডেট আমলে এটি সরকারিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হলেও, স্বাধীনতা-উত্তর কালে তার সেই সাংবিধানিক মর্যাদা রদ করা হয়। তবুও ইংরেজি শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কার্যত একটি ‘ডি-ফ্যাক্টো’ সরকারি ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। স্কুল পর্যায়েই ইংরেজি শিক্ষা শুরু হয়, এবং বেশিরভাগ টেলিভিশন অনুষ্ঠান, বিশেষ করে বিদেশি সিরিজ ও চলচ্চিত্র ইংরেজি ভাষায় সাবটাইটেলসহ প্রচারিত হয়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও ইংরেজি মাধ্যমিক ভাষা হিসেবে বহুল ব্যবহৃত—বিশেষত বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও ব্যবসা প্রশাসনের ক্ষেত্রে।
এই বহুভাষিক পরিবেশ ইসরায়েলি সমাজকে জটিল ও বিচিত্র করে তুলেছে। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে জাতিগত, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের দ্বন্দ্ব যেমন ভাষাগত পরিচয়ে প্রতিফলিত হয়, তেমনি ভাষাই আবার জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেকার সেতুবন্ধন গঠনের একটি সম্ভাবনাও তৈরি করে। ইসরায়েল তাই ভাষা রাজনীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—যেখানে ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং জাতীয় পরিচয়, আধিপত্য এবং অন্তর্ভুক্তির এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষেত্র।
ধর্ম
ইসরায়েল এমন একটি রাষ্ট্র, যেখানে ধর্মীয় পরিচয় কেবল ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয় নয়—এটি একইসঙ্গে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার গভীরে প্রোথিত। ২০২২ সালের হিসাবে, দেশটির জনসংখ্যার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ অর্থাৎ ৭৩.৫% মানুষ নিজেদের ইহুদি হিসেবে চিহ্নিত করেন। কিন্তু এই পরিচয়ের ভেতরেও রয়েছে স্তরবিন্যাস ও বৈচিত্র্য। ২০১৬ সালের পিউ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের একটি জরিপে দেখা যায়, ইসরায়েলি ইহুদিদের মধ্যে ৪৯% নিজেদের হিলোনি বা ধর্মনিরপেক্ষ বলে মনে করেন, ২৯% মাসোর্তি অর্থাৎ ঐতিহ্য সংরক্ষণকারী, ১৩% দাতি বা আধা-ধর্মীয় এবং ৯% হারেদি বা অতি-অর্থডক্স ঘরানার অনুসারী। এই পরিসংখ্যান একটি গতিশীল সমাজ কাঠামোর ইঙ্গিত দেয়, যেখানে ধর্মীয় নিষ্ঠা একটানা নয়, বরং প্রজন্ম, অঞ্চল এবং অভিবাসন অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। হারেদি জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে চলেছে এবং অনুমান করা হয় যে ২০২৮ সালের মধ্যেই ইহুদি জনসংখ্যার অন্তত ২০% হারেদিদের দ্বারা গঠিত হবে।
ইহুদিদের পর, মুসলমানরা ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় সংখ্যালঘু। তারা জনসংখ্যার প্রায় ১৮.১%—প্রধানত আরব বংশোদ্ভূত নাগরিক, যারা বহু প্রজন্ম ধরে এই অঞ্চলে বসবাস করছেন। খ্রিস্টানরা ১.৯% এবং দ্রুজ সম্প্রদায় ১.৬% নিয়ে একেকটি ছোট অথচ সাংস্কৃতিকভাবে প্রভাবশালী গোষ্ঠী। খ্রিস্টানরা প্রধানত আরব খ্রিস্টান এবং অ্যারামীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত, যদিও তাঁদের মধ্যে পোস্ট-সোভিয়েত অভিবাসী, বিদেশী শ্রমিক, এবং মেসিয়ানিক ইহুদিরাও আছেন—যাঁরা খ্রিস্টান বিশ্বাস গ্রহণ করলেও নিজেদের ইহুদি পরিচয় বজায় রাখেন।
এছাড়াও, সামান্যসংখ্যক হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীও ইসরায়েলে বসবাস করছেন—বিশেষত অভিবাসী শ্রমিক ও সাময়িক কর্মরত বিদেশিদের মধ্যে। ধর্মীয় বৈচিত্র্যের আরেকটি জটিল দিক হলো প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আগত প্রায় ১০ লক্ষ অভিবাসীর মধ্যে প্রায় তিন লক্ষ মানুষ ধর্মীয় আইনের ভিত্তিতে ইহুদি হিসেবে গণ্য হন না, যদিও তাঁরা ‘ল অফ রিটার্ন’-এর অধীনে ইসরায়েলি নাগরিকত্ব অর্জন করেছেন। তাঁদের এই ধর্মীয় অনির্ধারিত অবস্থান ইসরায়েলি সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিচয় সংকট তৈরি করেছে।
ধর্ম শুধু সংখ্যা নয়, বরং ইসরায়েলি ভূখণ্ড ও স্থাপত্যেও তার প্রভাব সুগভীর। এই রাষ্ট্রটি এমন এক ভূখণ্ডের উপর গড়ে উঠেছে, যা তিনটি প্রধান আব্রাহামিক ধর্ম—ইহুদি, ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্মের জন্য পবিত্র বলে বিবেচিত। জেরুজালেম শহর এই ত্রিমাত্রিক পবিত্রতার কেন্দ্রবিন্দু। এখানেই রয়েছে ইহুদিদের পবিত্রতম স্থান—ওয়েস্টার্ন ওয়াল বা পশ্চিম প্রাচীর, ইসলামের অন্যতম পবিত্র স্থান আল-আকসা মসজিদ কমপাউন্ড (যা মুসলমানদের কাছে হারাম আল-শরিফ নামে পরিচিত), এবং খ্রিস্টানদের কাছে পবিত্র গবরখানা হিসেবে পরিচিত চার্চ অফ দ্য হোলি সেপুলখার।
এই শহর ছাড়াও, ধর্মীয় ইতিহাসে ঠাঁই করে নেওয়া একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছড়িয়ে আছে গোটা দেশে—নাজরেথ, যেখান থেকে যিশুর কাহিনি শুরু; তিবেরিয়া ও সাফেদ, ইহুদি মিস্টিসিজম বা কাবালার কেন্দ্রস্থল; রামলার ঐতিহাসিক সাদা মসজিদ; লোড শহরের সেন্ট জর্জের চার্চ এবং আল-খদর মসজিদ, যেটি ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিম—তিন ধর্মের অনুসারীদের কাছেই ভক্তির স্থান।
পশ্চিম তীর এবং আশপাশের অঞ্চলও এই ধর্মীয় মানচিত্রে স্থান পেয়েছে। এখানে রয়েছে রাচেলের কবর, যোসেফের সমাধি, পিতৃপুরুষদের গুহা (মাকপেলা), এবং যিশুর জন্মস্থান বেথলেহেম—যা আজও পর্যটক ও তীর্থযাত্রীদের আকর্ষণ করে।
বাহাই ধর্ম, যদিও তুলনামূলকভাবে নতুন, ইসরায়েলে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরি করেছে। বাহাই ধর্মের বিশ্ব প্রশাসনিক কেন্দ্র হাইফায় অবস্থিত এবং বাহাই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বাহা’উল্লাহ আক্রেতে সমাহিত। এই কেন্দ্রটি শুধু বাহাইদের জন্য নয়, ধর্মীয় স্থাপত্যের দৃষ্টিকোণ থেকেও এক বিশেষ আকর্ষণ।
ইসরায়েলের হাইফা শহরে অবস্থিত কাবাবির পাড়া, যেখানে ইহুদি ও আহমদিয়া মুসলিমরা একত্রে বসবাস করেন, সে পাড়াটি ধর্মীয় সহাবস্থানের এক বিরল নিদর্শন। এই এলাকায় অবস্থিত মাহমুদ মসজিদ আহমদিয়া মতবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।
এই ধর্মীয় বৈচিত্র্য শুধু দেশটির অভ্যন্তরীণ সমাজচিত্রে নয়, বরং তার আন্তর্জাতিক পরিচিতিতেও গভীর প্রভাব ফেলেছে। পবিত্র ভূমির এই রাষ্ট্রে, ধর্ম কখনও ঐতিহ্য, কখনও সংঘাত, আবার কখনও সহাবস্থানের গল্প বলেছে—যা ইসরায়েলকে শুধু রাজনৈতিক রাষ্ট্র নয়, বরং বিশ্ব ধর্ম-সভ্যতার এক জটিল, বহুবর্ণ ছায়ামণ্ডল হিসেবে উপস্থাপন করে।
শিক্ষা
প্রাচীন কালের ইসরায়েলি সমাজে শিক্ষা শুধু জ্ঞানার্জনের মাধ্যম ছিল না, বরং একটি মৌলিক সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতীক। ধর্মীয় পাঠ এবং জীবনাচারের গভীরে প্রোথিত এই শিক্ষা-সংস্কৃতি কালক্রমে আধুনিক ইসরায়েলের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এক দৃঢ় ভিত্তি দিয়েছে। সেই ঐতিহ্য অনুসরণ করে, আজকের ইসরায়েল শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বৈশ্বিক পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দখল করে রেখেছে।
২০১৫ সালের হিসাব অনুযায়ী, ২৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী ইসরায়েলিদের মধ্যে প্রায় ৪৯ শতাংশই উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করেছেন—যা ওইসিডির গড় ৩৫ শতাংশের তুলনায় অনেক বেশি। ২০১২ সালে মাথাপিছু একাডেমিক ডিগ্রির সংখ্যায় ইসরায়েল বিশ্বের তৃতীয় স্থানে উঠে আসে। পরিসংখ্যান বলছে, দেশের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ নাগরিকের রয়েছে কোনো না কোনো একাডেমিক ডিগ্রি। এরই সমান্তরালে সাক্ষরতার হার ৯৭.৮ শতাংশে পৌঁছেছে, যা একটি সুসংগঠিত শিক্ষাব্যবস্থার নির্দেশক।
ইসরায়েলের শিক্ষাব্যবস্থা ১৯৫৩ সালের রাষ্ট্র শিক্ষা আইনের মাধ্যমে একটি কাঠামোয় বদ্ধ হয়েছে। পাঁচটি স্বীকৃত ধরণের স্কুল রয়েছে: সাধারণ ধর্মনিরপেক্ষ, রাষ্ট্র-ধর্মীয়, হারেদি বা অতি-অর্থডক্স, সাম্প্রদায়িক বসতির স্কুল এবং আরব স্কুল। এদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ স্কুলগুলো সবচেয়ে বিস্তৃত, যেখানে ইহুদি ও অন্যান্য অ-আরব শিশুদের সংখ্যা সর্বাধিক। আরব নাগরিকরা সাধারণত তাদের সন্তানদের আরব ভাষাভিত্তিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠান। এই বহুস্বর শিক্ষা কাঠামো দেশের জাতিগত ও ধর্মীয় বৈচিত্র্যকে প্রতিফলিত করে।
ইসরায়েলে তিন থেকে আঠারো বছর বয়সী শিশুদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং এটি তিনটি স্তরে বিভক্ত: প্রাথমিক (গ্রেড ১–৬), নিম্ন মাধ্যমিক (গ্রেড ৭–৯) ও উচ্চ মাধ্যমিক (গ্রেড ১০–১২)। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের ‘বাগরুট’ নামক ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। এই পরীক্ষায় গণিত, হিব্রু ভাষা, সাহিত্য, ইংরেজি, ইতিহাস, নাগরিক শিক্ষা এবং বাইবেল—বা আরব ও খ্রিস্টান শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ধর্মীয় ঐতিহ্যভিত্তিক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে।
২০২০ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর হার ছিল ৬৮.৭ শতাংশ, যা দেশটির শিক্ষাক্ষেত্রে ধারাবাহিক উন্নয়নের একটি ইতিবাচক ইঙ্গিত। ইসরায়েলি ইহুদিদের মধ্যে ৪৬ শতাংশ পোস্ট-সেকেন্ডারি ডিগ্রি অর্জন করেছেন, যা গড়ে ১১.৬ বছরের শিক্ষাজীবন নিশ্চিত করে—বিশ্বের ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে অন্যতম উচ্চতম হার।
উচ্চশিক্ষার দিক থেকেও ইসরায়েল বিশ্বে একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। দেশটিতে রয়েছে ৯টি রাষ্ট্র-অনুদানপ্রাপ্ত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৪৯টি স্বীকৃত বেসরকারি কলেজ। এগুলির মধ্যে হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়, টেকনিয়ন, ওয়েইজম্যান ইনস্টিটিউট, তেল আবিব বিশ্ববিদ্যালয়, বেন-গুরিয়ন ইউনিভার্সিটি, বার-ইলান, হাইফা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ওপেন ইউনিভার্সিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় শুধু একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়—এটি জাতীয় গ্রন্থাগারও ধারণ করে, যেখানে জুদাইকা ও হিব্রাইকা চর্চার জন্য বিশ্বের বৃহত্তম সংগ্রহশালা রয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গবেষণা কার্যক্রম নিয়মিতভাবেই আন্তর্জাতিক পরিসরে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে। বিশেষত, টেকনিয়ন ও হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় এআরডব্লিউইউ বা একাডেমিক র্যাংকিং অফ ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটিজ-এ শীর্ষ ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অবস্থান করে, যা গবেষণা, উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি নির্ভর অর্থনীতির ভিত্তি গঠনে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।
সার্বিকভাবে, ইসরায়েলের শিক্ষাব্যবস্থা তার ঐতিহ্য, নীতিমালা এবং সমন্বিত কাঠামোর মাধ্যমে এমন এক অবস্থানে পৌঁছেছে, যেখানে বৈচিত্র্য ও মান একে অপরের সম্পূরক হয়ে উঠেছে। শিক্ষা এখানে কেবল একটি সামাজিক দায় নয়, বরং রাষ্ট্র নির্মাণ ও জাতীয় বিকাশের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার।
সংস্কৃতি
ইসরায়েলের সমাজ ও সংস্কৃতি এক অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় এবং বহুস্তরীয় বিন্যাসের প্রতিচ্ছবি, যা দেশটির অভ্যন্তরীণ জনসংখ্যাগত বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে। বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আগত ইহুদি সম্প্রদায় এখানে এসে শুধু বসতি স্থাপন করেনি, বরং তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় প্রথা এবং জীবনযাত্রার রীতিনীতিকে বহন করে এনেছে—যা মিলেমিশে গড়ে তুলেছে এক নতুন, অথচ বহুধা উৎসসন্ধানী সংস্কৃতিচর্চা।
এই বহুরূপী সংস্কৃতির বুনোটে যেমন ইউরোপীয় আশকেনাজি প্রভাব রয়েছে, তেমনি জায়গা করে নিয়েছে মিজরাহি ও সেফারদি ইহুদিদের ঐতিহ্য, যারা এসেছে মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা ও পারস্য থেকে। এদের প্রতিটি গোষ্ঠীই ইসরায়েলের সমসাময়িক সংস্কৃতিকে বিভিন্ন মাত্রা ও রঙে রাঙিয়ে তুলেছে। যেমন, রান্নায় একদিকে থাকছে পূর্ব ইউরোপীয় লাটকে, কুগেল বা gefilte fish-এর ধারা, অন্যদিকে মিজরাহি ইহুদিদের হাত ধরে এসেছে হরিসা, মালাওহ, জা‘তার আর হমসের মতো আরব ও লেভান্তীয় প্রভাবসম্পন্ন পদ।
সংস্কৃতির এই বহুস্বরতা শুধু খাদ্যাভ্যাসেই সীমাবদ্ধ নয়। স্থাপত্যশৈলীতেও এর প্রতিফলন স্পষ্ট। তেল আভিভের বাউহাউস স্থাপত্য যেমন ইউরোপীয় আধুনিকতাবাদকে ধারণ করে, তেমনি জেরুজালেম বা হাইফার পুরনো শহরগুলিতে রয়েছে ওসমানি ও আরব স্থাপত্যশৈলীর ছাপ। একদিকে কাচ ও স্টিলের আধুনিক ভবন, অন্যদিকে পাথরের প্রাচীন গৃহ—এই সহাবস্থান ইসরায়েলের নগর ও গ্রামীণ স্থাপত্যকে করে তুলেছে অনন্য।
সঙ্গীতক্ষেত্রেও এই বৈচিত্র্য দৃষ্টিগোচর। ইসরায়েলি সঙ্গীতজগৎ মিজরাহি, ইয়েমেনি, বুখারিয়ান, আশকেনাজি এবং এমনকি ইথিওপীয় সুরের সংমিশ্রণে এক নিজস্ব স্বরলিপি নির্মাণ করেছে। স্থানীয় রক ও পপ সঙ্গীতে পাশ্চাত্যের ছাপ থাকলেও, তাতে আরবী বাদ্যযন্ত্র ও ছন্দের অনুপ্রবেশ নতুন মাত্রা এনে দেয়। একইভাবে, লোকসঙ্গীত ও ধর্মীয় সঙ্গীতের ধারা এখনও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে জীবন্ত রয়েছে।
ইসরায়েল বিশ্বের একমাত্র দেশ যেখানে হিব্রু বর্ষপঞ্জিকা সরকারিভাবে ব্যবহৃত হয়, এবং এর প্রভাব দেশের সামাজিক জীবনযাত্রার প্রতিটি স্তরে স্পষ্ট। কর্মজীবন, শিক্ষাবর্ষ, ছুটি ও উৎসব—all হিব্রু ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। ইহুদি ধর্মীয় ছুটিগুলি যেমন রোশ হাশানাহ, ইয়ম কিপুর, পেসাখ বা সুখোত—দেশজুড়ে গভীর ধর্মীয় আবেগ ও সামাজিক সম্প্রীতির সঙ্গে পালিত হয়। শনিবার, অর্থাৎ ‘শাব্বাত’—যা ইহুদি ঐতিহ্যে বিশ্রামের দিন—তা সাপ্তাহিক ছুটি হিসেবে পালিত হয়, এবং এই সময় সরকারি পরিবহন থেকে শুরু করে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানই বন্ধ থাকে।
ইসরায়েলের আরব নাগরিকরা, যারা সংখ্যায় প্রায় ২১ শতাংশ, তাদের সংস্কৃতিও এই সাংস্কৃতিক মিশ্রণে একটি গুরুত্বপূর্ণ সুর সংযোজন করে। তাদের আরবি ভাষা, সঙ্গীত, খাদ্যাভ্যাস এবং ধর্মীয় উৎসব যেমন রমজান ও ঈদ ইসরায়েলি সমাজে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এছাড়াও, বেদুইন জনগোষ্ঠী এবং দ্রুজ সম্প্রদায়ের নিজস্ব লোকজ ও ধর্মীয় ঐতিহ্য, ইসরায়েলের সাংস্কৃতিক মানচিত্রকে করে তুলেছে আরও বহুস্তরীয়।
সার্বিকভাবে, ইসরায়েলের সংস্কৃতি এক বহুধা উৎসনির্ভর রসায়নের ফলাফল, যেখানে শেকড়ের স্মৃতি ও অভিবাসনের অভিজ্ঞতা, ধর্মীয় পরিচয় ও আধুনিক নাগরিক জীবন—সব মিলিয়ে এক জটিল অথচ ঐক্যবদ্ধ পরিচয় গড়ে তুলেছে। এই স্বরবর্ণসমৃদ্ধ মেলবন্ধনই ইসরায়েলকে করে তুলেছে মধ্যপ্রাচ্যের এক ব্যতিক্রমী সংস্কৃতিকেন্দ্র।
সাহিত্য
ইসরায়েলি সাহিত্য তার আত্মার গভীরতা এবং ইতিহাসের বিস্তৃত পরিসরের কারণে মধ্যপ্রাচ্যের সাংস্কৃতিক মানচিত্রে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রেখেছে। হিব্রু ভাষায় রচিত আধুনিক ইসরায়েলি সাহিত্য মূলত ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে হিব্রু ভাষার পুনরুজ্জীবনের আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ লাভ করে। এই আন্দোলন শুধু ভাষার পুনর্জাগরণ নয়, বরং এক নতুন সাহিত্যিক পরিচয়ের নির্মাণও ছিল, যা প্রাচীন ধর্মীয় ভাষাকে আধুনিক অভিব্যক্তির বাহনে রূপান্তরিত করেছিল।
যদিও হিব্রু আধুনিক ইসরায়েলি সাহিত্যের প্রধান ভাষা, তবু এই সাহিত্যরূপের পরিসর এর চেয়েও বহুবিস্তৃত। আইডিশ, রুশ, আরবি, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষাতেও রচিত হয়েছে অনেক সাহিত্যকর্ম—যা বিভিন্ন অভিবাসী সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে। যেমন রাশিয়ান অভিবাসীদের জীবন ও মনস্তত্ত্ব রুশ ভাষায় রচিত সাহিত্যে উঠে এসেছে, তেমনি মিজরাহি ইহুদিদের অভিজ্ঞান ও বঞ্চনার ইতিহাস আরবি ভাষাভাষী সাহিত্যেও খুঁজে পাওয়া যায়।
ইসরায়েলি রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে প্রকাশনা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি জাতীয় দায়িত্ব আরোপ করেছে। দেশটির যে কোনও মুদ্রিত পুস্তক, পত্রিকা, অডিও বা ভিডিও রেকর্ডিং—সবকিছুরই দুটি কপি জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। ২০০১ সালে এই আইনে সংশোধন করে অমুদ্রিত ও ডিজিটাল মাধ্যমগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই অনুশাসন শুধু সংরক্ষণ নয়, বরং একটি জাতীয় সাহিত্যিক উত্তরাধিকার নির্মাণের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৬ সালে জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা পড়া ৭,৩০০ গ্রন্থের প্রায় ৮৯ শতাংশই হিব্রু ভাষায় রচিত—যা একদিকে ভাষার পুনর্জন্মের শক্তি নির্দেশ করে, অন্যদিকে জাতীয় পরিচয়ের কেন্দ্রে সাহিত্যের উপস্থিতিকেও তুলে ধরে।
ইসরায়েলি সাহিত্যের স্বীকৃতি কেবল দেশের অভ্যন্তরে নয়, আন্তর্জাতিক পরিসরেও উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত। ১৯৬৬ সালে সাহিত্যজগতে একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত আসে, যখন হিব্রু ভাষার ঔপন্যাসিক স্যামুয়েল ইয়োসেফ অ্যাগনন জার্মান ইহুদি কবি নেলি সাচসের সঙ্গে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার ভাগ করে নেন। অ্যাগননের সাহিত্য ছিল ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংঘর্ষে গড়ে ওঠা এক গভীর অন্তর্জাগতিক বিশ্ব।
ইসরায়েলের কবিতাচর্চা বরাবরই শক্তিশালী ও সংবেদনময়। ইয়েহুদা আমিকাই—যাঁর কবিতা অস্তিত্ব, প্রেম, মৃত্যু ও যুদ্ধের বাস্তবতায় গভীরভাবে আলোড়িত—আধুনিক হিব্রু কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কণ্ঠস্বর। নাথান আল্টারম্যান, লেয়া গোল্ডবার্গ এবং র্যাচেল ব্লুভস্টেইন—এই তিনজন নারী ও পুরুষ কবি হিব্রু কবিতার সৌন্দর্য, লিরিসিজম এবং আবেগের স্বরকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন।
সমসাময়িক গদ্য সাহিত্যে আমোস ওজ, ডেভিড গ্রসম্যান এবং এতগার কেরেটের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ওজের লেখনী যেমন রাজনৈতিক দ্বিধা ও ব্যক্তিমানসের টানাপোড়েনকে সাহসিকতার সঙ্গে তুলে ধরে, তেমনি গ্রসম্যানের উপন্যাসে ধ্বংস ও মানবিকতা পাশাপাশি সহাবস্থান করে। অন্যদিকে এতগার কেরেটের গল্পচর্চা এক অনন্য স্টাইল নির্মাণ করেছে—সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর, সরল অথচ প্রগাঢ়, যেটি তরুণ পাঠকের মধ্যেও দারুণ জনপ্রিয়।
ইসরায়েলি সাহিত্য, তার সব বৈচিত্র্য, ভাষা ও ঐতিহ্য সত্ত্বেও, একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়—অস্তিত্বের প্রশ্ন, ব্যক্তিসত্তার অনুসন্ধান, এবং ইতিহাস ও পরিচয়ের জটিল টানাপোড়েন। তাই এই সাহিত্য একদিকে ব্যক্তির আত্মজিজ্ঞাসার ভাষা, অন্যদিকে গোটা জাতির আত্মপরিচয়ের অঙ্গীকারও।
সঙ্গীত এবং নৃত্য
ইসরায়েলের সঙ্গীত জগৎ তার জাতিগত বৈচিত্র্য, অভিবাসনের ইতিহাস এবং ধর্ম-সংস্কৃতির আন্তঃপ্রবাহের দর্পণস্বরূপ। এখানকার সংগীত শুধু শ্রবণের অভিজ্ঞতা নয়—এটি একটি জীবন্ত সাংস্কৃতিক ভাষা, যা অতীতের স্মৃতি, বর্তমানের আবেগ এবং ভবিষ্যতের স্বপ্নকে একত্রে বহন করে।
ইসরায়েলি সংগীতের সুরতাল গঠিত হয়েছে মিজরাহী ও সেফার্দি ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে, যেখানে মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা এবং স্পেনীয় ইহুদি ঐতিহ্যের সুরভিত গন্ধ পাওয়া যায়। মিজরাহী সংগীতে যেমন আরব ও পারসিক ধ্রুপদী রীতির প্রভাব রয়েছে, তেমনি সেফার্দিক গানের মাঝে আছে লাদিনো ভাষার গভীর ব্যথা ও স্মৃতিমেদুরতা। এইসব সংগীত ঐতিহ্য প্রায়শই ধর্মীয় আবহ থেকে জন্ম নিলেও আধুনিক ইসরায়েলি সঙ্গীতের বুকে তা নতুন করে প্রাণ পেয়েছে।
ধর্মীয় ধারার সংগীতচর্চায়ও ইসরায়েল একসময় গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান অধিকার করেছে। হাসিদিক সংগীতের মেলোডিগুলি, যা মূলত ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মিক সংলাপের রূপ, এখন শুধু উপাসনার মধ্যেই আবদ্ধ নয়—তারা শহুরে যুব সমাজের মধ্যেও নিজের স্থান করে নিয়েছে। এমনকি আধুনিক পপ বা রক ধারার মধ্যেও কখনও কখনও এই হাসিদিক গানের সুর ও আবেগ মিশে যেতে দেখা যায়।
ইসরায়েলের সংগীত মানচিত্রে পশ্চিমা ধারার প্রভাবও শক্তিশালী। গ্রীক সংগীত থেকে শুরু করে জ্যাজ, ক্লাসিকাল এবং পপ-রক—সব ধারাই এখানে গৃহীত হয়েছে এক নতুন অভিব্যক্তিতে। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সিম্ফোনিক সংগঠন ইসরায়েল ফিলহারমোনিক অর্কেস্ট্রা দীর্ঘ সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে সঙ্গীতপ্রেমীদের হৃদয় জয় করে চলেছে। প্রতিবছর ২০০-রও বেশি সঙ্গীতানুষ্ঠান উপস্থাপনকারী এই প্রতিষ্ঠান বিশ্বমানের এক সাংস্কৃতিক মঞ্চ, যেখানে বিখ্যাত সঙ্গীতবিদদের পাশাপাশি ইসরায়েলি প্রতিভাও তুলে ধরা হয়।
বিশ্বসংগীতের প্রেক্ষাপটে ইসরায়েলের মুখ উজ্জ্বল করেছেন বেশ কিছু আন্তর্জাতিক তারকা। ইটঝাক পার্লম্যান ও পিনচাস জুকারম্যান—বিশ্বখ্যাত বেহালাবাদক, যাঁদের শৈল্পিকতা শুধু ইসরায়েল নয়, সমগ্র জগতের শ্রোতাদের সমাদৃত করেছে। অন্যদিকে আফরা হাজা তাঁর সুরেলা কণ্ঠে মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিমা সুরের মেলবন্ধন ঘটিয়ে এক আন্তর্জাতিক সুরসম্রাজ্ঞীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন।
ইউরোপের ইউরোভিশন সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ইসরায়েলের সংগীত চর্চার আন্তর্জাতিক দিগন্তকে প্রসারিত করেছে। ১৯৭৩ সাল থেকে প্রায় নিয়মিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশটি চারবার শীর্ষস্থান অর্জন করেছে, এবং দুটি ঐতিহাসিক বছর প্রতিযোগিতাটির আয়োজক হিসেবেও নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে।
দেশটির সঙ্গীতজগতের আরেক উজ্জ্বল দিক হলো আন্তর্জাতিক উৎসব। প্রতি গ্রীষ্মে এইলাত শহরে অনুষ্ঠিত ‘রেড সি জ্যাজ ফেস্টিভাল’ সঙ্গীতপ্রেমীদের এক বিশাল মিলনস্থল, যেখানে জ্যাজের অনুরণন গিয়ে মিশে যায় লাল সাগরের ঢেউয়ের সাথে। দেশি-বিদেশি শিল্পীদের অংশগ্রহণে এই উৎসব হয়ে ওঠে এক সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের উত্সব।
এছাড়া ইসরায়েলি পরিচয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকা “ইয়ার হা-আরেত্স” বা “ভূমির গান”—যা দেশপ্রেম, কৃষিকাজ, ঐতিহ্য এবং মানুষের মাটির সঙ্গে সংযুক্ত থাকার অনুভূতিকে তুলে ধরে—এই ধারার গানগুলো একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে।
ইসরায়েলের সংগীত তাই কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়—এটি ইতিহাস ও পরিচয়ের গীতিকথা, যেখানে হারানো শিকড়, পাওয়া স্বপ্ন, এবং জাতিগত বৈচিত্র্যের বর্ণালী ছায়াপাত করে প্রতিটি সুরে। এই মেলবন্ধনই দেশটির সংগীতকে একটি অভিনব বৈশ্বিক ভাষায় রূপ দিয়েছে, যেখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, ঐতিহ্য ও আধুনিকতা, স্থানীয়তা ও বিশ্বায়ন—all come together in one resounding harmony.
সিনেমা এবং থিয়েটার
ইসরায়েলের চলচ্চিত্র ও মঞ্চশিল্প একদিকে যেমন রাষ্ট্রের আত্মপরিচয়, যুদ্ধ, অভিবাসন ও জাতিগত বৈচিত্র্যের ইতিহাস বহন করে, তেমনি অন্যদিকে শিল্পের মাধ্যমে জটিল বাস্তবতাগুলিকে সংবেদনশীলভাবে তুলে ধরার এক অনন্য মাধ্যম হয়ে উঠেছে।
চলচ্চিত্র শিল্পে ইসরায়েল অনেকটা নীরব কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। একাডেমি পুরস্কারে শ্রেষ্ঠ বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্র বিভাগে ইসরায়েলি চলচ্চিত্র দশবার মনোনয়নপ্রাপ্ত হয়েছে, যা দেশটির চলচ্চিত্র নির্মাতাদের নান্দনিকতা ও শিল্পগুণের প্রতিচ্ছবি। যুদ্ধ, পরিচয় সংকট, ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম ধর্মীয় অনুশাসন, অভিবাসন, ও আরব-ইহুদি সম্পর্ক—এই সব জটিল সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েই ইসরায়েলের চলচ্চিত্র নির্মিত হয়ে থাকে। এই চলচ্চিত্রগুলোতে প্রায়ই এক ধরনের আত্মসমালোচনামূলক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়, যা রাজনৈতিক বিতর্কেও প্রবেশ করে।
এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে আরব-ইসরায়েলি সংঘাত এবং ইসরায়েলের অভ্যন্তরে ফিলিস্তিনি নাগরিকদের অবস্থান নিয়ে যাঁরা চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন মোহাম্মদ বাকরি। তাঁর পরিচালিত ২০০২ সালের বিতর্কিত ও আলোচিত ডকুমেন্টারি জেনিন, জেনিন ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুশিবিরে সংঘটিত ঘটনাবলি তুলে ধরে, যা একদিকে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সমালোচনামূলক চিত্র তুলে ধরে, অন্যদিকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রবিষয়ক আলোচনায় প্রবল আলোড়ন তোলে। আরেকটি স্মরণীয় চলচ্চিত্র দ্য সিরিয়ান ব্রাইড, যেখানে মধ্যপ্রাচ্যীয় সীমান্ত বাস্তবতা, জাতিসত্তার বিভাজন এবং নারী জীবনের টানাপোড়েন একসঙ্গে এসে মিশে গেছে মানবিকতার এক সূক্ষ্ম পর্দায়।
চলচ্চিত্রের পাশাপাশি ইসরায়েলের থিয়েটার জগতও তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। পূর্ব ইউরোপের ইয়িদ্দিশ থিয়েটারের দীর্ঘ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার নিয়ে গঠিত হয়েছে ইসরায়েলের নিজস্ব নাট্যচর্চা। নাটকের ভাষা হিব্রু হলেও থিয়েটার সংলগ্ন ভাবধারায় বহুভাষিক, বহুপরিচয়ের স্পন্দন লক্ষ করা যায়। এই নাট্যচর্চা শুধু ইহুদি জনগোষ্ঠীর নয়—আরব, ড্রুজ, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীরও অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে নাট্যরূপ দিতে শুরু করেছে।
তেল আভিভের হাবিমা থিয়েটার, যা ১৯১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত, কেবল ইসরায়েলের জাতীয় থিয়েটারই নয়, এটি হিব্রু ভাষার নাট্যচর্চার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবেও পরিচিত। এর মঞ্চে স্থান পেয়েছে শেক্সপিয়ার থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক ইসরায়েলি নাট্যকারদের সৃষ্টি—সবই স্থানীয় সংস্কৃতি ও আন্তর্জাতিক দর্শনের এক সংলগ্ন রূপ।
ওহেল থিয়েটার, ক্যামেরি থিয়েটার, এবং রুশ-ভাষাভাষীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত গেশের থিয়েটার—প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই তাদের নিজস্ব কণ্ঠস্বর ও শৈলীতে সমাজ, ইতিহাস ও মানবমনের গভীর আবেগ ফুটিয়ে তোলে। বিশেষ করে ক্যামেরি থিয়েটারকে সমকালীন সামাজিক ইস্যু নিয়ে কাজ করার জন্য প্রশংসিত করা হয়।
ইসরায়েলি থিয়েটার ও চলচ্চিত্র তাই কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং রাষ্ট্র ও সমাজের সংলাপের একটি বলিষ্ঠ মঞ্চ—যেখানে জাতীয় পরিচয়, ব্যক্তিসত্তা, স্মৃতি ও প্রতিরোধ একই সঙ্গে বসবাস করে। এখানে শিল্প হয়ে ওঠে প্রতিচিন্তা, প্রতিবাদ ও পুনরাবিষ্কারের এক রাজনৈতিক ও নন্দনতাত্ত্বিক ভাষা।
কলা
ইসরায়েলি শিল্প এমন এক ধারাবাহিক অভিযাত্রার নাম, যেখানে অতীতের গূঢ় ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ও আধুনিকতা-বীক্ষণের স্পন্দন একসঙ্গে ধরা দেয়। দেশটির ইহুদি শিল্পচর্চার শিকড় গেঁথে আছে কাব্বালাহ, তলমুদ এবং জোহারের মতো গূঢ় ও ভাবগম্ভীর ধর্মীয় পাঠে। এই শাস্ত্রসমূহ শুধু বিশ্বাসের জগৎ নয়, শিল্পের প্রতীকময় ভাষাও নির্মাণ করেছে। বিশেষত সাফেদের রহস্যময় আবহ বা জেরুজালেমের আধ্যাত্মিক দীপ্তি—এসবই বারবার উঠে এসেছে ইসরায়েলি শিল্পীদের রঙতুলিতে।
ঊনবিংশ শতক ও বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ইয়িশুভ নামে পরিচিত ইহুদি বসতির শিল্পজগতে বেজালেল স্কুলের প্রভাব সুগভীর ছিল। ধর্ম, ঐতিহ্য এবং প্রাক-বসতিগামী ইহুদি অভিব্যক্তিকে কেন্দ্র করে এই শিল্পধারা একধরনের আত্ম-অন্বেষার রূপরেখা হয়ে উঠেছিল। বেজালেল স্টাইল মূলত স্থানীয় মোটিফ, বাইবেলিক প্রতীক এবং আরব-ইহুদি কারুকার্যকে একসূত্রে বেঁধে একটি সনাতন শৈলী নির্মাণে সহায়তা করে।
তবে ১৯২০-এর দশক থেকে এই দৃশ্য পাল্টাতে থাকে। ইউরোপ, বিশেষ করে ফ্রান্সের আধুনিক চিত্রকলার ছোঁয়া ইসরায়েলের শিল্পজগতে এক নবতর যুগের সূচনা করে। ইসাক ফ্রেঙ্কেল ফ্রেনেল ছিলেন সেই রূপান্তরের অন্যতম পুরোধা, যিনি ফরাসি চিত্রকলার সাবলীলতা, আলোছায়া, ছন্দ ও বিমূর্ততার ভাষা স্থানীয় শিল্পীদের সামনে উন্মুক্ত করেন। প্যারিস স্কুলের ইহুদি শিল্পী—সাউটিন, কিকোইন, চাগাল ও ফ্রেঙ্কেল—শুধু ইউরোপীয় আধুনিকতাকে নয়, বরং অভিবাসনের স্মৃতি, শিকড় ও সংস্কৃতিকে রূপ দিয়েছেন বিমূর্ত ও আধা-বাস্তবতায়। এদের প্রভাবে ইসরায়েলি চিত্রকলা এক নতুন আত্মপরিচয় গঠন করতে শুরু করে, যেখানে ধর্ম আর বাস্তবতা পাশাপাশি চলেছে।
ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও ইসরায়েলি শিল্পীরা ইতিহাস ও আধুনিকতার সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কাজ করে গেছেন। ইউরোপীয় আধুনিক ভাস্কর্য-রীতির পাশাপাশি মেসোপটেমীয় ও অ্যাসিরীয় শিল্পধারার প্রতিফলনও দেখা যায় স্থানীয় শিল্পে। যেমন আভ্রাহাম মেলনিকভের গর্জনরত সিংহ অথবা ডেভিড পোলুসের আলেকজান্ডার জায়িদের মূর্তি কেবল ইতিহাসের দলিল নয়, বরং একটি জাতির সংগ্রামের গূঢ় ভাষ্যও বটে। জেভ বেন জভির কিউবিস্ট ভাস্কর্য প্রথাবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক, যেখানে ফর্ম ভেঙে গড়ে তোলা হয়েছে এক নতুন গঠনশৈলী।
ইসরায়েলি শিল্পের থিমগুলো বহুমাত্রিক—একদিকে যেমন আছে পুরাতন শহর সাফেদ ও জেরুজালেমের আধ্যাত্মিক বিভা, তেমনি আছে টেল আভিবের কফিশপ-সংস্কৃতির ছটায় আলোকিত শহরজীবনের খণ্ডচিত্র। কৃষিভিত্তিক দৃশ্যাবলি, যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা কিংবা বাইবেল-ভিত্তিক মিথ—সব মিলিয়ে ইসরায়েলি শিল্প হয়ে উঠেছে একান্তই ব্যক্তিগত ও গভীরভাবে রাজনৈতিক।
সাম্প্রতিক সময়ে ইসরায়েলি শিল্পীদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে নতুন প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পচর্চা—অপটিক্যাল আর্ট, ডিজিটাল পেইন্টিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা তৈরি চিত্র ও ভাস্কর্য। এমনকি অপ্রচলিত উপকরণ যেমন লবণের মতো প্রাকৃতিক উপাদানও এখন শিল্পমাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই অভিমুখ একদিকে যেমন প্রথাগত শিল্প-রীতির বাইরে নতুন অভিব্যক্তি খোঁজার ইঙ্গিত দেয়, অন্যদিকে ইসরায়েলি শিল্পকে আরো বৈচিত্র্যময়, প্রশ্নমুখর ও অন্তর্মুখী করে তুলছে।
এই শিল্পচর্চা তাই শুধুমাত্র নান্দনিকতার অনুশীলন নয়, বরং তা দেশ, ধর্ম, শিকড় ও বর্তমান সময়ের সঙ্গে এক গভীর সাংস্কৃতিক সংলাপ। এবং সেই সংলাপেই জন্ম নিচ্ছে এক বহুরৈখিক, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, বৈশ্বিক ও একই সঙ্গে স্থানীয় ইসরায়েলি শিল্পভুবন।
স্থাপত্য
ইসরায়েলের স্থাপত্যজগৎ মূলত অভিবাসনের ধাক্কায় গড়ে ওঠা এক বহুরৈখিক, বহুধা শৈলীর মেলবন্ধন। দেশটির স্থাপত্যধারা কখনও পুণর্গঠনের, কখনও প্রত্যাবর্তনের, আবার কখনও বা অভিজ্ঞান নির্মাণের এক মাধ্যম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিশেষত ইউরোপ থেকে আগত ইহুদি স্থপতিরা, যাঁরা ২০ শতকের প্রথমার্ধে ইহুদি বসতিগুলিতে (ইয়িশুভ) স্থায়ী হতে শুরু করেন, পশ্চিম ও প্রাচ্যের স্থাপত্য ঐতিহ্যের এক আকর্ষণীয় মিশ্রণ সৃষ্টি করেন।
এই একলেকটিক ধারায় মধ্যপ্রাচ্যের গম্বুজ, ক্যালিগ্রাফিক শোভা, ইট ও পাথরের ঐতিহ্য যেমন এসেছে, তেমনই ইউরোপীয় রেনেসাঁস ও ক্লাসিক স্থাপত্যের ছাপও বিদ্যমান। তবে এই সংমিশ্রণের মধ্যেই এক আধুনিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা হয়। নাৎসি অত্যাচার থেকে পালিয়ে আসা জার্মান ইহুদি স্থপতিরা, বিশেষত বাউহাউস আন্দোলনের অনুগামীরা, ইসরায়েলে এক নতুন স্থাপত্য ভাষা গড়ে তোলেন—সহজ রেখা, জ্যামিতিক কাঠামো এবং কার্যকরী রূপের উপর জোর দিয়ে। এরিখ মেনডেলসনের মতো ব্যক্তিত্ব এই রূপান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
এই প্রগতিশীল ভাবনার ফলেই জন্ম নেয় তেল আভিভের হোয়াইট সিটি। এটি মূলত বাউহাউস ধাঁচের শত শত সাদাসিধে ভবনের এক অনন্য সংগ্রহ, যা ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকাভুক্ত হয়েছে। এখানে আর্কিটেকচারের ভাষা হয়ে উঠেছে এক নতুন রাষ্ট্রের স্বপ্ন, উদ্বাস্তুদের ঘর, এবং মরুভূমির মধ্যকার এক শৃঙ্খলিত আধুনিকতা।
স্বাধীনতা-উত্তর ইসরায়েলে রাষ্ট্র-চালিত বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্পে এক ভিন্ন মাত্রার আভাস পাওয়া যায়। ব্রুটালিস্ট স্থাপত্য—যেখানে কাঁচা কংক্রিট ও কঠিন গঠনবিশিষ্ট নকশা ব্যবহৃত হয়—একটি প্রধান শৈলী হয়ে ওঠে। মরুভূমির শুষ্ক আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্যই এই ধরনের নির্মাণ কাঠামো প্রাধান্য পায়, বিশেষত সরকারি দফতর, আবাসন প্রকল্প ও সামরিক স্থাপনাগুলিতে। এরই মধ্যে আবার স্থানীয় উপকরণ ও জলবায়ু অনুযায়ী স্থাপত্যের পরিবেশ-বান্ধব দিকটি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়।
ইসরায়েলের শহর পরিকল্পনার ইতিহাসেও উল্লেখযোগ্য উদাহরণ রয়েছে। ‘গার্ডেন সিটি’ ধারণার সফল বাস্তবায়ন তেল আভিভের পরিকল্পনায় পরিলক্ষিত হয়। স্কটিশ প্রকৌশলী প্যাট্রিক গেডেসের পরিকল্পনা অনুসারে গড়ে ওঠা এই শহরটি বৈশ্বিক শহর পরিকল্পনার ইতিহাসে এক মডেল হয়ে উঠেছে। এখানে গাছপালা, উন্মুক্ত স্থান এবং মানুষের গতিশীলতার মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করা হয়েছে যা শহরজীবনকে নিছক বসবাসযোগ্যতার চেয়ে বেশি কিছু করে তোলে—একটি প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক কাঠামো।
এছাড়াও, ইসরায়েলের কিবুতজ বা সমবায় কৃষি সম্প্রদায়ের স্থাপত্যধারাতেও একরকম আদর্শবাদ পরিলক্ষিত হয়। রিচার্ড কাউফম্যান পরিকল্পিত নাহালাল কিবুতজ, যার বৃত্তাকার কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা চারপাশে ছড়ানো খামার ও আবাসিক ইউনিটের মাধ্যমে সমবায় কাঠামোর প্রতীক হয়ে ওঠে, সেই আদর্শবাদের এক স্থাপত্য রূপ।
এইভাবে ইসরায়েলের স্থাপত্য শুধু সৌন্দর্যবোধের বিষয় নয়; এটি অভিবাসনের ইতিহাস, রাজনৈতিক চিন্তা, জলবায়ু-সংবেদনশীলতা এবং আধুনিক রাষ্ট্র নির্মাণের এক জ্যামিতিক ভাষা। প্রাচীন ধর্মীয় কেন্দ্রের ছায়ায় দাঁড়িয়েও আধুনিক স্থাপত্য এখানে নিজের স্বর সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, যা সমসাময়িক বিশ্বে একটি স্বতন্ত্র স্থানের দাবিদার।
গণমাধ্যম
ইসরায়েলের গণমাধ্যম কাঠামো এক বহুরৈখিক ও বিতর্কমুখর পরিবেশের নিদর্শন, যা রাষ্ট্রটির রাজনৈতিক বৈচিত্র্য, ভাষিক বৈভিন্ন্য এবং অভ্যন্তরীণ সংঘাতপূর্ণ বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটায়। সংবাদপত্র, টেলিভিশন এবং অনলাইন সংবাদমাধ্যমগুলো একদিকে যেমন বহুধাবিভক্ত জনমতের ভাষ্য পরিবেশন করে, অন্যদিকে তেমনি রাষ্ট্রশক্তি ও সামরিকতন্ত্রের সঙ্গে এর দ্বন্দ্বপূর্ণ সম্পর্কও ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।
ইসরায়েলের প্রিন্ট মিডিয়া বহু দশকের পুরনো ঐতিহ্যের ধারক। ‘হারেৎজ’ দীর্ঘদিন ধরে একটি প্রগতিশীল ও বামপন্থী অবস্থান থেকে সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে আসছে। অন্যদিকে ‘ইয়েদিওথ আহরোনথ’ একটি অপেক্ষাকৃত মধ্যমপন্থী অবস্থানে থেকেও দেশের মূলধারার পাঠকদের সঙ্গে সংলাপ গড়ে তোলে। তবে ২০০৭ সালের পর থেকে দৃশ্যপটে প্রবেশ করে ‘ইসরায়েল হায়োম’, যাকে অনেকেই ডানঘেঁষা ও প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর অনুগত বলে বিবেচনা করে থাকেন। এর বিনামূল্যে বিতরণ এবং কর্পোরেট পৃষ্ঠপোষকতা প্রথাগত সংবাদমাধ্যমের আর্থিক কাঠামোতে এক ধরনের চ্যালেঞ্জও তৈরি করেছে।
টেলিভিশনের জগতে ইসরায়েল বহুভাষিকতার এক বাস্তব উদাহরণ। রুশভাষী অভিবাসীদের জন্য ‘চ্যানেল ৯’ এবং আরব সংখ্যালঘুদের জন্য ‘কান ৩৩’—এই দুটি চ্যানেল আলাদা জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন পূরণ করে। এছাড়া ইসরায়েলি টেলিভিশনের মূলধারায় রাজনৈতিক টক-শো, রিয়েলিটি শো এবং সামাজিক নাট্যধর্মী অনুষ্ঠানগুলোও অত্যন্ত জনপ্রিয়, যা জনমত গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।
যদিও ইসরায়েলে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার একটি আইনি কাঠামো বিদ্যমান, বাস্তবতা অনেক ক্ষেত্রেই জটিল। ২০২৪ সালে ফ্রিডম হাউস তাদের প্রতিবেদনে ইসরায়েলকে ‘জীবন্ত মিডিয়া পরিবেশ’ হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও, আন্তর্জাতিক সংগঠন রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্সের প্রেস ফ্রিডম সূচকে দেশের অবস্থান ১০১তম স্থানে নামিয়ে আনা হয়েছে। বিশেষত গাজা পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সাংবাদিকদের উপর দমন-পীড়ন ও হত্যার অভিযোগ এই অবস্থান অবনমনের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।
ইসরায়েল-হামাস সংঘাতের সময় সাংবাদিকদের নিরাপত্তা, তথ্য প্রবাহের অবরুদ্ধতা এবং সরকারি পর্যায় থেকে আরোপিত নিয়ন্ত্রণের দৃষ্টান্ত বিশ্বজুড়ে সমালোচনার জন্ম দেয়। বিশেষভাবে ২০২৪ সালের মে মাসে কাতার-ভিত্তিক আল জাজিরা টিভি চ্যানেলের স্থানীয় কার্যালয় বন্ধ করে দেওয়া এবং পরবর্তী সময়ে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সরঞ্জাম জব্দ করা—এই ঘটনাগুলি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পরিসর সম্পর্কে গভীর প্রশ্ন তোলে। যদিও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের হস্তক্ষেপে পরে সেই সরঞ্জাম ফিরিয়ে দেওয়া হয়, ঘটনাটি মিডিয়া-নিয়ন্ত্রণ ও কূটনৈতিক দ্বিধার এক প্রতীক হয়ে ওঠে।
ইসরায়েলের মিডিয়া বাস্তবতা তাই একদিকে নান্দনিক মুক্তমত প্রকাশের ক্ষেত্র, অন্যদিকে নিয়ন্ত্রিত অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রতিধ্বনি। এখানে সংবাদপত্র শুধু তথ্যের বাহক নয়, বরং রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে এক উত্তপ্ত সেতুবন্ধ, যা প্রতিনিয়ত পুনর্নির্মাণের মুখোমুখি।
জাদুঘর
ইসরায়েল এমন একটি রাষ্ট্র, যেখানে অতীত, ধর্ম, স্মৃতি এবং শিল্পের এক গভীর সংলাপ মিউজিয়ামের দেয়ালে অক্ষয় হয়ে থেকে যায়। এই দেশের সাংস্কৃতিক পরিসরে জাদুঘরের ভূমিকা কেবল নিদর্শন সংরক্ষণেই সীমাবদ্ধ নয়—তা ইতিহাসের ব্যাখ্যা, পরিচয়ের পুনর্নির্মাণ এবং ভবিষ্যতের সঙ্গে সংলাপের এক জটিল পরিসর রচনা করে।
জেরুজালেমের হৃদয়ে অবস্থিত ইসরায়েল মিউজিয়াম এদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এর সংগ্রহশালায় হিব্রু বিবলিক যুগ থেকে শুরু করে ইউরোপীয় রেনেসাঁ পর্যন্ত বিস্তৃত শিল্প ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সমাহার রয়েছে। এর প্রধান আকর্ষণ অবশ্যই ডেড সি স্ক্রোলস—বিশ্বের প্রাচীনতম ও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ পাণ্ডুলিপি, যা ‘শ্রাইন অফ দ্য বুক’-এ সংরক্ষিত। এই স্থাপত্যটি নিজেই একটি চমৎকার শিল্পকর্ম, যেখানে সাদা গম্বুজ এবং নীচু স্তরের অন্ধকার প্রতিচ্ছবি আদিতে আলোর ও অন্ধকারের দ্বন্দ্বকে চিত্রিত করে।
তবে ইসরায়েলি জাদুঘরের পরিসর শুধুমাত্র ধর্মীয় ও জাতীয় পরিচয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ইয়াদ ভাশেম, জেরুজালেমের আরেক উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান, হলোকাস্ট স্মরণ ও গবেষণার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র। এখানে সংরক্ষিত আছে লক্ষ লক্ষ নিহত ও বেঁচে যাওয়া ইহুদিদের দলিল, ছবি, এবং ব্যক্তিগত বস্তুর এক বিশাল সংগ্রহ। এই প্রতিষ্ঠানটি শুধুমাত্র একটি জাদুঘর নয়, বরং এটি এক যন্ত্রণাবিদ্ধ ইতিহাসের নিঃশব্দ সাক্ষী, যা নৃশংসতার মধ্যেও মানবতার বর্ণময় প্রতিরোধের কথা বলে।
তেল আবিব বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অবস্থিত এএনইউ – মিউজিয়াম অফ দ্য জিউইশ পিপল এক নতুন ধরণের জাদুঘর যেখানে ইহুদি জাতির বৈশ্বিক ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং সমসাময়িক জীবনচর্চা অন্তরঙ্গভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এটি একটি ইন্টারঅ্যাকটিভ, বহুমাত্রিক জাদুঘর, যেখানে ইতিহাস নিছক পেছনের দরজা নয়, বরং জীবন্ত আলাপচারিতা। আর্জেন্টিনার এক রাবাই থেকে শুরু করে মরক্কোর একটি স্ফার্দি রান্নাঘর কিংবা নিউ ইয়র্কের একটি সিনাগগ—সব কিছুই যেন এখানে এক সঙ্গে উপস্থিত।
আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, প্রতি ব্যক্তির অনুপাতে ইসরায়েলে বিশ্বের সর্বাধিক মিউজিয়াম বিদ্যমান। এই বহুসংখ্যক জাদুঘরের মধ্যে অনেকগুলো ইসলামী শিল্প ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, যা একধরনের আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ রচনা করে। রকফেলার মিউজিয়াম, জেরুজালেমে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক ভবন, মধ্যপ্রাচ্যের পুরাতত্ত্বে বিশেষায়িত। এখানেই আবিষ্কৃত হয়েছিল গ্যালিলি ম্যান—পশ্চিম এশিয়ায় পাওয়া প্রথম হোমিনিড খুলি, যা মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।
আরও একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান হলো এল. এ. মেয়ার ইনস্টিটিউট ফর ইসলামিক আর্ট, যেখানে ইরান, তুরস্ক, মিশর ও মুঘল ভারতের অগণিত শিল্পকর্ম সংরক্ষিত। এই মিউজিয়ামে থাকা ঘণ্টা, ধূপদান, অস্ত্রশস্ত্র, সূচিশিল্প ও অলঙ্কারশিল্প এই অঞ্চলের শিল্প ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ।
সার্বিকভাবে ইসরায়েলের জাদুঘরসমূহ শুধুমাত্র নিদর্শনের প্রদর্শনী নয়; বরং এগুলি ইতিহাস, রাজনীতি, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের এক আন্তঃসম্পর্কিত বিন্যাস। এখানে প্রতিটি করিডর, প্রতিটি প্রদর্শনী, প্রতিটি অক্ষর আমাদের মনে করিয়ে দেয়—ইতিহাস একদিকে যেমন শিক্ষার ভাণ্ডার, তেমনি অপরদিকে স্মৃতির চিত্রমালা।
রন্ধনপ্রণালী
ইসরায়েলি রান্নার বৈচিত্র্য যেন এই দেশের ইতিহাস ও সমাজের বহুস্তরীয় পরিচয়েরই একটি অনুপম প্রতিচ্ছবি। এই ভূখণ্ডে বসবাসকারী নানা দেশের অভিবাসীরা তাঁদের নিজস্ব খাদ্যসংস্কৃতি নিয়ে এসেছেন, যার ফলে ইসরায়েলি রন্ধনপ্রণালী হয়ে উঠেছে এক বহুজাতিক ফিউশন ধারার আকর। স্থানীয় উপাদান ও কৃষিভিত্তিক খাদ্যসংস্কৃতির সঙ্গে মিলিয়ে অভিবাসী ইহুদি জনগোষ্ঠীর—বিশেষত মিজরাহী (মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা), সেফার্দি (স্পেন-পরবর্তী ইহুদি) এবং আশকেনাজি (পূর্ব ও মধ্য ইউরোপীয়)—রান্নার রীতিগুলো এক নতুন ঘরানা গঠন করেছে, যার উত্থান লক্ষ করা যায় ১৯৭০-এর দশকের শেষের দিকে।
এই যুগে ‘ইসরায়েলি কুইজিন’ বলতে একটি পরিচিত ধারার কথা বোঝানো শুরু হয়, যা রন্ধনশিল্পে আধুনিকতা, আন্তর্জাতিকতা এবং স্থানীয় স্বাদের সমন্বয় ঘটাতে সচেষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, লেভান্টাইন ও আরব খাবারের প্রভাব সুস্পষ্ট—ফালাফেল, হুমুস, শাকশৌকা, বাবা ঘানুশ এবং জাতার মিশ্রণ ইসরায়েলি প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় অনায়াসে জায়গা করে নিয়েছে। এইসব খাবার এখন শুধু রেস্তোরাঁয় নয়, বরং রাস্তার স্টল, পরিবারিক রান্নাঘর এবং অফিস ক্যান্টিনেও সমান জনপ্রিয়।
আধুনিক ইসরায়েলি সমাজে পশ্চিমা খাদ্যসংস্কৃতির প্রভাবও চোখে পড়ে। শ্নিটজেল (যার উৎপত্তি ইউরোপে), পিজ্জা, হ্যামবার্গার, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, এবং বিভিন্ন ধরণের চাল-সালাডের সংমিশ্রণ আজকের তরুণ প্রজন্মের কাছে দৈনন্দিন খাবারের অংশ। এতে যেমন বৈচিত্র্য এসেছে, তেমনই পরিবর্তন ঘটেছে খাদ্যাভ্যাসে।
তবে রন্ধনশৈলীর ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসনের গুরুত্ব ইসরায়েলে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অনেক ইহুদি পরিবারেই কোশার (কশরুত) আইন অনুযায়ী রান্নাবান্না হয়, যার মূলনীতি হলো ‘পবিত্র ও শুচি খাবার গ্রহণ’। এই আইন অনুযায়ী দুধ ও মাংস একসাথে খাওয়া নিষিদ্ধ, নির্দিষ্ট প্রাণী ও মাছ গ্রহণযোগ্য, এবং ধর্মীয়ভাবে অনুমোদিত পদ্ধতিতে জবাই অপরিহার্য। একটি জরিপ অনুযায়ী, প্রায় অর্ধেক ইসরায়েলি ইহুদি পরিবার কোশার অনুশাসন মেনে চলে, এবং ২০১৫ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায়—দেশটির প্রায় এক চতুর্থাংশ রেস্তোরাঁ এই আইন অনুসরণ করে পরিচালিত হয়।
তবে, ইসরায়েলি সমাজের বৈচিত্র্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখানেও বিভিন্ন রকম ‘বিরুদ্ধ খাদ্য সংস্কৃতি’ গড়ে উঠেছে। যেমন—যদিও ইহুদি ও মুসলিম উভয় ধর্মে শূকরের মাংস নিষিদ্ধ, তথাপি একে ইসরায়েলে “সাদা মাংস” নামে বেচাকেনা হয় এবং কিছু নির্দিষ্ট সম্প্রদায় ও অভিবাসী গোষ্ঠী এটি গ্রহণ করে থাকে। এছাড়াও খরগোশ ও মহিষের মাংস—যা কোশার তালিকায় অনুমোদিত—বিকল্প প্রোটিন হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
ইসরায়েলে বসবাসকারী বিভিন্ন অভিবাসী সম্প্রদায়—যেমন রাশিয়ান, ইথিওপীয়, ইরানি বা ফরাসি ইহুদি—তাঁদের নিজস্ব রন্ধনঐতিহ্য নিয়েও এসেছে। রাশিয়ান বোরশ্চ, ইথিওপীয় ইঞ্জেরা ও দোরো ওয়াট, অথবা ফরাসি প্যাস্ট্রি-এর মতো পদ এখন তেল আবিব কিংবা হাইফার রেস্তোরাঁগুলিতে পাওয়া যায় অনায়াসে। এইসব উপাদান ও প্রস্তুত প্রণালির বৈচিত্র্য একদিকে যেমন রসনাতৃপ্তির ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছে, তেমনি অন্যদিকে ইসরায়েলের বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতিফলন ঘটিয়েছে।
অতএব, ইসরায়েলি খাদ্যসংস্কৃতি কেবলমাত্র রান্নার উপাদান বা রেসিপির সমষ্টি নয়; বরং এটি এক জাতীয় ইতিহাস, অভিবাসনের ধারাবাহিকতা, ধর্মীয় অনুশাসন এবং সামাজিক বৈচিত্র্যের মোহনীয় সমবায়। এই রান্নার পাত্রে ফুটে ওঠে ইহুদি আত্মপরিচয়ের স্বাদ, স্মৃতির ঝাঁজ, এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার সুগন্ধ।
খেলাধুলা
ইসরায়েলে ক্রীড়াজগৎ শুধু শারীরিক কসরত কিংবা প্রতিযোগিতার সীমায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি এক সামাজিক আবেগ, জাতীয় গর্ব এবং আন্তর্জাতিক পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ বাহক। দেশটির ক্রীড়া সংস্কৃতিতে ফুটবল এবং বাস্কেটবল সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি খেলা, যা ইসরায়েলি সমাজের নানান স্তরে গভীরভাবে প্রোথিত।
ফুটবলের ক্ষেত্রে, ইসরায়েলি প্রিমিয়ার লিগ দেশটির শীর্ষস্থানীয় প্রতিযোগিতা, যেখানে নানা অঞ্চলভিত্তিক দলগুলি অংশগ্রহণ করে এবং হাজারো দর্শকের আবেগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। মাকাবি হাইফা, মাকাবি তেল আভিভ, হাপোয়েল তেল আভিভ এবং বেইতার জেরুজালেম এই চারটি ক্লাব সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং ঐতিহ্যবাহী। আন্তর্জাতিক মঞ্চেও এই দলগুলো তাদের পরিচিতি তৈরি করেছে। যেমন, মাকাবি তেল আভিভ এবং হাপোয়েল তেল আভিভ ইউইএফএ চ্যাম্পিয়নস লিগ ও ইউইএফএ কাপ-এ অংশগ্রহণ করেছে। হাপোয়েল তেল আভিভ ২০০১ সালে ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছায়—যা একটি যুগান্তকারী অর্জন।
ইসরায়েল ১৯৬৪ সালে নিজস্ব মাটিতে এএফসি এশিয়ান কাপ আয়োজন করে এবং শিরোপা জয় করে। ১৯৭০ সালে ইসরায়েলি জাতীয় ফুটবল দল একমাত্রবারের মতো ফিফা বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য রাজনীতির অভিঘাতে, বিশেষত আরব দেশগুলির বয়কটের কারণে, ইসরায়েল ১৯৭৪ সালের পর থেকে আর এশিয়ান গেমসে অংশ নিতে পারেনি। ১৯৯৪ সালে ইউরোপীয় ফুটবল সংস্থা ইউইএফএ-র অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর, ইসরায়েলি দলগুলো ইউরোপীয় লিগ ও প্রতিযোগিতায় খেলে আসছে।
বাস্কেটবলে মাকাবি তেল আভিভ বাস্কেটবল ক্লাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ক্লাবটি ইউরোপীয় স্তরে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে—ছয়বার ইউরোলিগ চ্যাম্পিয়নশিপ জয় করে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে নিজেদের অবস্থান মজবুত করেছে।
অলিম্পিকে ইসরায়েলের সাফল্য তুলনামূলকভাবে সীমিত হলেও তা গৌরবজনক। ১৯৯২ সালে প্রথম অলিম্পিক পদক অর্জনের পর দেশটি মোট নয়টি অলিম্পিক পদক জিতেছে। ২০০৪ সালের গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে উইন্ডসার্ফিংয়ে একটি সোনার পদক ছিল এক বিশেষ প্রাপ্তি। তবে পারালিম্পিক গেমস-এ ইসরায়েলের অবস্থান অত্যন্ত সম্মানজনক—এখনও পর্যন্ত ১০০টিরও বেশি সোনার পদক অর্জন করেছে এবং অলটাইম তালিকায় ২০তম স্থানে রয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৬৮ সালের গ্রীষ্মকালীন পারালিম্পিক গেমস ইসরায়েলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
বিশ্বব্যাপী ইহুদি ক্রীড়াবিদদের একত্রিত করার লক্ষ্যে ম্যাকাবিয়া গেমস—যা অনেকাংশে অলিম্পিকের অনুরূপ—১৯৩০-এর দশকে শুরু হয়েছিল। এই প্রতিযোগিতা চার বছর অন্তর অন্তর অনুষ্ঠিত হয় এবং ইসরায়েলি ক্রীড়াজগতের এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে।
একটি অনন্য ইসরায়েলি অবদান হলো ক্রাভ মাগা—এক ধরণের আত্মরক্ষামূলক মার্শাল আর্ট, যার উৎপত্তি ইউরোপীয় ইহুদি গেটোগুলোর মধ্যে। পরবর্তীকালে এটি ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং পুলিশের আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কৌশল হিসেবে গৃহীত হয়।
ক্রীড়া মানচিত্রে ইসরায়েলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নাম দাবা। দেশটিতে একাধিক গ্র্যান্ডমাস্টার রয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যুব দাবা প্রতিযোগিতায় ইসরায়েলি খেলোয়াড়রা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন। ২০০৫ সালে বিশ্ব দল দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ ইসরায়েলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যা দেশের দাবা মর্যাদাকে আরও উঁচুতে তুলে ধরে।
সার্বিকভাবে, ইসরায়েলের ক্রীড়াজগৎ শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র—যার মাধ্যমে এই দেশ বিশ্বমঞ্চে তার শক্তিশালী, আত্মবিশ্বাসী এবং বহুমাত্রিক পরিচয় গড়ে তুলেছে।

 নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা
নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা