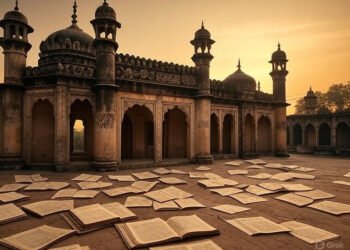লিখেছেনঃ মুহম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক
লোকাচার ও মিশ্র–সংস্কৃতি থেকে ইসলামী নবজাগরণবাদ: মুঘল ও ব্রিটিশ আমল
![প্রত্নলিপি, বাঙালি, বাঙালিয়ানা ও বাংলায় ইসলাম: কিছু জিজ্ঞাসা [পর্ব ২]](http://nobojagaran.com/wp-content/uploads/2023/07/1-298x300.png)
ষোড়শ শতকের শেষে আকবরের আমলে একটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পর অবশেষে বাংলা মুঘলদের অধিকারে আসে। শীঘ্রই এটি মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যতম একটি সুবা অথবা প্রদেশে পরিণত হয়।61 মুঘল সাম্রাজ্যের দূরবর্তী একটি প্রদেশ হিসেবে গণ্য হলেওবাংলার গুরুত্ব কোনকমে ভাবে কমে যায়নি, কারণ এটি সে সময়েদক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম সমৃদ্ধ এলাকা ছিল। প্রাচ্যের অনেক হজ্জযাত্রী মক্কা-মদীনায় ভ্রমণের জন্য সে সময়ে বাংলার বন্দরগুলো ব্যবহার করত। মুঘলরা দেশে অত্যন্ত কার্যকর একটি প্রশাসনিক ও রাজস্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। তাদের শক্তিশালী প্রশাসনের অধীনে বাংলার অর্থনৈতিক বিকাশ অব্যাহত থাকে।
![প্রত্নলিপি, বাঙালি, বাঙালিয়ানা ও বাংলায় ইসলাম: কিছু জিজ্ঞাসা [পর্ব ২]](http://nobojagaran.com/wp-content/uploads/2023/07/2-1-300x295.png)
বাংলা ব-দ্বীপের অপেক্ষাকৃত স্বল্প বসতিসম্পন্ন অথবা জনবসতিহীন এলাকায়, বিশেষ করে দক্ষিণে এ আমলে অনেক নতুন বসতি গড়ে ওঠে। এটি এ এলাকায় ইসলামের দৃঢ় প্রতিষ্ঠার পথে এক বিশেষ ভূমিকা রাখে। এ সমস্ত নিম্ন জলাভূমির ব্যাপারে একটি বাংলা প্রবাদ প্রচলিত আছে: ‘জলে কুমির ডাঙায় বাঘ’। দক্ষিণে সুন্দরবনের জঙ্গলের পাশে আঞ্চলিক ভাষায় ‘বুনো’ বলে পরিচিত এক শ্রেণীর আদিবাসী সম্পূর্ণভাবে বন সম্পদের (যেমন শিকার ও মধু আহরণ) উপর নির্ভরশীল ছিল। মুসলমানদের সাথে সংস্পর্শের ফলে তারা ইসলামের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততার পরিচয় দেওয়া শুরু করে। সুদূর দক্ষিণের স্থাননাম সমূহ গ্রাম বাংলার প্রাকৃতিক জীবনের ইঙ্গিত বহন করে, যেমন: সাতক্ষীরা জেলার নামের অর্থ সাতটি শশা (বা ক্ষীরা) যা সে অঞ্চলে কৃষি সংস্কৃতির সম্প্রসারণের প্রতীক। আবার একই জেলার বুলার আটি নামের গ্রাম দ্বারা বসবাস স্থাপনের জন্য ঘন জঙ্গলের মধ্যে একপ্রকার বাঁশের শিকড় (বুলার আটি) পরিষ্কার করার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।
বাংলার নতুন বসতিগুলো প্রায়শই তাদের নামেই নামকরণ করা হত যারা এগুলোর গোড়াপত্তন করতেন, যেমন: সাতক্ষীরার নিকটবর্তী মাহমুদপুর (মাহমুদের প্রতিষ্ঠিত একটি বসতি বা পুর) গ্রাম, কুষ্টিয়া শহরের নিকটবর্তী মোল্লা তেরঘরিয়া (জনৈক মোল্লার অধীনে প্রতিষ্ঠিত তের পরিবারের বসতি) গ্রাম এবং চাঁপাই নওয়াবগঞ্জের নিকটবর্তী বারঘরিয়া (বার পরিবারের বসতি) গ্রাম।62 এ এলাকায় বসতি স্থাপন প্রক্রিয়া এমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যে ঔপনিবেশিক আমলে বসতি তথা ইংরেজি ‘সেটলমেন্ট’ শব্দটি ভূমি এবং রাজস্ব প্রশাসনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দাপ্তরিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শব্দে পরিণত হয়। সমগ্র ব্রিটিশ আমল জুড়ে মাঝে মধ্যেই বসতি জরিপ সংক্রান্ত রেকর্ড এবং অত্যন্ত খুঁটিনাটি বর্ণনাসহ বিস্থারিত নকশা প্রস্তুত করা হত (জরিপ সংক্রান্ত রেকর্ডগুলোর দু’একটি নমুনার জন্য দেখুন পরিশিষ্ট ৩)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অনেকগুলো জরিপের মধ্যে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার নিকটবর্তী চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ ও মালদা জেলায় পদ্মা নদীর উভয় তীরে এবং চরগুলোতে একটি জরিপ পরিচালিত হয় যার নাম দিয়ার (আরবী এবং ফার্সীতে এর অর্থ বসতি; স্থানীয় ভাষায় দিয়াড়া) জরিপ (আরও দেখুন পরিশিষ্ট ৩)। এতদঞ্চলে বসতি স্থাপনকারীগনকে আফগান শাসনের সময়কার সৈন্যদের বংশধর বলে মনে করা হয় যারা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় লোকেদের সাথে মিলে মিশে তাদের বহিরাগত স্বাতন্ত্রের কোন কিছুই ধরে রাখেনি।63

মোটের উপর মুঘল শাসকগণ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রজাসাধারণের প্রতি উদার ছিলেন। মদদ–ই–মা‘আশ–এর ন্যায় অনুদান ও জায়গীরদারির মাধ্যমে তাঁরা যে শুধু মসজিদ-মাদ্রাসার ন্যায় মুসলমানদের প্রতিষ্ঠানগুলোর ভরণ-পোষণ যোগাতেন তা নয়, মাঝে-মধ্যে তাঁরা মন্দিরের ন্যায় হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠানেরও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।64 এই আমলে এ এলাকায় ভারতীয় ও পারসিক ঐতিহ্যের সংমিশ্রণের ধারাটি নতুন গতি পায়। একবারে প্রথম থেকেই মুসলিম সমাজে এক ধরনের অনুচ্চারিত শ্রেণীভেদ চালু ছিল। যেমন সুলতান ‘আলা আল-দীন খলজীর প্রথম ইসলামী শিলালিপিতে খাস তথা বিশেষ (উচুঁ) শ্রেণী এবং ‘আম তথা সাধারণ জনগণ – এই দুইটি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। এই শ্রেণীভেদ মুঘল আমলে আরও স্পষ্টরূপে দেখা দেয়। হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণদের মত মুসলমান সমাজের বহিরাগত উচ্চ শ্রেণীকে ‘আশরাফ’ তথা সম্ভ্রান্ত বলা হত, যাদের সাংস্কৃতিক ভাষা ও চালচলন ছিল রাজধানী দিল্লীর অনুকরণে ফার্সী ঘেঁসা। মুঘল সম্রাজ্যের পতন ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পর্যায়ক্রমে ক্ষমতা দখলের পর ‘আশরাফ’ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে ধীরে ধীরে উর্দু ভাষার প্রচলন বৃদ্ধি পায় এবং এক পর্যায়ে ফার্সীর জায়গায় এদের অনেকের পারিবারিক ভাষা উর্দুতে রুপান্তরিত হয়। মুসলমান ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বৃহদাংশ এই আশরাফগণ শুরু থেকেই নিজেদেরকে প্রশাসনিক এবং অন্যান্য সরকারি ও আধা-সরকারি পদগুলো দখল করার একমাত্র দাবিদার মনে করত। পক্ষান্তরে হিন্দু সমাজের অব্রাহ্মণদের মত মুসলিম সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ‘আতরাফ’, কখনো বা ‘আজলাফ’ অথবা ‘আরজাল’ অর্থাৎ প্রান্তসীমার জনসাধারণ বলে অভিহিত করা হত, যা প্রকারান্তরে হিন্দু শ্রেণীভেদে ‘নিম্ন বর্গ’ পর্যায়ের মুসলিম ছিল। গ্রামবাংলার বৃহৎ সাধারণ জনগোষ্ঠী এই আতরাফদের নিয়ে গঠিত ছিল। আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শাসন ক্ষমতা মুঘলদের হাত থেকে ক্রমান্বয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে চলে যাওয়ার পর আশরাফদের জায়গায় হিন্দুদের একটি উচ্চ শ্রেণী সমাজের সুবিধা ভোগকারী দল হিসাবে ধীরে ধীরে প্রকাশ লাভ করে। বাঙালি সমাজে এদেরকে ‘ভদ্রলোক’ বলা হত। এরাই ক্রমশ মুসলমান আশরাফদের স্থান দখল করে।
আশ্চর্য হলেও সত্য যে, খোদ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলেই একাধিক জনপ্রিয় ইসলামী আন্দোলনের উদয় হয় যেগুলো মুসলমানদের মনে তাদের পৃথক সত্তার ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করে। এই সময়ে বাংলায় ইসলামের যে নজিরবিহীন প্রসার ঘটে, তা নিসন্দেহে অতি কৌতুহলোদ্দীপক (এ বিষয়ে কিছু নমুনার জন্য দেখুন পরিশিষ্ট ৩)। আলেমগণ পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় সামাজিক নেতৃত্বে সক্রিয় হন। বাংলার আলেমরা তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনার জন্য উত্তর ভারতের ইসলামী প্রতিষ্ঠান ও আলেমদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে তাঁরা তাঁদের বাণী গ্রাম বাংলার সাধারণ লোকদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য অঞ্চলের আলেমদের চেয়ে বেশি সফল ছিলেন। উনিশ ও বিশ শতকে এ এলাকায় অনেক সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলন হয়। মুসলমানদের জন্য এটি ছিল আত্মবিশ্বাস, সংস্কার, পুনর্জাগরণ এবং আত্মোপলব্ধির যুগ। ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে উনিশ শতকে মুসলমানদের সংগ্রাম, বিশেষ করে ‘জিহাদ’ আন্দোলন গ্রামবাংলার জনসাধারণের একটি বড় অংশের সমর্থন লাভ করে, যা সুদূর আরব উপদ্বীপের ‘সালাফী’ (ঔপনিবেশিকদের পরিভাষায় ’ওহাবী’) ধর্মীয় নবজাগরণের ঐতিহ্যের মধ্যে তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য কাঠামো বা নমুনা খুঁজে পায়। গণভিত্তিক এ আন্দোলন সাধারণ মুসলমান জনগণ এবং উচ্চ শ্রেণীর আশরাফ মুসলমান তথা হিন্দু ভদ্রলোকের মধ্যে শ্রেণীগত একটি বিরোধের সৃষ্টি করে। কিন্তু একই সঙ্গে এটি গ্রামবাংলার জনগণের একটি বড় অংশের মধ্যে বিশুদ্ধতাবাদী ইসলামী আত্মপরিচয় জাগ্রত করে, যারা ইতিপূর্বে লৌকিক আচার-বিশ্বাস ও মিশ্র ধারার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক ছিল।
![প্রত্নলিপি, বাঙালি, বাঙালিয়ানা ও বাংলায় ইসলাম: কিছু জিজ্ঞাসা [পর্ব ২]](http://nobojagaran.com/wp-content/uploads/2023/07/3-3.png)
মাদ্রাসার আলেমদের দ্বারা পরিচালিত ‘তরীকায়ে মুহম্মাদিয়া’ বা ‘আহলে হাদীস’ নামে পরিচিত এই ধারাটি কখনো কখনো ঔপনিবেশিকদের দ্বারা ‘মৌলবী আন্দোলন’ নামেও অভিহিত হয়েছে। বর্ধমান থেকে উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার দুরে কুলসোনা গ্রামটি এখন পর্যন্ত সেই ধারার ঐতিহ্য বহন করে আসছে। ১৮৩১ সালে বালাকোটে পরাজিত মুজাহেদীনদের একটি দল বর্তমান খাইবার পোখতুনখাওয়াহ অঞ্চলের নৌশেরাহ জেলার সিত্তানা (সিন্ধু নদী থেকে প্রায় এক মাইল উত্তরে) নামক জায়গায় তাদের আন্দোলনের একটি কেন্দ্র গড়ে তোলে। এক পর্যায়ে দলের নেতা মাওলানা ইনায়াত আলী ধর্ম (মুজাহেদীনদের ভাষায় ’বিশুদ্ধ ইসলাম’) প্রচার কার্যে তাঁর বহু শাগরিদ্দেরকে বাংলায় পাঠাতে শুরু করেন। একজন শিষ্য বর্ত্তমান রাজশাহী জেলার বাঘমারা থানার চাপড়া গ্রাম নিবাসী গাজ্বী নাযীরুদ্দীন হুসাইন সুদূর কুলসোনায় প্রচারাভিযানে এসে ১২৭০ বাংলা সনের (১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ) দিকে ‘মাদ্রাসা ইসলামিয়্যা’ (পরবর্তিকালে ‘মাদ্রাসা দারুল হুদা’) নামক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তাঁর উত্তরসূরী মাওলানা নি‘য়ামাতুল্লাহ এবং পরবর্তিতে মাওলানা সাদেমানী প্রতিষ্ঠানটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান, যা আজ অবধি টিকে রয়েছে। এসব প্রচেষ্টার ফলে এ গ্রামের মুসলিমরা সকলেই ‘আহলে হাদীস’ মতবাদ গ্রহণ করে। অন্যদিকে উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান, সনাতন পীর ও মোল্লাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ‘আহলে হাদীস’ ধরনের বিশুদ্ধবাদী (তথা ধর্মীয় নবজাগরন) আন্দোলনের বিরোধিতা করেন, কারন পূর্ব থেকে চলে আসা বিভিন্ন ধর্মের মিশ্র ধারার ঐতিহ্যের পরিপন্থী হওয়ায় এধরনের আন্দোলনকে তাঁরা তাঁদের স্বার্থ ও মতবাদের পরিপন্থী বলে সাব্যস্ত করেন। প্রাচীনপন্থী সনাতন ধারার একটি উদাহরন হল বর্ধমান শহরের প্রায় তিন কিলোমিটার উত্তরে হটুদেওয়ান গ্রামের পীরতলা পাড়ার পীরপন্থি মুসলিম গোষ্ঠী, যাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও উৎসবের কেন্দ্র হল হটুদেওয়ান পীরের মাযার। এ মাযারে অর্ঘ্য নিবেদন করতে ও দক্ষিণা দিতে মুসলিম ছাড়াও স্থানীয় আদিবাসী ও নিম্ন বর্গের হিন্দুরা বিপুল সংখ্যায় ভিড় করে।
ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে গ্রামবাংলার মুসলিম সমাজে জিহাদ আন্দোলনের বেশ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কেননা সৈয়দ আহমদ শহীদ (১৭৮৬-১৮৩১) এবং তাঁর শিষ্য সৈয়দ ইসমাইল শহীদের (১৭৭৯-১৮৩১) বাঙ্গালী অনুসারীদের অনেকে জিহাদে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে কাশ্মীর ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। এই মুজাহিদদের অনেকে প্রশিক্ষণ ও নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য সুদূর য়াগিস্থান ও আফগানিস্থানের চামারকন্দ পর্যন্ত গমন করেন।65 মওলানা বিলায়েত আলীর (১৭৯০-১৮৫২) ভাই মওলানা ইনায়েত আলী (১৭৯২-১৮৫৮) বাংলায় সৈয়দ আহমদ শহীদের অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন, যিনি এক পর্যায়ে যশোরের হাকিমপুর গ্রামে একটি বড় ধরনের প্রচারকেন্দ্র গড়ে তোলেন। তাঁর জীবনের সর্বশেষ বার বছর তিনি একজন প্রচারক হিসেবে বাংলার বিভিন্ন এলাকায় সক্রিয় ছিলেন। এই আন্দোলন সাধারণত তরীকায়ে মুহম্মাদিয়া নামে পরিচিত এবং বাংলার পশ্চিম ও উত্তর এলাকার জেলাগুলোতে তা ব্যাপক জনসমর্থন অর্জন করে। এ আন্দোলনের অনেক অনুসারী কুরআন ও হাদীসের প্রতি তাদের অন্ধ বিশ্বাসের জন্য ‘আহলে হাদীস’ নামে পরিচিত হয়। ঐ সমস্ত এলাকার কোন কোন অংশে তারা এখনও বহুল সংখ্যায় বিদ্যমান।
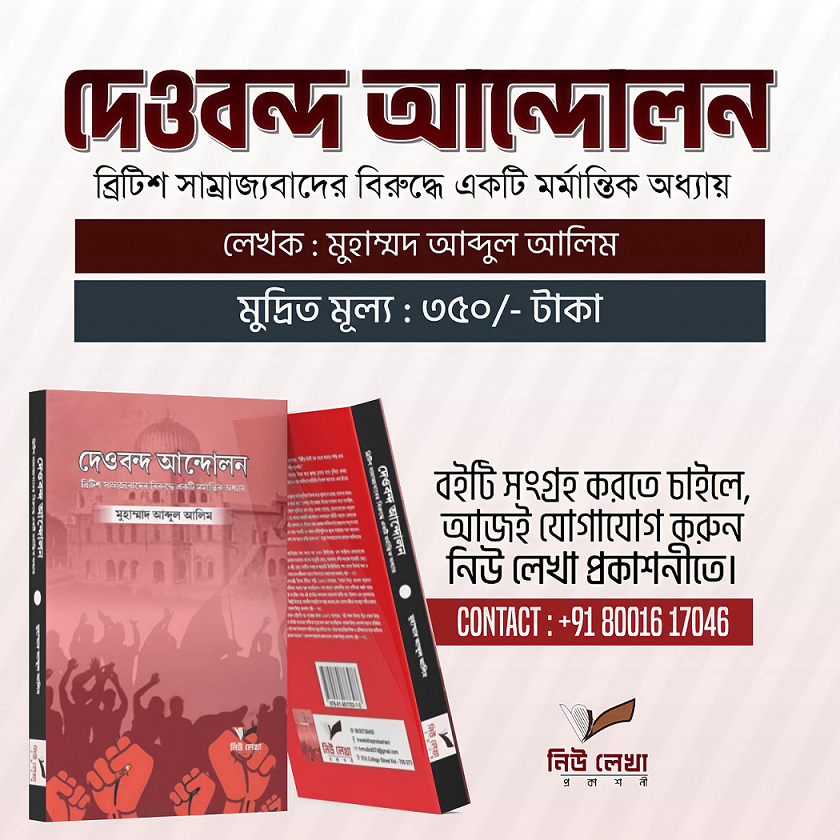
মুসলমানদের জন্য হজ্জ এমন একটি ব্যবস্থা যা বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের পারস্পরিক যোগাযোগের একটি আদর্শ সুযোগ হিসেবে দেখা হয়। বাগদাদে খিলাফতের পতন ও মোঙ্গলদের ধ্বংসযজ্ঞের পর বিশ্বের মুসলমানদের পুনরেকত্রীকরণের ক্ষেত্রে এটি একটি বিরাট ভূমিকা পালন করে। মক্কা-মদীনা থেকে তীর্থযাত্রীগণ নবী ও সাহাবীদের মূল শিক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নিজ নিজ এলাকায় প্রত্যাবর্তন করে তথাকথিত ‘সঠিক ইসলামের’ আলোকবর্তিকা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন। হজ্জফেরত এ সব নব-অনুপ্রাণিত মুসলিমদের চোখে প্রত্যন্ত এলাকার মুসলমানরা স্থানীয় লোকাচার ও মিশ্র ভাবধারা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিল। অনেক ক্ষেত্রে হজ্জ উপলক্ষে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আরবে আগত তীর্থযাত্রীরা বিভিন্ন নিখিল-ইসলামী ও বিপ্লবী আন্দোলনের (যেমন আরব উপদ্বীপের ‘ওহাবী’ বা ‘সালাফী’ আন্দোলন) সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করার সুযোগ পেত। হাজী শরিয়তুল্লাহ ও তাঁর পুত্র দুদু মিঞা ‘ফারায়েজি’ (প্রতীকী অর্থে ফারজ তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়াদির ধারক) আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন যাঁরা আরবের শেখ মুহম্মদ আব্দুল ওয়াহাব ও জিহাদ আন্দোলন দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। উপনিবেশবিরোধী একজন ইসলামী আন্দোলনকারী ও কৃষক আন্দোলনের অন্যতম নেতা সৈয়দ মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১) এই সমস্ত আন্দোলনের অন্যতম পূর্বসূরী ছিলেন। মক্কায় হজ্জব্রত পালনের সময় তিনি সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর দ্বারা প্রভাবিত হন এবং মিশ্র সংস্কৃতি ও লোকাচারমুক্ত ইসলামের আদি শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের আহ্বান জানান। সম-অধিকারের দাবিদার বাঙালি আলেমদের এই অগ্রনায়ক তিতুমীর ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে এক ধরনের শ্রেণী-সংগ্রামের ডাক দেন (যদিও কার্ল মার্কস ভুল ধারণা বশত এটিকে একধরনের ধর্মীয় উন্মাদনা বলে অভিহিত করেছিলেন)।66 এই ধারাটি বিভিন্ন নামে একবিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। মজলুম কৃষক নেতা মাওলানা ভাসানীর (মৃত্যু ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ) রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথেও এই ধারার কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়।67
সুদূর পল্লী অঞ্চলে তখন পর্যন্ত অনেক মুসলমানই প্রাতিষ্ঠানিক ইসলামী শিক্ষার সংস্পর্শে না থাকার কারণে শুধুমাত্র নামে মুসলমান ছিলেন। এই সময়ের সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে সমাজে নিত্য-নতুন কিছু প্রবণতা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ সে সময়ে সনাতনপন্থী তথা ‘সাবেকী’ ও সংস্কারবাদীদের মধ্যে ‘বাহাস’ বা ‘মুনাজ্বিরা’ নামে ধর্মীয় বিতর্কের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল, যা সমাজে এক নতুন ধরনের ধর্মীয় সচেতনতা সৃষ্টি করে। এ ধরনের নানা রকম বিচিত্র ধর্মীয় কর্মকাণ্ড বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিবিধ নামে পরিচিতি লাভ করতে থাকে, যেমন: মাওলানা কেরামত আলীর (১৮০০-৭৩) ‘তাআয়্যুনী মতবাদ’।68 সব মিলিয়ে এসব ধর্মীয়-সামাজিক তৎপরতা সে যুগে একটি ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল, যার উদাহরণ কিছুটা বর্তমান কালের একটি ইসলামী জনপ্রিয় আন্দোলন তাবলীগী জামাতের কর্মতৎপরতার মাঝে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।
আঠার শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলার নিম্নাঞ্চল, বিশেষ করে দক্ষিণের এলাকাগুলোতে জনবসতি খুব কম ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ১৭৯৩ সালে বাংলার মাত্র ৬০ শতাংশ এলাকা কৃষি কাজের জন্য আবাদ করা হত। কিন্তু মুসলমান জনসংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধির ফলে ১৯০০ সাল নাগাদ বাংলা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ কৃষিভিত্তিক এলাকায় পরিণত হয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সাধারণভাবে মনে করা হত যে বাংলার বড় একটা অংশ প্রধানত আদিবাসী এবং নিম্নশ্রেণীর হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা। বাংলার প্রথম আদমশুমারি প্রতিবেদনের লেখক এইচ. বেভারিজ গ্রামবাংলার এসব সাধারণ লোকদেরকে ‘আধা জল ও আধা স্থলে বসবাসকারী এক ধরনের উভচর জাতীয় আদিবাসী’ (‘সেমি-অ্যাম্ফিবায়াস অ্যাবোরিজিনস অব বেঙ্গল’) বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে ‘সমাজে এদের স্থান তাদের উচ্চশ্রেণীর প্রভুদের জন্য কাঠ বহনকারী মুটে ও জল সরবরাহকারী আজ্ঞাবাহী ভৃত্যের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না।’69 এদের অধিকাংশের নামধাম ও ধর্মীয় আচার-বিধিগুলো মূল ধারার হিন্দুদের থেকে যথেষ্ট আলাদা ছিল এবং খাদ্যাভ্যাস (যেমন গোমাংশ ভক্ষন) থেকে শুরু করে অনেক বিষয়ে মুসলমানদের সঙ্গে অনেক মিল ছিল। এছাড়া যুগ যুগ ধরে এদের মধ্যে মুসলিম সংস্কৃতির অনেক কিছু অনুপ্রবেশ করেছিল।
যাই হোক, ১৮৭২ সালে এ অঞ্চলে এ ধরনের প্রথম আদমশুমারি একটি অকল্পনীয় ফলাফল প্রকাশ করে। ঔপনিবেশিক শাসকরা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন, বাংলার জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশি মুসলমান এবং তাদের অধিকাংশই কৃষক। এই আদমশুমারি সম্ভবত পুরোপুরি সঠিক ছিল না, কেননা মুসলমানরা আদমশুমারিতে অংশ নিতে খুব একটা উৎসাহী ছিল না। আদমশুমারি পরিচালনার পেছনে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের উদ্দেশ্য নিয়ে তারা যথেষ্ট সন্দিহান ছিল। তাদের অনেকে সন্দেহ করেছিল যে আদমশুমারিতে তাদের নাম মুসলমান হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হলে বিপদের আশঙ্কা আছে এবং সেকালে চলমান ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনে (বিশেষ করে জিহাদ আন্দোলনে) সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী হিসেবে তাদেরকে চিহ্নিত করা হতে পারে। যা হোক, আদমশুমারির এ প্রক্রিয়া গ্রামবাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীকে পরোক্ষভাবে তাদের ইসলামী পরিচয় সম্বন্ধে সজাগ করে তোলে। এর বহুবিধ কারণের মধ্যে অন্যতম একটি কারন ছিল যে বাংলার আধা-মুসলমান জাতীয় আদিবাসিদের বেশীরভাগ লোকই ততদিনে নিজেদের মুসলিম ভাবতে শুরু করেছিল, যাদের অধিকাংশই আগে শুধু নামেমাত্র মুসলিম ছিল।
জীবনের স্বাভাবিক গতিপথে নিত্য-নতুন প্রতিবন্ধকতা এবং ঔপনিবেশিক শাসন ও স্থানীয় জমিদারদের বিভিন্নমুখি চাপের মুখে মুসলমানদের মধ্যে এক ধরনের ঐক্য গড়ে ওঠে। তাদের মধ্যে নতুন এক চেতনার উদয় হয় যে তারা ‘উম্মাহ’ তথা উম্মতের (অর্থাৎ মুসলিম জাতির) একটি অংশ, যা যে কোন ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে। ১৮৮১, ১৮৯১ ও ১৯০১ সালে পরিচালিত আদমশুমারিগুলোতে আরও সঠিক ফলাফল পাওয়া যায়। এই সময় মুসলমানেরা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে শুরু করে যে আদমশুমারি আসলে তাদের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র নয়। মুসলমানদের বর্ধিত সহযোগিতার ফলে পরবর্তী আদমশুমারিগুলো আরও সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হয়। এর দ্বারা মুসলমান জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার তথ্য জানা যায়। বিশেষ করে ১৯০১ সালের আদমশুমারিতে এক বিস্ময়কর পরিসংখ্যানগত তথ্য প্রকাশ পায়। এতে দেখা যায়, গ্রামবাংলার, বিশেষ করে বাংলার পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর এলাকার জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই মুসলমান। সাধারণ বাঙালিদের ধর্মমত সম্পর্কে নতুন পরিসংখ্যানের চাঞ্চল্যকর তথ্যের কথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের মত তখনকার সাহিত্যিকদের অত্যন্ত জনপ্রিয় উপন্যাস ও ছোট গল্পেও লক্ষ্য করা যায়।70 বিভিন্ন সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানদের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণে বাংলা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
রাজকীয়তা ও রাজকীয় প্রতিষ্ঠান
![প্রত্নলিপি, বাঙালি, বাঙালিয়ানা ও বাংলায় ইসলাম: কিছু জিজ্ঞাসা [পর্ব ২]](http://nobojagaran.com/wp-content/uploads/2023/07/4-1.png)
বাংলায় মুসলিম শাসনের ইতিহাস ঘটনাবহুল। এই আমলে বাংলায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, কেননা এ মুলুকের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলাম বিস্তৃত হতে শুরু করে। রিয়াদ আল–সালাতীনের মত কয়েকটি আকর গ্রন্থে রাজপ্রাসাদ, শাসকদের প্রকাশ্য ও ব্যক্তিগত জীবন, তাঁদের আগ্রহের বিষয়, দৈনন্দিন কার্যাবলি, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, আইনগত ও বাস্তব মর্যাদা, শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা, ধর্মীয় ঝোঁক ও প্রবণতা, বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ ইত্যাদির পাশাপাশি আরও অনেক বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা এবং এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা কোন সহজ ব্যাপার ছিল না। অনেক শাসক এই এলাকার বাইরে জন্মগ্রহণ করেন বিধায় বহিরাগত হয়ে এ দেশের মাটিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করাও তাঁদের জন্য একটি কঠিন পরীক্ষা ছিল। অনেকে বাংলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, অথচ তাঁদের বংশধারা ছিল মূলত বাংলার বাইরের। এঁদের অনেকের পূর্বপুরুষরা ছিলেন বর্তমান আফগানিস্থান (তথা খুরাসান) থেকে আগত। ফলে নিজের শাসনের বৈধতা প্রতিষ্ঠা করাও যেন কখনো কখনো তাঁদের জন্য কঠিন হত। অধিকন্তু, তাঁদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক ছিলেন রাজকীয় বংশোদ্ভূত। বরং এঁদের কেউ কেউ অতি সাধারণ ও দীনহীন অবস্থা, যেমন ক্রীতদাস-দশা থেকে ক্রমশ সেনাবাহিনীর উঁচু পদে উঠে বাংলার শাসনক্ষমতা দখল করেন। তাঁদের অনেকেরই সামনে ছিল পর্বতপ্রমাণ সমস্যা, অগণিত প্রতিবন্ধকতা। এতদসত্ত্বেও সুলতানী বাংলা ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধি অর্জন করতে থাকে এবং দুই শতাব্দীকাল পর্যন্ত টিকে থাকে (৭৪০-৯৪৪ হিজরী/ ১৩৩৯-১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ)।
সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় যে সংস্কৃতি ও কৃষ্টি গড়ে ওঠে, তা ছিল অভিনব ও বহুমাত্রিক। ইসলামী বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন এলাকা থেকে আগত, বিশেষ করে মধ্য এশিয়া ও পারস্য অঞ্চলের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মুসলমানদের বিচিত্র সংস্কৃতি বিভিন্নভাবে বাংলার জনজীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। স্থানীয় জনসাধারণের এসব ঐতিহাসিক পরিবর্তনে অংশগ্রহণ যথেষ্ট স্বত:স্ফূর্ত ছিল। মুসলিম রাজধানীগুলোতে পারস্য সংস্কৃতির ছাপ সে সময়ে ব্যবহৃত দরবারি উপাধি থেকে দৈনন্দিনের ভাষা ইত্যাদি সব কিছুতেই পড়েছিল। মুসলিম বাংলায় প্রাপ্ত প্রথম ও তৃতীয় ফার্সী শিলালিপির দ্বারা এ ধারণাটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে। মুসলিম শাসনামলে গোড়ার দিকে বাংলার জনসাধারণের সিংহভাগ ছিল হিন্দু, বৌদ্ধ বা অ্যানিমিস্ট (প্রকৃতি পুজারী)। কাজেই এ সময়ের একটি বিশেষ দিক হল আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক। স্বাভাবিক কারণেই অমুসলমানরা মুসলমানদের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করত। শাসনক্ষমতা মূলত মুসলমানদের হাতে থাকলেও অমুসলমানদের অধিকার সাধারণভাবে সুরক্ষিত ছিল। যুদ্ধকালীন সময়ের হানাহানি ও লুণ্ঠনের কথা বাদ দিলে শান্তিপূর্ণ সময়ের জীবন যাত্রা ছিল স্বাভাবিক। সকল সম্প্রদায়ের লোকজন মিলেমিশে থাকত এবং একে অপরের ধর্মীয় স্থাপনাগুলোর প্রতি কমবেশি সকলেই শ্রদ্ধাশীল ছিল।
দেশের সুলতান, শাসক, প্রশাসক, আমীর-উমরাহদের অনেকে তাঁদের ক্ষমতা, শক্তি ও জৌলুস প্রদর্শনের জন্য নিত্য নতুন শহর-জনপদ গড়ে তোলার বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। কেউ কেউ আবার ইন্দ্রিয়পরবশ হয়ে রাজপ্রাসাদের অন্দরমহলে আরাম-আয়েশে ডুবে থাকতেন। একদিকে কেউ কেউ যেমন একাধিক স্ত্রী পরিগ্রহ করতেন, অন্যদিকে অনেকে আবার দূর-দূরান্ত থেকে সুন্দরী ক্রীতদাসী সংগ্রহ করে নিজেদের হারেমের জৌলুস বাড়াতে তৎপর থাকতেন। আবার এঁদেরই মধ্যে জন্ম নেওয়া ব্যতিক্রমধর্মী বদান্য সুলতানেরা যথেষ্ট উদ্যম ও অনুপ্রেরণা নিয়ে জনকল্যাণমূলক কাজ করতেন, যার প্রতিফলন আমরা বাংলার প্রথম সুলতান আলা-দীন আলী মর্দান খলজীর একটি ফার্সী শিলালিপিতে দেখতে পাই। সেই শিলালিপিটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে সুলতানের কল্যাণকর ও সেবামূলক কর্মসূচী আপামর জনসাধারণের জন্য বিস্তৃত ছিল (খায়ের কারদেহ দার হাক্ক–এ খাস ‘আম)।
বাংলার সুলতানদের কারো কারো আমলে বহু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যথা: মকতাব, মাদ্রাসা, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি নির্মিত হয়েছিল। এছাড়াও ‘বিমারিস্থান’ অর্থাৎ হাসপাতাল বা চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার উদাহরণও মাঝে-মধ্যে দেখা যায়। ইসলাম বিস্তারের ক্ষেত্রে এসব জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। বাংলার সুলতানদের এসব জৌলুস, গরিমা ও বিভিন্নমুখি সফলতা অর্জন করা সত্ত্বেও তাঁদের অনেকেই রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় পর্যায়ের বেশ কিছু বুনিয়াদি ও মৌলিক উন্নতি অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। সুলতানী ও মুঘল আমলে মুসলিম শাসকরা বিজ্ঞান, প্রকৌশল, কারিগরি এবং উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে উন্নতি অর্জন করা তো দূরের কথা, প্রাথমিক পদক্ষেপগুলোও নিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ইসলামে সর্বস্তরের মানুষদের জন্য শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া সত্ত্বেও বিষয়টি বাংলার সুলতান কিংবা শাসকের কাছে কোন প্রাধান্য পায়নি। ফলশ্রুতিতে এই নবাগত ইসলামী সভ্যতা একদিকে যেমন ব্যাপক আকারে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে অক্ষম হয়, অন্যদিকে তেমনি নাগরিক সমাজ বিকাশের প্রাথমিক শর্ত যে সর্বস্তরে শিক্ষার প্রসার, সেই দিকে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।
প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেও খুব স্বল্পসংখ্যক সুলতানই কোন বড় ধরনের নৌ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। নদী-নালা, খাল-বিল ও জলাকীর্ণ নিম্নভূমি সম্বলিত এই অঞ্চলটিতে কোন শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তুলতে না পারার কারণে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলবর্তী এলাকাগুলো একরকম অরক্ষিত থেকে যায়, যেখানে মুঘল আমলে একদিকে যেমন বর্তমান মায়ানমার এবং বিশেষ করে আরাকানের মগদস্যুরা দীর্ঘদিন ধরে তাণ্ডব লীলা চালাতে সক্ষম হয়, অন্যদিকে তেমনি ইউরোপের ক্রমবর্ধমান নৌ-শক্তিগুলো বাংলার দিকে লোলুপ দৃষ্টি দিতে শুরু করে।
একপর্যায়ে বাংলার দক্ষিণ দিকে উপকূলের এলাকাগুলো পর্তুগীজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় নৌ-শক্তিগুলোর আখড়ায় পরিণত হয়। সে আমলে বাংলায় তুলনামূলকভাবে উন্নতমানের সামরিক প্রকৌশল, কারিগরি দক্ষতা ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের যথেষ্ট অভাব থাকার কারণে এ অঞ্চলটি ক্রমশই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্বে চলে যেতে থাকে। তবুও স্বীকার করতেই হবে যে পলাশি যুদ্ধের সময় সামরিক কলাকৌশল, রসদ, অস্ত্রশস্ত্র, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য বেশ কিছু দিক থেকে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সামরিক বাহিনী নবাগত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যদের চেয়ে বহুগুণ উন্নত ও শক্তিশালী ছিল। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পতনের কারণ মোটেই কোন সামরিক দুর্বলতা ছিল না। বরং সেটি ছিল ছলে-বলে-কৌশলে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁর সেনাবাহিনীর বড় একটি অংশকে নিষ্ক্রিয় করে, সেনাপতি মীরজাফরের আনুগত্য ক্রয় করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা দখল। এভাবেই লর্ড ক্লাইভ বাজিমাত করে এদেশে কোম্পানির রাজত্ব কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিখ্যাত মানচিত্রবিদ রেনেলের ভাষায় এটি ছিল ‘ক্লাইভের কৌশলে বাজিমাত করে জিতে নেওয়া পলাশীর যুদ্ধ’ (‘ব্যাটল অব প্লাসী গেইমড বাই ক্লাইভ’)।
![প্রত্নলিপি, বাঙালি, বাঙালিয়ানা ও বাংলায় ইসলাম: কিছু জিজ্ঞাসা [পর্ব ২]](http://nobojagaran.com/wp-content/uploads/2023/07/5-1.png)
বাণিজ্য ও সামুদ্রিক যোগাযোগ
প্রাচীন বিশ্বে ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগাযোগ জাতিতে জাতিতে সম্পর্ক, লেনদেন ও বিশ্বায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সে যুগে মুসলিম বিশ্বে তথা প্রাচ্যে বাণিজ্য বহরগুলোর দূর-দূরান্তে যাতায়াত ও বাণিজ্যিক লেনদেন চিরাচরিত মূল্যবোধ ও প্রচলিত নিয়মে সংগঠিত হত। যুদ্ধবিগ্রহ ও অন্যান্য দুর্যোগের কারণে মাঝেমাঝে বাধাপ্রাপ্ত হলেও ঐতিহ্যবাহী এই বাণিজ্যিক প্রক্রিয়াদি উত্তরোত্তর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিকাশ লাভ করতে থাকে। বাংলার প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীর জনপ্রিয় ভ্রমণকাহিনী দেশে–বিদেশে বইটিতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আফগানিস্থানের ঐতিহাসিক বাণিজ্য পথগুলো সম্পর্কে একটি স্পষ্ট মনোরম চিত্র ফুটে উঠে। একই সঙ্গে উট, ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার পিঠে রকমারি বাণিজ্য সামগ্রী বহন করে নিয়ে যাওয়ার চাক্ষুষ বিবরণ পাঠককে এক কল্পনার রাজ্যে নিয়ে যায়। কখনো কখনো এই বাণিজ্যবহরগুলো এতই বড় হত যে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত মাইলেরও বেশি লম্বা হত। আর এই বাণিজ্যবহরগুলোতে থাকত চিকিৎসার জন্য সে যুগের প্রচলিত ব্যবস্থাদি, যেমন: হেকিম (চিকিৎসক), ঔষধপত্র ও চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ইত্যাদি। এগুলোর জন্য একটি বিশেষ উট বা ঘোড়া কিংবা খচ্চর নির্দিষ্ট করা থাকত, যার পিঠে ঔষধ-পত্র বোঝাই করা থাকত। এছাড়াও কোন একটি পশুর পিঠের উপর চাপানো থাকত বিভিন্ন ধরনের পাঠ্যপুস্তক ও লেখার সরঞ্জাম, যা ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার হিসাবে কাজ করত। সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করার সময় অবসর মুহূর্তে কাফেলার জ্ঞানপিপাসুরা তাঁদের তাঁবুতে জিরানোর সময়ে পুস্তকবাহী পশুর পিঠ থেকে পছন্দ মত বই নামিয়ে তাঁদের জ্ঞানপিপাসা নিবৃত করতেন। আর তার সঙ্গে চলত তাঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ কাহিনীগুলোর লিপিবদ্ধকরণ কিংবা বসত শেয়ের, শায়েরী ও মুশা‘ইরার মত মন মাতানো নানা ধরনের মজলিস।
প্রাচীন বাণিজ্যিক পথগুলো দিয়ে সুদূর আফগানিস্থান থেকে আসত শুকনো মেওয়া, আখরোট, বাদাম, পেস্তা ও আরও অনেক কিছু, যার ঝলক কিছুটা আমরা দেখতে পাই রবি ঠাকুরের বিখ্যাত ‘কাবুলিওয়ালা’ গল্পে। এই বাণিজ্যিক পথগুলো বিকাশ লাভ করেছিল স্বাভবিকভাবে, প্রাকৃতিক নিয়মে, ঐতিহ্যবাহী সমাজগুলোর সর্বস্তরের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তা ও সরবরাহের উপর ভিত্তি করে। এই যুগ-যুগের শান্তিপূর্ণ বাণিজ্যিক ব্যবস্থা ও পথগুলো প্রাচ্যে ইউরোপীয় বাণিজ্যের আক্রমণাত্মক নীতির সম্মুখে ধীরে ধীরে অকেজো হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য থেকে আগত এসব বণিক পেশাদারভাবে, প্রয়োজনে সামরিক শক্তি ব্যবহার করে এবং ছলে-বলে-কৌশলে তাদের বাণিজ্যিক প্রাধান্য বিস্তারের প্রতিটা সুযোগই কাজে লাগাতে শুরু করে। ইউরোপীয়দের চাপিয়ে দেওয়া এই বাণিজ্যিক আগ্রাসনের সামনে স্থানীয় ও দেশি বাণিজ্যিক পথ ও ব্যবসাপদ্ধতিগুলো ক্রমশ ভেঙে পড়তে শুরু করে, যার অশুভ প্রভাব ও ফলাফল প্রাচ্যের দেশগুলোতে এখনো পর্যন্ত কোন না কোনভাবে রয়ে গেছে।

বাংলার সাথে বর্হিবিশ্বের বাণিজ্যিক যোগাযোগের বেশ কিছু তথ্য মধ্যযুগের আরবী ও ফার্সী উৎসগুলোতে পাওয়া যায়। বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক নৌপথগুলোর উপর বিস্থারিতভাবে লিখে গেছেন ষোল শতকের গোড়ার দিকে একজন ওমানী নাবিক সুলাইমান ইবনে আহমাদ ইবনে সুলাইমান আল-মাহরী। তাঁর আল-‘উমদা আল–মাহরিয়্যা ফী দ্বাবতে আল-‘উলুম আল–বাহরিয়্যাহ এবং আল–মিনহাজ আল–ফাখির ফী ‘ইলম আল–বাহর আল–যাখির নামের বই দুটোতে বঙ্গোপসাগর সম্পর্কে বহু চাঞ্চল্যকর ও চিত্তাকর্ষক তথ্যাদি পরিবেশিত হয়েছে, যেমন: জোয়ার-ভাটা, বিভিন্ন জায়গার সামুদ্রিক জলের স্রোতপ্রবাহ, স্রোতের দিক নির্ণয়, বায়ুর বেগ, গতিপথ, ইত্যাদি। সেই যুগের পাল তোলা জাহাজের গতি সঞ্চালন এবং এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাতায়াতের জন্য যেসব তথ্যের প্রয়োজন, সেসব বিস্তারিত ও মূল্যবান তথ্যাদি এই বইগুলোতে পাওয়া যায়। সুবিশাল ভারতীয় মহাসাগরের প্রতিটি জায়গার বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্যের ভাণ্ডার মুসলিম নাবিকদেরকে তাদের বিশাল সামুদ্রিক কার্যক্রম আরও বিস্থারিত ও সুনিপুণভাবে সম্পাদন করতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে প্রাচ্যের এসব সামুদ্রিক জ্ঞানভাণ্ডার ক্রমশ ইউরোপীয় নাবিকদের কাছে পৌঁছতে শুরু করে, যা পরবর্তীকালে তাদের সামুদ্রিক পথে পাড়ি জমিয়ে প্রাচ্যে পৌঁছতে সাহায্য করে। এক পর্যায়ে ইউরোপীয় সামুদ্রিক জাহাজগুলোর আগ্রাসনের মুখে প্রাচ্যের নৌ-যানগুলো এক রকম অসহায় হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে। পরিণামে এক সময় পুরোপুরিভাবে ইউরোপীয়রা প্রাচ্যের সামুদ্রিক পথগুলো দখল করে নেয়।
ষোল শতকের প্রথম থেকে ভারত মহাসাগরে প্রাচ্যের সামুদ্রিক কার্যক্রমের প্রতি ক্রমাগত ইউরোপীয় হুমকি সত্ত্বেও আরব ও পারসিক বাণিজ্যিক জাহাজগুলো আঠার শতক পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন বন্দর, বিশেষ করে ওমান থেকে বঙ্গোপসাগরে আসতে থাকে। বাংলার সুতিবস্ত্র মসলিন এবং অন্যান্য উন্নতমানের পণ্যের জন্য তারা এই দেশে আসত। সুলতানী আমলে, বিশেষ করে রাজা গণেশের পুত্র বাঙালি মুসলমান সুলতান জালাল আল-দীন মুহম্মদ শাহের (৮১৮-৩৬ হিজরী/ ১৪১৪-৩৩ খ্রিস্টাব্দ) শাসনামলে বাংলার সঙ্গে মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশের যোগাযোগ বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও ঘটে। এভাবে বাংলার বাজার ভারতীয় মহাসাগরের ক্রমবর্ধমান সমুদ্র-বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। বাংলার কৃষি ও শিল্পপণ্য সমুদ্র-বাণিজ্যের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে রপ্তানির সুযোগ পায়। ধীরে ধীরে বাংলা তথা সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া ক্রমাগত বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হতে থাকে। মধ্যযুগে ইসলামী সভ্যতা সমসাময়িক প্রাচীন দুনিয়ার উপর বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল এবং এ প্রভাব পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক শক্তির আগমন পর্যন্ত বজায় ছিল। সম্রাট আকবরের আমলে সমগ্র বাংলা মুঘলদের অধিকারে আসে এবং গ্রামে-গঞ্জে তৃণমূল পর্যায়ে, এমনকি দক্ষিণের নিচু জলাভূমি অঞ্চলেও, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিস্তার ঘটে। এর ফলে বহির্বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে বাংলা অঞ্চল অধিকতর যুক্ত হয়। ইটনের দৃষ্টিতে ইসলাম বাংলা ভূখণ্ডে একটি সভ্যতা নির্মাণকারী আদর্শ হিসেবে নিজের স্থান করে নেয়।72
বাংলার মসজিদ: সমাজ ও আধ্যাত্মিক জীবনের মিলনকেন্দ্র
![প্রত্নলিপি, বাঙালি, বাঙালিয়ানা ও বাংলায় ইসলাম: কিছু জিজ্ঞাসা [পর্ব ২]](http://nobojagaran.com/wp-content/uploads/2023/07/6-2.png)
ইবনে খালদুন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ মুকাদ্দিমায় মন্তব্য করেছেন যে স্থাপত্য হচ্ছে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতি (আল-‘উমরান) প্রকাশের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ইসলামী সভ্যতায় বরাবরই স্থাপত্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে দেখা যায়। বিভিন্ন সময়ে শাসকগণ তাঁদের বৈধতা, ক্ষমতা ও মাহাত্ম্যের প্রতীক ও দ্যোতক হিসেবে স্থাপত্যকে বেছে নেয়। ইসলামী স্থাপত্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইমারত হল মসজিদ। মসজিদ স্থাপত্য কতকটা স্বাভাবিক কারণেই মুসলিম জীবনযাত্রার সাংস্কৃতিক প্রকাশ এবং বহুলাংশে ইসলামী ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র। আরবী ভাষার মাসজিদ (مسجد) শব্দের মূল ধাতু সজদ, অর্থাৎ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত। গভীরভাবে দেখতে গেলে মসজিদ হল ইসলামের আধ্যাত্মিক জগতের বাস্তব রূপায়ণ। এখানে স্থাপত্য ও ইসলামী ধ্যান-ধারণার সম্পর্ক স্পষ্ট। মসজিদের গঠন, এর মিনার, মিম্বার এবং অন্যান্য স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যগুলি ইসলামী সংস্কৃতির এক অভিনব নান্দনিক প্রকাশ। সাহন তথা উঠানের দুইদিকের সারিবদ্ধ খিলানের উন্মুক্ত জায়গা নামাজের দিক নির্দেশ করে এবং একই সঙ্গে মসজিদে আগমনকারীকে পার্থিব জগৎ থেকে পারলৌকিক জগতের দিকে ক্রমাগত গমনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এর মিহরাব মাত্রই কিবলার (অর্থাৎ মক্কা বা কাবা) অভিমুখ বলে দেয়, যা প্রকারান্তরে ঐক্যের এবং তাওহীদের (তথা একত্ববাদের) শক্তিশালী বাণীর প্রতীক বহন করে। মুসলিম সমাজে মসজিদের একটি শক্তিশালী আবেদন রয়েছে। কেননা প্রতি সপ্তাহে শুক্রবারে জুমআর প্রার্থনা ছাড়াও দিনে ও রাতে প্রার্থনার উদ্দেশ্যে মুসলমানরা এখানে একত্র হয়। এভাবে মসজিদ মুসলমানদের সামগ্রিক জীবনকে এক সূত্রে গাঁথে ।
অনেকে জেনে আশ্চর্য হতে পারেন যে বাংলায় এবং অন্যান্য অনেক মুসলিম দেশে মসজিদের সংখ্যা এখনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। খোদ বাংলাদেশেই দু লাখেরও বেশি মসজিদ রয়েছে। এর অন্যতম অন্তর্নিহিত কারণ হল, বাঙালি সমাজে মসজিদ বহুবিধ কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত মসজিদগুলো মুসলমান সমাজের মক্তব বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ করত এবং কোথাও কোথাও এখনো করে। নগর-জীবনে দেখা যায় যে মসজিদের সঙ্গে অনেক সময় বিপণী-বিতান বা বাজার সংযুক্ত করা হয়েছে। ঢাকার তথা বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মসজিদ ‘বায়তুল মুকার্রাম’ এর অন্যতম উদাহরণ। ইসলামী জীবনদর্শনে ধর্মীয় কাজকর্ম থেকে জাগতিক জীবনের কাজ যে তেমন বিচ্ছিন্ন কিছু একটা নয় এটি তারই নমুনা মাত্র। স্থানীয় জনগণের জীবনের স্রোতধারাকে ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার জন্যই যেন মসজিদগুলোকে জনবসতির ঠিক মাঝামাঝিই গড়ে তোলা হয়।
ঐতিহাসিক দিক থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে বাংলার অনেক মুসলিম জনবসতি একটি জুম‘আ মসজিদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। শহরের কেন্দ্রস্থলে কেন্দ্রীয় মসজিদের আশেপাশে দৈনন্দিন জীবনের স্থাপনাগুলোর নির্মাণ (বাজার, সরাইখানা, হাসপাতাল, ঝরনা, কুয়া, পুকুর ইত্যাদি) ধর্মীয় জীবন ও সাধারণ জীবনের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে। একই সঙ্গে তা জনকল্যাণমূলক কাজকর্মের বিস্তারের লক্ষে কাজ করে এবং সে এলাকায় ইসলাম বিস্থারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখতে গেলে লক্ষ্য করা যায়, বাংলায় মসজিদ নির্মাণ এবং সুলতানদের জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি সাধারণ জনগণের মধ্যে ইসলামের প্রসারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বেশ কিছু প্রাথমিক শিলালিপি এ সমস্ত পূর্ত কাজের বিবরণ দেয়।73 ১২০৫ থেকে শুরু করে ১৭০৭ পর্যন্ত বাংলায় প্রাপ্ত ইসলামী শিলালিপিগুলোর মধ্যে মসজিদের শিলালিপি সর্বাধিক (সংখ্যায় তিন শতাধিক)। এসব শিলালিপি ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সামগ্রিক ক্ষেত্রে মসজিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার দিকে ইঙ্গিত করে (মানচিত্র ৩ দ্রষ্টব্য)।74 বাংলায় প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীন ইসলামী সাহিত্যকর্ম হাউজ আল–হায়াতে বর্ণিত ঘটনাবলির আলোকে সহজে অনুমান করা যায় যে অমুসলিমদের ইসলামী উপাসনা রীতি পরিদর্শন, ইসলামের বিষয়ে অনুসন্ধান ও ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা ও বিতর্কের জন্য মসজিদে আহ্বান জানানো হত। মসজিদের দরজা মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্য খোলা রাখার ঐতিহ্য সাধারণ জনমানসের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। মন্দিরে প্রবেশের ক্ষেত্রে সাধারণত যেমন জাতপাতের নিষেধাজ্ঞা থাকত, মসজিদের ক্ষেত্রে সেটা ছিল না। আন্তঃধর্মীয় হৃদ্যতা প্রতিষ্ঠায়ও মসজিদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। মুসলিম শাসক ও ধনবানরা যেমন কখনো কখনো মন্দির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়াত, তেমনি কোন কোন ধনী ও প্রভাবশালী হিন্দু জনকল্যাণমূলক কাজ হিসেবে মসজিদ নির্মাণে সহায়তার জন্য এগিয়ে আসত।
![প্রত্নলিপি, বাঙালি, বাঙালিয়ানা ও বাংলায় ইসলাম: কিছু জিজ্ঞাসা [পর্ব ২]](http://nobojagaran.com/wp-content/uploads/2023/07/7-1.png)
ছোট শহরগুলোতে দেশীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সাধারণ গোছের পাঞ্জেগানা অর্থাৎ দৈনিক পাঁচবার নামাজের জন্য মসজিদ তৈরি করার রীতি এ দেশে মুসলিমদের আগমনের পর পরই আরম্ভ হয়ে যায় এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। গ্রামবাংলার মসজিদের ঐতিহ্যগত স্থাপত্যের মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে মিল সৃষ্টি করার একটি চমকপ্রদ দিক লক্ষ্য করা যায়। স্থানীয় ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য অনুসারে এই মসজিদগুলো মাটির দেওয়ালের উপর চালার তৈরি ছাদ দিয়ে তৈরি করা হত। এটি অনেকটা ইতিহাসের সর্বপ্রথম মসজিদ মদীনার ‘মসজিদ নাবাওয়ী’ (নবী মসজিদ) এর মত। বাংলার এ মসজিদগুলির সঙ্গে প্রায়শই একটি গভীর ও বড় পুকুর বা দীঘি সংযুক্ত থাকত, যা পরিবেশে একটি স্নিগ্ধ ছাপ এনে দিত, সেই সঙ্গে ওযু বা প্রক্ষালনের স্থান হিসেবেও ব্যবহৃত হত। ভাবতেই আশ্চর্য লাগে যে বাংলার পল্লী এলাকার এ মসজিদগুলির স্থানীয় স্থাপত্য অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ইসলামের আদি যুগের মদীনার নবীর মসজিদের আয়তাকার নকশার অনুরূপ ছিল। উত্তর বাংলার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাল, খেজুর জাতীয় গাছগুলো পল্লী এলাকায় দোচালা বা চৌচালা রীতির মসজিদের ছাদের জন্য বর্গার কাজে ব্যবহৃত হত, ঠিক যেমনটি আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগে নবীজীর মসজিদের কাঠামোটি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। সাহন বা উঠান নবীর মসজিদের আরেকটি মূল বৈশিষ্ট্য ছিল যার ছাপ এখন পর্যন্ত বাংলার গ্রামের অনেক মসজিদে রয়ে গেছে। যে বিষয়টি আমাদের অবাক করে, তা হল মসজিদ স্থাপত্যের অনেক রীতিই যুগের পর যুগ ধরে নবীজির মসজিদের মূল নকশার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো বহন করে এসেছে। নবীর যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মসজিদ স্থাপত্যের এই ধারার সুদূর গ্রামবাংলার পল্লী এলাকায় অনুসৃত হওয়ার ঐতিহ্যটি সত্যিই অদ্ভূত। ক্ষুদ্রাকারের এ সাধারণ মসজিদগুলো এককালে গ্রামবাংলার সর্বত্রই দেখা যেত। এগুলো প্রায়শই বাংলার মুসলিম পল্লীগুলোর কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করত। গ্রামবাংলার কিছু কিছু মসজিদে এখনো এ ঐতিহ্যর ছাপ রয়ে গেছে। মসজিদের গ্রাম্য স্থাপত্য আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে সত্যিকারের সময়োপযোগী ও সুদূরপ্রসারী সফল স্থাপত্য শুধুমাত্র কারিগরি শৈলী ও অবকাঠামোর নৈপুণ্যের দিকে দৃষ্টি দেয় না, বরং এটি জনসাধারণ, তাদের পরিবেশ ও প্রকৃতির দিকেও নজর রাখে।
ইসলামী উপাসনালয় ও প্রার্থনা-স্থলের এ ধরনের সাদামাটা অথচ পরিবেশ উপযোগী স্থাপত্য জনসাধারণের ধর্মান্তরেও সহায়তা করে। সুলতানী ও মুঘল আমলে শহর এলাকার মসজিদগুলো সুলতান অথবা তাঁদের পরিবারের সদস্যবর্গ, উযীর, কর্মকর্তা এবং ধনী নারী-পুরুষগণ তৈরি করত। গৌড়ের পুরুলিয়ায় বোয়া মালতী নামের এক ধনী মহিলা একটি জামে মসজিদ তৈরি করেছিলেন (জাহানিয়ান জামে মসজিদের শিলালিপি ৯৪১ হিজরী/ ১৫৩৪-৩৫ খ্রিস্টাব্দ)। পক্ষান্তরে গ্রাম্য মসজিদগুলো জনসাধারণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অথবা সূফী-সাধক, আলেম কিংবা সাধারণ ধার্মিক ব্যক্তিদের দ্বারা নির্মিত হত। এখন পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ ধার্মিক লোকের সক্রিয় সহযোগিতায় এবং দরিদ্র জনসাধারণের চাঁদার টাকায় গ্রাম বাংলার সাদামাটা মসজিদগুলো নির্মিত হয়। ঐতিহাসিকভাবে এগুলো ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং জঙ্গল পরিষ্কার করে নতুন বসতি স্থাপনে সহায়তা করত। অন্যদিকে নিত্য-নতুন গড়ে ওঠা জনবসতিগুলো নতুন মসজিদ স্থাপনের বিষয়ে বিশেষ সাড়া জাগাত। সার্বিকভাবে বাংলায় নতুন মসজিদ স্থাপন ইসলামের প্রসারের ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে।76 এসব মসজিদ প্রায়শই লা-খেরাজ বা নিষ্কর সম্পত্তি লাভ করত। এ সমস্ত জমি চাষাবাদের ফলে প্রাপ্ত রাজস্ব একদিকে মসজিদগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যেমন ব্যয় হত, তেমনিভাবে এসব আয় থেকে মসজিদের দায়িত্বে নিয়োজিত ও সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের (যেমন সূফী, আলেম ইত্যাদি), বিশেষ করে ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের ভরণ-পোষণের খরচও বহন করা হত।
ধর্মীয় কাজে ওয়াক্বফকৃত ধনসম্পত্তি ও দানের প্রথা মদদ–ই–মা‘আশ নামে পরিচিত ছিল। এর দ্বারা মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহের মত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিক সহায়তা পেত ও মদদপুষ্ট হত। এছাড়া এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে আগত দরিদ্ররাও সহায়তা পেত, যার কিছুটা আভাস আমরা বর্ধমান শহরের বাহরাম সাক্কার সমাধিলিপি (১০১৫ হিজরী/ ১৬০৬-০৭ খ্রিস্টাব্দ) এবং ঢাকার বড় কাটরার শিলালিপিসমূহে (১০৫৫ হিজরী/ ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ) উৎকীর্ণ তথ্যে দেখতে পাই।77 দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় এবং বাংলার নদীর গতি পরিবর্তনের কারণে জেগে ওঠা অনাবাদী জমিতে অনেকে নিজে উদ্যোগী হয়ে নতুন মসজিদ তৈরি করতেন। দূরবর্তী এলাকায় এসব নতুন মসজিদ স্থাপনকারীদেরকে কখনো কখনো সরাসরি এ ধরনের লাখেরাজ সম্পত্তি দেওয়া হত। নোয়াখালী, সিলেট ও চট্টগ্রামে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়গুলোর রেকর্ড রুমে এখন পর্যন্ত মুঘল আমলের কিছু দুর্লভ ভূমি-দানপত্র তথা সনদ রক্ষিত রয়ে গেছে। এগুলোর বেশির ভাগই ফার্সী ভাষায় লেখা। এসব সনদে স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দ্বারা মসজিদ স্থাপনের জন্য ভূমি দানের উল্লেখ রয়েছে।78 সুলতানী আমলের শেষের দিকে এবং মুঘল আমলের প্রথমার্ধে বাংলার বিভিন্ন জায়গায় এমন অনেক মসজিদ স্থাপিত হয়, যেখানে মদদ–ই–মাআশের জন্য সম্পত্তি ওয়াক্বফ করা হয়।79 নতুন মানব বসতি স্থাপনে এবং কৃষি সমাজ গঠনে মসজিদগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনবিরল পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার নিচু ও জঙ্গল এলাকায় মদদ–ই–মা‘আশ এর জন্য সম্পত্তি ওয়াক্বফ করার রীতি একদিকে যেমন নতুন মসজিদ গড়ে তুলতে সাহায্য করে, অন্যদিকে তেমনি নতুন নতুন গ্রাম স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
রাজধানী ও তার আশেপাশে এবং অন্যান্য বড় শহরে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বহু সংখ্যক মসজিদ নির্মিত হয়। গৌড়, পাণ্ডুয়া, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের মত জাঁকজমকপূর্ণ রাজধানীগুলোর মসজিদ স্থাপত্য অবশ্য কিছুটা ভিন্ন ভাবের পরিচয় বহন করে। বলা বাহুল্য যে এসব স্থাপত্য রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও দরবারি রুচির আভাস দেয়। পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ (৭৭৬ হিজরী/ ১৩৭৪ খ্রিস্টাব্দ) এবং বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ (উলুঘ খান জাহানের সমাধির শিলালিপির তারিখ ৮৬৩ হিজরী/ ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দ) দুটি এখন পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়ায় নির্মিত বৃহত্তম মসজিদগুলোর মধ্যে গণ্য হয়। শুধু তাই নয়, মধ্যযুগের মুসলিম বিশ্বের বৃহত্তম মসজিদগুলোর মধ্যে এ দুটি নিঃসন্দেহে অন্যতম ছিল।
![প্রত্নলিপি, বাঙালি, বাঙালিয়ানা ও বাংলায় ইসলাম: কিছু জিজ্ঞাসা [পর্ব ২]](http://nobojagaran.com/wp-content/uploads/2023/07/8-2.png)
মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষা ও জ্ঞান–বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার
বাংলার শিলালিপিগুলোতে বেশ কিছু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বিরাট সংখ্যক মাদ্রাসা একদিকে যেমন শিক্ষা-দীক্ষা সম্প্রসারণে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল, অন্যদিকে এগুলো একটি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বভাবতই এসব বিদ্যাপীঠ থেকে যেসব শিক্ষাবিদ ও পণ্ডিত তথা উলামা বের হতেন, তাঁরা দেশের বিভিন্ন জায়গায় ও বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা সম্প্রসারণের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতেন। এঁদের অনেকে ছিলেন সূফী সাধক, যাঁরা খানকাহে বসে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক চর্চার প্রশিক্ষণও দিতেন। এঁদের অনেকেই স্থানীয় সন্ন্যাসী ও যোগীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন, যাদের সাথে তাঁদের একটা মানসিক যোগসূত্র কায়েম হয়েছিল।
তের শতকের একেবারে প্রথমদিকে সুলতান ‘আলা-দীন আলী মর্দান খিলজীর শাসনকালে এমনই একটা যোগাযোগ ঘটেছিল কামরূপের কামাখ্যা মন্দিরের পুরোহিত ভোজার ব্রাহ্মণ এবং লক্ষণাবতীর মুফতী ও ইমাম রুকন আল-দীন সামারক্বান্দীর মধ্যে। এই সাক্ষাৎ এক পর্যায়ে গড়ায় পণ্ডিত ভোজার ব্রাহ্মণের ইসলাম দীক্ষার মধ্য দিয়ে। পণ্ডিতজির সাহায্য নিয়ে রুকন আল-দীন সামারক্বান্দী যোগবিদ্যার উপর সংস্কৃত ভাষায় লেখা অমৃতকুণ্ড নামের সে যুগের অন্যতম একটি বই প্রথমে আরবীতে ও পরে ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেন। এর নামকরণ করা হয় আরবীতে হাউজ আল–হায়াত আর ফার্সীতে আবে হায়াত । অতি স্বাভাবকি কারণে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদান-প্রদানের প্রক্রিয়া একেবারে মুসলিম শাসনের প্রারম্ভ থেকে আরম্ভ হয়ে যায়। দু-চারটে বিরল উদাহরণ থেকে এও অনুমান করা যায় যে জ্ঞানপিপাসু হিন্দু তথা অমুসলিম ছাত্ররা মাদ্রাসা থেকেও শিক্ষা আহরণে পিছপা হত না। রাজা রামমোহন রায় স্বয়ং নিজেই একটি মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করে সে যুগের একজন বিখ্যাত আরবী ও ফার্সীবিদ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তাঁকে সেকালের একজন ‘জবরদস্ত মৌলবী’ বলে অভিহিত করা হত। তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থগুলো আরবী ও ফার্সী ভাষায় রচিত (যেমন: তুহফাতু ’ল–মুওয়াহ্হিদীন) এবং ধর্ম বিষয়ে সে যুগের একটি অনবদ্য রচনা। কুরআনের সর্বপ্রথম বাংলা অনুবাদক গিরীশচন্দ্র সেনের আরবী-ফার্সী জ্ঞান খুব গভীর ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে গৌড় অঞ্চলের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত মুনশী শ্যামপ্রসাদ আরবী ও ফার্সী ভাষায় এতই দখল রাখতেন যে সে এলাকার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন কর্মচারী কর্নেল উইলিয়াম ফ্রাঙ্কলিনের মুন্শী হিসেবে তিনি নিয়োগ প্রাপ্ত হন। এই মুনশী শ্যামপ্রসাদই গৌড় ও পান্ডুয়ার পুরাকীর্ত্তির উপরে সর্বপ্রথম একটি ফার্সী বই আহওয়াল–ই–গৌড় ওয়া পাণ্ডুয়া রচনা করেন।80
![প্রত্নলিপি, বাঙালি, বাঙালিয়ানা ও বাংলায় ইসলাম: কিছু জিজ্ঞাসা [পর্ব ২]](http://nobojagaran.com/wp-content/uploads/2023/07/10-1.png)
বাংলার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু সংখ্যক আলেম সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন খাতে চাকরির সুযোগ সুবিধা পেতেন, ঠিক যেমন বর্তমানকালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন ধরনের চাকরির সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে সে যুগের মাদ্রাসাগুলো বর্তমান কালের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মতই ভূমিকা পালন করত। মাদ্রাসা ও খানকাহ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রশিক্ষণের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। তবে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা গ্রহণের জন্য সাধারণত শিক্ষানবিশদের প্রায় সকলকেই স্থানীয় মাদ্রাসায় বা মক্তবে গিয়ে হাতেখড়ি নিতে হত। মাদ্রাসায় শিক্ষা সমাপ্তির পর যারা চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ পেতে চাইত, তারা সে এলাকার কোনো বিখ্যাত হাকিমের তথা চিকিৎসকের দ্বারস্থ হত এবং তার সহায়ক হিসেবে কাজ করতে করতে হাতে কলমে চিকিৎসাবিদ্যা রপ্ত করত। অনেকে আবার সে যুগের হাসপাতাল বা চিকিৎসালয়গুলোতে (যা ‘বীমারিস্থান’ নামে খ্যাত ছিল) যোগদান করত এবং সেখানে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত পুরোদস্তুর হেকিম (চিকিৎসক/ ডাক্তার) হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেত। আর যারা জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে আগ্রহী হত, তারা প্রশিক্ষণের জন্য যোগদান করত মানমন্দিরগুলোতে। সামরিক শিক্ষার জন্য আবার শিক্ষানবিশরা সেনাবাহিনীতে যোগদান করত। অনেক ক্ষেত্রে কারিগরি ও পেশাদার প্রশিক্ষণগুলো পারিবারিক সূত্রে বংশানুক্রমে শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে চলতে থাকত। ঠিক যেমন যুগ যুগ ধরে হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় কুমোররা মৃত্তিকার কাজ, কামাররা লোহার কাজ, স্বর্ণকাররা সোনার কাজ ইত্যাদি ধরনের পিতৃপুরুষের পেশাগত কর্মগুলো বংশপরম্পরায় প্রশিক্ষণ পাওয়ার মাধ্যমে ধরে রাখার ব্যবস্থা জারি রাখে।
বাংলার শিলালিপিগুলো এসব বিষয়ে কিছু কিছু আলোকপাত করে। এসব শিলালিপির মাধ্যমে আমরা কিছুটা জানতে পারি যে বাংলার বিভিন্ন জায়গায় মাদ্রাসাবাড়ি, দারসবাড়ি ইত্যদি নামের বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। অনেক ক্ষেত্রে বড় বড় জামে মসজিদ মাদ্রাসার ভূমিকা পালন করত। আবার ছোট ছোট ওয়াক্তিয়া অর্থাৎ দৈনিক পাঁচ বারের নামাজের জন্য নির্মিত মসজিদের বেশির ভাগই মক্তব হিসেবে কাজ করত, যেখানে ছোট বাচ্চারা অক্ষরজ্ঞান ও প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করত। আজ পর্যন্ত আরবী অক্ষর শিক্ষাদানের সেই পুরাতন ঐতিহ্য অনেকাংশে টিকে রয়েছে। রাজশাহী শহরের কাছাকাছি নৌহাটা নামক জায়গায় প্রাপ্ত তের শতকের বাংলার ক্ষণস্থায়ী মুসলিম শাসক বলকা খান খিলজীর ( ৬২৬-২৮হিজরী/ ১২২৯-৩১ খ্রিস্টাব্দ) আমলের একটি শিলালিপিতে আমরা দেখতে পাই যে সে এলাকায় এমন একটি ইমারত তৈরি করা হয়েছিল, যা মসজিদের ভূমিকা পালন করার সঙ্গে সঙ্গে একটি উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষাঙ্গন ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাংলার যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য আরবী-ফার্সী শিলালিপির আলোকে আমরা সহজে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে তের শতকের প্রারম্ভ থেকে রাজধানী গৌড় শহর বাংলার উত্তরাঞ্চলে সাংস্কৃতিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার একটি মুখ্য কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। সেখানে বহু শিক্ষাকেন্দ্র ও মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। এছাড়া গৌড়ে অসংখ্য মসজিদও নির্মিত হয়, যেগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাদ্রাসার ভূমিকা পালন করত। খোদ গৌড় ও তার আশেপাশের এলাকাগুলোতে ৫০টিরও বেশি মসজিদ সংক্রান্ত শিলালিপি পাওয়া গেছে। এছাড়া সেখানে বেশ কিছু খানকাহও নির্মিত হয়েছিল, যেখানে সূফীদের আধ্যাত্মিক তালিম অর্থাৎ প্রশিক্ষণও দেওয়া হত।
বাংলার উত্তরাঞ্চলের আরেকটি শহর হজরত পাণ্ডুয়ায়ও একইভাবে মসজিদ, খানকা ও মাদ্রাসার বহু শিলালিপি পাওয়া গেছে। সেগুলো পাণ্ডুয়া শহর ও তৎসন্নিহিত এলাকার সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডের প্রতি ইঙ্গিত রাখে। বাংলার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ঢাকা সন্নিহিত সোনারগাঁ অঞ্চলটিও চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়, যেখানে ইসলামী জীবনদর্শনের হান্বালী মজহাবের (ইসলামের চারটি মূল ধারার আইন ও আইনি দর্শনের একটি ঘরানা) একজন প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট পণ্ডিত শায়খ শারাফ আল-দীন আবু তাওয়ামার তত্ত্বাবধানে একটি মাদ্রাসা বিশাল আকারের আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্রের রূপ নেয়। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেশ বিদেশ থেকে জ্ঞান অন্বেষণে আগত বিদ্যার্থীরা ভিড় জমাত। চৌদ্দ শতকে বিখ্যাত মনীষী শাইখ শারাফ আল-দীন য়াহয়া মানেরীও এক পর্যায়ে উত্তর ভারত থেকে এই বিদ্যা নিকেতনে এসে বিভিন্ন শাস্ত্রে এতই ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন যে সমগ্র উপমহাদেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে গিয়েছিল। এর পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে ষোল ও সতের শতকে তান্ডা (তাঁড়া), রাজমহল, জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা) ও মুর্শিদাবাদ বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে।
মুঘল যুগে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে বর্তমান দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট নামক জায়গার একটি সুবিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা না উল্লেখ করলেই নয়, যা বহু মনীষী ও প্রখ্যাত শিক্ষাবিদকে আকর্ষণ করেছিল। অন্যদিকে বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ত্রিবেণী এবং বর্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত ছোট পাণ্ডুয়া ইত্যাদি শহরগুলোতেও বেশ কতগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ও নামকরা বিদ্যাপীঠটির নাম ছিল দার আল-খায়রাত। সেখানে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি অনুযায়ী এটি ৭১৩ হিজরীতে/ ১৩১৩ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল। ত্রিবেণী থেকে অদূরে বর্তমান বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট শহরে যে বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিল, তা উনিশ শতকের শেষ অবধি কোনমতে টিকে থাকে। এর বিখ্যাত গ্রন্থাগারের বহু দুর্লভ পাণ্ডুলিপি ও বই মাদ্রাসাটি শোচনীয়ভাবে বিলুপ্ত হওয়ার সময় কলকাতার ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থাগার বা ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ করা হয়। ব্রিটিশ আমলে বাংলার দক্ষিণ-পূর্বাঅঞ্চলের বন্দর শহর চট্টগ্রামও একটি শিক্ষা-দীক্ষার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। উনিশ শতকের শেষের দিকে গড়ে ওঠা মহসিনিয়া মাদ্রাসা এবং বিশ শতকে গড়ে উঠা হাটহাজারী মাদ্রাসা সে এলাকায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো ছড়াতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। হাটহাজারী মাদ্রাসায় বার্মা (বর্তমান মায়ানমার) এবং বিশেষ করে আরাকান ইত্যাদি দূর-দূরান্ত অঞ্চল থেকে ছাত্ররা পড়াশুনা করতে আসত। মাদ্রাসাটি এখন পর্যন্ত বেশ সাফল্যের সঙ্গে টিকে আছে।
মুসলিম শাসনামলে বাংলার সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান দক্ষিণ এশিয়ার পরিধি ছাড়িয়ে কতকটা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সময়ে মধ্য এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া ও আরব বিশ্ব থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ, উলামা ও সূফী সাধকদেরকে বাংলায় আনাগোনা করতে দেখা যায়। এদের অনেকেই বাংলার বিখ্যাত মাদ্রাসা, খানকাহ এবং অন্যান্য বিদ্যাপীঠের সঙ্গে ক্রমশ জড়িয়ে পড়ে এবং কেউ কেউ এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। ৮১৩-১৪ হিজরী/ ১৪১০-১১ খ্রিস্টাব্দ) সময়কালে বাংলার ইলিয়াস শাহী বংশের একজন বিখ্যাত সুলতান আ‘যম শাহ মক্কা শরীফ ও মদীনা শরিফে একটি করে বিদ্যাপিঠ বা বিশ্ববিদ্যালয় (মাদ্রাসা) নির্মাণ করেন। মক্কার মাদ্রাসাটি মসজিদ-আল-হারামের উম্মে হানী তোরণদ্বার (যা আল-রুকন আল-য়ামানী বা য়ামানী কোণার দিকে অবস্থিত ছিল) থেকে অনতিদূরে স্থাপিত হয়েছিল। আবার মদীনার মাদ্রাসাটি নবীজীর মসজিদ অর্থাৎ মসজিদ নাবাওয়ীর একটি দরজা বাব আল-সালামের (অর্থাৎ শান্তির দরজা) কাছাকাছি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সুলতান গিয়াস আল-দীনের নামে নামাঙ্কিত এই মাদ্রাসা দুটি ‘আল-মাদ্রাসা আল-সুলতানিয়্যা আল-গিয়্যাসিয়্যাহ আল-বাঙ্গালিয়াহ’ (অর্থাৎ বাঙালি বিশ্ববিদ্যালয়) নামে খ্যাত হয়েছিল। সুলতান আ‘যম শাহ এ মাদ্রাসাটির রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণ-পোষণ ও খরচাদির জন্য বেশ কিছু জমি-জায়গা ও ধন-সম্পত্তি ওয়াক্বফ স্বরূপ বরাদ্দ করেন। খুব শীঘ্রই এ বাঙ্গালি বিশ্ববিদ্যালয় দুটির সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে যায় যা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাঙালি জাতির পরিচয়কে বিশেষভাবে তুলে ধরে।
মক্কার মাদ্রাসাটির নির্মাণকার্য শুরু হয় ৮১৩ হিজরী (১৪১১ খ্রিস্টাব্দ) সালের রমজান মাসে এবং উদ্বোধন করা হয় ৮১৪ হিজরী/ ১৪১২ খ্রিস্টাব্দ সালে। সে যুগের বহু গণ্যমান্য পণ্ডিতবর্গ এই মাদ্রাসা দুটিতে অধ্যাপনা ও গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। এদের মধ্যে একজন শাইখ তাক্বী আল-দীন আল-ফাসী (৭৭৫-৮৩২ হিজরী/ ১৩১৪-১৪২৮ খ্রিস্টাব্দ) ইসলামী আইন শাস্ত্রে মালিকী মজহাবের বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এছাড়া সে যুগের একজন শিলালিপি বিশেষজ্ঞ হিসাবেও তিনি পরিচিতি লাভ করেছিলেন। এই মাদ্রাসাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরেকজন উল্লেখযোগ্য পণ্ডিত ছিলেন জামাল আল-দীন আহমদ ইবন আলী আল-শীবী (৭৭৯-৮৩৭ হিজরী/ ১৩৭৮-১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দ)। শিলালিপি গবেষণায় তাঁর মৌলিক অবদানটি নিঃসন্দেহে শিলালিপি বিদ্যার পথের দিশারী। আল-শীবীর পরিবারটি মক্কার সে যুগের একটি অতি পরিশীলিত ও সংস্কৃতিমনা পরিবার বলে গণ্য হত। এই পরিবারের আরও অনেকে মক্কার বাঙালি মাদ্রাসায় পঠন-পাঠন ও শিক্ষাদানের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে সংযুক্ত হয়েছিল।
মক্কার এ বাঙালি মাদ্রাসার সঙ্গে সংযুক্ত পণ্ডিতবর্গ ও অধ্যাপকদের সম্পর্কে আল-ফাসী বেশ কিছু চমৎকার তথ্য পরিবেশন করে গেছেন। এ বাঙালি মাদ্রাসার সঙ্গে সংযুক্তদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কাজী (বিচারপতি) জামাল আল-দীন আহমাদ ইবন ‘আবদ-আল্লাহ আল-কারশী (মৃত্যু ৮১৭ হিজরী/ ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দ), শিহাব আল-দীন আবু ’ল-খায়ের আহমাদ ইবন মুহম্মদ আল-সাগানী (মৃত্যু ৮২৫ হিজরী/ ১৪২২ খ্রিস্টাব্দ), কাজী মুহয়ী ’ল-দীন ‘আবদ আল-কাদীর আল-হুসাইনী আল-ফাসী (মৃত্যু ৮২৭ হিজরী/ ১৪২৪ খ্রিস্টাব্দ) প্রমুখ মনীষী। মক্কার এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির চিন্তাধারা ছিল উদার। এখানে সব ধরনের ফিকহ বা ইসলামী মতবাদ পড়ান হত। বাংলার মাটিতে অনুসৃত আ‘যম শাহের উদার নীতি ও খোলা মনের চিন্তাধারার জোয়ার সুদূর মক্কার বাঙালি মাদ্রাসার উপরও প্রভাব ফেলেছিল। সে যুগের বিশ্বায়নে বাংলা দেশও যে একটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছিল, মক্কায় বাঙালি মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা তারই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শুধু কি তাই! গিয়াস আল-দীন আ‘যম শাহের মৃত্যুর পর বাংলার রাজনৈতিক মানচিত্রে অভ্যুদয় হওয়া নতুন একটি দেশীয় রাজপরিবারের কর্তা রাজা গণেশের ছেলে যদু (জালাল আল-দীন মুহম্মদ শাহ, রাজত্বকাল ১৪১৪-৩৩ খ্রিস্টাব্দ) সুলতান রূপে মসনদে অসীন হন। বাংলার মাটির এই খাঁটি বাঙালি সন্তান নিজেও মক্কার বাঙালি মাদ্রাসার জন্য যথেষ্ট সহায় সম্পত্তি ওয়াক্বফ করে পাঠান, যা মাদ্রাসা দুটিকে আরো জাঁকজমকপূর্ণ করে তোলে। কোন কোন ঐতিহাসিক সূত্রে এমন ও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে তিনি স্বয়ং নিজেও মক্কা ও মদীনায় দুটি আলাদা মাদ্রাসা তৈরি করেছিলেন।
বাংলার উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন বহির্বিশ্বের ছাত্রদের আকর্ষণ করত, তেমনি বাংলার ছাত্ররাও খুরাসান, মধ্য এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া ও আরব বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় উচ্চতর শিক্ষার জন্য পাড়ি জমাত। উল্লেখ্য যে উপনিবেশ আমল এবং স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বাংলার মুসলিম ছাত্ররা ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণার জন্য উত্তর ভারতের কতগুলো বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গমনাগমন শুরু করে। এগুলোর অন্যতম ছিল অধুনালুপ্ত মাদ্রাসা রাহমানিয়া দিল্লী, দার আল-‘উলূম দেওবান্দ, মাযাহির আল-‘উলূম সাহারানপুর এবং নাদওয়াত আল-‘উলামা লক্ষ্ণৌ এবং সর্বোপরি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়। উত্তর ভারতের ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসাগুলো থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্ররা বাংলায় ফিরে এসে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদান করত। আবার অনেকে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ নিত। যুগ যুগ ধরে নিত্য-নতুন মাদ্রাসা গড়ে তোলার প্রক্রিয়াটি এখনো পুরোদস্তুর বাংলায় চালু আছে। ঐতিহ্যবাহী এসব মাদ্রাসায় যে নিয়ম পদ্ধতি ও পাঠ্যক্রম চালু ছিল, সাধারণভাবে তাকে আল–দারস্ আল–নিযামী বলা হত। তার কারণ এগার শতকে আব্বাসীয় খলীফাদের একজন বিখ্যাত মন্ত্রী নিযাম আল-মুলক প্রথমে বাগদাদে এবং পরে নিশাপুর ও খুরাসানে বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করেন, যা পরবর্তীকালে আল-মাদ্রাসা আল-নিযামিয়্যা নামে খ্যাতি লাভ করে। এক পর্যায়ে নিযামিয়্যা পাঠ্যক্রম ইসলামী বিশ্বে প্রায় সবগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়ে। আজ অবধি এগুলো দারস–ই–নিযামী নামে পরিচিত। অবশ্য দক্ষিণ এশিয়ার মাদ্রাসাগুলোতে ঔরঙ্গজেবের সময় থেকে এক বিশেষ পাঠ্যক্রম অনুসৃত হত, যার উদ্যোক্তা ও প্রবক্তা ছিলেন মোল্লা নিযাম আল-দীন। উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসাগুলোতে প্রচলিত পাঠ্যক্রম তাঁর নামেই নিযামী পাঠ্যক্রম নামে খ্যাত। এই পাঠ্যক্রমে হানাফি ফিক্হ ঘরানার উপরে বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করা হয়ে থাকে। বস্তুত আগের যুগে মাদ্রাসাগুলোতে শাস্ত্রীয় শিক্ষা-দীক্ষা ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হত। এক কথায়, সে যুগের মাদ্রাসাগুলো ঠিক একই ধরনের ভূমিকা পালন করত, যা বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো করে থাকে।
১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের পর উলামাদের এক বড় অংশ নিজেদেরকে ধর্মীয় শিক্ষাদীক্ষার একটি সংকীর্ণ গণ্ডির আওতায় গুটিয়ে ফেলে। এর মুখ্য কারণ ছিল ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তাদের সশস্ত্র আন্দোলনের শোচনীয় ব্যর্থতা। শিক্ষার অস্ত্রে বলীয়ান হয়ে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে মাঠে নামাকেও তারা জিহাদের একটি অন্যতম বিকল্প পন্থা হিসাবে দেখেছিল। কিন্তু বিশ শতকের এগিয়ে যাওয়া আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ রূপে অবহেলা করে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রাচীন পাঠ্যক্রমগুলোর মধ্যে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রেখে টিকে থাকা যে একরকম অসম্ভব, তা আলেম সমাজ অনুধাবন করতে শোচনীয়ভাবে ব্যার্থ হয়েছিল। এভাবে মুসলিম বিশ্বের মাদ্রাসা কার্যক্রম, যা একসময় পুরনো বিশ্বের এক বিরাট এলাকা জুড়ে শিক্ষার আলো জ্বালাতে পেরেছিল, ক্রমশই তার জৌলুস হারাতে শুরু করে। ফলে প্রাচীন শাস্ত্রীয় শিক্ষার কঙ্কালসার কাঠামোটিকে কোনমতে টিকিয়ে রাখার এক ক্ষীণ প্রচেষ্টা ছাড়া এগুলোর আর কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রইল না।
অবশ্য মাদ্রাসাগুলোর দুরবস্থার আরও বহুবিধ কারণ ছিল। মাদ্রাসাগুলোর মুখ্য অর্থনৈতিক উৎস ছিল রাজা-বাদশা ও সুলতানদের ওয়াক্বফ করা সম্পত্তি। ১৮২৮ সালের দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একটি নতুন আইন প্রবর্তন করে মাদ্রাসাগুলোর ওয়াক্বফকৃত সম্পত্তিগুলো বাজেয়াপ্ত করে ফেলে। এর পরের ধাক্কাটি আসে লর্ড হার্ডিঞ্জের সময়কালে ১৮৪৪ সালে। তিনি মাদ্রাসা থেকে পাশ করা কেবলমাত্র আরবী ও ফার্সী ভাষায় দক্ষতা অর্জনকারী শিক্ষিত যুবকদের সরকারি চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে বিধিনিষেধ আরোপ করে তাদের উপর্জনের পথ বন্ধ করে দেন। এর ফলে মাদ্রাসার স্নাতকোত্তর যুবকরা ইসলামী আইনবিশারদের ‘কাজী’ পদটিতে আবেদন করার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়ে পড়ে। উলেস্নখ্য যে নতুন প্রবর্তিত নিয়মে ‘কাজী’ পদে আবেদন করার জন্য ব্রিটিশ আইনের সম্যক জ্ঞান অর্জনের শর্তটিও জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। তথাপি ঔপনিবেশিক শক্তি স্থানীয় লোকাচার, দেশীয় আইন, সংস্কৃতি এমনকি মাদ্রাসার শিক্ষাব্যবস্থাকে পুরোপুরি উপড়ে ফেলতে সক্ষম হয়নি। বরং তাদের প্রশাসনিক স্বার্থে এক পর্যায়ে তারাও এক নতুন ধরনের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভব করতে শুরু করে। প্রায় ২০০ বছরের ঔপনিবেশিক শাসনামলের প্রথম পর্যায়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালে ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, আচার, সংস্কার, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ভারততত্ত্বের প্রতি সবচেয়ে বেশি যিনি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, তিনি হলেন ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭৩-৮৪ খ্রিস্টাব্দ)। ১৭৮১ সালে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পরে কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা নামে খ্যাতি লাভ করে সর্বত্র বিপুল সাড়া জাগায়।
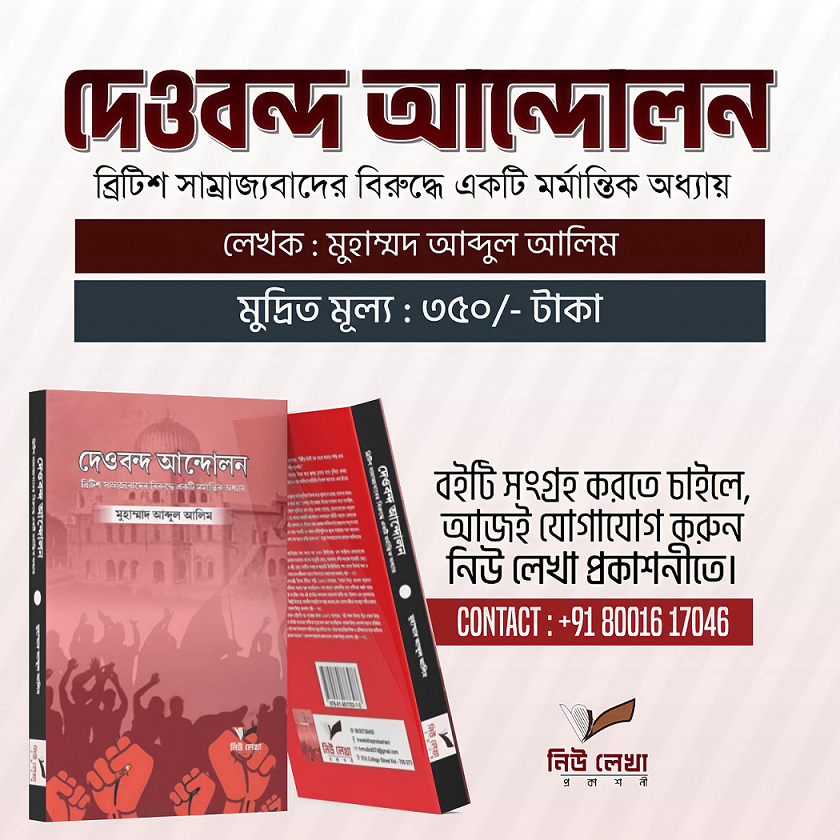
অতি সম্প্রতিকালে এই প্রতিষ্ঠানটি আলিয়া ইউনিভার্সিটি নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। জন্মলগ্ন থেকেই এই প্রতিষ্ঠানটিতে চিরাচরিত ধর্মীয় শাস্ত্রের পাঠ্যক্রম ছাড়াও নিত্য-নতুন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম সংযোজিত হতে থাকে। ফলে একদিকে যেমন এখানে আরবী ও ফার্সীর উপর জোর দেওয়া হয়, তেমনিভাবে এখানে পড়ানো হয় ইংরেজি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। আলিয়া মাদ্রাসা ঔপনিবেশিক প্রশাসনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে প্রথম দিকে মুসলিম সমাজের অনেকেই এর প্রতি বিরাগভাজন ছিলেন। এতদসত্ত্বেও ক্রমশ এর জনপ্রিয়তা বাড়তে শুরু করে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে আলিয়া মাদ্রাসাগুলো জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশে এর জনপ্রিয়তা আরও বেশি। এখানে সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিভিন্ন আকারের ও পরিধির আলিয়া মাদ্রাসা। এসব মাদ্রাসা দ্বারা বাংলার প্রান্তিক জনগণের এক বিরাট অংশের শিক্ষা ঘাটতিজনিত সমস্যাগুলো সম্পূর্ণভাবে দূর না হলেও কিছুটা নিবারণ অবশ্যই হয়েছে।81
সমাপনী বক্তব্য
সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে বাংলার স্বাধীন শাসক মহারাজা শশাঙ্কের আমল থেকেই অঞ্চলটিতে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত ও অন্যান্য বিভিন্ন দিক থেকে একটি সার্বভৌম সত্তার অঙ্কুরোদগম শুরু হয় এবং এই এলাকাকে ঘিরে জনগনের মধ্যে এক স্বাধীন চেতনা ও মনোভাব তৈরী হতে শুরু করে, যা পাল ও সেন আমলে আরও বিকাশ লাভ করে। ১২০৫ সালে বখতিয়ার খিলজীর গৌড় বিজয়ের পর বাংলা অঞ্চলটি একদিকে যেমন ইসলামী সভ্যতার সংস্পর্শে আসতে শুরু করে, অন্যদিকে অঞ্চলটির স্বাধীন সত্তা একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। উত্তর ভারতে দিল্লির মসনদে আসীন সুলতানদের বিভিন্ন সামরিক আগ্রাসনের মুখে বাংলার স্বাধীনতা মাঝে মধ্যে ক্ষুন্ন হলেও একটি সার্বভৌম, স্বচ্ছল ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে অঞ্চলটি সে সময়ে সার্বজনীন পরিচিতি পায়, যার প্রবাদপ্রতীম প্রাকৃতিক সম্পদ, কৃষিজাত ও অন্যান্য বহুবিধ পণ্যের ব্যাপক উৎপাদন ও রফতানি দেশটিকে বিশেষভাবে খ্যাত করে। প্রাথমিক মুসলিম লেখকদের বর্ণিত ‘বিলাদ-ই-বঙ্গ’ (বা ‘বঙ্গদেশ’) এর মধ্যে আধুনিক সার্বভৌম ও স্বাধীন দেশ, রাষ্ট্র ও জাতি বলতে আধুনিককালে যা বোঝায়, তার সবকিছুই নীহিত ছিল। দেশটির ভূভাগ ও মানচিত্র সম্পর্কে সাধারনভাবে একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল, যার মূল ভূখণ্ডটি ছিল মোটামুটিভাবে বর্ত্তমানকালের পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ কেন্দ্রিক, যদিও বিভিন্ন সুলতানদের আমলে এর সীমানার সম্প্রসারন ও সঙ্কোচন একটি নিত্যনৈমত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সীমানা রক্ষা ও বহিরাগ্রাসন মোকাবেলা করার জন্য দেশটিতে ধীরে ধীরে একটি নিয়মতান্ত্রিক সেনাবাহীনি গড়ে উঠে। প্রশাসন পরিচালনা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন সংস্থা ও ছিল, আর ছিল একটি শক্তিশালী বিচার বিভাগ। মুঘল সম্রাট আকবর কর্তৃক ১৫৭৫-৭৬ সালে বাংলা বিজয় পর্যন্ত অঞ্চলটি মোটামুটি স্বাধীন থাকে। মুঘল বিজয়ের পর দেশটি মুঘল সম্রাজ্যের একটি সুবা বা প্রদেশে পরিণত হয় এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের মুত্যু (১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত মুঘল বাদশাহরা রাজধানী দিল্লি থেকে তাঁদের সুবেদারদের (গভর্নরদের) মাধ্যমে এই প্রদেশটিকে শাসন করেন। এক শতাব্দিরও কিছু বেশী সময় দিল্লির মুঘল বাদশাহরা দৌড়দ- প্রতাপে বাংলা শাসন করলেও সম্রাট আওরঙ্গজেবের মুত্যুর পরে আঠার শতকের গোড়ার দিকে মুঘল সুবেদার নওয়াব মুর্শিদকুলি খানের আমলের শেষের দিকে বাংলায় দিল্লির মুঘল বাদশাহদের কর্তৃত্ব হ্রাস পেতে শুরু করে। পরবর্ত্তিকালে এই অঞ্চলের মুঘল সুবেদাররা সকলেই নওয়াব উপাধি গ্রহণ করেন এবং একরকম স্বাধীনভাবেই শাসন পরিচালনা করেন। মুঘল আমলের এই দূরবর্ত্তী সুবা-ই-বাঙ্গাল থেকে যে পরিমান রাজস্ব আদায় হত, সম্রাজ্যের অন্য কোন প্রদেশ থেকে এত পরিমান রাজস্ব আদায় করা কখনই সম্ভবপর হয়নি।
১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে ক্লাইভের বিজয়ের পর বাংলার শাসন ক্ষমতা ক্রমাগত ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির হাতে চলে যায়। ইংরেজ আমলে অঞ্চলটি ইংরেজদের উপনিবেশে পরিণত হওয়ার পর কার্যত বাংলা এবং পরবর্তীকালে বৃটিশ ইন্ডিয়ার রজধানী কলকাতা হয়ে দাঁড়ায় যা ১৯১২ পর্যন্ত বলবত থাকে। ফলে ভারতের প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের বলয় উপমহাদেশের উত্তর বা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল না হয়ে বাংলা কেন্দ্রিক হয়ে দাড়ায়। উপনিবেশ আমলের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বাংলার বহুবিধ বিবর্তন ঘটে।
প্রায় দু’শত বছরের ইংরেজ উপনিবেশ আমলের শুরু হয় বড় ধরণের একটি দুর্ভিক্ষ (ছিয়াত্তরের [১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের] মন্বন্তর) দিয়ে, এবং অবসানও ঘটে একটি ভয়াবহ খাদ্য সংকটের (পঞ্চাশের [১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের) মন্বন্তর) মধ্য দিয়ে। এই সুদীর্ঘ সময়ে ঘটে যাওয়া বহুবিধ দুর্ভিক্ষ গ্রাম বাংলার অর্থনীতিকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে ফেলে। ইতিহাসের বইয়ে যে সব উল্লেখযোগ্য দুর্ভিক্ষ স্থান পেয়েছে, শুধুমাত্র সেসব দুর্ভিক্ষের সংখ্যাই হল ২২টি। ছিয়াত্তরের ( ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের) মন্বন্তর নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সে সময়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা John Shore (পরবর্তীকালে গভর্নর জেনারেল ১৭৯৩-৯৮) যে মর্মস্পর্শী কবিতাটি লেখেন, তার প্রথম চরণগুলো হলঃ
Still fresh in memory’s eye the scene I view,
The shrivelled limbs, sunk eyes, and lifeless hue;
Still hear the mother’s shrieks and infant moans,
Cries of despair and agonising moans,
ইংরেজ উপনিবেশ আমলেই উনিশ শতক থেকে কলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেনীর মধ্যে ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ ভিত্তিক এক ধরণের জাতীয়তাবাদের উন্মেষ দেখা দেয়। এই উপমহাদেশ ভিত্তিক জাতীয়তাবোধ বাংলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠির মননে তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি, কারন গ্রাম বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারন বাঙালির আশা ও ভরসা অতীতের সেই সুজলা সুফলা স্বাধীন বাংলাদেশকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল, যার মধ্যে তাদের বাঙালিয়ানার স্বপ্ন নীহিত ছিল। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙ্গালি ভদ্রলোকদের স্বার্থে আঘাত হানলেও পূর্ব বাংলার হতদরিদ্র কৃষক শ্রেণী এর মধ্যে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে হয়তোবা পরবর্তিকালে পাকিস্থানের দাবি কিংবা আরো পরে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা তেমন একটা জোর পেত না। বলতে গেলে বাঙালি ভদ্রলোকদের বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার জের স্বরূপ ব্রিটিশ ভারতে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের রাজধানী ঢাকাতেই ১৯০৬ সালের শেষ দিকে মুসলিম লীগ গঠিত হয়। বাংলার মুসলিম নেতৃবর্গ ও সাধারন জনগণের একটা বড় অংশ পাকিস্থান আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তবে সামন্ত্রালভাবে অবিভক্ত স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন ও অনেকে দেখতে শুরু করেছিল, যার নেতৃত্বে ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু, কিরনশঙ্কর রায়, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশেম এর মত মুষ্টিমেয় কিছু অসাধারন দূরদর্শী নেতৃবর্গ। কিন্তু হিন্দু মহাসভার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও কংগ্রেসের অন্যান্য বড় বড় কিছু নেতাদের প্রবল বিরোধিতার মুখে অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা গড়ে তোলার পরিকল্পনাটি গোড়াতেই নষ্যাৎ হয়ে যায়।
পাকিস্তান দাবির সমর্থনে পূর্ব বাংলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠি যে উৎসাহ দেখিয়েছিল, সেখানে একটি বড় ধরনের আশা ও স্বপ্ন লুকিয়ে ছিল। পাকিস্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগন হিসেবে এই অঞ্চলটির বঞ্চিত সাধারন বাঙালিরা মনে করেছিল যে এই নতুন দেশটিতে তারা তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ পাবে। কিন্তু কার্যত বাংলা থেকে প্রায় দেড় বা দুই হাজার কিলোমিটারের দুরে উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন রাজধানীগুলোতে অবাঙালি রাষ্ট্রপ্রধানরা নিজেদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার বিষয়ে যতটা উৎসাহিত ছিলের, ততটাই উদাসীন ছিলেন বাংলার সার্বিক উন্নতি ও বাংলা ভাষার বিকাশের প্রতি। পাকিস্থানের সর্বাপেক্ষা জনবহুল প্রদেশ ‘পূর্ব পাকিস্থান’ থেকে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় নিসন্দেহে বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ সেখান থেকে বহু দূরে উত্তর বা উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত উপমহাদেশের উর্দু বা হিন্দি ভাষাভাষি বলয়ের প্রভাব ও কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে বাংলা ভাষা ও বাঙালিয়ানাকে তার নিজস্ব মর্যাদা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে।
টীকা ও গ্রন্থপঞ্জি
_________________________________________________________________________________________________________________
- [61] সি. ই. বসওয়ার্থ, দ্য ইসলামিক ডাইন্যাস্টিজ (এডিনবার্গ : এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৭), ১৯৪–৯৫।
- [62] মুর্শিদাবাদ জেলার সুতী থানার অন্তর্গত গোপালগঞ্জ গ্রামের পাশেও বারঘরিয়া নামের একটি পাড়া রয়েছে।
- [63] খুরাসান, মধ্য এশিয়া ইত্যাদি অঞ্চল থেকে আগত পাঠান, আফগান, উজবেক, তাজিক ইত্যাদি বিভিন্ন জাতির অধিবাসীরা বিভিন্ন সূত্রে বাংলায় এসে এদেশের স্থানীয় লোকজনের সাথে এক পর্যায়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। দূর-দূরান্ত থেকে আগত মুসলিমরা অনেক সময় স্থানীয় লোকজনের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করত। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত এমন কিছু পরিবার রয়ে গেছে, যারা তাদের প্রাচীন গোষ্ঠীগত ও পারিবারিক পদবিগুলো তাদের নামের সাথে ব্যবহার করে; যেমন: খান, পাঠান, ইউসুফযায়ী, লোহানী, আফ্রিদী, পান্নী ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ এখানে আমরা একটি মুসলিম পরিবারের পূর্বপুরুষ পরম্পরার কিয়দাংশ উদ্ধৃত করতে পারি, যারা মধ্যযুগের কোন এক সময়ে সুদূর খুরাসান থেকে এসে মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি থানার সুজনীপাড়া রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে পদ্মা তীরের একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম গোপালগঞ্জে এসে বসবাস করতে শুরু করেছিল। বংশ পরম্পরার তালিকাটি নিম্নরূপ: কুলসুম ইউসুফ > বিনত মুহম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক (এই বইয়ের লেখক) > ইবন মুহম্মদ মুজীবুর রহমান > ইবন ‘আব্দুল গনী > ইবন আইয়ুব হুসেন > ইবন হাজী শাহাদাত মণ্ডল > ইবন নিযাম আল-দীন মণ্ডল > ইবন ‘আবদ আল-কারীম মণ্ডল > ইবন হায়দার আলী খান। সম্ভবত ইংরেজ উপনিবেশ আমলের কোন এক পর্যায়ে পরিবারটি উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায় এবং নিজেদের আদি পারিবারিক উপাধি ‘খান’ রাজনৈতিক কারণে উহ্য রাখতে বাধ্য হয়। এই পরিবারের অন্য একটি শাখা বীরভূম জেলার রাজগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনের পার্শ্ববর্তী গ্রাম আম্ভুয়ায় বসবাস করতে শুরু করে। এই পাঠান পরিবারটির বংশ পরম্পরা নিম্নরূপ: কুলসুম বিবি (লেখকের দাদি) > বিনত মৌলানা ‘আবদ আল-রহীম > ইবন হাজী কালান্দার হুসেন > ইবন শিহাব আল-দীন খান > ইবন লা‘আল মুহম্মদ খান > ইবন শেরখান। আম্ভুয়ার এ পরিবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্য একটি শাখার একটি মহিলা সদস্যের পূর্বপুরুষ পরম্পরার তালিকাটি নিম্নরূপ: মাজেদা খাতুন (কুলসুম বিবির মা) > বিনত তাপলু খান > ইবন সামীর আল-দীন খান > ইবন যামীর আল-দীন খান > ইবন নাকবীর খান পাঠান। শেষোক্ত পাঠান পরিবার দুটি সম্ভবত উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে অর্থাৎ বর্তমানকালের খাইবার পোখতুনখাওয়াহ কিংবা আফগানিস্থানের নিনগারহার এলাকাগুলো থেকে এসেছিল এবং সে যুগের আহলে হাদীস নামক একটি ধর্মীয় আন্দোলন এবং একইসঙ্গে ব্রিটিশ উপনিবেশবিরোধী তৎপরতার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল।
- [64] রেজিস্টার অব সনদস,’ সিলেট ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরেট রেকর্ড রুম, নং ১৭:৭৫, ২৪৩, ১৮; নং ৯৪, ১৫৪, ১৫৮, ২৭৯, ১৯; নং ৩৩৪, ৬১৮, ৬১৯, ২০; নং ৮৫১, ৮৫৩, ৯৫৯; নং ৩৯৭, ৪০০।
- [65] য়াগিস্তান নামটি ফার্সী ও পুশতু ভাষা থেকে উদ্ভ‚ত, যার অর্থ বিদ্রোহীদের আবাসভুমি। শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ করলে দাঁড়ায় ‘ইয়াগী’ যার অর্থ বিদ্রোহী এবং ‘ইস্তান’ যার অর্থ স্থান। এই পরিভাষাটি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে সেই সব জায়গার জন্য ব্যবহৃত হত, যেখানে ব্রিটিশবিরোধী জিহাদী দলগুলো আস্তানা গেড়ে বসত। উনিশ শতকের শেষার্ধে এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে এই সব জিহাদী কেন্দ্রগুলো মূলত গড়ে উঠেছিল বর্তমান কালের খাইবার পোখতুনখাওয়াহ প্রদেশের মোহমান্দ এজেন্সী, বুনাইর, দীর, বাজোড়, সোয়াত, কোহিস্তান, হাযারা এবং আফগানিস্থানের কুনার প্রদেশের চামারকান্দ এলাকাগুলোতে। এই এলাকাগুলোর বেশিরভাগ নামেমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হলেও কার্যত এখানে পাঠান উপজাতিরা স্বাধীনভাবে বসবাস করত। এমনকি ব্রিটিশদের আগমনের আগেও এই এলাকাগুলো ঐতিহাসিকভাবে য়াগিস্তান-ই-কাদীম কিংবা রিয়াসাত-হায়ে-য়াগিস্তান নামে পরিচিত ছিল। দুর্গম পাহাড়ি এলাকার এসকল উপত্যকায় প্রবাহিত খরস্রোতা পাহাড়ি নদীগুলোর দুদিকের উর্বর জমি ব্রিটিশবিরোধী মুজাহিদীনের জন্য একদিকে যেমন নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছিল, অন্যদিকে এগুলোই তাদের জন্য নিয়মিত খাদ্য, পানি ও রসদ সরবরাহ করার একটি চমৎকার প্রাকৃতিক উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে এসকল এলাকা ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য বেশ উপযোগী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মোঘল শাসন দুর্বল হতে থাকলে ধীরে ধীরে শিখ রাজাদের প্রতাপ এ এলাকায় বাড়তে থাকে। মূলত এ এলাকায় শিখ শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে গিয়ে জিহাদ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। সৈয়দ আহমাদ বেরেলভীর নেতৃত্বে শিখদের বিরুদ্ধে মুজাহিদীনদের সামরিক তৎপরতা প্রথমদিকে কিছুটা সফল হলেও ১৮৩১ সালের ৬ই মে মুজাহিদীন বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এর অব্যবহিত পরেই শিখ শাসকদের পরাজিত করে ব্রিটিশরা এ এলাকায় তাদের ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ নিলে জিহাদ আন্দোলন ক্রমশ ব্রিটিশবিরোধী সামরিক তৎপরতায় রূপ নেয়।
- ১৮৩৯–৪২ সালে আফগানিস্তানের সাথে ব্রিটিশদের যুদ্ধের সময় মুজাহিদীনদের নেতা মাওলানা নাসির আল-দীন আফগানিস্তানের শাসক দোস্ত মুহম্মদকে যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য কাবুল ও গজনীতে বেশ কিছু সৈন্য পাঠান। পরবর্তীকালে মাওলানা বিলায়াত আলী (মৃত্যু: ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ) এবং তার পরে তাঁর ছোট ভাই মৌলানা ইনায়াত আলীর (মৃত্যু: ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ) নেতৃত্বে ব্রিটিশ উপনিবেশবিরোধী তৎপরতা ক্রমাগত বাড়তে থাকে, যার প্রভাব সুদূর বাংলা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। গ্রামবাংলার মুসলমানদের অনেকে গোপনে গোপনে সুদূর য়াগিস্তানের সিতানা, মুল্কা, আমবিলা ইত্যাদি বিভিন্ন কেন্দ্রে গিয়ে জিহাদী দীক্ষা নিত। অনেকে আবার নিজ নিজ এলাকা থেকে আর্থিক অনুদান পাঠাত এবং নৈতিক সমর্থন যোগাত। ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন জায়গার এসব ব্রিটিশ উপনিবেশবিরোধী জঙ্গি কর্মকাণ্ডের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের জন্য সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করা হত। উনিশ শতকের শেষার্ধে ব্রিটিশ উপনিবেশ সরকার য়াগিস্তানের বেশিরভাগ জিহাদী কেন্দ্র ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। এর পরেও নাজম আল-দীন হাড্ডামোল্লা (মৃত্যু: ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ) এবং সা’আদ-আল্লা খান মোল্লা মাস্তান (মৃত্যু: ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ) ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানীয় শক্তিশালী নেতৃবৃন্দের পরিচালনায় এসব ব্রিটিশ বিরোধী তৎপরতা চলতে থাকে। বিরোধী ঔপনিবেশিক (ব্রিটিশ) শক্তি ব্যঙ্গ করে তাঁদরকে ‘পাগল মোল্লা’ বা ‘ম্যাড মোল্লা’ ডাকনাম দিয়েছিল।
- ১৯০২ সালে মুজাহিদীনের নেতা আব্দুল করিম ইবন বিলায়েত আলী সোওয়াত উপত্যকায় বুনাইর এলাকার আসমাসত্ নামক জায়গাটিকে তাঁর কেন্দ্র হিসাবে বেছে নেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আফগানিস্তানের কুনার প্রদেশের চামারকান্দ নামক জায়গায় অন্য একটি জিহাদী সংগঠন গড়ে উঠে। এখান থেকে মুহম্মদ আলী কাসুরী (মৃত্যু: ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ), মাওলানা ‘আব্দুল করিম কান্নুজী (মৃত্যু: ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ) মৌলভী মুহম্মদ বাশীর (মৃত্যু: ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ), হাজী তারাঙ্গজায়ী (মৃত্যু: ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ), মৌলভী ফাদল-ইলাহী ওয়াজিরাবাদী (মৃত্যু: ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ) প্রমুখ নেতার পরিচালনায় বেশ কিছু উপনিবেশবিরোধী তৎপরতা চালানো হয়। উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে শাবকাদার, চাকদহ, মোহমান্দ এজেন্সী এবং আরও বেশ কয়েক জায়গায় ব্রিটিশ সৈন্যদলের সঙ্গে এদের বেশ কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধ হয়। এ সময়ে এ এলাকাগুলোতে আরও কয়েকটি ব্রিটিশবিরোধী সংগঠন গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে হিযব-আল্লাহ, জুনুদ-রাব্বানিয়্যা, হুকুমাত-ই-মুআক্কাতা-ই-হিন্দ, জাম’ইয়াত আল-আনসার ইত্যাদি দলগুলোর সঙ্গে মুজাহিদীনরা আঁতাত গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। এসব জঙ্গী তৎপরতার বিস্তার রোধের জন্য ব্রিটিশরা য়াগিস্তান এলাকাগুলোতে যাতায়াতের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে শুরু করে এবং এক পর্যায়ে সে এলাকায় প্রবেশের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ অনুমতিপত্র নেওয়ার শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়।
- ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হলে য়াগিস্তানের এলাকাগুলো স্বাভাবিকভাবে পাকিস্তানের অংশ হয়ে দাঁড়ায়। তবে এ এলাকার বিভিন্ন পাঠান উপজাতিদের (যেমন, আফ্রীদী) ‘জিরগা’ নামে পরিচিত নিজস্ব নিয়মকানুন স্বাধীনভাবে বলবৎ থাকে। ঔপনিবেশিক শাসন শেষ হওয়ার পর জিহাদী তৎপরতা স্তিমিত হয়ে গেলেও এ আন্দোলনটি সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়নি। এদের অনেকেই ১৯৪৮ সাল থেকে কাশ্মীর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ১৯৮০ সালে কাবুল তথা আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্শীবাদপুষ্ট কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে মুজাহিদীনরা সেই সরকারের পতন ঘটানোর লক্ষে আফগানদের সঙ্গে মিলে এক গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে এবং সে সরকারকে নির্মূল করে। পরবর্তীকালে তালেবানদের সরকার গঠন করার প্রচেষ্টায় তারা পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করে। আমেরিকা কর্তৃক তালেবানদের উৎখাতের পর আফগানিস্তানে মোল্লা উমারের নেতৃত্বে আফগান তালেবান ও উসামা-বিন-লাদেনের নেতৃত্বে আল কায়দা সংগঠনগুলো যখন আমেরিকা বিরোধী সংগ্রামে তৎপর হয়, সে সময়েও ঐতিহাসিক য়াগিস্তানের এলাকাগুলোকেই মূলত মুজাহিদীনরা তাদের গোপন আস্তানা হিসাবে বেছে নিয়েছিল।
- বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন: কর্নেল জন অ্যাডি, সিতানা: এ মাউন্টেন ক্যাম্পেন অন দ্য বর্ডারস অব আফগানিস্তান, লন্ডন, রিচার্ড বেন্টলি, ১৮৬৭; সৈয়দ মুহম্মদ আলী, মাখজান-ই-আহমদী, আগ্রা, ১৮৮১; মুইন-উদ-দীন আহমদ খান, সিলেকশনস ফ্রম বেঙ্গল গবর্নমেন্ট রেকর্ডস অন ওয়াহাবি ট্রায়ালস, ঢাকা, ১৯৬১; কিয়ামুদ্দীন আহমদ, দ্য ওয়াহাবি মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, নিউ দিল্লি, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৬; মাওলানা উবাইদ আল্লাহ সিন্ধী, সরগুজাশত-ই-কাবুল, ইসলামাবাদ, কওমী ইদারা বারাই তাহকীক ওয়া সাকাফাত, ১৯৮০; মৌলভী আবদ আল-করীম কান্নুজি (মৃত্যু ১৯২২), মৌলভী মুহম্মদ বশীর (মৃ. ১৯৩৪), হাজী তারাঙ্গাজায়ী (মৃ. ১৯৩৭) ও মৌলভী ফাজল ইলাহী ওয়াজিরাবাদী, কাওয়া’ইফ-ই-য়াগীস্তান, গুজরানওয়ালা, ১৯৮১; মুহম্মদ খাওয়াস খান, রুঈদাদ-ই-মুজাহিদীন-ই-হিন্দ, লাহোর, ১৯৮৩; মাওলানা মুহম্মদ আলী কাসূরী, মুশাহাদাত-ই-কাবুল ওয়া য়াগীস্তান, লাহোর, ইদারা মাআরিফ-ই-ইসলামী, ১৯৮৬; এম. আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলে হাদীস আন্দোলন, রাজশাহী, ১৯৯৬; মুহম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক, এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, ২য় সংস্করণ, প্রবন্ধ ‘য়াগিস্তান’।
- [66] নোট অন ইন্ডিয়ান হিস্টরি, মস্কো, তারিখবিহীন, ১৫২।
- [67] মুহম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক, এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, ২য় সংস্করণ, প্রবন্ধ ‘তিতুমীর’।
- [68] তাজ্জব ব্যাপার এই যে, যেসব ধর্মীয় মতবাদ বা আন্দোলনগুলো উপনিবেশ শক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বা জিহাদের কথা বলত না, ব্রিটিশ উপনিবেশ সরকার শুধুমাত্র তাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাত তা নয়; বরং তাদেরকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মদদ যোগাত। উপমহাদেশে এ ধরনের মনোভাব পোষণকারীদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা কিরামত আলী জৌনপুরী ও তাঁর প্রবর্তিত তা‘আইয়্যুনী চিন্তাধারার দল। আরেকটি দল ছিল মির্জ্জা গুলাম আহমাদ কাদিয়ান প্রবর্তিত আহমাদী বা কাদিয়ানী দল। তারা ও জিহাদের বিরোধিতা করত।
- [69] এইচ. বেভারলি, রিপোর্ট অব দি সেন্সাস অব বেঙ্গল, ১৮৭২, প্যারাগ্রাফ ৫২৫।
- [70] উদাহরণস্বরূপ দেখুন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পল্লীসমাজ, ঢাকা, সালমা বুক ডিপো, ১৯৯৯, ১৩১।
- [71] ফার্সী পাণ্ডুলিপি, খুদা বখশ ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরি, পাটনা, নং এইচ. এল. ৫৪৭৩, ফোলিও ২।
- [72] দ্য রাইজ অব ইসলাম, ৩০৮।
- [73] উদাহরণস্বরূপ লক্ষীসরাইয়ের একটি প্রাচীন জামে মসজিদের শিলালিপিতে (নং ৯, তারিখ ৬৯৭ হিজরী/ ১২৯৭ খ্রিস্টাব্দ) এ ধরনের জনসেবামূলক কর্মতৎপরতার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যা শিলালিপিতে বর্ণিত ফার্সী বাক্য যাদা খায়রুহু (তাঁর জনসেবা কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাক) মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।
- [74] মসজিদের ক্রমাগত বর্ধমান প্রভাব সম্পর্কে ‘আলা আল-হক মসজিদের একটি শিলালিপিতে (নং ১৯, তারিখ ৭৪৩ হিজরী/ ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দ) কিছুটা আভাস পাওয়া যায়, যেখানে লেখা আছে আ‘লা আসার আল-মসজিদ (আক্ষরিক অর্থে: যিনি মসজিদের মর্যাদা ও প্রভাব বৃদ্ধি করেছেন)।
- [75] ফার্সী পাণ্ডুলিপি, খুদা বখ্শ ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরি, পাটনা, নং এইচ. এল. ৩৭১৭, পৃষ্ঠা ১; আরও দেখুন জার্নাল এশিয়াটিক ২১৩ (অক্টোবর–ডিসেম্বর, ১৯২৮): ২৯১–৩৪৪; মূল সংস্কৃত বইটি টিকে না থাকলেও এর একাধিক আরবী ও ফার্সী অনুবাদের খোঁজ পাওয়া যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় লেখা প্রাচীন কালের বহু পান্ডুলিপি এক সময়ে কালের স্রোতে হারিয়ে গেছে, কিন্তু সেগুলো থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করা গ্রন্থগুলোর মাধ্যমে এখন পর্যন্ত কিছু কিছু টিকে রয়ে গেছে। এই অনুদিত গ্রন্থগুলোর বড় একটা অংশ আরবী ও ফার্সী ভাষায় রয়েছে।
- [76] দ্য রাইজ অব ইসলাম, ২২৯–৬৭।
- [77] মদদ-ই-মা‘আশ (জীবিকা নির্বাহ ভাতা) রীতি বা ঐতিহ্যটি এখন পর্যন্ত কোন না কোনভাবে আফগানিস্তান, ইরান ও মধ্য এশিয়ার কোন কোন জায়গায় টিকে রয়েছে।
- [78] এ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্যের জন্য দেখুন: ‘কানুনদানের নথি’, চিটাগাং ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরেট রেকর্ড রুম, বান্ডিল নং ৬২, কেস নং ৪০০৫, যেখানে ১৭৩৫ সালে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার সুন্দরপুর গ্রামে একটি খড়ের দোচালা মসজিদ স্থাপনের কথা উল্লেখ আছে। একই রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত অন্য একটি দলিল বান্ডিল নং ২৯, কেস নং ১৮০৮-এ সাতকানিয়া থানার লোহাগড়া গ্রামে একটি চৌচালা মসজিদ স্থাপনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আবার বান্ডিল নং ৫১, কেস নং ৩৩২৯-এ হাটহাজারী থানার ডাবরা গ্রামে একটি চৌচালা মসজিদ তৈরির জন্য জমি প্রদানের কথা উল্লেখ আছে। এ মসজিদগুলোর নকশা ও অন্যান্য বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন: ইটন, দ্য রাইজ অব ইসলাম, ২৪১–৪৩।
- [79] উদাহরণস্বরূপ দেখুন ঢাকার নয়াবাড়ি শিলালিপি ১০০৩ হিজরী/ ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দ।
- [80] ফার্সী ভাষায় শিক্ষালাভ করে হিন্দুদের (বিশেষ করে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির) অনেকেই মুসলমান শাসকের দরবারে আমলার চাকরি গ্রহণ করতেন। পরবর্তীকালে (বিশেষ করে মুঘল আমলের শেষের দিকে) কায়স্থদের অনেকে মুঘল আমলা হিসাবে চাকরি পাওয়ার আশায় উর্দু শিক্ষার বিষয়ে বিশেষভাবে তৎপর হয়।
- [81] শিক্ষা বিস্তারে মাদ্রাসার ভুমিকা ব্যাপক। বাংলায় নবজাগরণের আগে থেকেই এই ব্যবস্থা চলে আসছে। এমন কি আজও পশ্চিমবঙ্গের বহু প্রত্যন্ত অঞ্চলের হিন্দু-মুসলিম সর্বস্তরের ছাত্র-ছাত্রীরা মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করে।
‘নবজাগরণ’ এর টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।
‘নবজাগরণ’ এর ফেসবুক পেজে লাইক করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

 নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা
নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা
![প্রত্নলিপি, বাঙালি, বাঙালিয়ানা ও বাংলায় ইসলাম: কিছু জিজ্ঞাসা [পর্ব ১]](https://nobojagaran.com/wp-content/uploads/2023/07/Parthenon_30276156187-750x375.jpg)