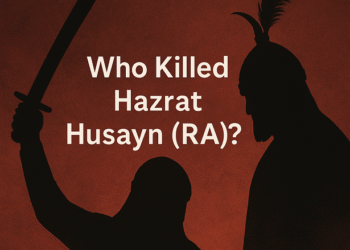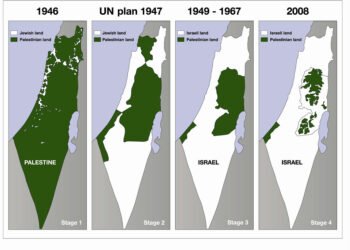বিবাহ কথাটির অভিধানিক অর্থ—পুরুষ ও নারীর স্বামী-স্ত্রী হিসাবে জীবনযাপন করার সামাজিক বিধি। ঠিক কোন সময় থেকে এই সামাজিক বিধির উদ্ভব হয়েছিল তার প্রামাণ্য নথি পাওয়া দুষ্কর। তবে পৃথিবীর সব দেশের, সব সমাজের, মুসলিম তথা সব সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে কোনাে না কোনাে সময় থেকে এই সামাজিক প্রথা চলে এসেছে যা আজও বর্তমান।

বিবাহের মধ্য দিয়ে পরিবার তথা সমাজের সৃষ্টি হয়, এমনই মন্তব্য করেছিলেন বিশিষ্ট নৃবিজ্ঞানী ডেভিড পােকোক। বিবাহ হল পুরুষের সঙ্গে মহিলার নির্দিষ্ট আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সমাজ স্বীকৃত মিলন। এই মিলনের ফলে যে সন্তান-সন্ততির জন্ম হয় সমাজ ও আইন তাদের স্বীকৃতি প্রদান করে। বিয়ের ইতিহাস বিশেষজ্ঞ ওয়েস্টার মার্ক তার ‘A short History of Human Marriage’ গ্রন্থে বিবাহের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে—
Marriage is a relation of one or more men women which is recognized by custom or law and involves certain rights and duties both in case of children born of it.
সুতরাং এক বা একাধিক পুরুষের সঙ্গে এক বা একাধিক মহিলার রীতি বা প্রথাসম্মত সম্পর্ক হল বিবাহ, যার সঙ্গে কিছু নির্দিষ্ট অধিকার ও কর্তব্য যুক্ত থাকে। সম্পর্কজাত সন্তান-সন্ততির ক্ষেত্রেও অধিকার ও কর্তব্যের বিষয়টি প্রসারিত। বিশিষ্ট নৃবিজ্ঞানী জি.পি. মাউকের মতে, বিবাহ হল,
‘…a universal institution that involves residential cohabitation, economic co-operation and formation of family.‘
অর্থাৎ সহাবস্থান, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং পরিবার গড়ে তােলার মধ্য দিয়ে সৃষ্ট হয় বিবাহ নামক সার্বজনীন সংস্থাটির। বিবাহের সার্বজনীনতা নিয়ে কখনও কখনও বিতর্ক দেখা যায়। কিয়দংশে সেই বিতর্কের সারবত্তা স্বীকার করে নিয়েও বলা যায়, সংস্থা হিসেবে বিভিন্ন সমাজে বিবাহের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বিবাহ সম্পর্কে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি বিবাহের মাধ্যমে পুরুষ ও নারী একটি নির্দিষ্ট বন্দোবস্ত-এর সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, যেখানে তারা অবস্থান করে শান্তিতে এবং সংযুক্ত হয় ভালােবাসা ও অনুকম্পার জগতে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ঘােষণা করেন,
“তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তােমাদের জন্য তােমাদের মধ্য হতেই তােমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তােমরা ওদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি তােমাদের (অন্তরের) মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও স্নেহ সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।” (কোরআন ৩০/২১)
ইসলাম বৈরাগ্যবাদকে বর্জন করেছে। আর উৎসাহিত করেছে বিবাহিত জীবনকে। ইসলাম কট্টরভাবে ব্যভিচার বিরােধী। এজন্য এর নিষেধাজ্ঞাও স্পষ্ট “অবৈধ যৌনসংসর্গের নিকটবর্তী হয়াে না, এ অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।” (কোরআন ১৭/৩২) ইসলাম মানুষের দুর্বলতার কথা জানে, জৈবিক প্রয়ােজনকে উপলব্ধি করে। নরনারীর যৌন-কামনার প্রাবল্যকেও সে স্বীকার করে। কিন্তু এ ব্যাপারটিকে সে সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রয়ােজনেই লাগাম ছাড়া হতে দেয় না। বরং এ উদ্দাম প্রবৃত্তিকে বিবাহবন্ধনে এনে উজ্জীবিত, ফলপ্রসূ ও অর্থপূর্ণ করতে চায়। বিবাহের বৃহত্তর তাৎপর্যের মধ্যে যৌন-সংযমও উল্লেখযােগ্য একটি। বিবাহ সম্পর্কে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গী কী, তা দেখে নিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে—
- ১) “আর তােমরা যদি আশংকা কর যে পিতৃহীনাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ করবে (স্বাধীনা) নারীদের মধ্যে, যাকে তােমাদের ভালাে লাগে, দুই, তিন অথবা চার। আর যদি আশংকা কর যে সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে অথবা তােমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে ক্রীতদাসী অথবা যুদ্ধ বন্দিনীকে)। এতেই তােমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা।” (কোরাআন ৪/৩)।
- ২) “নারীদের মধ্যে তােমাদের পিতৃপুরুষ যাদের বিবাহ করেছে তােমরা তাদের বিবাহ করাে না।” (কোরআন ৪/২২)।
- ৩) “তােমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা (বিবাহ করা) হয়েছে তােমাদের মাতা, কন্যা, ভগিনী, ফুফু, খালা, ভ্রাতুস্পুত্রী, ভাগিনেয়ী, দুগ্ধমাতা, দুগ্ধ-ভগিনী, শাশুড়ি ও তােমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সহবাস হয়েছে তার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা, যারা তােমার অভিভাবকত্বে আছে, তবে যদি তাদের (কন্যাদের মাতার সাথে সহবাস না হয়ে থাকে তবে তাতে তােমাদের (বৈধভাবে সংগত হওয়া) কোন দোষ নেই। এবং তােমাদের জন্য তােমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী ও দুই ভগিনীকে এক সঙ্গে বিবাহ (করাকে) নিষিদ্ধ করা হয়েছে।” (কোরআন ৪/২৩)।
- ৪) “এবং নারীর মধ্যে তােমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তােমাদের জন্য নিষিদ্ধ। তােমাদের জন্য এ আল্লাহর বিধান। উল্লিখিত নারীগণ ব্যতীত আর সকলকে অর্থের বিনিময়ে বিবাহ করা তােমাদের জন্য বৈধ করা হল, অবৈধ যৌন সংসর্গের জন্য নয়। বিবাহের সামর্থ্য না থাকলে তােমরা তােমাদের অধিকারভুক্ত বিশ্বাসী যুবতী বিবাহ করবে। আল্লাহ তােমাদের বিধাস সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। তােমরা একে অপরের সমান। সুতরাং তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে তাদের বিবাহ করবে এবং তারা ব্যভিচারিণী অথবা উপপতি গ্রহণকারিণী না হয়ে সচ্চরিত্র হলে তাদের মােহর ন্যায়সঙ্গতভাবে দেবে। …আর তােমরা ধৈর্য ধারণ কর (তবে তাতে) তােমাদের মঙ্গল। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।” (কোরআন ৪/২৫)
- ৫) “আজ তােমাদের জন্য সমস্ত ভালাে জিনিস বৈধ করা হল, যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের খাদ্যদ্রব্য তােমাদের জন্য বৈধ ও তােমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ এবং বিধাসী সচ্চরিত্রা নারীও তােমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে। তাদের সচ্চরিত্রা নারী তােমাদের জন্য বৈধ করা হল, যদি তােমরা বিবাহের জন্য তাদের মােহর প্রদান কর, প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা উপপত্নী গ্রহণের জন্য নয়।” (কোরআন ৫/৫)।
- ৬) “তােমাদের মধ্যে যাদের স্বামী-স্ত্রী নেই তাদের বিবাহ সম্পাদন কর। এবং তােমাদের দাসদাসীদের মধ্যে যারা সৎ, তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ তাে প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।” (কোরআন ২৪/৩২)
- ৭) “যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই আল্লাহ তাদের নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে। …তােমাদের দাসদাসীগণ সততা রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন-লালসায় তাদের ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করাে না।” (কোরআন ৪ ৩৩)
- ৮) “আর তােমরা নারীদের মােহর (পাত্র কর্তৃক প্রদেয় স্ত্রী-ধন) সন্তুষ্ট মনে দিয়ে দাও, পরে তারা খুশি মনে ওর (মােহরের) কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তােমরা তা স্বচ্ছন্দে ভােগ করবে।”
- পরিচ্ছন্ন সমাজ আর সুন্দর জীবনবােধ গড়ে তােলার জন্য হজরত মােহাম্মদের (সঃ) বাণীগ্রন্থ তথা হাদিসেও রয়েছে। বিবাহের কল্যাণকর প্রেরণা। বিবাহ যেহেতু এক-পাক্ষিক ব্যাপার নয়, অতএব সেখানে নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সম্মতি-অসম্মতি ইত্যাদির স্বাধীনতাও বর্তমান। যেমন—
- ১) হজরত মােহাম্মদ (সঃ) বলেন, পূর্বে বিবাহিত স্ত্রীলােককে তার সম্মতি ছাড়া বিবাহ করা চলবে না। সম্মতি ছাড়া কুমারীকেও বিবাহ করা যাবে না। সম্মতিটা হবে যদি সে নীরব থাকে। (অর্থাৎ এক্ষেত্রে তার নীরবতাকে সম্মতি বলে ধরা যাবে)।
- ২) হজরত মােহাম্মদ (সঃ) বলেন, একজন প্রাপ্তবয়স্কা বালিকাকে তার সম্মতি জিজ্ঞাসা করা হবে। যদি সে চুপচাপ থাকে, তাহলে এটাই তার সম্মতি। কিন্তু সে যদি তার অসম্মতি জ্ঞাপন করে, তবে তাকে বাধ্য করানাে যাবে না।
- ৩) হজরত মােহাম্মদ (সঃ) বলেন, তােমাদের মধ্যে কেউ যদি বিবাহ করার জন্য কোন পাত্রীর সন্ধান করে, আর যদি তাকে একবার দেখে নেওয়ার সুযােগ থাকে, তাে তাকে দেখতে দাও।
- ৪) হজরত আনাস (রাঃ) বলেন, হজরত মােহাম্মদ (সঃ) আবদুর রহমান বিন আউফ (রাঃ)-এর গায়ে একটা হলুদ রঙের ছােপ লক্ষ করলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এটা কী? তিনি উত্তর দিলেন, ৫ দিরহাম পরিমাণ সােনার বিনিময়ে একজন স্ত্রীলােককে বিবাহ করেছি। তিনি বললেন, আল্লাহ তােমার ভাল করুন। একটা ভােজ দাও—এমনকী একটি ছাগল জবেহ করেও।
- ৫) ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রাপ্তবয়স্কা এক কুমারী হজরত মােহাম্মদের (সঃ) কাছে এসে জানাল যে, তার বাবা তার বিবাহ দেয় যা তার অপছন্দ। হজরত মােহাম্মদ (সঃ) তাকে তার পছন্দ করার অধিকার ও ক্ষমতা দিলেন।
- ৬) হজরত আলী (রাঃ) বলেন, খয়বর বিজয়ের দিনে হজরত মােহাম্মদ (সঃ) মুতা বিবাহ (সাময়িক বিবাহ নিষিদ্ধ করেন।
- ৭) হজরত মেসওয়ার বিন মাকরামা (রাঃ) বলেন যে, স্বামীর মৃত্যুর পর কয়েক রাত ধরে সােবাইয়াতা আল আসলামিয়ার শিশু প্রসবের পর রক্তস্রাব দেখা দেয়। সে হজরত মােহাম্মদের (সঃ) কাছে এসে পুনর্বিবাহের অনুমতি প্রার্থনা করে। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। তখন সে পুনরায় বিবাহ করল।
- ৮) হজরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, হজরত মােহাম্মদ (সঃ) সিগারকে নিষেধ করলেন। সিগার সেই লােক, যে তার মেয়ের বিয়ে দিতে চায় এই শর্তে যে ঐ পক্ষও তার সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দেবে। আর তাদের মধ্যে কোন মােহর থাকবে না।
- ৯) হযরত আয়েশার (রাঃ) বর্ণনায় হজরত মােহাম্মদ (সঃ) বলেন, রক্ত-সম্পর্কের কারণে যা হারাম, তা পালন-পােষণের কারণেও হারাম।।
কোরআন ও হাদিসের এইসব বক্তব্য থেকে বুঝতে অসুবিধা নেই যে, নর-নারীর পবিত্র জীবনযাপনের জন্যই ইসলাম বিবাহের সুপারিশ করে। বিবাহ পবিত্র জীবনযাপনে মানুষকে সাহায্য করে। তাতে অবৈধ ও গােপন যৌনাচারের পথও বন্ধ হয়। এই দ্বিমাত্রিক মূল্যবােধের উপরেই রচিত হয় নর-নারীর বিবাহ পরিকল্পনা। আধুনিককালে পণ্ডিতগণের মতামতও প্রায় অনুরূপ। যেমন,ওয়েস্টার মার্ক মনে করেন, যেকোন স্বাভাবিক বিবাহের জরুরী উপাদান হল তিনটি। যেমন,
- ১. যৌনতৃপ্তি,
- ২. এর বাইরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার সম্পর্ক এবং
- ৩. সন্তান উৎপাদন।
বিবাহ যেহেতু মূল্যবােধ ভিত্তিক, এবং দ্বিপারিক ব্যাপার, সেইজন্য সেখানে যুক্তিসঙ্গত ভাবেই পুরুষের পাশাপাশি নারী অধিকারও সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত। ‘তােমাদের মধ্যে যারা একা (মানে স্বামী বা স্ত্রী হীন), তাদের বিবাহ সম্পাদন কর’,— কোরআন যখন একথা বলে (কোরআন ২৪ ৩২), তখন তার তাৎপর্য বহুদূর যায়। একা’র আরবি শব্দটি ‘আইয়ামা’। স্ত্রী হােক, কিংবা পুরুষ, একা থাকলে তার বিবাহ করা উচিত। নানা কারণে মানুষ একা হয়। যে অবিবাহিত, সে যেমন একা, তেমনি বিপত্নীক বা বিধবাও একা। বিবাহ বিচ্ছিন্ন বা তালাক-ঘটিত কারণেও কেউ একা হয়ে পড়ে। সবক্ষেত্রেই রয়েছে তার বিবাহ বা পুনর্বিবাহের অধিকার। এমনকী দারিদ্রও বিবাহের পথে বাধা বলে বিবেচ্য নয়। কেননা কোরাআনী অভয়াবাস এরকম ‘তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাব মুক্ত করে দেবেন। (কোরআন ২৪ ৩২)
বিবাহ : একটি চুক্তি
ইসলামে বিবাহ হল বিবাহিত দম্পতির মধ্যে একটি অঙ্গীকার ও চুক্তি। কোরআনে বলা হয়েছে, “তারা তােমাদের কাছ থেকে পাকাপােক্ত অঙ্গীকার নিয়েছে। অর্থাৎ পুরুষদের কাছ থেকে নারীরা গ্রহণ করে একটি পাকাপােক্ত অঙ্গীকার’ অর্থাৎ বিবাহ এটা এমন এক চুক্তি যার মাধ্যমে প্রত্যেক শরিক তার দায়বদ্ধতা (বাধ্যবাধকতা) মেনে চলবে। এই ‘পাকাপােক্ত অঙ্গীকার’এর গুরুত্ব আসলে নিরাপত্তা, ভালােবাসা ও অনুগ্রহের সমন্বয়মূলক বাস্তবায়নের মধ্যে নিহিত। এটা একটি ‘বিক্রয় চুক্তি’, লিজ অথবা এক ধরণের দাসত্বের মত একটি সাধারণ স্বত্ব বা মালিকানার ‘দলীল’ নয়। এটা এমন এক চুক্তি যাতে (চুক্তিবদ্ধ হতে) কোনাে ‘যাজক’-এর উপস্থিতি প্রয়ােজন হয় না, অথবা এরজন্য কোনাে বাহ্যিক অনুষ্ঠানের দরকার হয় না। ইসলাম বিবাহকে গণ্য করে এমন এক চুক্তি, যা স্থাপিত হয় একজন পুরুষ ও মহিলার মধ্যে পারস্পরিক সম্মতি ও বােঝাপােড়ার ওপর। এর বুনিয়াদী শর্ত হল উভয় পক্ষের সম্মতি।
পাত্র-পাত্রী নির্বাচন ও দিন ধার্য
মুসলমান সমাজে বিবাহের পূর্বে পাত্রীকে চাক্ষুস করার নিয়ম রয়েছে, তবে বিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্যে পাত্র-পাত্রীর পরস্পরকে দেখার কোনও সুযােগ নেই। বিবাহের পূর্বে অবশ্য পাত্রীকে দেখে পছন্দ করার ব্যাপারটি পাত্রের আত্মীয়দের ওপর ছেড়ে দেওয়া হলেও পাত্র-পাত্রী একে অপরকে দেখে পছন্দ করার অধিকারও স্বীকৃত। বিবাহের সম্মতির ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষ সমানভাবে স্বাধীন। পুরুষ যেমন তার পছন্দ মাফিক স্ত্রী পেতে পারে, তেমনি নারীও তার পছন্দের স্বামীর কথা বলতে পারে। নারীর সম্মতি ছাড়া কখনই বিবাহ হতে পারে না। তার এ অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না। নিলে তা হবে জবরদস্তিমূলক, জুলুম, অন্যায় ও বেআইনী।
বিয়ে করাকে ইসলাম ধর্মে খুব পুণ্যকর্ম বলে মনে করা হয়। হজরত মােহাম্মদ (সঃ) বলেছেন যখন কোন বান্দা বিবাহ করে, সে তার ধর্মের অর্ধেক ইমান পূর্ণ করে। বিবাহ যখন এতই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তখন হুট করে যার-তার সঙ্গে তাে আর বিবাহকাৰ্য্য সম্পন্ন করে দেওয়া চলে না। পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের মাপকাঠি কি? কোরাআন শরীফে আছে—সমস্ত মানবমণ্ডলী একজাতি। বিয়ের পাত্রী নির্বাচনের ব্যাপারে হজরত মােহাম্মদের (সঃ) সুস্পষ্ট নির্দেশ “বিবাহে চারটি বিষয় দেখতে হবে— ১। তার ঐশ্বর্য, ২। তার বংশের আভিজাত্য, ৩। তার সৌন্দর্য, ৪। তার ধর্মীয় পরায়নতা। অতএব যে নারী সাধ্বী এবং পুণ্যবতী তাকেই বিবাহ কর।”
পাত্র-পাত্রী পছন্দ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদির মীমাংসা হয়ে যাওয়ার পর বিবাহের দিন স্থিরীকৃত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইসলামি চান্দ্রমাসের কয়েকটি তারিখ ছাড়া (চান্দ্র মাসের ৩/৫/১৩/১৬/২১/২৪/২৫ তারিখকে অভিশপ্ত দিন হিসেবে গণ্য করা হয়) যে কোনও দিন বিবাহের ধার্য করা চলে। তবে সাধারণত বাংলা মাসের ভাদ্র ও পৌষ মাসে বিবাহের প্রচলন নেই। বিবাহের অনুষ্ঠান সাধারণত দিনের বেলায়ই হয়, যদিও রাত্রে হওয়ায় কোনও বাধা নেই।
বিবাহের শর্ত
ইসলাম ধর্মে বিবাহের গােপনীয়তা স্বীকৃত নয়। সামাজিক ঘােষণা ব্যতীত ইসলাম বিবাহকে বৈধ করেনি। ইসলামি শরীয়ত বিশেষজ্ঞগণ বিবাহ বৈধ হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত অবশ্য পালনীয় করেছেন
- ১) পাত্র-পাত্রীর পরস্পরের প্রতি প্রস্তাব ও সমর্থন অর্থাৎ ইজাব ও কবুল।
- ২) প্রস্তাব প্রেরণের সময় পাত্রের পক্ষ থেকে দেনমােহর সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। শাস্ত্র মতে, অন্তত আড়াই তােলা চাদির বা রূপার বাজার দরের অংকে দেনমােহর ধার্য করার নিয়ম। তবে এদেশে কার্যত তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ অংকে দেনমােহর ধার্য হয়ে থাকে।
- ৩) এই সময় দু’জন সাথীকে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে। সাক্ষী ব্যতীত ইসলামি বিধানে বিবাহ বৈধ নয়।
- ৪) পাত্র ও পাত্রীপথের সম্মতিতে উকিল নির্বাচন।
- ৫) অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য অভিভাবক নির্বাচন।
গায়ে হলুদ ও বিভিন্ন লােকাচার এবং বিবাহের গীত আপাতদৃষ্টিতে মুসলমান সমাজে বিবাহের অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত হলেও অজস্র লােকাচার, দেশাচার সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে দীর্ঘায়ত ও বর্ণময় করে রেখেছে। বর্তমান রচনায় পশ্চিমবঙ্গে এ ধরনের লােকাচারের একটা ধারণা দেওয়া হচ্ছে। বিবাহের কয়েকদিন আগে—সচরাচর ২/৩ দিন আগে পাত্র-পাত্রীর গায়ে হলুদ মাখান হয়। এ উপলক্ষে পাত্রপক্ষ থেকে পাত্রীর উদ্দেশ্যে গায়ে হলুদের সামগ্রী হিসাবে হলুদ, তেল, সাবান, তােয়ালে, কাপড়, মিষ্টি ও মাছ পাঠান হয়। পাত্রের দিক থেকে এই সব সামগ্রী না আসা পর্যন্ত পাত্রীর গায়ে হলুদ চড়ানাের নিয়ম নেই। যে কোনও মেয়েই পাত্রীর দেহে হলুদ মাখাতে পারে, হলুদ মাখানাের সময় পাত্রীকে এবং পক্ষান্তরে পাত্রকে ঘিরে স্ব স্ব আত্মীয়া-পড়শিরা গাইতে থাকে বিবাহের গান, এগুলিকে বলা হয় “গীত”। এই সব গীত নির্ভেজাল লােকগীতি—স্থানভেদে বিষয় ও ভাষাভেদ ঘটলেও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্র এগুলির প্রচলন রয়েছে। পাত্রপাত্রী এবং তাদের বাবা মা ভাই বােন ইত্যাদি আত্মীয়স্বজনকে কেন্দ্র করে রচিত এই গীতগুলি গ্রামীণ লােকদের নিজস্ব সৃষ্টি। এগুলির ভাষা মুসলিম গণজীবনের কথ্যভাষা। এখানে এ ধরনের কয়েকটি গীত উদ্ধার করা যেতে পারে। এগুলি উদাহরণস্বরূপ মাত্র। এ থেকে পূর্ণাঙ্গ তালিকার ধারণা গড়ে তােলা সম্ভব নয়—
“উঁচু ঘরের চৌরঙ্গি উসারা
আবিল কাঠের ক্যাওট যে
সেই না উসারায় বলে নয়ালাল
বিয়ার লিখন লিখে যে,
লিখিতে লিখিতে হাতের কলম।
গেল পড়ে যে।
কুথায় গেলে গাে ওগাে কামিনী
দাও না কলম গুড়ায়ে।
বাবাজি দিয়েছে সাত বাঁদি।
কেমনে কলম গুড়াইব।
তুমার হাতের কলম হলে গাে কামিনী
লিখন হবে মাের ভাল যে
বাঁদির হাতের কলম কামিনী
লিখন হবে মাের বাঁকা যে।
উঁচু ঘরের চৌরঙ্গি উসারা
আবিল কাঠের ক্যাওট যে।
সেই না উসারায় বলে নয়ালাল।
বিয়ার লিখন লিখে যে।।
লিখিতে লিখিতে নয়ালালের
গরমি মালুম হল যে।
কুথায় আছে গাে ওগাে কামিনী
দাও না পাংখা হিলায়ে।
বাবাজি দিয়েছে সাত বাঁদি।
কেমনে পাংখা হিলাইব।
তুমার হাতের পাংখা হলে গাে কামিনী
জু হবে মাের ঠাণ্ডা যে
বাঁদির হাতের পাংখা হলে গাে
জু যাবে মাের জ্বলে যে।।”
অর্থাৎ “উঁচু ঘরের প্রশস্ত উঠোন, তাতে আবলুশ কাঠের কপাট, সেই উঠোনে বসে নববর প্রেমলিপি লিখছে। হঠাৎ হাত থেকে লেখনী গেল পড়ে। তখন নববধূর উদ্দেশে বরের নিবেদন, কোথায় গেলে গাে প্রেয়সী, কলমটা কুড়িয়ে দিয়ে যাও। নববধূর জবাব, আমার বাবা সাত সাতজন বাঁদি পাঠিয়েছে না? আমি কী করে কলম কুড়ােই? নববরের সানুনয় কৈফিয়ৎ, বাঁদি যদি কলম কুড়িয়ে দেয় তবে লেখা যে আমার বাঁকা হয়ে যাবে, একমাত্র তুমিই যদি লেখনীখানা কুড়িয়ে দাও প্রেয়সী, তবেই না আমার লিপি হবে সুচারু।
পুনরায় লিখতে লিখতে নববরের গরম বােধ হতে লাগল। সুতরাং পুনরায় নিবেদন, কোথায় গেলে প্রিয়তমা, একটু পাখা নাড়বে এসাে। কামিনীর একই উদ্ধত উত্তর, আমার বাবা না পাঠিয়েছে সাত-সাতজন বাঁদি? পাখা নাড়বে তাে তারাই—আমি কেন? অনাহত নায়কের এবারও সানুনয় কৈফিয়ত, তা ঠিকই তবে বাঁদির হাতের ব্যজনে আমার অন্তর যে জ্বলে যাবে। কেবল তুমি যদি পাখা নেড়ে বাতাস কর তবেই না আমার অন্তর জুড়ােবে।”
হলুদ মাখানাের সময় একদল মেয়ে হলুদ মাখায় আর একদল মেয়ে গান গায়—
“ও বুনসীআলা, সােনার বুন্সীআলা
ঘুরিয়ে চাদর ফিরিয়ে দে রে বুন্সীআলা
টাকা হয়ত ফেরী দে রে বুন্সীআলা
সিকি হয়ত লিবনারে বুনসীআলা
বুনসীআলা সােনার বুনসীআলা
সাড়ী হয়ত ফেরী দেরে বুন্সীআলা
ছেড়া সাড়ী লিবনারে বুনসীআলা।”
(বুন্সী আলা—বংশীয়ালা—বাঁশীধারী) হলুদ মাখানাের পর হাতে (পাত্র/পাত্রী উভয়ের) দেওয়া হয় লােহার জাঁতি। গ্রাম্য ভাষায় জাঁতিকে বলা হয় সরতা। এই নিয়ে মেয়েরা গান গায়—
“বিদেশী ছেলে লাল, সােনার সরতা কৈ তােমার
গায়ে তােমার হলুদ মাখা, গলে তােমার সােনার হার।
বিদেশী ছেলে লাল, সােনার সরতা কৈ তােমার
গায়ে তােমার জরির জামা, সােনার সরতা কৈ তােমার
পায়ে তােমার নাগরা জুতাে, সােনার সরতা কৈ তােমার
হাতে তােমার মােহন বাঁশী সােনার সরতা কৈ তােমার।”
নববিবাহিতা পাত্র-পাত্রীর প্রথম পরিচয়ের গাঢ়তার পর সামান্য কারণে হয়ত স্ত্রীর উপর অভিমান করেছে পাত্র, তাকে মানাচ্ছে পাত্রী— এই বিষয়টা ‘গীত’ হিসেবে গাওয়া হয় এইভাবে
“মিছে অভিমানাে
তুমি দই খেয়েছ, ভাঁড় ফেলাও নাই কেন ।
মিছে অভিমানাে।
তুমি মাছ খেয়েছ, কঁটা ফেলাও নাই কেন,
মিছে অভিমানাে।
তুমি জুতাে পরেছ মােজা লাগাও নাই কেন,
মিছে অভিমানাে।
তুমি জামা পরেছ গেঞ্জি পর নাই কেন,
মিছে অভিমানাে।
তুমি ধুতি পরেছ অন্তার প্যান পার নাই কেন,
মিছে অভিমানাে।”
নতুন বর চলে যাওয়ার পর বউ রাত্রে একাকী ঘুমানাের পর মনে করেছে বর তার পাশে আছে। কিন্তু ঘুম ভেঙে দেখে বর নেই। কন্যার মন খারাপ। এই নিয়ে মেয়েরা গান গায়-
“শ্যাম যে আমার মনােশশী
ঘুমায়ে আছি সারা নিশি
উঠে দেখি শ্যাম আমার নাইহে
শ্যামকে নিয়ে গিয়েছে নিশিতে
আহা খুঁজে খুঁজে পেলাম তাকে
কাঠবিড়ালীর বাসাতে
আমার শ্যামকে নিয়ে গেল নিশিতে
মন খারাপ করে আর কি হবে।
শ্যাম আবার বাঁশী হাতে আসবে।”
এ ধরনের আরও অজস্র ‘গীত’ রয়েছে। দ্রুত নগরীকরণ এইসব গীতের প্রচলন খর্বিত করলেও আজও গ্রামবাংলার মুসলমান সমাজজীবনে এগুলির ভূমিকা সজীব। আগেই বলা হয়েছে, এইসব গীতের ভাষা গণজীবনের কথ্য ভাষা এবং সেইহেতু স্থানভেদে ভাষাভেদও স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকাশভঙ্গি ও বিষয়বস্তুতে সারল্য ও মানবিকতাবােধ গীতগুলির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।
হলুদ পাত্রকেও মাখতে হয় এবং তার নিয়মকানুনও পাত্রীরই অনুরূপ। কেবল পাত্রীপক্ষ থেকে এ বাবদে—কোনও উপহারসামগ্রী আসে না, এই যা পার্থক্য। হলুদ মাখানাের পর পাত্র-পাত্রীর মুখে ক্ষীর বা মিষ্টি খাওয়ানাে হয়। সম্মানার্থে টাকা-পয়সা দিতে হয়। হলুদ মাখানাের পূর্বে অবশ্য পাত্র ও পাত্রীকে তাদের আত্মীয়স্বজনেরা নিমন্ত্রণে আপ্যায়িত করতে থাকে। একে বলে ‘আইবুড়াে ভাত’। প্রতিক্ষেত্রে পাত্রপাত্রীকে একখানা করে বস্ত্র উপহার দেওয়ার নিয়ম। বিয়ের এক-দুদিন আগে সকালে হয় ‘আইবুড়াে ডুবুক’। এই অনুষ্ঠানে বর ও কনেকে আর একদফা হলুদ মাখান হয় এবং তারপর তাদের স্ব স্ব আত্মীয়স্বজন শােভাযাত্রা সহকারে পুকুরঘাটে স্নান করতে নিয়ে যায়। স্নানের শােভাযাত্রাও স্নানগীত’-এ মুখরিত হয়ে ওঠে।
বিবাহের গীত : ‘জীবন সঙ্গীত’
বিয়ের গীত, কেবলমাত্র আচার সঙ্গীত নয়, বরং বলা সঙ্গত ‘জীবন সঙ্গীত’। জীবনের এমন কোন দিক নেই যা নিয়ে বিয়ের গীত রচিত হয়নি। বহু বিচিত্র বিষয়বস্তুকে সে নিজ অঙ্গে সন্নিবিষ্ট করেছে, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক, আচার সঙ্গীত, শ্রমসঙ্গীত, মামলা মােকদ্দমা, যুদ্ধ বিগ্রহ, ইন্দিরা গান্ধী হত্যা, বাবরী মসজিদ ধ্বংস, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, আই সি ডি এস প্রকল্প, আধুনিক চিকিৎসা, টিকাকরণ—এমনভাবে গীতগুলিকে প্রায় চল্লিশ বিয়াল্লিশ রকম শ্রেণিবিভাগ করা যেতে পারে। এটি আঙ্গিকের দিক থেকেও তেমনি বৈচিত্র্যময়। ছােট্ট দু-লাইনের সাদা-সাপ্টা। গীত্ থেকে শুরু করে পনের কুড়ি পাতা জোড়া এক-একটি গীত-কাপ রয়েছে। কোনটি সােজা-সরল তাে কোনটি মনস্তাত্ত্বিক জটিল বুননে ঋদ্ধ, কোনটি আবার নাটকীয়তায় সমৃদ্ধ। মুসলিম বিয়ের ‘গীত’-এর বিশিষ্ট অনন্যতা এই যে, বিয়েকে উপলক্ষে করে গাওয়া হলেও, মূলত বিবাহের অনুপুঙ্খ খুঁটিনাটি ফুটিয়ে তুললেও, অনায়াস সাফল্যে সে টপকে গেছে ছাঁদনাতলার আনুষ্ঠানিকতার গণ্ডী, এবং ব্যাপ্ত হয়েছে। এক বহুধা বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই এ-ধরনের গীতের প্রচলন রয়েছে। কেবলমাত্র এই গীতগুলির পূর্ণাঙ্গ সংকলনেই বাংলার লােকগীতির একটা দিক উন্মােচিত হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া এইসব গানের ভাষা ও বিষয়বস্তু যে ভাষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে গবেষণার উপাদানরূপে পরিগণিত হবার যােগ্য তা বলা বাহুল্য।
ঊষা
বিবাহের পূর্বদিন পাত্র-পাত্রীর বাড়িতে এক বিশেষ অনুষ্ঠান হয় যার নাম ঊষা। এই অনুষ্ঠানে নিজ নিজ গৃহে পাত্র-পাত্রীকে বাড়ির আঙিনায় পিঁড়ে ও জলচৌকির ওপর বসান হয়। বর বা কনে আসন গ্রহণ করলে পর তাদের সামনে রাখা হয় জলপূর্ণ একটি মঙ্গল-কলস। এই কলস পূর্ণ করে আনে সাধারণত বর-কনের পরিহাসভাজন কোনও আত্মীয় বা আত্মীয়া (যথা— ভগ্নিপতি, বৌদি ইত্যাদি)। বরের বাড়িতে এই পূর্ণকুম্ভ তিন দিন রেখে দেওয়ার নিয়ম। বিয়ের পর তৃতীয় দিনে বরের বাড়িতে এই পূর্ণকুম্ভের জল বর-কনে উভয়ের মাথায় সিঞ্চন করা হয়। উষাের অনুষ্ঠানে পিঁড়ে বা জলচৌকিতে বসা বর ও কনের (নিজ নিজ বাড়িতে) মাথায় একটা চুমকি থেকে সরষের তেল ঢালতে থাকে নিজ নিজ মা বা মায়ের অবর্তমানে অন্য কোনও নিকট আত্মীয়া। এই সময়ও গীত গাওয়া হয়। উষাের অনুষ্ঠানেও পাত্র-পাত্রীর আত্মীয়রা ক্ষীর খাওয়ায়। প্রত্যেককে নিজের হাতে পাত্রপাত্রীর মুখে ক্ষীর তুলে দিতে হয় এবং সেই সঙ্গে দিতে হয় সম্মানস্বরূপ কিছু টাকা পয়সা। পাত্র-পাত্রীকে ক্ষীর খাওয়ানাে হয়ে গেলে একটা জলভর্তি থালায় কয়েকটি কড়ি ফেলে দিয়ে তাদের সামনে ধরা হয় এবং থালার জল থেকে ডুবন্ত কড়িগুলােকে মুঠো করে তুলতে বলা হয়। একটি মুঠোয় যে কয়েকটি কড়ি ওঠে তার সংখ্যার ভিত্তিতে বর-কনের দাম্পত্য সৌভাগ্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।
বরাগমন ও বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা
বিয়ের দিন সকালে পাত্র সাজসজ্জা করে বরযাত্রীসহ পাত্রীর গৃহের উদ্দেশে রওনা হয়। গ্রামাঞ্চলে বর-কনে পূর্বে বেশিরভাগ জায়গায় পাল্কিতে বা ঘােড়াগাড়িতে যাতায়াত করত, তবে এখন যাতায়াতের জন্য ট্যাক্সি মারুতি বা অন্যান্য যানবাহন ব্যবহৃত হয়।
বিবাহের অনুষ্ঠান খুবই সরল ও সংক্ষিপ্ত। বিবাহের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জনৈক মৌলবি সাহেব বা কাজি সাহেব। মজলিস থেকে দুপরে একজন করে দু’জনের এক প্রতিনিধিদল মনােনীত হন, এঁদের নেতাকে বলে উকিল আর অপর জনকে বলা হয় সাক্ষী, সেই সঙ্গে সর্বজনসমক্ষে উভয়পথের সম্মতিতে বিবাহের অন্যতম অপরিহার্য এক শর্ত স্থিরীকৃত হয়, তা হল দেনমােহরের অঙ্ক। দেনমােহর বিবাহের অব্যবহিত পরে বা অন্তত দাম্পত্যজীবনের পরিসরের মধ্যে স্বামীর পথে স্ত্রীকে মিটিয়ে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।
কন্যার অভিভাবকের আহ্বানে উল্লিখিত প্রতিনিধিদ্বয় অর্থাৎ উকিল ও সাথী অন্দরে কন্যার কাছে উপস্থিত হয়ে বরের পরিচয় দিয়ে নির্ধারিত দেনমােহরের শর্তে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাব পেশ করেন উকিল সাহেব স্বয়ং, সাক্ষীর গােচরে কন্যা বার বার তিনবার বিবাহের প্রস্তাবে তার সম্মতি জ্ঞাপন করলে পর প্রতিনিধিদ্বয় মজলিসে ফিরে এসে সর্বজনসমক্ষে কন্যার সম্মতিদানের কথা ঘােষণা করেন। এরপর মৌলবি সাহেব কনের পরিচয় ও দেনমােহরের অংক উল্লেখ করে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করেন। বর তিনবার সুস্পষ্টভাবে তার সম্মতিজ্ঞাপন করলে পর বিবাহ সিদ্ধ হয়ে যায়। এরপর মৌলবি বা কাজি সাহেব খােৱা (কোরআনের কিছু অংশ) পাঠ করেন। এবং শেষে দোওয়া (প্রার্থনা) চাওয়া হয়।
বড়জোর দশ থেকে পনেরাে মিনিটের অনুষ্ঠান। মুসলমান সমাজে বিবাহের মূলভিত্তি পাত্র ও পাত্রীর পারস্পরিক সম্মতি। মুসলমান বিবাহে কন্যা সম্প্রদানের কোনও স্থান নেই বড়জোর পাত্রী নাবালিকা হলে তার অভিভাবক তার হয়ে বিবাহ-প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপন করতে পারে মাত্র। অনুষ্ঠান পরিচালনায় মৌলবির ভূমিকা থাকলেও তা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, অর্থাৎ একা মৌলবিই বিবাহকে সুসিদ্ধ করে তুলতে পারেন না।
সমর্পণ পর্ব
বিবাহের মূল অনুষ্ঠানের কথা পুনরুল্লেখ নিস্প্রয়ােজন। বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর বরকে মজলিস থেকে পাত্রীর অন্দরমহলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কনের পাশে বরকে বসিয়ে কনের পিতা বা অভিভাবক বরের হাতে আংটি দিয়ে কন্যা সমর্পণের প্রতীকস্বরূপ কনের হাতকে বরের হাতে তুলে দেন। এই সময় আরও দু-একটি অনুষ্ঠান হয়। যেমন, কোনও কোনও ক্ষেত্রে বরকে এক স দুধ বা সরবত দিয়ে এক চুমুক পান করতে বলা হয়। বর তা এক চুমুক পান করার পর কনে সেই স থেকে এক চুমুক দুধ বা সরবত পান করে। কিংবা কনের সামনে একটি আয়না ধারণ করা হয় এবং বরকে সেই আয়নাতে প্রতিবিম্বিত কনের মুখ দেখতে দেওয়া হয়। এইভাবেই বিয়ের মজলিসে বরের কনেকে দেখার সুযােগ ঘটে।
একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়ােজন। বিয়ের দিন কনের মাকে উদয়াস্ত রােজা রাখতে হয় অর্থাৎ উপবাস পালন করতে হয়। বর-কনে বা আর কাউকে অবশ্য এভাবে উপবাস করতে হয় না।
চৌথি
বিয়ের পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিবসে বরের বাড়িতে যে অনুষ্ঠান হয় তার নাম চৌথি। এই দিন কনের বাড়ি থেকে স্নানের তেল, সাবান, তােয়ালে ইত্যাদি ও এক ঘটি দুধসহ মিষ্টি উপহার আসে। চৌথির দিন দুপুরে বর-কনেকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে বরের অভিভাবক বা অভিভাবিকা উষাের দিনের পূর্ণকুম্ভ থেকে জল নিয়ে তাদের মাথায় বর্ষণ করে। চৌথির দিন নানান জায়গায় নানা লােকাচার পালিত হয়, এইসব আচার অনুষ্ঠানের কেন্দ্রে থাকে বর আর কনে। এই দিন বরের বাড়িতে প্রীতিভােজেরও আয়ােজন হয়। চৌথির অপরাহে কনে বরের সঙ্গে তার পিত্রালয়ে ফিরে যায়। চৌথিই বিবাহের শেষ অনুষ্ঠান।
তাহলে দেখা যায় মুসলমান সমাজে বিবাহের অনুষ্ঠানের সমগ্র ব্যাপ্তি সাত থেকে এগারাে দিন। পাত্র-পাত্রীর গাত্র হরিদ্রায় এই অনুষ্ঠানের সূচনা, চৌথিতে সমাপ্তি। শরিয়তি অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী যতটুকু অনুষ্ঠান পালনীয় তা সব জায়গাতেই বাধ্যতামূলক এবং অভিন্ন। কিন্তু অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলি স্থানভেদ ভিন্নরূপ। সমাজজীবনে বিবাহের অনুষ্ঠান সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই অন্যতম প্রধান অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্প্রদায় বিশেষের সংস্কৃতির বিশেষ রূপটি অভ্রান্তভাবে ফুটে ওঠে।
ঐক্যের সুর
বিবাহে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রসঙ্গটিও বলা দরকার। আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সমন্বয়ে সৃষ্ট বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বিবাহের লৌকিক আচারের অনেক উদাহরণ আছে—যা হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় গণ্ডী পেরিয়ে বিশেষ এক সামাজিক রীতিতে উভয় সম্প্রদায়কে ঘনিষ্ঠ করে তুলছে। প্রথমত বিয়ের পূর্বে প্রাথমিক যােগাযােগের ক্ষেত্রে ঘটকের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজেই ঘটককে বিয়ের মাধ্যম হিসেবে কাজে লাগানাে হয়। বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর ঘটকের পাওনা মেটানাের ব্যাপারটা উভয় সমাজেই রয়েছে। ঘটকের পাওনার কথা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত উভয় সমাজেই বর-কনের গায়ে হলুদ মাখানাে ও বিয়ের গীত গাওয়ার রীতি রয়েছে। তৃতীয়ত বিয়ের আগে আইবুড়াে ভাত অনুষ্ঠানটি হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও প্রচলিত রয়েছে। এই অনুষ্ঠানে আত্মীয়দের পক্ষ হতে বর বা কনেকে আমন্ত্রণ দিয়ে খাওয়ানাে হয়। চতুর্থত দই মিষ্টি মাছ বিয়ের এই তত্ত্বগুলি উভয় সমাজের কাছে এখনও মঙ্গলের প্রতীক বলে মনে করা হয়। তাই এগুলাে না দিলে কথা হয়। বিয়েতে যে মাছ পাঠানাে হয় সে মাছের মুখে পানের খিলি দেওয়ার রীতি হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজের মধ্যে লক্ষ করা যায়। পঞ্চমত বিয়ে বাড়ির সর্বত্র যখন ভােজনপর্বে জমজমাট তখন নিভৃতে উপবাস চলে দু-একজনের। হিন্দু বরের মা অথবা মাতৃস্থানীয় যে কেউ এবং কনের বাড়িতে কনের মা ও বাবা অথবা ঐরূপ গুরুজনকে উপােস করে থাকতে হয়। মুসলমান-কনের মা বা মাতৃস্থানীয়া মহিলাকে ‘রােজা’ রাখতে হয়। বর ও কনের মঙ্গলের জন্য এ-ধরণের উপবাস লােকাচারের পর্যায়েই পড়ে। ষষ্ঠত মুসলমান-বিবাহে বর-কনেকে পান-চিনি বা পান সরবৎ খাওয়ানাের প্রথা হিন্দু-বিবাহে পান-মিষ্টির কথা স্মরণ করায়। সপ্তমত হলুদ মাখানাের সময়েও আমরা ঐক্যের সুর শুনতে পাই। গ্রামের একান্ত নিভৃতে ঢােলক বাজিয়ে পর্দানশীন মুসলিম রমণীর মুখে যখন কৃষ্ণ নামােচ্চারণ শুনি তখন অবাক না হয়ে পারা যায় না। এইসব গানগুলিতে কৃষ্ণ এবং জামাই অবিচ্ছেদ্য ও একাকার হয়ে গেছে। যেমন—
“পায়ের ওপর পা দিয়ে।
কদমে হেলান দিয়ে
বাজাও বাঁশী নিরালায় বসে, হে শ্যাম শুনে যাও
বারে বারে ডাকো তুমি
কি শুনিতে যাবাে আমি
পরের ঘরে বসতি আমার, হে শ্যাম শুনে যাও।”
কিংবা যমুনার ধারে জল আনতে যাওয়ার গান—
“রে পিতােলের কলােসি
তােরে নােয়ে জল আনিতে যাই
কোলসিরে তাের পায়ে পড়ি
নিয়ে চলাে বন্ধুর বাড়ি
বন্ধু আমার বাঁশরী বাজায়।”
এইসব গান থেকেই অনুমান করা যায়, কেবলমাত্র বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবিগণই ধর্মীয় বেড়াজাল ছিন্ন করে মহামিলনের গান শুনিয়ছিলেন, গ্রামে-গঞ্জের নিরক্ষর সাধারণ মানুষের মুখেও তা প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।
কোনও কোনও গানে শ্যামদেবের কথা খুব স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে। কয়েকটি গানের ছন্দ এবং অর্থেও বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। নীল যমুনার ধারে শ্যামদেব বাঁশী বাজাচ্ছে, / সেই মরলীধ্বনি প’শেছে দয়িতার কানে। /ওকে এবার অভিসারে যেতে হবে। রাধা বলে,
“নীল যুমনা না ভার বেদনা
এমন মিলনের বাঁশী কে বা বাজালে
শ্যাম বাজালে না নাগর বাজালে।
এমন মিলনের ডাক কে বা ডাকিলে—”
ইসলাম ধর্মে গান বাজনা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এ গান কবে কার কণ্ঠে প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল তা আজ সমীক্ষার বিষয়। তবে মুসলমানী গানে যথেষ্ট বৈষ্ণব প্রভাব পড়েছিল এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। অসাম্প্রদায়িকতার স্বর্ণময় মধ্যযুগে যে সব গােষ্ঠীচেতনাহীন কবিরা কাব্য রচনা করেছিলেন এ হয়তাে তাদেরই উদার আকাশ হতে উড়ে আসা। অষ্টমত বিবাহের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পরে বর ও কনেকে পাশাপাশি বসিয়ে কনের পিতা বা পিতৃস্থানীয় ব্যক্তি মেয়ের হাতটিকে জামাইয়ের হাতে ঠেকিয়ে সজল-নয়নে যে ভাষায় সঁপে দেন সে ভাষা বাঙালি কন্যার পিতার একান্ত অন্তরের ভাষা, সে ভাষা। নিঃসন্দেহে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে।
বিধবা বিবাহ ও ইসলাম
ইসলাম বিধবাদের বিবাহের অধিকার দিয়েছে। এজন্য এ নিয়ে আইন প্রণয়নেরও প্রয়ােজন পড়েনি। ইসলাম একেবারে শুরুতেই বিধবার পুনর্বিবাহের আইনী অধিকার দিয়ে রেখেছে,
“তােমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে। যখন তারা ইদ্দত (অর্থাৎ ৪ মাস ১০ দিন) পূর্ণ করবে, তখন তারা নিজেদের জন্য কোন বিধিমত কাজ (বিবাহ) করলে তাতে তােমাদের কোন পাপ হবে না।” (কোরআন ২ ২৩৪)
বিধবাদের অসহায়ত্বের সুযােগ নিয়ে পুরুষ সমাজ যাতে তাদের উক্ত না করে, তার জন্য কোরাআন বড় সতর্ক। বিধবাদের নিয়ে পুরুষেরা আলােচনা করতেই পারে। তাদের বিয়ে করার ইচ্ছাও থাকতে পারে। সে ইচ্ছা প্রকাশ করা বা গােপন রাখা সবকিছুই স্বাভাবিক। তাতে কারও কোন দোষ নেই। কিন্তু কোরআন এই বলে মানুষকে সাবধান করে যে, বিধিমত কথাবার্তা ছাড়া গােপনে তাদের নিকট কোন অঙ্গীকার করাে না। (কোরআন ২ ২৩৫) অর্থাৎ কোন কথাবার্তা বলতে হলে তা বলতে হবে প্রচলিত ও পরিচিত পদ্ধতিতে। কেননা, গােপন চুক্তি বা কথাবার্তায় বিধবারা প্রতারিত হতে পারে। কোরাআন আরও সতর্ক করে এই বলে যে, নির্দিষ্ট সময় (ইদ্দতকাল) পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহকার্য সম্পন্ন করার সংকল্প করাে না। (কোরআন ২ ২৩৫) ঐ সময়কাল এত গুরুত্ব কেন? কারণ সহজবােধ্য। গর্ভাবস্থায় বিধবা হলে সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে হয়। যে কোন দিক দিয়েই এটি রীতি বা নীতিসম্মত। অন্য কারও মৃত্যু হলে সাধারণভাবে স্ত্রীলােককে তিন দিনের বেশি শােক পালন করার প্রয়ােজন হয় না। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে অন্তত ১৩০ দিন সাজগােজ থেকে বিরত থাকতে হয়। বাইরের লােকসমাজ থেকেও সরে থাকতে হয়। তার এইইদ্দত পালনের মধ্যে তার নিজেরও একটা স্বার্থ থাকে। কেননা, ঐ সময়ে তার গর্ভে যদি সন্তান থাকে, তাহলে স্বভাবতই সেটি তার সদ্যমৃত স্বামীর ঔরসজাত বলেই সম্মানিত হয়। সমাজ তার উপর কোন অপবাদ আরােপ করতে পারে না। ঐ সময়টুকু অতিবাহিত না করে কেউ যদি বিবাহ করে, তাহলে নতুন স্বামীটি গর্ভস্থ সন্তান নিয়ে গণ্ডগােলও পাকাতে পারে। পুনর্বিবাহের শুরুতেই দাম্পত্য জীবন বিষময় হয়ে উঠতে পারে।
সবদিক থেকে চিন্তা করে হজরত মােহাম্মদ (সঃ) বলেছিলেন, “ইদ্দতকাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিজের বাড়িতেই (যেখানে বা যে বাড়িতে স্বামীর মৃত্যু হয়) অবস্থান কর। ইদ্দতকাল পর্যন্ত মৃত স্বামীর সঙ্গে বিধবা স্ত্রীর সম্পর্ক থাকে। এইজন্য মৃত স্বামীর অন্তিম ওযু, গােসল ইত্যাদি সে সম্পন্ন করতে পারে। আর এইজন্যই ইদ্দতকালের মধ্যে সে অন্য পুরুষকে বিবাহ করতে পারে না। অপরদিকে মৃতা স্ত্রীর ঐসব কৃত্যাদি করার অধিকার স্বামীর থাকে না। কেননা স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। ইচ্ছে করলে পরদিনই সে বিবাহ করতে পারে।” (সফিয়া ইকবাল, ওমেন অ্যাণ্ড ইসলামিক ল, পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃ. ১৪৯) মৃত ব্যক্তিকে কোথায় কবরস্থ করা হবে, বিধবা স্ত্রী তাও ঠিক করে দিতে পারে।
বিধবা হওয়ার পরও তার পূর্ণ স্বাধীনতা বহাল থাকে। স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়ে সে এর পরিচালনভার গ্রহণ করতে পারে। সাহায্য নিতে পারে প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের, কিংবা পিতৃ-পরিবারের। সেটা তার ইচ্ছাধীন। বাধ্যবাধকতার কোন প্রণ নেই। তেমনি, তার বর্তমান বা ভবিষ্যৎও তারই করতলে। সে বিধবা হয়ে থাকবে, নাকি পুনর্বিবাহিতা হবে, সে-ই তা স্থির করবে। কারও অভিভাবকত্ব গ্রহণে সে বাধ্য নয়। কারও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাে নয়ই।
বৈধব্যকে যদি একটি অসহায় অবস্থা হিসেবে গণ্য করা হয়, তাহলে তার জন্যও রয়েছে কোরআনী রক্ষাকবচ। যেমন, “এবং তােমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তারা তাদের স্ত্রীদের জন্য এই ‘অসিয়ত’ করবে যে, তাদের যেন এক বছর পর্যন্ত ভরণ-পােষণ দেওয়া হয় এবং গৃহ থেকে বার করে দেওয়া না হয়, কিন্তু যদি (স্বেচ্ছায়) তারা বেরিয়ে যায় তবে নিয়মমত নিজেদের জন্য যা করবে তাতে তােমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।” (কোরআন ২ ২৪০)।
বিবাহ-বিচ্ছেদ ও ইসলাম
বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত কঠোর। হজরত মােহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, “পৃথিবীতে আল্লাহ মানুষের জন্য যা কিছু বৈধ ঘােষণা করেছেন সেই সকল ঘােষণার মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা অপ্রিয় ঘােষণা হল তালাক।”
ইসলাম বিবাহবিচ্ছেদ সেই ক্ষেত্রেই মেনে নিয়েছে যেখানে বিচ্ছেদ ব্যতীত অন্য কোনও পথ খােলা থাকে না। যে ব্যক্তি একটার পর একটা বিবাহ করে এবং একটার পর একটা বিবাহ বিচ্ছেদ করে ইসলাম সেই ব্যক্তিকে আল্লাহর শত্রু বলে মনে করে। হজরত মােহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, “একমাত্র প্রামাণ্য ব্যভিচার ও ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ ব্যতীত অন্য কোনও কারণে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া যাবে না।”
হজরত মােহাম্মদ আরও বলেছেন “বিবাহ কর কিন্তু তালাক দিও না, কারণ যখন তালাক ঘটে তখন আল্লাহর আরশ (সিংহাসন) কম্পিত হয়।”
ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ-বিচ্ছেদ এত ঘৃণা হওয়া সত্ত্বেও তা নিষিদ্ধ ঘােষিত হয়নি। এইখানেই ইসলামের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে। ইসলাম একটি সম্পূর্ণ জীবনবিধান প্রতিষ্ঠা করেছে। একতরফা কিংবা খণ্ডিত বিধান দিয়ে নরনারীর জীবন বিষময় করে তােলেনি। সেজন্যেই ইসলাম বিবাহবিচ্ছেদকে একমাত্র বিশেষ পরিস্থিতিতেই মেনে নিয়েছে। কোরআনে এ সম্পর্কে যে ধরণের বিধান দেওয়া হয়েছে তাতে বিবাহ-বিচ্ছেদ করা অর্থাৎ তালাক দেওয়া অতি সহজ ব্যাপার নয়। কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে বর্জন করতে চাইলে তাকে উপযুক্ত কারণ ও প্রমাণ উপস্থিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পবিত্র কোরআনে। একতরফাভাবে পুরুষের স্বেচ্ছা সিদ্ধান্তের সুযােগ পবিত্র কোরআনে কঠোরভাবে প্রতিরােধ করা হয়েছে। কোরআনের বিধান মানলে পুরুষ স্বেচ্ছাচারিতার কোন সুযােগই পেতে পারে না।
অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি, সমাজে যা ঘটছে তাকে ইসলামের বিধান মনে করে ইসলামি নীতিগুলিকেই দায়ী করা হচ্ছে। কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এ সম্পর্কে সুচিন্তিত সন্ধানের দায়িত্ব পালন করতেও উদ্যোগী নন। অথচ ইসলামের বিধানের জন্যই এসব ঘটছে এমন রব তুলছেন। বাস্তবে যাই ঘটুক না কেন, কোরআনের বিধানে কোনভাবেই ‘তালাক’কে উৎসাহ ও শ্রেয় কাজ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। তালাককে প্রতিরােধ করার জন্য কঠোর বিধিনিষেধ আরােপ করা হয়েছে। কোরআনের পদ্ধতি অনুসৃত হলে একমাত্র অপ্রতিরােধ্য ক্ষেত্র অর্থাৎ যে পর্যায়ে পৌঁছে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটতে না দিলে বা বিচ্ছেদ আইন কঠোর নিয়মে বাঁধা থাকলে মানুষকে জীবনের মূল্যে হলেও, বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তি অর্জন করতে হয়, সে অবস্থা ছাড়া কখনই বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটতে পারে না।
স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পরিবারের ভুল বােঝাবুঝির অবসান না হয়—সেই চরম পর্যায়ে এসে ইসলাম বিবাহ-বিচ্ছেদ অর্থাৎ তালাককেই ঘৃণ্য পন্থা হিসেবে অনুমােদন দিয়েছে।
ইসলামের বিবাহ-বিচ্ছেদের নীতি ও পদ্ধতি আলােচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামের নবজাগরণকালেই বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে এক যুগান্তকারী বৈপ্লবিক বিধান ঘােষিত হয়েছিল। যে কোনও মুসলমানের তালাক দেওয়া বা বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানাের সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগেই পবিত্র কোরআনে নিম্নলিখিত কার্যকরী পন্থা গ্রহণের নির্দেশ রয়েছে—
- ১) বিরােধ দেখা দিলে প্রথমে সৎ উপদেশ দিতে হবে।
- ২) অতঃপর পরস্পর শয্যা পৃথক করতে হবে।
- ৩) অতঃপর সালিশ নিযুক্ত করতে হবে।
- ৪) অতঃপর উভয়পক্ষ থেকে একজন করে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরােধ নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করতে হবে।
এই চারটি পদ্ধতি প্রয়ােগের পরেও যদি বিবাহবিচ্ছেদ ঘটানাের প্রয়ােজন হয় তবে প্রথমে এক ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হওয়ার পর পরবর্তী ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার পূর্বে পবিত্র থাকার সময় এক তালাক দিতে হবে। এতে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটবে না। এরপর দ্বিতীয় ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হওয়ার পর তৃতীয় ঋতুস্রাব শুরুর পূর্বে আর এক তালাক দিতে হবে। এই দ্বিতীয় তালাকেও বিবাহবিচ্ছেদ ঘটবে না। এবার গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করে মন স্থির করতে হবে যে স্ত্রীকে গ্রহণ করবেন, না বর্জন করবেন। একান্তই বর্জন করতে চাইলে তৃতীয় ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হওয়ার পর পবিত্র থাকার সময় তৃতীয় তথা শেষ তালাক দিতে হবে। এবার চূড়ান্ত তালাক তথা বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গেল। এবার স্ত্রীকে সসম্মানে তার পাওনা মিটিয়ে অভিভাবকের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। ইসলামের এই বৈজ্ঞানিক নীতি প্রয়ােগ করলে দেখা যাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তালাক হবে না বরং স্বাভাবিক জীবনযাপন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।
অথচ মুসলমান বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন নিয়ে যে-সব কাণ্ডকারখানা চলছে তা বস্তুত বিবাহ-বিচ্ছেদ সমস্যার মূল মনােভঙ্গিকে পাশ কাটিয়ে সমাজ বিকাশের গতিশীল প্রক্রিয়াকে অস্বীকারের উন্মত্ত তাণ্ডবে পরিণত হয়েছে। সমস্যাটা কি শুধু মুসলিম মহিলাদের? নাকি তা সমগ্র ভারতীয় মহিলাদের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযােজ্য? সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিচ্ছেদজনিত ঘটনার আর্থসামাজিক পরিপ্রেক্ষিত, স্বামী-স্ত্রীর মানসিক গঠন প্রকৃতি, স্বাবলম্বনের সমস্যা ও তার বাস্তব ভিত্তি, ভূমিভাগ জনিত সম্পর্ক, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবােধ ও আধুনিক সমাজমনস্কতা, মধ্যযুগীয় সামন্ত-সম্পর্কের অন্তসারশূন্যতা এবং সর্বোপরি, ভারতীয় সমাজে নারীর স্থান ইত্যাদি ব্যাপারগুলােকে পাশ কাটিয়ে গােটা সমস্যাকে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে বিচ্ছেদপ্রাপ্ত মুসলিম মহিলার ভরণপােষণের নিমিত্ত আর্থিক ব্যবস্থা বিধানের পরিমাণগত প্রশ্ন। অর্থাৎ ভরণ-পােষণ ব্যয়ের গুণগত যথার্থতা যাচাইকে অস্বীকার করে সােজা কথায় যে প্রটো ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে তা হলাে, বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনায় মুসলিম মহিলাদের জন্য কতােটা পরিমাণ আর্থিক ভরণ-পােষণের ব্যয় নির্ধারিত হবে। বিচ্ছেদের পর তার অবশিষ্ট গােটা জীবনটার জন্য যে পরিমাণ অর্থ লাগে তার সম্পূর্ণ অংশ, না সাময়িক কিছু দিন, মাস বা বছরের জীবিকা নির্বাহের খরচটুকু মাত্র?
বাস্তব জীবনের এই বস্তুগত প্রয়ােজন-অপ্রয়ােজনের সাধারণ একটা ব্যাপার নিয়ে এতােটা জটিলতা সৃষ্টির কী এমন কারণ থাকতে পারে যার জন্য ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতি সমূহ, সংবিধানের ৪৪তম ও ১৪তম ধারা ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১২৫তম বিধান এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের একমাত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআনের নির্দেশাবলী ইত্যাদি বিষয়গুলাে জড়িয়ে পড়ে? আমাদের বাস্তব জীবনে এর চাইতে অনেক বড়াে বড়াে ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে কেন্দ্র করে তাে এতাে সব সাংবিধানিক ন্যায়-নীতি ও ধর্মীয় উপদেশাবলীর প্রসঙ্গ এসে যুক্ত হয় না! বাস্তব দুনিয়ায় পৃথিবীর মানুষ যখন পারমাণবিক যুদ্ধের মুখােমুখি, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে কি পারবে না সেই ভাবনায় অস্থির, যখন সমগ্র সভ্যতার স্থায়িত্বের সংকট ঘনীভূত, যখন আমাদের মতাে উন্নয়নশীল দেশগুলােতে শতকরা ৩০ ভাগেরও বেশি মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করছেন, যখন এদেশের বহু মানুষ নিরক্ষরতার অভিশাপে জর্জরিত, যখন দেশের অগুনতি মানুষের কোনাে কাজ নেই, যখন ভারতের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে—জীবন জীবিকার বেঁচে থাকার এই নিদারুণ সংকটের কথা না ভেবে হঠাৎ এই সমাজ ব্যবস্থার একটা সাধারণ উপসর্গ নিয়ে এতাে চেঁচামেচির কী এমন কারণ থাকতে পারে?
আর নারীকে বিবাহজনিত ব্যবহারিক মূল্যের নিরিখে বিচার করার পদ্ধতিটা যে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবােধেরই নামান্তর ছাড়া আর কিছুই নয় তা-ও কি সমাজ-বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে অস্বীকর করার উপায় আছে? বিবাহ-বিচ্ছেদের পর তার ভরণপােষণ বরাদ্দের অনুষঙ্গে কি নারীকে পণ্য হিসেবে ব্যবহারের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিভাত হয় না? ব্যক্তি স্বাতন্ত্রে বিধাসী নারীরা এ সম্পর্কে কী মত পােষণ করেন ? আজকের দিনের পুরুষ-প্রধান সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, নারীকে পণ্য হিসেবে, সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে নারীর স্বাতন্ত্র রক্ষা, সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারীর শােষণ মুক্তির আন্দোলনে নারী সমাজের মূল স্লোগান ও কর্মনীতি কী হবে? যে স্বামীর স্বেচ্ছাচারে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা সংঘটিত হয় সেই স্বামীরই কাছ থেকে প্রত্যাশিত খােরপােষের পরিমাণগত চুলচেরা বিচার ? না কি দাম্পত্য জীবনে পুষের স্বেচ্ছাচার প্রতিরােধের অনুষঙ্গে নারীমুক্তি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শােষণের মূল উৎসকে নির্মূল করা? তার অর্থ এই নয় যে, সাময়িক সমস্যাগুলােকে এড়িয়ে শুধু সমাজ বি-বের হঠকারী কর্মনীতি গ্রহণ করলেই হবে। বরং সাময়িক প্রাবলীকে সমাজবি-বের সেই নিগূঢ় জিজ্ঞাসায় ধাপে ধাপে উত্তরণ ঘটানােই হবে যে কোনাে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা-প্রিয় নারীর অবশ্য কর্তব্য। আমাদের মতাে উন্নয়নশীল দেশে, যেখানে নারী এখনাে আর্থনীতিক ভাবে স্বাবলম্বী নয়, সেখানে বিচ্ছেদের পর ও বিধবা হবার পর পুনর্বিবাহের সম্ভাবনা না থাকলে নারীর জীবন নির্বাহ হবে কী ভাবে? সে ক্ষেত্রে বিচ্ছেদপ্রাপ্তরা যে চলতি ভরণ-পােষণ বরাদ্দের অধিকার ভােগ করে আসছেন তা বাতিলের প্র অবশ্যই ওঠে না, বরং তাকে সম্প্রসারিত ও আরও বেশি গ্যারান্টিযুক্ত করতেই হবে, কিন্তু নারী মুক্তির চিন্তা এখানেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং পরিপূর্ণ শােষণ মুক্তির চিন্তায় তার উত্তরণ ঘটাতে হবেই। তাই বিবাহ-বিচ্ছেদের পর নারীকে ভরণ-পােষণের খরচ দেবার পরিমাণগত সমস্যা নিয়ে যারা ধর্মীয় বিধান, সাংবিধানিক ন্যায়নীতি ও ফৌজদারী দণ্ডবিধির সামঞ্জস্য-অসামঞ্জস্য কিংবা বৈপরীত্যের মধ্যেই শুধু ঘুরপাক খেতে চান তারা নারী মুক্তির মূল প্রণকে ধামাচাপা দিয়ে নারীকে সমান্ততান্ত্রিক ও ধনবাদী সমাজের দাসত্বের জায়গা থেকে একটু এপাশ-ওপাশ করিয়ে পুরনাে শােষণের শৃঙ্খলেই বােধ হয় বেঁধে রাখতে চাইছেন।
মুখে তিনবার ‘তালাক’ শব্দ উচ্চারণ করে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানাের বিধি নিয়ে মুসলিম মহিলার প্রতি অবিচার প্রসঙ্গে যথেষ্ট শােরগােল তােলা হয়েছে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে পুরুষ মানুষ তার বেকার স্ত্রীর ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিচ্ছে, তার সন্তানাদির খােরপােশ দিতে চাইছে, তখন ‘তালাক’ উচ্চারণ তিনবার করুক, কী নাই করুক, ব্যাপারটার কোনও হেরফের তেমন ঘটছে না। “আমি তােমাকে তালাক দিলাম’ বলার সঙ্গে ওই অবস্থার তফাতটুকুই বা কী?
নারীবাদী লেখিকা ও কর্মী মধু কিশােয়ার লিখেছেন,
“বহু সংখ্যক পরিত্যক্ত হিন্দু মহিলা সাহায্যের জন্য আমাদের শরণাপন্ন হয়েছেন। পরিত্যক্তা মুসলিম মহিলাদের চেয়ে তাদের দুরবস্থা কোনও অংশে কম নয়। এই তাে কিছুদিন আগেই এক যুবতী দুটি ছােট্ট বাচ্চা নিয়ে আমাদের কাছে এল। এতকাল স্বামীর সঙ্গে সে বিদেশে ছিল। তার স্বামী সেখানে ব্রাহ্মণ পুরােহিত। স্ত্রীকে ভদ্রলােক হঠাৎ বর্জন করে বেমালুম গা ঢাকা দিয়েছেন। এতটুকু আভাসও পায়নি হতভাগিনী। মন্দির কর্তৃপক্ষ তাকে দয়া করে ভারতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। গরিব বাবা মায়ের তাকে খেতে দেবার ক্ষমতা নেই। শুড়বাড়ির লােকেরা তার ওপর খাপ্পা। মেয়েটি জানে না তার স্বামী এখন কোথায়। কথা হল, স্বামী মুখে তিনবার ‘তালাক’ উচ্চারণ করে চলে যায়নি, বা ওই ধরনের নিয়ম পালন করেনি, এটা কোনও মেয়ের কাছে সান্ত্বনা নয়। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে, নিখােজ স্বামীর গতিবিধি জানার পর স্ত্রী খােরপােশের মামলা করেছে। কিন্তু স্বামী আদালতের থােড়াই পরােয়া করে। স্ত্রী আবার আদালতের ধরণা দেয়। ওই রকম চলতেই থাকে এবং শেষ পর্যন্ত যেটুকু আদায় তার বরাতে যদি বা জোটে তা মামলার খরচের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর।”
কাজেই মােদ্দা যে কথাটা ভেবে দেখার মতাে তা হল স্বামী স্ত্রীকে ছেড়ে চলে গেলেও স্ত্রীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা আছে কিনা, যাতে সে কোনও অবস্থাতেই দুর্দশায় না ভােগে। মূল সমস্যার চাবিকাঠিটি এখানেই। কোনও স্ত্রী স্বামীকে ছেড়ে গেলে স্বামী তাে আর সহায় সম্বলহীন দুঃস্থে পরিণত হন না এ সমাজে। স্বামী ও স্ত্রীর—পুরুষ ও মহিলার সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থায় নিহিত রয়েছে বর্তমান অসাম্যের বীজ। মহিলাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার প্রভূত পরিবর্তন সাধনের যেখানে অভাব, সেখানে ওপর থেকে কোনও আইন চাপিয়ে সাম্য গড়ে তােলা যায় না।
মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রক্রিয়া নিয়েও ভারতে সমালােচনা কিছু কম হয়নি। যদিও ভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের আনুপাতিক হারে খুব বেশী তফাৎ নেই। তবে পর পর তিনবার ‘তালাক উচ্চারণ করে বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রথা যে কোরান নির্দেশিত পথ থেকে বিচ্যুতি, একথা সত্যি। আদালতের হস্তক্ষেপে এই প্রথার পরিবর্তে চালু হওয়া উচিত সমঝােতা ভিত্তিক ও প্রতিষ্ঠানসম্মত একটি বিধি। বিবাহ-বিচ্ছেদ নিষিদ্ধ করা কিন্তু এর কোনও যুক্তিগ্রাহ্য সমাধান নয়। কারণ এর ফলে নানা ছলছুতােয় ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতাই শুধু বাড়বে না, বাড়বে আইনকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও। আসলে যা দরকার তা হল, বিধবাদের মতই বিবাহ বিচ্ছিন্নাদেরও পুনর্বিবাহে উৎসাহিত করা। কেননা শুধু আইন করে তালাক বা ডিভাের্স বা বিবাহ বিচ্ছেদের মত বাস্তব সামাজিক তথা পারিবারিক সমস্যাকে রােধ করা যাবে না। যেমন আইন করেও পণপ্রথা রােধ করা যায়নি।
বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা যাতে সমাজে ক্রমশই কমে যায় এবং দাম্পত্য জীবনের সুস্থতা বজায় থাকে, দাম্পত্য জীবনকে কেন্দ্র করে পুরুষের একপেশে স্বেচ্ছাচারের ধারণা বা সেই স্বেচ্ছাচারকে অধিকার বলে মনে করার সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবােধকে যাতে দোর্দণ্ড আঘাত দেওয়া যায় সেদিকে না গিয়ে নারীকে ব্যবহারিক বস্তু মনে করে তার ব্যবহারিক মূল্য ধরে দেবার সমস্যা নিয়ে ধর্মীয় বিধান টেনে এনে যারা হৈ-হট্টগােল বাধাবার তাল খুঁজে বেড়ান তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ জাগরিত হওয়াটা খুব স্বাভাবিক।
এই সন্দেহ উদ্রেকের আর একটা কারণ হলাে, বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারটা বর্তমান মুসলমান সমাজের মূল সমস্যা হিসাবে ব্যাপকভাবে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করছে কি না, অর্থাৎ এটা এ-যুগের বার্নিং ইস্যু কি না সেই প্রকে এড়িয়ে যাওয়ার মনােভঙ্গি। আদতে মুসলমান সমাজের কাছে জ্বলন্ত বাস্তব সমস্যা হিসাবে এই ঘটনার প্রধান গুরুত্ব আছে কি? তাদের কাছে সংখ্যার বিচারে চাকরির বা স্বাবলম্বনের সমস্যা ও বিধবা অবস্থায় উঞ্ছবৃত্তির সমস্যার চেয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদের সমস্যা কি ব্যাপক? সমাজ বিজ্ঞানীরা কি বলেন? এ দেশের ১৬কোটি মুসলমানের জীবনে শতকরা কতাে জনের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে?
বহুবিবাহ ও ইসলাম
শুধু বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপার নয় বহুবিবাহ ও আত্মীয়-বিবাহের সমস্যাটা এ প্রসঙ্গে এসে পড়ে এ-কারণেই যে, এ-দেশের অমুসলমানদের অনেকের ধারণা একমাত্র মুসলমানরাই বােধ হয় এ-সব উপসর্গের দ্বারা আক্রান্ত। তাদের ধর্মেরও এ-ব্যাপারে সায় আছে এমন ভ্রান্ত ধারণারও অভাব নেই। সমাজ-বিকাশের বিভিন্ন স্তর, আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেথিত পর্যবেক্ষণের দ্বারা বিষয়টা বিচার করলে এ ধারণা যে ভুল বুঝতে অসুবিধা হয় না। ইসলাম বহুবিবাহ প্রথার প্রথম প্রবর্তক নয়। অতীতের প্রায় সকল জাতিতেই এই প্রচলন ছিল। গ্রীক, চৈনিক, ভারতীয়, ককেশীয়, অ্যাসেরীয়, মিশরীয় প্রভৃতি সব জাতিতেই বহুবিবাহ চালু ছিল। এই জাতিগুলাের অধিকাংশেই শুধু বহু বিবাহ চালু ছিল তা নয়, বরং তারা এর কোন সীমা সংখ্যাও মেনে চলত না। ঐতিহাসিকভাবেও প্রমাণিত যে, প্রাচীন খ্রিস্টানরা একাধিক বিয়ে করত। এমনকী প্রাচীনকালের ধর্মযাজকদেরও কারাে কারাে একাধিক স্ত্রী থাকত। বিশেষ বিশেষ স্থানে ও জরুরি অবস্থায় একাধিক স্ত্রী বিয়ে করা প্রাচীন খ্রিস্টীয় আমলে বৈধ মনে করা হতাে।
ওয়েস্টার মার্ক বলেন, গির্জার স্বীকৃত প্রথা হিসাবে বহুবিবাহ সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত চালু ছিল। ১৬৫০ সালে ত্রিশ বছর ব্যাপী যুদ্ধে ব্যাপক লােক ক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে নুরেমবার্গে ঘােষণা করা হয় যে, এক সাথে দুই স্ত্রী রাখা বৈধ। এমনকী কোন কোন খ্রিস্টান উপদল বহুবিবাহকে বাধ্যতামূলক বলেও ঘােষণা করে। ডিক্সনারী অফ দ্য বাইবেল অনুসারে, একজন সাধারণ মানুষ চার এবং একজন রাজা ১৮টি বিবাহ করতে পারত। বাইবেলে জেকবের ঘটনা বর্ণনায় আছে—লেবানয়ের বাড়িতে বছরের পর বছর গতর খাটার পর জেকব তার প্রভু লেবানয়ের দুই মেয়েরই পতীত্ব লাভ করে। শুধু তাই নয়, সেই দুই পত্নী থাকা সত্বেও জেকব আরও কয়েকজন দাসীকেও বিয়ে করে। বহুবিবাহ ছিল প্রাচীন হিন্দু সমাজেরও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বৈদিক সমাজে ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুবিবাহের মাধ্যমে সামাজিক মর্যাদা নির্ণীত হত। যুদ্ধে বিজয়ী সেনাদের কয়েকটি পত্নী রাখার অধিকার ছিল, যাদের মধ্যে একজনকে ‘মহিষী’ অথবা ‘বড়রাণী’ আখ্যায়িত করা হত। সংস্কৃত গবেষিকা সুকুমারী ভট্টাচার্য তার গবেষণামূলক গ্রন্থ ‘প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য’-এ বহুবিবাহের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা এককথায় রােমহর্ষক। ‘বৈদিক সমাজে নারীর স্থান’ শীর্ষক অধ্যায়ে তিনি মন্তব্য করেছেন,
“পুরুষের বহুবিবাহ ঋগ্বেদের যুগ থেকেই চলে আসছে, তবে ঋগ্বেদের সময়ে নারীরও বহুপতিত্বে অধিকার ছিল, যদিও এ অধিকার সে অল্প কিছুকালের মধ্যেই হারায়।”
মহাকাব্যের যুগেও বহুবিবাহ চলত। তাছাড়া ব্রাহ্মণ্য সমাজে একজন পুরুষের শতাধিক বিয়ের অধিকার কতাে দিন আগে লােপ পেয়েছে? উনিশ শতকের শেষার্ধের বাংলা নাটকে এ নিয়ে তাে যথেষ্ট বিদ্রুপ আমাদের চেখে পড়ে। আবার, এখনােও দক্ষিণ ভারতের কোনাে অংশে নিজের ভাগ্নীকে বিয়ে করার রীতি আদর্শ পন্থা হিসেবে চালু রয়েছে হিন্দুদের মধ্যেই। অরুণাচল প্রদেশে উপজাতিদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত। এমন পর্যন্ত দেখা গেছে যে, একজন পুরুষ ১০ জন স্ত্রীকে নিয়ে আছেন। সেখানে বিয়ে হলে মেয়ের পরিবার যৌতুক পায়। গােয়াতে বহু বিবাহ আইন সিদ্ধ। ব্যাপারটা মুসলমানদেরই কি তাহলে একচেটিয়া অভ্যাস? আসলে কোন্ ঐতিহাসিক পর্বে, কী ধরনের সমাজ বাস্তবতার মধ্যে অবাধ যৌনাচার থেকে বিবাহ-ব্যবস্থার উৎপত্তি ঘটলাে, বা এক পতি-পত্নী ব্যবস্থা কোন সম্পত্তি সম্পর্কের সূত্র ধরে চালু হলাে, আর বহু বিবাহই বা কী ধরনের সমাজ মানসিকতার ফল—এ সবের সমাজবিজ্ঞানসুলভ অনুসন্ধিৎসু ধারণার অভাবের ফলেই ধর্মীয় শীলমােহরের রঙে এক একটা সম্প্রদায়ের দোষ ত্রুটি বিচারের অভ্যাস আমাদের এখনাে রয়ে গেছে। মজ্জায় মজ্জায়।
এদেশের মুসলমান সম্প্রদায় সৃষ্টির ইতিহাস তাে মাত্র ত্রয়ােদশ শতকে শুরু হয়েছিল। ভারতে প্রায় সমস্ত মুসলমানদেরই পূর্বপুরুষ ছিলেন হয় ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী, নয় তাে হীনযান বৌদ্ধদের একটা অংশ। খােদ আরব বা মুসলমান দেশ থেকে কতাে জন এদেশে এসেছিলেন? তা কি পরিসংখ্যানগত মাত্রা অর্জন করতে পারে? যে-অর্থে পরবর্তীকালের ব্রিটিশদের বিদেশী বলে আখ্যাত করা যায়, সেই অর্থে কি হুমায়ুন, আকবর, শাহজাহান বিদেশী কি? না কি, ইন্দো-এরিয়ান গােষ্ঠীর মতাে তারাও ভারতকেই তাদের জন্ম-মৃত্যুর কেন্দ্রস্বরূপে মাতৃভূমি হিসেবেই মেনে নিয়েছিলেন।
আর মুসলমানদের মধ্যে বহু-বিবাহ সাধারণ প্রথা হিসাবে কোনাে কালেই স্বীকৃতি পায়নি। সপ্তম শতকে খােদ আরবে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের সময়েও পৌত্তলিক আরবের এই বদভ্যাস বর্জনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। কোরআনেও এর স্বাভাবিক সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় কিছু কিছু ঘটনা স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ এই নয় যে, নির্বিচারে তা আইন বা রীতি হিসাবে গ্রহণ করা যায়। কোরআনে বহু বিবাহ বিষয়ক ঘটনার যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা ওহােদের যুদ্ধ পরবর্তী সমস্যা হিসাবে। সপ্তম শতকে ওহােদের যুদ্ধে ৭০ জন মুসলমান নিহত হন। এটা বদর যুদ্ধের পরের ঘটনা। এ যুদ্ধে হজরত মােহাম্মদের (সঃ) নিজের জীবনও বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। সেই যুদ্ধে নিহত মুসলমানদের বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের কথা মনে রেখেই ৬২৬ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ কিছু বিধান সৃষ্টি হয়। কোরআনের চতুর্থ অধ্যায় ‘নিসা’ অর্থাৎ ‘নারী’ তে এই বিধান বিধৃত। ‘নারী’ শীর্ষক এই চতুর্থ অধ্যায়ের ২য় অংশে বলা হয়েছে,
“অনাথদের সম্পত্তি অনাথদেরই দিয়ে দাও। আর উৎকৃষ্ট বস্তুর বদলে নিষ্কৃষ্ট বস্তু দিও না কিংবা তােমাদের সম্পত্তির মধ্যে তাদের সম্পত্তি গ্রাস করে নিও না। সেটা হবে ভয়ানক দোষনীয়।”
এভাবে এই সমস্যার সুবিচার করা যে বেশ দুরূহ সে-কথা মনে রেখেই এর ঠিক পরের অংশে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে,
“আর যদি আশঙ্কা করাে যে, অনাথদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে পারবে না তাহলে সেই অনাথদের মায়েদের মধ্যে তাদের বিয়ে করে নাও যাদের তােমার পছন্দ হয়—দু’জন, তিন জন বা চার জন। কিন্তু যদি আশঙ্কা করাে যে, তাদের ওপর ন্যায়বিচার করতে পারবে তবে একজনকেই (বিয়ে করাে) অথবা তােমাদের অধীনে আসা দাসীদের। এটাই অধিকতর সঙ্গত যে, তােমরা অবিচার করবে।”
এই অংশের মর্মার্থ কী? এ থেকে কী শিক্ষা গ্রহণ করা যায়? একাধিক বিয়েকে এখানে সমর্থন করা হয়েছে? কোরআনে যুদ্ধ পরবর্তী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যদি এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করে একজনকে বিয়ে করার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থায় কি একের বেশি দুজনকে বিয়ে করা যায়? নাকি দু’জন মহিলাকে একই সঙ্গে সমানভাবে ভালােবাসা যায়? তা যদি না যায়, যে-কোনাে অবস্থাতেই এক পত্নী গ্রহণের নির্দেশই তাে দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। কোরআনে অন্য কোথাও কি আর একাধিক বিয়ে সম্পর্কে কিছু বলা হয়েছে যা এই মৌলিক সিদ্ধান্তের বিরােধী?
তাছাড়া খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে, যখন সারা আরব দেশে অর্থের বিনিময়ে নারী কেনা-বেচার ব্যবসা চলছে আইনগত পদ্ধতিতেই তখন ব্যাভিচার বা যৌন অনাচার বন্ধ করার জন্য একলাফে ‘একটাই’ বলে কঠোর বিধি-নিষেধ আরােপ না করে কিছুটা সীমিত সংখ্যক নারীকে বিবাহ-বিধির দ্বারা বৈধভাবে গ্রহণের কথা যদি কেউ বলেও থাকেন, তা কি খুব অযৌক্তিক? আধুনিক যুগেও তাে এমন ঘটনা আকসার ঘটছে—একটা বৈধ স্ত্রী আর দু-তিনটা উপপত্নি নিয়ে লক্ষে অলক্ষে মানুষ দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটা কি নারীত্বের অবমাননা নয়?
আসলে ইসলাম ধর্মের দেশ বলে যারা খ্যাত তার মধ্যে অনেক দেশে সাধারণ ভাবে বহু বিবাহ তাে আইনের বলেই রাষ্ট্র কর্তৃক নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যদিও কোরআনের ‘নারী’ বিষয়ক মূল অধ্যায়ে অবাধ ও একাধিক বিবাহের ব্যাপারটা সেই সপ্তম শতকে ইসলামি বিধি প্রবর্তনের যুগেও কখনােই ঢালাও ভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়নি এবং কোরআনের অন্যত্রও বহু। বিবাহের পক্ষে অন্য কোনাে বিধান নেই। তবু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই অভ্যাস রয়ে গেছে। বিভিন্ন সমাজে ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একাধিক বিবাহের রীতি যে চালু হয়েছে তার পেছনে মূলত যে-দর্শন ক্রিয়াশীল তা হলাে সামন্তযুগীয় শােষণের ও সামন্তরাজন্যবর্গের সম্পত্তি-সম্পর্কের ও নিপীড়নেরই মধ্যযুগীয় তত্ত্ব। এটা যে শুধু মুসলমানদেরই চারিত্র ধর্ম বলে ব্যাখ্যা করা হয় তা ঠিক নয়। এ ভাবনা মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িক চিন্তার দাসত্ব থেকে উৎসারিত। একটা নজির দেওয়া যাক। ১৯৭৫ সালে ভারতে মহিলাদের মর্যাদা বা অবস্থা নির্ণয় সংক্রান্ত একটি কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয় লােক গণনা বিষয়ক একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, পুরুষদের বহু বিবাহের হার হিন্দুদের মধ্যে ৮.৫ শতাংশ এবং মুসলিমদের মধ্যে ৫.৭ শতাংশ। তার মানে, বহুবিবাহের ব্যাপারে হিন্দুদের সঙ্গে মুসলিমদের কোনও তাৎপর্যপূর্ণ তফাত নেই, যদিও বহু বিবাহ মুসলিমদের ক্ষেত্রে বৈধ এবং হিন্দুদের ক্ষেত্রে অবৈধ।
১৯৫৫ সালের হিন্দু দত্তক এবং খােরপােশ আইনে কোনও হিন্দু পুরুষ বা মহিলা একা থাকলে নিজের নিজের নামে কোনও শিশুকে দত্তক নিতে পারেন। কিন্তু কোনও বিবাহিতা মহিলা নিজের নামে কোনও শিশুকে দত্তক নিতে পারেন না। দত্তক নিলে তা নিতেই হবে তার স্বামীকেই। অর্থাৎ দত্তক গ্রহণের অধিকারী স্ত্রী নন।
এ সব ছাড়াও হিন্দু ব্যক্তিগত আইনে বহু ধর্মীয় ব্যাপার আছে, যা মহিলাদের ক্ষেত্রে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করে এবং করছেও। যেমন ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইনে রেজিস্ট্রিকৃত না হলেও হিন্দু বিয়ে বৈধ। সপ্তপদী বা ঐ ধরণের কিছু অনুষ্ঠান পালিত হলেই হিন্দু বিয়ে আইনত সিদ্ধ বলে গণ্য হয়। কিন্তু বহু পুরুষ দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন এবং ওইসব অনুষ্ঠানের কিছু অংশ ইচ্ছে করেই বাদ দেন। দ্বিতীয় বিয়েও যেহেতু প্রকাশ্যে জাঁকজমক দেখিয়ে করা হয়, সেই হেতু তা সমাজের স্বীকৃতিও পায়। কিন্তু আইনের কিছু নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের কথা বলা আছে, তা পালিত হয়নি বলে আদালত সে বিয়েকে বৈধ হিন্দু বিয়ে বলে গ্রাহ্য করবেন না। ঠিক এজন্যই স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হিন্দু স্ত্রীর পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। হিন্দু পুরুষের এক স্ত্রীর বর্তমানে দ্বিতীয় বিয়ে নিষিদ্ধ হলেও এখনও এটা তাই বাস্তবে সমানে ঘটে চলেছে।
কু-আচার, অনাচার, শােষণ, ব্যাভিচার কোনাে বিশেষ ধর্মের ফল নয়। বিশেষ যুগের বিশেষ সমাজ ব্যবস্থারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। ইতিহাসের এক পর্বে একটা সময় ছিল যখন পুরুষ ইচ্ছা করলে একাধিক স্ত্রী কিনে নিতে পারতাে। যুদ্ধে জয়লাভ করে পরাজিতদের কাছে থেকে নারীদের সম্পত্তির মতাে দখল নিত। পরবর্তী সময়ে যখন সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা একেবারেই অসমান হতে লাগলাে আর নারীদের ভরণ-পােষণের সমস্যা দেখা দিল, তখন অল্প সংখ্যক পুরুষই একসঙ্গে এতাে নারী রাখেতে সমর্থ হতাে। এভাবেই ক্রমেই সেই সংখ্যা কমে যেতে থাকলাে।
প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতে ভাইয়ে-ভাইয়ে, বংশে-বংশে যে খুনােখুনি, দ্বন্দ্বের কাহিনি তাে আর অপ্রকাশ্য নয়। তাছাড়া একটা সময়ে কুমারী মেয়েদের বেচে দিয়ে যে পুরােহিতরা বেশ্যায় পরিণত করতাে তারা কোন্ ধর্মের ছিল? রােমান সাম্রাজ্যে খুনােখুনির নায়ক কারা ছিল, গ্রীসে রাজতন্ত্রের অধিকার নিয়ে যে রক্ত হানাহানি, পিতা-পুত্র, ভাইয়ে ভাইয়ে যে সংঘর্ষের ঘটনা তা যে কোনাে রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্রের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। অথচ পিতা-পুত্র ভাইয়ে ভাইয়ে খুনােখুনির বা বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারটা যেমন মুসলমানদের একচেটে ব্যাপার—এমন বস্তাপচা, কুপমণ্ডুক ও অনাধুনিক ধারণা আমাদের দেশে অনেক প্রগতিশীল বলে শীলমােহরযুক্ত শিক্ষিত মানুষের মধ্যে পাকাপােক্তভাবে দানা বেঁধে রয়েছে। রাস্তাঘাটে এ ধরনের উক্তি হামেশাই এ-দেশের তথাকথিত অমুসলিম ভদ্রজনের মুখে শােনা যায়। ইতিহাসবােধ ও সমাজচেতনার এ হেন পর্যায়ে যাদের অবস্থান তারাই আবার বিবাহ-বিচ্ছেদের মতাে বিষয়কে ইস্যু হিসেবে দাঁড় করিয়ে নানান কায়দায় প্রগতিশীল চিন্তার দাবিদার বলে গালগলা ফুলিয়ে চেঁচাতে থাকেন! নারীরা মনুষ্য জাতি কিনা বা তাদের আত্মা আছে কিনা এই পুরনাে প্রণ নিয়ে এখনাে অনেক মানুষ দোটানায় ভুগছে। এদের মধ্যে সব ধর্মেরই লােক আছে। বিশেষ কোনাে ধর্মকে কি এ ব্যাপারে দায়ী করা যায়? হজরত মােহাম্মদের (সঃ) বহু বিবাহের তাৎপর্য ইসলামে শর্তসাপেক্ষা চারটির অধিক বিবাহের বিধান না থাকা সত্বেও হজরত মােহাম্মদের (সঃ) চারটির অধিক স্ত্রী বর্তমান থাকার তাৎপর্য কি? ইউরােপীয় সঙ্কীর্ণতাবাদীগণ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও অন্যান্য কারণগুলি অনুসন্ধান না করেই হজরত মােহাম্মদের (সঃ) জীবনের এই ঘটনাকে সমালােচনা করেছেন। তারা কিছু ভিত্তিহীন ঐতিহাসিক মন্তব্য ও কল্পকাহিনির আশ্রয়ে এক অপাপবিদ্ধ, নির্মল, মানবচরিত্রের উপর কলঙ্ক আরােপ করেছেন। এইসব ছিদ্রান্বেষণকারীদের সঙ্গে আমরাও একমত যে,
- ১) হজরত মােহাম্মদ (সঃ) বহুপত্নীক ছিলেন।
- ২) তার এগারােজন সহধর্মিনী ছিলেন।
- ৩) মক্কার সম্ভ্রান্ত বংশীয় খােয়ায়লেদের বিধবা কন্যা হজরত খাদিজাকে (রাঃ) পঁচিশ বছর বয়সে প্রথম পত্নীত্বে বরণ করেন।
- ৪) হজরত মােহাম্মদের (সঃ) ইহজীবন ত্যাগের পর তার ন’জন পত্নী জীবিত ছিলেন।
একটি বিষয়ে সমালােচক একমত যে, তার প্রথমা পত্নী হজরত খাদিজার (রাঃ) জীবদ্দশায় তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেননি। যদিও এই সময় সমগ্র আরবে অসংখ্য স্ত্রী গ্রহণ সমাজ-স্বীকৃত প্রথা ছিল। এরপরও তারা এরকম মন্তব্য করেন যে, কাম-প্রবৃত্ত হয়েই হজরত মােহাম্মদ (সাঃ) এতগুলি বিবাহ করেছিলেন। বিশ্বের সকল মনােবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীগণই কামুকদের কিছু স্বভাব বৈশিষ্ট্যের কথা ঘােষণা করেছেন। যেমন কেউ কামুক হলে তার চরিত্রে থাকবে মিথ্যাচারিতা, ভােগবিলাসিতা, পানাসক্তি, ধর্মবিমুখতা, ছলচাতুরী, বিধাসঘাতকতা ও চরিত্রহীনতা—এসবই একজন লম্পট ও কামুকের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। সারা বিধের কোনও সমালােচকই প্রমাণ করতে পারেননি যে, হজরত মােহাম্মদের (সঃ) চরিত্রে এর একটি দোষও ছিল।
হজরত মােহাম্মদ (সঃ)-এর বিবাহ বিশ্লেষণ করলে যে সহজ চিত্র পাওয়া যায় তা হলােঃ-
- ১) জন্ম থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত অকৃতদার যুবক। নিষ্কলঙ্ক নির্মল চরিত্রের অধিকারী। আল-আমিন (চির বিশ্বাসী) আখ্যায় আখ্যায়িত।
- ২) ২৫ বছর বয়স থেকে ৫০ বছর পর্যন্ত—একমাত্র প্রৌঢ়া স্ত্রীর সঙ্গে সংসার জীবনযাপন। অতুলনীয় চরিত্র মাধুর্যে সুমহান।
- ৩) ৫১ বছর বয়স থেকে ৫৫ বছর বয়স পর্যন্ত—একজন ৭০ বছর বয়স্কা বৃদ্ধা স্ত্রী ও আর একজন ৭ বছরের শিশু স্ত্রী।
- ৪) ৫৬ বছর বয়স থেকে ৬০ বছর সময়কালে—নানা কারণে নানা শ্রেণির ৯ জন মহিলাকে পত্নীত্বে বরণ ও আশ্রয় দান।
- ৫) ৬০ বছর থেকে ৬৩ বছর বয়স পর্যন্ত—আর কোনও বিবাহ নেই।
উপরােক্ত বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, পরিপূর্ণ যৌবন থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত এমন এক নারীর (হজরত খাদিজা) সঙ্গে পরম তৃপ্তি ও সম্মানজনকভাবে সংসার নির্বাহ করেছেন যিনি কুমারী নন। যাঁর ইতিপূর্বে দু-দুবার বিবাহ হয়েছে, যিনি কিশােরী নন। যাঁর পূর্ব স্বামীর সন্তান-সন্ততিও ছিল। এই সময় তাকে বহু সুন্দরী লাস্যময়ী কুমারী মহিলার প্রলােভনও দেখানাে হয়েছে। তাছাড়া সেই সময়ের সমাজে অধিক সংখ্যক বিবাহ স্বীকৃত প্রথা ছিল। হযরত মােহাম্মদের (সঃ) কোনওভাবেই ওই প্রথার সুযােগ গ্রহণ করেননি।
আমরা দেখি, তার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর ৫১ থেকে ৫৫, এই ছ’বছর বিবাহিত হয়েও অবিবাহিতের মতাে জীবন কাটিয়েছেন। এই সময় তার দু’জন স্ত্রীর একজন ৭০ বছরের বৃদ্ধা, অন্যজন ৭ বছরের বালিকা। ‘লেটার ফ্রম ইজিপ্ট’ গ্রন্থের ১৩৯-১৪০ পৃষ্ঠায় একজন প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক লিখেছেন,
“হজরত মােহাম্মদ (সঃ) যে সকল নারীকে বিবাহ করেছিলেন তাদের মধ্যে একজন ব্যতীত বাকিদের ৫৪ বছর বয়সের পর বিবাহ করেন। তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই আশ্রয়হীনা ও বিধবা। তাদের তিনজন তারই শিষ্যদের বিধবা পত্নী, যাঁরা মক্কাবাসীদের উৎপীড়ন ও অত্যাচারে জন্মভূমি ত্যাগ করে স্ত্রী পুত্রসহ আবিসিনিয়ায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। অপর দু’জনের স্বামী ইসলাম রক্ষার্থে মদিনায় শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ হারান। যাঁরা অপরের জন্য জীবন দান করেন তাদের অসহায় নিঃসহায় বিধবাদের বিবাহ করে আশ্রয় দান ও রক্ষা করা আইন সিদ্ধ এই কাজকে আরববাসীগণ উদারনৈতিক ও দয়ালু কাজ বলে বিবেচনা করেন।”
এ থেকে আমরা সহজে যা পাই তা হলাে, একজন মুসলমানের তথা প্রকৃত বিশ্বাসীর আত্মচরিতার্থ, আত্মসুখ বা হৃদয়বৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণ অপ্রয়ােজনীয় ও অনভিপ্রেত। হজরত মােহাম্মদ (সঃ) নিজেও ৫৫ বছর বয়স কাল পর্যন্ত এই নীতি পালন করেছেন। সমাজে ও আইনে অনুমােদন থাকা সত্বেও একাধিক স্ত্রী গ্রহণ না করে এক প্রৌঢ়া স্ত্রীকে নিয়েই ২৫ বছর বয়স থেকে ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত সংসার করেছেন। বিৰ্বের মুসলমানের সামনে পালনীয় আদর্শ হিসেবে এর চেয়ে বাস্তব বিধান আর কি হতে পারে! এই আলােচনা ও ইতিহাসের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, হজরত মােহাম্মদের (সঃ) বার্ধক্য কালের বিবাহসমূহ কোনওভাবেই দৈহিক প্রয়ােজনে নয়, বরং বিশেষ পরিস্থিতি পর্যালােচনা করে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ও রাষ্ট্রনৈতিক কারণে গৃহীত সিদ্ধান্ত।

উপসংহারে বলি, ইসলামে অনাড়ম্বর বিবাহকেই শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে হজরত মােহাম্মদের (সঃ) সুস্পষ্ট নির্দেশ, “সেই বিবাহই উত্তম যাতে অল্প যন্ত্রণা এবং অল্প ব্যয় হয়।” হজরত মােহাম্মদ (সঃ) আরও বলেছেন, “যে বিবাহে সর্বাপেক্ষা কম কষ্ট হয়, তাতে সর্বাপেক্ষা অধিক বরকত (শ্রীবৃদ্ধি) আছে।” অতএব বােঝা যাচ্ছে যে, ইসলামে বিয়ের মূল গুরুত্বটাই রয়েছে তার অনাড়ম্বরতায়, তার মিতব্যয়িতায়। জন্মজন্মান্তরের দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করার ব্যাপারটি মুসলিম বিয়েতে একেবারেই নেই, স্বর্গীয় কাব্যিক বাতাবরণ তৈরী করার চেষ্টামাত্রও করা হয় না। ঠিক ঠিক বলতে গেলে এটা ভীষণই গদ্যময় বাস্তবসম্মত এক সামাজিক চুক্তিমাত্র, যার মাধ্যমে একটা বিশেষ অঙ্কের দেনমােহর’ পণ রেখে নারী ও পুরুষ স্ব-স্ব ইচ্ছায় বিবাহিত হয়। কোন কারণে বিয়ে টিকলে, সম্পর্কের মধ্যে থাকা ঐ বিবাহ অনুষ্ঠানকালীন নারীকে প্রদেয় চুক্তিকৃত দেনমােহর প্রত্যার্পণ ও গ্রহণের মাধ্যমে শেষ হয়ে যাবে পূর্বচুক্তি (বিবাহ)।
ঋণ স্বীকার :
- সুকুমারী ভট্টাচার্য, মুহম্মদ আয়ুব হােসেন সাহিত্যবিনােদ, কানিজ মুস্তাফা, জিয়াদ আলী, আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান, আবদুর রাকিব, আবু রিদা, আফিফ এ তাব্বারাহ, সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় দেব, রত্না রশীদ, রফিকুল ইসলাম, খাইরুল বাসার।
‘নবজাগরণ’ অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপ্লিকেশনটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।
![]()
‘নবজাগরণ’ এর টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।
‘নবজাগরণ’ এর ফেসবুক পেজে লাইক করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

 নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা
নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা