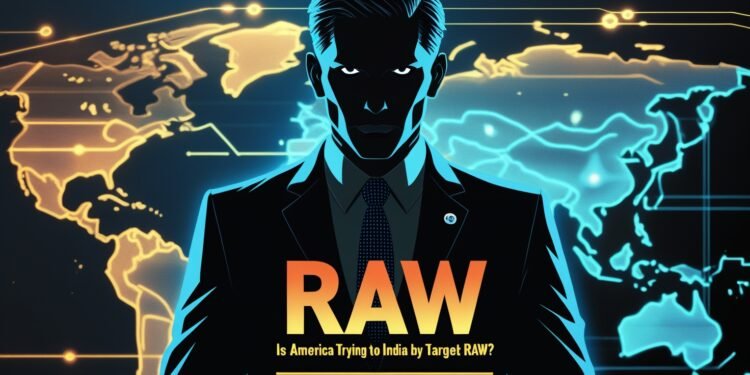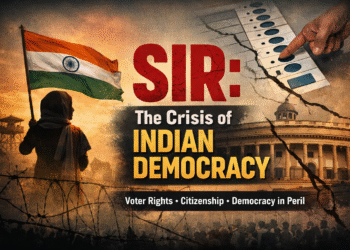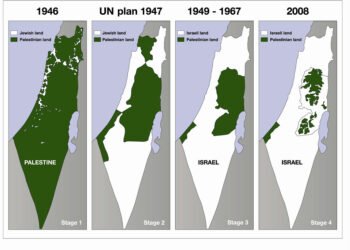লিখেছেনঃ মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম
সাম্প্রতিক কালে ভারতের বৈদেশিক গুপ্তচর সংস্থা ‘রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং’— সংক্ষেপে ‘র’ (RAW) —কে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তীব্র বিতর্ক দানা বেঁধেছে। এই বিতর্কের মূলে রয়েছে এমন অভিযোগ, যা সংস্থাটিকে বিদেশে শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের হত্যার পরিকল্পনায় জড়িত বলে চিহ্নিত করেছে। সেই সঙ্গে উঠে এসেছে ভারতের অভ্যন্তরে ধর্মীয় স্বাধীনতা লঙ্ঘনের প্রসঙ্গও। বিষয়টিকে ঘিরে আলোড়ন আরও ঘনীভূত হয়েছে যখন যুক্তরাষ্ট্রের ‘ইউনাইটেড স্টেটস কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম’ (ইউএসসিআইআরএফ) একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে এবং তাতে ভারতের গোয়েন্দা কার্যক্রমের উপর নিষেধাজ্ঞার সুপারিশ করা হয়। মার্চ মাসে প্রকাশিত সেই রিপোর্টে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, ‘র’ (RAW) একদিকে যেমন বিদেশে শিখ নেতাদের নির্মূলের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তেমনি দেশের ভেতর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর বৈষম্যমূলক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা খর্বকারী নানা কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশ নিয়েছে।
এই অভিযোগ যে নিছক অনুমান নির্ভর নয়, তার প্রমাণ হিসেবে উল্লেখযোগ্য দু’টি ঘটনা বিশেষভাবে সামনে এসেছে— ২০২৩ সালে কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যাকাণ্ড এবং ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে গুরপতবন্ত সিং পান্নুনের বিরুদ্ধে গোপন হত্যাচক্রান্ত। এই দুটি ঘটনাই আন্তর্জাতিক মহলের চোখ ফেরাতে বাধ্য করেছে ভারতের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও কূটনৈতিক নীতির দিকটিতে। যদিও ভারত সরকার দৃঢ়তার সঙ্গে ইউএসসিআইআরএফ-এর এই সুপারিশকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং একে ‘পক্ষপাতদুষ্ট’ ও ‘ভিত্তিহীন’ বলেই অভিহিত করেছে, তবু এই প্রতিক্রিয়া যে কূটনৈতিক জগতে বিশেষ সাড়া ফেলেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ভারতের পক্ষ থেকে এমন প্রতিক্রিয়া অনভিপ্রেত নয়, বরং রাজনৈতিক ও কূটনৈতিকভাবে তা প্রত্যাশিতই ছিল। কিন্তু যা বিস্ময়কর, তা হল— মার্কিন কংগ্রেসের দুই কক্ষের সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি কমিশন, অর্থাৎ ইউএসসিআইআরএফ, বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে দীর্ঘকাল ধরে বিবেচিত ভারতের অন্যতম প্রধান সরকারি গোয়েন্দা সংস্থার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারির সুপারিশ করেছে। আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ইতিহাসে এই পদক্ষেপ প্রায় নজিরবিহীন। প্রায় আড়াই দশক ধরে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে ভারতকে অন্যতম ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে পাশে পেয়েছে আমেরিকা। সেই ভারতের প্রতি এমন সন্দেহের দৃষ্টি এবং সরাসরি গোয়েন্দা সংস্থার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান বিশ্বরাজনীতির গতিপথে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।
এই বিতর্কের নেপথ্যে রয়েছে খালিস্তান প্রশ্ন ও শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাস, যা ভারতের সঙ্গে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ককেও সময় সময় জটিল করে তুলেছে। বিশেষত কানাডা ও আমেরিকায় বসবাসকারী শিখদের একটি অংশ এখনও খালিস্তান আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল, এমনকি তা সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে থাকে। এই বাস্তবতা ভারতের জন্য সর্বদা সংবেদনশীল। ইউএসসিআইআরএফ-এর দাবি অনুযায়ী, ‘র’ (RAW) এই আন্দোলনকে রুখতে চরম পদক্ষেপ নিয়েছে, যার মধ্যে বিদেশের মাটিতে রাজনৈতিক হত্যার ছক কষাও অন্তর্ভুক্ত।
যতই ভারত সরকার এই অভিযোগ খণ্ডন করুক, ততই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এক নতুন বিতর্কের জন্ম হচ্ছে— রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনটা সীমালঙ্ঘন, আর কোনটা বৈধ প্রতিরক্ষা কৌশল? বিদেশে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত গুপ্তহত্যার মতো অভিযোগ, যদি প্রমাণিত হয়, তবে তা শুধু একটি দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার নয়, বরং তা গোটা আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা কাঠামোকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দেয়। আবার, কোনো কোনো রাষ্ট্রের ভেতরে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সংখ্যালঘু অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়েও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চুপ করে থাকা সম্ভব নয়। এই দ্বিমুখী চাপ ও দ্বিধার মধ্যেই ‘র’ সংক্রান্ত সাম্প্রতিক বিতর্ককে দেখতে হবে।
সুতরাং, আজকের এই বিতর্ক কেবল শিখ নেতাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বা হত্যার অভিযোগে সীমাবদ্ধ নয়— এটি ভারতের অভ্যন্তরীণ নীতি, বিদেশ নীতি, কূটনৈতিক অবস্থান ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বরূপ নিয়ে এক গভীর আত্মসমালোচনার সুযোগ এনে দিয়েছে। একদিকে বিদেশে সক্রিয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কার্যকলাপ, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মানবাধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতা সংক্রান্ত উদ্বেগ— এই দুইয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে ভারত এখন এক জটিল নৈতিক ও কৌশলগত দ্বন্দ্বের মুখোমুখি। এই দ্বন্দ্বের ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ভর করবে কূটনৈতিক দক্ষতা, তথ্যের স্বচ্ছতা এবং আন্তর্জাতিক সমঝোতার উপর।
এর আগে কখনও ইউএসসিআইআরএফ-এর পক্ষ থেকে কোনও দেশের সরকারি গোয়েন্দা সংস্থার বিরুদ্ধে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা আরোপের সুপারিশ করার দৃষ্টান্ত স্পষ্টভাবে সামনে আসেনি। সেই প্রেক্ষিতে ভারতের ‘রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং’ বা ‘র’ (RAW) -এর বিরুদ্ধে এমন সুপারিশ নিঃসন্দেহে এক ব্যতিক্রমী ঘটনা হিসেবে নজরে পড়ে। সাধারণত ইউএসসিআইআরএফ ব্যক্তি বা বেসরকারি সংগঠনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরামর্শ দিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ধর্মীয় স্বাধীনতা লঙ্ঘনের অভিযোগে তারা চীন, মায়ানমার কিংবা ইরানের একাধিক সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার পরামর্শ দিয়েছে, তবে কোনো দেশের গোটা একটি সরকারি সংস্থাকে নিষিদ্ধ করার দাবি এই প্রথম। এই কমিশনের প্রধান কাজ মূলত বিশ্বজুড়ে ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে সেই নিরিখে দেশভিত্তিক পরামর্শ প্রদান। এদের সুপারিশের পরিসর সাধারণত কোনও দেশকে ‘বিশেষ উদ্বেগের দেশ’ (Country of Particular Concern – CPC) হিসেবে চিহ্নিত করা অথবা ব্যক্তি বা সংগঠনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপে সীমাবদ্ধ থাকে। সেক্ষেত্রে ‘র’-এর মতো একটি গোয়েন্দা সংস্থার উপর সরাসরি নিষেধাজ্ঞার সুপারিশ নিঃসন্দেহে অভূতপূর্ব এবং বিস্ময়কর।
২০২৫ সালের ২৫ মার্চ প্রকাশিত ইউএসসিআইআরএফ-এর বার্ষিক প্রতিবেদনে ভারতকে কেন্দ্র করে এই সুপারিশ উঠে এসেছে। এই সময়ে একদিকে যেমন হরদীপ সিং নিজ্জর হত্যাকাণ্ড এবং গুরপতবন্ত সিং পান্নুনের ওপর হামলার ষড়যন্ত্রের তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া চলছিল, তেমনি অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে ‘শিখস ফর জাস্টিস’ (SFJ)-এর মতো সংগঠন ও মানবাধিকার সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে চাপও ছিল প্রবল। দীর্ঘদিন ধরেই ইউএসসিআইআরএফ ভারতের ধর্মীয় স্বাধীনতা লঙ্ঘন এবং সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ নিয়ে সমালোচনায় সরব ছিল, এবারের সুপারিশ সেই ধারাবাহিকতারই এক নতুন পর্যায়।
আন্তর্জাতিক কূটনীতির পরিসরে গোয়েন্দা সংস্থাগুলির ভূমিকা প্রায়শই আলোচনার কেন্দ্রে উঠে আসে, বিশেষ করে যখন তা অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের অভিযোগের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ‘র’ (RAW)— ভারতের বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা— তার কাজের স্বাভাবিক গোপনীয়তার কারণে বহুবার বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে, যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়নি। পাকিস্তান বহু বছর ধরেই অভিযোগ করে আসছে যে, ‘র’ তাদের অভ্যন্তরে গোপন অভিযান চালিয়ে থাকে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলিকে প্রশ্রয় দেয়। ২০১৬ সালে পাকিস্তানে কূলভূষণ জাধব নামের এক ভারতীয় নাগরিক গ্রেফতার হওয়ার পর সে অভিযোগ আরও ঘনীভূত হয়। পাকিস্তান দাবি করে, তিনি ‘র’-এর সক্রিয় এজেন্ট এবং বেলুচিস্তানে অস্থিরতা ছড়ানোর কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ভারত সরকার বরাবরই এই দাবি অস্বীকার করে জানায়, তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত নৌসেনা কর্মকর্তা এবং ব্যবসায়িক কারণে পাকিস্তানে ছিলেন। এই ঘটনাটি আন্তর্জাতিক মহলে বিতর্ক উসকে দেয় এবং ‘র’-এর কার্যকলাপ নিয়ে নানা প্রশ্ন তোলে।
১৯৮০-র দশকে শ্রীলঙ্কার তামিল বিদ্রোহী সংগঠন লিবারেশন টাইগার্স অফ তামিল ইলম (LTTE)-কে প্রশিক্ষণ ও সহায়তা দেওয়ার অভিযোগও এক সময় ‘র’-এর বিরুদ্ধে উঠেছিল। যদিও পরে ভারত সরকার এলটিটিই-এর বিরুদ্ধেই অবস্থান নেয় এবং তাদের মোকাবিলায় সামরিক পদক্ষেপ নেয়, তবুও এই পূর্ববর্তী সহযোগিতা শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ভারতের সম্পর্কে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে এবং গোয়েন্দা কার্যক্রম নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে এক বিতর্ক তৈরি করে।
আবার ২০২৩ সালে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো প্রকাশ্যে দাবি করেন, শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যার সঙ্গে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা জড়িত থাকতে পারে। এই অভিযোগ কানাডা-ভারত সম্পর্কের মধ্যে মারাত্মক টানাপোড়েন সৃষ্টি করে। যদিও ভারত সরকার এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয়, তবুও এটি ‘র’-কে ঘিরে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আরেকটি বিতর্কের জন্ম দেয়। এমনকি বাংলাদেশের মতো ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী রাষ্ট্রও একাধিকবার অভিযোগ তুলেছে যে, ‘র’ তাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে থাকে। নেপাল ও মালদ্বীপও সময়ে সময়ে একই অভিযোগ করেছে। যদিও অনেক সময়ই এসব অভিযোগ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই ধরে নেওয়া হয়, তবুও এগুলো ‘র’ (RAW)-এর আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তিকে অনিবার্যভাবেই প্রভাবিত করেছে।

ভারত-চিন যুদ্ধ (১৯৬২) এবং ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ (১৯৬৫)-এর পর ভারতের গোয়েন্দা পরিকাঠামোর দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই ১৯৬৮ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির উদ্যোগে ‘র’-এর প্রতিষ্ঠা হয়। সংস্থাটির মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত স্বার্থ সংরক্ষণ ও সেই সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ। যদিও এর কার্যক্রম সর্বদাই গোপনীয়, তবুও বিভিন্ন সময়ে ইতিহাসে এর প্রভাব স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশেষত পাকিস্তান ও চিনের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন, কাশ্মীর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের পরিস্থিতি, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা এবং দক্ষিণ এশিয়ার কৌশলগত ভারসাম্য রক্ষায় সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।
‘র’-এর ইতিহাসে একাধিক গোপন অভিযান আজ কিংবদন্তির মর্যাদা পেয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম ‘কালবৈশাখী অপারেশন’ নামে পরিচিত একটি কথিত মিশন। জনশ্রুতি অনুযায়ী, ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের প্রাক্কালে এবং যুদ্ধকালীন সময়ে এই অপারেশন পরিচালিত হয় পূর্ব পাকিস্তানে। মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করা, তাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সহায়তা প্রদান এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহই ছিল এই মিশনের মূল লক্ষ্য। ‘কালবৈশাখী’ নামটি এই অভিযানের সঞ্চালন-দক্ষতা এবং ধ্বংসাত্মক প্রভাবের প্রতীক হিসেবেই বেছে নেওয়া হয়েছিল। যদিও এটি কোনও একক মিশন ছিল না, বরং একাধিক গোপন তৎপরতার সম্মিলিত রূপ বলে মনে করা হয়। ধারণা করা হয়, কূটনৈতিক পরিচয় বা স্থানীয় সহযোগীদের মাধ্যমে ‘র’-এর এজেন্টরা কাজ চালিয়ে যান এবং ১৯৭১ সালের যুদ্ধে ভারতের বিজয়ে তা মুখ্য ভূমিকা রাখে।
এই সব ঘটনার আলোকে সাম্প্রতিক সময়ে ইউএসসিআইআরএফ-এর পক্ষ থেকে ‘র’-এর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার সুপারিশ যে এক ঐতিহাসিক পর্বের সূচক, তা বলা চলে নিঃসংশয়ে। একদিকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের নিরাপত্তা ও কৌশলগত স্বার্থ রক্ষায় একটি সংস্থার ভূমিকা, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের প্রশ্নে সেই সংস্থার জবাবদিহি— এই দুইয়ের সংঘর্ষে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, তা শুধু ভারত বা যুক্তরাষ্ট্র নয়, গোটা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে রাষ্ট্র, নিরাপত্তা ও ন্যায়ের দ্বন্দ্ব নিয়ে।
১৯৮৪ সালে চালানো ‘অপারেশন মেঘদূত’ ছিল ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর, বিশেষ করে সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনীর এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ, যার মূল লক্ষ্য ছিল সিয়াচেন হিমবাহের দখল কায়েম করা। যদিও ‘রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং’— বা সংক্ষেপে ‘র’— সরাসরি কোনও সামরিক অভিযানে অংশ নেয় না, তবু এই অভিযানের পেছনে এর গোয়েন্দা তথ্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ‘র’-এর এক গোপন নজরদারিতে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী সল্টোরো রিজ দখলের প্রস্তুতি নিচ্ছে, এমন তথ্য ভারতীয় বাহিনী আগেভাগেই জানতে পারে। লন্ডনের এক সরবরাহকারীর মাধ্যমে পাকিস্তান আর্কটিক অঞ্চলের উপযোগী সরঞ্জাম সংগ্রহ করছে— এই খবরও প্রথম আসে ‘র’-এর মাধ্যমেই। উক্ত সরবরাহকারী ভারতীয় বাহিনীকেও সরঞ্জাম সরবরাহ করতেন, ফলে এই তথ্য ছিল অবিশ্বাস্যরকম কার্যকর। ভারতের প্রতিক্রিয়া ছিল দ্রুত এবং পরিকল্পিত। এর ফলে সিয়াচেন হিমবাহে পাকিস্তানের আগেই ভারতের পতাকা ওড়ে।
১৯৮৬-৮৭ সালে সংঘটিত ‘অপারেশন ফালকন’-এর ক্ষেত্রেও ‘র’ (RAW) প্রমাণ করে দেয়, শুধু সীমান্ত নয়, কৌশলগত তথ্য সংগ্রহেও তাদের ক্ষমতা কতটা গভীর। সুমদোরং চু সংকটের সময় চিনা বাহিনী অরুণাচল ও সিকিম সীমান্তে অগ্রসর হচ্ছিল। এই অবস্থায় ‘র’ চিনা সেনাদের গতিবিধি, তাদের সরবরাহ চক্র এবং সুমদোরং চু-তে সামরিক চৌকি স্থাপনের পরিকল্পনার সংবাদ যথাসময়ে ভারতীয় বাহিনীর কাছে পৌঁছে দেয়। বিশেষ করে তিব্বত অঞ্চলে থাকা তাদের স্থানীয় সংযোগ ও প্রবাসী তিব্বতিদের মাধ্যমে সংগৃহীত এই তথ্য ভারতীয় প্রতিরক্ষাকে নির্ভুল প্রতিক্রিয়া জানাতে সাহায্য করে। চিনের কৌশলগত আগ্রাসনের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্ভাব্য সহযোগিতার বিষয়েও ‘র’ সতর্ক ছিল, যা ভারতের প্রতিরক্ষা নীতিতে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।
২০১৪ সালের পর ‘র’-এর নীতিতে যে গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর এসেছে, তা মূলত আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, প্রযুক্তির বিবর্তন এবং ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের প্রতিফলন। নরেন্দ্র মোদি সরকারের অধীনে ভারতের গোয়েন্দা কাঠামোয় প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ‘র’ সাইবার গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা শাখায় নতুনভাবে সক্রিয় হয়। বিশেষ করে পাকিস্তান ও চিনের তরফে সাইবার হামলার সম্ভাব্য হুমকির প্রেক্ষিতে ‘র’ তথ্য বিশ্লেষক, সাইবার বিশেষজ্ঞ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কাজ করা প্রযুক্তিবিদদের সক্রিয়ভাবে কাজে লাগাতে শুরু করে।
২০১৯ সালের পুলওয়ামা হামলার পরে পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি গোষ্ঠীর সাইবার যোগাযোগ নেটওয়ার্ক চিহ্নিত করতে ‘র’ (RAW) যে কার্যকরী ভূমিকা নেয়, তা গোয়েন্দা সংস্থার প্রচলিত সীমা অতিক্রম করে। স্যাটেলাইট বিশ্লেষণ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে সন্দেহজনক ডেটা ট্র্যাকিং, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বিশ্লেষণ— এই সবকিছুই মিলে এক নতুন ধরনের গোয়েন্দা কাঠামোর উন্মোচন ঘটায়।
‘লুক ইস্ট’ এবং ‘নেবারহুড ফার্স্ট’ নীতির বাস্তবায়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ‘র’ (RAW) -এর উপস্থিতিও আরও দৃঢ় হয়েছে। আফগানিস্তানে তালিবানের পুনরুত্থান বা মায়ানমারে রোহিঙ্গা সংকটের সময় এই অঞ্চলে ‘র’ (RAW) -এর গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক বিস্তৃত হয়। একই সঙ্গে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কায় চিনা প্রভাব মোকাবিলায় নানা গোপন কৌশল নেওয়া হয়, যা এই অঞ্চলে ভারতের কৌশলগত অবস্থানকে রক্ষায় সহায়ক হয়।
পূর্বে ‘র’ (RAW) -এর কার্যক্রম যেখানে মূলত পাকিস্তান ও চিনের উপর কেন্দ্রীভূত ছিল, এখন তা ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজির অন্তর্গত বৃহত্তর পরিসরে ছড়িয়ে পড়েছে। ২০১৯ সালে স্যমন্ত কুমার গোয়েল ‘র’ (RAW) -এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেন। পাঞ্জাবে সন্ত্রাসদমন এবং বালাকোট অপারেশনের পরিকল্পনায় তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। এরপর ২০২৩ সালে দায়িত্ব গ্রহণ করেন রবি সিনহা, যিনি প্রযুক্তিনির্ভর গোয়েন্দা ব্যবস্থায় পারদর্শী। নতুন নেতৃত্বের অধীনে ‘র’-এর কর্মপদ্ধতিতে যে দৃশ্যমান রূপান্তর ঘটেছে, তা শুধু কৌশলগত নয়, দৃষ্টিভঙ্গিতেও এক বিপুল পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে।
এই নতুন কৌশলের বাস্তব রূপ দেখা যায় ২০২৩ সালে কানাডায় শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে। অভিযোগ উঠেছে, এই ঘটনার পেছনে ভারতের সরকারি গোয়েন্দা সংস্থার হাত রয়েছে। যদিও ভারত এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে, তবে এতদ্বারা বোঝা যায়, ‘র’ (RAW) এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি আক্রমণাত্মক, সাহসী এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে সক্রিয়।
সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যাচ্ছে। পাকিস্তানভিত্তিক সংগঠন ছাড়াও বৈশ্বিক সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক যেমন ISIS-এর উপরও ‘র’ (RAW) নজরদারি বাড়িয়েছে। শুধু তথ্য সংগ্রহে নয়, এখন ‘র’ (RAW) আগাম পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রেও সচেষ্ট। ২০১৯ সালের বালাকোট হামলা তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয় এবং সহযোগিতাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের CIA, ইজরায়েলের Mossad এবং ব্রিটেনের MI6-এর সঙ্গে ‘র’ (RAW) -এর তথ্য বিনিময় ও যৌথ অভিযানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে ২০২১ সালে আফগানিস্তানে তালিবানের ক্ষমতা দখলের পর। এই সমন্বয় ‘র’ (RAW) -কে শুধু দক্ষিণ এশিয়ায় নয়, গোটা বিশ্বে একটি প্রভাবশালী গোয়েন্দা সংস্থার মর্যাদা দিয়েছে।
২০১৪ সালের পর ‘র’ (RAW) -এর এই রূপান্তর প্রযুক্তির ব্যবহারে দক্ষতা, কৌশলগত বিস্তৃতি, নেতৃত্বের কার্যকর দৃষ্টিভঙ্গি এবং সন্ত্রাস দমন কৌশলে আগ্রাসী মনোভাবের মাধ্যমে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। তবে এই পরিবর্তনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বিতর্ক, প্রশ্ন এবং আন্তর্জাতিক টানাপড়েন। বিশেষত পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের জটিলতা এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর অভিযোগ, ‘র’ (RAW) -এর ভবিষ্যৎ পথচলায় একাধিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। তবুও, এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, বর্তমান বিশ্বে কৌশল, তথ্য ও প্রযুক্তির যুগে ‘র’ (RAW) এক বহুমাত্রিক শক্তি হয়ে উঠেছে— একাধারে নিরব, নির্ভুল এবং প্রতিক্রিয়াশীল।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ‘ইউএস কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম’ বা ইউএসসিআইআরএফ-এর পক্ষ থেকে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা ‘র’ (RAW) -এর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের সুপারিশ আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক পরিসরে এক নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকাণ্ড নিয়ে সাধারণত আন্তর্জাতিক মঞ্চে সরাসরি মন্তব্য করা হয় না, সেখানে এই পদক্ষেপ ‘র’ (RAW) -এর ভাবমূর্তি এবং ভারত-আমেরিকা সম্পর্কের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে তীব্র বৌদ্ধিক পর্যালোচনার অবকাশ তৈরি করেছে।
অনেক পর্যবেক্ষক মনে করছেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সহযোগিতার পরিসর যেভাবে বিস্তৃত হয়েছে, বিশেষ করে মার্কিন CIA, ইজরায়েলের মোসাদ এবং ব্রিটেনের MI6-এর সঙ্গে ‘র’ (RAW) -এর সহযোগিতা যেভাবে ঘনিষ্ঠ হয়েছে, তা ভারত-আমেরিকা কৌশলগত সম্পর্কের গভীরতাকেই প্রতিফলিত করে। কিন্তু ইউএসসিআইআরএফ-এর এই সুপারিশ সেই ইতিবাচক চিত্রে ছায়া ফেলতে পারে। ২০২৩ সালে কানাডায় শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যাকাণ্ড এবং আমেরিকায় গুরপতবন্ত সিং পান্নুনকে হত্যার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার ঘটনায় ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তা বিকাশ যাদবের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ এই সুপারিশের প্রেক্ষাপট গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ফলে আন্তর্জাতিক পরিসরে ‘র’-এর গোপনীয়তা, নির্ভরযোগ্যতা এবং কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, যা সংস্থাটিকে একটি বিতর্কিত চরিত্রে চিহ্নিত করতে পারে।

এই প্রস্তাবের ফলে কয়েকটি দিক থেকে ‘র’ (RAW) -এর আন্তর্জাতিক অবস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। প্রথমত, সংস্থাটিকে আইনের ঊর্ধ্বে ও অতিরিক্ত আগ্রাসী হিসেবে তুলে ধরা হলে, পশ্চিমি গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সঙ্গে পারস্পরিক আস্থা বিনিময়ে টান পড়তে পারে। CIA কিংবা MI6-এর মতো সংস্থাগুলি ‘র’-এর সঙ্গে তথ্য আদানপ্রদানে অনীহা প্রকাশ করতে পারে, কারণ এ ধরনের অভিযোগ সংস্থাটির বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে।
দ্বিতীয়ত, দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে ভারতের প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রগুলি এই পরিস্থিতিকে ভারতের বিরুদ্ধে প্রচারে ব্যবহার করতে পারে। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই বহুবার ‘র’ (RAW) -এর বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলেছে; এই প্রস্তাব তাদের সেই দাবিকে আরও জোরদার করতে সহায়তা করতে পারে এবং ভারতের আঞ্চলিক নৈতিক নেতৃত্বের দাবিকে দুর্বল করে তুলতে পারে।
তৃতীয়ত, গোয়েন্দা কার্যক্রমের গোপন স্বভাবের কারণে এর কর্মকর্তাদের মনোবলে প্রভাব পড়তে পারে। যদি আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার সম্ভাবনা মাথার উপর ঝুলে থাকে, তবে তারা আগের মতো স্বাধীনভাবে, সাহসের সঙ্গে পদক্ষেপ নিতে সংকোচ বোধ করতে পারেন, যার ফলে গোয়েন্দা কর্মকাণ্ডের গতিশীলতা ও কার্যকারিতাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
তবে, এই সম্ভাব্য ক্ষতির পরিসর সীমিত বলেই মনে করেন অধিকাংশ বিশ্লেষক। কারণ ইউএসসিআইআরএফ-এর সুপারিশ বাধ্যতামূলক নয় এবং মার্কিন প্রশাসন তা গ্রহণ করবে না বলেই অধিক সম্ভাবনা রয়েছে। এর অন্যতম কারণ, ভারত বর্তমানে চিনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের এক কৌশলগত প্রধান অংশীদার, এবং এই কৌশলগত বাস্তবতা মানবাধিকার সম্পর্কিত উদ্বেগের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
এই সুপারিশ ভারত-আমেরিকা সম্পর্কের ওপর স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদি উভয় রকম প্রভাব ফেলতে পারে। স্বল্পমেয়াদে, দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ভারত ইতিমধ্যে ইউএসসিআইআরএফ-এর প্রতিবেদনকে ‘পক্ষপাতদুষ্ট’ এবং ‘প্রত্যাখ্যানযোগ্য’ বলে বিবৃতি দিয়েছে। এই ধরণের প্রতিক্রিয়া দুই দেশের পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিতে পারে। অথচ ২০১৪ সালের পর থেকে এই সম্পর্ক নানা দিক থেকে গভীর হয়েছে—আফগানিস্তানে তালিবান পুনরুত্থানের সময় পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সঙ্গে সমন্বয়, বালাকোট হামলার মতো অভিযানে যুক্তরাষ্ট্রের পরোক্ষ সমর্থন—এইসবের মধ্য দিয়েই তা পরিস্ফুট হয়েছে।
তবে এই মুহূর্তে যদি মার্কিন প্রশাসন নীরব থাকে বা কোনোভাবে সুপারিশটিকে সমর্থন করে, তবে ভারত একে যুক্তরাষ্ট্রের ‘দ্বিমুখী নীতি’ হিসেবে দেখতে পারে। বিশেষ করে যদি মার্কিন কংগ্রেস বা বিচার বিভাগ এই প্রস্তাব নিয়ে সোচ্চার হয়, তাহলে সেটা দুই দেশের সম্পর্কের মধ্যে নতুন চাপ সৃষ্টি করতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে, এই চাপ ভারত-আমেরিকার কৌশলগত বন্ধুত্বকেও বিপর্যস্ত করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র যদি ‘র’-এর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, তবে তা শুধু একটি সংস্থাকে লক্ষ্য করে নয়, বরং ভারতের গোয়েন্দা কাঠামো এবং কৌশলগত সক্ষমতাকে দুর্বল করার সমার্থক হিসেবে বিবেচিত হবে। এই পরিস্থিতিতে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চিনের বিরুদ্ধে যৌথ কৌশল বাস্তবায়নও ব্যাহত হতে পারে।
তবুও বিশ্লেষকদের একটি বড় অংশ বিশ্বাস করেন, এমন নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ, কারণ অতীতেও আমেরিকা ভারতের কৌশলগত গুরুত্বের কারণে মানবাধিকার বা আন্তর্জাতিক আইনের অভিযোগকে পাশে সরিয়ে রেখেছে। ২০২২ সালে রাশিয়ার ‘এস-৪০০’ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা কেনার ক্ষেত্রে CAATSA আইন অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ার কথা থাকলেও, যুক্তরাষ্ট্র ভারতের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করেছে। সেই দৃষ্টান্ত এই পরিস্থিতিতেও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।
তবে, এই সুপারিশ ভারতের জন্য একটি বার্তা— যে আন্তর্জাতিক মঞ্চে কার্যক্রম পরিচালনার সময় স্বচ্ছতা, আন্তর্জাতিক আইন এবং কূটনৈতিক সংবেদনশীলতার প্রতি যত্নবান হতে হবে। একদিকে, ভারত চাইবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গোয়েন্দা সহযোগিতা বজায় রাখতে; অন্যদিকে, বিদেশে নিজস্ব স্বার্থ রক্ষার্থে ‘র’ (RAW) -এর অভিযানের পরিসর ও প্রক্রিয়াতেও ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে।

ভারতের প্রতিক্রিয়া এই প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যদি ভারত এই ঘটনাকে মার্কিন অভ্যন্তরীণ রাজনীতির অনুষঙ্গ হিসেবে বিচার করে এবং তাৎপর্যপূর্ণ কূটনৈতিক বার্তা দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে পারে, তবে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষয়রেখা থামানো সম্ভব। কিন্তু যদি প্রতিক্রিয়া প্রতিশোধমূলক হয়— যেমন গোয়েন্দা সহযোগিতা কমানো কিংবা তথ্য আদানপ্রদানে অনিচ্ছা— তবে তা দীর্ঘমেয়াদে ভারত-আমেরিকা কৌশলগত অংশীদারিত্বে ছায়া ফেলতে পারে।
এই প্রেক্ষাপটে বলা যায়, ইউএসসিআইআরএফ-এর সুপারিশ যদিও ‘র’ (RAW) -এর আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তিতে তাৎক্ষণিক কিছু নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, তবু ভারত ও আমেরিকার সম্পর্কের কৌশলগত গভীরতা ও বাস্তববাদী স্বার্থ শেষপর্যন্ত এই প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হবে। তবে, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার এবং ‘র’ (RAW) যদি গোয়েন্দা কার্যক্রমে আরও পরিশীলন, সংবেদনশীলতা এবং আন্তর্জাতিক আইনগত পরিমণ্ডলে চলাফেরার দিকে মনোনিবেশ করে, তবে ভবিষ্যতের বিতর্ক অনেকটাই এড়ানো সম্ভব হতে পারে।

 নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা
নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা