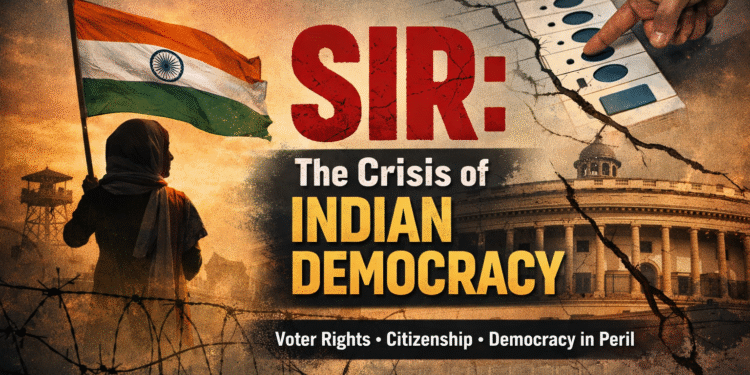লিখেছেনঃ মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম
রাষ্ট্র যখন কোনো নীতিকে “প্রশাসনিক প্রক্রিয়া” বলে ঘোষণা করে, তখন সেটি প্রায়শই নাগরিককে আশ্বস্ত করার ভাষা হয়। প্রশাসনিক শব্দভাণ্ডার নিরীহ শোনায়—যেন এতে কোনো রাজনীতি নেই, কোনো ক্ষমতা নেই, কোনো উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রে প্রশাসনিক প্রক্রিয়াগুলোই সবচেয়ে রাজনৈতিক, কারণ সেগুলো প্রশ্নহীনভাবে প্রয়োগ করা যায়। Special Intensive Revision বা এসআইআর সেই ধরনেরই একটি প্রক্রিয়া, যা বাহ্যিকভাবে ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রযুক্তিগত কাজ বলে প্রচারিত হলেও বাস্তবে নাগরিকত্ব, ভোটাধিকার এবং রাজনৈতিক অস্তিত্ব পুনর্নির্ধারণের এক গভীর রাষ্ট্রীয় কৌশলে পরিণত হয়েছে।
ভোটার তালিকা আধুনিক গণতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিলগুলোর একটি। এই তালিকাই নাগরিককে রাষ্ট্রের সামনে দৃশ্যমান করে তোলে। ভারতের সংবিধান নাগরিকত্বের সঙ্গে ভোটাধিকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত করেনি, কিন্তু বাস্তবে ভোটার তালিকাই নাগরিকের অস্তিত্বের সবচেয়ে কার্যকর প্রমাণ। কারণ রাষ্ট্রীয় সুযোগ, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব, এমনকি সামাজিক স্বীকৃতিও এই তালিকার ওপর নির্ভরশীল। ফলে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া মানে শুধু ভোট না দিতে পারা নয়; এর মানে রাষ্ট্রের চোখে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া। এই অদৃশ্যকরণ কোনো আকস্মিক প্রশাসনিক ভুল নয়, বরং একটি কাঠামোগত প্রক্রিয়া।
এসআইআর-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর সময় ও প্রয়োগ। ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই লক্ষ্য করা যায়, বড় নির্বাচন বা রাজনৈতিক ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসের আগে এই প্রক্রিয়া তীব্র হয়। ২০০৪, ২০০৯, ২০১৪, ২০১৯ এবং ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে বিভিন্ন রাজ্যে “ইনটেনসিভ রিভিশন” চালানো হয়েছে। যদি এটি কেবল প্রশাসনিক সংশোধনের কাজ হতো, তবে তা নিয়মিত হতো, ধারাবাহিক হতো, রাজনৈতিক সময়ের সঙ্গে যুক্ত হতো না। কিন্তু বাস্তবে এসআইআর সবসময়ই রাজনৈতিক উত্তেজনার সময় ফিরে আসে। এই সময়কাল নিজেই প্রমাণ করে যে প্রক্রিয়াটি নিরপেক্ষ নয়।
নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে প্রায় ৩ কোটির বেশি ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। এই বাদ পড়াদের বড় অংশই কখনো জানতে পারেননি যে তাঁদের নাম বাদ গেছে। অনেকেই ভোটকেন্দ্রে গিয়ে প্রথমবার বুঝেছেন যে তাঁরা আর ভোটার নন। এই পরিস্থিতি প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়; এটি প্রশাসনিক সহিংসতা। কারণ রাষ্ট্র নাগরিককে না জানিয়ে তাঁর অধিকার কেড়ে নিচ্ছে, এবং সেই অধিকার ফেরত পাওয়ার পথও জটিল করে তুলছে।
এসআইআর-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বিপজ্জনক দিক হলো Booth Level Officer (BLO)-এর ভূমিকা। এই অস্থায়ী ও কম প্রশিক্ষিত কর্মচারীদের হাতে নাগরিকের রাজনৈতিক ভাগ্য তুলে দেওয়া হয়। BLO কোনো বাড়িতে গিয়ে কাউকে না পেলে, বা প্রতিবেশীর কথায় সন্দেহ হলে, নাগরিককে “অনুপস্থিত” বা “অযোগ্য” বলে চিহ্নিত করা হয়। এই একটি চিহ্নই নাগরিকের রাজনৈতিক জীবনের সমাপ্তি ঘটাতে পারে। এখানে রাষ্ট্র নাগরিকের অস্তিত্ব প্রমাণ করে না; নাগরিককে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হয়। এই উল্টো সম্পর্কই আধুনিক কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্য।
এসআইআর-এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে সেই সব জনগোষ্ঠীর ওপর, যাদের জীবন রাষ্ট্রীয় নথির বাইরে। পরিযায়ী শ্রমিকেরা মাসের পর মাস অন্য রাজ্যে থাকেন। শহরের বস্তিবাসীরা ঘন ঘন ঠিকানা বদলান। গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের কাছে জন্মসনদ, বয়সের নথি বা বাসস্থান প্রমাণ নেই। মুসলিম নারীদের নাম প্রায়ই স্বামীর বা বাবার নামের সঙ্গে মেলেনা। আদিবাসী সমাজের মানুষ সরকারি কাগজে বিশ্বাস করেন না। এই সব বাস্তবতা রাষ্ট্র জানে, তবুও এসআইআর-এর নকশা এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে এই মানুষরাই সবচেয়ে বেশি বাদ পড়ে। এটি প্রশাসনিক নয়, কাঠামোগত বৈষম্য।
এসআইআর-এর মাধ্যমে রাষ্ট্র নাগরিকের জীবনের বাস্তবতাকে অপরাধে রূপান্তর করে। কাজের জন্য বাইরে থাকা অপরাধ, ঘন ঘন ঠিকানা বদলানো অপরাধ, নথি না থাকা অপরাধ। নাগরিকের জীবনধারা রাষ্ট্রের সন্দেহে পরিণত হয়। এই সন্দেহই রাষ্ট্রের অস্ত্র। কারণ সন্দেহের ভিত্তিতে রাষ্ট্র কাউকে গ্রেপ্তার না করেও তাঁর অধিকার কেড়ে নিতে পারে। এসআইআর এই কাজটিই করে—নীরবে, আইনের ভাষায়, প্রশাসনিক কাগজে।
এই প্রক্রিয়া কেবল রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্পর্ক বদলায় না; নাগরিকদের মধ্যকার সম্পর্কও বদলে দেয়। BLO যখন প্রতিবেশীর কাছ থেকে তথ্য নেয়, তখন সামাজিক বিদ্বেষ রাষ্ট্রীয় নথিতে ঢুকে পড়ে। মুসলমান প্রতিবেশী সন্দেহজনক হয়ে ওঠে, ভাড়াটে সন্দেহজনক হয়, একা থাকা নারী সন্দেহের চোখে দেখা হয়। সামাজিক বিভাজন রাষ্ট্রীয় বৈষম্যে রূপ নেয়। এসআইআর তাই কেবল ভোটার তালিকা সংশোধন নয়; এটি সমাজ পুনর্গঠনের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া।
নারীদের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া আরও ভয়ংকর। একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় নারীদের নাম বাদ পড়ার হার পুরুষদের তুলনায় বেশি, বিশেষত মুসলিম ও দরিদ্র সমাজে। নারীর নাম ভুল, বয়সের নথি নেই, ঠিকানা পরিবর্তন হয়েছে—এই সব অজুহাতে তাঁদের নাম বাদ পড়ে যায়। পরিবারে পুরুষের নাম থেকে গেলেও নারীর নাম মুছে যায়। রাষ্ট্র এখানে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে নীতিতে রূপান্তর করে।
এসআইআর-এর রাজনৈতিক ফলাফল নির্বাচনেই সবচেয়ে স্পষ্ট হয়। ভারতের বহু নির্বাচনে জয়-পরাজয়ের ব্যবধান কয়েক হাজার ভোটের বেশি নয়। সেখানে যদি লক্ষ লক্ষ মানুষ ভোটার তালিকায় না থাকে, তবে নির্বাচনের ফল আর জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন থাকে না। এটি হয়ে ওঠে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ফল। এই কারণেই এসআইআর বিরোধী রাজনীতির জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক অস্ত্র। বিরোধী দল ভোটের ওপর নির্ভর করে, প্রশাসনের ওপর নয়। ভোটার কমলে বিরোধী দুর্বল হয়, রাষ্ট্র শক্তিশালী হয়।
এই প্রক্রিয়াকে বহু গবেষক “নীরব ভোটার দমন” বা silent voter purge বলে অভিহিত করেছেন। কারণ এখানে কোনো আইন পরিবর্তন হয় না, কোনো জরুরি অবস্থা ঘোষণা হয় না, কোনো বড় খবর হয় না। কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ ধীরে ধীরে ভোটাধিকার হারায়। এই নীরবতা রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সাফল্য, কারণ প্রতিরোধ তৈরি হওয়ার আগেই ক্ষতি সম্পন্ন হয়।
ভারতের এসআইআরকে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দেখলে এটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। যুক্তরাষ্ট্রে ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে আফ্রিকান-আমেরিকান ও লাতিনো ভোটারদের বাদ দেওয়া হয়েছে। মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের ভোটার তালিকা মুছে দিয়ে নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের ভোটাধিকার সংকুচিত করা হয়েছিল তালিকার মাধ্যমে। ইতিহাস দেখায়—তালিকা দিয়ে শুরু হয়, অধিকার দিয়ে শেষ হয়।
ভারতের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া আরও বিপজ্জনক, কারণ এটি NRC ও CAA বিতর্কের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাগরিকত্বকে কাগজনির্ভর করে তুলছে। এসআইআর-এর মাধ্যমে রাষ্ট্র নাগরিককে বলছে—তুমি নাগরিক, যদি তুমি কাগজ দেখাতে পারো। এই শর্ত সংবিধানের মৌলিক ধারণার বিপরীত, যেখানে নাগরিকত্ব জন্মসূত্রে ও সমান অধিকারে নির্ধারিত।
এসআইআর তাই প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নয়; এটি রাষ্ট্রীয় অস্ত্র। এটি নাগরিককে দুর্বল করে, রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করে। এটি গণতন্ত্রকে সংখ্যায় পরিণত করে, কিন্তু মানবিকতা থেকে খালি করে দেয়। ভোটার তালিকা এখানে কেবল তালিকা নয়; এটি নাগরিকত্বের সীমান্ত। আর সেই সীমান্তের পাহারাদার রাষ্ট্র।
রাষ্ট্রের ক্ষমতা যখন প্রশাসনিক নিয়মের আড়ালে লুকিয়ে থাকে, তখন সেটিই সবচেয়ে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। কারণ নাগরিক তখন বুঝতেই পারে না, তার বিরুদ্ধে কী ঘটছে। এসআইআর ঠিক এই ধরনের ক্ষমতার প্রযুক্তি, যা দৃশ্যমান দমন নয়, বরং অদৃশ্য বর্জনের মাধ্যমে কাজ করে। নাগরিককে রাষ্ট্রের শত্রু বানাতে হয় না—শুধু তাকে তালিকা থেকে বাদ দিলেই যথেষ্ট। এই বাদ দেওয়ার মুহূর্তে কোনো শব্দ হয় না, কোনো সংবাদ হয় না, কোনো প্রতিবাদ হয় না; কিন্তু নাগরিকের রাজনৈতিক জীবন শেষ হয়ে যায়।
এসআইআর-এর সবচেয়ে মৌলিক সমস্যা হলো এটি নাগরিকত্বকে শর্তাধীন করে তোলে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব জন্মগত ও সমান অধিকারের ভিত্তিতে স্বীকৃত, কিন্তু এসআইআর সেই ধারণাকে উল্টে দেয়। এখানে নাগরিককে বারবার প্রমাণ করতে হয় যে সে নাগরিক। রাষ্ট্র আর নাগরিককে বিশ্বাস করে না; রাষ্ট্র সন্দেহ করে। এই সন্দেহই আধুনিক কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি—যেখানে প্রশাসনিক নিয়মের মাধ্যমে রাজনৈতিক বর্জন ঘটানো হয়।
এসআইআর এই সন্দেহকে প্রাতিষ্ঠানিক করে। “অনুপস্থিত”, “অপ্রমাণিত”, “স্থানান্তরিত”—এই শব্দগুলো প্রশাসনিক মনে হলেও এগুলো রাজনৈতিক, কারণ এই শব্দের ভিত্তিতেই নাগরিকের অধিকার কাটা হয়। একজন শ্রমিক কাজের জন্য বাইরে থাকলে সে অনুপস্থিত, একজন নারী বিয়ের পরে ঠিকানা বদলালে সে স্থানান্তরিত, একজন গৃহহীন মানুষ ঠিকানা না থাকায় অপ্রমাণিত হয়ে যায়। রাষ্ট্র জীবনের বাস্তবতাকে অপরাধে রূপান্তর করে, তারপর সেই অপরাধের শাস্তি দেয়—ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে।
এই প্রক্রিয়ায় নাগরিকের বিরুদ্ধে প্রতিবেশীকেও ব্যবহার করা হয়। BLO যখন কোনো বাড়িতে গিয়ে কাউকে না পায়, তখন সে প্রতিবেশীর বক্তব্যের উপর নির্ভর করে। কিন্তু সমাজে প্রতিবেশী সম্পর্ক নিরপেক্ষ নয়—এখানে ধর্ম, জাত, শ্রেণি ও লিঙ্গভিত্তিক বিদ্বেষ কাজ করে। সেই বিদ্বেষ যখন প্রশাসনিক নথিতে ঢুকে পড়ে, তখন সামাজিক বৈষম্য রাষ্ট্রীয় বৈষম্যে পরিণত হয়।
নারীদের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া আরও নির্মম। ভারতের সামাজিক বাস্তবতায় নারীর পরিচয় প্রায়শই স্বামীর বা বাবার সঙ্গে যুক্ত। বিয়ে হলে ঠিকানা বদলায়, নামের বানান বদলায়, বয়সের নথি মেলে না। এই সব “ভুল” রাষ্ট্রের চোখে অপরাধ হয়ে ওঠে। একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় নারীদের নাম বাদ পড়ার হার পুরুষদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি, বিশেষত মুসলিম ও দরিদ্র সমাজে। এসআইআর তাই কেবল রাজনৈতিক নয়, লিঙ্গভিত্তিক দমনও।
এসআইআর-এর রাজনৈতিক তাৎপর্য এখানেই শেষ নয়। এই প্রক্রিয়া বিরোধী রাজনীতিকে কাঠামোগতভাবে দুর্বল করে। ভারতের নির্বাচনী সমাজতত্ত্ব দেখায়, দরিদ্র ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সাধারণত বিরোধী দলকে ভোট দেয়। ফলে এই জনগোষ্ঠীর ভোটার তালিকা সংকুচিত করা মানে বিরোধী ভোট কমানো। এটি প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার ছদ্মবেশে পরিচালিত রাজনৈতিক প্রকৌশল।
নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা এই প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সংবিধান অনুযায়ী কমিশন স্বাধীন প্রতিষ্ঠান, কিন্তু তার কার্যপ্রণালী সম্পূর্ণভাবে প্রশাসনিক কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল। BLO, জেলা প্রশাসন, রাজ্য সরকার—সবই নির্বাহী ক্ষমতার অংশ। বহু আইনবিদ দেখিয়েছেন, কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা বাস্তবে কাঠামোগতভাবে সীমাবদ্ধ, এবং এই সীমাবদ্ধতাই এসআইআর-এর মতো প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিণত করে।
আদালতের ভূমিকা এই প্রক্রিয়ায় প্রায় অদৃশ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদালত ভোটার তালিকা সংশোধনকে প্রশাসনিক বিষয় বলে বিবেচনা করে এবং হস্তক্ষেপ করতে চায় না। ফলে নাগরিক আইনি আশ্রয় থেকেও বঞ্চিত হন। প্রশাসন, আদালত ও মিডিয়ার যৌথ নীরবতা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে প্রশ্নহীন করে তোলে।
এসআইআর-এর সঙ্গে ডিজিটাল প্রযুক্তি যুক্ত হলে এই পরিস্থিতি আরও ভয়ংকর হবে। আধার, বায়োমেট্রিক ডেটা, মুখচেনা প্রযুক্তি, এআই-ভিত্তিক তালিকা বিশ্লেষণ—এই সব মিলিয়ে নাগরিক সম্পূর্ণভাবে ডেটায় রূপান্তরিত হবে। তখন আর BLO-এর দরকার হবে না; অ্যালগরিদম ঠিক করবে কে নাগরিক, কে নয়। প্রযুক্তিগত ভুল তখন মানবিক ট্র্যাজেডিতে পরিণত হবে।
এসআইআর তাই প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নয়, রাষ্ট্রীয় অস্ত্র। এটি এমন এক অস্ত্র, যা আইন ভাঙে না, কিন্তু সংবিধানের আত্মাকে ক্ষতবিক্ষত করে। এটি এমন এক অস্ত্র, যা রক্তপাত করে না, কিন্তু রাজনৈতিক জীবন শেষ করে। ভোটার তালিকা এখানে কেবল তালিকা নয়—এটি নাগরিকত্বের সীমান্ত। আর সেই সীমান্তের পাহারাদার রাষ্ট্র।
এসআইআর কী?
রাষ্ট্র যখন কোনো প্রক্রিয়াকে “প্রশাসনিক” বলে চিহ্নিত করে, তখন সেই শব্দটিই প্রথম বিভ্রান্তি তৈরি করে। প্রশাসনিক শব্দভাণ্ডার নিরীহ শোনায়, যেন সেখানে কোনো রাজনীতি নেই, কোনো ক্ষমতা নেই, কোনো উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রে প্রশাসনিক প্রক্রিয়াগুলোই সবচেয়ে রাজনৈতিক, কারণ এগুলো প্রশ্নহীনভাবে প্রয়োগ করা যায়, এবং এগুলোকে চ্যালেঞ্জ করা সবচেয়ে কঠিন। Special Intensive Revision বা এসআইআর সেই ধরনেরই একটি প্রক্রিয়া—যার নাম প্রশাসনিক, কিন্তু যার কার্যকারিতা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে।
নির্বাচন কমিশনের ভাষায় এসআইআর হলো ভোটার তালিকা বিশেষভাবে শুদ্ধ করার একটি প্রক্রিয়া। মৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া, স্থানান্তরিত ভোটারদের সংশোধন করা, দ্বৈত নাম মুছে ফেলা—এই হলো ঘোষিত উদ্দেশ্য। এই সংজ্ঞার ভেতরে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্তু সমস্যা শুরু হয় তখন, যখন এই ঘোষিত উদ্দেশ্যের সঙ্গে বাস্তব প্রয়োগের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ এসআইআর কেবল কী, তা জানলেই যথেষ্ট নয়; তার চেয়ে জরুরি প্রশ্ন হলো—এসআইআর কী নয়।
এসআইআর কোনো সাধারণ রিভিশন নয়। ভারতীয় নির্বাচন ব্যবস্থায় নিয়মিত summary revision হয়, যেখানে নাগরিক নিজে আবেদন করে, তথ্য সংশোধন করে, নাম যোগ করে। এটি একটি অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া। কিন্তু এসআইআর সেই কাঠামোর বাইরে দাঁড়ানো একটি ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা, যেখানে উদ্যোগ নেয় রাষ্ট্র, নাগরিক নয়। এখানে যাচাই শুরু হয় নাগরিকের সম্মতি ছাড়াই, উপস্থিতি ছাড়াই, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে জানানো ছাড়াই। এই বৈশিষ্ট্যই এসআইআর-কে প্রশাসনিক কাজের সীমা পেরিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োগে পরিণত করে।
এসআইআর-এর মাধ্যমে রাষ্ট্র নাগরিককে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। সাধারণ রিভিশনে নাগরিক আবেদনকারী, এসআইআর-এ নাগরিক অভিযুক্ত। রাষ্ট্র যাচাই করে—সে আদৌ আছে কি না, সে এখানেই থাকে কি না, সে যোগ্য কি না। এই যাচাইয়ের ভাষা প্রশাসনিক হলেও এর অর্থ গভীরভাবে রাজনৈতিক। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকের অস্তিত্ব প্রশ্নের বিষয় হওয়া উচিত নয়। রাষ্ট্র নাগরিককে স্বীকৃতি দেয়, নাগরিক রাষ্ট্রকে বৈধতা দেয়। এসআইআর এই সম্পর্ক উল্টে দেয়।
নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী Booth Level Officer বা BLO ঘরে ঘরে গিয়ে যাচাই করবেন। কিন্তু বাস্তবে এই যাচাই মানে নাগরিকের ব্যক্তিগত জীবনে রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ। BLO যদি কাউকে না পান, যদি প্রতিবেশী বলেন “এখানে থাকে না”, যদি দরজা বন্ধ থাকে—তাহলেই নাগরিক “অনুপস্থিত” হিসেবে চিহ্নিত হয়। এই একটি শব্দই নাগরিককে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হয়ে ওঠে। এখানে কোনো শুনানি নেই, কোনো নোটিশ নেই, কোনো আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ নেই। এসআইআর তাই সংশোধন নয়—এটি বাছাই।
এসআইআর কেবল মৃতদের নাম বাদ দেয় না; জীবিত মানুষও বাদ পড়ে। কারণ রাষ্ট্র এখানে জীবনের বাস্তবতা বোঝে না। ভারতীয় সমাজে পরিযান স্বাভাবিক—মানুষ কাজের জন্য বাইরে যায়, মাসের পর মাস থাকে না, গ্রামে ফিরে আসে। কিন্তু প্রশাসনিক চোখে এই অনুপস্থিতি অপরাধ। এই অপরাধের শাস্তি ভোটাধিকার হরণ। রাষ্ট্রের কাছে নাগরিকের জীবনধারা গ্রহণযোগ্য নয়, যদি তা প্রশাসনিক ছকে না ফিট করে।
এখানেই এসআইআর আর প্রশাসনিক থাকে না। এটি হয়ে ওঠে জীবন ও কাগজের সংঘর্ষ। কাগজের কাছে মানুষ হার মানে। যাদের কাছে কাগজ নেই, যাদের ঠিকানা বদলায়, যাদের নামের বানান বদলায়, যাদের বয়সের নথি নেই—তাঁরা সবাই এসআইআর-এর ঝুঁকিতে থাকেন। এই ঝুঁকি সমানভাবে বণ্টিত নয়। এটি দরিদ্র, সংখ্যালঘু, নারী ও পরিযায়ী জনগোষ্ঠীর দিকে বেশি ঝুঁকে থাকে।
এসআইআর নাগরিক-সহায়ক প্রক্রিয়া নয়। এটি নাগরিকবান্ধব নয়। এটি অংশগ্রহণমূলক নয়। এটি স্বচ্ছ নয়। এটি আপিলযোগ্য নয়। অধিকাংশ নাগরিক জানতেই পারেন না তাঁদের নাম যাচাই হচ্ছে। অনেকেই ভোটকেন্দ্রে গিয়ে প্রথমবার জানতে পারেন যে তাঁরা আর ভোটার নন। এই অজ্ঞাতসারেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সবচেয়ে ভয়ংকর রূপ প্রকাশ পায়।
এসআইআর নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ হয় না। কোন এলাকায় কতটা কঠোরতা, কোন এলাকায় কতটা ছাড়—তা প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের চেয়ে রাজনৈতিক বাস্তবতার উপর নির্ভর করে। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা, বস্তি, শ্রমিক কলোনি, বিরোধী ভোটব্যাংক হিসেবে পরিচিত অঞ্চল—এই জায়গাগুলোতেই এসআইআর সবচেয়ে তীব্র হয়। কারণ ভোটার তালিকা কেবল তালিকা নয়; এটি নির্বাচনের গণিত।
এসআইআর তাই একটি নীরব রাজনৈতিক প্রযুক্তি। এখানে আইন বদলায় না, সংবিধান বদলায় না, কিন্তু নাগরিকের অধিকার বদলে যায়। এটি রাষ্ট্রকে সেই ক্ষমতা দেয়, যা প্রকাশ্যে দিলে প্রতিরোধ হতো। প্রশাসনিক ভাষাই এখানে ঢাল, আর তালিকা হলো অস্ত্র।
এসআইআর কী নয়, তা এখানেই স্পষ্ট—এটি কোনো নিরীহ প্রশাসনিক কাজ নয়। এটি কোনো সাধারণ সংশোধন নয়। এটি কোনো নাগরিকবান্ধব উদ্যোগ নয়। এটি একটি রাষ্ট্রীয় কৌশল, যার মাধ্যমে নাগরিকত্ব শর্তাধীন করা হয়। যে নাগরিক প্রমাণ করতে পারবে, সে থাকবে; যে পারবে না, সে বাদ যাবে। এই বাছাই প্রক্রিয়াই গণতন্ত্রের বিপরীত দর্শন।
অনেক গবেষক এই প্রক্রিয়াকে “নীরব ভোটার বর্জন” বা silent voter purge বলেছেন। কারণ এখানে কোনো ঘোষণা নেই, কোনো জরুরি অবস্থা নেই, কোনো সংবাদ নেই। কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ রাজনৈতিকভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই অদৃশ্যকরণই আধুনিক রাষ্ট্রের সবচেয়ে ভয়ংকর সহিংসতা—কারণ এখানে রক্তপাত নেই, কিন্তু অধিকার শেষ হয়ে যায়।
এসআইআর তাই একটি সীমান্ত। নাগরিকত্বের সীমান্ত। এই সীমান্তে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্র ঠিক করে—কে থাকবে, কে থাকবে না। আর যখন রাষ্ট্র নাগরিকের অস্তিত্ব ঠিক করতে শুরু করে, তখন গণতন্ত্র আর গণতন্ত্র থাকে না; তা হয়ে ওঠে অনুমতির শাসন।
এই কারণেই এসআইআর কী—এই প্রশ্নের চেয়ে বড় প্রশ্ন হলো—এসআইআর কী নয়। এটি কোনো প্রযুক্তিগত সংশোধন নয়। এটি কোনো নিরপেক্ষ প্রক্রিয়া নয়। এটি কোনো ভুল ধরার উদ্যোগ নয়। এটি একটি রাষ্ট্রীয় অস্ত্র—নীরব, বৈধ, কিন্তু গভীরভাবে রাজনৈতিক।
‘রিভিশন’ শব্দের আড়ালে লুকোনো ক্ষমতা
রাষ্ট্র যখন কোনো প্রক্রিয়াকে নাম দেয়, তখন সেই নামটিই তার প্রথম অস্ত্র। ভাষা নিরীহ হলে ক্ষমতাও নিরীহ মনে হয়। “রিভিশন” শব্দটি সেই নিরীহতার একটি নিখুঁত উদাহরণ। সাধারণ অর্থে রিভিশন মানে সংশোধন, ঠিক করা, ভুল মেরামত করা। এতে কোনো দমন নেই, কোনো আক্রমণ নেই, কোনো ক্ষমতার প্রদর্শন নেই। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রে প্রশাসনিক ভাষা কখনোই নিরীহ নয়; বরং প্রশাসনিক ভাষাই ক্ষমতার সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়। কারণ এই ভাষা ব্যবহার করে রাষ্ট্র এমন সব কাজ করতে পারে, যা সরাসরি করলে প্রতিরোধ হতো।
ভোটার তালিকার ক্ষেত্রে “রিভিশন” শব্দটি বিশেষভাবে রাজনৈতিক। এটি এমন একটি শব্দ, যা নাগরিককে আশ্বস্ত করে—যেন রাষ্ট্র তার উপকার করছে, তালিকা শুদ্ধ করছে, গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করছে। অথচ বাস্তবে এই শব্দের আড়ালে ঘটে যায় নাগরিকত্বের পুনর্বিন্যাস, রাজনৈতিক বর্জন, ভোটাধিকার সংকোচন। ভাষা এখানে সত্যকে আড়াল করে, অন্যায়কে ঢেকে রাখে, আর ক্ষমতাকে স্বাভাবিক করে তোলে।
প্রশাসনিক ভাষা কখনোই সরাসরি বলে না যে কাউকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। বলা হয় “ডিলিশন”, “করেকশন”, “ভেরিফিকেশন”, “রিভিশন”। এই শব্দগুলো এমনভাবে বেছে নেওয়া হয় যাতে তাতে কোনো নৈতিক প্রশ্ন না ওঠে। “নাম বাদ দেওয়া” সহিংস শোনায়, কিন্তু “তালিকা সংশোধন” শোনায় দায়িত্বশীল। আধুনিক রাষ্ট্র এই ভাষাগত কৌশল ব্যবহার করেই নাগরিকের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে।
ভোটার তালিকার Special Intensive Revision–এর ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে। “ইনটেনসিভ” শব্দটি যুক্ত করে প্রক্রিয়াটিকে আরও জরুরি, আরও প্রযুক্তিগত, আরও বৈধ করে তোলা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো—কেন এই অতিরিক্ত তীব্রতা? কেন সাধারণ সংশোধন যথেষ্ট নয়? এই প্রশ্নের উত্তর ভাষার ভেতর নেই; উত্তর আছে রাজনীতিতে। কারণ রিভিশনের নামে যা ঘটে, তা আসলে শুদ্ধিকরণ নয়—তা বাছাই।
রাষ্ট্র এখানে নিজেকে দেখায় মেরামতকারী হিসেবে, কিন্তু আচরণ করে বিচারকের মতো। কে থাকবে, কে থাকবে না—এই সিদ্ধান্ত রাষ্ট্র নেয়, কিন্তু ভাষায় সে নিজেকে কেবল সংশোধনকারী বলে দাবি করে। এই দ্বৈততা আধুনিক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সবচেয়ে সূক্ষ্ম রূপ।
প্রশাসনিক ভাষা সবসময় নিজেকে নিরপেক্ষ বলে দাবি করে। বলা হয়—“নিয়ম অনুযায়ী”, “প্রক্রিয়া অনুযায়ী”, “নির্দেশিকা অনুযায়ী”। এই শব্দগুলো শুনলে মনে হয় সিদ্ধান্ত কেউ নিচ্ছে না, সিদ্ধান্ত নিজে থেকেই হয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্র যেন অদৃশ্য হয়ে যায়, আর নিয়ম যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু বাস্তবে নিয়মও মানুষই বানায়, নির্দেশিকাও মানুষই লেখে, আর প্রয়োগও মানুষই করে। প্রশাসনিক ভাষা সেই মানুষের দায় অদৃশ্য করে দেয়।
এসআইআর-এর ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে। যখন বলা হয় “নিয়ম অনুযায়ী নাম বাদ গেছে”, তখন প্রশ্ন ওঠে না—কেন এই নিয়ম, কার জন্য এই নিয়ম, কাদের বিরুদ্ধে এই নিয়ম? ভাষা প্রশ্নকে থামিয়ে দেয়। রাষ্ট্র এই ভাষা ব্যবহার করে নাগরিকের সঙ্গে নৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে।
এই ভাষা সবচেয়ে ভয়ংকর হয়ে ওঠে তখন, যখন তা “ভুল”কে অস্বীকার করে। প্রশাসনিক ভাষায় ভুল বলে কিছু থাকে না; থাকে “ডিসক্রেপেন্সি”, “মিসম্যাচ”, “ইনকনসিস্টেন্সি”। এই শব্দগুলো মানুষের জীবনের বাস্তবতা অস্বীকার করে। নামের বানান ভুল হলে তা জীবনের ভুল নয়, কিন্তু প্রশাসনিক ভাষায় তা অপরাধে পরিণত হয়। বয়সের নথি না থাকলে তা দারিদ্র্যের ফল, কিন্তু প্রশাসনিক ভাষায় তা অযোগ্যতা। ঠিকানা বদলানো জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা, কিন্তু প্রশাসনিক ভাষায় তা সন্দেহ।
এইভাবে প্রশাসনিক ভাষা মানুষের জীবনকে সমস্যায় রূপান্তর করে, আর সেই সমস্যার সমাধান হিসেবে হাজির করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। রাষ্ট্র এখানে সমস্যার সমাধানকারী নয়; রাষ্ট্র সমস্যার স্রষ্টা।
প্রশাসনিক ভাষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এটি সহিংসতাকে অদৃশ্য করে। যখন কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়, সহিংসতা দৃশ্যমান হয়। যখন কাউকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়, সহিংসতা অদৃশ্য হয়। প্রশাসনিক ভাষা এই অদৃশ্য সহিংসতাকে স্বাভাবিক করে তোলে। বলা হয়—“প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে”, “রিভিশন সম্পন্ন হয়েছে”, “তালিকা চূড়ান্ত হয়েছে”। এই বাক্যগুলোর ভেতরে লুকিয়ে থাকে লক্ষ লক্ষ মানুষের রাজনৈতিক মৃত্যু।
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এখানে রক্তপাত ছাড়াই কাজ করে। প্রশাসনিক ভাষা রক্তের দাগ মুছে দেয়। এই কারণেই আধুনিক কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রগুলো বন্দুকের চেয়ে ফাইলকে বেশি পছন্দ করে। কারণ ফাইল প্রশ্ন তোলে না, প্রতিবাদ করে না, বিচার চায় না।
“রিভিশন” শব্দটি তাই কেবল একটি শব্দ নয়; এটি একটি রাজনৈতিক কৌশল। এই কৌশলের মাধ্যমে রাষ্ট্র নাগরিককে বোঝায় যে তার বিরুদ্ধে যা হচ্ছে, তা আসলে তারই মঙ্গলের জন্য। ভাষা এখানে সম্মতির উৎপাদন করে।
এই সম্মতির রাজনীতি সবচেয়ে স্পষ্ট হয় মিডিয়ার ভাষায়। সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেলও রাষ্ট্রীয় শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করে। বলা হয়—“ভোটার তালিকা সংশোধন শুরু”, “ভুয়া ভোটার বাদ দেওয়া হবে”, “তালিকা শুদ্ধ করা হচ্ছে”। এই বাক্যগুলো শুনে নাগরিক নিজেই ভাবতে শুরু করে—হয়তো এটা দরকার। ভাষা এইভাবে প্রতিরোধকে দুর্বল করে।
কিন্তু প্রশ্ন হলো—ভুয়া কে? রাষ্ট্র কি কখনো স্পষ্টভাবে বলে? কোনো ডেটা কি প্রকাশ করে? কোনো স্বাধীন অডিট কি হয়? না। প্রশাসনিক ভাষা এই প্রশ্নগুলোকে অপ্রয়োজনীয় করে তোলে। কারণ ভাষা আগেই সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয়—এটা শুদ্ধিকরণ, এটা ভালো, এটা প্রয়োজনীয়।
এই ভাষাগত কৌশল নতুন নয়। ইতিহাস দেখায়, সব রাষ্ট্রই ক্ষমতা প্রয়োগের আগে ভাষা পরিষ্কার করে। জার্মানিতে ইহুদিদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল “রেজিস্ট্রেশন” শব্দের মাধ্যমে। দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের ভোটাধিকার কাটা হয়েছিল “অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রি-অর্গানাইজেশন” বলে। মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের বাদ দেওয়া হয়েছিল “ভেরিফিকেশন” নামে। ভাষা এখানে আগেই সহিংসতার পথ তৈরি করে দেয়।
ভারতে এসআইআর-এর ভাষাও সেই ধারার অংশ। “রিভিশন” শব্দটি নাগরিকত্বের প্রশ্নকে প্রযুক্তিগত করে তোলে, নৈতিক নয়। নাগরিক আর নাগরিক থাকে না; সে হয়ে ওঠে ডেটা, এন্ট্রি, রেকর্ড। রাষ্ট্র তখন মানুষের সঙ্গে কথা বলে না, কথা বলে তালিকার সঙ্গে।
এই রূপান্তর গণতন্ত্রের জন্য ভয়ংকর। কারণ গণতন্ত্রের ভিত্তি হলো নৈতিক সম্পর্ক—রাষ্ট্র ও নাগরিকের পারস্পরিক স্বীকৃতি। প্রশাসনিক ভাষা এই সম্পর্ক ভেঙে দেয়। রাষ্ট্র তখন আর নাগরিকের কাছে দায়বদ্ধ থাকে না; সে কেবল নিয়মের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। আর নিয়ম সবসময় রাষ্ট্রের পক্ষে লেখা হয়।
এই কারণেই এসআইআর কেবল একটি প্রক্রিয়া নয়, এটি একটি ভাষাগত রাজনীতি। এখানে ভাষা দিয়ে অন্যায় ঢেকে রাখা হয়, ক্ষমতা স্বাভাবিক করা হয়, নাগরিকত্ব শর্তাধীন করা হয়। “রিভিশন” শব্দটি সেই ঢালের মতো কাজ করে, যার আড়ালে রাষ্ট্র নাগরিকের উপর আঘাত হানে।
এসআইআর-এর সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক এখানেই—এটি মানুষকে বোঝায় যে তার সঙ্গে যা হচ্ছে, তা স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকতাই সবচেয়ে বড় সহিংসতা। কারণ যেখানে অন্যায় স্বাভাবিক হয়ে যায়, সেখানে প্রতিরোধ মরে যায়।
এই প্রবন্ধের মূল কথা তাই সহজ—এসআইআর-এর সমস্যা কেবল প্রক্রিয়ায় নয়, ভাষায়। কারণ ভাষা বদলালেই রাজনীতি বদলায়। যতদিন “রিভিশন” শব্দটি প্রশ্নহীন থাকবে, ততদিন অন্যায় বৈধ থাকবে। আর যতদিন অন্যায় বৈধ থাকবে, ততদিন নাগরিকের ভোটাধিকার নিরাপদ থাকবে না।
ভোটার তালিকা: নাগরিকত্বের গোপন দরজা
রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের সম্পর্ক সাধারণত আইনের মাধ্যমে বোঝানো হয়, কিন্তু বাস্তবে এই সম্পর্কের সবচেয়ে কার্যকর দরজাটি আইন নয়—একটি তালিকা। সেই তালিকাই ভোটার তালিকা। আধুনিক রাষ্ট্রে নাগরিকত্বের প্রবেশদ্বার আর কেবল জন্মসনদ বা পাসপোর্ট নয়; ভোটার তালিকাই হয়ে উঠেছে নাগরিক অস্তিত্বের সবচেয়ে সহজলভ্য, সবচেয়ে দৃশ্যমান ও সবচেয়ে কার্যকর প্রমাণ। এই কারণেই ভোটার তালিকা কেবল একটি নির্বাচনী দলিল নয়, এটি নাগরিকত্বের গোপন দরজা—যার একদিকে অধিকার, আরেকদিকে বর্জন।
ভারতের সংবিধান নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকারকে তাত্ত্বিকভাবে পৃথক রেখেছে। নাগরিকত্ব নির্ধারিত হয় নাগরিকত্ব আইনে, আর ভোটাধিকার নির্ধারিত হয় সংবিধানের ৩২৬ অনুচ্ছেদে। কিন্তু বাস্তব রাষ্ট্রচর্চায় এই দুটি সম্পূর্ণভাবে আলাদা নয়। কারণ অধিকাংশ সাধারণ নাগরিকের কাছে নাগরিকত্বের একমাত্র দৃশ্যমান প্রমাণ হলো ভোটার পরিচয়পত্র। গ্রামাঞ্চলে, বস্তিতে, পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে, দরিদ্র মানুষের কাছে পাসপোর্ট নেই, জন্মসনদ নেই, সম্পত্তির দলিল নেই; আছে কেবল ভোটার কার্ড। ফলে ভোটার তালিকায় নাম থাকা মানেই নাগরিক হওয়া, আর নাম না থাকা মানেই নাগরিকত্বের ওপর প্রশ্নচিহ্ন।
এই বাস্তবতা রাষ্ট্র খুব ভালোভাবেই জানে। এবং সেই জ্ঞানই ভোটার তালিকাকে একটি প্রশাসনিক নথি থেকে রাজনৈতিক অস্ত্রে রূপান্তর করেছে। রাষ্ট্র যখন ভোটার তালিকা নিয়ন্ত্রণ করে, তখন সে আসলে নাগরিকত্বের প্রবেশ ও বহিষ্কারের দরজাটি নিয়ন্ত্রণ করে। এই দরজার সামনে কোনো সাইনবোর্ড নেই, কোনো আইনগত সতর্কতা নেই—কিন্তু কার্যকারিতা ভয়ংকর।
ভোটার তালিকা তৈরির ইতিহাস দেখলে বোঝা যায়, এটি কখনোই নিরীহ ছিল না। ব্রিটিশ আমলে ভোটাধিকার সীমাবদ্ধ ছিল সম্পত্তি ও শিক্ষার ভিত্তিতে। তালিকা তখনই বাছাইয়ের অস্ত্র ছিল। স্বাধীনতার পর সর্বজনীন ভোটাধিকার চালু হলেও তালিকার ক্ষমতা কমেনি, বরং তার চরিত্র বদলেছে। আগে তালিকা দিয়ে বাছাই হতো শ্রেণিভিত্তিক, এখন হয় নথিভিত্তিক। বাছাইয়ের পদ্ধতি বদলেছে, উদ্দেশ্য বদলায়নি।
ভোটার তালিকার সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক হলো এটি নাগরিকত্বকে ধীরে ধীরে প্রমাণনির্ভর করে তোলে। রাষ্ট্র নাগরিককে আর স্বীকৃতি দেয় না, নাগরিককে প্রমাণ করতে হয়। এই প্রমাণের ভাষা কাগজের ভাষা, আর কাগজের ভাষা দরিদ্র মানুষের ভাষা নয়। নামের বানান, জন্মতারিখ, ঠিকানা, বাসস্থানের ধারাবাহিকতা—এই সব কিছুর সামান্য অমিল নাগরিককে সন্দেহের কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। তালিকা এখানে কেবল নামের তালিকা নয়; এটি একটি যাচাই যন্ত্র।
এই যাচাই যন্ত্রের কাজ সবচেয়ে স্পষ্টভাবে দেখা যায় Special Intensive Revision-এর সময়। এসআইআর-এর মাধ্যমে ভোটার তালিকাকে “বিশেষভাবে শুদ্ধ” করার কথা বলা হয়, কিন্তু এই শুদ্ধিকরণ মানে আসলে নাগরিকত্বের ফিল্টারিং। কে থাকবে, কে থাকবে না—এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় প্রশাসনিক মানদণ্ডে, কিন্তু ফলাফল রাজনৈতিক। কারণ ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া মানে শুধু ভোট হারানো নয়; এর মানে সামাজিক স্বীকৃতি হারানো, রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব হারানো।
ভারতের বহু রাজ্যে দেখা গেছে, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার পর নাগরিকরা রেশন কার্ড, স্বাস্থ্য পরিষেবা, সরকারি প্রকল্প—সবকিছুর ক্ষেত্রেই সমস্যায় পড়েছেন। কারণ একটার সঙ্গে আরেকটা নথি যুক্ত। ভোটার তালিকা এখানে নাগরিকত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে। এটি একটি গোপন দরজা—যে দরজা খোলা থাকলে নাগরিক রাষ্ট্রের ভেতরে থাকে, আর বন্ধ হলে সে বাইরে পড়ে যায়।
এই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে প্রশাসন। Booth Level Officer, জেলা অফিস, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা—এই সব মিলিয়ে একটি প্রশাসনিক প্রহরী ব্যবস্থা তৈরি হয়, যারা ঠিক করে কে ঢুকবে আর কে ঢুকবে না। এই প্রহরীরা কোনো আদালত নয়, কোনো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নয়, কিন্তু তাদের সিদ্ধান্ত নাগরিকত্বের ওপর প্রভাব ফেলে। এটি গণতন্ত্রের একটি গভীর সংকট, কারণ নাগরিকত্বের মতো মৌলিক প্রশ্ন প্রশাসনিক হাতে চলে যায়।
ভোটার তালিকার সঙ্গে নাগরিকত্বের এই অদৃশ্য সংযোগ সবচেয়ে ভয়ংকর হয়ে ওঠে সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে। মুসলমান, দলিত, আদিবাসী, পরিযায়ী শ্রমিক, শহরের বস্তিবাসী—এই সব জনগোষ্ঠীর নথি অসম্পূর্ণ, জীবনযাপন অনিশ্চিত, ঠিকানা অস্থায়ী। ফলে ভোটার তালিকার যাচাইয়ে তাঁরাই প্রথম বাদ পড়েন। এই বাদ পড়া কোনো কাকতাল নয়; এটি কাঠামোগত।
অসমে NRC প্রক্রিয়ার সময় দেখা গেছে, যাদের নাম ভোটার তালিকায় নেই বা ছিল না, তাদের নাগরিকত্ব সহজেই প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে¹। এই অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে, ভোটার তালিকা নাগরিকত্বের একটি অঘোষিত সিঁড়ি। তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া মানে সেই সিঁড়ি ভেঙে যাওয়া। এসআইআর সেই ভাঙনের জাতীয় সংস্করণ।
রাষ্ট্র কখনোই প্রকাশ্যে বলে না যে ভোটার তালিকা নাগরিকত্ব নির্ধারণ করে। বলা হয়—এটি কেবল নির্বাচনের জন্য। কিন্তু বাস্তব জীবনে নাগরিকত্বের চর্চা এই কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করে। সরকারি অফিসে, পুলিশ স্টেশনে, আদালতে, এমনকি সমাজের ভেতরেও ভোটার কার্ড নাগরিক পরিচয়ের প্রথম দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফলে তালিকা নিয়ন্ত্রণ মানে পরিচয় নিয়ন্ত্রণ।
এই পরিচয় নিয়ন্ত্রণের রাজনীতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। এখানে রাষ্ট্র সরাসরি কাউকে “অ-নাগরিক” বলে না। সে কেবল বলে—“তুমি তালিকায় নেই।” এই একটি বাক্যই নাগরিককে সবকিছু থেকে বঞ্চিত করতে পারে। এই বঞ্চনা নীরব, ধীরে ধীরে, কিন্তু স্থায়ী। কারণ তালিকায় ফিরে আসা সহজ নয়। আবেদন, আপিল, নথি, সাক্ষ্য—এই সব প্রক্রিয়া দরিদ্র মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব।
ভোটার তালিকা তাই নাগরিকত্বের গোপন দরজা—কারণ এই দরজাটি সবাই দেখতে পায় না, কিন্তু সবাই তার প্রভাব অনুভব করে। রাষ্ট্র এই দরজার মাধ্যমে নাগরিকত্বকে শর্তাধীন করে তোলে। নাগরিককে রাষ্ট্রের কাছে বারবার প্রমাণ করতে হয় যে সে আছে, সে যোগ্য, সে গ্রহণযোগ্য। এই প্রমাণের রাজনীতি গণতন্ত্রের বিপরীত, কারণ গণতন্ত্রে নাগরিকত্ব কোনো পরীক্ষার ফল নয়; এটি অধিকার।
এই দরজা দিয়ে রাষ্ট্র শুধু মানুষ ঢোকায় না, মানুষ বাদও দেয়। বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া এতটাই নীরব যে নাগরিক বুঝতেই পারে না সে কখন বাইরে চলে গেছে। একদিন ভোট দিতে গিয়ে সে জানতে পারে—তার নাম নেই। এই মুহূর্তেই নাগরিকত্বের গোপন দরজা তার সামনে বন্ধ হয়ে যায়। এই বন্ধ হওয়ার কোনো ঘোষণা নেই, কোনো ব্যাখ্যা নেই, কোনো দয়া নেই।
ভোটার তালিকার এই ক্ষমতা ইতিহাসে নতুন নয়। ফ্রান্সে বিপ্লবের পর নাগরিক তালিকা তৈরি হয়েছিল রাজনৈতিক শুদ্ধিকরণের জন্য। যুক্তরাষ্ট্রে আফ্রিকান-আমেরিকানদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে নাগরিকত্ব সীমিত করা হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের তালিকা সংকুচিত করে বর্ণবাদী শাসন চালানো হয়েছিল। সব ক্ষেত্রেই তালিকা ছিল রাষ্ট্রের দরজা।
ভারতেও সেই দরজা এখন দৃশ্যমান হচ্ছে। এসআইআর-এর মাধ্যমে রাষ্ট্র নাগরিকত্বকে তালিকাভুক্ত হওয়ার শর্তে পরিণত করছে। এই শর্ত মানতে না পারলে নাগরিকত্ব প্রশ্নবিদ্ধ। এই রাজনীতি সরাসরি বলা হয় না, কিন্তু প্রশাসনিক ভাষায় প্রতিদিন কার্যকর হয়।
এই প্রক্রিয়াকে অনেক গবেষক “ডকুমেন্টারি সিটিজেনশিপ” বলেছেন—যেখানে মানুষ নাগরিক নয়, কাগজ নাগরিক। ভোটার তালিকা সেই কাগজের রাজ্যের প্রধান প্রবেশপথ। এই প্রবেশপথ রাষ্ট্রের হাতে থাকায় রাষ্ট্রই ঠিক করে কে নাগরিক আর কে নয়।
ভোটার তালিকার এই গোপন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আজ ভারতের গণতন্ত্র। প্রশ্ন হলো—এই দরজা কি নাগরিকের জন্য খোলা থাকবে, নাকি কেবল নির্বাচিতদের জন্য? এই প্রশ্নের উত্তর এখনো লেখা হয়নি, কিন্তু এসআইআর-এর মতো প্রক্রিয়া সেই উত্তর লিখে দিচ্ছে—নীরবে, প্রশাসনিক ভাষায়, তালিকার অক্ষরে অক্ষরে।
এই কারণেই ভোটার তালিকা নাগরিকত্বের সীমান্ত। আর সেই সীমান্তে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্র। যে রাষ্ট্র তালিকা নিয়ন্ত্রণ করে, সে নাগরিকত্ব নিয়ন্ত্রণ করে। আর যে নাগরিকত্ব নিয়ন্ত্রণ করে, সে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করে।
BLO-এর সীমাহীন ক্ষমতা ও নাগরিকের অসহায়তা
রাষ্ট্রের ক্ষমতা সাধারণত বড় বড় দপ্তরে, আইনসভায় বা আদালতে বসে কাজ করে—এমনটাই আমরা ভাবতে অভ্যস্ত। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রে ক্ষমতার সবচেয়ে কার্যকর প্রয়োগ ঘটে ছোট, নীরব, প্রায় অদৃশ্য জায়গায়—যেখানে কোনো ক্যামেরা থাকে না, কোনো সংবাদ পৌঁছায় না, কোনো বড় অফিসারের সই লাগে না। ভোটার তালিকার ক্ষেত্রে সেই জায়গাটির নাম Booth Level Officer বা BLO। প্রশাসনিক কাঠামোয় BLO একজন সামান্য কর্মচারী, কিন্তু বাস্তবে তাঁর হাতে থাকে নাগরিকের রাজনৈতিক অস্তিত্বের চাবিকাঠি। এই বৈপরীত্যই আধুনিক গণতন্ত্রের সবচেয়ে ভয়ংকর সংকেত।
BLO-এর কাজ কাগজে খুবই সীমিত বলে মনে হয়। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী তাঁর দায়িত্ব হলো ভোটারদের তথ্য যাচাই করা, নতুন ভোটার যুক্ত করা, ঠিকানা সংশোধন করা এবং মাঠপর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করা। এই কাজগুলো শুনতে নিরীহ, এমনকি প্রয়োজনীয়। কিন্তু বাস্তবে এই দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় এমন ক্ষমতা, যা কোনো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকার কথা নয়। BLO ঠিক করেন কে “পাওয়া গেল”, কে “পাওয়া গেল না”, কে “অনুপস্থিত”, কে “সন্দেহজনক”। এই শব্দগুলোর প্রতিটিই একটি নাগরিকের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে।
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকের অধিকার কাগজে নয়, আইনে নির্ধারিত হওয়ার কথা। কিন্তু এসআইআর প্রক্রিয়ায় নাগরিকের অধিকার নির্ধারিত হয় মাঠপর্যায়ের একটি রিপোর্টে। BLO যদি কোনো বাড়িতে গিয়ে কাউকে না পান, যদি প্রতিবেশী বলেন “এখানে থাকে না”, যদি দরজা বন্ধ থাকে—তাহলেই নাগরিক “অনুপস্থিত” হিসেবে চিহ্নিত হন। এই একটি শব্দ ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হয়ে ওঠে। এখানে কোনো নোটিশ নেই, কোনো শুনানি নেই, কোনো আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ নেই। নাগরিক জানতেই পারেন না যে তাঁর বিরুদ্ধে কী লেখা হলো।
এই ক্ষমতা সীমাহীন, কারণ এর বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিকার নেই। BLO-এর রিপোর্টকে চ্যালেঞ্জ করতে হলে নাগরিককে জেলা অফিসে যেতে হয়, প্রমাণ দিতে হয়, আবেদন করতে হয়—যা দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। ফলে একটি রিপোর্ট, একটি কলাম, একটি টিক চিহ্ন—এই সবই নাগরিকের রাজনৈতিক জীবন শেষ করে দিতে পারে। এটি আইন নয়, কিন্তু আইনের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।
এই ক্ষমতার সবচেয়ে ভয়ংকর দিক হলো এটি ব্যক্তিগত ও সামাজিক পক্ষপাতকে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে রূপান্তরিত করে। BLO-রা সাধারণত স্থানীয় বাসিন্দা, স্থানীয় সামাজিক কাঠামোর অংশ। তাঁদের নিজস্ব ধর্মীয়, জাতিগত, রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকে। কিন্তু রাষ্ট্র তাঁদের হাতে এমন ক্ষমতা দেয়, যার প্রয়োগে এই ব্যক্তিগত পক্ষপাত নাগরিকত্বের প্রশ্নে প্রভাব ফেলে। মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় BLO-এর সন্দেহ বেশি, বস্তিতে BLO-এর অনীহা বেশি, শ্রমিক কলোনিতে BLO-এর উপস্থিতি কম—এই বাস্তবতা বহু নাগরিক অধিকার সংগঠনের রিপোর্টে উঠে এসেছে¹। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এখানে সামাজিক বৈষম্যের সঙ্গে মিশে যায়।
BLO-এর কাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো এর অদৃশ্যতা। আদালতের রায় প্রকাশিত হয়, প্রশাসনিক আদেশ নথিভুক্ত হয়, কিন্তু BLO-এর রিপোর্ট নাগরিকের কাছে পৌঁছায় না। এটি প্রশাসনিক ফাইলের ভেতর থাকে, এবং সেই ফাইলই নাগরিকের ভাগ্য নির্ধারণ করে। এই অদৃশ্য ক্ষমতা আধুনিক রাষ্ট্রের সবচেয়ে বিপজ্জনক রূপ, কারণ এখানে দায় কেউ নেয় না। নাগরিক যখন জানতে চান কেন তাঁর নাম বাদ গেছে, তখন এক দপ্তর আরেক দপ্তরের দিকে আঙুল তোলে, আর শেষ পর্যন্ত নাগরিক একা থেকে যান।
এই প্রক্রিয়ায় নাগরিকের অসহায়তা সম্পূর্ণ। কারণ এখানে কোনো সমান লড়াই নেই। একদিকে আছে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক যন্ত্র, অন্যদিকে আছে একজন একা নাগরিক। নাগরিকের হাতে কাগজ নেই, সময় নেই, টাকা নেই, আইনি জ্ঞান নেই। অথচ তাঁর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত হয়ে যায় কয়েক মিনিটের মধ্যে। এই অসমতা গণতন্ত্রের মৌলিক ধারণার বিপরীত।
BLO-এর ক্ষমতা আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠে যখন তা “নিয়ম” ও “নির্দেশিকা”-র ভাষায় ঢাকা পড়ে। বলা হয়—“নিয়ম অনুযায়ী করা হয়েছে”, “নির্দেশ অনুযায়ী রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে”। কিন্তু এই নিয়মগুলো কে বানায়? কার জন্য বানায়? কাদের বিরুদ্ধে বানায়? এই প্রশ্নগুলো কখনো আলোচনায় আসে না। প্রশাসনিক ভাষা এই প্রশ্নগুলোকে অপ্রয়োজনীয় করে তোলে, আর নাগরিকের অসহায়তাকে স্বাভাবিক করে তোলে।
এসআইআর প্রক্রিয়ায় BLO কার্যত নাগরিকত্ব যাচাইয়ের প্রথম বিচারক হয়ে ওঠেন, যদিও তাঁর হাতে কোনো সাংবিধানিক ক্ষমতা নেই। এই বিচারক কোনো শুনানি নেন না, কোনো যুক্তি শোনেন না, কোনো ব্যাখ্যা দেন না। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তের প্রভাব নাগরিকত্বের মতো মৌলিক বিষয়ের ওপর পড়ে। এটি রাষ্ট্রের একটি ভয়ংকর কৌশল—বড় সিদ্ধান্ত ছোট হাতে দিয়ে দায় এড়িয়ে যাওয়া।
এই ক্ষমতার কাঠামো সবচেয়ে বেশি আঘাত হানে নারীদের ওপর। অনেক ক্ষেত্রে BLO বাড়িতে গিয়ে কেবল পুরুষ সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। নারীরা বাইরে থাকলে বা উপস্থিত না থাকলে তাঁদের নাম “অনুপস্থিত” হিসেবে চিহ্নিত হয়। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে, পরিবারের পুরুষদের নাম তালিকায় থেকে গেছে, নারীদের নাম বাদ গেছে²। এই বৈষম্য কেবল সামাজিক নয়; এটি রাষ্ট্রীয় হয়ে ওঠে BLO-এর রিপোর্টের মাধ্যমে।
পরিযায়ী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই অসহায়তা আরও গভীর। কাজের জন্য বাইরে থাকা মানেই প্রশাসনিক চোখে অনুপস্থিত। BLO জানেন শ্রমিকেরা বাইরে যান, কিন্তু নিয়ম তাঁদের জীবনের বাস্তবতা স্বীকার করে না। ফলে শ্রমিকেরা নাগরিক হিসেবে নয়, সমস্যার মতো আচরণ পান। তাঁদের ভোটাধিকার কাগজে হারিয়ে যায়, কারণ তাঁরা সেই মুহূর্তে ঘরে ছিলেন না। রাষ্ট্র এখানে নাগরিককে নয়, ঠিকানাকে ভোটার হিসেবে দেখে।
BLO-এর ক্ষমতা কার্যত নাগরিকত্বের ফিল্টার হিসেবে কাজ করে। এই ফিল্টার কোনো আইনি কাঠামোর ভেতর নেই, কোনো গণতান্ত্রিক নজরদারির আওতায় নেই। এটি প্রশাসনিক স্তরের একটি ছায়া ক্ষমতা, যা নাগরিককে বেছে বেছে বাদ দেয়। এই ছায়া ক্ষমতাই আধুনিক গণতন্ত্রের সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক, কারণ এখানে ক্ষমতা আছে, কিন্তু দায়িত্ব নেই।
এই প্রক্রিয়ায় নাগরিক ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের উপর আস্থা হারায়। সে বুঝতে পারে, তার অধিকার কোনো আদালতে নয়, কোনো আইনে নয়—একজন অচেনা কর্মচারীর রিপোর্টে নির্ধারিত হচ্ছে। এই উপলব্ধি নাগরিকত্বের নৈতিক ভিত্তিকে ধ্বংস করে। নাগরিক তখন আর রাষ্ট্রের অংশ মনে করে না, রাষ্ট্রকে ভয় করতে শেখে।
বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে, BLO-এর রিপোর্টের ভিত্তিতে নাম বাদ যাওয়ার পরে নাগরিকরা রেশন কার্ড, স্বাস্থ্য পরিষেবা, সরকারি প্রকল্প—সবকিছুর ক্ষেত্রেই সমস্যায় পড়েছেন। কারণ ভোটার তালিকা অন্যান্য নথির সঙ্গে যুক্ত। অর্থাৎ BLO-এর একটি রিপোর্ট নাগরিককে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বাইরে ঠেলে দিতে পারে। এই প্রভাব কেবল রাজনৈতিক নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিকও।
এই অসহায়তার বিরুদ্ধে লড়ার কোনো কার্যকর পথ নেই। নাগরিক আপিল করতে পারেন, কিন্তু সেই আপিল আবার প্রশাসনিক পথেই যায়। আদালতে যেতে পারেন, কিন্তু সেই পথ ব্যয়বহুল ও দীর্ঘ। ফলে অধিকাংশ মানুষ চুপ করে যান। এই চুপ করে যাওয়াই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সবচেয়ে বড় সাফল্য। কারণ যেখানে প্রতিবাদ নেই, সেখানে অন্যায় স্থায়ী হয়।
এই কারণে BLO-এর ক্ষমতা সীমাহীন বলা কোনো অতিশয়োক্তি নয়। এটি আইনগতভাবে সীমিত হলেও বাস্তবে সীমাহীন, কারণ এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ নেই। এটি রাষ্ট্রের সেই স্তর, যেখানে ক্ষমতা সবচেয়ে নগ্ন, কিন্তু সবচেয়ে অদৃশ্য।
আধুনিক রাষ্ট্র বন্দুক দিয়ে নয়, ফাইল দিয়ে শাসন করে—এই কথা বহু চিন্তক বলেছেন। BLO সেই ফাইলের প্রথম পৃষ্ঠা লেখেন। আর সেই প্রথম পৃষ্ঠাতেই নাগরিকের ভাগ্য লেখা হয়ে যায়।
এই বাস্তবতা বুঝতে পারলে স্পষ্ট হয়—এসআইআর-এর আসল সমস্যা কেবল নীতিতে নয়, কাঠামোতে। যে কাঠামো একজন সামান্য কর্মচারীর হাতে নাগরিকত্বের দরজা তুলে দেয়, সেই কাঠামো গণতান্ত্রিক হতে পারে না। BLO-এর সীমাহীন ক্ষমতা আর নাগরিকের অসহায়তা একে অপরের প্রতিবিম্ব। যতদিন এই ক্ষমতা থাকবে, ততদিন নাগরিক নিরাপদ থাকবে না।
ভোটাধিকার হরণ: জনগণকে পঙ্গু করার পরিকল্পনা
রাষ্ট্র যখন কোনো নাগরিকের হাত থেকে ভোটাধিকার কেড়ে নেয়, তখন সে শুধু একটি অধিকার কেড়ে নেয় না—সে নাগরিকের রাজনৈতিক শরীরকে অচল করে দেয়। ভোটাধিকার আধুনিক গণতন্ত্রে নাগরিকের পেশি, স্নায়ু ও কণ্ঠস্বর—যার মাধ্যমে নাগরিক রাষ্ট্রকে স্পর্শ করতে পারে, প্রশ্ন করতে পারে, শাস্তি দিতে পারে। এই অধিকার হরণ মানে নাগরিককে রাষ্ট্রের সামনে পঙ্গু করে দেওয়া, যাতে সে আর দাঁড়াতে না পারে, আর প্রতিরোধ করতে না পারে। আধুনিক রাষ্ট্রে এই পঙ্গুকরণ আর ট্যাংক দিয়ে হয় না, বন্দুক দিয়ে হয় না—হয় কাগজ দিয়ে, তালিকা দিয়ে, নিয়ম দিয়ে। ভোটাধিকার হরণ তাই কোনো বিচ্ছিন্ন প্রশাসনিক ত্রুটি নয়; এটি একটি পরিকল্পিত রাজনৈতিক কৌশল, যার লক্ষ্য জনগণকে নিষ্ক্রিয় করা।
গণতন্ত্রের ইতিহাসে ভোটাধিকার হরণ সবসময়ই ক্ষমতা রক্ষার সবচেয়ে পুরোনো অস্ত্র। ব্রিটিশ শাসনামলে ভোটাধিকার ছিল সম্পত্তি ও শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত, যাতে শাসিত জনগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও ক্ষমতার বাইরে থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের ভোটাধিকার সীমিত করা হয়েছিল বর্ণবাদী রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখার জন্য। যুক্তরাষ্ট্রে আফ্রিকান–আমেরিকানদের ভোটাধিকার নানা নিয়মের মাধ্যমে সংকুচিত করা হয়েছিল—poll tax, literacy test, registration purge-এর মাধ্যমে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই যুক্তি ছিল প্রশাসনিক, কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক¹।
ভারতে স্বাধীনতার পর সর্বজনীন ভোটাধিকার একটি বিপ্লবী অর্জন ছিল। কিন্তু এই অধিকার চিরস্থায়ী নয়—রাষ্ট্র চাইলে একে সীমিত করতে পারে, যদি সে সরাসরি না গিয়ে পরোক্ষ পথে যায়। আধুনিক ভারতের ভোটাধিকার হরণের কৌশল সেই পরোক্ষ পথেই চলছে। এখানে কোনো আইন করে ভোটাধিকার বাতিল করা হচ্ছে না; বরং ভোটার তালিকা এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে যাতে মানুষ নিজের অজান্তেই ভোটের বাইরে চলে যায়। এই নীরবতা রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সাফল্য।
ভোটাধিকার হরণ আজ আর নিষেধাজ্ঞার ভাষায় আসে না, আসে “শুদ্ধিকরণ”, “রিভিশন”, “ভেরিফিকেশন” শব্দে। এই ভাষা নাগরিককে আশ্বস্ত করে, মিডিয়াকে নীরব করে, আদালতকে দূরে রাখে। কিন্তু এই ভাষার আড়ালেই ঘটে রাজনৈতিক পঙ্গুকরণ। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া মানে নাগরিকের রাজনৈতিক পা কেটে দেওয়া—সে আর ভোটের মাঠে হাঁটতে পারে না।
এই প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এর নির্বাচনী লক্ষ্যবস্তু। সব নাগরিক সমানভাবে বাদ পড়ে না। বাদ পড়ে তারা, যারা রাজনৈতিকভাবে দুর্বল, অর্থনৈতিকভাবে অসুরক্ষিত, সামাজিকভাবে প্রান্তিক। পরিযায়ী শ্রমিক, শহরের বস্তিবাসী, গ্রামীণ দরিদ্র, সংখ্যালঘু, নারীরা—এই জনগোষ্ঠীর ভোটাধিকার হরণ সবচেয়ে সহজ, কারণ তাদের জীবন রাষ্ট্রীয় কাগজের বাইরে চলে। রাষ্ট্র এই বাস্তবতাকে অপরাধে রূপান্তর করে এবং তারপর সেই অপরাধের শাস্তি দেয় ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে।
এই পঙ্গুকরণের প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে চলে। প্রথমে নাগরিককে সন্দেহ করা হয়। তারপর তার নাম যাচাই করা হয়। তারপর তাকে “অনুপস্থিত”, “অপ্রমাণিত”, “স্থানান্তরিত” বলে চিহ্নিত করা হয়। শেষে তার নাম বাদ দেওয়া হয়। এই পুরো প্রক্রিয়ায় নাগরিকের সম্মতি নেই, অংশগ্রহণ নেই, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ নেই। সে বুঝতেই পারে না কখন তার অধিকার চলে গেল। এই অজ্ঞানতাই রাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে কার্যকর পরিবেশ।
ভারতের বহু রাজ্যে দেখা গেছে, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার পরে মানুষ সরকারি পরিষেবা পেতেও সমস্যায় পড়েছেন। কারণ ভোটার কার্ড অনেক জায়গায় পরিচয়পত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফলে ভোটাধিকার হরণ ধীরে ধীরে নাগরিকত্ব হরণে পরিণত হয়। এটি একটি ধাপে ধাপে পঙ্গুকরণ—প্রথমে রাজনৈতিক, তারপর সামাজিক, শেষে নাগরিক।
এই পঙ্গুকরণের রাজনীতি সবচেয়ে ভয়ংকর হয়ে ওঠে যখন তা নির্বাচন-পূর্ব সময়ে ঘটে। তখন নাগরিকের হাতে সময় নেই, আইনি লড়াইয়ের সুযোগ নেই, প্রশাসনিক আপিলের শক্তি নেই। নির্বাচন চলে যায়, আর নাগরিক বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। পরবর্তী পাঁচ বছর সে কেবল দর্শক। রাষ্ট্র এই পাঁচ বছর ধরে নীতিনির্ধারণ করে, আইন পাস করে, ক্ষমতা শক্ত করে—নাগরিক কিছুই করতে পারে না। এই সময়ই পঙ্গুকরণের সাফল্যের সময়।
ভোটাধিকার হরণ বিরোধী রাজনীতির জন্য বিশেষভাবে বিধ্বংসী। কারণ বিরোধী রাজনীতি ভোটের ওপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। যখন ভোটার তালিকা সংকুচিত হয়, বিরোধী দল সংখ্যায় ছোট হয়ে যায়। এটি নির্বাচনী প্রকৌশল—যেখানে ভোটার কমিয়ে ফলাফল বদলে দেওয়া হয়। এই প্রকৌশলের সুবিধা হলো—এটি আইনসম্মত দেখায়, কিন্তু নৈতিকভাবে ধ্বংসাত্মক।
এই প্রক্রিয়ায় মিডিয়ার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মিডিয়া যখন “ভুয়া ভোটার বাদ দেওয়া” বা “তালিকা শুদ্ধিকরণ” শব্দ ব্যবহার করে, তখন নাগরিক নিজেই মনে করে—এটা হয়তো দরকার। রাষ্ট্র এই সম্মতি তৈরি করে ভাষার মাধ্যমে। নাগরিক বুঝতেই পারে না, যে প্রক্রিয়াকে সে সমর্থন করছে, সেটাই তার অধিকার কেড়ে নিচ্ছে।
এই পঙ্গুকরণের আরেকটি স্তর হলো ডিজিটালাইজেশন। আধার, বায়োমেট্রিক, অনলাইন যাচাই—এই সব প্রযুক্তি ভোটাধিকার হরণকে আরও নিখুঁত করে তোলে। কারণ প্রযুক্তিগত ভুলের বিরুদ্ধে লড়াই করা সবচেয়ে কঠিন। যদি কোনো ডেটাবেসে নাম মিসম্যাচ হয়, নাগরিক প্রমাণ করতে পারে না যে সে ঠিক। প্রযুক্তি এখানে নিরপেক্ষ নয়; এটি রাষ্ট্রের হাতিয়ার।
ভোটাধিকার হরণ তাই কেবল একটি প্রশাসনিক ফল নয়; এটি একটি রাজনৈতিক পরিকল্পনা, যার লক্ষ্য জনগণকে পঙ্গু করা। পঙ্গু জনগণ বিদ্রোহ করতে পারে না, প্রশ্ন করতে পারে না, ক্ষমতা বদলাতে পারে না। তারা কেবল ভোগ করে, সহ্য করে, মেনে নেয়। এই অবস্থাই আধুনিক কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের স্বপ্ন।
এই প্রক্রিয়া সবচেয়ে ভয়ংকর কারণ এটি দৃশ্যমান নয়। কোনো আইন পাস হয় না, কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি হয় না, কোনো সেনা নামে না। কেবল একটি তালিকা বদলায়। কিন্তু এই তালিকার বদল মানেই গণতন্ত্রের বদল। রাষ্ট্র এই তালিকার মাধ্যমে জনগণের শরীরের স্নায়ু কেটে দেয়—যাতে তারা আর নড়তে না পারে।
ভোটাধিকার হরণ তাই কোনো বিচ্ছিন্ন প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়; এটি একটি সুপরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় কৌশল। এই কৌশলের লক্ষ্য জনগণকে শাসিত করা নয়, জনগণকে অক্ষম করা। কারণ অক্ষম জনগণই সবচেয়ে নিরাপদ জনগণ—রাষ্ট্রের চোখে।
এই বাস্তবতা বুঝতে পারলে স্পষ্ট হয়—গণতন্ত্রের সংকট শুধু নির্বাচন জেতা–হারার সংকট নয়, এটি ভোট দেওয়ার সক্ষমতার সংকট। যেখানে মানুষ ভোট দিতে পারে না, সেখানে গণতন্ত্র কেবল একটি শব্দ। আর যেখানে ভোটাধিকার হরণ স্বাভাবিক হয়ে যায়, সেখানে রাষ্ট্র আর গণতান্ত্রিক থাকে না—সে হয়ে ওঠে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব।
এই কারণে ভোটাধিকার হরণকে ছোট ঘটনা হিসেবে দেখা যায় না। এটি নাগরিকের শরীরকে ধীরে ধীরে পঙ্গু করার একটি প্রক্রিয়া। এবং এই পঙ্গুকরণ যত নীরব, তত ভয়ংকর।
ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া মানে রাজনৈতিক হত্যা
রাষ্ট্র যখন কোনো নাগরিকের ভোটাধিকার কেড়ে নেয়, তখন সে কেবল একটি সাংবিধানিক অধিকার হরণ করে না—সে নাগরিককে রাজনৈতিকভাবে হত্যা করে। এই হত্যা কোনো রক্তপাতের মাধ্যমে ঘটে না, কোনো কারাগারের দেয়ালে ঘটে না, কোনো গুলির শব্দে ঘটে না। এই হত্যা ঘটে নীরবে, কাগজে, তালিকায়, ফাইলের ভেতর। কিন্তু এর ফলাফল একই—একজন নাগরিক রাষ্ট্রের চোখে মৃত হয়ে যায়। ভোটহীন মানুষ মানে মৃত নাগরিক; কারণ আধুনিক গণতন্ত্রে নাগরিকের জীবনের একমাত্র কার্যকর প্রকাশ হলো ভোট।
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব কোনো কেবল আইনি মর্যাদা নয়, এটি একটি সক্রিয় রাজনৈতিক অস্তিত্ব। নাগরিক বেঁচে থাকে কারণ সে ভোট দিতে পারে, মত দিতে পারে, ক্ষমতা বদলাতে পারে। ভোটাধিকারই নাগরিকের সেই শেষ অস্ত্র, যার মাধ্যমে সে রাষ্ট্রকে বাধ্য করতে পারে তাকে গণ্য করতে। যখন সেই অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়, নাগরিক বেঁচে থেকেও রাষ্ট্রের কাছে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই অদৃশ্যকরণই রাজনৈতিক হত্যা—যেখানে দেহ বেঁচে থাকে, কিন্তু অধিকার মরে যায়।
ইতিহাসে রাজনৈতিক হত্যা সবসময় শাসনের প্রথম শর্ত ছিল। একনায়কতন্ত্রে এই হত্যা হতো সরাসরি—কারাবরণ, নির্বাসন, ফাঁসি। আধুনিক কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রে এই হত্যা আরও উন্নত ও নিখুঁত—এটি ঘটে প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। নাগরিককে মেরে ফেলতে হয় না; তাকে ভোটের বাইরে ঠেলে দিলেই যথেষ্ট। সে তখন জীবিত, কিন্তু রাজনৈতিকভাবে মৃত।
ভোটাধিকার ছাড়া মানুষ রাষ্ট্রের কাছে আর কোনো গুরুত্ব বহন করে না। রাষ্ট্র তখন তার কথা শোনে না, তার দাবি শোনে না, তার কষ্টের হিসাব রাখে না। কারণ সে আর শাসনের গণিতে নেই। রাষ্ট্র শাসন করে যাদের ভোট আছে, যাদের ভোটের ভয় আছে। যাদের ভোট নেই, তারা রাষ্ট্রের জন্য কেবল পরিসংখ্যান। এই কারণেই ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া মানে নাগরিককে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সমাজ থেকে মুছে ফেলা।
এই মুছে ফেলার প্রক্রিয়া আজ আর প্রকাশ্যে ঘটে না। এটি ঘটে তালিকা দিয়ে। ভোটার তালিকা আধুনিক রাষ্ট্রে মৃত্যুর তালিকা হিসেবেও কাজ করে—যেখানে নাম থাকলে নাগরিক জীবিত, নাম না থাকলে মৃত। এই মৃত্যু এতটাই নীরব যে নাগরিক নিজেও বুঝতে পারে না কখন সে মারা গেছে। একদিন সে ভোট দিতে যায়, দেখে তার নাম নেই—সেই মুহূর্তেই তার রাজনৈতিক মৃত্যু সম্পন্ন হয়।
এই রাজনৈতিক হত্যার সবচেয়ে ভয়ংকর দিক হলো এটি অপরাধ বলে গণ্য হয় না। রাষ্ট্র বলে—এটি প্রশাসনিক ত্রুটি, সংশোধনযোগ্য ভুল, নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। এই ভাষা হত্যাকে বৈধ করে তোলে। নাগরিক তখন আর বিচার চায় না; সে সংশোধনের আবেদন করে। রাষ্ট্র হত্যা করে, নাগরিক আবেদন করে—এই অসম সম্পর্কই আধুনিক দমনের চূড়ান্ত রূপ।
ভোটাধিকার হরণ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; এটি একটি কাঠামোগত প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া সবচেয়ে বেশি আঘাত হানে সেই জনগোষ্ঠীর ওপর, যারা সামাজিকভাবে দুর্বল। পরিযায়ী শ্রমিকেরা কাজের জন্য বাইরে থাকেন, নারীরা বিয়ের পরে ঠিকানা বদলান, দরিদ্র মানুষের কাগজপত্র নেই, সংখ্যালঘুদের পরিচয় সন্দেহের চোখে দেখা হয়। রাষ্ট্র এই বাস্তবতাগুলোকে অপরাধে রূপান্তর করে এবং সেই অপরাধের শাস্তি দেয় ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে¹।
এই রাজনৈতিক হত্যা সবচেয়ে ভয়ংকর হয়ে ওঠে যখন তা নির্বাচন-পূর্ব সময়ে ঘটে। তখন নাগরিকের হাতে সময় নেই, লড়াইয়ের শক্তি নেই, আইনি পথ নেই। নির্বাচন শেষ হয়ে যায়, আর নাগরিক পাঁচ বছর ধরে মৃত থাকে। সে বেঁচে থাকে, কিন্তু রাষ্ট্রের জন্য তার অস্তিত্ব নেই। এই পাঁচ বছর রাষ্ট্র তার নামে আইন বানায়, ট্যাক্স নেয়, নীতি বানায়, কিন্তু নাগরিক কিছুই করতে পারে না। এটি জীবন্ত মৃতের শাসন।
ভোটাধিকার হরণের মাধ্যমে রাষ্ট্র শুধু ব্যক্তিকে হত্যা করে না, সমাজকেও হত্যা করে। কারণ গণতন্ত্র ব্যক্তির সমষ্টি। যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ ভোটের বাইরে চলে যায়, তখন গণতন্ত্র আর জনগণের শাসন থাকে না; হয়ে ওঠে নির্বাচিত জনগোষ্ঠীর শাসন। এই নির্বাচিত জনগোষ্ঠী সাধারণত সুবিধাভোগী, মধ্যবিত্ত, উচ্চবর্ণ, ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা মানুষ। দরিদ্র ও প্রান্তিকরা তখন রাষ্ট্রের বাইরে পড়ে যায়। এই রাষ্ট্র আর গণতান্ত্রিক থাকে না; এটি হয়ে ওঠে প্রশাসনিক অভিজাততন্ত্র।
এই রাজনৈতিক হত্যার আরেকটি স্তর হলো আত্মসম্মানের মৃত্যু। ভোট দিতে না পারা মানে নাগরিক নিজেকে আর নাগরিক মনে করতে পারে না। সে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে পারে না, বুথে ঢুকতে পারে না, নিজের আঙুলে কালি দেখতে পারে না। এই ছোট ছোট প্রতীকগুলো নাগরিকের অস্তিত্বের অংশ। যখন এগুলো কেড়ে নেওয়া হয়, তখন নাগরিক ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়ে। সে নিজেকে রাষ্ট্রের বাইরে মানুষ বলে ভাবতে শুরু করে। এই মানসিক মৃত্যু রাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে লাভজনক, কারণ মৃত মানুষ আর প্রশ্ন করে না।
গণতন্ত্রে ভোট শুধু একটি পছন্দ নয়, এটি একটি স্বীকৃতি। রাষ্ট্র নাগরিককে স্বীকার করে যখন সে তাকে ভোট দিতে দেয়। ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া মানে রাষ্ট্র নাগরিককে অস্বীকার করে। এই অস্বীকৃতিই রাজনৈতিক হত্যা—যেখানে নাগরিককে বলা হয়: তুমি আছো, কিন্তু আমাদের জন্য তুমি নেই।
এই প্রক্রিয়া সবচেয়ে বিপজ্জনক কারণ এটি আইনসম্মত দেখায়। কোনো আইন ভাঙা হয় না, কোনো সংবিধান সংশোধন করা হয় না। কেবল তালিকা সংশোধন হয়। কিন্তু এই তালিকার সংশোধনই নাগরিকত্বের সংশোধন হয়ে যায়। রাষ্ট্র এইভাবে আইন ভাঙা ছাড়াই সংবিধানের আত্মাকে হত্যা করে।
এই রাজনৈতিক হত্যার ইতিহাস নতুন নয়। ফ্যাসিস্ট ইতালিতে ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে বিরোধীদের অদৃশ্য করা হয়েছিল। নাৎসি জার্মানিতে ইহুদিদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার প্রথম ধাপ হিসেবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের ভোটাধিকার সংকুচিত করা হয়েছিল বর্ণবাদী শাসনের ভিত্তি হিসেবে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই হত্যার শুরু হয়েছিল তালিকা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, নিয়ম দিয়ে।
ভারতে আজ এই হত্যার রূপ আরও সূক্ষ্ম। এখানে কাউকে অ-নাগরিক ঘোষণা করা হয় না; তাকে কেবল ভোটার বলা হয় না। এই নীরবতা রাষ্ট্রের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। কারণ যেখানে হত্যার শব্দ নেই, সেখানে প্রতিবাদের ভাষাও জন্মায় না।
এই রাজনৈতিক হত্যা আদালতের চোখে অপরাধ নয়, প্রশাসনের চোখে সমস্যা নয়, মিডিয়ার চোখে খবর নয়। কিন্তু নাগরিকের চোখে এটি জীবনের শেষ দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া। এই দরজা বন্ধ হলে নাগরিক আর রাষ্ট্রের সঙ্গে কথা বলতে পারে না। সে তখন কেবল শাসিত হয়।
এই কারণেই ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া মানে রাজনৈতিক হত্যা। কারণ নাগরিক বেঁচে থাকলেও রাষ্ট্রের কাছে সে মৃত। তার কণ্ঠ নেই, তার উপস্থিতি নেই, তার ভয় নেই। রাষ্ট্র তখন একা কথা বলে, একা সিদ্ধান্ত নেয়, একা শাসন করে।
এই প্রবন্ধের মূল কথা তাই নির্মমভাবে সরল—ভোট ছাড়া মানুষ মানুষ থাকলেও নাগরিক থাকে না। আর নাগরিক ছাড়া গণতন্ত্র থাকে না। যে রাষ্ট্র ভোটাধিকার কেড়ে নেয়, সে জনগণকে হত্যা করে—নীরবে, নিয়মতান্ত্রিকভাবে, প্রশাসনিক ভাষায়। এই হত্যাই আধুনিক রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় অপরাধ, কারণ এটি আইনের আড়ালে ঘটে, আর নৈতিকতার বাইরে থাকে।
এই হত্যাকে যদি আমরা হত্যা বলে না চিহ্নিত করি, তবে আমরা নিজেরাই এই মৃত্যুর অংশীদার হয়ে যাই। কারণ রাজনৈতিক মৃত্যু তখন স্বাভাবিক হয়ে যায়। আর যেখানে মৃত্যু স্বাভাবিক, সেখানে স্বাধীনতা অসম্ভব।
এসআইআর ও বিরোধী ভোটার দমন
রাষ্ট্র যখন ভোটার তালিকার নামে কোনো প্রক্রিয়া চালায়, তখন তার প্রভাব কখনো সমানভাবে পড়ে না। ভোটার তালিকা কখনোই নিরপেক্ষ মাঠ নয়—এটি ক্ষমতার মানচিত্র। কারা বাদ পড়বে, কারা থাকবে, কারা লাভবান হবে—এই সব প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে থাকে রাষ্ট্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায়। এসআইআর (Special Intensive Revision) প্রক্রিয়াও তার ব্যতিক্রম নয়। বরং এই প্রক্রিয়াই সবচেয়ে স্পষ্টভাবে দেখায়, কীভাবে প্রশাসনিক ভাষার আড়ালে বিরোধী ভোটার দমন ঘটে, এবং কীভাবে এই দমন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক লাভে পরিণত হয়।
এসআইআর-এর প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো—এটি কখনোই সমাজের সব স্তরকে সমানভাবে প্রভাবিত করে না। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া একটি সামাজিকভাবে বাছাই করা প্রক্রিয়া। যারা স্থায়ী, সচ্ছল, নথিপূর্ণ, শহুরে, প্রশাসনের সঙ্গে সংযুক্ত—তারা তালিকায় থেকে যায়। আর যারা অস্থায়ী, দরিদ্র, পরিযায়ী, সংখ্যালঘু, গ্রামীণ বা বস্তিবাসী—তারাই বাদ পড়ে। এই বাছাই কাকতাল নয়, কারণ ভারতের রাজনৈতিক বাস্তবতায় এই বাদ পড়া জনগোষ্ঠীগুলোই বিরোধী রাজনীতির মূল ভরকেন্দ্র।
ভারতের নির্বাচনী সমাজতত্ত্ব বহুবার দেখিয়েছে, দরিদ্র, সংখ্যালঘু, পরিযায়ী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সাধারণত ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে নয়; তারা বিরোধী দলকেই ভোট দেয়। কারণ ক্ষমতাসীন রাজনীতি তাদের কাছে শাসনের অভিজ্ঞতা, আর বিরোধী রাজনীতি তাদের কাছে প্রতিবাদের ভাষা। ফলে এই জনগোষ্ঠীর ভোটার তালিকা সংকুচিত করা মানে বিরোধী ভোট সংকুচিত করা। এসআইআর এখানে প্রশাসনিক নয়, এটি নির্বাচনী প্রকৌশল।
এসআইআর-এর সময় সবচেয়ে বেশি বাদ পড়ে পরিযায়ী শ্রমিকরা। ভারতের প্রায় ৪৫ কোটি মানুষ জীবনের কোনো না কোনো সময়ে পরিযায়ী শ্রমিক। এরা কাজের জন্য এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে যায়, মাসের পর মাস ঘরে থাকে না। BLO যখন যাচাই করতে আসে, তারা অনুপস্থিত থাকে। প্রশাসনিক ভাষায় তারা “স্থানান্তরিত” বা “পাওয়া যায়নি” হয়ে যায়। কিন্তু রাজনৈতিক বাস্তবতায় এরা সেই জনগোষ্ঠী যারা শহরের বস্তিতে থাকে, অস্থায়ী কাজ করে, এবং ভোট দেয় বিরোধী শক্তিকে। এই বাদ পড়া সরাসরি বিরোধী ভোট কমিয়ে দেয়।
নারীদের ক্ষেত্রে এসআইআর আরও নির্দিষ্টভাবে কাজ করে। বিয়ের পরে ঠিকানা বদল, নামের বানান বদল, বয়সের নথি না থাকা—এই সব কারণে নারীদের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ার হার বেশি। বহু গবেষণায় দেখা গেছে, ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় পুরুষদের নাম থেকে গেলেও নারীদের নাম বাদ পড়েছে। রাজনৈতিকভাবে এটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ নারীদের ভোটিং প্যাটার্ন অনেক রাজ্যে ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে গেছে। ফলে এই বাদ পড়া একটি নীরব রাজনৈতিক লাভে পরিণত হয়।
মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এসআইআর আরও ভয়ংকর রূপ নেয়। মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় যাচাই বেশি কড়াকড়ি হয়, BLO-এর সন্দেহ বেশি, প্রতিবেশী রিপোর্ট বেশি নেতিবাচক হয়। এই সামাজিক পক্ষপাত প্রশাসনিক নথিতে ঢুকে পড়ে। রাষ্ট্র সরাসরি কাউকে টার্গেট করে না, কিন্তু প্রক্রিয়াটি এমনভাবে তৈরি যে সংখ্যালঘুরাই সবচেয়ে বেশি বাদ পড়ে। এই বাদ পড়া রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত কার্যকর, কারণ এই জনগোষ্ঠী ঐতিহাসিকভাবে বিরোধী রাজনীতির মূল ভোটব্যাংক।
গ্রামীণ দরিদ্র ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও একই চিত্র দেখা যায়। তাঁদের কাগজ নেই, ঠিকানা স্থায়ী নয়, প্রশাসনিক অফিসে যাওয়ার ক্ষমতা নেই। ফলে তাঁরা আপিল করতে পারেন না, সংশোধন করতে পারেন না। তাঁদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া মানে সেই এলাকার রাজনৈতিক ভারসাম্য বদলে যাওয়া। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যে বুথগুলোতে বিরোধী দল শক্তিশালী ছিল, সেখানে এসআইআর-এর পরে ভোটার সংখ্যা হঠাৎ কমে গেছে।
এই বাদ পড়ার রাজনীতির বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকে একটি ছোট কিন্তু শক্তিশালী জনগোষ্ঠী—যারা লাভবান হয়। তারা হলো শহুরে মধ্যবিত্ত, উচ্চবর্ণ, স্থায়ী চাকুরিজীবী, প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত মানুষ। তাদের নথি আছে, ঠিকানা আছে, BLO-এর সঙ্গে সম্পর্ক আছে, সময় আছে আপিল করার। এই জনগোষ্ঠী সাধারণত ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ঘনিষ্ঠ। ফলে এসআইআর তাঁদের ছোঁয় না। এই বৈষম্যই এসআইআর-এর রাজনৈতিক ফলাফল নির্ধারণ করে।
এসআইআর তাই শুধু বাদ পড়ার প্রক্রিয়া নয়; এটি নির্বাচনী ভারসাম্য পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া। যারা বাদ পড়ে, তারা সাধারণত বিরোধী ভোটার। যারা থেকে যায়, তারা সাধারণত ক্ষমতাসীনদের ভোটার। এই অদৃশ্য ভারসাম্য বদলই এসআইআর-এর প্রকৃত কাজ। এই কারণেই এসআইআর কখনোই সমানভাবে হয় না, এবং কখনোই নিরপেক্ষ ফল দেয় না।
এই প্রক্রিয়ার সবচেয়ে বড় শক্তি হলো—এটি আইনি দেখায়। আদালতে গেলে বলা যায়—নিয়ম মেনেই করা হয়েছে, নির্দেশিকা মেনে করা হয়েছে। কিন্তু আইন এখানে ন্যায়বিচারের বাহন নয়; আইন এখানে ক্ষমতার বাহন। রাষ্ট্র জানে, বিরোধী ভোটারদের সরাসরি দমন করলে প্রতিরোধ হবে। কিন্তু তালিকা বদলে দিলে প্রতিরোধ হয় না। নাগরিক জানতেই পারে না যে সে দমন হচ্ছে। এই নীরবতাই রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় জয়।
এসআইআর-এর সঙ্গে মিডিয়ার ভূমিকা এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মিডিয়া যখন বলে “ভুয়া ভোটার বাদ দেওয়া হয়েছে”, তখন নাগরিক নিজের বাদ পড়াকেও অপরাধ হিসেবে ভাবতে শুরু করে। রাষ্ট্র এই ভাষা ব্যবহার করে দমনকে নৈতিক করে তোলে। বিরোধী ভোটার তখন শুধু বাদ পড়েন না; তিনি লজ্জিতও হন। এই মানসিক দমন শারীরিক দমনের চেয়েও কার্যকর।
এই পুরো প্রক্রিয়ায় বিরোধী দল কার্যত অচল হয়ে পড়ে। কারণ তাদের ভোটার তালিকা সংকুচিত, তাদের সমর্থকরা বাদ পড়া, তাদের অভিযোগ প্রশাসনিকভাবে অগ্রাহ্য। বিরোধী দল তখন মাঠে ভোটের জন্য লড়তে পারে না, কারণ ভোটারই নেই। এটি গণতন্ত্রের একটি কাঠামোগত ধ্বংস—যেখানে নির্বাচন হয়, কিন্তু প্রতিযোগিতা থাকে না।
আন্তর্জাতিকভাবে এই কৌশল নতুন নয়। যুক্তরাষ্ট্রে voter purge প্রক্রিয়া সবচেয়ে বেশি আঘাত করেছে আফ্রিকান–আমেরিকান ও লাতিনো ভোটারদের, যারা ডেমোক্র্যাটদের ভোট দেয়। হাঙ্গেরিতে, তুরস্কে, রাশিয়ায় ভোটার তালিকা ও নিবন্ধন প্রক্রিয়া ব্যবহার করে বিরোধী ভোট সংকুচিত করা হয়েছে। সব ক্ষেত্রেই প্যাটার্ন এক—প্রশাসনিক ভাষা, নির্বাচনী টাইমিং, বিরোধী ভোটার বর্জন।
ভারতে এসআইআর সেই বৈশ্বিক ধারার অংশ। এখানে রাষ্ট্র সরাসরি বিরোধী দলকে নিষিদ্ধ করে না, নেতাকে গ্রেপ্তার করে না—সে কেবল ভোটারকে বাদ দেয়। এই বাদ পড়া নীরব, কিন্তু গভীর। এই বাদ পড়াই বিরোধী রাজনীতিকে পঙ্গু করে দেয়।
এই প্রক্রিয়ার সবচেয়ে ভয়ংকর দিক হলো—এটি দীর্ঘমেয়াদি। একবার ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়লে ফিরে আসা কঠিন। আবেদন, আপিল, প্রমাণ—এই সব পথ দরিদ্র মানুষের জন্য প্রায় অসম্ভব। ফলে এক নির্বাচনে বাদ পড়া মানে বহু নির্বাচনে বাদ পড়ে থাকা। এই দীর্ঘমেয়াদি বর্জনই বিরোধী রাজনীতির মৃত্যুদণ্ড।
এই কারণে এসআইআর কেবল একটি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নয়; এটি একটি রাজনৈতিক অস্ত্র, যার লক্ষ্য বিরোধী ভোটার দমন। কারা বাদ পড়ে, কারা লাভবান—এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে সামাজিক কাঠামোতে, নির্বাচনী মানচিত্রে, এবং রাষ্ট্রের নীরব কৌশলে। এসআইআর সেই কৌশলের সবচেয়ে কার্যকর রূপ।
এই বাস্তবতা বুঝতে পারলে স্পষ্ট হয়—ভোটার তালিকা আর কেবল তালিকা নয়। এটি ক্ষমতার মানচিত্র। আর যে রাষ্ট্র এই মানচিত্র আঁকে, সে নির্বাচনের ফল আগেই ঠিক করে ফেলে—আইন ভাঙা ছাড়াই, গণতন্ত্র ভাঙা ছাড়াই, কিন্তু গণতন্ত্রের প্রাণ কেটে দিয়ে।
গরিব, পরিযায়ী ও প্রান্তিক মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
রাষ্ট্র যখন যুদ্ধ করে, তখন তা সবসময় বন্দুক দিয়ে হয় না। আধুনিক রাষ্ট্র সবচেয়ে সফল যুদ্ধগুলো করে নথি দিয়ে, ফর্ম দিয়ে, নিয়ম দিয়ে, ডেটাবেস দিয়ে। এই যুদ্ধের শিকার হয় সেই মানুষগুলো, যাদের জীবন কাগজের বাইরে—গরিব, পরিযায়ী, প্রান্তিক, অস্থায়ী, নথিহীন মানুষ। এসআইআর সেই যুদ্ধের একটি নিখুঁত উদাহরণ, যেখানে ডকুমেন্ট নিজেই অস্ত্র হয়ে ওঠে, আর নাগরিকের জীবন সেই অস্ত্রের নিচে ক্ষতবিক্ষত হয়।
ভারতের সামাজিক বাস্তবতায় গরিব মানুষ মানেই নথিহীন মানুষ। জন্মের সময় জন্মসনদ হয়নি, স্কুলে ভর্তি হয়নি বলে বয়সের রেকর্ড নেই, জমি নেই বলে ঠিকানার দলিল নেই, কাজের জন্য ঘন ঘন জায়গা বদলায় বলে স্থায়ী ঠিকানা নেই। রাষ্ট্র এই বাস্তবতা জানে, কিন্তু নীতি তৈরি করে এমনভাবে, যেন এই বাস্তবতা অপরাধ। ডকুমেন্ট না থাকা মানে রাষ্ট্রের চোখে নাগরিক না হওয়া। এই রূপান্তরই আধুনিক দমনের সবচেয়ে নিষ্ঠুর কৌশল।
পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবন ডকুমেন্টের বিরুদ্ধে এক নিরন্তর লড়াই। ভারতের প্রায় ৪৫ কোটির বেশি মানুষ জীবনের কোনো পর্যায়ে পরিযায়ী শ্রমিক¹। তারা কাজের জন্য গ্রাম ছেড়ে শহরে যায়, রাজ্য ছাড়ে, মাসের পর মাস বাড়ি ফেরে না। তাদের জীবনের কেন্দ্র স্থির নয়, কিন্তু রাষ্ট্রের ডকুমেন্ট স্থিরতা দাবি করে। ভোটার তালিকার মতো নথিতে “স্থায়ী ঠিকানা” একটি মৌলিক শর্ত। ফলে পরিযায়ী শ্রমিকের জীবনযাপনই তাকে অযোগ্য করে তোলে। BLO যখন যাচাই করতে আসে, সে থাকে না। প্রশাসনিক ভাষায় সে “অনুপস্থিত” হয়ে যায়। বাস্তবে সে কাজ করছে, রাষ্ট্রের অর্থনীতি চালাচ্ছে, কিন্তু রাজনৈতিকভাবে সে অদৃশ্য।
এই অদৃশ্যকরণ কাকতাল নয়। পরিযায়ী শ্রমিকরা সাধারণত শহরের প্রান্তে, বস্তিতে, অস্থায়ী কলোনিতে থাকে। এই জায়গাগুলোতেই ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় সবচেয়ে বেশি নাম বাদ পড়ে। কারণ BLO-রা সেখানে যেতে চান না, সময় দেন না, বা নিরাপত্তার অজুহাত দেন। এই অবহেলা পরে প্রশাসনিক রিপোর্টে রূপ নেয়—যেখানে লেখা হয় “পাওয়া যায়নি”, “ঠিকানা ভুল”, “স্থানান্তরিত”। এই শব্দগুলোই নাগরিকের রাজনৈতিক মৃত্যু ঘোষণা করে।
গরিব মানুষের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ আরও ভয়ংকর কারণ তাদের লড়াইয়ের সামর্থ্য নেই। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়লে ধনী মানুষ আপিল করে, আইনজীবী নেয়, অফিসে যায়, সময় দেয়। গরিব মানুষ তা পারে না। সে দিনে দিনে কাজ করে, কাজ না করলে খায় না। প্রশাসনিক লড়াই তার জন্য বিলাসিতা। রাষ্ট্র এই অসাম্য জানে, এবং সেই অসাম্যকেই অস্ত্র বানায়। ডকুমেন্ট এখানে কেবল প্রমাণ নয়—এটি শ্রেণিগত অস্ত্র।
এই যুদ্ধের আরেকটি বড় শিকার হলো শহুরে বস্তিবাসী। বস্তি মানেই অস্থায়ী, অবৈধ, অনিশ্চিত—রাষ্ট্রের চোখে। কিন্তু বস্তিবাসীরাই শহরের শ্রমশক্তি। তবু ভোটার তালিকার সময় এই মানুষগুলোকেই প্রথম সন্দেহ করা হয়। ঠিকানা বদল, ঘর ভাঙা, পুনর্বাসন, উচ্ছেদ—এই সব কারণে তাদের নথি বারবার বদলায়। প্রশাসনিক ডেটাবেস এই গতিশীল জীবনকে ধরতে পারে না। ফলে তালিকায় তারা ভুল হয়ে যায়, আর ভুল মানেই বাদ।
এই বাদ পড়া একটি সামাজিক নিপীড়নের ধারাবাহিকতা। কারণ গরিব মানুষ রাষ্ট্রের কাছে আগে থেকেই সন্দেহজনক। এসআইআর সেই সন্দেহকে নথিতে পরিণত করে। “ডকুমেন্ট নেই” কথাটি এখানে “তুমি নেই” হয়ে যায়। এই ভাষাগত রূপান্তরই রাজনৈতিক হত্যার প্রথম ধাপ।
প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এই যুদ্ধ আরও নির্মম। আদিবাসী মানুষদের কাছে জন্মসনদ, ঠিকানা, বয়সের নথি—এই সব ধারণাই নতুন। তাদের জীবনে ভূমি মানে বন, ঘর মানে প্রকৃতি, ঠিকানা মানে গোত্র। কিন্তু রাষ্ট্র এই সাংস্কৃতিক বাস্তবতা অস্বীকার করে কাগজের বাস্তবতা চাপিয়ে দেয়। ফলে আদিবাসী নাগরিকেরা ভোটার তালিকায় বারবার “ভুল” হয়ে যায়²। এই ভুলের শাস্তি ভোটাধিকার হরণ, এবং শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক নিশ্চিহ্নতা।
এই যুদ্ধের ভয়ংকর দিক হলো—এটি রাষ্ট্রের চোখে যুদ্ধ নয়। রাষ্ট্র বলে—এটি নিয়ম, এটি যাচাই, এটি সংশোধন। কিন্তু যারা বাদ পড়ে, তাদের কাছে এটি অস্তিত্বের যুদ্ধ। কারণ ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া মানে কেবল ভোট হারানো নয়; মানে রাষ্ট্রের সঙ্গে সব সম্পর্ক হারানো। এই সম্পর্কহীনতাই আধুনিক রাষ্ট্রে সবচেয়ে বড় শাস্তি।
ডকুমেন্ট যখন অস্ত্র হয়ে ওঠে, তখন নাগরিকের শরীরই যুদ্ধক্ষেত্র। নামের বানান, বয়সের সংখ্যা, ঠিকানার লাইন—এই সব ছোটখাটো ত্রুটি বড় অপরাধে রূপ নেয়। রাষ্ট্র এখানে ভুল ধরার অজুহাতে মানুষ বাদ দেয়। এই বাদ দেওয়া কখনোই সমানভাবে হয় না; এটি সবসময় নিচের দিকে আঘাত করে। ডকুমেন্টের যুদ্ধ সবসময় গরিবের বিরুদ্ধে।
এই যুদ্ধের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো—এটি নীরব। কেউ গ্রেপ্তার হয় না, কেউ গুলি খায় না, কেউ রাস্তায় পড়ে থাকে না। কেবল একটি তালিকা বদলায়। কিন্তু এই তালিকার বদল মানে জীবনের বদল। মানুষ ভোট দিতে পারে না, প্রকল্প পায় না, পরিচয় হারায়, রাষ্ট্রের কাছে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই অদৃশ্য মৃত্যু রাষ্ট্রের সবচেয়ে সফল যুদ্ধ।
এসআইআর প্রক্রিয়া এই যুদ্ধকে আরও প্রাতিষ্ঠানিক করে তোলে। এখানে BLO, জেলা অফিস, কমিশন—সবাই নিয়ম মেনে কাজ করে। কিন্তু এই নিয়মগুলোই যুদ্ধের কৌশল। যুদ্ধ এখানে ঘোষণাহীন, কিন্তু ফলাফল স্পষ্ট—গরিব ও প্রান্তিক মানুষ বাদ পড়ে, ক্ষমতাবানরা থেকে যায়।
এই যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—এটি ভবিষ্যতের জন্য মানুষকে প্রস্তুত করে। ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া মানুষ ধীরে ধীরে নাগরিকত্বের অন্যান্য ক্ষেত্র থেকেও বাদ পড়ে। আজ ভোট নেই, কাল রেশন নেই, পরশু স্বাস্থ্য নেই, তারপর বাসস্থান নেই। ডকুমেন্টের একটিমাত্র ভুল জীবনকে ধাপে ধাপে রাষ্ট্রের বাইরে ঠেলে দেয়³। এসআইআর সেই প্রথম ধাপ, যেখানে রাষ্ট্র মানুষকে শত্রু না বানিয়ে অদৃশ্য করে দেয়।
এই যুদ্ধের আরেকটি ভয়ংকর দিক হলো—মানুষ নিজেরাই নিজেদের দোষী ভাবতে শুরু করে। ডকুমেন্ট নেই মানে নিজের ব্যর্থতা, নিজের লজ্জা। রাষ্ট্র এই লজ্জাকে ব্যবহার করে। মানুষ আর প্রতিবাদ করে না, আবেদন করে। প্রতিবাদ রাজনীতি, আবেদন প্রশাসন। রাষ্ট্র সবসময় প্রশাসন চায়, রাজনীতি নয়।
এই প্রক্রিয়া আন্তর্জাতিকভাবেও পরিচিত। যুক্তরাষ্ট্রে voter ID laws দরিদ্র ও আফ্রিকান-আমেরিকান জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে⁴। ব্রাজিলে পরিযায়ী ও গরিব মানুষদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ঠিকানা যাচাইয়ের নামে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ডকুমেন্ট ব্যবহার করে কৃষ্ণাঙ্গদের নাগরিকত্ব সীমিত করা হয়েছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ডকুমেন্ট যুদ্ধের অস্ত্র।
ভারতের ক্ষেত্রে এই যুদ্ধ আরও ভয়ংকর, কারণ এখানে জনসংখ্যা বিপুল, দারিদ্র্য গভীর, পরিযান ব্যাপক। রাষ্ট্র যদি ডকুমেন্টকে অস্ত্র বানায়, তবে কোটি কোটি মানুষ সেই অস্ত্রের আঘাতে পড়ে। এসআইআর সেই আঘাতের একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ।
এই যুদ্ধের লক্ষ্য শুধু ভোটাধিকার নয়; লক্ষ্য নাগরিকত্বের পুনর্গঠন। কে থাকবে, কে থাকবে না—এই সিদ্ধান্ত রাষ্ট্র ডকুমেন্টের মাধ্যমে নেয়। আর যে নাগরিক ডকুমেন্ট দিতে পারে না, সে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের শত্রুতে পরিণত হয়, যদিও সে কোনো অপরাধ করেনি।
এই বাস্তবতা বুঝতে পারলে স্পষ্ট হয়—এসআইআর কোনো প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নয়, এটি গরিব ও প্রান্তিক মানুষের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধ। এই যুদ্ধে বন্দুক নেই, কিন্তু ক্ষত আছে; সেনা নেই, কিন্তু মৃত্যু আছে; রক্ত নেই, কিন্তু নিঃশব্দ নিধন আছে।
এই যুদ্ধ থামানো না গেলে গণতন্ত্র থাকবে না। কারণ গণতন্ত্র গরিবের ভোটে জন্মায়। আর যে রাষ্ট্র গরিবকে ভোট দিতে দেয় না, সে রাষ্ট্র আর জনগণের রাষ্ট্র থাকে না। সে হয়ে ওঠে নথির রাষ্ট্র—যেখানে মানুষ নয়, কাগজই নাগরিক।
নারীদের নাম মুছে যাওয়ার ইতিহাস
রাষ্ট্রের ইতিহাসে নারীদের নাম মুছে যাওয়ার ঘটনা কখনোই হঠাৎ ঘটে না। এটি একটি দীর্ঘ, নীরব, প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া—যেখানে ঘরের ভেতরের বৈষম্য ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অংশ হয়ে ওঠে। এসআইআর (Special Intensive Revision) সেই প্রক্রিয়াকে আরও স্পষ্ট ও দৃশ্যমান করেছে। ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে নারীদের নাম বাদ পড়া কোনো প্রশাসনিক দুর্ঘটনা নয়; এটি শতাব্দীপ্রাচীন লিঙ্গবৈষম্যের আধুনিক রূপ, যেখানে নারীকে প্রথমে পরিবারে অদৃশ্য করা হয়, তারপর রাষ্ট্রে।
ভারতের সমাজব্যবস্থায় নারীর পরিচয় ঐতিহাসিকভাবে পরোক্ষ। সে কন্যা, স্ত্রী, মা—কিন্তু স্বাধীন নাগরিক নয়। তার ঠিকানা বদলায় বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে, নাম বদলায় স্বামীর পরিচয়ে, বয়সের হিসাব থাকে না, জন্মের নথি থাকে না। এই সামাজিক বাস্তবতাকে রাষ্ট্র জানে, কিন্তু নীতি তৈরি করে এমনভাবে, যেন নারী নিজেই তার অনুপস্থিতির জন্য দায়ী। ভোটার তালিকার মতো নথিতে “স্থায়ী ঠিকানা”, “অবিচ্ছিন্ন বাসস্থান”, “স্বতন্ত্র পরিচয়” এই সব শর্ত নারীর জীবনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ফলে এসআইআর প্রক্রিয়ায় নারীরা সবচেয়ে বেশি বাদ পড়ে—নীরবে, অদৃশ্যভাবে।
এই বাদ পড়ার ইতিহাস কোনো একদিনের নয়। স্বাধীনতার পর থেকেই দেখা গেছে, ভোটার তালিকায় পুরুষদের তুলনায় নারীদের নাম কম, ভুল বেশি, বাদ পড়ার হার বেশি। ১৯৭০ ও ৮০-এর দশকে গ্রামীণ ভারতের বহু এলাকায় নারীদের ভোটার হিসেবে গণনা করা হতোই না, কারণ তাদের নাম পরিবারের পুরুষের অধীনে লেখা হতো। আধুনিক ডিজিটাল যুগেও সেই বৈষম্য বদলায়নি, কেবল রূপ বদলেছে। আজ নারী বাদ পড়ে বানানভুলে, বয়সের অমিলের কারণে, ঠিকানা না মেলায়, বিয়ের পরে নথি আপডেট না করার কারণে। রাষ্ট্র এই সামাজিক বাস্তবতাকে সংশোধনের চেষ্টা না করে, তাকে অপরাধে রূপান্তর করে।
এসআইআর-এর সময় এই বৈষম্য আরও প্রাতিষ্ঠানিক হয়। BLO যখন বাড়ি বাড়ি যাচাই করতে আসে, তখন পুরুষ সদস্যের সঙ্গে কথা বলে, পুরুষের নথি দেখে, পুরুষের বক্তব্যকে সত্য ধরে নেয়। নারী তখন ঘরের ভেতরে থাকে, কাজ করে, বা উপস্থিত থাকলেও তার বক্তব্য গুরুত্ব পায় না। বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, BLO পুরুষের কথায় নারীকে “স্থানান্তরিত”, “বিয়ে হয়ে গেছে”, “এখানে থাকে না” বলে চিহ্নিত করেছেন—যদিও নারী সেই বাড়িতেই থাকেন। এই সামাজিক পক্ষপাত প্রশাসনিক রিপোর্টে ঢুকে পড়ে, আর রিপোর্টই পরে রাষ্ট্রীয় সত্য হয়ে যায়¹।
নারীদের নাম বাদ পড়ার সবচেয়ে বড় কারণ বিয়ে। ভারতের প্রায় ৮০ শতাংশ নারী বিয়ের পরে ঠিকানা বদলান। কিন্তু ভোটার তালিকা সেই পরিবর্তনের জন্য সহজ পথ দেয় না। নতুন জায়গায় নাম তোলার প্রক্রিয়া জটিল, সময়সাপেক্ষ, পুরুষ-নির্ভর। অনেক নারী এই প্রক্রিয়া জানেন না, বা জানলেও করতে পারেন না। ফলে এক তালিকা থেকে নাম কেটে যায়, নতুন তালিকায় ওঠে না। এই শূন্যতার সময়েই নারী রাজনৈতিকভাবে অদৃশ্য হয়ে যান। রাষ্ট্র এই শূন্যতাকে পূরণ করে না; বরং তাকে স্থায়ী করে।
শহুরে নারীদের ক্ষেত্রেও এই বৈষম্য ভিন্নভাবে কাজ করে। চাকরি, শিক্ষা, বাসস্থান—এই সব কারণে তারা ঘন ঘন ঠিকানা বদলান। কিন্তু ভোটার তালিকার ডেটাবেস এই গতিশীল জীবনকে ধরতে পারে না। ডিজিটাল যাচাইয়ে নাম মেলে না, ঠিকানা মেলে না, ফলে নারী বাদ পড়ে। এই বাদ পড়া শহুরে মধ্যবিত্ত নারীদের মধ্যেও ব্যাপক, কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে লড়াইয়ের ক্ষমতা কিছুটা বেশি। দরিদ্র নারীদের ক্ষেত্রে এই বাদ পড়া প্রায় স্থায়ী।
এই প্রক্রিয়া নারীর রাজনৈতিক অস্তিত্বকে ধ্বংস করে। ভোট দিতে না পারা মানে নারী আর নাগরিক নয়—সে আবার কেবল পরিবারের সদস্যে পরিণত হয়। রাষ্ট্র এখানে পরিবারের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোকে শক্তিশালী করে। নারী রাষ্ট্রের সঙ্গে কথা বলতে পারে না, কারণ রাষ্ট্র তাকে স্বীকারই করে না। এই অস্বীকৃতি নারীর স্বাধীনতার ওপর সরাসরি আঘাত।
এসআইআর-এর সময় নারীদের বাদ পড়া শুধু একটি সংখ্যাগত সমস্যা নয়; এটি একটি কাঠামোগত সহিংসতা। কারণ নারীর ভোট মানে শুধু একটি ভোট নয়—এটি নারীর কণ্ঠস্বর, তার শরীরের ওপর অধিকার, তার জীবনের সিদ্ধান্তের অধিকার। যখন রাষ্ট্র এই ভোট কেড়ে নেয়, তখন নারীকে আবার পুরুষের ছায়ায় ঠেলে দেয়। এই প্রক্রিয়া ঘরোয়া বৈষম্যকে রাষ্ট্রীয় বৈষম্যে রূপান্তর করে।
বহু গবেষণায় দেখা গেছে, ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় পুরুষদের তুলনায় নারীদের নাম বাদ পড়ার হার বেশি²। কিন্তু এই তথ্য কখনোই রাষ্ট্রীয় আলোচনার কেন্দ্রে আসে না। কারণ নারী বাদ পড়া রাষ্ট্রের জন্য রাজনৈতিকভাবে সুবিধাজনক। নারী ভোটিং প্যাটার্ন বহু রাজ্যে ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে গেছে—বিশেষত সামাজিক নিরাপত্তা, মূল্যবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রশ্নে। ফলে নারীর ভোট কমে গেলে রাজনৈতিক প্রতিরোধও কমে।
এই নীরব ইতিহাসের আরেকটি দিক হলো—নারীরা নিজেরাও অনেক সময় বুঝতে পারেন না যে তাদের নাম বাদ পড়েছে। পরিবারে ভোটার তালিকা দেখার দায়িত্ব পুরুষের, ভোটের খবর রাখার দায়িত্ব পুরুষের। নারী ভোটের দিন জানতে পারেন, তার নাম নেই। তখন সংশোধনের সময় শেষ। এই বিলম্বই রাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র।
ডকুমেন্ট এখানে লিঙ্গীয় অস্ত্র হয়ে ওঠে। পুরুষের জীবনে নথি স্বাভাবিক, নারীর জীবনে নথি ব্যতিক্রম। রাষ্ট্র এই পার্থক্যকে অস্বীকার করে সমান নিয়ম চাপিয়ে দেয়, আর সেই সমান নিয়মই বৈষম্য তৈরি করে। এটি “নিরপেক্ষ বৈষম্য”—যেখানে নিয়ম সবাইকে সমানভাবে আঘাত করে, কিন্তু ফল অসমান হয়।
এই বৈষম্যের শিকড় গভীরে। জন্মসনদ না থাকা, স্কুলের রেকর্ড না থাকা, সম্পত্তির কাগজ না থাকা—এই সব নারীর ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। কিন্তু ভোটার তালিকার সময় এই স্বাভাবিকতাই অপরাধে রূপ নেয়। রাষ্ট্র বলে—প্রমাণ দাও। নারী পারে না। ফলে সে বাদ পড়ে। এই বাদ পড়াই নারীর রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারাবাহিকতা—যেখানে নারী সবসময় তালিকার বাইরে।
এই নীরব ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকর দিক হলো—এটি অদৃশ্য। নারী বাদ পড়লেও পরিবারে আলোচনা হয় না, মিডিয়ায় খবর হয় না, আদালতে মামলা হয় না। কারণ নারী নিজেই অভ্যস্ত—তার নাম বাদ পড়া মানে কিছু না। রাষ্ট্র এই নীরবতাকে ব্যবহার করে। এই নীরবতা ভাঙা না গেলে নারীর রাজনৈতিক মৃত্যু চলতেই থাকবে।
আন্তর্জাতিকভাবে এই প্যাটার্ন পরিচিত। বহু দেশে voter registration প্রক্রিয়ায় নারীরা বেশি বাদ পড়ে, কারণ তাদের নথি কম, চলাচল বেশি, পরিচয় বদলায় বেশি। কিন্তু ভারতে এই সমস্যা আরও গভীর, কারণ এখানে লিঙ্গবৈষম্য সামাজিকভাবে স্বীকৃত। রাষ্ট্র সেই স্বীকৃতিকে নথিতে পরিণত করে।
এসআইআর তাই শুধু ভোটার তালিকার প্রক্রিয়া নয়; এটি নারীর বিরুদ্ধে একটি নীরব যুদ্ধ। এই যুদ্ধে বন্দুক নেই, কিন্তু প্রতিদিন হাজার হাজার নারীর নাম মুছে যায়। এই মুছে যাওয়া মানে নারীর রাজনৈতিক অস্তিত্ব মুছে যাওয়া। এই মুছে যাওয়া মানে ঘরের বৈষম্য রাষ্ট্রের সিল পেয়ে যাওয়া।
এই ইতিহাস বুঝতে পারলে স্পষ্ট হয়—নারীর ভোটাধিকার শুধু একটি অধিকার নয়, এটি লিঙ্গসমতার শর্ত। আর যে রাষ্ট্র নারীর নাম মুছে দেয়, সে রাষ্ট্র কখনো সমান হতে পারে না। গণতন্ত্র তখন পুরুষের গণতন্ত্র হয়ে ওঠে, আর নারী আবার নীরব দর্শক।
এই নীরবতা ভাঙা জরুরি। কারণ নারীর নাম মুছে যাওয়ার ইতিহাস মানে গণতন্ত্রের অর্ধেক ইতিহাস মুছে যাওয়া। আর যে রাষ্ট্র অর্ধেক নাগরিককে অদৃশ্য করে, সে রাষ্ট্র নিজেই অর্ধেক গণতান্ত্রিক।
এসআইআর: এক ধরনের ‘নীরব ইমার্জেন্সি’
রাষ্ট্র যখন কোনো অধিকার স্থগিত করে, তখন সাধারণত সে ঘোষণা দেয়। সংবিধানের অনুচ্ছেদ স্থগিত হয়, মৌলিক অধিকার স্থগিত হয়, সংবাদপত্র বন্ধ হয়, আদালত স্তব্ধ হয়। মানুষ জানে—এটা ইমার্জেন্সি। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র আরও পরিণত, আরও ধূর্ত। সে এখন আর ঘোষণা দেয় না। সে নীরবে অধিকার কেড়ে নেয়। সে বলে না—“তোমার অধিকার নেই”, সে কেবল এমন পরিস্থিতি তৈরি করে যাতে অধিকার ব্যবহার করা অসম্ভব হয়ে যায়। এসআইআর সেই নীরব ইমার্জেন্সির নিখুঁত উদাহরণ—যেখানে কোনো ঘোষণা নেই, কিন্তু অধিকার নেই; কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, কিন্তু নাগরিক অচল।
এই নীরব ইমার্জেন্সির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো—এটি আইনের বাইরে নয়, আইনের ভেতরেই ঘটে। ১৯৭৫ সালের ইমার্জেন্সিতে রাষ্ট্র সংবিধান স্থগিত করেছিল, তাই মানুষ প্রতিরোধ করেছিল। আজ রাষ্ট্র সংবিধান ব্যবহার করেই অধিকার স্থগিত করে। সে বলে—নিয়ম মানা হচ্ছে, প্রক্রিয়া মানা হচ্ছে, সংশোধন হচ্ছে। এই ভাষা এতটাই প্রশাসনিক যে মানুষ বুঝতেই পারে না—তার রাজনৈতিক জীবন স্থগিত হয়ে গেছে।
এসআইআর প্রক্রিয়ায় কোনো অধিকার আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল হয় না। ভোটাধিকার কাগজে থাকে, সংবিধানে থাকে, বক্তৃতায় থাকে। কিন্তু বাস্তবে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়লে সেই অধিকার অস্তিত্বহীন হয়ে যায়। এটি সেই অবস্থা, যেখানে অধিকার আছে কিন্তু ব্যবহার নেই। রাষ্ট্র এখানে অধিকার কেড়ে নেয় না, অধিকারকে অকার্যকর করে। এই অকার্যকরকরণই নীরব ইমার্জেন্সির মূল কৌশল।
নীরব ইমার্জেন্সির সবচেয়ে ভয়ংকর দিক হলো—মানুষ জানে না যে সে ইমার্জেন্সির ভেতরে আছে। কোনো কারফিউ নেই, কোনো সেনা নেই, কোনো টিভি ঘোষণা নেই। জীবন স্বাভাবিক চলছে। দোকান খোলা, ট্রেন চলছে, নির্বাচন হচ্ছে। কিন্তু নাগরিকের রাজনৈতিক জীবন থেমে গেছে। সে ভোট দিতে পারে না, সে সিদ্ধান্তে অংশ নিতে পারে না, সে শাসনকে প্রভাবিত করতে পারে না। এই স্বাভাবিকতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে রাজনৈতিক মৃত্যু।
এসআইআর-এর সময় এই ইমার্জেন্সি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নাগরিককে বলা হয়—তোমার নাম যাচাই হবে। যাচাই শব্দটি নিরীহ, কিন্তু এর অর্থ ভয়ংকর। যাচাই মানে সন্দেহ। রাষ্ট্র প্রথমে নাগরিককে সন্দেহ করে, তারপর প্রমাণ চাইতে বলে, তারপর প্রমাণ না পেলে বাদ দেয়। এই তিনস ধাপই নীরব ইমার্জেন্সির কাঠামো। এখানে নাগরিক অপরাধী নয়, কিন্তু সন্দেহভাজন। আর সন্দেহভাজনের অধিকার সবসময় অনিশ্চিত।
এই ইমার্জেন্সির একটি বড় দিক হলো—এটি অসমভাবে প্রয়োগ হয়। শহরের ধনী, মধ্যবিত্ত, স্থায়ী মানুষদের ক্ষেত্রে যাচাই সহজ, দ্রুত, আনুষ্ঠানিক। গরিব, পরিযায়ী, নারী, সংখ্যালঘু, প্রান্তিক মানুষের ক্ষেত্রে যাচাই মানে বাদ পড়া। এই অসম প্রয়োগই প্রমাণ করে—এটি প্রশাসনিক নয়, রাজনৈতিক। কারণ ইমার্জেন্সি সবসময় দুর্বলদের ওপর নেমে আসে।
নীরব ইমার্জেন্সির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো—এতে আদালতও প্রায় অকার্যকর হয়ে যায়। কারণ আদালত তখন বলে—এটি প্রশাসনিক বিষয়, নিয়মের বিষয়। অধিকার এখানে প্রশ্ন নয়, প্রক্রিয়া প্রশ্ন। কিন্তু গণতন্ত্রে অধিকারই সবকিছু, প্রক্রিয়া তার বাহন মাত্র। যখন প্রক্রিয়া অধিকারকে হত্যা করে, তখন আদালতের নীরবতা নিজেই ইমার্জেন্সির অংশ হয়ে ওঠে।
এসআইআর-এর মাধ্যমে রাষ্ট্র একটি বিকল্প শাসনব্যবস্থা তৈরি করে—যেখানে ভোটাধিকার শর্তসাপেক্ষ। আজ ভোট দিতে চাইলে নাগরিককে কাগজ দেখাতে হবে, কাল হয়তো ডেটা মিলাতে হবে, পরশু হয়তো বায়োমেট্রিক দিতে হবে। অধিকার তখন আর অধিকার থাকে না; হয়ে ওঠে অনুমতি। রাষ্ট্র অনুমতি দেয়, রাষ্ট্র অনুমতি কেড়ে নেয়। এই অনুমতির রাজনীতিই নীরব ইমার্জেন্সির মূল দর্শন।
এই ইমার্জেন্সি এতটাই নীরব যে মিডিয়াও তা ধরতে পারে না বা ধরতে চায় না। কারণ এখানে কোনো নাটক নেই, কোনো ভাঙচুর নেই, কোনো রক্ত নেই। কেবল তালিকা বদলায়। এই বদল সংবাদ নয়, কিন্তু এই বদলই ইতিহাস। ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকর মুহূর্তগুলো সবসময় নীরবেই ঘটে—যখন মানুষ বুঝতে পারে না যে সে তার অধিকার হারিয়েছে।
১৯৭৫ সালের ইমার্জেন্সিতে মানুষ রাস্তায় নেমেছিল, কারণ শত্রু দৃশ্যমান ছিল। আজ শত্রু অদৃশ্য—সে ফর্মে, ডাটাবেসে, সার্ভারে, নির্দেশিকায়। তার বিরুদ্ধে লড়াই করা কঠিন, কারণ তার কোনো মুখ নেই। এই অমুখ শত্রুই আধুনিক কর্তৃত্ববাদকে অপ্রতিরোধ্য করে তোলে।
নীরব ইমার্জেন্সির আরেকটি স্তর হলো—এটি দীর্ঘস্থায়ী। ঘোষণা করা ইমার্জেন্সি সীমিত সময়ের হয়, কিন্তু নীরব ইমার্জেন্সি স্থায়ী হয়ে যায়। প্রতি নির্বাচনের আগে এসআইআর আসে, প্রতি বার নতুন করে বাদ পড়ে মানুষ, আর প্রতি বার গণতন্ত্র একটু করে সঙ্কুচিত হয়। এই ধীর মৃত্যু মানুষ টের পায় না, কারণ মৃত্যু একদিনে আসে না।
এই ইমার্জেন্সির সবচেয়ে ভয়ংকর ফল হলো—মানুষ ধীরে ধীরে অধিকার ভুলে যায়। সে ভাবে, ভোট দেওয়া হয়তো তার জন্য নয়। সে ভাবে, কাগজ না থাকলে ভোট পাওয়া যায় না। এই ভাবনাই রাষ্ট্রের চূড়ান্ত জয়, কারণ তখন রাষ্ট্র আর অধিকার কেড়ে নেয় না—মানুষ নিজেই অধিকার ত্যাগ করে।
এসআইআর-এর মাধ্যমে রাষ্ট্র আসলে নাগরিকত্বের নতুন সংজ্ঞা তৈরি করে। নাগরিক সে নয় যে এখানে জন্মেছে, এখানে বেঁচে আছে, এখানে কাজ করে। নাগরিক সে, যার কাগজ ঠিক আছে। এই কাগজভিত্তিক নাগরিকত্বই নীরব ইমার্জেন্সির ভিত্তি। কারণ কাগজ সবসময় রাষ্ট্রের হাতে, মানুষের হাতে নয়।
এই ইমার্জেন্সি ঘোষণা না হওয়ায় এর বিরুদ্ধে কোনো গণপ্রতিরোধ গড়ে ওঠে না। মানুষ ভাবে—এটি তার ব্যক্তিগত সমস্যা, তার নাম বাদ পড়েছে, তার কাগজ ভুল। সে বোঝে না—এটি একটি কাঠামোগত সমস্যা। এই বিচ্ছিন্নতা নীরব ইমার্জেন্সির সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। কারণ বিচ্ছিন্ন মানুষ কখনো আন্দোলন করতে পারে না।
এই বাস্তবতা আমাদের একটি ভয়ংকর সত্যের সামনে দাঁড় করায়—গণতন্ত্র আর হঠাৎ করে মরে না, সে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে মারা যায়। এসআইআর সেই নিঃশব্দ মৃত্যুর প্রক্রিয়া। এখানে ট্যাংক নেই, কিন্তু তালিকা আছে; সেনা নেই, কিন্তু সার্ভার আছে; ঘোষণা নেই, কিন্তু নিষেধাজ্ঞা আছে। এই নিষেধাজ্ঞা এতটাই নীরব যে মানুষ তা স্বাভাবিক মনে করে।
এই কারণেই এসআইআরকে শুধু প্রশাসনিক সংস্কার বলা যায় না। এটি এক ধরনের নীরব ইমার্জেন্সি—যেখানে রাষ্ট্র নিজের ক্ষমতা বাড়ায়, আর নাগরিকের ক্ষমতা কমে। যেখানে অধিকার কাগজে থাকে, কিন্তু জীবনে থাকে না। যেখানে গণতন্ত্র থাকে, কিন্তু জনগণ থাকে না।
এই নীরব ইমার্জেন্সির বিরুদ্ধে লড়াই সবচেয়ে কঠিন, কারণ এখানে শত্রু দৃশ্যমান নয়। কিন্তু ইতিহাস বলে—যে সমাজ নীরব ইমার্জেন্সিকে স্বাভাবিক মেনে নেয়, সে একদিন প্রকাশ্য ইমার্জেন্সিকেও মেনে নেয়। আর তখন প্রতিরোধের ভাষা আর থাকে না।
এই প্রবন্ধের শেষ কথা তাই সতর্কবার্তা—এসআইআর কোনো বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া নয়, এটি একটি শাসনরীতি। এটি সেই শাসনরীতি, যেখানে রাষ্ট্র ঘোষণা না দিয়েই নাগরিকের অধিকার স্থগিত করে। এই নীরবতা ভাঙা না গেলে, একদিন আমরা বুঝতেই পারব না—কবে আমাদের নাগরিকত্ব শেষ হলো।
মুসলমান, সংখ্যালঘু ও “সন্দেহভাজন নাগরিক” নির্মাণ
আধুনিক রাষ্ট্র যখন কাউকে শাসন করতে চায়, তখন সে প্রথমে তাকে শত্রু বানায় না—সে তাকে সন্দেহভাজন বানায়। শত্রু মানে প্রতিরোধ, কিন্তু সন্দেহভাজন মানে নীরব আত্মসমর্পণ। এই রূপান্তরই আজকের ভারতের রাজনৈতিক বাস্তবতার সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক। মুসলমান, সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক মানুষদের আর সরাসরি “শত্রু” বলা হয় না; তাদের বলা হয় “যাচাইযোগ্য”, “অনিশ্চিত”, “সন্দেহভাজন নাগরিক”। এই ভাষা যত নিরীহ, এর পরিণতি তত ভয়ংকর। কারণ সন্দেহভাজন নাগরিকের কোনো অধিকার স্থায়ী নয়—তার প্রতিটি অধিকার প্রমাণসাপেক্ষ, অস্থায়ী, শর্তাধীন।
এই সন্দেহভাজন নাগরিক নির্মাণ কোনো হঠাৎ নীতির ফল নয়। এটি দীর্ঘ সময় ধরে গড়ে ওঠা একটি রাষ্ট্রীয় প্রকল্প, যেখানে মুসলমান ও সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব ধীরে ধীরে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে। ইতিহাস বলছে, রাষ্ট্র কখনোই একদিনে কাউকে অ-নাগরিক বানায় না; সে আগে তাকে সন্দেহের আওতায় আনে, তারপর যাচাইয়ের নামে হেনস্তা করে, তারপর অধিকার কেড়ে নেয়, শেষে তাকে অদৃশ্য করে দেয়। এসআইআর, এনআরসি, নাগরিকত্ব যাচাই, ভোটার তালিকা শুদ্ধিকরণ—এই সব প্রক্রিয়া সেই একই ধারাবাহিকতার অংশ।
মুসলমানদের ক্ষেত্রে এই সন্দেহের রাজনীতি আরও গভীর। উপনিবেশিক আমল থেকেই মুসলমানকে “বহিরাগত”, “অনিশ্চিত আনুগত্যের মানুষ”, “দ্বৈত পরিচয়ের নাগরিক” হিসেবে দেখা হয়েছে। স্বাধীনতার পর সংবিধান এই সন্দেহ ভাঙার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু সাম্প্রতিক রাষ্ট্রীয় চর্চা সেই সন্দেহকে আবার ফিরিয়ে এনেছে—আরও আধুনিক, আরও প্রশাসনিক, আরও নীরব রূপে। আজ মুসলমান নাগরিক রাষ্ট্রের কাছে নাগরিক নয়; সে প্রথমে “প্রমাণযোগ্য ব্যক্তি”। তাকে বারবার প্রমাণ করতে হয় যে সে এখানে থাকার যোগ্য।
এই সন্দেহভাজন নাগরিক নির্মাণের প্রথম ধাপ হলো ভাষা। রাষ্ট্র যখন বলে “ভুয়া ভোটার”, “অনুপ্রবেশকারী”, “অবৈধ বাসিন্দা”, তখন সে আসলে একটি সম্প্রদায়ের ওপর সমষ্টিগত সন্দেহ চাপিয়ে দেয়। এই ভাষা নির্দিষ্ট কাউকে লক্ষ্য করে না, কিন্তু সবাই জানে কার দিকে আঙুল। এই অস্পষ্টতা রাষ্ট্রের জন্য সুবিধাজনক, কারণ এতে দায় নেই, কিন্তু প্রভাব আছে। মুসলমান নাগরিক তখন নিজেকেই সন্দেহ করতে শুরু করে—সে ভাবে, তার কাগজ যথেষ্ট কিনা, তার নাম ঠিক আছে কিনা, তার জন্ম গ্রহণযোগ্য কিনা।
এই আত্মসন্দেহই রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সাফল্য। কারণ যে নাগরিক নিজেকে সন্দেহ করে, সে আর রাষ্ট্রকে প্রশ্ন করে না। সে আর অধিকার দাবি করে না; সে কেবল প্রমাণ দিতে থাকে। এই প্রমাণের চক্র কখনো শেষ হয় না। আজ ভোটার তালিকার জন্য কাগজ, কাল রেশন কার্ডের জন্য কাগজ, পরশু বাসস্থানের জন্য কাগজ। নাগরিকের জীবন তখন কাগজের দাসত্বে বন্দি হয়ে যায়। মুসলমান ও সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে এই দাসত্ব আরও কঠিন, কারণ তাদের নথি ঐতিহাসিকভাবেই দুর্বল, অসম্পূর্ণ, বিচ্ছিন্ন।
সন্দেহভাজন নাগরিক নির্মাণের দ্বিতীয় ধাপ হলো প্রশাসনিক প্রক্রিয়া। এসআইআর-এর মতো প্রক্রিয়ায় মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় যাচাই বেশি হয়, প্রশ্ন বেশি হয়, প্রতিবেশী রিপোর্ট বেশি নেতিবাচক হয়। এই সামাজিক পক্ষপাত প্রশাসনিক রিপোর্টে ঢুকে পড়ে। BLO-এর ব্যক্তিগত ধারণা রাষ্ট্রীয় সত্য হয়ে যায়। এই সত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার সুযোগ নাগরিকের নেই, কারণ সে জানেই না কবে তাকে সন্দেহভাজন বানানো হলো¹।
এই প্রক্রিয়ার সবচেয়ে ভয়ংকর দিক হলো—এটি সমষ্টিগত। একজন মুসলমানের কাগজে সমস্যা মানে পুরো পাড়ার সন্দেহ, পুরো সম্প্রদায়ের ওপর চাপ। এই সমষ্টিগত দায় আধুনিক আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, কিন্তু প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় এটি স্বাভাবিক হয়ে যায়। মুসলমান নাগরিক তখন একা নয়; সে একটি সন্দেহভাজন গোষ্ঠীর অংশ। এই গোষ্ঠীভিত্তিক সন্দেহই ভবিষ্যতের দমনকে সহজ করে।
সন্দেহভাজন নাগরিক নির্মাণের তৃতীয় ধাপ হলো মিডিয়া। মিডিয়া যখন অনুপ্রবেশ, অবৈধতা, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, নিরাপত্তা—এই শব্দগুলো ব্যবহার করে, তখন রাষ্ট্রীয় সন্দেহ সামাজিক সত্যে রূপ নেয়। প্রতিবেশী মুসলমানকে তখন আর প্রতিবেশী মনে হয় না; সে হয়ে ওঠে সম্ভাব্য অপরাধী। এই সামাজিক সন্দেহ প্রশাসনিক দমনকে বৈধতা দেয়। রাষ্ট্র তখন একা নয়; সমাজও তার সঙ্গে থাকে।
এই সন্দেহভাজন নাগরিক নির্মাণের চূড়ান্ত ফল হলো অধিকারহীনতা। মুসলমান ও সংখ্যালঘু নাগরিকের ভোটাধিকার প্রথমে অনিশ্চিত হয়, তারপর শর্তাধীন হয়, শেষে অকার্যকর হয়। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া এখানে শুধু প্রশাসনিক ত্রুটি নয়; এটি একটি রাজনৈতিক বার্তা—তোমার উপস্থিতি নিশ্চিত নয়। এই অনিশ্চয়তা মানুষকে স্থায়ী আতঙ্কে রাখে। আতঙ্কগ্রস্ত নাগরিক কখনো প্রতিবাদ করে না।
এই আতঙ্কের রাষ্ট্রায়নই আধুনিক কর্তৃত্ববাদের ভিত্তি। রাষ্ট্র আর বন্দুক দেখায় না, সে আতঙ্ক দেখায়। মুসলমান নাগরিক জানে না—তার নাম আছে কিনা, তার কাগজ যথেষ্ট কিনা, তার ভবিষ্যৎ নিরাপদ কিনা। এই অনিশ্চয়তা তাকে নীরব করে দেয়। নীরব নাগরিকই রাষ্ট্রের আদর্শ নাগরিক।
এই প্রক্রিয়া আন্তর্জাতিকভাবেও পরিচিত। ইউরোপে মুসলমানদের নাগরিকত্ব নিয়ে সন্দেহ, যুক্তরাষ্ট্রে লাতিনোদের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন, মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব অস্বীকার—সব ক্ষেত্রেই একই কৌশল দেখা যায়: আগে সন্দেহ, তারপর যাচাই, তারপর বর্জন²। ভারতে এই কৌশল আরও বিপজ্জনক, কারণ এখানে মুসলমানরা সংখ্যায় বিপুল, কিন্তু রাজনৈতিকভাবে দুর্বল। রাষ্ট্র এই দুর্বলতাকেই ব্যবহার করে।
সন্দেহভাজন নাগরিক নির্মাণের সবচেয়ে গভীর দিক হলো—এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রভাবিত করে। শিশু জন্মায় সন্দেহের মধ্যে, বড় হয় কাগজের ভয়ে, যুবক হয় প্রমাণের দাস। নাগরিকত্ব তখন আর জন্মসূত্রে পাওয়া অধিকার নয়; হয়ে ওঠে আজীবন পরীক্ষার বিষয়। এই পরীক্ষায় মুসলমান ও সংখ্যালঘুরা সবসময় ফেল করে, কারণ পরীক্ষার নিয়মই তাদের বিরুদ্ধে।
এই অবস্থায় গণতন্ত্র আর সকলের জন্য থাকে না। গণতন্ত্র তখন নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর অধিকার হয়ে যায়। মুসলমান নাগরিক তখন ভোটার নয়, সে “ভেরিফায়েড ভোটার”—যদি সে বেঁচে থাকে, যদি সে প্রমাণ দিতে পারে, যদি সে সন্দেহমুক্ত হতে পারে। এই শর্তাধীন গণতন্ত্র আসলে গণতন্ত্রের বিপরীত।
এই প্রবন্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সত্য তাই নির্মমভাবে স্পষ্ট—মুসলমান ও সংখ্যালঘুদের সন্দেহভাজন নাগরিক বানানো মানে রাষ্ট্র নিজেই সংবিধানকে সন্দেহভাজন বানায়। কারণ সংবিধান নাগরিককে সন্দেহ নয়, অধিকার দেয়। যে রাষ্ট্র সন্দেহ দিয়ে শাসন করে, সে আর গণতান্ত্রিক থাকে না; সে হয়ে ওঠে যাচাইকরণ রাষ্ট্র, যেখানে মানুষ নয়, কাগজই সত্য।
এই বাস্তবতা যদি আমরা এখনই বুঝতে না পারি, তবে একদিন বুঝব—আমরা সবাই সন্দেহভাজন নাগরিক। কারণ সন্দেহ কখনো এক সম্প্রদায়ে থামে না; সে একদিন সবাইকে গ্রাস করে। ইতিহাস বারবার দেখিয়েছে—আজ যে সন্দেহভাজন, কাল সে নিয়ম। আর যে নিয়মে সন্দেহ ঢুকে পড়ে, সেখানে স্বাধীনতার কোনো জায়গা থাকে না।
মুসলমানদের ডকুমেন্ট সংকট—একটি পরিকল্পিত ফাঁদ
মুসলমানদের ডকুমেন্ট সংকট কোনো আকস্মিক প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়; এটি ইতিহাসকে অপরাধে রূপান্তর করার একটি পরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় ফাঁদ। এই ফাঁদের সবচেয়ে ভয়ংকর দিক হলো—এটি মুসলমান নাগরিককে দোষী প্রমাণ করার জন্য কোনো অপরাধের প্রয়োজন রাখে না। ইতিহাসই এখানে অপরাধ, স্মৃতি এখানেই সন্দেহ, আর বংশপরিচয় এখানে শাস্তিযোগ্য। রাষ্ট্র যখন ডকুমেন্টের নামে মুসলমানদের নাগরিকত্ব যাচাই করতে বসে, তখন সে আসলে একটি জনগোষ্ঠীর ইতিহাসকে কাঠগড়ায় দাঁড় করায়।
ভারতের মুসলমানদের ডকুমেন্ট সংকটের শিকড় উপনিবেশিক আমলে। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা মুসলমানদের সন্দেহের চোখে দেখত—কারণ তারা ছিল পূর্ববর্তী শাসক শ্রেণির অংশ। ফলে ভূমি রেকর্ড, শিক্ষার নথি, প্রশাসনিক কাগজে মুসলমানদের উপস্থিতি পরিকল্পিতভাবে কমিয়ে রাখা হয়েছিল। বহু মুসলমান পরিবার তখন কৃষিজীবী, হস্তশিল্পী, যাযাবর বা আধা-যাযাবর জীবনে ছিল—যেখানে কাগজের প্রয়োজন ছিল না, রাষ্ট্রের উপস্থিতিও ছিল না। এই নথিহীন জীবন তখন অপরাধ ছিল না; কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র সেই নথিহীনতাকেই অপরাধে রূপান্তর করেছে।
দেশভাগ মুসলমানদের ডকুমেন্ট ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ভাঙন আনে। লক্ষ লক্ষ মানুষ স্থানচ্যুত হয়, ঘর হারায়, কাগজ হারায়, পরিচয় হারায়। বহু পরিবার পূর্বপুরুষের গ্রাম ছাড়ে, আবার কেউ কেউ থেকে যায় কিন্তু রাষ্ট্রীয় নথিতে তারা “অনিশ্চিত” হয়ে পড়ে। এই ক্ষত কখনো পূরণ হয়নি। স্বাধীন ভারত সেই ক্ষত সারানোর পরিবর্তে ধীরে ধীরে তাকে রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিণত করেছে। আজ মুসলমান নাগরিককে যখন বলা হয়—“প্রমাণ দাও”, তখন আসলে তাকে বলা হয়—“দেশভাগের ইতিহাস প্রমাণ করো”, যা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়।
ডকুমেন্ট সংকটের দ্বিতীয় স্তর হলো দারিদ্র্য ও বঞ্চনা। ভারতের মুসলমানরা শিক্ষায়, চাকরিতে, সম্পত্তিতে ঐতিহাসিকভাবে পিছিয়ে। ফলে জন্মসনদ, স্কুল সার্টিফিকেট, জমির দলিল—এই সব কাগজ তাদের কাছে কম। রাষ্ট্র এই সামাজিক বাস্তবতাকে সমাধান করার বদলে তাকে সন্দেহের ভিত্তি বানিয়েছে। যে নাগরিক সবচেয়ে বঞ্চিত, সেই নাগরিকই সবচেয়ে বেশি প্রমাণ দিতে বাধ্য। এই বৈষম্য কাকতাল নয়; এটি পরিকল্পিত।
ডকুমেন্ট সংকটের তৃতীয় স্তর হলো প্রশাসনিক পক্ষপাত। ভোটার তালিকা সংশোধন, এসআইআর, নাগরিকত্ব যাচাই—এই সব প্রক্রিয়ায় মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় যাচাই বেশি কড়াকড়ি হয়, প্রতিবেশী রিপোর্ট বেশি নেতিবাচক হয়, BLO-এর সন্দেহ বেশি হয়। এই সন্দেহ কোনো নিয়মে লেখা নেই, কিন্তু বাস্তবে সেটিই নিয়ম। প্রশাসনিক রিপোর্টে “পাওয়া যায়নি”, “সন্দেহজনক”, “ঠিকানা অনিশ্চিত”—এই শব্দগুলো মুসলমান নাগরিককে রাষ্ট্রীয়ভাবে অপরাধী বানায়¹।
এই প্রক্রিয়ার সবচেয়ে ভয়ংকর দিক হলো—ইতিহাস এখানে অপরাধে পরিণত হয়। মুসলমানদের পারিবারিক ইতিহাস, স্থানান্তর, বিয়ের সম্পর্ক, কাজের প্রয়োজনে ঘন ঘন ঠিকানা বদল—এই সবকিছু রাষ্ট্রের চোখে অপরাধ। যে ইতিহাস একসময় স্বাভাবিক জীবন ছিল, আজ সেটাই সন্দেহের ভিত্তি। রাষ্ট্র মুসলমানদের বলে—তোমরা কেন এতবার জায়গা বদলেছ, কেন তোমাদের কাগজ নেই, কেন তোমাদের ঠিকানা বদলায়? কিন্তু রাষ্ট্র কখনো জিজ্ঞেস করে না—কেন এই ইতিহাস তৈরি হলো? কেন মুসলমানদের ভূমি হারাতে হলো, শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতে হলো, নথির বাইরে থাকতে হলো?
ডকুমেন্ট সংকটের চতুর্থ স্তর হলো ডিজিটালাইজেশন। আধার, ডেটাবেস, অনলাইন মিল—এই সব প্রযুক্তি মুসলমানদের সংকট আরও বাড়িয়েছে। কারণ প্রযুক্তি ইতিহাস বোঝে না, সামাজিক বাস্তবতা বোঝে না; সে কেবল মিল খোঁজে। নামের বানান বদল, বয়সের সামান্য অমিল, ঠিকানার ভিন্নতা—এই সব মুসলমান নাগরিকের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়, কারণ তাদের নথি বিচ্ছিন্ন। প্রযুক্তি এই বিচ্ছিন্নতাকে অপরাধে রূপান্তর করে। অ্যালগরিদম এখানে বিচারক হয়ে ওঠে, আর মুসলমান নাগরিক তার সামনে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পায় না²।
এই ফাঁদের সবচেয়ে ভয়ংকর দিক হলো—এটি ভবিষ্যৎ তৈরি করে। আজ মুসলমান নাগরিক ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে, কাল সে রেশন তালিকা থেকে বাদ পড়ে, পরশু সে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান থেকেও বাদ পড়ে। ডকুমেন্ট সংকট এখানে একটি দরজা, যার ভেতর দিয়ে নাগরিকত্ব ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়। এই ধীর ক্ষয় রাষ্ট্রের সবচেয়ে কার্যকর কৌশল, কারণ এতে কোনো বিদ্রোহ হয় না, কোনো বিস্ফোরণ হয় না—কেবল নিঃশব্দ নিশ্চিহ্নতা হয়।
এই প্রক্রিয়া আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত। মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব অস্বীকার করা হয়েছিল নথির নামে; ইউরোপে মুসলমান শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রশ্নবিদ্ধ করা হয় ডকুমেন্টের নামে; যুক্তরাষ্ট্রে লাতিনোদের ভোটাধিকার সংকুচিত করা হয় কাগজের নামে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইতিহাসকে অপরাধ বানানো হয়েছে³। ভারতে এই কৌশল আরও বিপজ্জনক, কারণ মুসলমানরা এখানে বিদেশি নয়—তারা এই দেশের ইতিহাসের অংশ। তবু রাষ্ট্র তাদের ইতিহাসকেই সন্দেহের চোখে দেখে।
ডকুমেন্ট সংকটের শেষ স্তর হলো মানসিকতা। মুসলমান নাগরিক ধীরে ধীরে নিজের অস্তিত্ব নিয়েই সন্দেহ করতে শুরু করে। সে ভাবে—হয়তো আমার কাগজ ঠিক নয়, হয়তো আমি সত্যিই অনিশ্চিত। এই আত্মসন্দেহ রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় জয়, কারণ তখন নাগরিক আর অধিকার দাবি করে না, সে ক্ষমা চায়। ক্ষমা চাওয়া নাগরিক কখনো মুক্ত থাকে না।
এই প্রবন্ধের মূল সত্য তাই নির্মমভাবে স্পষ্ট—মুসলমানদের ডকুমেন্ট সংকট একটি পরিকল্পিত ফাঁদ, যেখানে ইতিহাসই অপরাধ। যে রাষ্ট্র ইতিহাসকে অপরাধ বানায়, সে নাগরিককে কখনো নিরাপত্তা দিতে পারে না। কারণ আজ মুসলমানের ইতিহাস অপরাধ, কাল অন্যের ইতিহাস হবে। সন্দেহের রাজনীতি কখনো এক জায়গায় থামে না।
এই ফাঁদ ভাঙা জরুরি, কারণ এটি শুধু মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়—এটি নাগরিকত্বের বিরুদ্ধে। আজ মুসলমান নাগরিককে বলা হচ্ছে—প্রমাণ দাও। কাল সবাইকে বলা হবে। আর যে সমাজ এই প্রমাণের রাজনীতি মেনে নেয়, সে একদিন বুঝবে—তার নিজের ইতিহাসও রাষ্ট্রের কাছে অপরাধ হয়ে গেছে।
এসআইআর = নরম NRC
এসআইআর যখন চালু হয়, তখন রাষ্ট্র বলে—এটি ভোটার তালিকার একটি প্রশাসনিক সংশোধন। কিন্তু বাস্তবে এসআইআর এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে নাগরিকের নাম কাগজে থেকে যায়, অথচ নাগরিকত্ব ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়। এই কারণেই এসআইআরকে “নরম NRC” বলা ভুল নয়। এখানে কাউকে প্রকাশ্যে অ-নাগরিক ঘোষণা করা হয় না, কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হয় না, কিন্তু নাগরিকের সব কার্যকর অধিকার একে একে অকার্যকর করে দেওয়া হয়। এটি এমন এক শাসনপ্রক্রিয়া, যেখানে নাম থাকে, কিন্তু অধিকার থাকে না; পরিচয় থাকে, কিন্তু স্বীকৃতি থাকে না।
এনআরসি ছিল প্রকাশ্য, আক্রমণাত্মক, দৃশ্যমান—আর সেই কারণেই প্রতিরোধের মুখে পড়েছিল। মানুষ রাস্তায় নেমেছিল, আদালতে গিয়েছিল, আন্তর্জাতিক নজর তৈরি হয়েছিল। রাষ্ট্র সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছে—নাগরিকত্ব কেড়ে নিতে হলে আর প্রকাশ্য পথ নয়, নীরব পথ বেছে নিতে হবে। এসআইআর সেই নীরব পথ। এখানে রাষ্ট্র একই কাজ করে, কিন্তু অন্য নামে, অন্য কৌশলে, অন্য গতিতে। এসআইআর তাই এনআরসির পরবর্তী সংস্করণ—নরম, ধীর, কিন্তু গভীর।
নরম এনআরসির মূল বৈশিষ্ট্য হলো—এটি নাগরিকত্বকে অস্বীকার না করে, নাগরিকত্বকে অকার্যকর করে। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া মানে শুধু ভোটাধিকার হারানো নয়; এটি রাষ্ট্রের কাছে নাগরিকের উপস্থিতি হারানো। নাগরিক তখন রেশন, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা—সব কিছুর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কারণ ভোটার পরিচয় ভারতের বহু জায়গায় নাগরিকত্বের কার্যকর প্রমাণ। এসআইআর এই কার্যকর প্রমাণটিকেই দুর্বল করে দেয়। নাম মুছে না, কিন্তু নাগরিকত্ব মুছে দেয়।
এনআরসিতে নাগরিককে সরাসরি বলা হয়েছিল—প্রমাণ দাও। এসআইআরে নাগরিককে বলা হয়—যাচাই হবে। কিন্তু যাচাই আর প্রমাণের মধ্যে পার্থক্য কেবল ভাষাগত। উভয় ক্ষেত্রেই নাগরিক সন্দেহভাজন। উভয় ক্ষেত্রেই নাগরিকের অধিকার শর্তাধীন। উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র বিচারক, প্রশাসন সাক্ষী, আর নাগরিক অভিযুক্ত। পার্থক্য শুধু এই যে, এসআইআরে এই বিচারটি নিঃশব্দে ঘটে।
নরম এনআরসির সবচেয়ে বড় শক্তি হলো—এটি বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে। এনআরসিতে সবাই একসঙ্গে আতঙ্কিত হয়েছিল, তাই প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল। এসআইআরে মানুষ একা বাদ পড়ে, একা আবেদন করে, একা লড়ে, একা হারে। এই একাকীত্বই নরম এনআরসির প্রাণ। রাষ্ট্র জানে—যে মানুষ একা লড়ে, সে কখনো জেতে না।
এসআইআর-এর মাধ্যমে নাগরিকত্ব একটি প্রক্রিয়া হয়ে যায়, অধিকার থাকে না। আজ তোমার নাম আছে, কাল যাচাই হবে, পরশু সংশোধন হবে, তারপর হয়তো বাদ যাবে। নাগরিক কখনো নিশ্চিত হতে পারে না—সে নাগরিক কিনা। এই অনিশ্চয়তাই নাগরিকত্বের মৃত্যু। কারণ নাগরিকত্ব মানে নিরাপত্তা, স্থায়িত্ব, স্বীকৃতি। এসআইআর সেই সবকিছুকে অস্থায়ী করে দেয়।
নরম এনআরসির আরেকটি দিক হলো—এটি নির্বাচনী। এনআরসি ছিল সামগ্রিক, তাই বিপজ্জনক ছিল। এসআইআর নির্বাচনী সময়ের কাছাকাছি আসে, নির্দিষ্ট এলাকাকে লক্ষ্য করে, নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে। মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা, বস্তি, পরিযায়ী অঞ্চল, দরিদ্র গ্রাম—এই জায়গাগুলোতেই যাচাই বেশি, সন্দেহ বেশি, বাদ পড়া বেশি। এই বাছাই প্রমাণ করে—এটি প্রশাসনিক নয়, রাজনৈতিক।
এসআইআর-এর মাধ্যমে রাষ্ট্র এক ধরনের ধাপে ধাপে নাগরিকত্ব হরণ চালায়। প্রথম ধাপে ভোটাধিকার দুর্বল হয়, দ্বিতীয় ধাপে সামাজিক পরিষেবা ঝুঁকির মুখে পড়ে, তৃতীয় ধাপে পরিচয় প্রশ্নবিদ্ধ হয়। এই ধাপে ধাপে হরণ এনআরসির চেয়েও কার্যকর, কারণ এখানে কোনো বিস্ফোরণ নেই, কোনো প্রতিবাদ নেই, কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া নেই। নাগরিকত্ব নিঃশব্দে ঝরে পড়ে।
এই প্রক্রিয়ায় ডকুমেন্টই বিচারক হয়ে ওঠে। যে নাগরিকের কাছে কাগজ নেই, সে দোষী। যে নাগরিকের কাগজে ভুল আছে, সে সন্দেহভাজন। যে নাগরিকের কাগজ মেলে না, সে বাদ। এনআরসিতে এই কাগজের রাজনীতি প্রকাশ্য ছিল; এসআইআরে তা লুকানো। কিন্তু ফল একই—নাগরিকের জীবনের ইতিহাসকে রাষ্ট্রীয় অপরাধে রূপান্তর করা।
নরম এনআরসির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—এটি সংবিধানের ভেতরেই কাজ করে। এনআরসির ক্ষেত্রে সংবিধান ও আদালত সামনে ছিল, তাই প্রশ্ন উঠেছিল। এসআইআরে রাষ্ট্র বলে—এটি নির্বাচন কমিশনের কাজ, প্রশাসনিক কাজ, নিয়মিত কাজ। আদালত তখন পিছু হটে, কারণ এখানে মৌলিক অধিকার প্রশ্ন নয়, প্রক্রিয়া প্রশ্ন। এই আইনি ধোঁয়াশাই এসআইআরের সবচেয়ে বড় অস্ত্র।
এই প্রক্রিয়া দীর্ঘমেয়াদি। এনআরসি একবার হলে শেষ। এসআইআর বারবার হয়—প্রতি নির্বাচন, প্রতি বছর, প্রতি সংশোধনে। নাগরিকত্ব এখানে স্থায়ী নয়, পুনর্নবীকরণযোগ্য লাইসেন্সের মতো। আজ বৈধ, কাল সন্দেহভাজন। এই অনিশ্চয়তা মানুষকে রাজনৈতিকভাবে ক্লান্ত করে দেয়। ক্লান্ত নাগরিক আর লড়াই করে না।
এই কারণেই এসআইআরকে নরম এনআরসি বলা হয়—কারণ এটি একই কাজ করে, কিন্তু নরমভাবে। এখানে দমন নেই, কিন্তু ক্ষয় আছে; এখানে ঘোষণা নেই, কিন্তু নিষেধ আছে; এখানে শাসন নেই, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ আছে। এই নরমতা রাষ্ট্রকে নিরাপদ করে, নাগরিককে অসহায় করে।
এই প্রক্রিয়া আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত। হাঙ্গেরিতে, তুরস্কে, রাশিয়ায় ভোটার তালিকা ও নিবন্ধন প্রক্রিয়া ব্যবহার করে নাগরিকত্ব সংকুচিত করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে voter purge প্রক্রিয়া লাতিনো ও আফ্রিকান–আমেরিকানদের ভোটাধিকার কমিয়েছে। সব ক্ষেত্রেই কৌশল এক—নাগরিকত্বকে নামের সঙ্গে রেখে অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন করা¹।
ভারতের ক্ষেত্রে এই কৌশল আরও বিপজ্জনক, কারণ এখানে নাগরিকত্ব মানে শুধু অধিকার নয়—এটি নিরাপত্তা। যে নাগরিক ভোট দিতে পারে না, সে রাষ্ট্রের কাছে অদৃশ্য। এই অদৃশ্য মানুষকে নিয়ে রাষ্ট্র যেকোনো নীতি নিতে পারে, কারণ সে আর গণনায় নেই। নরম এনআরসি সেই অদৃশ্য জনগোষ্ঠী তৈরির কারখানা।
এই প্রবন্ধের শেষ সত্য তাই স্পষ্ট—এসআইআর এনআরসির বিকল্প নয়, এনআরসির পরিণত রূপ। এটি সেই রূপ, যেখানে রাষ্ট্র আর নাগরিককে শত্রু বানায় না; সে নাগরিককে অপ্রাসঙ্গিক বানায়। আর যে নাগরিক অপ্রাসঙ্গিক, সে আর রাষ্ট্রের জন্য সমস্যা নয়।
নাগরিকত্ব যখন নামের সঙ্গে থাকে কিন্তু অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন রাষ্ট্র কার্যত নাগরিকত্বকে বাতিল করে দেয়—ঘোষণা ছাড়াই, আইন ছাড়াই, প্রতিরোধ ছাড়াই। এই নীরব বাতিলই নরম এনআরসির মূল দর্শন।
এই বাস্তবতা বুঝতে পারলে স্পষ্ট হয়—এসআইআর কোনো প্রশাসনিক সংস্কার নয়, এটি একটি রাজনৈতিক প্রকল্প। এই প্রকল্পের লক্ষ্য কাউকে সরাসরি বের করে দেওয়া নয়; লক্ষ্য সবাইকে ভিতরে রেখে অধিকারহীন করা। আর যে সমাজ এই প্রকল্প মেনে নেয়, সে একদিন বুঝবে—সে আর নাগরিক নয়, সে কেবল তালিকার একটি নাম।
মাদ্রাসা, পরিযায়ী জীবন ও রাষ্ট্রীয় সন্দেহ
রাষ্ট্র যখন কোনো জনগোষ্ঠীর জীবনযাপনকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে, তখন অপরাধ আর কাজের ফল থাকে না—অপরাধ হয়ে ওঠে অস্তিত্ব। মাদ্রাসা, পরিযায়ী জীবন, অস্থায়ী বাসস্থান, ধর্মীয় শিক্ষা, কাজের প্রয়োজনে ঘন ঘন স্থানান্তর—এই সবকিছু মুসলমান ও প্রান্তিক মানুষের জীবনে স্বাভাবিক, কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রের চোখে এগুলো হয়ে ওঠে “অনিশ্চিত আচরণ”। এসআইআর-এর মতো প্রক্রিয়ায় এই জীবনযাপনই অপরাধে রূপ নেয়, কারণ রাষ্ট্র নাগরিককে আর তার কাজ দিয়ে বিচার করে না, বিচার করে তার জীবনধারা দিয়ে। এই বিচার সবচেয়ে বিপজ্জনক, কারণ এখানে নাগরিকের কোনো প্রতিকার নেই—সে তার জীবন বদলাতে পারে না।
মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা শতাব্দীপ্রাচীন। উপনিবেশিক শাসনের সময় রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থা যখন মুসলমানদের নাগালের বাইরে ছিল, তখন মাদ্রাসাই ছিল শিক্ষার একমাত্র পথ। আজও ভারতের বহু দরিদ্র মুসলমান পরিবার সন্তানকে মাদ্রাসায় পাঠায়, কারণ তা বিনামূল্যে, স্থানীয়, এবং সামাজিক নিরাপত্তার অংশ। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র এই শিক্ষাকে শিক্ষা হিসেবে নয়, সন্দেহ হিসেবে দেখে। এসআইআর-এর সময় মাদ্রাসা-শিক্ষিত মানুষদের নথি যাচাইয়ে আলাদা দৃষ্টিতে দেখা হয়—তাদের শিক্ষার সার্টিফিকেট “অস্বাভাবিক”, তাদের ঠিকানা “অনিশ্চিত”, তাদের পরিচয় “যাচাইযোগ্য” বলে চিহ্নিত হয়। এই সন্দেহ কোনো আইনে লেখা নেই, কিন্তু প্রশাসনিক আচরণে স্পষ্ট।
এই সন্দেহের ইতিহাস নতুন নয়। উপনিবেশিক আমলে মুসলমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় নজরদারির আওতায় আনা হয়েছিল “রাজনৈতিক ঝুঁকি” বলে। সেই নজরদারি আজ নতুন ভাষায় ফিরেছে—“নিরাপত্তা”, “ভেরিফিকেশন”, “রেকর্ড মিল”। মাদ্রাসা শিক্ষিত নাগরিক তাই আজ রাষ্ট্রের কাছে নাগরিক নয়, বরং একটি প্রশ্নচিহ্ন। এই প্রশ্নচিহ্নই এসআইআর-এর সময় নাগরিকত্ব হরণের প্রথম ধাপ।
পরিযায়ী জীবন মুসলমান ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আরেকটি বাস্তবতা। কাজের জন্য রাজ্য ছাড়তে হয়, শহর বদলাতে হয়, মৌসুমি শ্রমে যেতে হয়। এই চলাচল ভারতের অর্থনীতির ভিত্তি, কিন্তু রাষ্ট্রের নথির চোখে এটি অস্থিরতা। এসআইআর-এর সময় এই অস্থিরতাই অপরাধ। BLO যখন যাচাই করতে আসে, পরিযায়ী শ্রমিক বাড়িতে থাকে না। রিপোর্টে লেখা হয়—“পাওয়া যায়নি”, “স্থানান্তরিত”, “অস্থায়ী বাসিন্দা”। এই শব্দগুলো নিরীহ মনে হলেও এগুলো নাগরিকের রাজনৈতিক মৃত্যু ঘোষণা করে। কারণ ভোটার তালিকায় অস্থায়ী নাগরিক বলে কিছু নেই—থাকলে সে বাদ।
এই প্রক্রিয়া সবচেয়ে ভয়ংকর কারণ পরিযায়ী জীবন মুসলমানদের মধ্যে বেশি, দরিদ্রদের মধ্যে বেশি, প্রান্তিকদের মধ্যে বেশি। রাষ্ট্র এই বাস্তবতাকে জানে, কিন্তু নীতি বদলায় না। বরং এই বাস্তবতাকেই সে অস্ত্র বানায়। যে নাগরিক সবচেয়ে বেশি শ্রম দেয়, সেই নাগরিকই সবচেয়ে কম অধিকার পায়। এই উল্টো সমীকরণই আধুনিক দমনের মূল কৌশল।
মাদ্রাসা ও পরিযায়ী জীবনের সঙ্গে যুক্ত আরেকটি বিষয় হলো—ডকুমেন্টের বিচ্ছিন্নতা। এক জায়গায় জন্ম, অন্য জায়গায় শিক্ষা, তৃতীয় জায়গায় কাজ, চতুর্থ জায়গায় বসবাস। এই ছিন্নভিন্ন জীবন রাষ্ট্রীয় ডেটাবেসে ধরা পড়ে না। আধার, ভোটার তালিকা, রেশন কার্ড—সব নথিতে আলাদা আলাদা ঠিকানা, আলাদা আলাদা বানান, আলাদা আলাদা বয়স। প্রযুক্তি এই বিচ্ছিন্নতাকে ব্যতিক্রম হিসেবে দেখে, আর ব্যতিক্রম মানেই সন্দেহ। এসআইআর সেই সন্দেহকে প্রাতিষ্ঠানিক করে।
এই সন্দেহের রাজনীতি শুধু প্রশাসনিক নয়, সামাজিকও। মাদ্রাসা মানেই আজ মিডিয়ার ভাষায় “চরমপন্থা”, “অস্বচ্ছতা”, “পিছিয়ে পড়া”। এই সামাজিক ধারণা BLO-এর চোখে ঢুকে পড়ে, প্রশাসনিক রিপোর্টে ঢুকে পড়ে, রাষ্ট্রীয় সত্যে পরিণত হয়। নাগরিক তখন আর কেবল রাষ্ট্রের কাছে সন্দেহভাজন নয়, সমাজের কাছেও সন্দেহভাজন। এই দ্বৈত সন্দেহ নাগরিককে সম্পূর্ণভাবে একা করে দেয়।
এসআইআর-এর সময় এই সন্দেহ সবচেয়ে ভয়ংকর হয়ে ওঠে, কারণ এখানে নাগরিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে প্রমাণ লাগে না। জীবনযাপনই যথেষ্ট। তুমি মাদ্রাসায় পড়েছ—সন্দেহ। তুমি কাজের জন্য বাইরে গেছ—সন্দেহ। তুমি বারবার ঠিকানা বদলেছ—সন্দেহ। তুমি একাধিক জায়গায় নথি রেখেছ—সন্দেহ। এই সন্দেহের বিরুদ্ধে কোনো আপিল নেই, কারণ এটি আচরণের বিরুদ্ধে, অপরাধের বিরুদ্ধে নয়। নাগরিক কীভাবে প্রমাণ করবে যে তার জীবন অপরাধ নয়?
এই প্রশ্নই আধুনিক রাষ্ট্রের সবচেয়ে ভয়ংকর প্রশ্ন। কারণ রাষ্ট্র এখানে নাগরিকের জীবনের ধরন নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। নাগরিককে বলা হয়—স্থায়ী হও, নথিভুক্ত হও, এক জায়গায় থাকো, এক রকম জীবন যাপন করো। এই আদর্শ নাগরিক আসলে মধ্যবিত্ত, শহুরে, স্থির মানুষ। মুসলমান, দরিদ্র, পরিযায়ী, মাদ্রাসা-শিক্ষিত মানুষ এই আদর্শে পড়ে না, তাই সে সন্দেহভাজন।
এই সন্দেহভাজন নাগরিক নির্মাণের সবচেয়ে গভীর দিক হলো—এটি প্রজন্মান্তরে কাজ করে। মাদ্রাসায় পড়া শিশুটি বড় হয় রাষ্ট্রীয় সন্দেহের ভেতর। পরিযায়ী পরিবারের সন্তান জন্ম থেকেই নথির ঘাটতিতে বড় হয়। সে যখন ভোটার হতে যায়, তখন তার জীবন ইতিহাসই তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। এই ধারাবাহিকতা রাষ্ট্র তৈরি করে না, কিন্তু রাষ্ট্র ব্যবহার করে।
আন্তর্জাতিকভাবে এই কৌশল পরিচিত। ফ্রান্সে মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে “রিপাবলিকান মূল্যবোধের বিরোধী” বলে সন্দেহ করা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের চলাচল ও জীবনযাপন নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে, চীনে উইঘুরদের জীবনযাপনকে অপরাধে রূপান্তর করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই জীবনধারাই অপরাধ¹। ভারতে এই কৌশল আরও সূক্ষ্ম, কারণ এখানে তা প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার ভেতর ঢুকে গেছে।
এসআইআর এই সূক্ষ্মতার নিখুঁত যন্ত্র। এখানে রাষ্ট্র কোনো আইন করে না, কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি করে না, কোনো ঘোষণা দেয় না। সে কেবল জীবনযাপন যাচাই করে। কিন্তু এই যাচাইয়ের অর্থ হলো—জীবন গ্রহণযোগ্য কি না। নাগরিক তখন আর রাষ্ট্রের সমান সদস্য নয়, সে পরীক্ষার্থী।
এই পরীক্ষার ফলাফল প্রায় সবসময় একই—মুসলমান, মাদ্রাসা-শিক্ষিত, পরিযায়ী মানুষ ফেল করে। কারণ পরীক্ষার প্রশ্নই তাদের জীবনের বিরুদ্ধে। এই ব্যর্থতা রাষ্ট্রীয় নথিতে “বাদ” হয়ে ওঠে। আর এই বাদ পড়াই নাগরিকত্বের নীরব সমাপ্তি।
এই প্রবন্ধের মূল সত্য তাই নির্মমভাবে স্পষ্ট—এসআইআর কেবল নাম যাচাই করে না, জীবন যাচাই করে। আর যে রাষ্ট্র জীবন যাচাই করতে শুরু করে, সে আর গণতান্ত্রিক থাকে না। সে হয়ে ওঠে শাসক, আর নাগরিক হয়ে ওঠে সন্দেহভাজন প্রজা।
এই সন্দেহের রাজনীতি থামানো না গেলে, একদিন কোনো জীবনই নিরাপদ থাকবে না। কারণ আজ মাদ্রাসা ও পরিযায়ী জীবন সন্দেহভাজন, কাল অন্য কোনো জীবনধারা হবে। রাষ্ট্রের সন্দেহের তালিকা কখনো পূর্ণ হয় না; সে সবসময় নতুন শিকার খোঁজে।
এই বাস্তবতা বুঝতে পারলে স্পষ্ট হয়—মুসলমানদের জীবনযাপন অপরাধ বানানো মানে আসলে নাগরিকত্বকেই অপরাধ বানানো। আর যে রাষ্ট্র নাগরিকত্বকে অপরাধ বানায়, সে রাষ্ট্র একদিন নিজেকেই অপরাধে পরিণত করে।
মুসলিম নারীরা কেন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত
মুসলিম নারীরা যখন রাষ্ট্রীয় যাচাইয়ের মুখোমুখি হন, তখন তাদের বিরুদ্ধে সন্দেহ আসে তিন দিক থেকে—লিঙ্গ, ধর্ম ও শ্রেণি। এই তিন স্তরের বৈষম্য একসঙ্গে কাজ করে বলেই মুসলিম নারীর নাম ভোটার তালিকা, নাগরিক নথি ও রাষ্ট্রীয় ডেটাবেসে সবচেয়ে বেশি ঝরে পড়ে। এসআইআর, ভোটার তালিকা সংশোধন, নাগরিকত্ব যাচাই—এই সব প্রক্রিয়ায় মুসলিম নারী শুধু একজন নাগরিক নন, তিনি একসঙ্গে “ভুল নাম”, “ভুল বয়স” ও “ভুল ঠিকানার” মানুষ। তাঁর অস্তিত্বই রাষ্ট্রের কাছে সন্দেহ।
ভারতের সামাজিক কাঠামোয় নারী মানেই নথিগত দুর্বলতা। মুসলিম নারীর ক্ষেত্রে সেই দুর্বলতা বহুগুণে বাড়ে। কারণ বহু মুসলিম পরিবারে জন্মসনদ, স্কুলের রেকর্ড, জমির দলিল—এই সব নথি ঐতিহাসিকভাবে কম। বাল্যবিবাহ, ঘরোয়া শ্রম, ধর্মীয় শিক্ষার প্রাধান্য, দারিদ্র্য—এই বাস্তবতাগুলো মুসলিম নারীদের নথির বাইরে রেখেছে। রাষ্ট্র এই বাস্তবতাকে সংশোধনের চেষ্টা না করে তাকে অপরাধে রূপান্তর করেছে। ফলে এসআইআর-এর মতো প্রক্রিয়ায় মুসলিম নারীরা প্রথমেই সন্দেহভাজন হয়ে ওঠেন।
নামের সমস্যা মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ফাঁদ। একাধিক বানান, একাধিক নাম, বিবাহের পরে নাম বদল—এই সব মুসলিম সমাজে সাধারণ, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ডেটাবেসে এটি “অসঙ্গতি”। ফাতেমা হয়ে যায় ফাতিমা, খাতুন হয়ে যায় খানম, বিবাহের পরে বাবার নাম বদলে স্বামীর নাম যুক্ত হয়—এই সব পরিবর্তন রাষ্ট্রের কাছে সন্দেহের কারণ। পুরুষের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন কম, নারীর ক্ষেত্রে বেশি—তাই নারীর নামই প্রথমে বাদ পড়ে। নাম এখানে পরিচয় নয়, ফাঁদ হয়ে ওঠে।
বয়স মুসলিম নারীদের জন্য আরেকটি ভয়ংকর অস্ত্র। বহু মুসলিম নারী নিজের জন্মতারিখ জানেন না, কারণ জন্মসনদ ছিল না, স্কুলে ভর্তি হয়নি। বয়সের হিসাব করা হয়েছে অনুমানভিত্তিক, কখনো হিজরি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, কখনো স্থানীয় স্মৃতির ওপর ভিত্তি করে। রাষ্ট্রীয় নথিতে যখন এই বয়স মিলতে চায়, তখন সামান্য পার্থক্যও অপরাধে রূপ নেয়। ভোটার তালিকা, আধার, রেশন কার্ড—সবখানেই আলাদা বয়স। এই অমিল নারীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সন্দেহ তৈরি করে, আর সেই সন্দেহই বাদ পড়ার ভিত্তি হয়ে যায়।
ঠিকানা মুসলিম নারীর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। বিয়ের পরে নারীর ঠিকানা বদলায়—এটি সামাজিক স্বাভাবিকতা। কিন্তু রাষ্ট্রের নথিতে এটি অপরাধ। বহু মুসলিম নারী বিয়ের পরে নতুন ঠিকানায় নাম তোলেন না, বা তুলতে পারেন না। কারণ প্রক্রিয়া জটিল, পুরুষনির্ভর, সময়সাপেক্ষ। ফলে এক জায়গা থেকে নাম কেটে যায়, অন্য জায়গায় ওঠে না। এই শূন্যতার মধ্যেই নারী রাজনৈতিকভাবে অদৃশ্য হয়ে যান। এসআইআর সেই অদৃশ্যতাকে স্থায়ী করে।
মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রে BLO-র ভূমিকা আরও পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে ওঠে। বহু রিপোর্টে দেখা গেছে, যাচাইয়ের সময় BLO পুরুষ সদস্যের কথাই চূড়ান্ত বলে ধরে নেন। পুরুষ যদি বলেন—“সে এখানে থাকে না”, “বিয়ে হয়ে গেছে”, “ওর নাম অন্য জায়গায়”—তাহলেই নারী বাদ পড়ে। নারীর নিজের বক্তব্য, নিজের উপস্থিতি, নিজের পরিচয় এখানে গুরুত্ব পায় না। ঘরোয়া পিতৃতন্ত্র রাষ্ট্রীয় নথিতে ঢুকে পড়ে, আর রাষ্ট্র সেই পিতৃতন্ত্রকে বৈধতা দেয়¹।
এই প্রক্রিয়ায় মুসলিম নারী দ্বিগুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। একদিকে তিনি নাগরিক হিসেবে বাদ পড়েন, অন্যদিকে নারী হিসেবে তাঁর কণ্ঠস্বর মুছে যায়। ভোট দিতে না পারা মানে মুসলিম নারীর সামাজিক ক্ষমতাও কমে যায়। তিনি আর রাষ্ট্রের কাছে গণ্য নন, ফলে তাঁর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সহিংসতার প্রশ্ন রাষ্ট্রের নীতিতে গুরুত্ব পায় না। ভোটাধিকার হরণ এখানে কেবল রাজনৈতিক নয়, এটি লিঙ্গীয় সহিংসতা।
মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রে এই ক্ষতি প্রজন্মান্তরে কাজ করে। মা ভোট দিতে পারেন না, ফলে মেয়ের ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত। রাষ্ট্রীয় ডেটাবেসে পরিবারটাই সন্দেহভাজন হয়ে যায়। এই সন্দেহ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য উত্তরাধিকার হয়ে ওঠে। মুসলিম নারীর শরীর তখন কেবল ব্যক্তি নয়, রাষ্ট্রীয় ফাইল।
এই বৈষম্য আরও গভীর হয় দারিদ্র্যের সঙ্গে। দরিদ্র মুসলিম নারীর কাছে নথি নেই, সময় নেই, আইনি সহায়তা নেই। তিনি আপিল করতে পারেন না, সংশোধন করতে পারেন না। ফলে একবার বাদ পড়লে তিনি চিরতরে বাদ পড়েন। মধ্যবিত্ত মুসলিম নারী হয়তো লড়তে পারেন, দরিদ্র নারী পারেন না। রাষ্ট্র এই পার্থক্য জানে, এবং সেই জানার ওপরই তার নীতি দাঁড়ায়।
ডিজিটালাইজেশন মুসলিম নারীদের সংকট আরও বাড়িয়েছে। অনলাইন ফর্ম, ওটিপি, বায়োমেট্রিক—এই সব প্রযুক্তি পুরুষনির্ভর সমাজে নারীদের জন্য প্রায় অপ্রাপ্য। মোবাইল ফোন অনেক নারীর হাতে নেই, ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ নেই। ফলে সংশোধনের সময়সীমা পেরিয়ে যায়, আর নারী বাদ পড়ে। প্রযুক্তি এখানে নিরপেক্ষ নয়; এটি লিঙ্গীয় বৈষম্যের বাহক।
এই পুরো প্রক্রিয়া রাষ্ট্রীয় সন্দেহকে নারীর শরীরে লিখে দেয়। নাম সন্দেহ, বয়স সন্দেহ, ঠিকানা সন্দেহ—নারীর অস্তিত্বই সন্দেহ। মুসলিম নারীর জীবনের কোনো দিকই রাষ্ট্রের কাছে স্বাভাবিক নয়। এই অস্বাভাবিকতার ধারণা রাষ্ট্র তৈরি করে না, কিন্তু রাষ্ট্র ব্যবহার করে। এই ব্যবহারই এসআইআর-এর রাজনৈতিক প্রকৃতি।
আন্তর্জাতিকভাবে মুসলিম নারীদের এই অভিজ্ঞতা নতুন নয়। ফ্রান্সে মুসলিম নারীদের পোশাক সন্দেহের কারণ, যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিম নারীদের চলাচল সন্দেহের কারণ, মিয়ানমারে রোহিঙ্গা নারীদের পরিচয় সন্দেহের কারণ। সবখানেই নারী ও ধর্ম একসঙ্গে সন্দেহের বস্তু²। ভারতে এই সন্দেহ প্রশাসনিক নথিতে ঢুকে পড়েছে, তাই তা আরও ভয়ংকর।
এই বাস্তবতা বুঝতে পারলে স্পষ্ট হয়—মুসলিম নারীরা শুধু এসআইআর-এর শিকার নন, তারা রাষ্ট্রীয় সন্দেহের প্রতীক। রাষ্ট্র তাদের শরীরের ওপর সন্দেহ লিখে দেয়, যাতে সমাজও সন্দেহ করতে শেখে। এই সামাজিক সন্দেহই রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শক্তি, কারণ তখন দমন আর একা রাষ্ট্রের কাজ থাকে না।
এই প্রবন্ধের শেষ সত্য তাই নির্মম—মুসলিম নারীদের নাম, বয়স ও ঠিকানা নিয়ে সন্দেহ মানে নারীর নাগরিকত্বকেই সন্দেহ করা। আর যে রাষ্ট্র নারীর নাগরিকত্ব সন্দেহ করে, সে রাষ্ট্র কখনো ন্যায়ভিত্তিক হতে পারে না। গণতন্ত্র সেখানে কেবল কাগজে থাকে, জীবনে নয়।
এই নীরব ক্ষয় যদি এখনই থামানো না যায়, তবে একদিন মুসলিম নারীর নাম শুধু তালিকা থেকে নয়, ইতিহাস থেকেও মুছে যাবে। আর যে ইতিহাস নারীর নাম মুছে দেয়, সে ইতিহাস নিজেই অপরাধে পরিণত হয়।
সংখ্যালঘু মানেই সন্দেহভাজন—রাষ্ট্রের নতুন দর্শন
আধুনিক রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু মানে আর শুধু সংখ্যাগত বাস্তবতা নয়—সংখ্যালঘু মানে সন্দেহভাজন। এই রূপান্তরই রাষ্ট্রের নতুন দর্শন, যেখানে গণতন্ত্র ধীরে ধীরে বদলে গিয়ে হয়ে ওঠে “বাছাই রাষ্ট্র”—যে রাষ্ট্র নাগরিককে সমান অধিকার দেয় না, বরং আগে বাছাই করে নেয় কে অধিকার পাওয়ার যোগ্য, আর কে সন্দেহের অধিকারী। এসআইআর, ভোটার তালিকা সংশোধন, নাগরিকত্ব যাচাই, ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন—এই সব প্রক্রিয়া সেই বাছাই রাষ্ট্রের যন্ত্র, যার মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব ধাপে ধাপে অনিশ্চিত করা হয়।
গণতন্ত্রের মৌলিক ধারণা ছিল—রাষ্ট্র নাগরিককে বিশ্বাস করবে, যতক্ষণ না নাগরিক অপরাধ প্রমাণিত হয়। কিন্তু বাছাই রাষ্ট্রে এই নীতিটি উল্টে যায়। এখানে নাগরিককে প্রথমে সন্দেহ করা হয়, তারপর প্রমাণ দিতে বলা হয়, তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সে নাগরিক কি না। এই উল্টো নৈতিকতাই সংখ্যালঘুদের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক, কারণ সন্দেহের তীর সবসময় সংখ্যালঘুর দিকেই যায়। সংখ্যাগুরু কখনোই সন্দেহভাজন হয় না, কারণ তার জীবনধারাই রাষ্ট্রীয় আদর্শ।
ভারতের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন স্পষ্ট। মুসলমান, খ্রিস্টান, আদিবাসী, দলিত, ভাষাগত সংখ্যালঘু—এই সব গোষ্ঠীর জীবনযাপন, ইতিহাস ও সামাজিক অবস্থান রাষ্ট্রীয় নথির সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না। এই অমিল রাষ্ট্রের চোখে বৈচিত্র্য নয়, সমস্যা। ফলে রাষ্ট্র এমন নীতি তৈরি করে, যেখানে এই অমিলই সন্দেহের ভিত্তি হয়ে ওঠে। সংখ্যালঘু মানেই নথিগত দুর্বলতা, মানেই যাচাইযোগ্য নাগরিক, মানেই শর্তাধীন অধিকার।
এসআইআর এই দর্শনের একটি নিখুঁত প্রকাশ। এখানে রাষ্ট্র প্রকাশ্যে বলে না—সংখ্যালঘুরা সমস্যা। সে বলে—আমরা তালিকা শুদ্ধ করছি। কিন্তু এই শুদ্ধিকরণ কোথায় হয়, কাদের ওপর হয়, কারা বাদ পড়ে—এই সব প্রশ্নের উত্তর দেখলেই বোঝা যায়, শুদ্ধিকরণ আসলে বাছাই। এই বাছাইয়ে সংখ্যালঘুরাই বাদ পড়ে, আর সংখ্যাগুরু থেকে যায়। রাষ্ট্র এখানে গণতান্ত্রিক নয়, নির্বাচনমূলক।
বাছাই রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো—এটি আইনের ভাষায় বৈষম্য করে। কোনো আইন বলে না যে মুসলমান সন্দেহভাজন, কিন্তু প্রশাসনিক প্রক্রিয়া এমনভাবে তৈরি হয় যে মুসলমানই সবচেয়ে বেশি যাচাইয়ের মুখে পড়ে। কোনো নির্দেশিকা বলে না যে আদিবাসী নাগরিক অনিশ্চিত, কিন্তু তাদের কাগজই সবচেয়ে বেশি অগ্রহণযোগ্য। এই নীরব বৈষম্যই রাষ্ট্রের নতুন কৌশল—যেখানে দমন ঘটে নিয়মের ভেতর দিয়ে, বৈষম্য ঘটে নিরপেক্ষতার ভাষায়।
এই দর্শন শুধু প্রশাসনিক নয়, আদর্শিক। রাষ্ট্র ধীরে ধীরে নাগরিকত্বকে নৈতিকতার প্রশ্ন বানাচ্ছে—কে “ভাল নাগরিক”, কে “ঝুঁকিপূর্ণ নাগরিক”। ভাল নাগরিক মানে স্থায়ী, নথিসম্পন্ন, সংখ্যাগুরুভিত্তিক, রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মানানসই মানুষ। আর ঝুঁকিপূর্ণ নাগরিক মানে সংখ্যালঘু, চলমান, বহুবিধ পরিচয়ের মানুষ। এই নৈতিক বিভাজনই গণতন্ত্রের মৃত্যু, কারণ গণতন্ত্রে নাগরিকত্ব কোনো নৈতিক পুরস্কার নয়, এটি জন্মগত অধিকার।
বাছাই রাষ্ট্রের আরেকটি ভয়ংকর দিক হলো—এটি সমাজকে রাষ্ট্রের সহযোগীতে পরিণত করে। যখন রাষ্ট্র সন্দেহ তৈরি করে, তখন সমাজও সন্দেহ করতে শেখে। প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে সন্দেহ করে, BLO প্রতিবেশীর কথায় রিপোর্ট লেখে, মিডিয়া রাষ্ট্রীয় সন্দেহকে সামাজিক সত্যে রূপ দেয়। সংখ্যালঘু নাগরিক তখন শুধু রাষ্ট্রের কাছে নয়, সমাজের কাছেও সন্দেহভাজন। এই সামাজিক বৈধতাই রাষ্ট্রের দমনকে শক্তিশালী করে।
এই দর্শনের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো—এটি সংবিধানকে উল্টো করে দেয়। সংবিধান যেখানে নাগরিকের অধিকার নিশ্চিত করে, বাছাই রাষ্ট্র সেখানে নাগরিকের অধিকারকে শর্তাধীন করে। আজ ভোট, কাল রেশন, পরশু বাসস্থান—সবকিছুই প্রমাণসাপেক্ষ। নাগরিক তখন আর অধিকারভোগী নয়, আবেদনকারী। এই আবেদনকারী রাষ্ট্রের সামনে সবসময় নতজানু থাকে।
আন্তর্জাতিকভাবে এই প্রবণতা নতুন নয়। ইউরোপে মুসলমানরা, যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসীরা, মিয়ানমারে রোহিঙ্গারা—সবখানেই সংখ্যালঘু মানেই সন্দেহভাজন নাগরিক। কিন্তু ভারতে এই প্রক্রিয়া আরও ভয়ংকর, কারণ এখানে সংখ্যালঘুরা বিদেশি নয়; তারা এই ভূমির ইতিহাস। তবু রাষ্ট্র তাদের ইতিহাসকেই সন্দেহের কারণ বানায়। এই ইতিহাস-বিদ্বেষই বাছাই রাষ্ট্রের সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক।
বাছাই রাষ্ট্রের সবচেয়ে সূক্ষ্ম কৌশল হলো—এটি ধীরে ধীরে কাজ করে। একদিনে নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হয় না, এক নির্বাচনে গণতন্ত্র শেষ হয় না। ধাপে ধাপে অধিকার সংকুচিত হয়, ধাপে ধাপে সন্দেহ বাড়ে, ধাপে ধাপে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে যায়। এই অভ্যাসই রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সাফল্য। কারণ অভ্যস্ত মানুষ আর প্রতিবাদ করে না, সে নিয়ম মেনে নেয়।
এই প্রবন্ধের মূল কথা তাই স্পষ্ট—সংখ্যালঘু মানেই সন্দেহভাজন, এটি কোনো বিচ্ছিন্ন প্রশাসনিক ত্রুটি নয়, এটি রাষ্ট্রের নতুন দর্শন। এই দর্শনে গণতন্ত্র আর জনগণের শাসন নয়, এটি বাছাই করা জনগণের শাসন। আর যে রাষ্ট্র জনগণকে বাছাই করে, সে রাষ্ট্র একদিন নিজের নাগরিককেই চিনতে পারে না।
এই বাছাই রাষ্ট্র যদি থামানো না যায়, তবে গণতন্ত্র শব্দটি কেবল সংবিধানের পাতায় থাকবে, জীবনে নয়। আজ সংখ্যালঘু সন্দেহভাজন, কাল অন্য কেউ হবে। সন্দেহের তালিকা কখনো শেষ হয় না। ইতিহাস দেখিয়েছে—যে রাষ্ট্র সন্দেহ দিয়ে শুরু করে, সে একদিন শূন্য দিয়ে শেষ করে।
এই কারণেই সংখ্যালঘুদের সন্দেহভাজন বানানো মানে শুধু একটি জনগোষ্ঠীর ওপর আঘাত নয়—এটি গণতন্ত্রের ওপর আঘাত। আর গণতন্ত্রে আঘাত মানে শেষ পর্যন্ত সবাই আঘাতপ্রাপ্ত। কারণ বাছাই রাষ্ট্রে কেউই নিরাপদ নয়।
রোহিঙ্গা ও অনুপ্রবেশ: ভয় তৈরির প্রোপাগান্ডা
রোহিঙ্গা ও অনুপ্রবেশ—এই দুটি শব্দ আজ আর কেবল মানবিক সংকট বা সীমান্ত-বাস্তবতার বর্ণনা নয়; এগুলো রাষ্ট্রীয় ভয় তৈরির সবচেয়ে কার্যকর প্রোপাগান্ডা-যন্ত্র। আধুনিক রাষ্ট্র যখন নাগরিকের অধিকার সংকুচিত করতে চায়, তখন সে প্রথমে ভয় তৈরি করে। এই ভয় যদি বাইরের শত্রুকে ঘিরে হয়, তবে ভেতরের দমন সহজ হয়। রোহিঙ্গা সেই বাইরের শত্রু, অনুপ্রবেশ সেই ভয়ংকর শব্দ—যার মাধ্যমে রাষ্ট্র ভেতরের নাগরিকদের অধিকার হরণকে বৈধতা দেয়। এই প্রোপাগান্ডার সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক হলো, এটি সত্য ও মিথ্যার সীমা মুছে দেয়, মানবিক বিপর্যয়কে রাজনৈতিক অস্ত্রে রূপান্তর করে।
রোহিঙ্গা সংকট একটি ঐতিহাসিক মানবিক বিপর্যয়। মিয়ানমারে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, জাতিগত শুদ্ধি অভিযান, গণহত্যা ও নাগরিকত্ব অস্বীকারের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে। জাতিসংঘ একে “ethnic cleansing” ও “genocide” বলে চিহ্নিত করেছে। এই মানুষগুলো কোনো রাজনৈতিক প্রকল্পের অংশ ছিল না; তারা ছিল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার। কিন্তু ভারতীয় রাজনৈতিক বয়ানে রোহিঙ্গা আর শরণার্থী নয়—তারা “অনুপ্রবেশকারী”, “ঝুঁকি”, “নিরাপত্তা হুমকি”। এই ভাষান্তরই প্রোপাগান্ডার প্রথম ধাপ।
প্রোপাগান্ডা সবসময় ভাষা দিয়ে শুরু হয়। “শরণার্থী” শব্দে সহানুভূতি আছে, “অনুপ্রবেশকারী” শব্দে শত্রুতা। রাষ্ট্র যখন ভাষা বদলায়, তখন নাগরিকের অনুভূতিও বদলে যায়। রোহিঙ্গারা তখন আর নিপীড়িত মানুষ নয়, তারা হয়ে ওঠে সম্ভাব্য অপরাধী। এই অপরাধীকরণ রাষ্ট্রকে নৈতিক ছাড় দেয়—যাতে সে নাগরিকত্ব যাচাই, ভোটার তালিকা শুদ্ধিকরণ, এসআইআর-এর মতো প্রক্রিয়ায় কঠোর হতে পারে। রাষ্ট্র বলে—আমরা নিরাপত্তা রক্ষা করছি। কিন্তু বাস্তবে সে ভয়কে ব্যবহার করে অধিকার সংকুচিত করছে।
এই প্রোপাগান্ডার সবচেয়ে কার্যকর দিক হলো—এটি অস্পষ্ট। কত রোহিঙ্গা ভারতে আছে, কোথায় আছে, কী করছে—এই প্রশ্নগুলোর কোনো নির্ভরযোগ্য সরকারি তথ্য নেই। তবু সংখ্যা বারবার বাড়ে, হুমকি বারবার বাড়ে, আতঙ্ক বারবার বাড়ে। এই অস্পষ্টতা প্রোপাগান্ডার শক্তি, কারণ ভয় যত অনির্দিষ্ট, তত কার্যকর। নাগরিক তখন বুঝতে পারে না—সে কাকে ভয় করবে, তাই সে সবাইকেই সন্দেহ করে।
এই সন্দেহের রাজনীতি সরাসরি মুসলমানদের ওপর পড়ে। কারণ রোহিঙ্গারা মুসলমান, এবং প্রোপাগান্ডা মুসলমান পরিচয়কে “বহিরাগত”-এর সঙ্গে যুক্ত করে দেয়। ফলে ভারতীয় মুসলমান নাগরিকও সন্দেহের আওতায় পড়ে। তার কাগজ, তার নাম, তার ভাষা, তার জীবনযাপন—সবকিছু রাষ্ট্রীয় যাচাইয়ের মুখে পড়ে। রোহিঙ্গা প্রোপাগান্ডা এখানে এক ধরনের ঢাল—যার আড়ালে রাষ্ট্র নিজের নাগরিকদের অধিকার হরণ করে। এসআইআর সেই ঢালের নিচে চালানো প্রশাসনিক অস্ত্র।
এই প্রোপাগান্ডার আরেকটি ভয়ংকর দিক হলো—এটি ইতিহাস মুছে দেয়। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চলের মানুষদের চলাচল শতাব্দীপ্রাচীন। নদী বদলায়, গ্রাম সরে যায়, মানুষ স্থানান্তরিত হয়। এই ইতিহাস রাষ্ট্র জানে, কিন্তু স্বীকার করে না। সে বলে—অনুপ্রবেশ। এই এক শব্দে ইতিহাস অপরাধে পরিণত হয়। যে মানুষ নদীর ভাঙনে ঘর হারিয়েছে, সে “অনুপ্রবেশকারী”; যে মানুষ কাজের জন্য সীমান্ত পেরিয়েছে, সে “ঝুঁকি”; যে মানুষ দারিদ্র্যের কারণে স্থান বদলেছে, সে “অবৈধ”। রাষ্ট্র এই বাস্তবতাকে বুঝতে চায় না, কারণ না বুঝলেই দমন সহজ।
রোহিঙ্গা প্রোপাগান্ডা এসআইআর-এর মতো প্রক্রিয়াকে সামাজিক বৈধতা দেয়। যখন নাগরিক বিশ্বাস করতে শুরু করে যে “অনুপ্রবেশকারী” আছে, তখন সে ভোটার তালিকা শুদ্ধিকরণকে সমর্থন করে। সে ভাবে—ভালই হচ্ছে, খারাপরা বাদ যাচ্ছে। সে বুঝতে পারে না—বাদ যাচ্ছে সে নিজেই। এই আত্মঘাতী সম্মতিই প্রোপাগান্ডার চূড়ান্ত সাফল্য।
মিডিয়ার ভূমিকা এখানে নির্ণায়ক। টেলিভিশন স্ক্রিনে রোহিঙ্গা মানেই ভয়, মানেই অপরাধ, মানেই সংখ্যা। কোনো মানবিক গল্প নেই, কোনো প্রমাণ নেই, কেবল আতঙ্ক। এই আতঙ্ক রাষ্ট্রের নীতিকে নৈতিক করে তোলে। যখন রাষ্ট্র বলে—ডকুমেন্ট যাচাই হবে, নাগরিক বলে—হোক, নিরাপত্তা দরকার। এই নিরাপত্তার নামে অধিকার বলি যায়। ইতিহাস বলছে—সব ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রই নিরাপত্তার নামে শুরু করেছে।
এই প্রোপাগান্ডার সবচেয়ে গভীর প্রভাব পড়ে গণতন্ত্রে। কারণ গণতন্ত্র বিশ্বাসের ওপর দাঁড়ায়—রাষ্ট্র নাগরিককে বিশ্বাস করবে, নাগরিক রাষ্ট্রকে প্রশ্ন করবে। ভয় এই সম্পর্ক ভেঙে দেয়। আতঙ্কিত নাগরিক প্রশ্ন করে না, সে নিরাপত্তা চায়। নিরাপত্তা চাইলে রাষ্ট্র আরও ক্ষমতা পায়। এই ক্ষমতার সম্প্রসারণই এসআইআর, এনআরসি, ডকুমেন্টেশন রাজনীতির ভিত্তি।
রোহিঙ্গা প্রোপাগান্ডা আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত কৌশল। ইউরোপে শরণার্থীদের বিরুদ্ধে একই ভাষা ব্যবহার হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসীদের বিরুদ্ধে একই ভয় তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ফল এক—অধিকার সংকোচন, রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি, সংখ্যালঘুদের নিঃশব্দ বর্জন। ভারতে এই কৌশল আরও বিপজ্জনক, কারণ এখানে সংখ্যালঘুরা বহুসংখ্যক নাগরিক, তবু তাদের বহিরাগত বানানো হচ্ছে।
এই প্রোপাগান্ডা এসআইআরকে “প্রয়োজনীয়” করে তোলে। রাষ্ট্র বলে—যদি যাচাই না করি, অনুপ্রবেশ হবে। কিন্তু বাস্তবে এসআইআর অনুপ্রবেশ আটকায় না; সে নাগরিকদের বাদ দেয়। রোহিঙ্গারা কোথাও ভোটার তালিকায় নেই, তবু ভোটার তালিকা শুদ্ধিকরণ মুসলমান নাগরিকদের নাম মুছে দেয়। এই বৈপরীত্যই প্রমাণ করে—প্রোপাগান্ডার লক্ষ্য নিরাপত্তা নয়, নিয়ন্ত্রণ।
এই প্রবন্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সত্য তাই স্পষ্ট—রোহিঙ্গা ও অনুপ্রবেশের ভয় একটি রাজনৈতিক নির্মাণ। এই নির্মাণ ছাড়া এসআইআর-এর মতো প্রক্রিয়া বৈধতা পেত না, নাগরিকত্ব যাচাই সামাজিক সমর্থন পেত না, রাষ্ট্রীয় সন্দেহ স্বাভাবিক হতো না। ভয় এখানে কেবল আবেগ নয়, এটি নীতি।
এই ভয় যদি আমরা ভাঙতে না পারি, তবে গণতন্ত্র টিকবে না। কারণ যে রাষ্ট্র ভয় দিয়ে শাসন করে, সে আর নাগরিকের রাষ্ট্র থাকে না; সে হয়ে ওঠে সন্দেহের রাষ্ট্র। আর সন্দেহের রাষ্ট্রে সবাই একদিন অনুপ্রবেশকারী হয়ে ওঠে।
“রোহিঙ্গা” শব্দটি কীভাবে রাজনৈতিক অস্ত্র
“রোহিঙ্গা”—এই শব্দটি আজ ভারতে আর কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর পরিচয় নয়; এটি একটি রাজনৈতিক অস্ত্র, যার ধার দিয়ে ভয় তৈরি করা হয়, নাগরিকত্ব সন্দেহভাজন করা হয়, এবং গণতান্ত্রিক অধিকার সংকুচিত করা হয়। শব্দটি নিজেই একটি অস্ত্রে পরিণত হয়েছে, কারণ এটি বাস্তবতা ব্যাখ্যা করতে নয়, বরং বাস্তবতাকে ঢেকে রাখতে ব্যবহৃত হয়। রাষ্ট্র যখন কোনো শব্দকে প্রমাণ ছাড়াই বারবার উচ্চারণ করে, তখন সেই শব্দ সত্যে পরিণত হয় না—ভয়ে পরিণত হয়। আর ভয়ই আধুনিক শাসনের সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম।
রোহিঙ্গা সংকটের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট স্পষ্ট: মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে কয়েক দশক ধরে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, নাগরিকত্ব অস্বীকার, সামরিক অভিযান ও জাতিগত নির্মূল প্রক্রিয়ার ফলে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলমান পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা এই ঘটনাকে গণহত্যা ও জাতিগত শুদ্ধিকরণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে¹। কিন্তু ভারতে এই মানবিক বাস্তবতা প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তার ভাষা বদলে যায়। শরণার্থী শব্দটি মুছে যায়, ঢুকে পড়ে “অনুপ্রবেশকারী”। মানবিক বিপর্যয় হয়ে ওঠে নিরাপত্তা সমস্যা। এই ভাষান্তরই রাজনৈতিক অস্ত্রায়নের প্রথম ধাপ।
রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে “রোহিঙ্গা” শব্দটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো—এটি প্রমাণহীন। কত রোহিঙ্গা ভারতে আছে, তারা কোথায় আছে, তারা কী করছে—এই প্রশ্নগুলোর কোনো নির্ভরযোগ্য সরকারি পরিসংখ্যান নেই। সংসদে বারবার এই প্রশ্ন উঠলেও সরকার কখনো নির্দিষ্ট তথ্য দেয়নি। তবু জনসমক্ষে এমন একটি ধারণা তৈরি করা হয়েছে যেন রোহিঙ্গারা সর্বত্র, তারা বিপজ্জনক, তারা ভোটার তালিকায় ঢুকে গেছে। এই ভয় সংখ্যার ওপর দাঁড়ায় না, দাঁড়ায় পুনরুক্তির ওপর। একই কথা বারবার বললে তা সত্যের মতো শোনায়—এই মনস্তাত্ত্বিক কৌশলই প্রোপাগান্ডার মূল।
এই প্রমাণহীন ভয় সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় নির্বাচন-পূর্ব সময়ে। তখন হঠাৎ করে রোহিঙ্গা শব্দটি সংবাদ শিরোনাম হয়, রাজনৈতিক বক্তৃতায় ঢুকে পড়ে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। নির্বাচন মানেই তখন নাগরিকত্ব যাচাই, তালিকা শুদ্ধিকরণ, এসআইআর-এর মতো প্রক্রিয়ার নৈতিক অজুহাত। রাষ্ট্র বলে—আমাদের সাবধান হতে হবে। কিন্তু এই সাবধানতার ফল হয় নাগরিকের অধিকার হরণ। এখানে রোহিঙ্গা শব্দটি একটি ধোঁয়া—যার আড়ালে রাষ্ট্র নিজের ক্ষমতা বাড়ায়।
এই অস্ত্রায়নের সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক হলো—এটি ভারতীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। কারণ রোহিঙ্গারা মুসলমান, এবং প্রোপাগান্ডা মুসলমান পরিচয়কে বহিরাগত হিসেবে উপস্থাপন করে। ফলে ভারতীয় মুসলমান নাগরিকও সন্দেহের আওতায় পড়ে। তার নাম, তার ভাষা, তার কাগজ—সবকিছু রোহিঙ্গা প্রোপাগান্ডার ছায়ায় যাচাই হয়। রাষ্ট্র এখানে সরাসরি বলে না—মুসলমান সন্দেহভাজন। কিন্তু রোহিঙ্গা শব্দটি ব্যবহার করে সে একই ফল অর্জন করে। এই পরোক্ষতা রাষ্ট্রীয় কৌশলের অংশ।
মিডিয়া এই অস্ত্রায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। টেলিভিশন বিতর্কে রোহিঙ্গারা কখনো মানুষ নয়, তারা “সমস্যা”। কোনো অনুসন্ধান নেই, কোনো মাঠ-প্রতিবেদন নেই, কেবল আতঙ্কের ভাষা। এই আতঙ্ক সাধারণ নাগরিকের মধ্যে এমন এক মানসিকতা তৈরি করে যেখানে সে নিজেই অধিকার হরণের পক্ষে দাঁড়ায়। সে ভাবে—যদি এতে অনুপ্রবেশ ঠেকে, তাহলে ভালোই। এই সম্মতিই প্রোপাগান্ডার সবচেয়ে বড় সাফল্য, কারণ তখন দমন আর জোর করে নয়, সম্মতির মাধ্যমে হয়।
রোহিঙ্গা শব্দটি রাজনৈতিক অস্ত্র হওয়ার আরেকটি কারণ হলো—এটি সীমান্ত বাস্তবতার জটিল ইতিহাস মুছে দেয়। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চলে মানুষের চলাচল শতাব্দীপ্রাচীন। নদী ভাঙে, গ্রাম সরে যায়, মানুষ স্থানান্তরিত হয়। এই ইতিহাসকে অস্বীকার করে রাষ্ট্র “অনুপ্রবেশ” শব্দ ব্যবহার করে, যেন সব চলাচল অপরাধ। এই এক শব্দে দরিদ্রতা, বাস্তুচ্যুতি ও ইতিহাস অপরাধে রূপান্তরিত হয়। রোহিঙ্গা প্রোপাগান্ডা এই বৃহত্তর ইতিহাস মুছে ফেলার হাতিয়ার।
এই শব্দের অস্ত্রায়ন শুধু প্রশাসনিক নয়, দার্শনিকও। এটি নাগরিকত্বের ধারণাকে বদলে দেয়। নাগরিকত্ব আর জন্মসূত্রে অধিকার নয়, এটি শর্তাধীন অবস্থায় পরিণত হয়। রাষ্ট্র নাগরিককে বিশ্বাস করে না; নাগরিককে নিজেকে প্রমাণ করতে হয়। এই প্রমাণের চাপ সবচেয়ে বেশি পড়ে সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক মানুষের ওপর। রোহিঙ্গা শব্দটি এই প্রমাণের রাজনীতিকে স্বাভাবিক করে তোলে।
আন্তর্জাতিকভাবে এই কৌশল পরিচিত। ইউরোপে শরণার্থীদের বিরুদ্ধে “অভিবাসী সংকট”, যুক্তরাষ্ট্রে “অবৈধ অনুপ্রবেশ”, অস্ট্রেলিয়ায় “বোট পিপল”—সবখানেই শব্দ অস্ত্র হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ফল এক—রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি, নাগরিকের অধিকার সংকোচন, মানবিক প্রশ্নের মৃত্যু²। ভারত এই বিশ্বব্যাপী প্রবণতার অংশ, কিন্তু এখানে এর প্রভাব আরও গভীর, কারণ এটি সংবিধানপ্রদত্ত নাগরিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে।
এই প্রবন্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সত্য তাই স্পষ্ট—“রোহিঙ্গা” শব্দটি একটি রাজনৈতিক নির্মাণ, যার শক্তি প্রমাণে নয়, ভয়তে। এই ভয় তৈরি করে রাষ্ট্র নাগরিকত্বকে শর্তাধীন করে, গণতন্ত্রকে দুর্বল করে, এবং সমাজকে বিভক্ত করে। শব্দটি এখানে কেবল শব্দ নয়; এটি একটি নীতি, একটি কৌশল, একটি অস্ত্র।
যে রাষ্ট্র শব্দকে অস্ত্র বানায়, সে আর যুক্তির রাষ্ট্র থাকে না। সে ভয় দিয়ে শাসন করে। আর ভয় দিয়ে শাসিত রাষ্ট্রে গণতন্ত্র শুধু আনুষ্ঠানিকতা, বাস্তবতা নয়। এই কারণেই রোহিঙ্গা শব্দের রাজনৈতিক অস্ত্রায়ন বোঝা মানে কেবল একটি প্রোপাগান্ডা চিহ্নিত করা নয়—এটি গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ বোঝা।
আজ যদি এই অস্ত্রায়ন প্রশ্নহীন থাকে, তবে কাল অন্য কোনো শব্দ অস্ত্র হবে, অন্য কোনো জনগোষ্ঠী সন্দেহভাজন হবে। ইতিহাস বলে—যে রাষ্ট্র একবার ভয়কে নীতি বানায়, সে আর থামে না। তাই রোহিঙ্গা শব্দের রাজনীতি ভাঙা মানে কেবল মুসলমানদের রক্ষা করা নয়, গণতন্ত্রকেই রক্ষা করা।
মিডিয়া ও রাষ্ট্রের যৌথ কল্পকাহিনি
মিডিয়া ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক যখন তথ্যের ওপর নয়, কল্পনার ওপর দাঁড়ায়, তখন গণতন্ত্র ধীরে ধীরে গল্পের দেশে প্রবেশ করে। এই গল্পে পরিসংখ্যানের জায়গা নেয় আবেগ, গবেষণার জায়গা নেয় আতঙ্ক, আর প্রমাণের জায়গা নেয় পুনরুক্তি। “ডেটা নেই, গল্প আছে”—এটি কেবল একটি বাক্য নয়, এটি আধুনিক রাষ্ট্র–মিডিয়া যুগলের কাজের পদ্ধতি। রোহিঙ্গা, অনুপ্রবেশ, এসআইআর, নাগরিকত্ব যাচাই—এই সব বিষয়েই মিডিয়া ও রাষ্ট্র মিলিতভাবে এমন এক কল্পকাহিনি নির্মাণ করেছে, যেখানে সত্যের প্রয়োজন নেই, কারণ গল্পই সত্য হয়ে ওঠে।
রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শক্তি তার ক্ষমতা নয়, তার বর্ণনা। রাষ্ট্র যখন কোনো বাস্তবতাকে বর্ণনা করে, তখন সেটিই “সরকারি সত্য” হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই বর্ণনার বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করে মিডিয়া। মিডিয়া যদি প্রশ্ন না করে, অনুসন্ধান না করে, তবে রাষ্ট্রের প্রতিটি দাবি সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। রোহিঙ্গা প্রসঙ্গে ঠিক এটিই ঘটেছে। সংসদে বারবার প্রশ্ন উঠেছে—কত রোহিঙ্গা ভারতে আছে? তারা কোথায়? তাদের বিরুদ্ধে কী অপরাধ? কিন্তু সরকার কোনো নির্দিষ্ট ডেটা দেয়নি। তবু মিডিয়ায় সংখ্যা ঘোরে, ভয় ছড়ায়, মানচিত্র আঁকা হয়। এই অসঙ্গতি মিডিয়াকে প্রশ্ন করতে বাধ্য করেনি; বরং মিডিয়াই গল্প বানিয়ে দিয়েছে।
এই গল্প নির্মাণের প্রথম ধাপ হলো “বিশেষজ্ঞ” তৈরি করা। টেলিভিশন স্টুডিওতে এমন মানুষ হাজির হন, যারা কখনো সীমান্তে যাননি, কোনো ডেটা দেখেননি, কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বলেন—“রোহিঙ্গারা ঢুকে পড়েছে”, “ভোটার তালিকায় নাম ঢুকেছে”, “নিরাপত্তা ঝুঁকি”। এই বক্তব্যের পেছনে কোনো নথি নেই, কিন্তু বারবার প্রচারের ফলে তা সত্যে পরিণত হয়। দর্শক ভাবেন—এত মানুষ বলছে, নিশ্চয়ই সত্য। এভাবেই কল্পনা গণতান্ত্রিক সম্মতি পায়।
রাষ্ট্র এই মিডিয়া-কল্পকাহিনিকে ব্যবহার করে নীতি তৈরি করে। এসআইআর, ভোটার তালিকা সংশোধন, ডকুমেন্ট যাচাই—সবকিছুই তখন “প্রয়োজনীয়” হয়ে ওঠে, কারণ মিডিয়া আগে থেকেই ভয় তৈরি করে দিয়েছে। রাষ্ট্র আর ব্যাখ্যা দেয় না, সে শুধু বলে—আপনারাই তো দেখছেন। এই “আপনারাই তো দেখছেন” কথাটিই সবচেয়ে বিপজ্জনক, কারণ এতে রাষ্ট্র তার দায় মিডিয়ার ওপর ঠেলে দেয়, আর মিডিয়া রাষ্ট্রের মুখপাত্রে পরিণত হয়।
এই যৌথ কল্পকাহিনির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো—এটি নির্দিষ্ট শত্রু তৈরি করে। রোহিঙ্গা এখানে শত্রু, অনুপ্রবেশকারী শত্রু, সন্দেহভাজন নাগরিক শত্রু। কিন্তু এই শত্রুর কোনো মুখ নেই, কোনো ঠিকানা নেই, কোনো প্রমাণ নেই। সে একটি ছায়া—যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা যায়, কিন্তু যাকে কখনো ধরা যায় না। এই অদৃশ্য শত্রুই রাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে উপযোগী, কারণ তাকে দেখিয়ে যে কাউকে সন্দেহ করা যায়। মিডিয়া এই অদৃশ্য শত্রুকে দৃশ্যমান করতে গ্রাফিক্স, সাউন্ডট্র্যাক, নাটকীয় ভাষা ব্যবহার করে। খবর তখন আর খবর থাকে না, থ্রিলার হয়ে ওঠে।
ডেটাহীন গল্পের সবচেয়ে ভয়ংকর দিক হলো—এটি সংশোধনযোগ্য নয়। কারণ ডেটা থাকলে তাকে চ্যালেঞ্জ করা যায়, ভুল ধরা যায়, বিকল্প ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কিন্তু গল্পকে খণ্ডন করা যায় না, কারণ গল্প আবেগে দাঁড়ায়। কেউ যদি বলে—“রোহিঙ্গারা ভোটার তালিকায় নেই”, তখন মিডিয়া বলে—“কিন্তু ভয় তো আছে।” এই “ভয় তো আছে” যুক্তিই সব যুক্তির সমাধান। রাষ্ট্র তখন বলে—ভয় থাকলে ব্যবস্থা নিতে হবে। এভাবেই ভয় নীতি হয়ে ওঠে।
এই কল্পকাহিনি সবচেয়ে বেশি আঘাত করে সংখ্যালঘুদের। কারণ গল্পের নায়ক কখনো সংখ্যালঘু হয় না; সে সবসময় সন্দেহভাজন। মিডিয়া মুসলমান পরিচয়কে এমনভাবে উপস্থাপন করে যেন তা স্বাভাবিক নয়, বরং ব্যতিক্রম। নাম, পোশাক, ভাষা—সবকিছুই গল্পের উপাদান হয়ে ওঠে। রাষ্ট্র এই উপস্থাপনাকে ব্যবহার করে প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় কঠোরতা বাড়ায়। BLO সন্দেহ করে, অফিস সন্দেহ করে, সমাজ সন্দেহ করে। এই সন্দেহের চক্র মিডিয়া–রাষ্ট্র যৌথভাবে চালায়।
এই প্রক্রিয়া শুধু বর্তমান নয়, ঐতিহাসিক। উপনিবেশিক আমলেও ব্রিটিশরা সংবাদপত্র ব্যবহার করে “বিদ্রোহী”, “অপরাধী”, “অবিশ্বস্ত” জনগোষ্ঠী তৈরি করত। আজকের পার্থক্য হলো—এখন মিডিয়া স্বাধীন বলে পরিচিত, কিন্তু আচরণে রাষ্ট্রের সহচর। স্বাধীনতার মুখোশে এই কল্পকাহিনি আরও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে।
ডিজিটাল মিডিয়া এই কল্পকাহিনিকে আরও দ্রুত ছড়ায়। হোয়াটসঅ্যাপ ফরোয়ার্ড, ইউটিউব ভিডিও, ফেসবুক পোস্ট—সবখানে একই গল্প, একই ভয়, একই শব্দ। এই পুনরাবৃত্তি নাগরিকের চিন্তাশক্তিকে দুর্বল করে দেয়। সে আর প্রশ্ন করতে শেখে না, সে বিশ্বাস করতে শেখে। গণতন্ত্রে প্রশ্ন নাগরিকের অস্ত্র, কিন্তু কল্পকাহিনির যুগে বিশ্বাসই অস্ত্র।
এই মিডিয়া–রাষ্ট্র যুগলের সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো—তারা ডেটার অনুপস্থিতিকেই অদৃশ্য করে দেয়। কেউ আর ডেটা চায় না, কেউ আর রিপোর্ট পড়ে না, কেউ আর প্রমাণ খোঁজে না। গল্পই যথেষ্ট। এই যথেষ্টতাই গণতন্ত্রের মৃত্যু, কারণ গণতন্ত্রে কখনোই যথেষ্ট হওয়া যায় না; সেখানে প্রশ্ন চলতেই থাকে।
এই প্রবন্ধের মূল সত্য তাই নির্মমভাবে স্পষ্ট—রোহিঙ্গা, অনুপ্রবেশ, এসআইআর নিয়ে যে গল্প আমরা শুনছি, তা তথ্যের ফল নয়, ক্ষমতার ফল। মিডিয়া ও রাষ্ট্র মিলিতভাবে এই কল্পকাহিনি তৈরি করেছে, যাতে নাগরিকত্ব শর্তাধীন হয়, অধিকার সংকুচিত হয়, এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতা বাড়ে। এই কল্পকাহিনি ভাঙা মানে শুধু একটি গল্প ভাঙা নয়—এটি ক্ষমতার ভাষা ভাঙা।
যে রাষ্ট্র গল্প দিয়ে শাসন করে, সে আর গণতান্ত্রিক থাকে না। আর যে মিডিয়া গল্প বানায়, সে আর সাংবাদিকতা করে না। এই দুইয়ের মিলনস্থলেই জন্ম নেয় বাছাই রাষ্ট্র—যেখানে নাগরিক নয়, গল্পই সিদ্ধান্ত নেয় কে থাকবে, কে বাদ যাবে।
অনুপ্রবেশের মিথ বনাম বাস্তব পরিসংখ্যান
অনুপ্রবেশ—এই শব্দটি ভারতে আজ আর কোনো পরিসংখ্যানগত বা সমাজতাত্ত্বিক ধারণা নয়; এটি একটি রাজনৈতিক মিথ, যার শক্তি বাস্তব সংখ্যায় নয়, বরং সংখ্যার অনুপস্থিতিতে। রাষ্ট্র অনুপ্রবেশের কথা বলে, কিন্তু সংখ্যা দেয় না। মিডিয়া অনুপ্রবেশ নিয়ে ভয় দেখায়, কিন্তু কোনো ডেটা দেখায় না। রাজনৈতিক বক্তৃতায় অনুপ্রবেশকারী সর্বত্র, অথচ সরকারি নথিতে তারা প্রায় অদৃশ্য। এই দ্বন্দ্বই দেখায়—সমস্যা অনুপ্রবেশ নয়, সমস্যা সংখ্যা। কারণ সংখ্যা দেখালে মিথ ভেঙে যায়, আর মিথ ভাঙলে ভয় কাজ করে না।
রাষ্ট্র কেন সংখ্যাকে ভয় পায়—এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে আধুনিক শাসনের কৌশলে। সংখ্যা যুক্তির ভাষা, আর যুক্তি ভয়কে দুর্বল করে। রাষ্ট্র যখন ভয় দিয়ে শাসন করতে চায়, তখন সে যুক্তির বদলে কল্পনা ব্যবহার করে। অনুপ্রবেশের মিথ ঠিক সেই কল্পনা, যার মধ্যে অস্পষ্টতা রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সম্পদ। অস্পষ্টতা থাকলে নাগরিক প্রশ্ন করতে পারে না—কারা এসেছে, কতজন এসেছে, কোথা থেকে এসেছে, কবে এসেছে—এই প্রশ্নগুলোর কোনো নির্ভরযোগ্য উত্তর নেই, কিন্তু ভয় থেকে যায়।
ভারতের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ বিতর্ক মূলত তিনটি অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত—পূর্ব সীমান্ত (বাংলাদেশ), উত্তর-পূর্ব সীমান্ত (মিয়ানমার), এবং পশ্চিম সীমান্ত (পাকিস্তান)। রাষ্ট্রীয় ভাষ্যে এই তিন অঞ্চল একাকার হয়ে যায়, যদিও বাস্তবে এদের সামাজিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ আলাদা। বাংলাদেশ সীমান্তে মানুষের চলাচল বহু শতাব্দীর বাস্তবতা, যা নদীভাঙন, কাজ, আত্মীয়তা ও ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত। মিয়ানমার সীমান্তে রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট একটি আন্তর্জাতিক মানবিক বিপর্যয়। আর পশ্চিম সীমান্তে সীমিত অনুপ্রবেশ মূলত নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘটনা। কিন্তু রাষ্ট্র এই তিনটিকে আলাদা করে না, কারণ আলাদা করলে সংখ্যা দিতে হয়। এক করলে ভয় তৈরি সহজ হয়।
সরকারি পরিসংখ্যান দেখলে এই মিথের ভেতরের শূন্যতা স্পষ্ট হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বহুবার সংসদে স্বীকার করেছে যে অবৈধ অভিবাসীর কোনো নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান সরকারের কাছে নেই¹। তবু একই সরকার দাবি করে যে অনুপ্রবেশ একটি “বড় সমস্যা”। এই দ্বৈত বক্তব্য প্রমাণ করে—সমস্যা তথ্যের নয়, উদ্দেশ্যের। তথ্য দিলে নীতি প্রশ্নের মুখে পড়বে, তথ্য না দিলে নীতি ভয় দিয়ে চালানো যাবে।
রোহিঙ্গা প্রসঙ্গে এই বৈপরীত্য আরও স্পষ্ট। জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলির হিসাব অনুযায়ী, ভারতে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গার সংখ্যা কয়েক হাজারের বেশি নয়²। এই সংখ্যা ভারতের মোট জনসংখ্যার তুলনায় পরিসংখ্যানগতভাবে প্রায় শূন্য। তবু মিডিয়ায় রোহিঙ্গারা যেন সর্বত্র—ভোটার তালিকায়, শহরে, গ্রামে, নিরাপত্তায়। এই অতিরঞ্জনই প্রোপাগান্ডা, আর এই প্রোপাগান্ডার জন্যই রাষ্ট্র সংখ্যাকে ভয় পায়। কারণ সংখ্যা দেখালে বোঝা যাবে—ভয় অমূলক।
বাংলাদেশ সীমান্তের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা। ১৯৭১-এর পর বহু মানুষ ভারতে এসেছিল যুদ্ধের কারণে, কিন্তু সেই প্রবাহ কয়েক দশক আগেই থেমে গেছে। সরকারি শুমারি দেখায় যে সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশি নয়³। তবু রাজনৈতিক বক্তৃতায় বলা হয়—“জনসংখ্যা বিস্ফোরণ”, “সীমান্ত ঢলে পড়ছে”। এই বক্তব্যের পেছনে কোনো সমর্থনযোগ্য ডেটা নেই, কিন্তু ভয় আছে। এই ভয়ই ভোটার তালিকা শুদ্ধিকরণ, এসআইআর, এনআরসি-এর মতো প্রক্রিয়ার সামাজিক অনুমোদন তৈরি করে।
রাষ্ট্র সংখ্যাকে ভয় পায় আরেকটি কারণে—সংখ্যা দেখালে বৈষম্য প্রকাশ পায়। এসআইআর বা ভোটার তালিকা সংশোধনের পরিসংখ্যান যদি প্রকাশ করা হয়, তবে দেখা যাবে কোন অঞ্চলে কত নাম বাদ পড়েছে, কোন ধর্মীয় গোষ্ঠী বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কোন শ্রেণি সবচেয়ে বেশি বাদ পড়েছে। এই প্রকাশ রাষ্ট্রকে বিব্রত করবে, কারণ তখন নীতি আর নিরপেক্ষ থাকবে না। তাই রাষ্ট্র ডেটা গোপন রাখে, রিপোর্ট প্রকাশ করে না, বিশ্লেষণকে বাধা দেয়। অস্বচ্ছতাই এখানে ক্ষমতা।
গণতন্ত্রে সংখ্যা প্রশ্ন করার অধিকার নাগরিকের মৌলিক অস্ত্র। কিন্তু যখন রাষ্ট্র সংখ্যা লুকায়, তখন নাগরিক অন্ধ হয়ে যায়। সে ভয় শোনে, কিন্তু দেখতে পায় না। এই অন্ধত্বই বাছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি। রাষ্ট্র তখন যাকে খুশি সন্দেহভাজন বানাতে পারে, কারণ কেউ জানে না আসলে কী হচ্ছে। অনুপ্রবেশের মিথ তাই কেবল বিদেশি প্রশ্ন নয়, এটি নাগরিকত্বের প্রশ্ন।
এই মিথের আরেকটি ভয়ংকর দিক হলো—এটি ভবিষ্যতের ভয় তৈরি করে। বলা হয়—এখন হয়তো সংখ্যা কম, কিন্তু ভবিষ্যতে বাড়বে। এই “ভবিষ্যৎ” একটি কল্পিত সময়, যা কখনো আসে না, কিন্তু যার নামে বর্তমানের অধিকার কেটে নেওয়া হয়। রাষ্ট্র বলে—এখনই ব্যবস্থা না নিলে দেরি হয়ে যাবে। এই জরুরি অবস্থা ঘোষণাহীন জরুরি অবস্থা—যার মাধ্যমে অধিকার স্থগিত করা হয়, কিন্তু কেউ প্রশ্ন করতে পারে না, কারণ বিপদ নাকি আসছে।
আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাও দেখায়—অনুপ্রবেশ মিথ সবসময় ডেটাবিরোধী। ইউরোপে অভিবাসন নিয়ে ভয় দেখানো হয়েছে, কিন্তু পরিসংখ্যান দেখিয়েছে যে অভিবাসীরা অর্থনীতিতে অবদান রাখে। যুক্তরাষ্ট্রে “ইলিগ্যাল ইমিগ্রেশন” নিয়ে আতঙ্ক তৈরি করা হয়েছে, কিন্তু অপরাধের হার কমেছে। তবু রাষ্ট্র সংখ্যা উপেক্ষা করে, কারণ সংখ্যা শাসনকে দুর্বল করে⁴।
ভারতে অনুপ্রবেশ মিথের সবচেয়ে বড় শিকার মুসলমান নাগরিকরা। তাদের নাম, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক—সবকিছুই অনুপ্রবেশের ছায়ায় দেখা হয়। এই ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্র এসআইআর-এর মতো প্রক্রিয়া চালায়, আর সমাজ তা মেনে নেয়। সংখ্যার অভাব এখানে ইচ্ছাকৃত, কারণ সংখ্যা থাকলে এই প্রক্রিয়া টিকত না।
এই প্রবন্ধের মূল সত্য তাই স্পষ্ট—রাষ্ট্র অনুপ্রবেশের ভয় ব্যবহার করে, কারণ সে সংখ্যাকে ভয় পায়। সংখ্যা দেখালে বোঝা যাবে—ভয় রাজনৈতিক, বাস্তব নয়। ডেটা দেখালে বোঝা যাবে—সমস্যা সীমান্তে নয়, রাষ্ট্রের ভেতরে। আর এই সত্য প্রকাশ পেলে বাছাই রাষ্ট্র ভেঙে পড়বে।
যে রাষ্ট্র সংখ্যাকে ভয় পায়, সে আসলে নাগরিকের প্রশ্নকে ভয় পায়। কারণ প্রশ্নই গণতন্ত্রের প্রাণ। অনুপ্রবেশের মিথ ভাঙা মানে শুধু একটি রাজনৈতিক কৌশল ভাঙা নয়—এটি নাগরিকের চোখ খুলে দেওয়া। আর যে নাগরিক দেখতে শেখে, তাকে আর ভয় দেখিয়ে শাসন করা যায় না।
এসআইআর দিয়ে শত্রু চিহ্নিত করার কৌশল
এসআইআর যখন ভোটার তালিকার নামে হাজির হয়, তখন তা আর নাগরিক তালিকা থাকে না—তা হয়ে ওঠে সন্দেহের তালিকা। আধুনিক রাষ্ট্রের সবচেয়ে কার্যকর কৌশল হলো শত্রুকে আগে থেকে নির্দিষ্ট না করে, ধীরে ধীরে চিহ্নিত করা। এই চিহ্নিতকরণ প্রকাশ্য শাস্তি দিয়ে নয়, বরং প্রশাসনিক নথির মাধ্যমে করা হয়। এসআইআর সেই প্রশাসনিক অস্ত্র, যার সাহায্যে রাষ্ট্র নাগরিকদের মধ্যে থেকে “ঝুঁকিপূর্ণ”, “অযাচাইযোগ্য”, “সন্দেহভাজন” মানুষ বাছাই করে নেয়। এই বাছাই কোনো আদালতের রায়ে হয় না, কোনো আইনের ঘোষণায় হয় না—হয় ফর্ম, কলাম, রিপোর্ট আর নীরব বাদ পড়ার মধ্য দিয়ে। ভোটার তালিকা তখন আর গণতন্ত্রের ভিত্তি নয়, রাষ্ট্রীয় সন্দেহের মানচিত্র।
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ভোটার তালিকার উদ্দেশ্য ছিল নাগরিককে অন্তর্ভুক্ত করা। কে ভোট দিতে পারবে, কে রাষ্ট্রের অংশ—এই প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দেওয়া ছিল এর কাজ। কিন্তু এসআইআর-এর মাধ্যমে সেই তালিকার চরিত্র উল্টে গেছে। এখন প্রশ্ন আর কে নাগরিক নয়, বরং কে সন্দেহভাজন। এই বদল কেবল প্রশাসনিক নয়, দার্শনিক। রাষ্ট্র নাগরিককে বিশ্বাস করে না, বরং নাগরিককে পরীক্ষা করে। পরীক্ষায় ফেল করলে শাস্তি নয়, অদৃশ্যতা—নাম কেটে যাওয়া, অধিকার হারানো, অস্তিত্ব মুছে যাওয়া।
এই কৌশলের সবচেয়ে ভয়ংকর দিক হলো—এতে শত্রু নির্ধারণ হয় নীরবে। কোনো তালিকায় লেখা থাকে না “এরা শত্রু”, কিন্তু বাদ পড়া নামগুলোই সেই তালিকা। যারা বাদ পড়ে, তারা আর ভোটার নয়, আর নাগরিক নয়, তারা “সমস্যা”। এই সমস্যা চিহ্নিত করার পর রাষ্ট্রের পরবর্তী পদক্ষেপ সহজ হয়ে যায়—তাদের রেশন বন্ধ, পরিষেবা বন্ধ, কণ্ঠস্বর বন্ধ। এভাবেই এসআইআর একটি নাগরিক তালিকা থেকে শত্রু তালিকায় রূপ নেয়।
এই কৌশল কাজ করে কারণ এসআইআর ব্যক্তিগত অপরাধ নয়, সমষ্টিগত সন্দেহ তৈরি করে। কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, তবু সে বাদ পড়ে, কারণ তার নামের বানান মিলেনি, বয়সের অঙ্ক মেলেনি, ঠিকানা বদলেছে, সে বাড়িতে ছিল না, BLO তাকে পায়নি। এই “না পাওয়া”ই রাষ্ট্রীয় ভাষায় অপরাধ। রাষ্ট্র এখানে অপরাধ খোঁজে না, সে খোঁজে অনুপস্থিতি। আর অনুপস্থিতি প্রান্তিক মানুষের জীবনের স্বাভাবিক অংশ—পরিযায়ী শ্রমিক, দরিদ্র, নারী, মুসলমান, আদিবাসী—সবাই এই অনুপস্থিতির রাজনীতির শিকার।
এসআইআর-এর মাধ্যমে শত্রু চিহ্নিত করার আরেকটি কৌশল হলো—এটি নাগরিককে একা করে দেয়। আদালতে গেলে অন্তত আইনি লড়াই হয়, কিন্তু এসআইআর-এ বাদ পড়া মানুষ জানেই না সে বাদ পড়েছে কেন। তাকে বলা হয়—আপনি প্রমাণ দিতে পারেননি। কিন্তু কোন প্রমাণ? কোথায়? কখন? এই অস্পষ্টতা নাগরিককে ভেঙে দেয়। সে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়, নিজের বিরুদ্ধে লড়তে থাকে—কাগজ খুঁজে, অফিসে ঘুরে, আবেদন করে। এই আত্মলড়াই রাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে কার্যকর, কারণ তখন নাগরিক আর রাজনৈতিক নয়, প্রশাসনিক সমস্যা।
এই শত্রু চিহ্নিতকরণ কৌশল বিশেষভাবে কাজ করে সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে। মুসলমান, দলিত, আদিবাসী, পরিযায়ী—এই জনগোষ্ঠীর নথি ঐতিহাসিকভাবে দুর্বল, জীবনযাপন চলমান, ঠিকানা অস্থায়ী। রাষ্ট্র এই বাস্তবতা জানে, কিন্তু সংশোধন করে না; বরং এটিকেই অস্ত্র বানায়। ফলে এসআইআর-এর ফলাফল আগে থেকেই নির্ধারিত—কাদের নাম যাবে, কাদের থাকবে। ভোটার তালিকা এখানে নিরপেক্ষ নয়, এটি একটি রাজনৈতিক ছাঁকনি।
এই ছাঁকনির কাজ আরও সহজ হয় মিডিয়া ও রাজনৈতিক ভাষ্যের মাধ্যমে। যখন নাগরিক শুনতে থাকে—অনুপ্রবেশকারী ঢুকেছে, রোহিঙ্গা আছে, ভুয়া ভোটার আছে—তখন সে তালিকা শুদ্ধিকরণকে স্বাগত জানায়। সে বুঝতে পারে না, এই শুদ্ধিকরণ আসলে বাছাই। এই সামাজিক সম্মতিই এসআইআর-কে শক্তি দেয়। রাষ্ট্র একা কিছু করে না; সে নাগরিককে দিয়েই নাগরিকের বিরুদ্ধে কাজ করায়।
ইতিহাসে এই কৌশল নতুন নয়। উপনিবেশিক শাসনেও ব্রিটিশরা “ক্রিমিনাল ট্রাইব” তালিকা বানিয়ে পুরো জনগোষ্ঠীকে অপরাধী ঘোষণা করেছিল। সেই তালিকায় নাম মানেই সন্দেহভাজন জীবন। আজ এসআইআর সেই তালিকার আধুনিক সংস্করণ—আইন নেই, ঘোষণা নেই, কিন্তু ফল একই। নাগরিকত্ব শর্তাধীন, জীবন অনিশ্চিত, অধিকার স্থগিত¹।
এই কৌশলের আরেকটি গভীর দিক হলো—এটি প্রতিরোধকে দুর্বল করে। কারণ কেউ জানে না কতজন বাদ পড়েছে, কোথায় বাদ পড়েছে, কেন বাদ পড়েছে। ডেটা প্রকাশ করা হয় না, রিপোর্ট দেওয়া হয় না। অস্বচ্ছতা এখানে ইচ্ছাকৃত। যদি পরিসংখ্যান প্রকাশ পায়, তবে বোঝা যাবে কোন সম্প্রদায় সবচেয়ে বেশি বাদ পড়েছে। তাই রাষ্ট্র সংখ্যা গোপন রাখে, আর গোপনীয়তাই ক্ষমতা হয়ে ওঠে।
এসআইআর-এর মাধ্যমে শত্রু চিহ্নিত করার কৌশল শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রকে বাছাই রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করে। গণতন্ত্রে নাগরিকের তালিকা থাকে, বাছাই রাষ্ট্রে সন্দেহের তালিকা থাকে। গণতন্ত্রে ভোটার মানেই নাগরিক, বাছাই রাষ্ট্রে ভোটার মানেই যাচাইযোগ্য সত্তা। এই রূপান্তর ঘটলে আর কোনো নাগরিক নিরাপদ থাকে না। কারণ আজ মুসলমান সন্দেহভাজন, কাল অন্য কেউ হবে। সন্দেহের তালিকা কখনো স্থির থাকে না, কারণ রাষ্ট্রের ক্ষমতা তখনই বাড়ে যখন শত্রুর সংখ্যা বাড়ে।
এই প্রবন্ধের মূল সত্য তাই নির্মম—এসআইআর কোনো প্রশাসনিক ত্রুটি নয়, এটি একটি রাজনৈতিক প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তির কাজ শত্রু খুঁজে বের করা নয়, শত্রু তৈরি করা। ভোটার তালিকা এখানে গণতন্ত্রের দলিল নয়, রাষ্ট্রীয় সন্দেহের মানচিত্র। আর যে রাষ্ট্র সন্দেহকে নীতি বানায়, সে আর নাগরিকের রাষ্ট্র থাকে না; সে হয়ে ওঠে বাছাই রাষ্ট্র।
এই বাছাই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ হলো প্রশ্ন—কতজন বাদ পড়েছে? কেন বাদ পড়েছে? কারা বাদ পড়েছে? এই প্রশ্নগুলো রাষ্ট্র ভয় পায়, কারণ প্রশ্ন মানেই সংখ্যা, আর সংখ্যা মানেই মিথের মৃত্যু। এসআইআর দিয়ে শত্রু চিহ্নিত করার কৌশল ভাঙতে হলে এই প্রশ্নই ফিরিয়ে আনতে হবে গণতন্ত্রের কেন্দ্রে। কারণ যেখানে প্রশ্ন নেই, সেখানে নাগরিক নেই—শুধু সন্দেহভাজন মানুষ থাকে।
কেন এই প্রোপাগান্ডা সবসময় ভোটের আগে আসে
ভোটের ঠিক আগে ভয় হঠাৎ করে কেন বেড়ে যায়—এই প্রশ্নটি রাজনৈতিক নয়, কাঠামোগত। কারণ আধুনিক রাষ্ট্রে ভয় আর কেবল আবেগ নয়, এটি শাসনের একটি প্রযুক্তি। যে রাষ্ট্র গণতন্ত্রের ভিতরে থেকেও কর্তৃত্ববাদী হতে চায়, তাকে নিয়মিতভাবে ভয় তৈরি করতে হয়, আর সেই ভয় তৈরির সবচেয়ে কার্যকর সময় হলো নির্বাচন-পূর্ব মুহূর্ত। তখন নাগরিক সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হয়, তখন তার যুক্তি সক্রিয় হওয়ার কথা ছিল—কিন্তু রাষ্ট্র ঠিক সেই সময়েই যুক্তির জায়গা দখল করে ভয় বসিয়ে দেয়। তাই রোহিঙ্গা, অনুপ্রবেশ, ভুয়া ভোটার, এসআইআর, তালিকা শুদ্ধিকরণ—এই সব প্রোপাগান্ডা সবসময় ভোটের ঠিক আগে ফিরে আসে। এটি কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়; এটি শাসনের ছক।
ভোট একটি প্রশ্নের মুহূর্ত। নাগরিক তখন জিজ্ঞেস করে—কে শাসন করেছে, কী করেছে, কী ব্যর্থতা, কী দুর্নীতি, কী বেকারত্ব, কী মূল্যবৃদ্ধি, কী সামাজিক নিরাপত্তা। এই প্রশ্ন রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক, কারণ প্রশ্ন মানেই জবাবদিহি। ভয় এই প্রশ্নকে থামিয়ে দেয়। ভয় নাগরিককে বলে—এই প্রশ্নগুলো এখন নয়, এখন বিপদ আছে। শত্রু আছে। দেশ বিপন্ন। এই বয়ান নাগরিকের চিন্তাকে ঘুরিয়ে দেয়। সে তখন আর সরকারকে প্রশ্ন করে না, সে রাষ্ট্রের পাশে দাঁড়ায়। এই মানসিক স্থানান্তরই নির্বাচন-পূর্ব প্রোপাগান্ডার আসল লক্ষ্য।
ভোটের আগে ভয় তৈরির দ্বিতীয় কারণ হলো—ভয় পরিচয়কে সক্রিয় করে। গণতান্ত্রিক ভোটে মানুষ নিজের স্বার্থ, জীবন, রুটি-রুজি নিয়ে ভাবতে পারে। কিন্তু ভয় তাকে নিজের পরিচয়ের দিকে ঠেলে দেয়—ধর্ম, জাতি, ভাষা, জাতীয়তাবাদ। পরিচয় সক্রিয় হলে যুক্তি নিষ্ক্রিয় হয়। তখন নাগরিক ভোট দেয় শাসকের পক্ষে নয়, শত্রুর বিরুদ্ধে। এই “বিরুদ্ধে ভোট” রাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ ভোট, কারণ এটি শাসকের ব্যর্থতা ঢেকে দেয়। অনুপ্রবেশ, রোহিঙ্গা, সন্দেহভাজন নাগরিক—এই সব বয়ান সেই বিরুদ্ধের ভোট তৈরির যন্ত্র।
এসআইআর ও ভোটার তালিকা সংশোধন ভোটের আগে আসে কারণ এটি একসঙ্গে দুই কাজ করে—ভয় তৈরি করে এবং ভোটের ফল বদলে দেয়। প্রথমত, এটি বলে—তালিকায় ভুয়া আছে, বিপদ আছে, শত্রু ঢুকে গেছে। দ্বিতীয়ত, এটি বাস্তবে কিছু নাগরিককে তালিকা থেকে বাদ দেয়। এই বাদ পড়া কখনোই এলোমেলো নয়; এটি প্রান্তিক, সংখ্যালঘু, দরিদ্র, পরিযায়ী জনগোষ্ঠীকে বেশি আঘাত করে। ফলে ভয় যেমন ভোটারকে একদিকে ঠেলে দেয়, বাদ পড়া অন্যদিকে ভোটের ভারসাম্য বদলে দেয়। ভয় আর প্রশাসন এখানে একসঙ্গে কাজ করে।
ইতিহাসে এই প্যাটার্ন নতুন নয়। উপনিবেশিক শাসকেরাও বিদ্রোহের ভয় দেখিয়ে কর বাড়াত, সেনা নামাত, অধিকার স্থগিত করত। আধুনিক গণতন্ত্রে সেই কৌশল ফিরে আসে নির্বাচনের আগে। তখন “জরুরি অবস্থা” ঘোষণা করতে হয় না; ভয়ই জরুরি অবস্থা হয়ে ওঠে। এসআইআর সেই ঘোষণাহীন জরুরি অবস্থার প্রশাসনিক রূপ।
ভোটের আগে ভয় তৈরির আরেকটি কারণ হলো—মিডিয়ার মনোযোগ নিয়ন্ত্রণ। নির্বাচন-পূর্ব সময়ে মিডিয়া সবচেয়ে শক্তিশালী হয়, কারণ মানুষ তখন খবর দেখে, শোনে, সিদ্ধান্ত নেয়। রাষ্ট্র যদি এই সময় মিডিয়ার এজেন্ডা বদলে দিতে পারে, তবে সে নির্বাচনের কথাবার্তাই বদলে দিতে পারে। অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দুর্নীতি—এই সব প্রশ্ন হারিয়ে যায়। তার জায়গা নেয় অনুপ্রবেশ, নিরাপত্তা, দেশরক্ষা। মিডিয়া ও রাষ্ট্রের যৌথ কল্পকাহিনি তখন সর্বোচ্চ তাপে পৌঁছায়। ডেটা নেই, কিন্তু গল্প আছে। আর গল্পই ভোটের সিদ্ধান্ত তৈরি করে।
এই প্রোপাগান্ডার আরেকটি গভীর কারণ হলো—ভয় প্রশাসনিক ব্যর্থতা ঢাকে। যখন কর্মসংস্থান নেই, কৃষক সংকটে, মূল্যবৃদ্ধি আকাশছোঁয়া, তখন রাষ্ট্রকে অন্য কিছু দেখাতে হয়। ভয় সেই বিকল্প দৃশ্য। নাগরিক তখন ভাবে—হ্যাঁ, সমস্যা আছে, কিন্তু দেশ বাঁচানো জরুরি। এই “বড় বিপদ” বয়ান ছোট বিপদকে অদৃশ্য করে। ভোটের আগে এই অদৃশ্যকরণ রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।
ভোটের আগে ভয় তৈরির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—এটি বিরোধী রাজনীতিকে দুর্বল করে। বিরোধী দল তখন আর নীতির কথা বলতে পারে না, কারণ রাষ্ট্র বলে—তারা নিরাপত্তার পক্ষে নয়, তারা অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষে, তারা শত্রুর বন্ধু। ভয় বিরোধী কণ্ঠকে দেশদ্রোহিতায় রূপান্তরিত করে। এসআইআর, রোহিঙ্গা, অনুপ্রবেশ—এই সব শব্দ বিরোধী রাজনীতিকে কোণঠাসা করার ভাষা। ভোটের আগে এই ভাষা ব্যবহার করা সবচেয়ে কার্যকর, কারণ তখন সময় কম, ব্যাখ্যার সুযোগ নেই, আবেগ বেশি।
এই প্রোপাগান্ডা চক্রের সবচেয়ে ভয়ংকর দিক হলো—এটি নাগরিককে অভ্যস্ত করে তোলে। একবার নয়, বারবার ভোটের আগে একই ভয়, একই শব্দ, একই কৌশল। নাগরিক ধীরে ধীরে ভাবতে শেখে—ভোট মানেই ভয়, নির্বাচন মানেই জরুরি অবস্থা। এই অভ্যাসই গণতন্ত্রের মৃত্যু। কারণ গণতন্ত্র তখন আর ভবিষ্যৎ বেছে নেওয়ার মুহূর্ত নয়, এটি বিপদ সামলানোর অনুশীলন হয়ে ওঠে।
আন্তর্জাতিকভাবে এই প্যাটার্ন স্পষ্ট। যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন ভয় নির্বাচনের আগে বাড়ে, ইউরোপে শরণার্থী ভয় নির্বাচনের আগে বাড়ে, ব্রাজিলে অপরাধ ভয় নির্বাচনের আগে বাড়ে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যায়—যখন শাসক জবাবদিহি এড়াতে চায়, সে ভয় তৈরি করে¹। ভারতও এই বৈশ্বিক ছকের বাইরে নয়, বরং এখানে এটি আরও শক্তিশালী, কারণ প্রশাসনিক প্রক্রিয়া (এসআইআর) এই ভয়কে বাস্তবে রূপ দেয়।
রাষ্ট্র ভয় ছাড়া শাসন করতে পারে না—এই সত্য আধুনিক গণতন্ত্রের সবচেয়ে অস্বস্তিকর উপলব্ধি। কারণ গণতন্ত্রের আদর্শ ছিল সম্মতি, যুক্তি ও সমতা। কিন্তু যখন সেই আদর্শ ক্ষয় হয়, তখন ভয়ই সম্মতির বিকল্প হয়ে ওঠে। ভোটের আগে প্রোপাগান্ডা আসে কারণ তখন ভয় সবচেয়ে কার্যকর, তখন নাগরিক সবচেয়ে অসহায়, তখন সিদ্ধান্ত সবচেয়ে দুর্বল।
এই প্রবন্ধের মূল সত্য তাই নির্মমভাবে স্পষ্ট—ভোটের আগে ভয় আসে কারণ শাসনের অন্য ভাষা তখন ব্যর্থ হয়ে যায়। উন্নয়ন, নীতি, ন্যায়—এই সব ভাষা কাজ করে না। ভয় কাজ করে। এসআইআর, অনুপ্রবেশ, রোহিঙ্গা—এই সব শব্দ সেই ভয় ভাষার অভিধান। এই অভিধান যতদিন থাকবে, ততদিন নির্বাচন আর মুক্ত সিদ্ধান্ত হবে না, হবে নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া।
এই প্রোপাগান্ডা ভাঙা মানে শুধু একটি রাজনৈতিক কৌশল ভাঙা নয়—এটি ভোটকে আবার প্রশ্নের জায়গায় ফিরিয়ে আনা। নাগরিক যদি ভয় নয়, প্রশ্ন নিয়ে ভোট দেয়, তবে এই রাষ্ট্রীয় ছক ভেঙে পড়বে। কারণ ভয় ছাড়া শাসন সম্ভব, কিন্তু প্রশ্নের সামনে শাসন টেকে না।
এসআইআর–NRC–CAA: একই ষড়যন্ত্রের তিন অধ্যায়
এসআইআর–এনআরসি–সিএএ—এই তিনটি শব্দকে আলাদা করে দেখলে এগুলো প্রশাসনিক বা আইনি প্রক্রিয়া মনে হতে পারে। কিন্তু একসঙ্গে পড়লে স্পষ্ট হয়, এগুলো কোনো বিচ্ছিন্ন নীতি নয়; এগুলো একই রাজনৈতিক প্রকল্পের তিনটি অধ্যায়। এই প্রকল্পের লক্ষ্য নাগরিকত্বকে অধিকার থেকে শর্তে রূপান্তরিত করা, রাষ্ট্রকে বিশ্বাসের জায়গা থেকে সন্দেহের জায়গায় নিয়ে যাওয়া, এবং গণতন্ত্রকে ধীরে ধীরে একটি বাছাই রাষ্ট্রে পরিণত করা। এসআইআর এই প্রকল্পের প্রশাসনিক দরজা, এনআরসি তার আইনি চাবি, আর সিএএ তার আদর্শিক সিলমোহর। তিনটি মিলেই তৈরি হয় নাগরিকত্ব হরণের পূর্ণ কাঠামো।
নাগরিকত্বের ধারণা আধুনিক রাষ্ট্রের সবচেয়ে মৌলিক ভিত্তি। নাগরিক মানেই সমান অধিকার, সমান মর্যাদা, সমান আইনি সুরক্ষা। সংবিধান এই ধারণাকেই স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু এসআইআর–এনআরসি–সিএএ এই ধারণাকে উল্টে দেয়। এখানে নাগরিকত্ব আর জন্মসূত্রে বা সংবিধানপ্রদত্ত অধিকার নয়; এটি প্রমাণসাপেক্ষ, যাচাইযোগ্য, বাতিলযোগ্য একটি অবস্থা। রাষ্ট্র নাগরিককে আর বিশ্বাস করে না—সে নাগরিককে পরীক্ষা করে। আর যে পরীক্ষায় ফেল করে, সে কেবল ভোটাধিকার হারায় না, সে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের চোখে মানুষও থাকে না।
এসআইআর হলো এই প্রক্রিয়ার সবচেয়ে নীরব অধ্যায়। এটি কোনো আইন নয়, কোনো বড় ঘোষণা নয়। এটি ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে নাগরিক যাচাইয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থা। এর ভাষা নিরপেক্ষ, কিন্তু ফল পক্ষপাতদুষ্ট। এসআইআর প্রথমে নাগরিকের নাম, বয়স, ঠিকানা, অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলেই নাগরিক বাদ পড়ে। এই বাদ পড়া আইনি অপরাধ নয়, কিন্তু রাজনৈতিক মৃত্যুদণ্ড। কারণ ভোটাধিকার হারানো মানে রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া। এসআইআর নাগরিকত্ব হরণের সূচনা বিন্দু।
এর পর আসে এনআরসি—যেখানে এই সন্দেহকে আইনি রূপ দেওয়া হয়। এনআরসি নাগরিককে বলে—তুমি প্রমাণ করো তুমি নাগরিক। প্রমাণের ভার নাগরিকের ওপর চাপানোই এনআরসি-এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্র এখানে আর তার নথির দায় নেয় না; নাগরিককে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হয়। আসামের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে, এই প্রক্রিয়ায় লক্ষ লক্ষ মানুষ বাদ পড়েছে, যাদের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র, নারী, সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক¹। এই বাদ পড়া কোনো দুর্ঘটনা নয়; এটি কাঠামোগত। কারণ যে সমাজে নথির অভাব ঐতিহাসিক, সেখানে প্রমাণের শর্ত মানেই বর্জন।
এনআরসি নাগরিকত্বকে একটি আইনি গোলকধাঁধায় পরিণত করে, যেখানে ঢোকা সহজ, বের হওয়া প্রায় অসম্ভব। যারা বাদ পড়ে, তারা “ডাউটফুল সিটিজেন”, “ফরেনার”, “নন-সিটিজেন”—এইসব অস্পষ্ট শ্রেণিতে আটকে যায়। এই আটকে পড়া অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী, কারণ আপিলের প্রক্রিয়া জটিল, ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। নাগরিক তখন আর নাগরিক নয়, সে মামলার বিষয়। রাষ্ট্র তার ওপর শাসন করে, কিন্তু তাকে অধিকার দেয় না।
এনআরসি যেখানে বাদ দেয়, সিএএ সেখানে বেছে নেয়। সিএএ নাগরিকত্বের ধারণায় ধর্মকে ঢুকিয়ে দেয়। এই আইন প্রথমবারের মতো সংবিধানের নাগরিকত্ব নীতিকে ধর্মভিত্তিক করে। এতে বলা হয়—কিছু ধর্মের মানুষ নাগরিকত্ব পাবে, কিছু পাবে না। এই “না পাওয়া”-এর মধ্যে মুসলমানদের বাদ দেওয়া হয়। ফলে এনআরসি দ্বারা বাদ পড়া অমুসলমানদের জন্য সিএএ একটি সেফটি নেট, কিন্তু মুসলমানদের জন্য কোনো সুরক্ষা নেই। এই অসমতা দুর্ঘটনা নয়; এটি প্রকল্পের কেন্দ্রবিন্দু।
এসআইআর–এনআরসি–সিএএ একসঙ্গে কাজ করে কারণ প্রত্যেকটির কাজ আলাদা, কিন্তু লক্ষ্য এক। এসআইআর সন্দেহ তৈরি করে, এনআরসি বাদ দেয়, সিএএ বাছাই করে। সন্দেহ–বাদ–বাছাই—এই তিন ধাপেই নাগরিকত্ব ভেঙে ফেলা হয়। এই প্রক্রিয়া ধীরে চলে, যাতে প্রতিরোধ গড়ে উঠতে না পারে। মানুষ ভাবে—এটা তো শুধু তালিকা সংশোধন। তারপর ভাবে—এটা তো শুধু প্রমাণ। তারপর দেখে—কেউ কেউ নাগরিক, কেউ কেউ নয়। তখন অনেক দেরি হয়ে যায়।
এই তিন অধ্যায়ের সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক হলো—এগুলো একসঙ্গে কখনো আসে না। আলাদা আলাদা সময়ে, আলাদা ভাষায়, আলাদা অজুহাতে আসে। এই বিচ্ছিন্নতা নাগরিককে বিভ্রান্ত করে। কেউ ভাবে—এটা শুধু এসআইআর, এনআরসি আসেনি। কেউ ভাবে—এনআরসি তো এখন নেই। কেউ ভাবে—সিএএ তো শরণার্থীদের জন্য। এই বিভ্রান্তিই রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শক্তি। কারণ নাগরিক যখন পুরো চিত্র দেখতে পারে না, তখন সে প্রতিরোধ করতে পারে না।
এই প্রকল্পের আদর্শিক ভিত্তি হলো “সন্দেহভাজন নাগরিক” ধারণা। রাষ্ট্র ধরে নেয়—কিছু মানুষ স্বাভাবিক নাগরিক, কিছু মানুষ যাচাইযোগ্য। এই যাচাইযোগ্য মানুষ কারা? তারা সংখ্যালঘু, তারা দরিদ্র, তারা নারী, তারা পরিযায়ী, তারা মাদ্রাসা-শিক্ষিত, তারা সীমান্ত অঞ্চলের বাসিন্দা। এই সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসকে প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় রূপ দেওয়া হয় এসআইআর ও এনআরসি দিয়ে, আর আদর্শিক বৈধতা দেওয়া হয় সিএএ দিয়ে।
এই তিনটির মিলিত ফল হলো—রাষ্ট্র আর সবার নয়। রাষ্ট্র হয়ে ওঠে নির্বাচিত নাগরিকদের প্রতিষ্ঠান। এই নির্বাচনের মানদণ্ড আইনি নয়, রাজনৈতিক। কে রাষ্ট্রের আদর্শে মেলে, কে মেলে না—এই প্রশ্নই নাগরিকত্বের মাপকাঠি হয়ে ওঠে। এই রূপান্তর গণতন্ত্রের মৃত্যু, কারণ গণতন্ত্রে নাগরিকত্ব কোনো পুরস্কার নয়, এটি শাসনের ভিত্তি।
আন্তর্জাতিকভাবে এই ধরনের প্রকল্প পরিচিত। ইউরোপে অভিবাসন আইন, যুক্তরাষ্ট্রে ন্যাচারালাইজেশন রাজনীতি, ইসরায়েলে নাগরিকত্ব আইন—সবখানেই দেখা যায় একই কাঠামো: প্রথমে সন্দেহ, তারপর বর্জন, তারপর বাছাই²। ভারতে এই কাঠামো আরও বিপজ্জনক, কারণ এখানে এটি সংখ্যাগুরু–সংখ্যালঘু বিভাজনের ওপর দাঁড়িয়ে। ফলে নাগরিকত্ব প্রশ্নটি সামাজিক সংঘাতে পরিণত হয়।
এই প্রকল্পের আরেকটি গভীর দিক হলো—এটি রাষ্ট্রের প্রশাসনিক চরিত্র বদলে দেয়। প্রশাসন আর নাগরিকের সেবা করে না, প্রশাসন নাগরিককে যাচাই করে। BLO, অফিসার, ক্লার্ক—সবাই সন্দেহের বাহক হয়ে ওঠে। নাগরিকের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক হয়ে ওঠে পুলিশি। এই পুলিশি সম্পর্কই এসআইআর–এনআরসি–সিএএ-এর দীর্ঘমেয়াদি ফল।
এই প্রবন্ধের মূল সত্য তাই স্পষ্ট—এসআইআর, এনআরসি ও সিএএ আলাদা আইন নয়, আলাদা নীতি নয়, আলাদা ভুল নয়। এগুলো একটি একক রাজনৈতিক প্রকল্পের ধারাবাহিক অধ্যায়। এই প্রকল্পের লক্ষ্য একটি নতুন নাগরিকত্ব নির্মাণ—যেখানে নাগরিকত্ব আর অধিকার নয়, আনুগত্যের ফল। এই নাগরিকত্বে যারা প্রশ্ন করবে, তারা সন্দেহভাজন; যারা প্রশ্ন করবে না, তারা নিরাপদ।
এই প্রকল্প যদি সম্পূর্ণ হয়, তবে গণতন্ত্র কাগজে থাকবে, জীবনে নয়। কারণ নাগরিকত্ব ছাড়া গণতন্ত্র হয় না। ভোটাধিকার ছাড়া শাসন হয়, কিন্তু তা জনগণের শাসন নয়। এসআইআর–এনআরসি–সিএএ সেই শাসনের স্থাপত্য।
এই সত্য বোঝা মানে শুধু একটি নীতির বিরোধিতা নয়, এটি সংবিধানকে রক্ষা করা। কারণ সংবিধান নাগরিককে রাষ্ট্রের মালিক বানিয়েছিল, আর এই প্রকল্প নাগরিককে রাষ্ট্রের সন্দেহভাজন বানাচ্ছে। এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা না হলে রাষ্ট্র বদলে যাবে, কিন্তু সংবিধান থেকে যাবে একটি নথি হিসেবে—একটি স্মৃতিচিহ্ন।
ডকুমেন্ট নাগরিকত্ব: নতুন ভারতের সংজ্ঞা
নতুন ভারতের নাগরিকত্ব আর মানুষ দিয়ে সংজ্ঞায়িত হচ্ছে না, সংজ্ঞায়িত হচ্ছে কাগজ দিয়ে। যে রাষ্ট্র একসময় নাগরিকের অস্তিত্বকে স্বাভাবিক ধরে নিয়েছিল, সে রাষ্ট্র এখন নাগরিকের অস্তিত্বকে শর্তাধীন করে তুলছে—যতক্ষণ কাগজ আছে, ততক্ষণ নাগরিক; কাগজ হারালে মানুষও হারায় নাগরিকত্ব। এই রূপান্তরই “ডকুমেন্ট নাগরিকত্ব”—যেখানে মানুষের জীবন, স্মৃতি, ইতিহাস, ভাষা, বসবাস, সম্পর্ক সবকিছুকে পরাজিত করে কাগজের একক আধিপত্য। এসআইআর–এনআরসি–সিএএ মিলিয়ে এই নতুন সংজ্ঞা তৈরি হয়েছে, যেখানে নাগরিক আর রাষ্ট্রের অংশ নয়, সে রাষ্ট্রের ফাইলে সংরক্ষিত একটি নথি।
ডকুমেন্ট নাগরিকত্বের ধারণা আপাতদৃষ্টিতে আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর, “সুশাসন”-এর অংশ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এর ভিতরে লুকিয়ে আছে রাষ্ট্রের একটি মৌলিক অবিশ্বাস—রাষ্ট্র আর নাগরিককে বিশ্বাস করে না। রাষ্ট্র ধরে নেয় নাগরিক মিথ্যা বলবে, জাল করবে, ঢুকে পড়বে, প্রতারণা করবে। তাই তাকে বারবার প্রমাণ দিতে হবে। এই প্রমাণের চক্র কখনো শেষ হয় না, কারণ প্রতিটি প্রমাণ নতুন সন্দেহ তৈরি করে। নাগরিক তখন আর মানুষ নয়, সে এক চলমান কেস ফাইল।
এই ডকুমেন্ট নাগরিকত্বের সবচেয়ে ভয়ংকর দিক হলো—এটি ঐতিহাসিকভাবে বৈষম্যমূলক। ভারতের বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে জন্মসনদ, স্কুল সার্টিফিকেট, জমির দলিল কখনোই ছিল না। উপনিবেশিক শাসনে নথি ছিল ক্ষমতাবানদের জন্য, স্বাধীনতার পরেও নথি তৈরির প্রক্রিয়া ছিল অসম। নারী, দলিত, আদিবাসী, দরিদ্র, পরিযায়ী, সংখ্যালঘু—এই মানুষদের জীবন কাগজে নয়, স্মৃতিতে, মৌখিকতায়, সম্পর্কের জালে সংরক্ষিত। রাষ্ট্র এই বাস্তবতাকে জানে, তবু ডকুমেন্টকে নাগরিকত্বের একমাত্র মানদণ্ড বানায়। ফলে এই নাগরিকত্ব শুরু থেকেই বর্জনমূলক।
ডকুমেন্ট নাগরিকত্বে মানুষ আর নাগরিকত্বের ধারক নয়, কাগজ ধারক। নাগরিকত্ব তাই শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ফাইলে স্থানান্তরিত হয়। কেউ মারা গেলে তার নাগরিকত্ব থাকে ফাইলে, কেউ বেঁচে থেকেও নাগরিকত্ব হারায় কারণ তার ফাইল অসম্পূর্ণ। এই উল্টো জগতে রাষ্ট্র মানুষের চেয়ে কাগজকে বেশি বিশ্বাস করে। অথচ কাগজ সবচেয়ে সহজে জাল হয়, হারায়, বদলায়। তবু কাগজের ওপর বিশ্বাস আর মানুষের ওপর অবিশ্বাস—এটাই নতুন ভারতের নাগরিকত্ব দর্শন।
এসআইআর এই দর্শনের সবচেয়ে নীরব রূপ। এখানে নাগরিকত্ব প্রশ্নে আদালত লাগে না, পুলিশ লাগে না—শুধু ফর্ম লাগে। ফর্মে সামান্য ভুল, বানান অমিল, বয়সের গড়মিল, ঠিকানা বদল—এই সবই নাগরিকত্বের বিরুদ্ধে প্রমাণ হয়ে ওঠে। মানুষের জীবন কখনো স্থির নয়, কিন্তু কাগজ চায় স্থিরতা। এই দ্বন্দ্বে মানুষ হারে, কাগজ জেতে। রাষ্ট্র এই হার–জেতের নিয়ম এমনভাবে বানায় যাতে কাগজই শেষ কথা হয়।
ডকুমেন্ট নাগরিকত্বের ফলে নাগরিকত্ব একটি চলমান পরীক্ষা হয়ে ওঠে। আজ আধার, কাল ভোটার কার্ড, পরশু জন্মসনদ, তারপর জমির দলিল, তারপর বাবা–মায়ের কাগজ, তারপর দাদা–দাদির কাগজ। এই পরীক্ষার কোনো শেষ নেই, কারণ রাষ্ট্র প্রতিবার নতুন কাগজ চাইতে পারে। নাগরিকত্ব তখন আর অধিকার নয়, এটি একধরনের লাইসেন্স—যা বারবার নবায়ন করতে হয়, আর নবায়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে।
এই ব্যবস্থার সবচেয়ে ভয়ংকর ফল হলো—নাগরিক সবসময় ভয়ে থাকে। সে জানে না আগামীকাল কোন কাগজ চাইবে, কোন নথি মিলবে না, কখন সে বাদ পড়বে। এই ভয়ই শাসনের মূল। ভীত নাগরিক প্রশ্ন করে না, সংগঠিত হয় না, প্রতিবাদ করে না। সে নিজের কাগজ ঠিক রাখতেই ব্যস্ত থাকে। রাষ্ট্র এখানে নাগরিককে রাজনৈতিক সত্তা থেকে প্রশাসনিক সমস্যায় রূপান্তরিত করে। এটাই ডকুমেন্ট নাগরিকত্বের আসল রাজনৈতিক কাজ।
এই নাগরিকত্ব দর্শনের শিকড় উপনিবেশিক শাসনে। ব্রিটিশরা জনগণকে নথিতে বন্দি করে শাসন করত—জনগণনা, রেজিস্টার, পাস, সার্টিফিকেট। স্বাধীনতার পর সংবিধান সেই শাসনভাষা ভাঙতে চেয়েছিল। কিন্তু আজ সেই উপনিবেশিক কৌশল নতুন প্রযুক্তিতে ফিরে এসেছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়া, আধার, ডেটাবেস—এই সব আধুনিকতার মুখোশে পুরোনো দমন ফিরে এসেছে। কাগজ বদলেছে, দর্শন বদলায়নি।
ডকুমেন্ট নাগরিকত্বের আরেকটি দিক হলো—এটি নাগরিককে একা করে দেয়। আগে নাগরিকত্ব ছিল সামাজিক—গ্রাম জানত, পাড়া জানত, সমাজ জানত। আজ নাগরিকত্ব ব্যক্তিগত ফাইল। সমাজের সাক্ষ্য আর রাষ্ট্র মানে না, রাষ্ট্র মানে শুধু কাগজ। ফলে নাগরিক একা পড়ে যায় রাষ্ট্রের সামনে, নিরস্ত্র, অসহায়। এই একাকিত্বই ডকুমেন্ট নাগরিকত্বের সবচেয়ে ভয়ংকর ফল, কারণ একা মানুষ প্রতিরোধ করতে পারে না।
এই প্রক্রিয়া সবচেয়ে বেশি আঘাত করে নারীদের। নারীর নাম বদলায়, ঠিকানা বদলায়, পরিচয় বদলায়—এটি সামাজিক বাস্তবতা। কিন্তু কাগজে এই বদল অপরাধ। ফলে নারীর নাগরিকত্ব সবসময় ঝুঁকিপূর্ণ। একইভাবে পরিযায়ী শ্রমিক, যাদের জীবন চলমান, তারা কাগজের কাছে অপরাধী। ডকুমেন্ট নাগরিকত্ব এখানে একটি লিঙ্গীয় ও শ্রেণিগত অস্ত্র।
রাষ্ট্র এই ব্যবস্থাকে “শুদ্ধিকরণ” বলে, কিন্তু আসলে এটি বাছাই। কে নাগরিক থাকবে, কে থাকবে না—এই সিদ্ধান্ত ধীরে ধীরে কাগজের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আর কাগজ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে। এই নিয়ন্ত্রণই বাছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি।
আন্তর্জাতিকভাবে এই ধরনের ডকুমেন্ট নাগরিকত্ব নতুন কর্তৃত্ববাদের লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ফ্রান্সে অভিবাসী, যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গ, চীনে উইঘুর—সবখানেই নাগরিকত্বকে কাগজের পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। ভারত সেই বৈশ্বিক প্রবণতার অংশ, কিন্তু এখানে এটি সংখ্যাগুরু–সংখ্যালঘু রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, তাই আরও বিপজ্জনক।
এই প্রবন্ধের মূল সত্য তাই নির্মমভাবে স্পষ্ট—নতুন ভারতের নাগরিকত্ব মানুষ দিয়ে নয়, কাগজ দিয়ে সংজ্ঞায়িত হচ্ছে। এই নাগরিকত্বে যারা কাগজে দুর্বল, তারা রাষ্ট্রে দুর্বল। যারা কাগজে শক্ত, তারা রাষ্ট্রে নিরাপদ। এই অসমতা গণতন্ত্রের মৃত্যু, কারণ গণতন্ত্র মানুষের সমতার ওপর দাঁড়ায়, কাগজের সমতার ওপর নয়।
এই ডকুমেন্ট নাগরিকত্ব যদি প্রশ্নহীন থাকে, তবে ভবিষ্যতে নাগরিকত্ব আর নাগরিকের থাকবে না, থাকবে সার্ভারের কাছে, ফাইলের কাছে, অফিসের কাছে। মানুষ তখন রাষ্ট্রের মালিক নয়, রাষ্ট্রের রেকর্ড হবে।
এই কারণেই ডকুমেন্ট নাগরিকত্বের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা মানে শুধু প্রশাসনিক নীতির বিরোধিতা নয়, এটি মানুষকে আবার নাগরিক হিসেবে ফিরিয়ে আনার লড়াই। কারণ কাগজ রাষ্ট্রের হতে পারে, কিন্তু নাগরিকত্ব মানুষের।
আদালত, মিডিয়া ও নীরবতার রাজনীতি
রাষ্ট্র যখন আর জোরে কথা বলে না, তখন সে নীরব হয়ে ওঠে। আর সেই নীরবতা যখন আদালত, মিডিয়া ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তখন তা কেবল মৌনতা থাকে না—তা হয়ে ওঠে শাসনের ভাষা। আধুনিক কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রে নীরবতা কোনো দুর্ঘটনা নয়, এটি একটি পরিকল্পিত রাজনৈতিক কৌশল। এসআইআর, এনআরসি, সিএএ–এর মতো প্রক্রিয়া চালু থাকা অবস্থায় আদালতের দীর্ঘ নীরবতা, মিডিয়ার সমবেত চুপ করে থাকা, এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া এই কথাই প্রমাণ করে—নীরবতাও শাসন করে।
গণতন্ত্রে আদালত ছিল শেষ আশ্রয়, যেখানে নাগরিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারত। আদালতের নীরবতা তাই সবচেয়ে গভীর সংকেত—এটি নাগরিককে বলে, “এখানে আর কেউ নেই।” এসআইআর ও নাগরিকত্ব প্রশ্নে আদালতের ভূমিকা দেখলে এই নীরবতার রাজনীতি স্পষ্ট হয়। যখন লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়, যখন ডকুমেন্ট নাগরিকত্ব নাগরিককে সন্দেহভাজনে পরিণত করে, তখন আদালত দ্রুত শুনানি নেয়নি, অন্তর্বর্তী সুরক্ষা দেয়নি, বা রাষ্ট্রকে জবাবদিহির মুখে দাঁড় করায়নি। এই বিলম্বই নীরবতা, আর এই নীরবতাই রাষ্ট্রের শক্তি।
নীরবতা এখানে নিষ্ক্রিয়তা নয়, এটি সক্রিয় সহযোগিতা। কারণ রাষ্ট্র জানে—সময়ই সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র। মামলা ঝুলে থাকলে প্রক্রিয়া চলতে থাকে, মানুষ বাদ পড়ে, ক্ষতি স্থায়ী হয়। পরে রায় এলেও ততদিনে নাগরিকত্ব হারানো মানুষ রাজনৈতিকভাবে মৃত। আদালতের এই বিলম্বী নীরবতা রাষ্ট্রকে ঠিক সেই সুযোগটাই দেয়। ইতিহাসে একে বলা হয় “procedural violence”—যেখানে প্রক্রিয়াই শাস্তি¹।
আসামের এনআরসি প্রক্রিয়ায় আদালতের ভূমিকা এই নীরবতার রাজনীতির একটি পরীক্ষাগার। সুপ্রিম কোর্ট সরাসরি তত্ত্বাবধান করেছে, কিন্তু যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ বাদ পড়ল, তখন আদালত কোনো গণতান্ত্রিক প্রশ্ন তোলে নি—কাদের বাদ পড়ল, কেন বাদ পড়ল, এই বাদ পড়া কি বৈষম্যমূলক? আদালত প্রক্রিয়াকে রক্ষা করেছে, নাগরিককে নয়। এই অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিয়েছে—আইন যখন রাষ্ট্রের সঙ্গে দাঁড়ায়, তখন ন্যায় একা হয়ে যায়²।
মিডিয়ার নীরবতা এই রাজনীতির দ্বিতীয় স্তম্ভ। মিডিয়া যদি প্রশ্ন করত, তথ্য চাইত, ডেটা খুঁজত, তাহলে এসআইআর, অনুপ্রবেশ, সন্দেহভাজন নাগরিক—এই সব বয়ান টিকত না। কিন্তু মিডিয়া চুপ করে থাকে। সে রাষ্ট্রের ভাষাই পুনরাবৃত্তি করে, অথবা আরও ভয়ংকর—সে কিছুই বলে না। এই না বলা রাষ্ট্রের জন্য আশীর্বাদ, কারণ চুপ থাকা মানে সম্মতি। গণতন্ত্রে মিডিয়া ছিল প্রশ্নের প্রতিষ্ঠান, এখন সে নীরবতার প্রতিষ্ঠান।
এই নীরবতা তৈরি করা হয়েছে ভয় দিয়ে। আদালত ভয় পায় “সংবেদনশীল বিষয়” ছুঁতে, মিডিয়া ভয় পায় বিজ্ঞাপন হারাতে, প্রতিষ্ঠান ভয় পায় ক্ষমতার রোষে পড়তে। এই ভয়কে রাষ্ট্র আইন দিয়ে নয়, পরিবেশ দিয়ে তৈরি করে। কেউ জেলে গেলে, কেউ মামলায় জড়ালে, কেউ চ্যানেল হারালে বাকিরা চুপ করে যায়। এই চুপ করে যাওয়াই নীরবতার রাজনীতি।
নীরবতার রাজনীতি সবচেয়ে ভয়ংকর হয় যখন তা স্বাভাবিক হয়ে যায়। নাগরিক আর আশা করে না আদালত কথা বলবে, মিডিয়া প্রশ্ন করবে। সে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এই অভ্যাসই কর্তৃত্ববাদের সবচেয়ে বড় জয়। কারণ তখন আর দমন করতে হয় না, মানুষ নিজেই নিজেকে দমন করে।
আন্তর্জাতিকভাবে এই প্রক্রিয়া সুপরিচিত। হান্না আরেন্ট লিখেছিলেন—স্বৈরতন্ত্রের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র হলো সাধারণ মানুষের নিস্তব্ধতা³। আজ ভারতেও তাই ঘটছে। আদালত নীরব, মিডিয়া নীরব, বিশ্ববিদ্যালয় নীরব, প্রতিষ্ঠান নীরব। এই নীরবতার সমবায়ই বাছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি।
নীরবতা এখানে শুধু কথা না বলা নয়, এটি প্রশ্ন না তোলা, তথ্য না চাওয়া, অন্যায়কে স্বাভাবিক ধরে নেওয়া। এসআইআর যখন ভোটার তালিকাকে সন্দেহ তালিকায় পরিণত করে, তখন যদি আদালত প্রশ্ন না তোলে, মিডিয়া রিপোর্ট না করে, প্রতিষ্ঠান প্রতিবাদ না জানায়—তখন রাষ্ট্রের কাজ সহজ হয়ে যায়। নাগরিক তখন একা, আর একা মানুষ সহজেই ভাঙে।
এই প্রবন্ধের সবচেয়ে নির্মম সত্য হলো—নীরবতা নিরপেক্ষ নয়। নীরবতা সবসময় শক্তির পক্ষে থাকে। যখন আদালত চুপ থাকে, সে রাষ্ট্রের পক্ষে দাঁড়ায়। যখন মিডিয়া চুপ থাকে, সে প্রোপাগান্ডাকে জায়গা দেয়। যখন প্রতিষ্ঠান চুপ থাকে, তখন সংবিধান কাগজে থাকে, জীবনে নয়।
এই নীরবতার রাজনীতি ভাঙা সবচেয়ে কঠিন, কারণ এটি অদৃশ্য। এর বিরুদ্ধে মিছিল করা যায় না, মামলা করা যায় না, কারণ এটি নেই বলেই মনে হয়। কিন্তু নীরবতার ফল দৃশ্যমান—নাম কাটা যায়, অধিকার যায়, মানুষ অদৃশ্য হয়। এই অদৃশ্যতাই নীরবতার সাক্ষ্য।
এই কারণেই আদালত ও মিডিয়ার নীরবতা কেবল ব্যর্থতা নয়, এটি একটি রাজনৈতিক ভূমিকা। এসআইআর–এনআরসি–সিএএ প্রকল্প এই নীরবতার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। যদি আদালত কথা বলত, যদি মিডিয়া প্রশ্ন করত, যদি প্রতিষ্ঠান প্রতিবাদ করত—তবে এই প্রকল্প টিকত না। নীরবতা তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।
গণতন্ত্রের শেষ আশ্রয় প্রতিষ্ঠান নয়, নাগরিক। যখন প্রতিষ্ঠান চুপ থাকে, তখন নাগরিককেই কথা বলতে হয়। ইতিহাস বলে—যে সমাজ নীরবতার সঙ্গে লড়তে পারে না, সে একদিন কথা বলার অধিকারও হারায়। এই প্রবন্ধের শেষ সত্য তাই—নীরবতা ভাঙা মানেই গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা।
ডিজিটাল এসআইআর: ভবিষ্যতের ভয়
ডিজিটাল এসআইআর ভবিষ্যতের কোনো কল্পবিজ্ঞান নয়, এটি বর্তমানের মধ্যেই জন্ম নিচ্ছে—নীরবে, ধাপে ধাপে, প্রযুক্তির ভাষায় মোড়া এক নতুন রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা হিসেবে। যেখানে আগে কাগজ নাগরিকত্ব ছিল রাষ্ট্রের অস্ত্র, সেখানে এখন ডেটা নাগরিকত্ব তার পরবর্তী রূপ। আধার, বায়োমেট্রিক, এআই, মুখচেনা ক্যামেরা, অ্যালগরিদম, ডেটাবেস—এই সব মিলিয়ে তৈরি হচ্ছে এক নতুন রাষ্ট্র, যেখানে মানুষ নয়, তার ডেটাই তার পরিচয়; যেখানে নাগরিক নয়, তার ডিজিটাল ছায়াই রাষ্ট্রের কাছে বাস্তব। এই রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব আর রাজনৈতিক অধিকার নয়, এটি একটি প্রযুক্তিগত অনুমোদন, যা যে কোনো মুহূর্তে বাতিল করা যায়।
ডিজিটাল এসআইআর-এর মূল দর্শন হলো—রাষ্ট্র নাগরিককে আর বিশ্বাস করবে না, রাষ্ট্র নাগরিককে স্ক্যান করবে। নাম, বয়স, ঠিকানা, পরিবার, চলাচল, ফোন, চোখের মণি, আঙুলের ছাপ—সবকিছুই রাষ্ট্রের কাছে তথ্য। এই তথ্য একত্র হলে নাগরিক আর ব্যক্তি থাকে না, সে হয়ে ওঠে একটি প্রোফাইল। এই প্রোফাইলকে যাচাই, শ্রেণিবিন্যাস ও সন্দেহভাজন করা যায়। ডিজিটাল এসআইআর এই প্রোফাইলিংকে নাগরিকত্ব যাচাইয়ের নতুন রূপে পরিণত করছে।
আধার এই রাষ্ট্রের ভিত্তি। আধারকে প্রথমে পরিচয় হিসেবে আনা হয়েছিল, পরে তা পরিষেবা, রেশন, ব্যাংক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা—সব কিছুর দরজা হয়ে উঠেছে। এখন আধার ভোটার তালিকা, নাগরিকত্ব যাচাই, এমনকি বেঁচে থাকার শর্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু আধারের সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক হলো—এটি একটি কেন্দ্রীয় ডেটাবেস, যেখানে ভুল সংশোধনের অধিকার নাগরিকের নেই, আর রাষ্ট্রের জবাবদিহি নেই। আধার ব্যর্থ হলে নাগরিক ব্যর্থ হয়, কিন্তু রাষ্ট্র দায় নেয় না। এই অসম সম্পর্কই ডিজিটাল এসআইআর-এর ভিত্তি।
এআই এই রাষ্ট্রকে আরও শক্তিশালী করে। এআই নিরপেক্ষ নয়; এটি যে ডেটা পায়, সেই ডেটার পক্ষপাত বহন করে। ভারতের ডেটাবেসে যদি সংখ্যালঘু, দরিদ্র, নারী, পরিযায়ী মানুষের তথ্য অসম্পূর্ণ থাকে, তবে এআই সেই অসম্পূর্ণতাকেই সন্দেহ হিসেবে চিহ্নিত করবে। এআই তখন প্রশাসনিক কর্মচারীর মতো নয়, বরং একটি অদৃশ্য বিচারক—যার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল নেই। “সিস্টেম বলছে” এই বাক্যটাই তখন চূড়ান্ত রায় হয়ে ওঠে।
মুখচেনা প্রযুক্তি এই রাষ্ট্রকে সর্বক্ষণিক নজরদারিতে পরিণত করে। শহরে, রেলস্টেশনে, ক্যাম্পাসে, রাস্তায়—ক্যামেরা নাগরিককে দেখে, চেনে, নথিভুক্ত করে। রাষ্ট্র জানে নাগরিক কোথায় যায়, কার সঙ্গে যায়, কতক্ষণ থাকে। এই তথ্যকে নাগরিকত্ব যাচাইয়ের সঙ্গে যুক্ত করা হলে, চলাচলই অপরাধ হয়ে উঠতে পারে। পরিযায়ী শ্রমিক, প্রতিবাদকারী, সংখ্যালঘু, বিক্ষোভকারী—সবাই তখন সহজেই “ঝুঁকিপূর্ণ” প্রোফাইলে ঢুকে যায়। ডিজিটাল এসআইআর এখানে কেবল ভোটার তালিকা নয়, জীবন তালিকা তৈরি করে।
ডিজিটাল রাষ্ট্রের সবচেয়ে ভয়ংকর দিক হলো—এটি অদৃশ্য। কাগজের এসআইআর-এ নাগরিক অন্তত জানত সে যাচাইয়ের মধ্যে আছে। ডিজিটাল এসআইআর-এ নাগরিক জানেই না কখন, কোথায়, কীভাবে সে স্ক্যান হচ্ছে, কীভাবে তার স্কোর কমছে, কীভাবে সে সন্দেহভাজন হচ্ছে। এই অজ্ঞানতাই নতুন শাসনের শক্তি। নাগরিক ভীত, কিন্তু জানে না কেন। সে শাস্তি পায়, কিন্তু জানে না কী অপরাধে।
ডেটা যখন নাগরিকত্বের ভিত্তি হয়, তখন নাগরিকত্ব একটি চলমান অবস্থা হয়ে ওঠে। আজ তোমার স্কোর ঠিক, কাল কম। আজ তুমি নাগরিক, কাল যাচাইযোগ্য। এই অনিশ্চয়তা নাগরিককে স্থায়ী ভয় দেয়। সে প্রতিবাদ করে না, প্রশ্ন করে না, কারণ সে জানে—ডেটাবেস তাকে চিহ্নিত করতে পারে। ডিজিটাল এসআইআর এই ভীত নাগরিক তৈরি করে, আর ভীত নাগরিকই কর্তৃত্ববাদের সবচেয়ে নিরাপদ প্রজা।
ডিজিটাল এসআইআর-এর আরেকটি ভয়ংকর দিক হলো—এটি মানবিক বিচারকে অপ্রয়োজনীয় করে তোলে। আগে BLO ভুল করলে, অন্তত মানুষ দায়ী ছিল। এখন ভুল হলে বলা হবে—সিস্টেমে সমস্যা। এই “সিস্টেম” কেউ নয়, আবার সবাই। রাষ্ট্র তখন দায়মুক্ত। এই দায়মুক্তিই ডিজিটাল শাসনের চূড়ান্ত লক্ষ্য—ক্ষমতা থাকবে, দায় থাকবে না।
আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা দেখায়, ডিজিটাল নজরদারি রাষ্ট্র সবসময় সংখ্যালঘুদের আগে আঘাত করে। চীনে উইঘুরদের, যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গদের, ইউরোপে অভিবাসীদের, ইসরায়েলে ফিলিস্তিনিদের ওপর মুখচেনা ও ডেটা প্রোফাইলিং প্রথম প্রয়োগ হয়েছে। ভারতে এই প্রযুক্তি আসছে সেই একই ছকে, কিন্তু গণতান্ত্রিক ভাষার আড়ালে। এসআইআর-এর ডিজিটাল রূপ এই আন্তর্জাতিক কর্তৃত্ববাদের অংশ।
ডিজিটাল এসআইআর গণতন্ত্রের সবচেয়ে গভীর স্তরে আঘাত করে—গোপনীয়তায়। নাগরিকের ব্যক্তিগত জীবন যখন রাষ্ট্রের ডেটায় পরিণত হয়, তখন ব্যক্তিগত বলে কিছু থাকে না। আর যেখানে ব্যক্তিগত নেই, সেখানে স্বাধীনতা নেই। নাগরিক তখন রাষ্ট্রের সামনে নগ্ন, আর রাষ্ট্র অদৃশ্য। এই অসম দৃশ্যই ডিজিটাল স্বৈরতন্ত্রের রূপ।
এই প্রবন্ধের মূল সত্য তাই নির্মমভাবে স্পষ্ট—ডিজিটাল এসআইআর ভবিষ্যতের ভয় নয়, এটি বর্তমানের বাস্তবতা। আধার, এআই, মুখচেনা প্রযুক্তি, ডেটাবেস মিলিয়ে একটি নতুন রাষ্ট্র তৈরি হচ্ছে—যেখানে নাগরিকত্ব কাগজ নয়, কোড; অধিকার নয়, অনুমতি; মানুষ নয়, প্রোফাইল। এই রাষ্ট্রে প্রশ্ন করা সবচেয়ে বড় অপরাধ, কারণ প্রশ্ন মানেই অ্যালগরিদমিক ঝুঁকি।
এই ভবিষ্যৎ এড়ানো সম্ভব, কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন সচেতনতা, প্রতিরোধ ও সাংবিধানিক লড়াই। কারণ প্রযুক্তি নিজে খারাপ নয়, খারাপ হলো ক্ষমতার হাতে প্রযুক্তি। যদি নাগরিক প্রযুক্তিকে প্রশ্ন না করে, প্রযুক্তি নাগরিককে বাতিল করবে।
ডিজিটাল এসআইআর-এর বিরুদ্ধে লড়াই মানে প্রযুক্তির বিরুদ্ধে লড়াই নয়, এটি মানুষের পক্ষে লড়াই। কারণ শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন একটাই—রাষ্ট্র মানুষের জন্য, না মানুষ রাষ্ট্রের ডেটার জন্য?
বিরোধী রাজনীতি ধ্বংসের চূড়ান্ত রূপরেখা
ভোটার না থাকলে বিরোধী থাকবে কীভাবে—এই প্রশ্নটি আপাতদৃষ্টিতে একটি রাজনৈতিক স্লোগান মনে হলেও, এর মধ্যে লুকিয়ে আছে আধুনিক রাষ্ট্রক্ষমতার এক গভীর ও নির্মম কৌশল। বিরোধী রাজনীতি ধ্বংস করার জন্য আর সরাসরি দল নিষিদ্ধ করতে হয় না, নেতাদের জেলে ঢোকাতে হয় না, সংবাদপত্র বন্ধ করতে হয় না—শুধু ভোটারদের অদৃশ্য করে দিলেই যথেষ্ট। কারণ গণতন্ত্রে বিরোধী রাজনীতির ভিত্তি হলো ভোটার, আর ভোটার যদি তালিকা থেকেই মুছে যায়, তবে বিরোধী রাজনীতি নিজের শিকড় হারায়। এসআইআর, এনআরসি, সিএএ, ডেটা যাচাই, রিভিশন, ডিজিটাল প্রোফাইলিং—এই সব মিলিয়ে যে কাঠামো তৈরি হচ্ছে, তা মূলত বিরোধী রাজনীতিকে ধ্বংস করার একটি প্রশাসনিক রূপরেখা, যার কোনো ঘোষণাপত্র নেই, কিন্তু যার ফলাফল অত্যন্ত স্পষ্ট।
এই নতুন রাজনৈতিক কৌশলের মূল বৈশিষ্ট্য হলো—এটি আইন ও প্রশাসনের ভাষায় পরিচালিত হয়। ফলে একে দমন বলা যায় না, একে বলা হয় “পরিষ্কার করা”, “সংশোধন”, “যাচাই”, “শুদ্ধিকরণ”। এই শব্দগুলো নিরীহ মনে হলেও, বাস্তবে এগুলো রাজনৈতিক অস্ত্র। কারণ এগুলো ব্যবহার করে রাষ্ট্র নাগরিকদের মধ্য থেকে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিকে বাদ দেয়—যারা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে বিরোধী শক্তির ভিত্তি। দরিদ্র, পরিযায়ী, সংখ্যালঘু, প্রান্তিক, অনথিভুক্ত মানুষ—এই জনগোষ্ঠীগুলো ঐতিহাসিকভাবে বিরোধী রাজনীতির ভোটব্যাংক। তাদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া মানেই বিরোধী রাজনীতির ভিত্তি কেটে ফেলা।
এই প্রক্রিয়া কখনো একদিনে ঘটে না। এটি ধীরে ধীরে, স্তরে স্তরে কাজ করে। প্রথমে বলা হয় তালিকা সংশোধন হবে, পরে বলা হয় ডেটা মিলবে না, তারপর বলা হয় কাগজ অসম্পূর্ণ, তারপর বলা হয় আপত্তি তুলুন, শুনানি হবে। এই পুরো পথটাই একটি রাজনৈতিক গোলকধাঁধা, যেখানে নাগরিক পথ হারায়। আর যখন নাগরিক পথ হারায়, তখন রাজনীতিও পথ হারায়। বিরোধী দল তখন মাঠে নামতে পারে না, কারণ তাদের ভোটারই নেই।
বিরোধী রাজনীতি ধ্বংসের এই রূপরেখা ইতিহাসে নতুন নয়। লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা, পূর্ব ইউরোপে স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো প্রথমে ভোটার তালিকা নিয়ন্ত্রণ করেছিল, তারপর নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করেছে, শেষে বিরোধী রাজনীতি নিঃশেষ করেছে। ভারতের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া আরও সূক্ষ্ম, কারণ এটি গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভেতরেই হচ্ছে। নির্বাচন হচ্ছে, ব্যালট আছে, কমিশন আছে—কিন্তু ভোটার নেই। এই শূন্যতার মধ্যেই বিরোধী রাজনীতি হাঁপিয়ে ওঠে।
এসআইআর-এর সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক হলো—এটি নির্বাচন-পূর্বে আসে। এটি কোনো প্রশাসনিক কাকতালীয় ঘটনা নয়। নির্বাচন যত কাছে আসে, তত বেশি তালিকা সংশোধন হয়, তত বেশি নাম বাদ পড়ে, তত বেশি আপত্তি নিষ্পত্তি হয় না। ফলে বিরোধী দল মাঠে নামার আগেই তাদের সমর্থকদের বড় অংশ তালিকার বাইরে চলে যায়। বিরোধী দল তখন প্রমাণ করতে পারে না যে তার ভোট চুরি হয়েছে, কারণ ভোটারই আর নেই। এই নীরব চুরিই আধুনিক কর্তৃত্ববাদের সবচেয়ে নিখুঁত অস্ত্র।
এই প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় গ্রামীণ ও শহুরে গরিব জনগোষ্ঠী। কারণ তাদের ঠিকানা বদলায়, কাজ বদলায়, জীবন চলমান। কাগজে এই চলমান জীবন সন্দেহ হয়ে ওঠে। এই মানুষগুলোই বিরোধী রাজনীতির প্রাণ, কারণ তারা প্রশ্ন করে, দাবি তোলে, আন্দোলনে নামে। রাষ্ট্র যখন তাদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেয়, তখন সে শুধু ভোটার বাদ দেয় না, সে প্রতিরোধের সম্ভাবনাও বাদ দেয়।
এই রূপরেখার আরেকটি স্তম্ভ হলো ভয়। ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার ভয় মানুষকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। সে আর মিটিংয়ে যায় না, মিছিলে যায় না, পোস্টারে নাম দেয় না। কারণ সে জানে—রাষ্ট্রের নজরে পড়লে তার কাগজ বিপদে পড়তে পারে। এই ভয়ই বিরোধী রাজনীতির সবচেয়ে বড় শত্রু। রাষ্ট্র এই ভয়কে প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার আড়ালে তৈরি করে, যাতে তা রাজনৈতিক দমন বলে ধরা না পড়ে।
মিডিয়ার নীরবতা এই রূপরেখাকে আরও শক্তিশালী করে। যদি মিডিয়া দেখাত কারা বাদ পড়ছে, কেন বাদ পড়ছে, কোন এলাকায় কত শতাংশ ভোটার উধাও—তাহলে বিরোধী রাজনীতি জনসমর্থন পেত। কিন্তু মিডিয়া যখন চুপ থাকে, তখন বাদ পড়া মানুষগুলো অদৃশ্য হয়ে যায়। অদৃশ্য মানুষের রাজনীতি নেই। এভাবেই বিরোধী রাজনীতি ধ্বংস হয়—নীরবে, নিয়ম মেনে, আইনের ছায়ায়।
এই প্রক্রিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক হলো—এটি ভবিষ্যৎকে স্থায়ীভাবে বদলে দেয়। একবার ভোটার তালিকা বদলে গেলে, একবার ডেটাবেস তৈরি হলে, একবার মানুষ বাদ পড়লে—সেই বাদ পড়া সহজে ফেরে না। পরবর্তী প্রজন্মও সেই বাদ পড়ার বোঝা বহন করে। ফলে বিরোধী রাজনীতি শুধু আজ নয়, আগামীকালও দুর্বল হয়ে যায়। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক প্রকল্প।
এই প্রবন্ধের মূল কথা তাই স্পষ্ট—বিরোধী রাজনীতি ধ্বংসের জন্য আজ আর সেন্সরশিপ লাগে না, জরুরি অবস্থা লাগে না, সেনা লাগে না। লাগে শুধু তালিকা। তালিকার ভেতরে যারা থাকবে, তারা নাগরিক; যারা থাকবে না, তারা ইতিহাস। এসআইআর সেই তালিকার নতুন নাম।
এই রূপরেখা যদি প্রশ্নহীন থাকে, তবে ভবিষ্যতে নির্বাচন থাকবে, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে না; দল থাকবে, কিন্তু বিকল্প থাকবে না; গণতন্ত্র থাকবে, কিন্তু আত্মা থাকবে না। কারণ গণতন্ত্রের আত্মা হলো বিরোধী রাজনীতি, আর বিরোধী রাজনীতির প্রাণ হলো ভোটার।
উপসংহার: ভোট কার—রাষ্ট্রের না নাগরিকের?
ভোট কার—রাষ্ট্রের না নাগরিকের? এই প্রশ্ন দিয়েই বই শেষ হওয়া মানে কেবল একটি গ্রন্থের সমাপ্তি নয়, এটি একটি রাজনৈতিক যুগের মুখোমুখি দাঁড়ানো। কারণ এই প্রশ্নের উত্তরেই লুকিয়ে আছে আধুনিক ভারতের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ। ভোট যদি রাষ্ট্রের হয়, তবে গণতন্ত্র একটি আনুষ্ঠানিকতা মাত্র—একটি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, যেখানে নাগরিক কেবল উপাত্ত, সংখ্যা ও প্রোফাইল। আর ভোট যদি নাগরিকের হয়, তবে রাষ্ট্র একটি চুক্তি—যেখানে ক্ষমতা শাসন করে না, জবাবদিহি করে। এই দুই ধারণার সংঘর্ষই আমাদের সময়ের মূল রাজনৈতিক সংঘাত।
ভারতের সংবিধান ভোটাধিকারকে নাগরিকত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখেছে। এটি কোনো অনুগ্রহ নয়, এটি অধিকার। কিন্তু গত এক দশকে আমরা দেখেছি এই অধিকারকে ধীরে ধীরে শর্তাধীন করে তোলা হয়েছে—ডকুমেন্ট দিয়ে, যাচাই দিয়ে, সন্দেহ দিয়ে, নীরবতা দিয়ে, প্রযুক্তি দিয়ে। এই শর্তগুলো যত বাড়ে, তত স্পষ্ট হয়—রাষ্ট্র ভোটকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইছে। নাগরিক তখন ভোটাধিকার পায় না, সে ভোটাধিকার প্রমাণ করতে বাধ্য হয়।
ভোটাধিকার রাষ্ট্রের হলে, রাষ্ট্র ঠিক করে কে ভোট দেবে। আর রাষ্ট্র যদি ঠিক করে কে ভোট দেবে, তবে সে ঠিক করে কে থাকবে। এই সিদ্ধান্ত আর গণতান্ত্রিক থাকে না, এটি হয়ে ওঠে বাছাই। এসআইআর, এনআরসি, সিএএ, ডেটা রিভিশন, ডিজিটাল প্রোফাইলিং—সব মিলিয়ে একটি নতুন ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে, যেখানে নাগরিকত্ব আর জন্মসূত্রে নয়, এটি যাচাইসাপেক্ষ। এই যাচাই প্রক্রিয়ায় যারা কাগজে দুর্বল, তারা রাজনৈতিকভাবে অদৃশ্য। অদৃশ্য নাগরিকের ভোট নেই, আর ভোট নেই মানেই রাজনৈতিক অস্তিত্ব নেই।
এই বইয়ের প্রতিটি অধ্যায় একটাই কথা বলেছে—ভোটার তালিকা আর নিরীহ তালিকা নয়, এটি ক্ষমতার মানচিত্র। যে তালিকাকে নিয়ন্ত্রণ করে, সে রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই সত্য বুঝেই আধুনিক কর্তৃত্ববাদ ভোটার তালিকাকে অস্ত্র বানায়। আগেকার স্বৈরতন্ত্র সেনা নামাত, আজকের স্বৈরতন্ত্র নাম কাটে। আগেকার শাসক ভোট বাতিল করত, আজকের শাসক ভোটার বাতিল করে। ফলাফল একই—বিরোধী রাজনীতির মৃত্যু।
এই প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয় সেই নাগরিকের, যে রাষ্ট্রকে বিশ্বাস করেছিল। গ্রাম থেকে শহরে আসা শ্রমিক, নাম বদলানো নারী, কাগজহীন বৃদ্ধ, ভাষান্তরিত সংখ্যালঘু, পরিযায়ী পরিবার—এই মানুষগুলো রাষ্ট্রের চোখে সন্দেহভাজন হয়ে ওঠে। অথচ তারা রাষ্ট্রের ভিত্তি। তারা কর দেয়, কাজ করে, রক্ত দেয়, ভোট দেয়। কিন্তু যখন ভোট দেওয়ার সময় আসে, তখন রাষ্ট্র তাদের জিজ্ঞেস করে—তুমি কে? এই প্রশ্নই নাগরিকত্বের অবমাননা।
ভোট রাষ্ট্রের হলে নাগরিক কেবল শাসিত। তখন ভোট মানে পছন্দ নয়, অনুমতি। রাষ্ট্র চাইলে দেবে, চাইলে নেবে। এই রাষ্ট্রে নির্বাচন হয়, কিন্তু গণতন্ত্র থাকে না। কারণ গণতন্ত্র মানে শুধু ভোট নয়, গণতন্ত্র মানে সমান ভোট। আর সমান ভোট তখনই সম্ভব, যখন রাষ্ট্র নাগরিককে বিশ্বাস করে। বিশ্বাস ভেঙে গেলে গণতন্ত্রও ভেঙে যায়।
এই বই দেখিয়েছে, কীভাবে নীরবতা এই প্রক্রিয়ার সবচেয়ে বড় সহযোগী। আদালত চুপ থাকে, মিডিয়া চুপ থাকে, প্রতিষ্ঠান চুপ থাকে। এই নীরবতা রাষ্ট্রের কাজ সহজ করে দেয়। নাগরিক তখন একা হয়ে যায়—ফর্মের সামনে, সার্ভারের সামনে, অফিসের সামনে। একা নাগরিক প্রতিরোধ করতে পারে না। এই একাকিত্বই আধুনিক দমনের সবচেয়ে সূক্ষ্ম রূপ।
ডিজিটাল এসআইআর এই সংকটকে আরও গভীর করে। কাগজের যুগে অন্তত মানুষ জানত সে বাদ পড়েছে। ডিজিটাল যুগে মানুষ জানেই না সে কখন বাদ পড়ছে। অ্যালগরিদম তাকে স্কোর দেয়, ঝুঁকি দেয়, সন্দেহ দেয়। এই অদৃশ্য বাছাই রাষ্ট্রকে সর্বশক্তিমান করে তোলে, আর নাগরিককে সর্বদা অনিশ্চিত। অনিশ্চিত নাগরিক কখনো মুক্ত হতে পারে না।
এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ কোথায়? আদালতে? মিডিয়ায়? রাজনীতিতে? সমাজে? এই বইয়ের উত্তর নির্মম—প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ হলে নাগরিককেই প্রতিষ্ঠান হতে হয়। ইতিহাস বলে, কোনো গণতন্ত্র আদালত দিয়ে বাঁচে না, মিডিয়া দিয়ে বাঁচে না—বাঁচে নাগরিকের স্মৃতি ও প্রতিরোধ দিয়ে। যখন মানুষ মনে রাখে যে ভোট তার, তখন রাষ্ট্র তা কেড়ে নিতে পারে না।
এই উপসংহার কোনো আশাবাদী স্লোগান নয়, এটি একটি সতর্কবার্তা। যদি ভোট রাষ্ট্রের হয়, তবে আগামী দিনে রাষ্ট্র ঠিক করবে কে নাগরিক, কে নয়; কে কথা বলবে, কে নয়; কে থাকবে, কে মুছে যাবে। আর যদি ভোট নাগরিকের হয়, তবে রাষ্ট্রকে প্রতিদিন প্রমাণ করতে হবে—সে বৈধ, সে ন্যায্য, সে জনগণের।
এই বইয়ের শেষ প্রশ্ন তাই কোনো তাত্ত্বিক প্রশ্ন নয়, এটি একটি জরুরি প্রশ্ন—ভোট কার?
রাষ্ট্রের হলে আমরা প্রজা।
নাগরিকের হলে আমরা স্বাধীন।
এই দুইয়ের মধ্যে একটিই বেছে নিতে হবে। মাঝামাঝি কিছু নেই। কারণ ইতিহাস কখনো মাঝামাঝি দাঁড়ায় না। ইতিহাস সবসময় প্রশ্ন করে—তুমি কোন পাশে?

 নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা
নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা