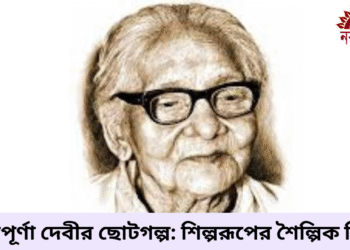আঠারাে শতক থেকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যে বাংলা গদ্যচর্চা শুরু হয়, তা ঐতিহাসিক কারণে পাদরী ও সংস্কৃত পন্ডিতদের দ্বারা গড়ে ওঠে। তারা বাংলাকে সংস্কৃতের দুহিতা জ্ঞান করে ব্যাকরণরীতি ও শব্দমালার দিক থেকে সংস্কৃতের উপর বেশি নির্ভর করেন। পন্ডিতদের হাতে বাংলা ভাষা কিরকম মূর্তি লাভ করেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন,
“আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথােপকথন করিতে শুনিয়াছি তাহা সংস্কৃত ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ ‘খয়ের’ বলিতেন না, ‘খদির’ বলিতেন, কদাচ চিনি বলিতেন না, ‘শর্করা’ বলিতেন। ‘ঘি’ বলিলে তাহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত, ‘আর্জাই’ বলিতেন, কদাচিৎ কেহ ঘৃতে নামিতেন। ‘চুল’ বলা হইবে না, ‘কেশ’ বলিতে হইবে। ‘কলা’ বলা হইবে না, রম্ভা বলিতে হইবে।…পন্ডিতদের কথােপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত বাংলাভাষা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল তাহা বলা বাহুল্য।”
এমন ভাষার প্রতি বাঙালি মুসলমানদের মনে প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়া স্বাভাবিক ছিল। তাই মুসলমান সমাজপতিদের কাছে তা গ্রহণযােগ্য ছিল না। আব্দুল লতিফ সংস্কৃতবহুল বাংলার পরিবর্তে কোর্ট-কাচারীতে ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দমিশ্রিত বাংলাকে গ্রামের মুসলমান বালকের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষ অভিমত জ্ঞাপন করেছিলেন। সাহিত্যের ভাবগত ও বিষয়গত দ্বন্দ্বেও অনেকে বিচলিত ও শঙ্কিত ছিলেন।

বিশ শতকের প্রথমের দিকে মােহাম্মদ শহীদুল্লাহ কলকাতা বিবিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়তে চেয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় রাজি ছিল, কিন্তু আপত্তি করলেন একজন সংস্কৃত পন্ডিত, যিনি বেদ-উপনিষদ পড়াতেন। কোনও ম্লেচ্ছকে তিনি বেদ-উপনিষদ পড়াবেন না। কিছুতেইনা। কলকাতা বিধবিদ্যালয়ে শহীদুল্লাহর সংস্কৃত পড়া হয়নি। ‘The Bengalee’ পত্রিকার সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি অবশ্য এতে রেগে তার পত্রিকায় প্রস্তাব করেছিলেন যে, ওই পন্ডিতকে গঙ্গার ‘পবিত্র’ জলে নিক্ষেপ করা হােক। তাতে কাজ হয়নি, উপাচার্য আশুতােষ মুখার্জির চেষ্টাতেও কাজ হয়নি। তবে শহীদুল্লাহ সংস্কৃত পড়েছিলেন ঠিকই, তবে সেটা বাংলায় সম্ভব হয়নি, সম্ভব হয়েছিল জার্মানীতে গিয়ে। এমনকি ইংরেজ কর্মচারীদেরও প্রথমের দিকে সংস্কৃত শেখাতে আগ্রহ দেখানাে হয়নি। জহরলাল নেহেরু তাঁর ‘The Discovery of India’ বইতে স্মরণ করেছেন যে, স্যার উইলিয়াম জোন্স (১৭৪৬-১৭৯৪), পরে যিনি ভারতবিদ হিসেবে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যকে ইউরােপে পরিচিত করতে অত্যন্ত জরুরি ভূমিকা গ্রহণ করেন, কলকাতা হাইকোর্টের একজন বিচারপতি হওয়া সত্ত্বেও তিনি সংস্কৃত শেখার ব্যাপারে প্রথমে সুবিধা করতে পারেননি। বিচিত্র ও কঠোর শর্তে এক পন্ডিতের কাছে জোন্স সংস্কৃত শিক্ষা করেছিলেন। উল্লেখ্য এই জোন্সের উদ্যোগেই কলকাতায় এশিয়াটিক সােসাইটির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় ১৭৮৪ সালে।
শূদ্রের জন্য তথা নীচুতলার মানুষদের জন্য সংস্কৃত শেখা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। শিখলে, শুনলে বা বললে কানে তরল সীসা ঢেলে দেওয়া, মুখের ভিতর লােহার তপ্ত শিক ঢুকিয়ে দেওয়া, জিভ কেটে নেওয়া প্রভৃতি যে সব শাস্তির ব্যবস্থা ছিল তা রােমহর্ষক, অবিবাস্য। মুসলিম সুলতানদের পৃষ্ঠপােষকতাতেই কৃত্তিবাস ওঝা রামায়ণের ও কাশীরাম দাস মহাভারতের অনুবাদ করেছিলেন। তাদের সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছিল—‘কৃত্তিবাসে, কাশীদাসে আর বামন ঘেঁষে, এই তিন সর্বনেশে।’ কিন্তু সংস্কৃত পন্ডিতদের এই রক্ষণশীলতা কেন? কিছুটা অবশ্যই সংস্কারবশত। কিন্তু আসল কারণ সংস্কার নয়, স্বার্থ। একই কারণে মুসলিম উর্দু-ঠিকাদারেরা বাংলা ভাষা শিক্ষাকেও এক সময়ে হারাম বলে ফতােয়া দিয়েছিল।
অব্রাহ্মণ তাে নয়ই, এমনকি ব্রাহ্মণ পন্ডিতরাও সংস্কৃত সাহিত্য বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারে অনুমােদন পাননি। ব্রাহ্মণেরা বাংলার চর্চাকে ভাল চোখে দেখেননি। বাংলা ভাষাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেছেন। যখন বাংলাকে মেনে নিতে বাধ্য হলেন, বাংলা চর্চাকারীদের সামাজিক শক্তি ও সংখ্যাবৃদ্ধির কারণে তখন এই ভাষার ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা। ব্যাকরণ ঠিক রইল, কিন্তু অভিধান স্ফীত হল সংস্কৃত শব্দাধিক্যে। এর ইতিহাসটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন ‘চর্যাপদের’ মােট দু’হাজার শব্দের মধ্যে প্রকৃত তৎসম শব্দ পাওয়া যাচ্ছে মাত্র একশ। শতকরা হিসাবে তা ৫টি। পরবর্তীকালে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যে সংস্কৃত শব্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তখনাে শতকরা ১২.৫-কে ছাড়িয়ে যায়নি। তৎসম শব্দ বাড়ল ঊনবিংশ শতাব্দীর গদ্যে ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের হস্তক্ষেপে। বাড়তে বাড়তে তা শতকরা ৮০-তে এসে দাঁড়াল। শতকরা ৮০ ভাগ সংস্কৃত শব্দের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি ইংরাজিতে লেখা বাংলা ভাষার ওপর তাঁর ব্যাকরণ বইতে (১৮১৮ তে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণে)। অথচ ওই বইয়েরই ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণে কেরী মন্তব্য করেছিলেন যে, সাধু বাংলা যদিও সংস্কৃত থেকেই উদ্ভুত, তবু, ‘Multitudes of words originally Persian are constantly employed in common conversation, which perhaps ought to be considered helping rather than corrupting the language.’ বাংলা ভাষা থেকে কিভাবে আরবি-ফারসি শব্দ দূর করে সংস্কৃতকরণ প্রক্রিয়া চালানাে হয়েছিল তার বিবরণ দিতে গিয়ে সজনীকান্ত দাস লিখেছেন,
“১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হালহেড এবং পরবর্তীকালে হেনরি পিস ফরষ্টার ও উইলিয়াম কেরী বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত জননীর সন্তান ধরিয়া আরবী পারসীর অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে রীতিমত ওকালতি করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে এই তিন ইংলভীয় পন্ডিতের যত্ন ও চেষ্টায় অতি অল্প দিনের মধ্যে বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এই আরবী-পারসী-নিসূদন-যজ্ঞের সূত্রপাত এবং ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে কোম্পানীর সদর মফস্বল আদালত সমূহে আরবী পারসীর পরিবর্তে বাংলা ও ইংরেজী প্রবর্তনে এই যজ্ঞে পূর্ণাহুতি। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মও এই বৎসরে। এই যজ্ঞের ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলােদ্দীপক আরবী পারসীকে অশুদ্ধ ধরিয়া শুদ্ধ পদ প্রচারের জন্য সেকালে কয়েকটি ব্যাকরণ-অভিধানও রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল সাহেবরা সুবিধা পাইলেই আরবী-ফারসীর বিরােধিতা করিয়া বাংলা ও সংস্কৃতকে প্রাধান্য দিতেন ফলে দশ পনর বৎসরের মধ্যে বাংলা-গদ্যের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছিল। …অদ্বিতীয় সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত ভগবদ্গীতার অনুবাদক চার্লস উইলকিন্স সংস্কৃত ও বাংলা শব্দসংগ্রহে মনােনিবেশ করিয়া সংস্কৃত রীতিতে বাংলা শব্দকোষ সমৃদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।”
১৭৭৮ সালে লিখিত হেলহেড সাহেবের (যদিও তিনিও সংস্কৃতকরণ প্রক্রিয়ার অন্যতম কান্ডারী) মন্তব্য পাঠে উপরােক্ত বিদেশী পন্ডিতদের মনােভাব পরিষ্কারভাবে ধরা পড়বে। তিনি লিখেছিলেন,
“Hitherto we have seen the formation and construction of the Bengal language in all its genuine simplicity; when it could borrow Shanscrit terms for every circumtances without the danger of becoming unintelligble, and when tyranny had not yet attempted to impose its fetters on the freedom of composition …how far the Modern Bengalees have been forced to debase the Purity of their native dialect, by the necessity of addressing themselves to their Mahommedan Rulers … [who] obliged the natives to procure a Persian translation to all the papers which they might have occasion to present. This practice familiarised to their ears such of the Persian terms as more immediately concerned their several affairs; and by long habit they learnt to assimilate them to their own language, by applying the Bengal inflexions and termination.”
সুলতানি ও নবাবি আমলে ফারসি ছিল সরকারি ভাষা, তখন মৌলবীরা সুবিধা পেয়েছেন তাদের ফারসি জ্ঞানের দরুণ। ব্রাহ্মণরাও শিখেছিলেন সেই ভাষা। রামমােহন চমৎকার ফারসি জানতেন। মধুসূদন, নবীনচন্দ্র সেন, প্রফুল্লচন্দ্র রায়—এদের পিতা ফারসিতে দক্ষ ছিলেন এবং এরা যে ব্যতিক্রম ছিলেন তা নয়। নিয়মের মধ্যেই পড়তেন, কিন্তু তবুও শ্রেণীগত নৈকট্যের ভেতরে সম্প্রদায়গত দূরত্বের একটা বােধ ছিল বৈ কি। সেই বােধটাই সক্রিয় হয়ে উঠল যখন ইংরেজরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় এল। ক্ষমতার নতুন অধিকারীরা যাদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল, সেই মুসলিম শাসকদের সম্প্রদায়ের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ মনােভাব গড়ে তুলবে এটা স্বাভাবিক ছিল না। গড়ে তুলতে ইংরেজ শাসকরা চেষ্টাও করেনি। বরং মুসলিম শাসনামলে হিন্দু মধ্যবিত্ত কেমন অনাচার ক্লিষ্ট ও নিরাপত্তাহীন অবস্থায় ছিল সেটা মনে করিয়ে দিয়ে এই শ্রেণীকে ইংরেজরা নিজেদের কাজের স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছে। ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের প্রতিহিংসাপরায়ণতা ওই শাসকদের প্রশ্রয়ে চরিতার্থতার সুযােগ পেয়ে বেশ স্ফীত হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই। পরবর্তীকালে এর প্রভাব কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজে বেশ প্রকটভাবে দেখা দেয়।
ভাষায় যে সংস্কৃতায়ণ ঘটেছিল তার প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশে জন্ম নিয়েছিল এক ‘অপূর্ব মুসলমানী’ ভাষা। কথাটা খুবই সত্য। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন,
“ভাষার পার্থক্য মানসিক পার্থক্যের সৃষ্টি করল কিনা সে সম্পর্কে এখানে কোনাে মতামত দেওয়া সঙ্গত হবে না।”
আসলে মতামত দেওয়া খুবই সঙ্গত ছিল। সবাই মিলে তা দিলে কে জানে হয়তাে ঘটনার গতি সেই সাম্প্রদায়িকতার অভিমুখে ধাবিত হত না। আর সেটা হয়নি বলেই বাঙালি জাতির জন্য ভয়াবহ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য এটা স্বীকার করেছেন যে, বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে ওই সংস্কৃতায়ণ ভাষার শক্তি তাে বৃদ্ধি করেইনি বরং জাতি হিসেবে বাঙালিকে দুর্বল করে ফেলেছে। খুবই খাঁটি কথা। অবশ্যই দুর্বল করেছে, কেননা তা সাহায্য করেছে বাঙালিকে বিভক্ত করতে।
ভাষার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা কেবল শব্দ নিয়ে গ্রহণ-বর্জনের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেনি, বিশেষ বিশেষ শব্দ নিয়ে প্রচন্ড কলহের জন্ম পর্যন্ত দিয়েছে। যেমন রক্ত অর্থে ‘খুন’ শব্দের ব্যবহার নিয়ে। এই বিশেষ কলহটা সৃষ্টি হয়েছিল কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায়, ওই শব্দটির (কবিতার লাইনটি ছিল—‘উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার’। ‘বাঙ্গালার কথা’ নামের কোনও একটি পত্রিকায় নাকি ওই আপত্তির কথা ছাপা হয়েছিল) ব্যবহার নিয়ে। হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। নজরুল ক্ষুব্ধ হৃদয়ে বলেন, “…আজকের ‘বাংলার কথা’-য় দেখলাম কবি গুরু আমায়ও বাণ নিক্ষেপ করতে ছাড়েননি। তিনি বলেছেন, আমি কথায় কথায় রক্তকে ‘খুন’ বলে অপরাধ করেছি। কবির চরণে ভক্তের সশ্রদ্ধ নিবেদন, কবি ত নিজেও টুপি পায়জামা ব্যবহার করেন, অথচ আমরা পরলেই তাঁর আক্রোশের কারণ হয়ে উঠি কেন, বুঝতে পারিনে। এই আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়ােগ কবিতায় শুধু আমিই করিনি। আমার বহু আগে ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি করে গেছেন। …‘খুন’ আমি ব্যবহার করি আমার কবিতায় মুসলমানী বা বলশেভিকী রং দেওয়ার জন্য নয়। আমি শুধু ‘খুন’ নয়—বাংলায় চলতি আরােও অনেক আরবি ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছি আমার লেখায়। আমার দিক থেকে ওর একটা জবাবদিহি আছে। …বাংলা কাব্যলক্ষ্মীকে দুটো ‘ইরানী জেওর’ পরালে তার জাত যায় না, বরং তাকে আরও খুবসুরতই দেখায়। …তাছাড়া যে খুনের জন্য কবিগুরু রাগ করেছেন তা দিনরাত ব্যবহৃত হচ্ছে ..খুন করা, খুন হওয়া ইত্যাদি। …হৃদয়েরও খুন-খারাবী হতে দেখি আজো।”
নজরুলের খুন শব্দের ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের কাছে সঠিক বলে মনে হয়নি। তাঁর বক্তব্য ছিল,
“হত্যা অর্থে খুন ব্যবহার করলে সেটা বেখাপ হয় না, বাংলায় সর্বজনের ভাষায় সেটা বেমালুম চলে গেছে। কিন্তু রক্ত অর্থে খুন চলেনি…।”
বিশ্বকবির এমন মত নিয়ে তর্ক চলতে পারে, যেমন আবুল ফজল লিখেছিলেন, “রাজশেখর বাবুর চলন্তিকায় ‘খুন চড়া’ শব্দটিও দেখলাম এবং তিনি তার অর্থ দিয়েছেন, “ক্রোধে রক্ত গরম হওয়া।”…রক্ত অর্থে খুন শব্দটি আমাদের ভাষার অভিধানে স্থান পেয়েছে। অথচ বালক রবীন্দ্রনাথ ‘বাল্মীকি প্রতিভা’ নামে যে কাব্য রচনা করেছিলেন তার পাতা উল্টে গেলে দেখা মিলবে ‘খুন’-র। ১২৮৭ সালে লেখা ‘বাল্মীকি প্রতিভা’-য় ‘পাখিটি মরিলে কাঁদিয়া খুন’ বলায় দস্যু রাজা বাল্মীকির প্রতি দস্যুদের অবহেলা প্রকাশ পেয়েছিল।

যাইহােক, প্রয়ােগ প্রসঙ্গ থেকে সরে গিয়ে বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারের বিতর্কটি বহুদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন, দেশ বা সমাজের পরিচয় দিতে গিয়ে জিদ বশত আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ প্রযােগ করলে উল্টো ফলই ঘটবে। অপরদিকে বন্দে আলি মিয়ার ‘ময়নামতীর চর’ কাব্যে পরিচিত প্রাদেশিক শব্দসমূহ ব্যবহার করায় কবি খুশি হয়েছিলেন। বাংলায় আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ ব্যবহার এবং তার জটিলতা নিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ ১১ চৈত্র ১৩৪০-এ এম এ আজমকে এক পত্র লিখেছিলেন। পত্রটি প্রবাসীতে ‘ভাষাশিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা’ শিরােনামে প্রকাশিত হয়,
“…ভাষা মাত্রেরই একটা মজ্জাগত স্বভাব আছে, তাকে না মানলে চলে না।…ইংরেজীতে সহজেই বিস্তর ভারতীয় ভাষার শব্দ চলে গেছে। একটা দৃষ্টান্ত Jungle-সেই অজুহাতে বলা চলে না, তবে কেন অরণ্য শব্দ চালাব না। ভাষা খামখেয়ালি, তার শব্দ-নির্বাচন নিয়ে কথা-কাটাকাটি করা বৃথা। বাংলা ভাষায় সহজেই হাজার হাজার পারসি আরবি শব্দ চলে গেছে। তার মধ্যে—আড়াআড়ি বা কৃত্রিম জেদের কোনাে লক্ষণ নেই। কিন্তু যে-সব পারসি আরবি শব্দ সাধারণ্যে অপ্রচলিত অথবা হয়তাে কোনাে এক শ্রেণীর মধ্যেই বদ্ধ, তাকে বাংলা ভাষার মধ্যে প্রপে করাকে জবরদস্তি বলতেই হবে। হত্যা অর্থে খুন ব্যবহার করলে সেটা বেখাপ হয় না, বাংলায় সর্বজনের ভাষায় সেটা বেমালুম চলে গেছে কিন্তু রক্ত অর্থে খুন চলেনি, তা নিয়ে তর্ক করা নিষ্ফল।”
আসলে রবীন্দ্রনাথ অকারণে আরবি, ফারসি, উর্দু, হিন্দী বা যেকোন বিদেশী শব্দকে বাংলায় ব্যবহার করা ভাষার সৌন্দয্যের পক্ষে ক্ষতিকর মনে করতেন। শুধু তাই নয়, তিনি জোর করে আরবি, ফারসি, উর্দু শব্দের এমন প্রয়ােগ বিশেষ করে প্রয়ােজনকে সাম্প্রদায়িকতা বলে গণ্য করতেন।।
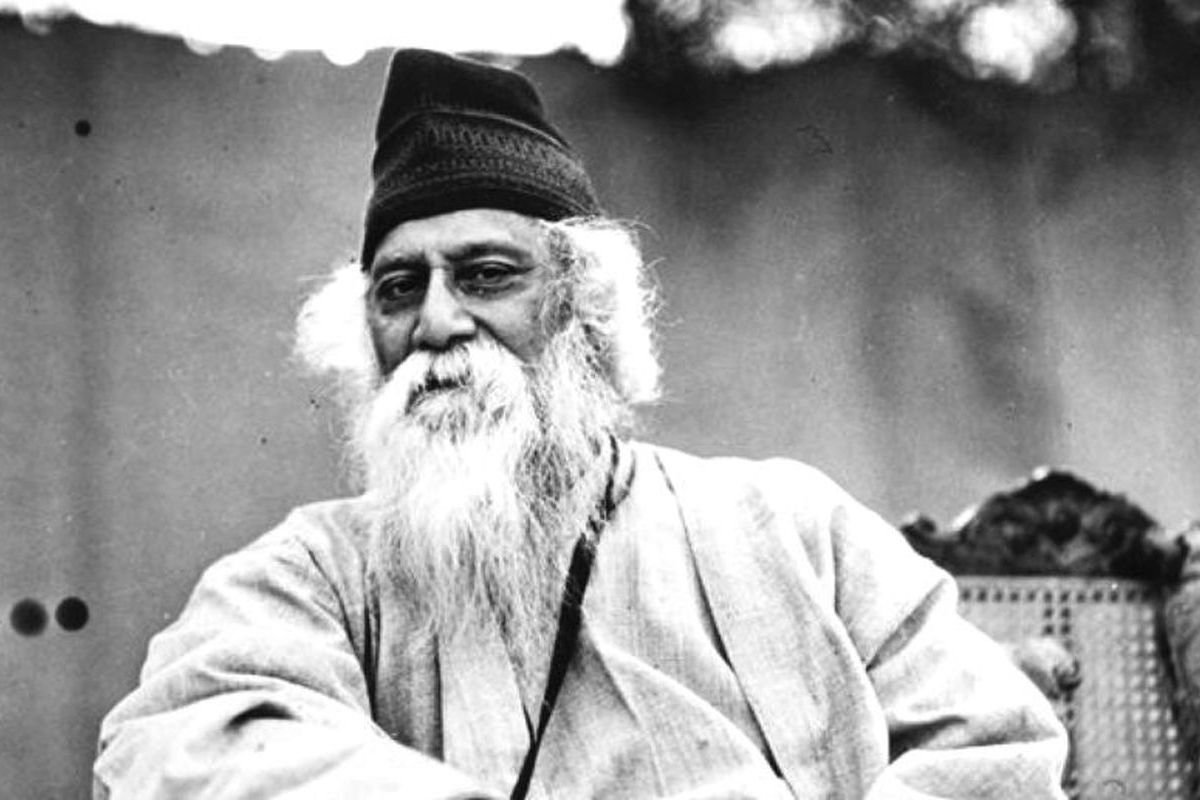
বস্তুত বাংলার মুসলমান বুদ্ধিজীবী মহল বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকের মধ্যে মােটামুটিভাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে ধর্মীয়, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিগত কারণে এবং সর্বোপরি ইসলামী সাহিত্য গঠনের প্রয়ােজনে বাংলা ভাষায় কিছু পরিমাণে আরবি, ফারসি ও উর্দু শব্দের আনয়ন প্রয়ােজন। ১৯২৬ সালের ৬ আগষ্ট বাংলার মুসলমান সমাজের কৃষ্টি ও সাহিত্য চিন্তার কর্ণধার বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি কলকাতার এম. এল. জুবিলি ইনষ্টিটিউসনে অনুষ্ঠিত এক গুরুত্বপূর্ণ সভায় আবেদন রেখেছিলেন যে কলকাতা বিধবিদ্যালয় যেন আরবি ও ফারসি শব্দবহুল বাংলাভাষাকে স্বীকৃতি দেয়। এই সমিতি পরবর্তীকালে ১৯৩২ সালে ২০শে আগষ্টকলকাতায় অনুষ্ঠিত আর একটি সভায় স্পষ্টভাবেই ঘােষণা করে যে বাংলার মুসলমানের ভাষা বাংলার হিন্দুর ভাষা থেকে পৃথক এবং যেসব ব্যক্তি বা মহল বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারে অনিচ্ছুক তারা অবশ্যই মুসলিম বাংলাভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করছে। ১৯৩৫ সালে ৬ ফেব্রুয়ারী স্টার অব ইণ্ডিয়া’ পত্রিকায় প্রকাশিত এক খােলা চিঠিতে তৎকালীন বাংলার মুসলমান সমাজের অগ্রগণ্য বুদ্ধিজীবী কাজী নজরুল ইসলাম, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, মােহাম্মদ হাবিবুল্লা, আবদুল কাদির, মুজিবর রহমান, শামসুননাহার, মােহাম্মদ মােদাব্বের, আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখ একই বক্তব্য উপস্থিত করেন এবং সার্থক মুসলিম সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে যে বাংলা ভাষায় প্রয়ােজনীয় কিছু আরবি ফারসি শব্দের প্রয়ােগ দরকার তা তারা উল্লেখ করেন। এই বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আবার সুসাহিত্যিক ও সমালােচক এস. ওয়াজেদ আলির মত ব্যক্তিও ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়ােগেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। ইসলামি শব্দের বাংলাভাষায় সঠিক উচ্চারণের জন্য তিনি বাংলা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণে উর্দু বর্ণমালার কিছু বৈশিষ্ট্য আরােপ করতেও চেয়েছিলেন। বুদ্ধিজীবীদের একাংশ যেমন কাজী আব্দুল ওদুদ, আবুল হােসেন, মােতাহার হােসেন চৌধুরি বা কাজী আনােয়ারুল কাদির (যারা শিখা গােষ্ঠী নামে পরিচিত) ইত্যাদি আরবি ফারসি শব্দের বহুল প্রয়ােগ চাননি বা স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ পরিবর্তনের পরিপন্থীও ছিলেন, তাঁদের বক্তব্য ছিল—বাংলা ভাষায় পরিবর্তন না করে সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে যদি প্রকৃত ইসলামী চিন্তা ও ভাব আনা যায় তবেই বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য গড়ে উঠবে।
একথা ঠিক যে, কাজী নজরুলের আগে কোনও বাঙালি সাহিত্যিক বাংলা ভাষায় সাফল্য ও সার্থকতার সঙ্গে আরবি, ফারসি ও উর্দু শব্দের প্রয়ােগ করতে সক্ষম হননি, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অবশ্য কিছু সীমিত প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু সার্থক হােক বা অসার্থক হােক বাঙালি মুসলমান লেখক ও সাহিত্যিকদের বাংলা ভাষায় আরবি, ফারসি বা উর্দু শব্দের প্রয়ােগে খানিকটা অনাবশ্যক প্রচেষ্টা অবশ্যম্ভাবীরূপে সমকালীন হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল যাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও।
১৩৩৯ সনের ‘প্রবাসী’ পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মােহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রণীত মক্তব মাদ্রাসা শিক্ষা- ‘২য় ভাগ’ ও মােহম্মদ মােবারক আলি প্রণীত মক্তব মাদ্রাসা সাহিত্য- ‘১ম ভাগ’ নামক শিশু পাঠ্যপুস্তক দুটির সমালােচনা করেছিলেন। প্রবন্ধের নাম ছিল ‘মক্তব মাদ্রাসার বাংলা ভাষা’। রমেশচন্দ্র এই দুই পুস্তকের বিভিন্ন অংশের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, অকারণে এই দুই লেখক কিছু অপ্রচলিত আরবি, ফারসি শব্দ প্রায় জোরপূর্বক এই শিশু পাঠ্যপুস্তকে ঢুকিয়েছেন এবং বাধ্য হয়েছেন এই শব্দগুলির বাংলা প্রতিশব্দ দিতে যাতে শিশুরা এই শব্দগুলির অর্থ বুঝতে পারে। এই লেখাতে আলােচ্য পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া কিছু শব্দার্থের যে বিবরণ ছিল তার কয়েকটি প্রসঙ্গত্র(মে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন—প্রদীপ = চেরাগ, ধার্মিক = দীনদার, স্বপ্ন = খাব, বিদ্যা = এলেম, সৃষ্টি = পয়দা, আশ্রয় = পানাহ, নিস্পাপ = বেগুনাহ, কৃতজ্ঞতা = শােকর গুজারি ইত্যাদি। রমেশচন্দ্র এই মনােবৃত্তির পিছনে মুসলমানের হিন্দু বিদ্বেষ এবং প্যান-ইসলামিজমের উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর সম্প্রদায়কে সাবধান করে বলেছেন, “শুনা যায় ঢাকা সেকেণ্ডারী বাের্ড মুসলমানি বাংলায় লিখিত পুস্তক সকল হিন্দু মুসলমান সকল ছাত্রের জন্যই অবশ্য পাঠ্য করিতেছেন, বাঙালি সাবধান।”
রবীন্দ্রনাথ ১৩৩৯ সনের ‘প্রবাসীর’ ভাদ্র সংখ্যায় ওই প্রবন্ধের বিষয় উল্লেখ করে বলেন,
“সহজভাবে বাংলা ভাষায় আগত আরবি ফারসি যেমন—হাজার, মেজাজ, বেচারা, নেশাখাের, বদমায়েস শব্দ বদল করবার কথা উঠতেই পারে না। কিন্তু ‘শিশু পাঠ্য’ বাংলা কেতাবে গায়ের জোরে আরবিআনা, পারসিআনা করাটাকেই আচার নিষ্ঠ মুসলমান যদি সাধুতা বলে জ্ঞান করেন তবে ইংরেজি স্কুল পাঠ্যের ভাষাকেও মাঝে মাঝে পারসি বা আরবি ছিটিয়ে শােধন না করেন কেন?”
ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,
“মৌলবী ছাহাব বলতে পারেন আমরা ঘরে যে বাংলা বলি সেটা ফারসি-আরবি জড়ানাে, সেইটাকেই মুসলমান ছেলেদের বাংলা বলে আমরা চালাব। আধুনিক ইংরেজি ভাষায় যাদের অ্যাংলাে-ইন্ডিয়ান বলে, তারা ঘরে যে ইংরেজি বলেন, সকলেই জানেন সেটা আডিফাইল্ড, আদর্শ ইংরেজি নয়—স্বসম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতবশত তাঁরা যদি বলেন যে, তাদের ছেলেদের জন্যে সেই অ্যাংলােইন্ডিয়ানি ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা না করলে তাদের অসম্মান হবে, তবে সে কথাটা বিনা হাস্যে গম্ভীরভাবে নেওয়া চলবে না।”
স্বাভাবিকভাবেই কৃষ্টি সচেতন বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবী তাঁদের চেষ্টার এই সমালােচনাকে মেনে নিতে পারেনি। প্রতিবাদস্বরূপ প্রথম সারির নেতা ও সাহিত্যসেবী আকরাম খাঁ তাঁর নিজের পরিচালিত মােহাম্মদীতে ‘মক্তব মাদ্রাসার পাঠ্য’ শীর্ষক এক প্রবন্ধে এই আরবি-ফারসিয়ানার স্বপক্ষে এক জবাবে উল্লেখ করেছেন যে, মুসলমানের বিশিষ্ট ভাব ও সংস্কার রার জন্য, হিন্দুর সঙ্গে ‘কালচারগত পার্থক্য রক্ষার জন্য কতকগুলি আরবিফারসি শব্দ ব্যবহার করা একান্তই প্রয়ােজনীয়। আকরাম খাঁর চিন্তাধারার প্রতিধ্বনি শােনা যায় আইনজীবী সাহিত্যিক এস. ওয়াজেদ আলির গুলিস্তায় প্রকাশিত নিবন্ধে। এই নিবন্ধে ওয়াজেদ আলি শুধু যে মাত্র রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেছেন তা নয়, খুব স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন যে মুসলমানের জাতীয় আত্মার বা কালচারের সঙ্গে আরবি, ফারসি এবং উর্দু ভাষা ঘনিষ্ঠ এবং সেই জাতীয় আত্মার সম্যক প্রকাশের জন্য যতটা আরবি, ফারসি এবং উর্দু শব্দের এবং ভাবের আমদানী করা দরকার ততটাই সে করবেই, কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না। হিন্দু সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবীরাও এর জবাব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন। ছােট, বড়, মাঝারি মাপের সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী এবং সংস্কৃতিচেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিরা প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছিলেন। শনিবারের চিঠি, বসুমতী, ভারতবর্ষ ইত্যাদি সাময়িক পত্র পত্রিকা সােচ্চার হয়ে উঠেছিল প্রতিবাদে।
আসলে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার অভিমুখ বিভিন্ন প্রকৃতির, তবে ভাষা ও সাহিত্যচর্চার রকমফের সাম্প্রদায়িকতা বিশেষ করে জাতি বিদ্বেষ ছড়িয়েছিল। ‘রূপরেখা’ পত্রিকায় সাম্প্রদায়িকতা ও ভাষা সমস্যা প্রসঙ্গে আলতাফ চৌধুরির একটি পত্র পড়ে কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ১৭ বৈশাখ ১৩৪১ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির অকল্যাণ প্রসঙ্গে লেখেন,
“রূপরেখায় তােমার চিঠিখানি পড়ে বিশেষ, আনন্দ পেয়েছি। আজকাল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে আশ্রয় করে ভাষা ও সাহিত্যকে বিকৃত করার যে চেষ্টা চলছে তার মতাে বর্বরতা আর হতে পারে না।”
প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, কর্মজীবনের প্রথমে উইলিয়াম কেরী যখন দিনাজপুরে ছিলেন তখন স্থানীয় লােকদের ভাষা ছিল একটি নয়, দুটি। ব্রাহ্মণরা যে ভাষা ব্যবহার করে সেটি বাংলা আর অন্যরা যে ভাষায় কথা বলে সেটি হলাে বাংলা, হিন্দুস্থানী, ফারসি ইত্যাদির একটি মিশ্রণ। এই দ্বিতীয় ভাষাটি মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের। কিন্তু ওই দুই ভাষার ব্যবধান তখন সাম্প্রদায়িক চেহারা নেয়নি, সেটা নিল পরে, মুসলিম সমাজে যখন মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠল তখন। আবারও স্মরণ করা যাক যে, সাম্প্রদায়িকতা আসলে দুই দিকের দুই মধ্যবিত্তের একটি বৈষয়িক সংগ্রাম, যে সংগ্রামে তারা ধর্মকে ব্যবহার করেছে একটি সুবিধাজনক অস্ত্র হিসাবে। ফলে দুই পক্ষের মৌলবাদীরা চেষ্টা করেছে শব্দের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতে।
তবে এটা ঠিক যে, শব্দ নিজে নিজে কিন্তু সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠে না। কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায় কোনও শব্দকে যখন বিশেষ অর্থে বা অনুষঙ্গযুক্ত করে ব্যবহার করে, তখনই তা সাম্প্রদায়িক পরিচয় লাভ করে। শব্দের স্বরূপ, উদ্ভব, বিকাশ যেদিক থেকেই আলােচনা করা যাক, শব্দ সব সময় সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ। শব্দকে সম্প্রদায়ের রঙে। রাঙিয়ে তােলা হয় মাত্র। শব্দ হিন্দু বা মুসলমান কোনটাই হয় না, ঐতিহাসিক কারণে ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই তা ধর্মীয় চরিত্র পরিগ্রহ করে। কিন্তু ধর্মীয় রূপ না থাকলেও সব ভাষাতেই অনেক এমনকী বেশিরভাগ শব্দেরই একটি কৃষ্টিগত রূপ থাকে। যেমন ‘গােন্ত’, ‘আন্ডা’ ও ‘পানি’-র মধ্যে ইসলামত্ব নেই বটে তবে মুসলমানত্ব আছে।
সংস্কৃত থেকে জাত ভারতীয় অন্যান্য ভাষার মত বাংলা ভাষাতেও কথ্য স্তরে পানি শব্দ একসময়ে সার্বজনীনভাবে প্রচলিত ছিল। তাছাড়া এটাও বােধ হয় জানা যে, ‘জল’ যেমন সংস্কৃত উৎসের, তৎসম শব্দ ‘পানি’-ও তেমনি সংস্কৃত উৎসের, তবে তদভব। তা না জেনেই এক শ্রেণীর হিন্দু বাঙালি ‘পানি’-র উপর বিদ্বেষ নিয়ে বসে থাকেন। ‘যবন’ স্পর্শদোষে পানিকে যেন কুল হারাতে হল। কিন্তু অভিধানে যখন এই বিকৃত মানসিকতার পরিচয় পাই তখন দুঃখ হয় বৈকি! একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বেশীরভাগ হিন্দু অভিধানপ্রণেতার অভিধানেই জল শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ‘বারি’ ‘সলিল’ ইত্যাদি শব্দের দেখা পাওয়া গেলেও ‘পানি’ কথাটির দেখা পাওয়া যায় না বললেই চলে। এটা অচেতন নয়, সচেতন বর্জন—এটাই বিপদের কারণ। মুসলিম। শাসকরা চৌদ্দঘাটের পানি পান করে বাংলায় এসেছিলেন, তাই তাদের উত্তরসূরীরাও পানি দখল করলেন আর সেই দুঃখে হিন্দুরা পানি ছেড়ে জল ধরলেন।
‘পানি’ সংস্কৃত জাত হলেও সাধারণ মুসলমানের ওই শব্দটি ব্যবহারে আপত্তি নেই। কিন্তু সংস্কৃতজাত ‘জল’-এ যত আপত্তি। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে জলযুক্ত সকল শব্দকেই কাফেরের স্পর্শদোষে দুষ্ট মনে করা হত। ‘জলপানি’-র মত (ছাত্রবৃত্তি) স্মৃতিধন্য শব্দ ও ‘জলকুন্তল’-র মত মনমুগ্ধকর শব্দটি ছিল মৌলবাদীদের কাছে নাপাক’। জলখাবার তাে বলাই যাবে না। বলতে হবে ‘নাশতা’। সৈয়দ আলাওল যদিও ‘জলসত্র’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ময়মনসিং গীতিকায় আছে, ‘বাপের বাড়ীতে আছে গাে জলটুঙ্গীর ঘর’। এখন সম্ভবত পানিটুঙ্গীর ঘর বলে পড়তে হবে। পানিবসন্ত হলেও হিন্দুরা জলবসন্তই বলবে। যদিও ‘ঠান্ডা ঠান্ডা পানিফল’ তারা খায় বৈকি! ‘পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডাঙ্গায় উঠ না’—উভয় সম্প্রদায়ই ব্যবহার করে। সত্যেন্দ্রনাথের ‘চুপচুপ ওই ডুব দ্যায় পানকৌটি’ এখনও শ্রুতিদুষ্ট নয় কারও কাছেই। সাম্প্রদায়িক অনুমােদনের ফলে ঐতিহ্যলুপ্ত আর একটি শব্দ হল ‘আন্ডা। উভয়বঙ্গের অভিধানেই বলা হয়েছে ‘আন্ডা’ শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত ‘অন্ড’ থেকে। ডিম শব্দটির উদ্ভব সংস্কৃত ‘ডিম্ব’ হতে। অথচ উৎস একই হলেও ‘ডিম’ আর ‘আন্ডা’তে যেন দ্বন্দ্ব রয়ে গেছে।
আবার ধরুন কাকা, বাবা। বাংলা অভিধানে এদের উৎস খুঁজতে গেলে সমস্যায় পড়বেন। শব্দ দুটি তুর্কি। বাংলায় (গৌড়) তুর্কি শাসনকালে ঢুকেছিল। মজার কথা, বাঙালি মুসলিমরা তুর্কি কাকা নেননি, হিন্দি চাচা। নিয়েছিলেন। হিন্দির ‘চাচা’ আবার সংস্কৃতজ (সং- তাত < চাচ < চাচা। হিন্দুরা তুর্কি ‘কাকা’ নেন (অনেকের মতে কাকা ফারসি শব্দ)। বাঙালি হিন্দুরা ‘বাবা’ও নেন। অনেক বাঙালি হিন্দু জাত্যাভিমানবশত দাবি করে। থাকেন যে, ‘বাবা’ শব্দ সংস্কৃত ‘বপ্র’ বা ‘বপ্ত’ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। সংস্কৃত বপ্র > বপ্প > বাপ-এ পরিণত হয়েছে। বাঙালি মুসলিমরাই পিতাকে তা বলে থাকে। তাছাড়া মুসলিমরা আরবি ‘আবু’জাত অপভ্রংশ শব্দ ‘আব্বা’-ও নেন (পিতাকে বােঝাতে)। উল্লেখ্য, দাদা/দাদি ফারসি শব্দ। তবে শব্দ দুটির সঙ্গে তুর্কি-আফগান অভিযানের সম্ভবত কোনও সম্পর্ক নেই। এগুলাে পূর্ব থেকে প্রচলিত ইন্দো-ইরানীয় শব্দ মাত্র। সুনীতিকুমার চ্যাটার্জি লিখেছেন, তুর্কি-আফগান অভিযানের বহু আগে থেকে ভারতের বিভিন্ন ইন্দোইউরােপীয় ভাষায় বহু ফারসি শব্দ বিভিন্ন কারণে গৃহীত হয়েছে। পৃথকীকরণের তাগিদেই বাঙালি হিন্দু প্রয়ােগের ক্ষেত্রে শব্দের আকৃতির কিছু পরিমার্জন বা পরিবর্তন করে অথবা সামান্য ভিন্নার্থে শব্দগুলিকে গ্রহণ করে নিয়েছে। বাঙালি হিন্দুর ‘দাদু শব্দও ফারসি (ফারসি দাদা শব্দের আদরের সংপ্তি রূপ—যেমন মামা > মামু, কালা > কালু, কাকা > কাকু, দাদা > দাদু)। বাঙালি হিন্দুরা দাদুকে ঠাকুরদাও বলেন। এই ঠাকুর শব্দটিও তুর্কিজাত। তুর্কিতে Tagri মানে ঈশ্বর, দেবতা ইত্যাদি। তবে শব্দটি ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় অপভ্রংশে বা বিকৃত উচ্চারণে ঠাকুর ঠক্কর/থ্যাকারে ইত্যাদি হয়ে যায়। কোনও প্রাচীন প্রাক-মুসলিম যুগের সংস্কৃত গ্রন্থে ঠক্কর বা ঠাকুর শব্দ নেই। সেই সঙ্গে ‘বু’ শব্দ / ধ্বনি সংস্কৃত ভগ্নী শব্দের রূপান্তরিত রূপ। আদরে দ্বিত্ব হয়ে তা। ‘বুবু’ হয়েছে—বু > বুন > বােন > বহিন > ভইন > ভগিনী > ভগ্নী। কিন্তু বাঙালি হিন্দু এর প্রতিশব্দ হিসেবে যে শব্দটি ব্যবহার করে, সেই ‘দিদি’ শব্দটি ফারসি। এই বুবু/দিদির প্রতিশব্দ ‘আপাও কিন্তু বিদেশী শব্দ— তুর্কি, যা বাঙালি মুসলিমদের কেউ কেউ ব্যবহার করে। শব্দকোষকার হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নানা’ (মায়ের বাবা) শব্দকে দেশজ মুন্ডারী (অষ্ট্রিক) বলে উল্লেখ করেছেন। উত্তর ভারতের সংস্কৃতের সন্তান বলে চিহ্নিত সব ভাষা-ভাষী মানুষের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাঙালি মুসলিমরা মায়ের বাবাকে ‘নানা’-ই বলে। বাঙালি হিন্দুই এ বিষয়ে ব্যতিক্রমী।
আবার ফুপা/ফুপী (পিসা/পিসী সংস্কৃত) শব্দও দেশীয়। আর ‘জী’ শব্দও সংস্কৃত থেকে এসেছে। জী > আজ্জী > আজ্জ > আর্য। প্রবীণ, বয়স্ক, সম্মানীয় বা গুরুস্থানীয় ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শনে ‘জী’ শব্দের ব্যবহার, যেমন—নেহরুজী। এছাড়া সম্মােধনে সাড়া দিতেও ‘জী’ শব্দ ব্যবহার করা হয়। অপরদিকে বাঙালি হিন্দু ব্যতিক্রমধর্মী আজ্ঞে (সং) বলে সাড়া দেয়। তাছাড়া বাপের সাথে ‘জী’ যােগ করলে বাপজী মুসলিম আর বাপুজী হিন্দু-মুসলিম সকলের বাবা জাতির জনক। বাবাজী কিন্তু জাতের বালাই ঘুচিয়ে হিন্দু-মুসলিম সকলের জামাই। আবার জ্যেষ্ঠ মানে বড় আর ভ্রাতা মানে ভাই। কেউ যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা না বলে বড় ভাই বলেন তা হলে তিনি মুসলিম। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দাদা হলেন কোন আইনে তা জানা নেই।
অনেকে আবার বলেন, বাঙালি মুসলমানেরা যদি তাদের সন্তান-সন্ততির পুরােপুরি বাংলা নাম রাখেন, তাহলে হয়তাে হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে নৈকট্যবােধ আরও বাড়বে। এপার বাংলা তথা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলমানের মুখের ভাষা সম্পর্কে এখনও অনেকের মনে ভুল ধারণা রয়েছে। তারা ভেবে থাকেন, বাঙালি মুসলিমদের মুখে আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ এত বেশী ব্যবহৃত হয় যে, বাংলা ভাষার সেখানে আর ঠাঁই হয় না। বলা বাহুল্য, তারা বাংলা ভাষা বলতে বাংলা সাহিত্যের ভাষা তথা লেখ্য বাংলা ভাষাকেই স্বীকৃতি দিয়ে। থাকেন। বাংলা শব্দভান্ডারে অসংখ্য আঞ্চলিক ও গােষ্ঠীগত ডায়ালেক্ট বা উপভাষার সম্পদ যে বিশাল ও বিচিত্র, সে-সম্পর্কে তারা তেমন সচেতন বলে মনে হয় না। এই সব উপভাষাই সুপ্ৰযুক্ত ও পরিমার্জিত হয়ে। লেখ্য শব্দভান্ডারের সমৃদ্ধি সাধন করে। অথচ তারা কিছু না জেনে, জানার চেষ্টা না করে, বাঙালি মুসলিমের পরিভাষা সমস্যা, আরও স্পষ্ট করে মুসলমানি’ শব্দ নিয়ে যথেষ্ট ভাবিত এবং এ নিয়ে তারা উশ্মা প্রকাশও করেন। শুধু তাই নয়, এমন শব্দের ব্যবহারকে তারা ‘অনৈক্য’ ও ‘বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রতীক’ হিসেবেই চিহ্নিত করেন।
বাংলা ভাষায় অন্য বহু ভাষার শব্দ মিশেছে, আজও ব্যবহৃত হচ্ছে—সে সবই বাংলা ভাষা। এত কথা বলতে হল বড় দুঃখে। সাধারণ মানুষের দোষ দিয়ে লাভ নেই। দোষ ছিল অসাধারণ মানুষ অথাৎ শিক্ষিত উচু গদিওয়ালা চেয়ারে বসা মানুষদের। নেই কাজ তাে খই ভাজ-এর মত গােটা কতক শব্দের জাত বিচার করে এবং শব্দ দিয়ে জাতের বিচার করে ওরা শিক্ষা ও জগটাকে কুস্তির আখড়ায় পরিণত করেছিলেন। শব্দ দূষণ হলে Polution Board আছে, কিন্তু শব্দ (Word) নিয়ে পরিবেশ দূষিত হলে তার সমাধান কী হবে? তবে যারা হিন্দুয়ানি বাংলা আর মুসলমানী বাংলা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন তারা ঠিক কখন কোনটি রাখবেন, কোনটি ছাড়বেন, না দুটোই রাখবেন। কেননা বাংলা সাহিত্যের মূলস্রোতে চলমান কোনও শব্দকে মুসলমানী শব্দ, হিন্দুয়ানি শব্দ, খ্রিষ্টান শব্দ বলে চিহ্নিত করার মৌলবাদী ভাবনা যেন কারও মনে স্থান না পায়।
অনেকে আবার বলেন, বাঙালি মুসলমানেরা যদি তাদের সন্তান-সন্ততির পুরােপুরি বাংলা নাম রাখেন, তাহলে হয়তাে হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে নৈকট্যবােধ আরও বাড়বে। বিষয়টিতে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে ‘বাংলা নাম’ আর ‘না-বাংলা নাম’ নিয়ে। তাছাড়া বাংলা নাম-ই বা কাকে বলে? প্রথমেই বলি, সারা ভারতের মত বাংলা অঞ্চলেও নামকরণের ক্ষেত্রে কোনও সমরূপ নিয়মকানুন নেই। দয়ানন্দ সরস্বতী, রামমােহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বা শ্যামাপ্রসাদ মুখােপাধ্যায় ইত্যাদি নাম যদি ভারতীয় হয় তবে থিরুমল আপ্পা, মুরাসলি মারান, গেগং আপাং, পি.এ. সাংমা তেনজিং নােরগে, তিলকা মুর্মু, বিরসা মুন্ডা, জর্জ ফার্নান্ডেজ, আবুল কামাল আজাদ, মীর নিসার আলি, রফিক মন্ডল কিংবা হুমায়ুন কবীর কোন অর্থে অভারতীয় হবেন? অথচ উক্ত নামধারী ব্যক্তিরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বনামধন্য এবং বর্তমানের সংজ্ঞায় ভারতীয় (কেউ কেউ এদের মধ্যে বাঙালিও বটে)।

বস্তুত যুগ যুগ ধরে বাইরের উৎস থেকে যে সমস্ত নৃ-গােষ্ঠী ভারতবর্ষে এসে এদেশকে নিজেদের করে নিয়েছে, তারা তাদের সঙ্গে বয়ে নিয়ে আসা ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির কিছু না কিছু অবশেষ নিজের নাম ও পদবির মধ্যে সংরক্ষিত করেছে অথবা এ বিষয়ে অপরকে প্রভাবিত করেছে কিংবা নিজেরাও প্রভাবিত হয়েছে। এই প্রভাবের বিষয়ে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। লালকৃষ্ণ আদবানি নামটির আদবানি পদবিটি আরবি শব্দ ‘আদওয়ান’ থেকে জাত। তিনি যে পােশাক পরেন তা তুর্কি-পাঠান-মুঘলদের ব্যবহৃত কুর্তা কামিজেরই সংস্কার করা রূপ মাত্র। যাক সে কথা। একমাত্র অস্ট্রিক বলে বর্তমানে চিহিত ‘কোল মুন্ডারি’ মানুষেরাই ভারতের আদিম অধিবাসী। আর্য, দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয় ইত্যাদি জাতিসত্তা অথবা নৃ-গােষ্ঠীর মানুষরা সব বহিরাগত। সুতরাং নামকরণের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য থাকবে এটাই স্বাভাবিক। বাঙালির নামকরণের বিষয়ে সেই একই কথা।
আমরা বাংলা ভাষায় আরবি, ফারসি, পর্তুগিজ ও ইংরেজি সহ বিভিন্ন ভাষার অনেক শব্দ উদারভাবে আত্মস্থ করেছি। কিন্তু ছেলেমেয়েদের নাম রাখার ব্যাপারে এই উদারতা দেখাতে পারি না। হিন্দুরা তাঁদের ঐতিহ্য অনুসরণ করে সংস্কৃত ভাষার অনুসারী শব্দ থেকেই ছেলেমেয়েদের নামকরণ করে থাকেন। মুসলমানেরা তেমনি আরবি, ফারসি শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন। হিন্দুরা মেরি, ডলি, ববি, জলি, কলিন, রবিন, পিটার প্রভৃতি নাম রাখতে দ্বিধা না করলেও মেহেরউন্নিসা, ফয়েজউন্নিসা, ফাতেমা বা বাহারউদ্দিন, ওসমান নাম রাখেন না। তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের এমন নাম রাখেন যে শব্দগুলি প্রধানত সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে। হিন্দু শাস্ত্র ও পুরাণের পাত্র-পাত্রীদের নাম অনুযায়ীও নামকরণ করে থাকেন তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের। একে
কী বলা যাবে? ঐতিহ্য না সংস্কার। তবে সব ক্ষেত্রে যে গোঁড়ামি আছে তা নয়। মেয়ের নাম নূরজাহান ও ছেলের নাম বাদশা অনেকেই রাখেন। মুসলমান পরিবারের ছেলেমেয়েদের আটপৌরে নাম মিনু, লীনা, জ্যোৎস্না, শান্ত, সান্ত্বনা, পার্থ, আশিস প্রভৃতি অনেকেই রেখে থাকেন। তবে পােশাকি নাম অবশ্যই আরবি, ফারসি শব্দ থেকে নির্বাচিত করা হয়। এরও নানা সামাজিক বা ধর্মীয় কারণ আছে নিশ্চয়ই। বাংলাদেশে মুসলমানদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে মিশ্ৰনাম নেওয়ার ও দেওয়ার প্রবণতা।
হিন্দুরা ‘দিল, ‘দরিয়া’, ‘দিল দরিয়া প্রভৃতি শব্দের মত অনেক শব্দ বাংলা ভাষায় অকপটে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ছেলের নাম ‘দিলদার’ রাখতে পারেননি। ‘দিলদার হােসেন’ যেমন মানায় ‘দিলদার ভট্টাচার্য’ বা ‘দিলদার চক্রবর্তী’ কি শুনতে কানে বাজে না? (‘সেই দিলও নাই, দিল্লীও নাই’—রবীন্দ্রনাথ) সময় তাে লাগবেই। প্রসঙ্গ ত, আর একটা কথা এসে গেল। হিন্দুদের মধ্যে বর্ণ পরিচিতির নিদর্শন হচ্ছে , ‘পদবি’। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও অন্যদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কতগুলি পদবি ব্যবহৃত হয়। আজও কেউ এগুলিকে ছাড়তে পারেননি। মুসলমানদের মধ্যেও রয়েছে নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ‘শেখ’ সৈয়দ ইত্যাদির ব্যবহার। উভয় সম্প্রদায়ের পােশাকের মধ্যে যে তফাৎ ছিল, তা অনেকটাই দূর হয়েছে। স্বাধীনতার আগে গোঁড়া হিন্দু পরিবারে লুঙ্গি-পাজামার ব্যবহার ছিল না। বললেই চলে। খাদ্যাভ্যাসের মধ্যেও কিছু কিছু পার্থক্য ছিল, এখন অনেকটাই পরিবর্তন ঘটছে। অনভ্যাস দুর করতে বা সংস্কার থেকে মুক্ত হতে সময় তাে লাগবে।
ভাষা বা শব্দ গ্রহণ বর্জনের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। তবে যারা বাংলা নাম বলতে রাম, দশরথ, সীতা, দুর্গা ইত্যাদি বােঝেন তাদের জেনে রাখা ভাল যে দশরথ, রাম, সীতাদের আবির্ভাব খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ বছর প্রায়। দুগার আর্বিভাব তারও আগে। তখন বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়নি। সে নামগুলি যদি বাংলা নাম বলে ধরে নেওয়া হয়, তবে বাংলা ভাষা আন্দোলনে শহিদ হয়ে যে সালাম, বরকত, জব্বার, রফিক বাংলা ভাষাকে আন্তজাতিক স্বীকৃতি দান করলেন, তাদের নামগুলি বাংলা নাম হবে না কোন যুক্তিতে? সমালােচক হয়তাে তপন, পবন, গায়ত্রী ইত্যাদি নামকেই বাংলা নাম বলতে চাইবেন। তাই যদি হয়, তাহলে তপন (সূর্য), পবন (বায়ু), গায়ত্রী এগুলি হিন্দু দেব দেবীর নাম। বাংলা নাম হতে পারে না এগুলিও।
আসলে বাংলা নাম বলে আলাদা কিছু নেই। তাই স্বাভাবিকভাবেই দশরথ, রাম, সীতা তপন, পবন, গায়ত্রী ইত্যাদি যেমন সংস্কৃত শব্দ হলেও বাংলা নাম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, ঠিক তেমনি সালাম, বরকত, জব্বার, রফিক ইত্যাদি আরবি শব্দ হলেও তা বাংলা হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, নাম যে শব্দ থেকেই নেওয়া হােক না কেন, বাংলা বর্ণমালায় লিপিবদ্ধ হলেই তাকে বাংলা নাম বলা উচিত বলে মনে করি। তাছাড়া নাম না হয় বাংলা শব্দে রাখা হল, কিন্তু পদবি? এই পদবির বাছবিচার দিয়েই তাে আমরা মানুষে-মানুষে বিভেদের প্রাচীর তুলে রেখেছি। খবরের কাগজ খুলে পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপন দেখুন, জাতপাতের কী বিশ্রী আস্ফালন আর নির্লজ্জ আত্মপ্রচার! এই অবস্থায় স্কুলে, কলেজে, চাকরির ক্ষেত্রে বাংলা নাম চাপা দিতে পারবে কি ধর্মীয় বিভেদের কাঁটাকে? ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী, বেরা, বসু, গাঙ্গুলী, মুখার্জি, চ্যাটার্জি, শেখ, সৈয়দদের অযুত বিভেদের নােংরা আস্ফালন বন্ধ হবে কি? সুতরাং আসুন, ভেবে দেখি, রাম, রাবণ, অর্জুন, অশােক, চাণক্য, কালিদাস, হজরত মােহাম্মদ (সঃ), হজরত ইব্রাহিম (আঃ)—এদের পদবি কী? যদি অতীত ভারতে পদবি না-ই থাকে কিংবা ইসলাম ধর্মের নবী বা রসুলরা পদবি ব্যবহার না করে থাকেন, তবে আমরা পদবি বর্জন করি না কেন?
শেষে বলি, বাংলা নাম গ্রহণ বা পদবি বর্জন করলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তা কিন্তু নয়। প্রয়ােজন মুক্তচিন্তাভাবনা। বদ্ধ ধারণা থেকে মুক্ত হতে পারলে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে অনেকে অনেকের কাছাকাছি আসতে সক্ষম হবেন। কিন্তু বর্তমানে তাে বিচ্ছিন্নতা বাড়ানাের সর্বগ্রাসী প্রয়াস চলছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অবস্থান ও অধিকার সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা, উগ্র-বিদ্বেষ ও হিংস্র মনােভাবের প্রসার ঘটানাের যে অপচেষ্টা চলছে। এবং মুক্তচিন্তার পরিবশেকে ধ্বংস করার যে অপচেষ্টা চলছে, তাকে রােধ করতে না পারলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের কাছাকাছি আসার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত।
‘নবজাগরণ’ অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপ্লিকেশনটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।
![]()

 নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা
নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা