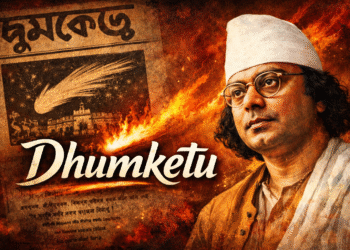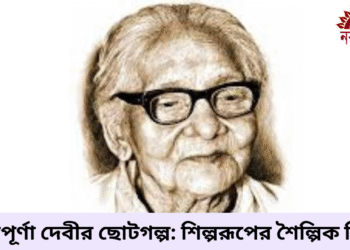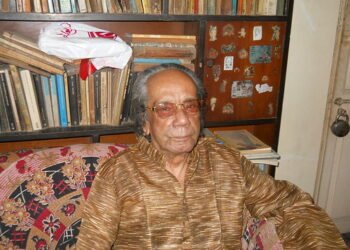লিখেছেনঃ মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম
নজরুল ইসলামকে মূলত কবি, গীতিকার ও সংগীতস্রষ্টা হিসেবেই আমরা চিনি ও শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাঁর রচনার বিশাল ভাণ্ডারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধও স্থান করে নিয়েছে। যদিও তিনি পেশাদার প্রাবন্ধিক ছিলেন না, তবু দেশ, সমাজ ও সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির তাগিদে তাঁকে প্রবন্ধ রচনায় আত্মনিয়োগ করতে হয়েছিল। তাঁর প্রবন্ধ রচনার পেছনে কোনো পূর্বপরিকল্পিত সাহিত্যিক প্রয়াসের তুলনায় ছিল তৎকালীন সময়ের বাস্তব চাহিদা ও সাংবাদিকতার অনিবার্য দায়বদ্ধতা। এ কারণে নজরুলের প্রবন্ধসংখ্যা খুব বেশি নয়, কিন্তু প্রতিটি রচনাই সময়ের এক এক নিখুঁত প্রতিচ্ছবি।
প্রধানত ‘নবযুগ’ ও ‘ধূমকেতু’ নামক দুটি পত্রিকায় সম্পাদকীয় দায়িত্ব পালনের সুবাদে তিনি নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ লিখতেন। সে সময় সংবাদপত্রের রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্তব্য পালনের অংশ হিসেবে নানা সমসাময়িক ইস্যুতে কলম ধরতে বাধ্য হয়েছিলেন নজরুল। সেই সব সম্পাদকীয় ও প্রাসঙ্গিক রচনাগুলিকেই পরবর্তীকালে সংকলিত করা হয়েছে তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থগুলিতে। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাঁচটি গ্রন্থ হল—
১) যুগবাণী (কার্তিক, ১৩২৯)
২) রাজবন্দীর জবানবন্দী (মাঘ, ১৩২৯)
৩) রুদ্রমঙ্গল (১৩৩৪)
৪) দুর্দিনের যাত্রী (১৩৩৩)
৫) ধূমকেতু (অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭)
এই রচনাগুলির মধ্যে একাধারে নজরুলের প্রতিবাদী চেতনা, সমাজবীক্ষা, রাজনৈতিক দ্রোহ ও আত্মার উত্তাপ অনুভব করা যায়। তাঁর ভাষা সাহসী, প্রত্যয়দীপ্ত এবং আবেগে উচ্ছল। বিশেষ করে, এসব প্রবন্ধে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত ভাবাবেগ, অকপট বক্তব্য ও দ্রোহী মনোভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনানুভব এই রচনাগুলিকে একটি স্বতন্ত্র মাত্রা প্রদান করেছে—যা নিছক সাংবাদিকতার গণ্ডি ছাড়িয়ে একান্ত সাহিত্যিক অবস্থান তৈরি করেছে।
তবে নজরুলের প্রবন্ধে কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে, যা পর্যালোচকের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। একদিকে তাঁর ভাষা আবেগে পূর্ণ, কাব্যিক রূপক, উৎপ্রেক্ষা ও উপমায় সমৃদ্ধ হলেও—অন্যদিকে প্রবন্ধের গঠনতাত্ত্বিক শৃঙ্খলা, ভাবনাগত গভীরতা এবং যুক্তিবাদী মননশীলতার কিছুটা অভাব পরিলক্ষিত হয়। অনেক সময় অতিরিক্ত আবেগ ও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় রচিত হওয়ায় এই রচনাগুলির বিন্যাসে অনিয়ম ও বিক্ষিপ্ততা লক্ষ্য করা যায়। সেই সাথে সাংবাদিকতার প্রয়োজনে তাড়াহুড়ো করে লেখা হওয়ায় কোথাও কোথাও রচনার যত্নে ঘাটতি থেকেছে। এই রচনাগুলিতে মাঝে মাঝেই অতিরিক্ত প্রচারমূলক সুর লক্ষ্য করা যায়, যা সাহিত্যিক গাম্ভীর্যকে খানিকটা হ্রাস করে।
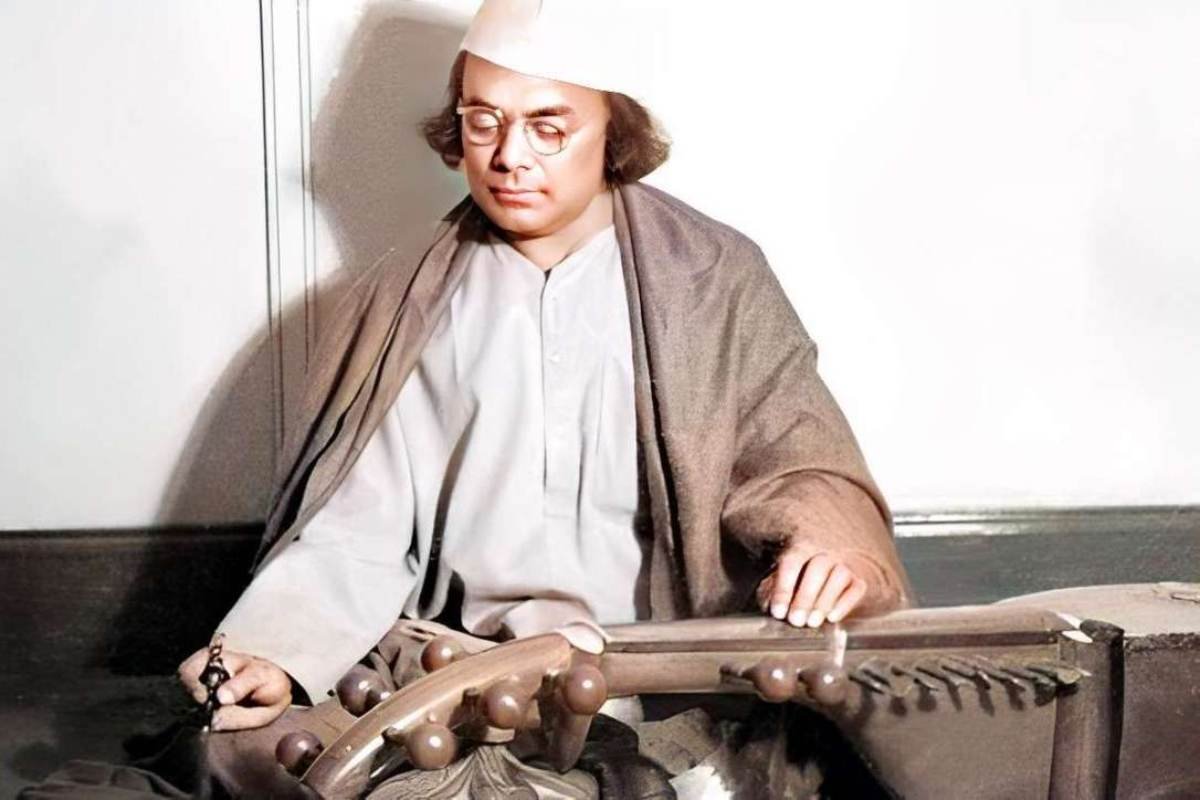
তবু এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও নজরুলের প্রবন্ধসমূহ আজও প্রাসঙ্গিক ও পাঠযোগ্য। তাঁর ভাষার উদ্দীপনা, কাব্যিক গঠন ও রোমান্টিক মানবিকতা প্রবন্ধগুলিকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। এই বিষয়ে বিশিষ্ট গবেষক ড. সশীলকুমার গুপ্ত এক গভীর পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন—
“নজরুলের রচনার সবচেয়ে বড় ত্রুটি মননশীলতার স্বল্পতা ও শিল্পসৌষ্ঠব সম্পর্কে আবেগ প্রাবল্যজনিত উদাসীনতা ও অসতর্কতা। তাঁর রচনার শ্রেষ্ঠগুণ যৌবনধর্ম, অন্তর্মুখী ভাববেগের অকৃত্রিমতা ও কাব্যধর্মী ওজস্বিতা। কোনো কোনো রচনায় তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে রোমান্টিক ভাবাদর্শের বিবাহ বন্ধনে অসামান্য শক্তি ও উদ্দীপনা সঞ্চারিত। প্রধানত সাংবাদিকতার উদ্দেশ্যে রচিত হলেও নজরুলের কতকগুলি প্রবন্ধ যে সাময়িকতার গন্ডি পেরিয়ে আজও টিকে আছে তাতে অবশ্যই তাদের সাহিত্যগুণের অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া যায়।”
এই মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, নজরুলের প্রবন্ধসমূহ কেবল সাংবাদিক কর্তব্য পালনের দলিল নয়, বরং তাঁর বিপ্লবী আত্মা, কাব্যিক আবেগ ও সময়চেতনার দুর্লভ সমাহার। সাহিত্যিক কাঠামোর বাইরে দাঁড়িয়ে থেকেও নজরুলের প্রবন্ধসমূহ বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে এক আলাদা বৈশিষ্ট্য বহন করে। সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, জাতীয়তা ও মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে যে সরল, দৃপ্ত এবং নিঃসংকোচ উচ্চারণ নজরুল করেছেন—তা বাংলা সাহিত্যে এক অনবদ্য সংযোজন।
নজরুলের প্রবন্ধরচনায় যে সাহসী ভাষাভঙ্গি ও বলিষ্ঠ উচ্চারণের পরিচয় মেলে, তা নিঃসন্দেহে তার বিপ্লবী আত্মার প্রতিফলন। তবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিংবা স্বামী বিবেকানন্দের গদ্যভাষায় যে অন্তর্মুখী চিন্তাশীলতার সূক্ষ্ম অথচ দৃঢ় বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে—সে রকম এক আত্মিক পুরুষার্থের অনুরণন নজরুলের গদ্যে সেইরূপ ব্যঞ্জনাময়ভাবে ধরা পড়ে না। তবুও নজরুলের প্রবন্ধে যে তীব্র ব্যক্তিমানস, জীবনের গভীরতর উপলব্ধি ও সমাজ বিশ্লেষণের প্রখরতা রয়েছে, তা বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে একটি অনন্য ব্যতিক্রমী উজ্জ্বলতা তৈরি করেছে। তার প্রতিটি রচনাই যেন বাস্তবের কোলাহলে গঠিত এক সংবেদী হৃদয়ের ক্ষুধার্ত উচ্চারণ।
বাংলা গদ্যের ইতিহাসে প্রবন্ধ সাহিত্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। উনিশ শতকের শুরুর দিকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এবং শ্রীরামপুর মিশনারিদের হাত ধরে বাংলা গদ্যচর্চার যে সূচনা, তা ছিল মূলত ধর্মীয়, নীতিশিক্ষামূলক ও অনুবাদভিত্তিক। কিন্তু এই প্রাথমিক পর্যায়েই গদ্যের ভিত রচনার মাধ্যমে তাঁরা যে বীজ বপন করেন, তা পরবর্তীকালে সমাজ সংস্কারক রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর প্রমুখের হাতে এক নতুন চেহারা পায়। তাঁদের চিন্তাভাবনার ধারক ও বাহক হয়ে ওঠে সাময়িক পত্রিকাগুলি, যার মাধ্যমে বাংলা গদ্যের একটি সাহিত্যিক রূপের পরিপক্বতা ঘটে। এই রূপই পরিণত সৌন্দর্যে প্রকাশ পায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখায়, যিনি বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে এক বিশিষ্ট রূপ ও মর্যাদা প্রদান করেন।
ঊনিশ শতকের বাঙালি সমাজ ছিল দ্বৈত স্রোতের প্রবাহ। একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে উদ্ভূত যুক্তিবাদ, ধর্মসংশোধন ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আহ্বান; অন্যদিকে ছিল ঐতিহ্যপন্থী বিশ্বাস ও সমাজব্যবস্থার প্রতিস্পর্ধা। এই দ্বন্দ্বময় রেনেসাঁ যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগুচ্ছ আত্মার উল্লাসের এক বুদ্ধিময় বাচনিক রূপে উদ্ভাসিত হয়। ১৮৭২ সালে বঙ্গদর্শন পত্রিকার সূচনার মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে প্রবেশ করেন এবং এই পত্রিকাই হয়ে ওঠে তাঁর চিন্তাভাবনার প্রধান বাহন। বঙ্গদর্শন-এর মাধ্যমে তিনি ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সমালোচনা প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করে বাংলা সাহিত্যে এক নব দিগন্তের সূচনা করেন।
বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থগুলির মধ্যে আছে—
লোকরহস্য (১৮৭৪),
বিজ্ঞানরহস্য (১৮৭৫),
কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫),
বিবিধ সমালোচনা (১৮৭৬),
সাম্য (১৮৭৯),
প্রবন্ধপুস্তক (১৮৭৯),
কৃষ্ণচরিত্র (১৮৮৬),
বিবিধ প্রবন্ধ (২য় ভাগ, ১৮৯২),
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১২৯৫ বঙ্গাব্দ),
এবং মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত (১৮৮৪)।
এই রচনাগুলির মধ্যে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র শুধু প্রবন্ধকার হিসেবেই নয়, এক জন বুদ্ধিজীবী সমাজসচেতন চিন্তাবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। উইলিয়াম কেরি, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগরের হাতে যে প্রবন্ধ সাহিত্য ছিল এক প্রাথমিক বিকাশে—বঙ্কিমচন্দ্র তাকে দান করেন পূর্ণ যৌবনের বলিষ্ঠতা ও সাহিত্যিক মাধুর্য।
লোকরহস্য একটি ব্যঙ্গাত্মক সমাজ বিশ্লেষণ—যেখানে তিনি সামাজিক আচার-আচরণ, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার নিয়ে কটাক্ষ করেছেন। কমলাকান্তের দপ্তর নামক রচনায় রস ও ব্যঙ্গ একসূত্রে গাঁথা। এখানে প্রভাব দেখা যায় ডি. কুইন্সির “Confessions of an English Opium Eater”-এর। কমলাকান্ত চরিত্রটির মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন সমাজের বাস্তব জীবন ও সমস্যা-সংকটকে হাস্যরসের ছায়ায় উপস্থাপন করেছেন। সেই সঙ্গে ব্যঙ্গচিত্রের অন্তরালে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর অন্তর্মুখী সমাজ-দৃষ্টিভঙ্গি।
বিশেষত সাম্য এবং কমলাকান্তের দপ্তর প্রবন্ধে তিনি সমকালীন অর্থনৈতিক কাঠামোর এক তীক্ষ্ণ সমালোচনা উপস্থাপন করেন। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কৃষকের শ্রমের মূল্যহীনতা, ধনসম্পদের ওপর মহাজন ও জমিদার শ্রেণির একচেটিয়া দখল এবং শ্রমিকের প্রতি সমাজের অবহেলা—এই সব সমস্যার গভীর চিত্র তুলে ধরেছেন তিনি। সেখানে তিনি লিখেছেন, রাজা, জমিদার, মহাজন সকলেই কৃষকের উৎপাদিত ধন ভোগ করে, কিন্তু কৃষক নিজে কিছুই পায় না। এই যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রতি তাঁর প্রতিবাদ—তা পরবর্তীকালে কাজী নজরুল ইসলামের প্রবন্ধেও অনুরণিত হয়।
নজরুলের প্রবন্ধে যেমন রাজনৈতিক অন্যায় ও সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সরব এক দ্রোহী কণ্ঠস্বর শোনা যায়, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাতেও সমাজ ও অর্থনীতির মৌলিক সংকট নিয়ে গভীর উদ্বেগ লক্ষ্য করা যায়। যদিও তাঁদের ভাষাশৈলী ও রচনাকৌশল পৃথক, তবু অভিন্ন হয়ে ওঠে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির মূল সুর—বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রত্যয়। এই মিল থেকেই বোঝা যায়, প্রবন্ধসাহিত্যের দুই ভিন্ন ধারার প্রতিনিধিত্ব করলেও বঙ্কিমচন্দ্র ও নজরুল এক গভীর মানবিক চেতনায় পরস্পরসম্পর্কিত।
এভাবেই বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হয়ে উঠেছেন তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও ভাষার শৈল্পিক ব্যঞ্জনার এক স্বর্ণময় নির্মাতা, আর নজরুল ইসলাম হয়েছেন বাস্তব জীবনের কণ্টকাকীর্ণ পথচলার বিদ্রোহী ভাষ্যকার।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধসাহিত্য শুধু বিষয়বস্তুর দিক থেকেই নয়, গঠনশৈলী ও রচনাভঙ্গিতেও এক বিশেষ পরিণতির পরিচায়ক। তাঁর প্রবন্ধসমগ্র মূলত দুইটি স্বতন্ত্র ধারায় বিভক্ত—(ক) ব্যক্তিধর্মী রচনা এবং (খ) বস্তুধর্মী রচনা। ব্যক্তিধর্মী রচনায় তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও দর্শন উঠে এসেছে আন্তরিক ভাষায়; অপরদিকে বস্তুধর্মী রচনায় দেখা যায় সমাজ, ধর্ম, ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতির যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণ ও মননশীলতা। এই দুই ধারার মেলবন্ধনেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধসাহিত্য হয়ে উঠেছে উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের অন্যতম দিকপাল।
বঙ্কিমচন্দ্র ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার মাধ্যমে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছিলেন, যার দ্বারা বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিলেন তাঁর বিশিষ্ট শিষ্য ও সহযাত্রী অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ মনীষীবৃন্দ। তাঁরা প্রত্যেকেই বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি, রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য নিয়ে।
অক্ষয়চন্দ্র সরকার ছিলেন এক গভীর সমাজবীক্ষণকারী চিন্তক। তাঁর প্রবন্ধে সমাজ ও সংস্কৃতির নানা অনিয়ম ও সংকট নিয়ে ছিল স্পষ্ট উচ্চারণ। উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির মধ্যে রয়েছে— ‘সমাজসমালোচনা’ (১৮৭৪), ‘আলোচনা’ (১৮৮২) এবং ‘সনাতনী’ (১৯১১)। এই গ্রন্থসমূহে তিনি ধর্মীয় কুসংস্কার, সামাজিক বৈষম্য এবং নৈতিক অবক্ষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও যুক্তিবাদী ভাষায় মত প্রকাশ করেছেন।
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ইতিহাস ও সমাজচিন্তায় গভীর আগ্রহী ছিলেন। তাঁর রচনাগুলি মূলত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নির্মিত হলেও, সমকালীন বাস্তবতাও সেখানে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ সংকলন— ‘বাঙ্গলার ইতিহাস’ এবং ‘নানা প্রবন্ধ’ (১৮৮৫)। এই রচনাগুলিতে বাংলা জাতির আত্মপরিচয়, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে তাঁর গভীর অনুসন্ধানী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।
চন্দ্রনাথ বসু ছিলেন এক গম্ভীর মনীষা, যিনি নান্দনিকতার চেয়ে নৈতিক দর্শনের প্রাধান্য বেশি দিয়েছেন প্রবন্ধরচনায়। তাঁর রচনায় বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ ও সমাজনৈতিক মূল্যবোধের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার লক্ষণীয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল— ‘শকুন্তলা তত্ত্ব’ (১৮৮১), ‘ত্রিধারা’ (১৮৯১), ‘হিন্দুত্ব’ (১৮৯২), ‘বাঙালী সাহিত্যে প্রকৃতি’ (১৮৯৯), এবং ‘সাবিত্রী তত্ত্ব’ (১৯০০)। এই প্রবন্ধগুলিতে নীতিবোধ ও জাতিসত্তার প্রশ্নে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে, যার ফলে সেগুলি সমসাময়িককালে সুপরিচিতি অর্জন করে।
কালীপ্রসন্ন ঘোষ, যিনি ঢাকার ‘বান্ধব’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, ছিলেন রচনাশৈলীতে কাব্যময়তা ও ভাবগম্ভীরতা মেশানো এক ব্যতিক্রমধর্মী প্রবন্ধকার। তাঁর গদ্যরীতিতে দর্শন, অনুভব ও শিল্পের এক সূক্ষ্ম সমন্বয় দেখা যায়, যা তাঁকে বাংলা সাহিত্যে ‘কার্লাইল’ উপাধিতে ভূষিত করে। তাঁর বিশিষ্ট প্রবন্ধগুলির মধ্যে অন্যতম— ‘প্রভাতচিন্তা’ (১৮৭৭), ‘ভ্রান্তিবিনোদ’ (১৮৮১), ‘নিভৃতচিন্তা’ (১৮৮৩), এবং ‘নিশীথচিন্তা’ (১৮৯৬)। এই রচনাগুলিতে গভীর অন্তর্মুখী ভাবনার পাশাপাশি কবিত্বময় ভাষার নিপুণ ব্যবহারের ফলে পাঠক এক অনন্য পাঠানুভব লাভ করেন।
কেশবচন্দ্র সেন সমাজ সংস্কার ও ব্রাহ্ম আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসেবে পরিচিত হলেও প্রবন্ধ সাহিত্যে তাঁর অবদানও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁর রচনাগুলি ধর্মীয় চিন্তন, সামাজিক আহ্বান ও আদর্শের অনুরণনে পূর্ণ। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলির মধ্যে রয়েছে— ‘সুলভ সমাচার’ (১৮৭০), ‘নববিধান’ (১৮৮০), ‘বালকবন্ধু’ (১৮৭৮), এবং ‘জীবনবেদ’ (১৮৮৪)। এই প্রবন্ধগুলিতে তিনি সমাজকে উন্নত করার এক স্বপ্ন ও নৈতিকতাবাদী ভাবনার বীজ রোপণ করেছিলেন।
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়-এর প্রবন্ধরচনার ক্ষেত্রেও সাহিত্যিক গভীরতা ও বিশ্লেষণাত্মক মনোভঙ্গি ছিল লক্ষণীয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল— ‘মসলা বাঁধা কাগজ’ (১৮৭২–৭৩), ‘সারস্বতকুঞ্জ’ (১৮৮৫), এবং ‘স্ত্রী চরিত্র’ (১৮৯০)। বিশেষত নারীর সামাজিক অবস্থান ও চারিত্রিক মূল্যায়ন নিয়ে তাঁর ‘স্ত্রী চরিত্র’ প্রবন্ধটি সে সময়ে যথেষ্ট আলোচিত ও প্রভাবশালী হয়ে ওঠে।
এইভাবে দেখা যায়, বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্যগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছিল, তারা প্রত্যেকে নিজস্ব রচনাশৈলী, দৃষ্টিভঙ্গি ও বিষয়নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে এক শক্তিশালী ভিত্তি নির্মাণ করেছিলেন। তাঁদের প্রবন্ধসমূহে যেমন ছিল গভীর চিন্তাভাবনা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, তেমনি ছিল ভাষার শৈল্পিকতা ও আবেগঘনতা। এই রচনাগুলি বাংলা সাহিত্যের রেনেসাঁ যুগের বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হিসেবে আজও মূল্যবান।
স্বামী বিবেকানন্দকে শুধু একজন ধর্মপ্রচারক হিসেবে চিহ্নিত করলে তাঁর কৃতিত্বকে ছোট করে দেখা হয়। তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক, সমাজচিন্তক, দেশনায়ক ও গদ্যসাহিত্যের এক বিশিষ্ট প্রতিভা। তাঁর প্রবন্ধসমূহ বাংলা গদ্যসাহিত্যে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে, বিশেষত চিন্তাশীলতা, ভাষার আবেগ এবং জাতীয় চেতনার এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণে। চলিত বাংলার সংলাপমুখর গদ্যরীতিকে আশ্রয় করে তিনি গড়ে তুলেছেন এমন এক প্রবন্ধভাষা, যা যুক্তি, আবেগ ও আদর্শের নিপুণ সমন্বয়ে পাঠকের চিন্তা ও চেতনাকে আলোড়িত করে।
‘পরিব্রাজক’, ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’, ‘ভাববার কথা’ ও ‘বর্তমান ভারত’—এই চারটি গদ্যগ্রন্থ বিবেকানন্দকে একজন মননশীল প্রাবন্ধিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়। এ সকল রচনা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল উদ্বোধন পত্রিকার প্রথম থেকে চতুর্থ বর্ষ পর্যন্ত পর্বে। প্রবন্ধগুলি যেমন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সমাজ বিশ্লেষণ দ্বারা সমৃদ্ধ, তেমনি তাত্ত্বিক গভীরতা, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও জাতীয় আত্মসচেতনার মেলবন্ধনে পরিপূর্ণ।
স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারি, কলকাতার সিমুলিয়া অঞ্চলে। তাঁর পৈতৃক নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি রামমোহন রায় প্রবর্তিত বেদান্ত দর্শন পাঠ করে ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এই ধর্মসম্প্রদায়ের সদস্যপদও গ্রহণ করেন। কিন্তু জীবনের এক গূঢ় বাঁকে তাঁর দর্শন ঘটে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে। রামকৃষ্ণের ভাবজগৎ, ঈশ্বরানুভূতি ও মানবপ্রেম নরেন্দ্রনাথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তিনি শ্রদ্ধাভরে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং এই গুরুর সান্নিধ্যে লাভ করেন মানবসেবার সর্বোচ্চ দীক্ষা। এই শিক্ষা-দীক্ষাই পরে তাঁর জীবনের মূল চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে।
সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি দীর্ঘ তিন বছর ধরে ভারত পরিভ্রমণে আত্মনিয়োগ করেন। পরিব্রাজক রূপে তিনি প্রত্যক্ষ করেন ভারতের বাস্তব চিত্র—দারিদ্র্য, অশিক্ষা, জাতিভেদ, কুসংস্কার ও সামাজিক অবক্ষয়। এই অভিজ্ঞতাই তাঁকে প্রস্তুত করে তুলেছিল একজন চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক ও সত্যনিষ্ঠ সমাজনায়কে রূপান্তরিত হতে। ভারতবর্ষের এই মানবিক বিপর্যয় সম্পর্কে বিশ্বমঞ্চে প্রতিবাদ জানানোর উদ্দেশ্যেই তিনি ১৮৯৩ সালে সিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত ধর্ম মহাসভায় অংশগ্রহণ করেন। গুরুভাই ও শিষ্যদের অনুরোধে, এবং মা সারদাদেবীর অনুমতিতে তিনি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সেখানকার তাঁর ভাষণ শুধু আমেরিকা নয়, সমগ্র বিশ্বে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরেছিল।
স্বামীজির গদ্যগ্রন্থগুলিতে যেমন আছে গভীর দার্শনিক উপলব্ধি, তেমনি রয়েছে সাহসী বচন ও বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা। তাঁর সাহিত্য আধুনিক মননের প্রকাশ, যেখানে অতীত ঐতিহ্যের পটভূমিতে নির্মিত হয়েছে ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল আদর্শ। তাঁর প্রতিটি রচনাই চিন্তাশীল এবং যুগপ্রসঙ্গিক। বেদান্ত দর্শনের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন এমন এক ভাবনা, যেখানে একদিকে রয়েছে বিজ্ঞানমনস্কতা, অন্যদিকে হৃদয়াবেগ ও মানবপ্রেমের অপূর্ব সমাহার। জাতির বিবেককে জাগিয়ে তোলার জন্য তিনি ব্যবহার করেছেন সাহিত্যকে এক শক্তিশালী অস্ত্ররূপে।
তাঁর সাহিত্যিক কল্পনার মূলে ছিল জাতীয়তাবাদ ও মানবতা। ভারতবর্ষের হতাশাগ্রস্ত, অবহেলিত, দারিদ্র্যপীড়িত জনসাধারণের প্রতি তাঁর গভীর দরদ ছিল। সেই উপলব্ধিই রূপ পেয়েছে তাঁর সাহিত্যে “বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেইজন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।”
তিনি ছিলেন সাহসিকতার প্রতিমূর্তি—একজন বীর সংগ্রামী। জাতীয় অবনতির বিরুদ্ধেই ছিল তাঁর ধ্বনিত আহ্বান। একদিকে ভারতবাসীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করতে চেয়েছেন, অন্যদিকে জাতিভেদ ও শ্রেণীবিভাজনের বিরুদ্ধেও উচ্চারণ করেছেন তীব্র প্রতিবাদ। তাঁর প্রত্যয়ভরা কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—“হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদপে বল—আমি ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী—আমার ভাই।”
স্বামী বিবেকানন্দের সাহিত্য গতানুগতিক চর্চার সীমা অতিক্রম করে একটি মৌলিক ও আধুনিক চিন্তাধারার পথ নির্মাণ করেছে। এখানে তাঁর মৌলিকতা নিহিত—তাঁর গভীর বোধ, বিস্তৃত মনন এবং এক অসাধারণ ভাবসম্পদের উন্মোচনে। তিনি রামচন্দ্র ও কৃষ্ণকে জাতীয় চেতনার প্রতীক মনে করতেন, কারণ তিনি ছিলেন বীররসের পূজারী। তাঁর কাছে এই দুই পুরুষ একদিকে আদর্শ রাজা, অন্যদিকে সংগ্রামের প্রতীক—যাঁদের মধ্যে জাতির শক্তির প্রতিচ্ছবি তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।
এইভাবেই স্বামী বিবেকানন্দ বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে এক অনন্য উচ্চতা অর্জন করেছেন। তাঁর ভাষা যেমন যুক্তিনিষ্ঠ, তেমনি আবেগময়; তাঁর চিন্তা যেমন ঐতিহ্যবাহী, তেমনি উদার ও আধুনিক। এই দ্বৈত ধারার মিলনেই সৃষ্টি হয়েছে তাঁর অসামান্য সাহিত্য, যা যুগ যুগ ধরে বাঙালির চিন্তা ও আত্মার আলোকবর্তিকা হয়ে পথ দেখিয়ে চলেছে।
নজরুল ইসলামের প্রবন্ধসাহিত্য আলোচনা করতে গেলে শুধু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিংবা স্বামী বিবেকানন্দের রচনার কথা মনে পড়ে—এমনটি নয়। বরং তাঁর প্রবন্ধভাষা, বৈপ্লবিক মনোভঙ্গি এবং সাংবাদিকচিন্তার সঙ্গে আরও কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ চিন্তানায়ক ও প্রাবন্ধিকের ভাবনার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন সখারাম গণেশ দেউস্কর (১৮৬৯–১৯১২) এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১–১৯০৭)। নজরুলের বহু প্রবন্ধ, বিশেষত ধূমকেতু পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের লেখনী ও ভাবনার সঙ্গে বিস্ময়কর মিল রেখে চলে।
এই দুই মনীষী ছিলেন মূলত সাংবাদিক, কিন্তু শুধু তথ্য পরিবেশনের উদ্দেশ্যে নয়—তাঁরা সাংবাদিকতাকে করেছিলেন আদর্শ প্রচারের এক বলিষ্ঠ মাধ্যম। বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ ও উচ্চমানের গদ্যরচনার মাধ্যমে তাঁরা সংবাদপত্রকে রূপ দিয়েছিলেন সাহিত্যের এক শাখায়। সাহিত্যরস ও রাজনৈতিক দ্রোহ, ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্ক ও জাতীয়তাবাদ—এই সমস্ত উপাদান তাঁরা গেঁথে তুলেছিলেন তাঁদের রচনার পরতে পরতে। তাঁদের রচনার মধ্যে যেমন আছে অন্তর থেকে উৎসারিত সাহসী ভাষা, তেমনি রয়েছে এক বুদ্ধিদীপ্ত সমাজচিন্তার দীপ্তি—যার কাছাকাছি অবস্থানে নজরুলের লেখনীকেও আমরা স্থাপন করতে পারি।
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, যাঁর প্রকৃত নাম ছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ছিলেন স্বদেশীয়ুগের অন্যতম বিকল্প চিন্তানেতা ও বিপ্লবী আন্দোলনের এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। জীবনের প্রারম্ভে তিনি কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে এসে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হন। কিন্তু খুব শীঘ্রই ১৮৮৮ সালে ব্রাহ্ম মত ত্যাগ করে তিনি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ধর্মান্তরের এই পর্বটি কেবল তাত্ত্বিক অনুসন্ধানেই সীমাবদ্ধ ছিল না—বরং তা ছিল আত্মজিজ্ঞাসা ও বিশ্বমানবিক ঐক্যের এক মহৎ প্রয়াস। পরে তিনি বেদান্ত দর্শনের অন্তর্নিহিত ভাবধারার সঙ্গে খ্রিষ্টধর্ম ও হিন্দুধর্মের মিলনসূত্র খুঁজে পান। এই দার্শনিক সন্ধি ও সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে তিনি এক নতুন ধারার আত্মচেতনা নির্মাণ করেন। তাঁর এই ভাবনার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের গভীর আত্মিক যোগ বিদ্যমান ছিল।
বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ইংল্যান্ড গমন করেন এবং অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত ও হিন্দুধর্ম বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করেন। এই আন্তর্জাতিক পরিসরে দাঁড়িয়েও তিনি ভারতীয় চিন্তাধারার শক্তি ও সৌন্দর্যকে বিশ্লেষণাত্মক এবং যুক্তিনির্ভর ভাষায় তুলে ধরেন। তাঁর চিন্তাভাবনার নিদর্শন স্বরূপ ১৩০৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ— ‘তিন শত্রু’, ‘ভারতের অধঃপতন’ এবং ‘বর্ণাশ্রমধর্ম’। এই রচনাগুলিতে তিনি সমকালীন জাতীয় জীবনের সংকট, ঔপনিবেশিক শাসনের শোষণ ও বর্ণপ্রথাজনিত অবক্ষয়কে স্পষ্ট ভাষায় চিহ্নিত করেন। তাঁর ভাষা ছিল সরাসরি, যুক্তিনির্ভর এবং অনিবার্যভাবে কাব্যময়; যার স্বর ও অন্তঃসার নজরুলের রচনার সঙ্গেও এক গভীর আত্মীয়তা নির্মাণ করে।
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের রণচণ্ডী সত্তা তখন আরও প্রবল হয়ে ওঠে যখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তিনি সরাসরি বিপ্লবী রাজনীতিতে যুক্ত হন। জাতীয়তা ও আত্মমর্যাদার প্রশ্নে তিনি কোনো আপস করেননি। তাঁর নেতৃত্বে প্রকাশিত হয় একাধিক সাহসী ও প্রভাবশালী পত্রিকা—যেমন সাপ্তাহিক সন্ধ্যা, স্বরাজ, এবং অর্ধসাপ্তাহিক করালী। এই সব পত্রিকায় তিনি জাতীয় চেতনার জাগরণ, ধর্মীয় সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং ঔপনিবেশিক শাসনের অপশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় লেখালেখি করেন। পত্রিকা সম্পাদনার পাশাপাশি তিনি জনসমাবেশ ও উৎসবের সাংস্কৃতিক রূপও বদলে দিতে সচেষ্ট হন। তাঁর উদ্যোগেই শিবাজী উৎসব ও ভারতমাতার পূজার অনুষ্ঠান শুরু হয়, যা পরবর্তীতে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনার সম্মিলিত রূপ পায়।
অন্যদিকে, সখারাম গণেশ দেউস্কর-ও ছিলেন সেই একই ধারার একজন বলিষ্ঠ প্রতিনিধি, যিনি ছিলেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রাক্কালে মহারাষ্ট্র থেকে উঠে আসা এক বাঙালি মনীষা। তাঁর ‘দেশের কথা’ প্রবন্ধগ্রন্থ ব্রিটিশ শাসনের অর্থনৈতিক শোষণ ও প্রশাসনিক বৈষম্যের এমন নির্ভুল বিশ্লেষণ দিয়েছিল, যা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি প্রদান করেছিল। এই ধরনের বক্তব্য ও মনোভাব নজরুলের যুগবাণী ও ধূমকেতুর রচনার মধ্যে সশব্দে প্রতিধ্বনিত হয়। সাহসী উচ্চারণ, জাতীয় গর্ব, ও অধিকারবোধ—এই ত্রিসূত্রে গাঁথা নজরুলের লেখার মূল সুর যেন সখারাম গণেশ ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের ভাষ্যকেই নবতর বলিষ্ঠতা দিয়ে পুনর্গঠিত করে।
এইভাবে বিচার করলে দেখা যায়, নজরুলের প্রবন্ধসাহিত্য একটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার উত্তরসূরি—যেখানে সাংবাদিকতা, চিন্তাভাবনা, দ্রোহ ও সাহিত্য একই প্রবাহে মিশে এক শক্তিশালী সৃজন নির্মাণ করে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও সখারাম গণেশ দেউস্করের মতো লেখকদের প্রভাবে যেমন নজরুল উপকৃত হয়েছেন, তেমনি নজরুল নিজেও সেই ধারার এক বিকাশ ও বিস্তার। তাঁদের ভাবনার সঙ্গে নজরুলের প্রবন্ধসমূহের যে ভাবগত ও ভাষাগত সাদৃশ্য তা কেবল আকস্মিক নয়—বরং তা একটি স্বদেশচেতনার যৌথ আত্মপ্রকাশ।
সখারাম গণেশ দেউস্কর—এক অসামান্য চিন্তানায়ক ও রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবী—ছিলেন জাতিতে মারাঠি, কিন্তু মননে ও সংস্কৃতিচর্চায় ছিলেন একজন প্রকৃত বাঙালি। জন্মেছিলেন দেবঘরের পাণ্ডা সম্প্রদায়ে, কিন্তু তাঁর শিক্ষা ও সাহিত্যসাধনার পরিসর বাংলাভাষাভাষী সমাজেই বিস্তার লাভ করে। পেশাগত জীবনে তিনি শিক্ষকতা করেছেন, কিন্তু পরে সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন জাতীয় চেতনার বিকাশে। কলকাতার হিতবাদী পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণের পর তাঁর চিন্তা ও রচনার অভিমুখ স্পষ্টভাবে জাতীয়তাবাদী হয়ে ওঠে। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি মারাঠি ভূমির ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং আত্মমর্যাদাবোধকে বাঙালি পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন এক গম্ভীর প্রয়াসে। তাঁর লেখায় উঠে এসেছে মারাঠা জাতির ঐতিহ্য, বীরত্ব এবং রাজনৈতিক চেতনার সেই উজ্জ্বল স্বর, যা সমকালীন বাংলায় নবজাগরণের আন্দোলনে এক নতুন প্রাণসঞ্চার করেছিল।
সখারামের ভাবধারায় প্রবলভাবে প্রভাবিত ছিল তিলক-নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদ, যার মূল ভিত্তি ছিল হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতি ও গৌরবময় অতীতচেতনা। তিলকের নেতৃত্বে ভারতবর্ষের স্বাধীন রাষ্ট্রভাবনার যে জাগরণ শুরু হয়, তার নিরবচ্ছিন্ন স্রোত বইতে থাকে সখারামের লেখনীতে। তিনি ছিলেন এই ভাবধারার অন্যতম বাহক ও সম্প্রসারক। বাংলার ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে এই জাতীয়তাবাদী চিন্তার প্রবাহ তাঁর মাধ্যমেই প্রবেশ করে বাংলার বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলে, বিশেষত সাহিত্য ও সাংবাদিকতার পরিসরে। এই প্রেক্ষিতে কাজী নজরুল ইসলামের রচনার সঙ্গে সখারাম দেউস্করের দার্শনিক বোধ, রাজনৈতিক সাহস ও জাতীয়তাবাদী মনোভাবের গভীর মিল লক্ষ্য করা যায়।
একইভাবে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ও ছিলেন এক যুগান্তকারী চিন্তাবিদ ও ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক সমন্বয়ক, যাঁর প্রবন্ধভাষা এবং রচনাশৈলী নজরুলের কাছাকাছি এসে যায়। তাঁদের সকলের রচনায় ছিল এক ধরনের প্রত্যক্ষতা, সমাজ ও দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা, এবং সাহিত্যিক কাঠামোর ঊর্ধ্বে উঠে জনমানসকে আলোড়িত করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। এই প্রেক্ষিতে ড. সুশীলকুমার গুপ্তের মূল্যায়ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:
“প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, জ্বলন্ত দেশ প্রেম এবং মানুষের প্রতি অবিচল ভালবাসা ও বিশ্বাস গণেশ দেউস্কর ও ব্রহ্মবান্ধবের রচনাকে আঙ্গিক শৈথিল্য ও প্রকরণ উদাসীনতা সত্ত্বেও যে প্রাণস্পর্শী আবেদনে ঐশ্বর্যশালী করেছে, নজরুলের রচনাতেও তার উপস্থিতি বিরল নয়।”
এই মন্তব্য নজরুলের প্রবন্ধসাহিত্যকে এক গভীর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করে, যেখানে সাংবাদিকতা, সাহিত্য এবং রাজনৈতিক বোধ একত্রে মিশে যায় মানবিকতার উচ্চস্তরে।
নজরুলের প্রবন্ধভাষা ছিল দুর্দান্ত আত্মবিশ্বাস, প্রচণ্ড আবেগ এবং দ্রোহী চেতনার মিশ্রণ—যা পাঠককে ভাবনার গভীরে পৌঁছে দিতে সক্ষম। এই গদ্যভাষার রূঢ়তা ও শক্তির মধ্যে একপ্রকার পৌরুষ নিহিত ছিল, যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী বিবেকানন্দের সেই বিশ্লেষণধর্মী ও জাতি-সচেতন গদ্যরীতিকে। তাঁদের সকলের লেখায় জাতীয় জীবনের যে মরণোন্মুখ সংকট ও আত্মসন্ধানের যে চেষ্টা, তা প্রবন্ধসাহিত্যকে নিছক সাহিত্যরসের পরিসর থেকে সরিয়ে এক বৃহৎ সমাজ ও রাষ্ট্রবীক্ষার সরণিতে স্থান দেয়।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নবজাগরণের বাংলা গদ্যভাষার সবচেয়ে প্রভাবশালী রূপকার। তাঁর রচনা একদিকে যেমন বিশ্লেষণমুখী, তেমনি চিন্তাসঞ্জাত; তাঁর ভাষা যুক্তিনির্ভর হলেও হৃদয়বৃত্তির সঞ্চার ঘটাতে সক্ষম। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজনীতি ও শিল্প—কোন বিষয়েই তাঁর কলম থেমে থাকেনি। জাতীয় আত্মপরিচয়ের অন্বেষণ এবং জনগণকে সচেতন করে তোলার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধকে বেছে নিয়েছিলেন এক কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পাঠকের চিন্তা-ভাবনায় আলোড়ন তোলা, যুক্তির মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করা এবং সাহিত্যের পরিসরে জাতীয়তাবাদী আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করা।
এই কারণে, তাঁর সাহিত্যিক প্রভাব এতটাই বিস্তৃত হয় যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধকে ‘বঙ্কিমযুগ’ বলেই চিহ্নিত করা হয়েছে। এই প্রভাব ছিল কেবল সাহিত্যিক নয়, বরং রাজনৈতিক, দার্শনিক ও সামাজিক দিক থেকেও সুগভীর। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের প্রায় পাঁচ দশক আগে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশরা একটি ব্যবসাভিত্তিক উপনিবেশে পরিণত করে। ঊনবিংশ শতকের সূচনালগ্নে ইউরোপীয় শিক্ষার প্রসার ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের বিস্তার ভারতীয়দের মধ্যে নতুন এক আত্মসচেতনার জন্ম দেয়। এই নতুন চেতনা—যা ছিল যুক্তিবাদী, আধুনিক এবং আত্মবিশ্বাসে সমৃদ্ধ—তার অন্যতম ভাষ্যকার হয়ে ওঠেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর সাহিত্যচর্চা সেই চিন্তাধারাকেই শক্ত ভিত প্রদান করে।
এভাবেই নজরুল, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, দেউস্কর ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—এই ব্যক্তিত্বরা কেউই শুধু প্রাবন্ধিক নন; তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন একটি বৃহত্তর চেতনার ধারক। তাঁরা প্রবন্ধকে একটি আত্মিক ও রাজনৈতিক ভাষ্যরূপে গড়ে তোলেন, যার মধ্য দিয়ে জাতির চেতনা, আত্মপরিচয় এবং সংগ্রামের অগ্নিস্নান প্রতিফলিত হয়েছে সাহিত্যের দৃঢ় ভঙ্গিতে। নজরুল এই ধারারই উজ্জ্বল উত্তরসূরি, যাঁর কলমে যুগের বজ্রনিনাদ ও হৃদয়ের আর্তি একাকার হয়ে উঠেছিল।
স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশ মূলত ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে করেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ রচনা, বক্তৃতা ও দার্শনিক নিবন্ধ ইংরেজিতে রচিত হলেও, বাংলা ভাষাতেও তাঁর প্রবন্ধসমূহ একটি স্বতন্ত্র সৌন্দর্য ও বলিষ্ঠতা অর্জন করে। গুরুভাইদের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিপত্রে যেমন দেখা যায় তাঁর আন্তরিক উপদেশ ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি, তেমনি ইউরোপ ভ্রমণকালে লেখা ডায়েরি-জাতীয় রচনায় ফুটে ওঠে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও নানান পর্যবেক্ষণ। বিবেকানন্দের সাহিত্য রুচি ছিল অত্যন্ত সংবেদনশীল ও তীক্ষ্ণ; তিনি বলিষ্ঠ, আবেগময় এবং প্রাণবন্ত গদ্যরীতিকে বিশেষভাবে পছন্দ করতেন। তাঁর মতে, চলিত ভাষায় লেখা প্রবন্ধ অধিকতর জীবন্ত, সরস ও প্রাঞ্জল, যা সহজেই পাঠকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম।
বিবেকানন্দের বাংলা প্রবন্ধগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—‘পরিব্রাজক’, ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’, ‘ভাববার কথা’ ও ‘পত্রাবলী’। এই রচনাগুলির ভাষা ছিল উত্তর কলকাতার জনজীবনে প্রচলিত মৌখিক বাংলার ধাঁচে, যা সাহিত্যের পরিমিত সংযম ও রসঘন আবেগকে একত্রে ধারণ করেছিল। তাঁর ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল প্রবল আত্মবিশ্বাস ও দুঃসাহস, কিন্তু তা কখনোই অশালীনতায় পরিণত হয়নি। গদ্যে ছিল বলিষ্ঠতা, স্পষ্টতা এবং একটি ক্লাসিক ধ্বনি-গম্ভীর সংযম, যা তাঁকে সমকালীন গদ্যরচয়িতাদের থেকে আলাদা মর্যাদা দেয়। তাঁর ভাষার বৈচিত্র্য ও আবেদন যেমন উপভোগ্য, তেমনি চিন্তনীয়। যেমন—
“বলি রঙের নেশা ধরেছে কখন কি? যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে? হুঁ বলি এই বেলা গঙ্গা মার শোভা যা দেখবার দেখে নাও ; আর বড় একটা কিছু থাকছে না। দৈত্যদানবের হাতে পড়ে এসব যাবে।”
এই উদ্ধৃতির ভাষা শক্তিশালী, আবেগময় ও আলঙ্কারিক। এখানে বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব ও কল্পনার অভ্যন্তরীণ গম্ভীরতা প্রকাশিত হয়েছে দুর্দমনীয় ভঙ্গিতে। এই ভাষিক দৃঢ়তা ও কাব্যময় পরিমিতির সঙ্গে আমরা মিল খুঁজে পাই কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহীমূলক গদ্যভঙ্গির। নজরুলের ‘যুগবাণী’, ‘রুদ্রমঙ্গল’ অথবা ‘দুর্দিনের যাত্রী’—সবখানেই তাঁর বিদ্রোহী মনন, সমাজ ও রাষ্ট্রবিরোধী অবস্থান এবং ভাষার দ্যুতিময় শক্তির প্রকাশে বিবেকানন্দের গদ্যরীতির সাদৃশ্য অনুভব করা যায়।
নজরুলের অন্যতম প্রবন্ধগ্রন্থ ‘যুগবাণী’ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে। গ্রন্থটি তিনি উৎসর্গ করেন বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তকে। উৎসর্গপত্রে নজরুল এক প্রগাঢ় ভ্রাতৃত্ববোধের নিদর্শন রেখে লেখেন—“শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত শ্রীচরণেষু তোমার আদর-সিক্ত ছোটভাই নুরু।”
এই সময় বাংলায় ও সমগ্র ভারতবর্ষে অগ্নিগর্ভ রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। অসহযোগ আন্দোলন এবং খিলাফত আন্দোলনের উত্তাল ধারা দেশজুড়ে আন্দোলিত হচ্ছিল। ইংরেজ সরকার সেই আন্দোলনের উত্তাপ রুখতে নানা রকম শোষণ, দমন ও নিপীড়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২০ সালের ১২ই জুলাই নবযুগ নামে একটি সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, যার সম্পাদক ছিলেন মিস্টার এ কে ফজলুল হক এবং যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে যুক্ত ছিলেন মুজফ্ফর আহমদ ও কাজী নজরুল ইসলাম।
এই পত্রিকায় নিয়মিতভাবে নজরুল লিখতে থাকেন, যেখানে তাঁর গদ্য এক নতুন ঘূর্ণিঝড়ের মতো ছুটে আসে। তাঁর কলম নিছক প্রতিবাদ নয়, ছিল আবেগময়, অগ্নিময়, বিদ্রোহের প্রতীক। সমাজের কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, ব্রিটিশ শাসনের অন্যায় এবং ভারতীয়দের আত্মবিস্মৃতি ও কাপুরুষতার বিরুদ্ধে তিনি লিখেছেন ধারালো প্রবন্ধ। সেই সময় নবযুগ ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত কুড়িটি প্রবন্ধ এবং ‘বকুল’ পত্রিকার ১৩২৭ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ নিয়ে সংকলিত হয় ‘যুগবাণী’। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে এবং এটিই ছিল নজরুলের প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ, যেটি ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা তৎক্ষণাৎ বাজেয়াপ্ত হয়।
ফৌজদারি আইনের ৯৯(এ) ধারায় গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করার পেছনে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রশাসনের ব্যাখ্যাও ছিল সুস্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে আজহারুদ্দীন খানের পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ—“যুগবাণী বইটির ওপর সরকারের ভীতি ১৯৪১ সালেও কাটেনি। সরকারি ফাইলে ১৬/০১/১৯৪১ সালে বইটি সম্পর্কে বলা হয়েছে বইটির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তোলা সমীচীন নয়, বইটি এখনও ‘Dangerous forceful and vindictive।’”
অন্যদিকে, বিশিষ্ট সমালোচক সুশীলকুমার গুপ্ত ‘সাহিত্য সাধক চরিতমালা’ গ্রন্থে বলেন— “ইংরেজদের প্রতি জাতিগত ঘৃণা, তদানীন্তন শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও তাহাকে কায়েম রাখিতে ইচ্ছুক দাসমনোবৃত্তিসম্পন্ন ভারতীয়দের তীব্র ভৎসনা প্রধানত এই তিনটি বিষয় যুগবাণীর প্রবন্ধগুলির মধ্যে দেখিয়া বাঙলা সরকার ফৌজদারী বিধির ৯৯ এ ধারানুযায়ী গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করেন।”
যুগবাণীতে ছিল মোট একুশটি প্রবন্ধ। এর মধ্যে তিনটি প্রবন্ধ ব্রিটিশ সরকারের চরম অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়: ‘ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ’, ‘মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?’ এবং ‘কালা আদমীকে গুলি মারা’। এই তিনটি প্রবন্ধের মধ্যে নজরুলের গদ্য সবচেয়ে প্রতিবাদমুখর ও তীক্ষ্ণ, যা সরাসরি ঔপনিবেশিক দমননীতির বিরুদ্ধে ছিল। এইসব রচনার দুঃসাহসিকতা ও জাতীয়তাবাদী চেতনা ইংরেজ সরকারের শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই অবিলম্বে গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। তবে পরে, ১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ—স্বাধীনতা আসার ঠিক পূর্বে—ব্রিটিশ সরকার যুগবাণী-র উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে।
এরও আগে নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ কবিতা ইংরেজ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, কিন্তু চতুর কৌশলের কারণে তারা সেটিকে ‘রাজদ্রোহী’ বলে ঘোষণা করেনি। কারণ, কবিতাটিতে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের পুরাণ ও ধর্মবিশ্বাসের উপাদান ছিল। ধর্মীয় অনুভূতির ব্যাপারে স্পর্শকাতর সরকার সেই কবিতাকে নিষিদ্ধ করতে সাহস করেনি। কিন্তু ‘যুগবাণী’-র প্রবন্ধগুলি ছিল ধর্মের সীমা ছাড়িয়ে রাজনৈতিক ও জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ, আর সেই কারণেই গ্রন্থটি অবিলম্বে সেন্সরের কোপে পড়ে।
এই সমস্ত ঘটনাই প্রমাণ করে, নজরুলের প্রবন্ধসাহিত্য ছিল নিছক ভাবালুতার নয়, বরং তা ছিল এক বিদ্রোহী মননের দৃঢ় প্রতিবিম্ব। তাঁর ভাষার বলিষ্ঠতা, বিবেকানন্দের মতোন গাম্ভীর্য, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মতোন মননশীলতা মিলেমিশে তৈরি করেছে এক দুর্বার ও প্রেরণাদায়ক সাহিত্যের ধারা, যা পরবর্তীকালের জাতীয়তাবাদী সাহিত্যধারায় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে বারবার।
নজরুল ইসলামের প্রবন্ধসাহিত্যের ইতিহাসে ‘যুগবাণী’ এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই গ্রন্থটি আসলে তাঁর দৈনিক নবযুগ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির একটি সংকলন, যা ১৯২২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতির ধারায় এক নবীন সঞ্চার ঘটানোর লক্ষ্যে এই প্রবন্ধগুলি রচিত হয়েছিল। রাজনৈতিক দমননীতি, ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও সমাজের দৈন্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘোষণা ছিল নজরুলের এই রচনাগুলির মূল সুর।
যুগবাণী গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলির তালিকা নিম্নরূপ—
১) নবযুগ
২) আবার তোরা মানুষ হ’
৩) ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ
৪) ধর্মঘট
৫) লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য
৬) বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান
৭) ছুঁৎমার্গ
৮) উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন
৯) মুখবন্ধ
১০) রোজ কেয়ামত বা প্রলয়দিন
১১) বাঙালির ব্যবসাদারী
১২) — আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন?
১৩) কালা আদমিকে গুলি মারা
১৪) শ্যাম রাখি না কুল রাখি
১৫) লাটপ্রেমিক আলিইমান
১৬) ভাব ও কাজ
১৭) সত্যশিক্ষা
১৮) জাতীয় শিক্ষা
১৯) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
২০) মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?
২১) জাগরণী
এই একুশটি প্রবন্ধ নজরুলের চিন্তাচেতনার ধারাকে বহুমাত্রিক রূপ দিয়েছে। এতে যেমন আছে তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতার সরাসরি ভাষ্য, তেমনি সমাজ সংস্কার, ধর্মীয় ভাবনা ও শিক্ষা বিষয়ে তাঁর উদার ও আধুনিক মননের অভিব্যক্তি।
গ্রন্থটির সূচনাপর্ব, অর্থাৎ প্রথম প্রবন্ধ ‘নবযুগ’-এ নজরুল এক নবদিগন্তের সূচনা কামনা করেছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষের অন্ধকার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে নতুন আলোর আহ্বান জানান। তাঁর এই আহ্বান কেবলমাত্র ভারতবর্ষের জন্য নয়—তিনি সারা বিশ্বের কাছে একটি মুক্ত, মানবিক ও ভ্রাতৃত্ববোধে পরিপূর্ণ সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই প্রবন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আন্তর্জাতিক; যেখানে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার শ্রমিক বিপ্লব, ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও বিশ্বজনীন সাম্যবাদের ভাবনাও প্রতিফলিত হয়েছে।
১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড নজরুলের মনে গভীর দহন সৃষ্টি করেছিল। নিরস্ত্র ভারতীয় নাগরিকদের উপর ব্রিগেডিয়ার ডায়ারের নেতৃত্বে চালানো সেই নির্মম গণহত্যা নজরুলের মতো সংবেদনশীল কবি-চিন্তকের মনে বীভৎস শোক ও ক্ষোভের সঞ্চার করে। শুধু পাঞ্জাব নয়, সেই সময় ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী দেশপ্রেমিক আন্দোলনকারীদের দমন করতে রক্তপাত ও হত্যা অবলম্বন করেছিল। এইসব ঘটনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব নজরুলের রচনায়, বিশেষ করে ‘যুগবাণী’-তে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।
নজরুল বিশ্বাস করতেন, আত্মত্যাগই নবযুগের প্রকৃত ভিত্তি। তাঁর কাছে নবযুগ মানে কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়—সামাজিক মুক্তি, ধর্মীয় সহনশীলতা, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার এবং মানবিক মর্যাদার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। এই নবযুগের সূচনা হতে পারে শুধু সেই সাহসী আত্মাদের হাত ধরে, যাঁরা নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়ে জাতিকে জাগিয়ে তুলেছেন। তিনি মনে করতেন, নবযুগ কেবল স্বপ্নে নয়, ত্যাগ, সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গের বাস্তব পথেই আসবে।
এই ভাবনার প্রতিফলন দেখা যায় ‘যুগবাণী’-র অন্যান্য প্রবন্ধগুলিতেও—যেমন ‘ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ’, ‘মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?’ কিংবা ‘কালা আদমিকে গুলি মারা’—এইসব রচনায় তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বজ্রনিনাদ। আবার ‘বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান’ ও ‘জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়’-র মতো প্রবন্ধে তিনি তুলে ধরেছেন মুসলমান সমাজের সাংস্কৃতিক অংশগ্রহণ, শিক্ষা-বঞ্চনা এবং আত্ম-পরিচয় অনুসন্ধানের সংকট।
সব মিলিয়ে ‘যুগবাণী’ শুধু নজরুলের প্রবন্ধ-সংগ্রহ নয়, এটি এক বিশেষ সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক দলিল, যেখানে কবি-সাংবাদিক-দার্শনিক-সংগ্রামী এক হয়ে কথা বলেন। তাঁর ভাষা যেমন প্রগলভ, তেমনি ব্যঙ্গাত্মক, আবার একই সঙ্গে করুণ ও দ্রোহী। নজরুলের আত্মত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত এই লেখা গুলি তাই কেবল সাহিত্যের পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং ইতিহাসের পাতায়ও তা স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। এইসব প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যের গদ্যভাষায় এক নতুন ধারার সূচনা করেছিল—যা সমকালকে যেমন প্রশ্ন করেছে, তেমনি ভবিষ্যৎকে দিয়েছে দিকনির্দেশ।
নবযুগ
নজরুল ইসলাম তাঁর যুগবাণী গ্রন্থের সূচনা-প্রবন্ধ ‘নবযুগ’-এ এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যুগের আহ্বানকে উচ্চারণ করেছিলেন দুর্বার কণ্ঠে। তিনি লিখেছিলেন—“আজ মহাবিশ্বে মহাজাগরণ, আজ মহামাতার মহাআনন্দের দিন, আজ মহামানবতার মধ্যযুগের মহাউদ্বোধন।” এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে তিনি শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সমগ্র বিশ্বের নিপীড়িত, শৃঙ্খলিত, পদদলিত মানুষদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন এক মহান মুক্তির অভিযাত্রায় অংশ নিতে। নজরুলের দৃষ্টিতে ইতিহাস তখন আর স্থবির নয়, বরং উত্তাল; শোষিত মানুষেরা যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পাচ্ছে।
কারারুদ্ধ মানুষ আজ শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে প্রস্তুত। শোষণের জিঞ্জির এখন আর বাঁধতে পারবে না মুক্তিচেতনার ঝড়। বন্দিদশার দীর্ঘ রজনী শেষে শঙ্খনিনাদে ধ্বনিত হচ্ছে নবযুগের অর্ঘ্য। জগদ্ধাত্রীর মঙ্গলধ্বনি যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে চারদিকে। বিশ্বজুড়ে জেগে উঠেছে বঞ্চিতেরা—তাঁদের চোখে ফুটে উঠেছে মুক্তির দীপ্তি, অন্তরে জেগেছে বিপ্লবের মন্ত্রশিখা। সেই বিপ্লবী প্রভাতে মানবতা যেন নতুন গান ধরেছে—
“পোহাল পোহাল বিভাবরী, পূর্ব তোরণে শুনি বাঁশরি।”
কিন্তু ভারতবর্ষ? সে যেন এই নব আলোকের মধ্যেও লজ্জায় কুঁকড়ে যায়। তার শরীরে এখনও বয়ে বেড়ায় শতাব্দীব্যাপী দাসত্বের দাগ, কলোনিয়াল পদাঘাতের ক্ষতচিহ্ন। তলোয়ার, বুলেট, লাঠি ও বেতের নির্মম আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে তার বুক, কুঁচকে গেছে আত্মমর্যাদা। শত বঞ্চনার পরেও যখন সে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চেয়েছিল, তখনই তার বুকের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল নিজেরই সন্তানের মৃতদেহ—ভোঁতা ছুরির আঘাতে নিহত এক নিষ্পাপ প্রাণ। সে সন্তানকে রক্ষা করতে গিয়ে মা যখন বুক বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তখন তাঁর মুখে ছিটকে পড়েছিল কলিজা-মথিত রক্তের ঝাপটা।
আর সেই রক্তমাখা দৃষ্টিতেই তিনি দেখলেন—
“সেই সন্তানের রক্ত মাখানো দৃষ্টি দিয়। সে জলভরা চোখে দেখিল, পূর্বতোরণে অগ্নিরাগে লেখা রহিয়াছে নবযুগ।”
এ যেন ইতিহাসের এক মহাকাব্যিক মুহূর্ত। সন্তানের বিচ্ছিন্ন মাথা পাশে রেখে, ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে সেই মা ছুটে এলেন নবযুগকে বরণ করতে। তাঁর দুই ব্যগ্র ও রক্তাক্ত বাহুতে তিনি নবযুগকে আলিঙ্গন করলেন—
“তুমি এসো।” নবযুগ, যাকে এতকাল হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন, এবার নিজেই সেই কোলের মধ্যে মাথা রেখে বলল— “আর আমায় ছাড়িও না মা। এমনই করিয়া যুগে যুগে আমায় আহ্বান করিয়ো।”
এই আত্মত্যাগ, এই আহ্বান কেবল ভারতবর্ষেই নয়—সেই সময় বিশ্বের নানা প্রান্তে একই রকম প্রতিধ্বনি তুলেছিল মুক্তিপিপাসু মানবসমাজ। রাশিয়ায় গর্জে উঠেছিল বিপ্লবের বাঁশি। শ্রমিক শ্রেণি বলেছিল, ‘আর নয় দাসত্ব, আর নয় শোষণ—ভেঙে দাও নিগড়’। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সেই বাঁশি যেন বিশ্বের কানে পৌঁছে দিল এক সর্বনাশা সংকেত। তুরস্ক থেকে গর্জে উঠল আল্লাহু আকবর—ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে এক জাতীয় পুনর্জাগরণের ডাক। আইরিশ বিদ্রোহী বলল, ‘যুদ্ধ শেষ হয়নি, এখনও সংগ্রাম বাকি’। এখনও শাসকের বজ্রমুষ্ঠি আমাদের টুটি চেপে ধরেছে—তখন পর্যন্ত মুক্তি অসম্পূর্ণ। নজরুলের দৃষ্টিতে, অসুরশক্তিকে বিনাশ না করলে দেবতারা মুক্তি পাবে না। তাই ভারতবর্ষসহ সমগ্র পৃথিবী ধ্বনিত হল এক আহ্বানে— “আবির্ভাব হও, আবির্ভাব হও।”
এই আহ্বান আর নিছক কাব্য নয়—এ ছিল এক ঐতিহাসিক চেতনার বিপ্লব, বিশ্বমানবতার মুক্তির ঘোষণা। নজরুল বুঝেছিলেন, মুক্তির জন্য শুধু রাজনৈতিক পরিবর্তন যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন আত্মজাগরণ, প্রয়োজন চেতনার বিপ্লব। নবযুগ সেই চেতনার রূপরেখা—যেখানে ক্ষুধার্ত, নিপীড়িত, দমিত, লাঞ্ছিত মানুষেরা উঠে দাঁড়াবে এক মহাশক্তির সম্মিলিত রূপ হয়ে। নবযুগ মানে কেবল ক্যালেন্ডারের পাতা বদলানো নয়—নবযুগ মানে নতুন মানুষ, নতুন সমাজ, নতুন ভাবনার জন্ম। সে যুগ শুরু হবে রক্ত, অশ্রু ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে।
এভাবে নজরুলের নবযুগ প্রবন্ধটি হয়ে ওঠে এক কাব্যিক বিপ্লবের দলিল—যেখানে ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজচিন্তা ও কবিতার ভাষা একত্রে প্রবাহিত হয়েছে এক মহাজাগরণ-স্রোতে। তার প্রতিটি বাক্য যেন বিদ্যুৎখণ্ড, তার প্রতিটি চিত্রকল্প যেন আগ্নেয়গিরির মতো উদগীরিত বিস্ফোরণ। এই রচনার মধ্য দিয়ে নজরুল কেবল একটি নবযুগের আহ্বান করেননি—তিনি নিজেই সেই যুগের প্রথম দূত হয়ে উঠেছিলেন।
নজরুল ইসলামের ‘নবযুগ’ প্রবন্ধ যেন কেবল একটি রাজনৈতিক ভাষ্য নয়, বরং এক নবজাগরণের মন্ত্রপাঠ। তিনি ঐতিহাসিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কলম ধরেন, যেখানে হৃদয়ের আবেগ, বিপ্লবের উত্তাপ এবং মানবতার গভীর আকুলতা মিলেমিশে এক উজ্জ্বল দ্যুতি ধারণ করে। প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি উচ্চারণ করেছেন—
“ওই শোনো, শৃঙ্খলিত নিপীড়িত বন্দিদের শৃঙ্খলের ঝনৎকার। তাহারা শৃঙ্খল-মুক্ত হইবে, তাহারা কারাগৃহ ভাঙ্গিবে। ওই শোনো মুক্তি-পাগল মৃত্যুঞ্জয় ঈশানের মুক্তি-বিষান !”
এই ঘোষণাই ছিল এক নতুন যুগের দ্বারোদ্ঘাটনের সংকেত—যেখানে শোষণ ও দাসত্বের শৃঙ্খল চূর্ণ করে মানুষ তার মুক্তির পথে যাত্রা শুরু করবে।
এই মুক্তির বাণী শুধু একটি দেশ বা জনগোষ্ঠীর জন্য নয়—নজরুল তাকে বিস্তার দেন সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যে। তিনি জাগাতে চেয়েছেন সকল নিপীড়িতকে, নিগৃহীতকে, ভীত ও পদদলিত জনসমাজকে। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় বিশ্বমানবতার গান—এক নতুন সভ্যতার আহ্বান। প্রবন্ধের অন্তরে উচ্চারিত হয়েছে সেই দীপ্তি—“ঐ শোনো নবযুগের অগ্নিশিখা, নবীন সন্ন্যাসীর মন্ত্রবাণী।” সেই মন্ত্রবাণী রণক্লান্ত সৈনিককে দেয় নতুন শক্তি, জাগিয়ে তোলে আশাভরা প্রত্যয়। সেই মন্ত্রে তরুণেরা বুক ঠুকে ঘোষণা করে—
“আমাদের মধ্যে ধর্ম বিদ্বেষ নাই, জাতি বিদ্বেষ নাই, বর্ণবিদ্বেষ নাই, অভিজাত্যাভিমান নাই।”
এ এক নব সমাজের নির্মাণভাষ্য, যেখানে ভাই ভাইকে চিনবে হৃদয় দিয়ে, যেখানে জাত, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সম্প্রদায়—সব বিভাজন থাকবে অতীতের ইতিহাসে। নজরুল আহ্বান জানান সেই মহামিলনের, যেখানে সমস্ত সংকীর্ণতা, কূপমণ্ডূকতা, আত্মস্বার্থপরতা বিলীন হয়ে যাবে একটি বৃহত্তর মানবিক বন্ধনের আলোয়। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় বিশ্বভ্রাতৃত্বের উদাত্ত আহ্বান—
“এসো ভাই হিন্দু! এসো মুসলমান! এসো বৌদ্ধ! এসো ক্রিশ্চিয়ান! আজ আমরা সব গন্ডি কাটাইয়া সব সংকীর্ণতা, সব মিথ্যা, সব স্বার্থচরিতের পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি।”
এই আহ্বান কেবল এক আবেগতাড়িত আহ্লাদ নয়—এ এক অনুশোচনাময় উপলব্ধি। নজরুল স্মরণ করিয়ে দেন অতীতের রক্তাক্ত দৃশ্যাবলি—শহীদদের মৃতদেহ, গোরস্থান, শ্মশানভূমির স্তব্ধতা, তরুণ আত্মার অতৃপ্ত ক্রন্দন। সেই স্মৃতি আমাদের স্তব্ধ করে দেয়, করে বেদনায় বাকরুদ্ধ। নজরুল বলেন—চেয়ে দেখো শহীদের মুখ, মনে রেখো সেই ত্যাগ। বুঝে নাও, সেই ত্যাগই আজ তোমার মুক্তির পথ প্রশস্ত করেছে। তাই এই পবিত্র আত্মবলিদান যেন কখনো কলহে অপমানিত না হয়। “আজ আর কলহ নয়”— এই উচ্চারণেই তিনি পরিসমাপ্ত করেন হানাহানি আর ঘৃণার রাজনীতি।
নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অসাধারণ দূরদর্শী। তিনি জানতেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কেবল একটি ভৌগোলিক দাবি নয়—এ এক নৈতিক ও আত্মিক জাগরণ। অতীতে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ দেশের বুককে ছিন্নভিন্ন করেছে; জালিয়ানওয়ালাবাগের মতো হত্যাকাণ্ড জাতিকে শুধু শোকাভিভূত করেনি, করেছে ক্রুদ্ধ ও সংবেদনশীল। পাঞ্জাবের গণহত্যার স্মৃতি তখনও দগদগে, আরও সংহত হয়ে উঠছিল অসহযোগ আন্দোলন, খিলাফত আন্দোলনের স্লোগান, শ্রমিক আন্দোলনের দাবিতে সারা ভারত জুড়ে ক্রমাগত বাড়ছিল উত্তেজনার পারদ।
এই প্রেক্ষিতেই নজরুল লিখেছেন নবযুগ প্রবন্ধ। সেই সময়ে তাঁর বন্ধু মুজফ্ফর আহমদ একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছিলেন— “আমি নজরুল ইসলামের নিকট জানতে চাইলাম সে রাজনীতিতে যোগ দেবে কি না। জওয়াবে নজরুল বললেন ‘তাই যদি না দেব তবে ফৌজে গিয়েছিলেম কিসের জন্যে? দেশের অবস্থা তখন খুবই গরম। তাপের ওপরে চড়ালে জল যেমন টগবগ করে ফোটে দেশের বিশুদ্ধ মানুষও সেই রকম টগবগ করে ফুটছিল। পাঞ্জাবে যে নিষ্ঠুর অত্যাচার হয়েছিল সেই কথা দেশের জনসাধারণ তখনও ভোলেননি। ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কার আইন দেশের লোকেরা মেনে নিতে চাইছেন না কিছুতেই। আবার বড় বড় নেতারা এই শাসন সংস্কারকে কাজে লাগাতে চাইছেন। পর্বত ও সমুদ্রের বাধা কাটিয়ে রুশ দেশের মজুর শ্রেণীর বিপ্লবের খানিকটা ঢেউ এদেশেও পৌছেছে। মজুর শ্রেণী চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ধর্মঘটের পর ধর্মঘট চলেছে নানা জায়গায়।”
এই উত্তাল সময়ে নবযুগ পত্রিকার মাধ্যমে নজরুল শুধু ভাষায় নয়, সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। এই পত্রিকা একদিকে যেমন দেশবাসীকে রাজনৈতিক চেতনার দিকে আহ্বান করছিল, তেমনি মজুর, কৃষক, শ্রমজীবী মানুষদের অধিকার-প্রতিষ্ঠার লড়াইয়েরও হাতিয়ার হয়ে উঠছিল। ফলে ইংরেজ সরকার এটিকে বিপজ্জনক মনে করে প্রথমে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ও দণ্ড প্রদান করে। হাজার টাকা জরিমানা করা হলে মুজফ্ফর আহমদ ও নজরুল তৎক্ষণাৎ দুই হাজার টাকা দিয়ে আবার পত্রিকাটি প্রকাশ করেন—যা ছিল নিছক আর্থিক প্রতিশোধ নয়, বরং এক দুঃসাহসিক আত্মদায়িত্বের প্রতীক।
নজরুল জানতেন, এই মুক্তির অভিযাত্রা শুধু ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ থাকবে না। তিনি তাই বিশ্বদৃষ্টিতে বুঝেছিলেন, তৎকালীন বিশ্বের নানা প্রান্তেই একই রকম বিদ্রোহ ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দানা বাঁধছে। তিনি লিখেছেন—
“রুশিয়া বলিল, মারো অত্যাচারীকে! ওড়াও স্বাধীনতা-বিরোধীর শিব! ভাঙ্গো দাসত্বের নিগড়! এ বিশ্বে সবাই স্বাধীন। ‘আল্লাহু আকবর’ বলিয়া তুর্কি সাড়া দিল। …. আইরিশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ‘যুদ্ধ শেষ হয় নাই।”
এই বাক্যাবলিতে উঠে আসে আন্তর্জাতিক মুক্তিসংগ্রামের ধ্বনি। নজরুল শুধু ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক বিশ্বমানবতাবাদী—যিনি সমস্ত নিপীড়নের বিরুদ্ধে কবিতা ও প্রবন্ধে তুলেছিলেন মানবমুক্তির বজ্রকণ্ঠ।
এই প্রবন্ধে নজরুল যেভাবে আত্মত্যাগ, দ্রোহ, ঐক্য, শোক ও স্বপ্নকে একসূত্রে গেঁথে এক বিপ্লবী ভাষার নির্মাণ করেছেন, তা বাংলা গদ্যসাহিত্যে এক অনন্য নিদর্শন। নবযুগ শুধু একটি প্রবন্ধ নয়—এ এক বিপ্লবের সার্বজনীন ঘোষণা, যেখান থেকে বাঙালি জাতি নিজের মুক্তির ইশারা পেয়েছিল। সেই মন্ত্র এখনও ধ্বনিত হয়—যখনই যুগ ক্লান্ত, সময় বিষণ্ন, ইতিহাস নিস্তব্ধ।
অসহযোগ আন্দোলনের সময় ভারতের সামগ্রিক পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত জটিল ও উত্তপ্ত। একদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অসীম সাহস ও আত্মদানের মধ্য দিয়ে দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জোয়ার, অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের চিরপরিচিত কৌশলে—চালনা, বিভাজন ও দমননীতি অবলম্বন করে সেই আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে সচেষ্ট ছিল। বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যকার সাম্প্রদায়িক বিভেদকে উস্কে দিয়ে তারা জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি ও অসহযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করছিল, যেন জাতীয় ঐক্য চিরতরে দুর্বল হয়ে পড়ে।
এই অপকৌশল নজরুল ইসলামের মতো দূরদৃষ্টি সম্পন্ন লেখক ও চিন্তকের দৃষ্টিগোচর হতে বিলম্ব হয়নি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, জাতির স্বার্থে যে কোনও মূল্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করতে হবে। কারণ, যদি দেশবাসী নিজেরাই ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তবে স্বাধীনতা কেবল সুদূর স্বপ্ন হয়ে থাকবে না—বরং জাতি চিরতরে গ্লানি ও পরাজয়ের অতল আঁধারে তলিয়ে যাবে। তাই নজরুল তাঁর ‘নবযুগ’ প্রবন্ধে এক উদাত্ত স্বরে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের আহ্বান জানান। তিনি লেখেন—
“এসো ভাই হিন্দু! এসো ভাই মুসলমান! এসো বৌদ্ধ! এসো ক্রিশ্চিয়ান! আজ আমরা সব গন্ডি কাটাইয়া সব সংকীর্ণতা, সব মিথ্যা, সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি। আজ আমরা আর কলহ করিব না। চাহিয়া দেখো পাশে তোমাদের মহা শয়নে শায়িত ওই বীর ভ্রাতৃগণের শব।”
এই আহ্বান নিছক আবেগময় কোনো কবিত্ব নয়—বরং তা ছিল বাস্তব পরিস্থিতির এক গভীর উপলব্ধিসঞ্জাত রাজনৈতিক ঘোষণা। নজরুল জানতেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা না করতে পারলে স্বাধীনতার সংগ্রাম ব্যর্থ হবে। তাঁর আহ্বান ছিল জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে নতুন ভারত গঠনের জন্য এক অন্তর্জাগরণের আহ্বান।
ঠিক সেইরকম আত্মজাগরণের বার্তাই উচ্চারিত হয় নজরুলের আরেকটি প্রবন্ধে—‘গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!’। এই রচনায় নজরুল সরাসরি হতাশ জাতিকে মুখোমুখি করেন বাস্তব সত্যের, আহ্বান জানান ভেঙে পড়া মনোবলকে জাগিয়ে তুলতে। তখন স্বাধীনতা আন্দোলন বারবার দমননীতির মুখে থমকে যাচ্ছে, বহু মানুষ ইংরেজদের অত্যাচারে নিরুৎসাহিত, পরাজিত, সংকুচিত। এই হতাশার অন্ধকারে নজরুল যেন উদ্দীপনার এক দীপ জ্বালালেন। তিনি সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘোষণা স্মরণ করিয়ে দেন—
“গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!”
এই আহ্বানের অন্তর নিহিত ছিল এক দার্শনিক সত্য—চিরকাল কেউ কারও দাসত্ব বহন করে না। দাসত্ব প্রকৃতির বিরুদ্ধে, স্বভাবতই তা চিরস্থায়ী নয়। নজরুল মনে করান, ইতিহাস কখনও অত্যাচারী শক্তিকে চিরজয়ী থাকতে দেয়নি। যারা সাময়িকভাবে ক্ষমতা ও শক্তির মোহে মানুষের স্বাধীনতা ও সম্মানকে পদদলিত করেছে, তারা একদিন সেই অমানবিক শক্তিরই শিকার হয়েছে।
তিনি স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করেন—“এয়সা দিন নেহি রহেগা”—এই দিন থাকবে না, এই শাসন, এই দমনচক্র, এই বৈষম্য একদিন নিশ্চিহ্ন হবে। সেই দিন কাছে আসবে, যেদিন মানুষের হৃদয় জয় করবে তার মনুষ্যত্বের দীপ্তি দিয়ে, অস্ত্র ও শক্তির ভয় দেখিয়ে নয়। নজরুল বিশ্বাস করতেন, যে শক্তি সম্মানবোধ, স্বাধীনতা ও মানবতার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়, সে শক্তি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ইতিহাস সে সাক্ষ্য বহন করে—রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল শক্তির ঔদ্ধত্যে, জার্মানির মতো পরাক্রমশালী সাম্রাজ্য পরাভূত হয়েছিল অহংকার ও অবিচারের দরুন।
নজরুল আরও স্মরণ করিয়ে দেন—ভারতবর্ষের ইতিহাসও এর ব্যতিক্রম নয়। তুর্কি, পাঠান, মোগল—যে যেই সময়ে এসেছে, নিজের শক্তিকে সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে গিয়ে তার অপব্যবহারেই শেষ পর্যন্ত পতনের পথ ধরেছে। শক্তি নিজে দোষী নয়, কিন্তু শক্তির অপব্যবহার, ক্ষমতার দম্ভ এবং স্বেচ্ছাচার যে সর্বনাশ ডেকে আনে—তা ইতিহাসের পাতায় রক্তাক্ত অক্ষরে লেখা রয়েছে।
এই প্রবন্ধের মাধ্যমে নজরুল একটি মৌলিক বোধে জাতিকে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন—শক্তি চাই, কিন্তু সেই শক্তি যেন হয় মানবিক। সম্মান ও স্বাধীনতাকে টিকিয়ে রাখতে যে বল লাগে, তা সংগ্রহ করতে হবে আত্মিক শুদ্ধতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শক্তির ব্যবহার চাই, কিন্তু তা যেন ধ্বংস নয়, হোক রক্ষা; তা যেন প্রতিহিংসা নয়, হোক মুক্তির চাবিকাঠি।
এইভাবে ‘নবযুগ’ ও ‘গেছে দেশ দুঃখ নাই’ প্রবন্ধে নজরুল যে ভাষায় সমাজ, রাজনীতি ও ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করেছেন—তা কেবল সাহিত্যসৃষ্টির এক নিদর্শন নয়, বরং যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে জাতির অন্তরের গভীরে প্রবেশ করা এক দুর্দান্ত প্রজ্ঞার প্রতিফলন। তাঁর কলমে যুগের সত্য, জাতির আশা ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা একত্রে মূর্ত হয়েছে। এইখানেই নজরুল শুধু কবি বা প্রাবন্ধিক নন—তিনি এক জনজাতীয় বোধের নির্মাতা, যুগ-দ্রষ্টা।
স্বাধীনতার সংগ্রাম কেবল ভারতবর্ষের একক ইতিহাস নয়, এটি সমগ্র বিশ্বের এক ঐক্যবদ্ধ জাগরণ। যে যুগে মানুষের হৃদয়ে রক্তঝরা ব্যথার মধ্যেও মুখে ধ্বনিত হচ্ছে এক অভিন্ন আহ্বান—‘মুক্তি-মুক্তি-মুক্তি’, সেই যুগে গোলামির অভিশাপ যেন আরও কর্কশভাবে মানুষের আত্মসম্মানকে পদদলিত করছে। দুঃখজনকভাবে দেখা যাচ্ছে, এই মুক্তির যুগেও অনেক মানুষ স্বেচ্ছায় মেনে নিচ্ছে দাসত্ব। একদিকে মুক্তির আহ্বানে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জেগে উঠেছে, অন্যদিকে কিছু মানুষ নিচু মানসিকতায় আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে মাথা নিচু করে থাকছে। তাঁদের আত্মসমর্পণের অজুহাত—‘দাসত্ব না মানলে খাবো কি?’ এই ভাবনায় যেন মনুষ্যত্ব ভূলুণ্ঠিত হয়েছে; যেন মানুষ কেবল উদর পূর্তির জন্য বেঁচে আছে, পশুর মতো।
নজরুল এমন আত্মবিস্মৃত, মোহাচ্ছন্ন, দাস মানসিকতার বিরুদ্ধে তাঁর কলমে বজ্র প্রহারের মতো আঘাত হেনেছেন। তিনি তীব্র বেদনা থেকে লিখেছেন—
“গোলামী মনের পরিচয় দিতে এতটুকু লজ্জা হয় না! বড়োই দুঃখে তাই বলিতে হয়, এ অভাগা দেশের বুকে বজ্র হানো প্রভু, যদ্দিনে না ভাঙছে মোহ-ভার।”
এই মোহভার ভেঙে ফেলাই স্বাধীনতার জন্য প্রথম শর্ত। শুধুমাত্র শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়, নিজস্ব অন্তর্গত দুর্বলতা, ভীরুতা ও কুচিন্তার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ গড়ে তুলতে হবে। শৃঙ্খল মোচনের পথ নিছক প্রতীক্ষার নয়—তার একমাত্র উত্তর মানুষ নিজেই। কবি এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—
“আমাদের এই মোহভার ভাঙিবে কে? এ শৃঙ্খল মোচন করিবে কে? আছে, উত্তর আছে, এবং তাহা আমরাই।”
এই আত্মবিশ্বাস, আত্মদায়বদ্ধতা ও আত্মোৎসর্গই জাতিকে মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।
তিনি আরও একটি গভীর দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন—যদি আমরা নির্বোধ ভেড়ার মতো ভয়ে কুঁকড়ে বসে থাকি, যদি নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন না হই, তবে হিংস্র শোষকেরা আমাদের নেকড়ে বাঘের মতো ছিঁড়ে খাবে। কবি একধারে রাজনৈতিক সচেতনতার আহ্বান জানাচ্ছেন, অন্যধারে জাতির আত্মিক পুনর্জাগরণের কথা বলছেন। বস্তুত, অন্যের দেখাদেখি পথ চলা কিংবা অন্ধ অনুসরণ জাতির পক্ষে কখনো কল্যাণকর নয়। ব্যক্তিত্বচেতনা, স্বাধীন চিন্তা ও সচেতন কর্তব্যজ্ঞানই জাতিকে মুক্তির পথে নিয়ে যায়। কারণ, নেতারা কখনো একা নেতৃত্ব দেন না—তাঁরা সাধারণ মানুষের বিবেক ও বোধেরই প্রতিধ্বনি।
এই প্রবন্ধে নজরুল বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন দায়িত্ববোধ ও আত্মত্যাগের উপর। তিনি মনে করতেন, কোনো জাতির মুক্তি শুধু বক্তব্যে আসে না, তা আসে আত্মোৎসর্গের বাস্তব চর্চায়। তাই তিনি বলেছে-
“কর্তব্য জ্ঞানের কাছে, ত্যাগের কাছে সম্ভব-অসম্ভব কিছুই নাই। সুতরাং ‘উহা সম্ভব, ইহা অসম্ভব’ বলিয়া ছেলেমানুষি করাও আর এক বোকামি।”
এই বক্তব্য কেবল সাহসী ঘোষণা নয়, এটি এক গভীর আত্মদর্শনের পরিচয়।
সত্যিই, দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য কষ্ট, দুঃখ ও দৈন্যকে সাদরে বরণ করে নিতে হবে। ত্যাগ, বিসর্জন, আত্মোৎসর্গ ও বলিদান—এই চতুষ্টয়ের ভিতেই স্বাধীনতার বীজ নিহিত। ব্যক্তিগত স্বার্থ, আনন্দ কিংবা নিরাপত্তার আশ্রয়ে গুটিয়ে থাকলে জাতির মুক্তি সম্ভব নয়। যন্ত্রণা বাইরের, কিন্তু দেশের মুক্তির মধ্যে নিহিত আছে অন্তরের আনন্দ—আত্মতৃপ্তি ও গৌরবের প্রশান্তি।
এই প্রেক্ষিতেই নজরুল আহ্বান করেন—রুদ্রের ভীষণতা হোক আমাদের আত্মবোধ জাগরণের মশাল। শোক, ক্ষোভ, দুর্ভোগ ও অবিচারের মধ্য দিয়েই জেগে উঠুক সত্যিকারের মনুষ্যত্ব। তাই তাঁর এই মহৎ উচ্চারণ—“গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!” এই উক্তি শুধুই এক আবেগময় উক্তি নয়—এ এক চেতনার আগ্নেয়গিরি, যা যুগে যুগে অপমানিত মানুষকে জাগিয়ে তুলেছে।
নজরুলের এই প্রবন্ধ আমাদের শেখায়—মুক্তি চাওয়া যায় না, তা অর্জন করতে হয়। আর সে অর্জন আসে আত্মদায়িত্ব, আত্মসংঘর্ষ ও আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে। তাঁর রচনার ভিতরে বিদ্যমান যে সত্য, তা আজও সমান প্রাসঙ্গিক—যতদিন দাসত্ব থাকবে, যতদিন মনুষ্যত্ব অপমানিত হবে, ততদিন তাঁর আহ্বান আমাদের রক্তে আগুন ধরিয়ে যাবে।
প্রতিবাদ মূলক প্রবন্ধ
নজরুল ইসলামের ‘নবযুগ’ প্রবন্ধের অন্তর্গত যে তিনটি প্রবন্ধ ইংরেজ সরকারকে তীব্রভাবে ক্ষুব্ধ করে তোলে, সেগুলি হল— ‘ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ’, ‘মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?’ এবং ‘কালা আদমীকে গুলি মারা’। এই তিনটি রচনা রাজনৈতিকভাবে যতটা দুঃসাহসিক, সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকেও ঠিক ততটাই বলিষ্ঠ, ব্যঙ্গধর্মী ও বিপ্লবসঞ্জাত।
এর মধ্যে ‘ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ’ একটি নিপুণ ব্যঙ্গাত্মক রচনা, যা নিছক ব্যঙ্গ নয়, বরং ব্যঙ্গকে অস্ত্র করে এক জাগরণমন্ত্র রচনা। প্রবন্ধটি সম্পর্কে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ আজাহারুদ্দীন খান যথার্থই মন্তব্য করেছেন— “ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ পুরোপুরি ব্যঙ্গাত্মক রচনা, যাকে বলা হয় ‘negative approach’ দিয়ে ‘positive gain’ করা।” এই প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম এক ভয়াবহ ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে ভারতবাসীর শৈথিল্য, ভীরুতা ও নীরবতার বিরুদ্ধে ধিক্কার ছুঁড়ে দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট করে বোঝাতে চেয়েছেন যে, যতদিন না জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্তাক্ত ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ভারতবাসী প্রতিরোধের বারুদে জেগে উঠবে, ততদিন স্বাধীনতা শুধুই অলীক কল্পনা।
জেনারেল ডায়ার ছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক পৈশাচিক রূপ, যার হাতে ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র ভারতীয়দের উপর চালানো গণহত্যা কেবল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতার চূড়ান্ত নিদর্শন নয়, ভারতীয়দের আত্মমর্যাদার উপরও এক অগ্নিপরীক্ষা ছিল। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেই রক্তপিপাসু হত্যাকারীর জন্য স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের ধারণা ভারতবাসীর মনে স্থান পেতে পারে! নজরুল এই ধারণাকেই ব্যঙ্গের তীরে বিদ্ধ করেছেন, তবে সে ব্যঙ্গ নিছক বিদ্রূপ নয়—তাতে আছে গভীর রাজনৈতিক প্রতীক ও অন্তর্জাগরণের আহ্বান।
তাঁর মতে, অত্যাচারীর স্মৃতিস্তম্ভ দাঁড় করিয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়ানোই শ্রেয়, যাতে জাতি প্রতিদিন সেই রক্তস্নাত স্মৃতি দেখেও যদি চেতনার ঘুম ভাঙাতে পারে, তবে তা জাতির পক্ষে মঙ্গলজনক। সেই কারণেই তিনি ব্যঙ্গের সুরে প্রস্তাব রেখেছেন—
“দুশমন ডায়ারকে বাদ দিলে চলিবে না। ইহার যে স্মৃতিস্তম্ভ খাড়া করা হইবে তাহার চূড়া হইবে এত উচ্চ যে ভারতের যে কোনো প্রান্তর হইতে তা যেন স্পষ্ট মূর্ত হইয়া চোখের সামনে জাগিয়া ওঠে।”
তাঁর এই বক্তব্য যেন জাতির ভেতর থেকে গভীর ঘুম কাটিয়ে তোলার এক সাংঘাতিক হাতুড়ি।
ডায়ারের রক্তমাখা নাম যেন জাতির রক্তচক্ষু খোলার প্রতীক হয়ে উঠুক—এই ছিল নজরুলের অন্তর্জাগতিক কামনা। তিনি চেয়েছেন, ভারতবাসী যেন এই স্মৃতিস্তম্ভ দেখেই শিখে নেয় অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে, আত্মসম্মান রক্ষায় প্রাণ দিতে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠে আওয়াজ তুলতে। কবির ভাষায়—
“এ ডায়ারকে ভুলিব না, আমাদের মুমূর্ষু জাতিকে চিরসজাগ রাখিতে যুগে যুগে এমনই জল্লাদ কশাই এর আবির্ভাব মস্ত বড়ো মঙ্গলের কথা। ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ যেন আমাদিগকে ডায়ারের স্মৃতি ভুলিতে না দেয়।”
এই দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে অভিনব, শাণিত ও আদর্শবাদী।
তাঁর ব্যঙ্গের মধ্যে নিহিত আছে গভীর বেদনাবোধ, জাতীয় অপমানের জ্বালা এবং আত্মমর্যাদা হারানোর যন্ত্রণার চিরন্তন স্মৃতি। ভারতবাসী যে দিনের পর দিন ইংরেজদের শাসন, অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার হয়ে নিজের আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিচ্ছে, সেই বাস্তবতা তাঁকে গভীরভাবে আহত করেছিল। তিনি বুঝেছিলেন, প্রতিবাদের ভাষা না থাকলে, আত্মসম্মানের অনুভূতি যদি না জাগে, তবে স্বাধীনতা একটি মরীচিকামাত্র। সেই কারণেই ডায়ারের মতো রক্তপিপাসু শত্রুর স্মৃতিকে জীবিত রাখা প্রয়োজন, যাতে জাতি নিজের রক্তাক্ত ইতিহাস ভোলে না। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন—
“ইহার জন্য আমাদের সর্বাগ্রে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। নতুবা আমরা অকৃতজ্ঞতার বদনামের ভাগী হইব।”
এই যে ঝাঁকুনি দিয়ে জাতিকে জাগিয়ে তোলার প্রয়াস, এই যে চেতনার মৃতপ্রায় নদীতে ঢেলে দেওয়া বিদ্যুৎধারা—এই সাহস, এই শাণিত কলমই নজরুলকে বাংলার ‘বিদ্রোহী কবি’ করে তুলেছিল। তাঁর ভাষা যেমন বাঙময়, তেমনি দাহপ্রবণ; তাঁর ব্যঙ্গ যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি উদ্দেশ্যবাহী। ‘ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ’ কোনো অকারণ রসবোধের ফল নয়; এটি এক অন্তর্জাগরণের কৌশলী সাহিত্যিক কৌশল, যেখানে এক ‘negative approach’-এর ভিতর দিয়েই তিনি জাতিকে ‘positive gain’-এর পথে চলতে অনুপ্রাণিত করেছেন।
সত্যিই, নজরুলের এই লেখাটি আমাদের শেখায়—ব্যঙ্গ কখনো নিছক রস নয়; ব্যঙ্গ হতে পারে এক জাতীয় অস্ত্র, যার আঘাতে কেঁপে উঠে ঘুমন্ত জাতির বিবেক। ডায়ারকে ভুলে গেলে নয়—তাকে মনে রেখেই এগিয়ে যেতে হবে, যেন তাঁর মতো অন্যায়ের প্রতিচ্ছবি সামনে রেখে চেতনায় জাগে প্রতিবাদের অগ্নি। এই অগ্নিই মুক্তির আলো।
নজরুল ইসলামের কলম কখনো শুধু কবিতার অলংকারে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং অত্যাচার, শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাঁর কলম ছিল তীক্ষ্ণ তরবারির মতো। ‘মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?’ ও ‘কালা আদমিকে গুলি মারা’—এই দুটি নিবন্ধ সেই সাহসী প্রতিবাদেরই জীবন্ত নিদর্শন, যেখানে তিনি যুক্তি, ন্যায়বোধ এবং আবেগের সম্মিলনে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন।
‘মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?’ প্রবন্ধটি একটি বাস্তব ও মর্মন্তুদ ঘটনার প্রেক্ষিতে রচিত। ঘটনাটি ঘটে কাঁচাগাড়ী নামক স্থানে, যেখানে কিছু মুহাজির—অর্থাৎ স্বদেশত্যাগে ইচ্ছুক জনগোষ্ঠী—সামরিক পুলিশের সঙ্গে একটি গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়েন। সেই ঘটনার পরিণতিতে তিনবার গুলিচালনা করা হয়, কিন্তু সরকারি হিসেবে দেখা যায় মাত্র একজন নিহত ও একজন আহত। এই তথ্যকে নজরুল প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। তাঁর মতে, এমন একটি সংখ্যাগত অসমতা—তিনবার গুলিচালনা আর মাত্র দুইজন হতাহত—নিশ্চয়ই বিশ্বাসযোগ্য নয়।
তিনি প্রশ্ন তোলেন, “একটি আঘাতের বদলেই তিন-তিনবার গুলিবর্ষণ করা, এ কোন সভ্য সমাজের রীতি?” তাঁর যুক্তি ছিল পরিষ্কার—এই মুহাজিররা অপরাধী হলে, তাদের গ্রেফতার করা যেত। কিন্তু তা না করে তাঁদের ওপর গুলি চালানো হয় কেন? তিনি ব্যঙ্গ করে বলেন, এই মুহাজিরেরা তো নিজের দেশ, পরিবার, সমাজ সবকিছু ত্যাগ করে কেবলমাত্র স্বাধীনতার বাসনায় নিজেকে মুক্ত করতে চেয়েছিল, অথচ সেই অসহায় মানুষের দেহেই চালানো হল দমনমূলক বুলেট। এই ঘটনাটি কেবল একটি হত্যাকাণ্ড নয়, বরং একটি নিগৃহীত জনগোষ্ঠীর আত্মমর্যাদাকে পদদলিত করার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, যা নজরুলের বিবেক ও কলমকে স্তব্ধ থাকতে দেয়নি।
অন্যদিকে, ‘কালা আদমিকে গুলি মারা’ শীর্ষক নিবন্ধটিও ছিল আরও একটি তীব্র প্রতিবাদের দলিল, যেখানে নজরুল ভারতীয়দের উপর ব্রিটিশ শাসকদের বর্ণবাদী মনোভাব এবং নির্মমতার নগ্ন বাস্তবতা প্রকাশ করেছেন। ইংরেজদের চোখে কালা আদমি ছিল কেবল একটি ব্যবহারযোগ্য প্রাণীমাত্র—যাদের মানবাধিকার বলে কিছু নেই, যাদের হত্যা করলে বিচার হয় না, আর যাদের বাঁচানো রাষ্ট্রের দায় নয়।
তিনি তীব্র ভাষায় লিখেছেন, এই কালা আদমি-চিন্তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূল ভিত্তি। অন্যদিকে, সাদা চামড়ার লোকদের জন্য রয়েছে বিচার, সম্মান ও আইনগত সুরক্ষা। নজরুল স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন যে, এই বৈষম্য একদিন ভারতবাসীর মধ্যে প্রতিক্রিয়ার বিস্ফোরণ ঘটাবে। তাঁর ভাষায়—
“এই একগুঁয়েমির জন্যই তো আজ এমন করিয়া হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত একটা বিপুল কম্পন শুরু হইয়া গিয়াছে।”
এই “কম্পন” বলতে তিনি দেশজুড়ে প্রতিবাদ, অসন্তোষ ও আত্মজাগরণের যে ঢেউ উঠতে শুরু করেছে তা বোঝাতে চেয়েছেন।
এ প্রবন্ধে নজরুল কেবল ঘটনার বর্ণনা দেননি; বরং বিশ্লেষণ করেছেন, সমালোচনা করেছেন, এবং চরম সাহসিকতার সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর মতে, কেবল কয়েকজনের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা থাকা মানেই তা অসীম দমনশক্তির বৈধতা নয়। তিনশো জন ইংরেজ তিনত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে অবহেলা করে, ঘৃণা করে, চাবুকের ঘায়ে শাসন করবে—এমন যুগ আর নেই, এমন বর্বরতা আর চলতে পারে না।
প্রবন্ধে তিনি স্মরণ করিয়েছেন শাস্ত্রী মহাশয়ের আবেদনকে—যেখানে বলা হয়েছিল, গুলি চালানোর আগে ম্যাজিস্ট্রেট বা সুপারিন্টেনডেন্টের অনুমতি বাধ্যতামূলক করতে হবে, নতুবা ঘটনার উপযুক্ত প্রমাণ দিতে হবে। কিন্তু সেই যুক্তিযুক্ত আবেদনও লাটসাহেবের অহংকারের কাছে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের শিকার হয়েছে। এই অবহেলার বিরুদ্ধে নজরুল তাঁর কলমকে মশালের মতো উঁচিয়ে ধরেন।
নজরুলের এই লেখাগুলি কেবল কাগজে ছাপা প্রতিবাদ নয়, বরং একটি নিরস্ত্র জাতির অস্তিত্বের আর্তনাদ, বিবেকের ক্রন্দন এবং বিদ্রোহের ডাক। তাঁর ভাষা কখনো তীব্র, কখনো রক্তাক্ত, কখনো বিদ্রুপময়, আবার কখনো মমতার সুরে ভরপুর। কিন্তু সর্বত্রই স্পষ্ট একটি বার্তা—ভারতবর্ষ আর চুপ থাকবে না। ঘুমন্ত আত্মা জেগে উঠছে। অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে নতুন প্রজন্ম। স্বাধীনতার জন্য, সম্মানের জন্য, এবং মানবাধিকারের জন্য এই যুদ্ধ চলবেই।
এই দুই নিবন্ধ নিঃসন্দেহে নজরুলের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, ন্যায়ের প্রতি অবিচল প্রতিশ্রুতি এবং জাতির প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতার এক ঐতিহাসিক দলিল হয়ে রইল। এগুলি শুধু প্রতিবাদ নয়, এগুলি হয়ে উঠেছে একটি যুগের বিবেক।
নবযুগের মুক্তি ও বিশ্বসৌহার্দ্যের উদ্বোধন
এই পর্যায়ের অন্তর্গত যে সকল প্রবন্ধ, তা হলো— ‘নবযুগ’, ‘ধর্মঘট’, ‘লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য’, ‘বাংলা সাহিত্যে মুসলমান’ ও ‘ছুৎমার্গ’। ‘নবযুগ’ প্রবন্ধটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, যেখানে দেখা গেছে যে কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও মানবতার পটভূমিতে নবযুগের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়—সামাজিক, ধর্মীয় ও মানবিক জাগরণ ছাড়া প্রকৃত মুক্তির স্বাদ পাওয়া সম্ভব নয়।
তাঁর ‘ধর্মঘট’ শীর্ষক প্রবন্ধটি ছিল এক বলিষ্ঠ আত্মঘোষণা, যা শ্রমজীবী মানুষের প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতার প্রকাশ। তিনি অনুভব করেছিলেন, সমাজের যাবতীয় উৎপাদন, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভিত্তিভূমি হল এই পরিশ্রমজীবী মানুষরা—চাষা, কুলি, মজুর, খনি শ্রমিক কিংবা রুটির দোকানের পেশাদার। অথচ এই মানুষগুলিই যুগের পর যুগ ধরে অবহেলিত, অপমানিত ও শোষিত। সমাজের উচ্চবিত্ত বা ধনপতিরা তাদের রক্ত-ঘামে গড়া সম্পদের উপর ভর করে আয়েশি জীবন যাপন করে, কিন্তু যারা সেই সম্পদের জন্ম দেয়, তাদের ভাগ্যে জোটে অনাহার, বঞ্চনা ও মৃত্যু।
এই প্রবন্ধের শুরুতেই নজরুল কৃষক-শ্রমিকের দুর্দশা তুলে ধরেন, আর সেই সঙ্গেই গণতান্ত্রিক চেতনার জন্মকেও অনিবার্য করে তোলেন। তাঁর হৃদয়বিদারক চিত্রণে উঠে আসে চাষির করুণ বাস্তব—
“চাষি সমস্ত বৎসর ধরিয়া হাড়-ভাঙ্গা মেহনত করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও দু বেলা পেট ভরিয়া মাড়ভাত খাইতে পারে না, ছেলেমেয়ের সাধ-আরমান মিটাইতে পায় না, অথচ তাহারই ধান-চাল লইয়া মহাজনরা পায়ের উপর পা দিয়া বারোমাস তেত্রিশ পার্বণ করিয়া নওয়াবি চালে দিন কাটাইয়া দেন।”
এই বর্ণনায় শুধু একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির শোষণের অভিযোগ নেই, আছে এক গভীর ব্যথা, আর সেই ব্যথা এসেছে কবির নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। কারণ নজরুল নিজেই ছিলেন শ্রমজীবী সমাজের সন্তান। তিনি রুটির দোকানে কাজ করেছেন, সৈনিক হয়েছেন, কুলি-মজুরদের সঙ্গে ঘাম ঝরিয়েছেন। ফলে শ্রমজীবী মানুষের প্রতি তাঁর মমতা কেবল ভাবনাজাত নয়, তা ছিল তাঁর রক্তমাংসের সত্য।
তিনি দেখেছেন কয়লাখনির কুলিরা কেমন করে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে শিল্পপতিদের কোটি টাকার সম্পদ গড়ে তোলে। অথচ তাদের জন্য পড়ে থাকে না একটুকরো সম্মান, এক ফোঁটা ন্যায়বিচার বা সামান্য সুরক্ষা। প্রবন্ধে নজরুল বিদ্রুপ করে বলেন, কলকারখানার মালিকদের মুখে Larger Humanity-র বুলি থাকলেও, হৃদয়ে তার লেশমাত্র নেই। তাঁরা নিজ নিজ ভোগ-বিলাসে ব্যস্ত, আর শ্রমিকদের কান্না বা অভাব-অভিযোগ তাদের মন ছুঁয়েই না।
এই পরিস্থিতির প্রতিবাদে, যখন শ্রমিকরা রাস্তায় নামে, ধর্মঘটের ডাক দেয়, তখন তা শুধুই অর্থনৈতিক দাবি নয়—তা এক বিপুল আত্মমর্যাদার ঘোষণাপত্র। নজরুল তাই লিখেছেন—
“সবারই অন্তরে একটা বিদ্রোহের ভাব আত্ম-সম্মানের স্থূল সংস্করণ রূপে নিদ্রিত থাকে, যেটা খোঁজা খাইয়া জর্জরিত না হইলে মরণ-কামড় কামড়াইতে আসে না। এ অভাগাদের বেদনার বোঝা নেহাত অসহ্য হওয়াতেই তাহাদের এ বিদ্রোহের মাথা ঝাঁকানি।”
এই আত্মজাগরণের কথা বলতে গিয়ে নজরুল ইউরোপ ও আমেরিকার দৃষ্টান্ত টানেন। সেখানে গণতন্ত্রের সূর্য উঠেছে, শ্রমজীবী মানুষ নিজের অধিকার রক্ষা করতে শিখেছে। ডিমোক্র্যাসি বা গণতন্ত্র সেখানে সর্বময় শাসনপদ্ধতি। সেই গণতান্ত্রিক জাগরণ নজরুল স্বপ্ন দেখেছেন ভারতবর্ষের মাটিতেও।
নজরুলের ‘ধর্মঘট’ প্রবন্ধটি নিছক রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দলিল নয়, বরং এক বিপুল আবেগ, দ্রোহ ও মানবিক চেতনার সাহিত্যিক রূপায়ণ। এটি একদিকে যেমন শোষিত মানুষের জাগরণের মন্ত্র, অন্যদিকে তেমনি শোষকদের হৃদয় কাঁপিয়ে দেওয়ার এক সতর্কবার্তা। তিনি বুঝেছিলেন—শ্রমিক শ্রেণি যদি জেগে ওঠে, তবে আর কোনো ক্ষমতা তাকে শাসন করতে পারবে না। কারণ উৎপাদনশীলতা, কর্মশক্তি ও সাংগঠনিক সংহতি যদি একই সঙ্গে বিকশিত হয়, তাহলে সে শক্তিকে আর দমিয়ে রাখা যায় না।
এই প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম একাধারে ছিলেন দার্শনিক, কল্পনাপ্রবণ স্বাপ্নিক ও বাস্তবজীবনের সৈনিক। তাঁর সাম্যবাদ ছিল যুক্তির কাঠামোতে নয়, বরং হৃদয়ের অগ্নিগর্ভ আবেগে। তাই আজও তাঁর কথাগুলি শোনালে মনে হয়—এ যেন কেবল ইতিহাসের দলিল নয়, এক অপ্রকাশ্য ন্যায়ের অন্বেষণের চিরন্তন আহ্বান।
কাজী নজরুল ইসলাম ব্যক্তি জীবনে কেবল কবি বা সাহিত্যিক ছিলেন না—তিনি ছিলেন চিন্তার বিক্ষোভে দীর্ণ এক বিপ্লবী মনন। তাঁর ভাবনায়, বক্তব্যে, বিশ্বাসে, এমনকি শিল্পসৃষ্টির ছত্রে ছত্রে জ্বলজ্বল করে জেগে ওঠে দ্রোহের স্পন্দন। নিছক তাত্ত্বিক বিপ্লব নয়, বরং প্রয়োজন হলে অস্ত্র তুলে নেওয়ারও সাহস রাখতেন তিনি। তাই অহিংস মতবাদকে তিনি নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা থাকলেও, রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত বিচার করে অনেক সময়েই নজরুল মনে করতেন—ইংরেজ শাসকদের উপনিবেশিক দমননীতির বিরুদ্ধে সম্মুখ সমর ব্যতীত মুক্তি অসম্ভব। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রয়োজন হলে সংগ্রাম হবে সশস্ত্র, প্রয়োজনে বিদ্রোহ হবে রক্তাক্ত।
এই প্রেক্ষিতেই তিনি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের প্রতি। তিলক ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বলিষ্ঠ এবং আপসহীন যোদ্ধা, যিনি শুধু মত ও বুদ্ধির মাধ্যমে নয়, বিপ্লবী মনোভাব ও প্রত্যক্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন। নজরুল তাঁর জীবন-দর্শনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েছিলেন, এবং স্বভাবতই যখন এই মহান নেতার মৃত্যু ঘটে, তখন কবির অন্তর কেঁপে ওঠে শোক ও দ্রোহে। সেই গভীর বেদনার অভিব্যক্তিতে নজরুল বলেন—
“বুঝি সারা বিশ্বের বুকের স্পন্দন থামিয়া গিয়াছে! এই স্তম্ভিত নিস্তব্ধতাকে ব্যথা দিয়া সহসা লক্ষ কন্ঠের ছিন্ন— ক্রন্দন কারবালা মাতমের (কারবালার শোকাচ্ছ্বাস) মতো মোচড় খাইয়া উঠল, হায় তিলক! ওরে এ কোন অসহনীয় ক্রন্দন?”
তিলকের মৃত্যু নজরুলের দৃষ্টিতে শুধু এক ব্যক্তির প্রস্থান ছিল না, বরং তা ছিল ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবন থেকে এক প্রধান স্তম্ভের ভেঙে পড়া। তিনি তাই ভয় না পেয়ে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে আহ্বান করেছিলেন একত্রে এসে এই জাতীয় বিপর্যয়ের মুহূর্তে হাতে হাত মিলিয়ে দাঁড়াতে। তাঁর আহ্বান ছিল এক আন্তরিক, হৃদয়গ্রাহী অনুরোধ—
“ওরে ভাই আজ যে ভারতের একটি স্তম্ভ ভাঙিয়া পড়িল! এ পড়-পড় ভারতকে রক্ষা করিতে এই মুক্ত জাহ্নবীতটে দাড়াইয়া, আয় ভাই আমরা হিন্দু-মুসলমান কাঁদ দিই। নহিলে এ ভগ্নসৌধ যে আমাদেরই শিরে পড়িবে ভাই। আজ বড় ভাইকে হারাইয়া এই একই বেদনাকে কেন্দ্র করিয়া, একই লক্ষে দৃষ্টি রাখিয়া যেন আমরা ভাইকে, পরস্পরকে গাঢ় অবলম্বন করি।”
এই উক্তির মধ্যে নজরুল যেমন জাতীয় ঐক্যের কথা বলেন, তেমনই তার অভ্যন্তরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এক আন্তঃধর্মীয় সহাবস্থানের মর্মবাণী। তাঁর কাছে জাতির শোক কেবলই কান্নার কারণ নয়, বরং তা এক অভিন্ন সংগ্রামের ভিত্তি হতে পারে।
অন্যদিকে, ‘বাংলা সাহিত্যে মুসলমান’ প্রবন্ধে নজরুল যে প্রস্তাবনাগুলি দিয়েছেন, তা শুধু সাহিত্যিক বক্তব্য নয়—তা ছিল মুসলমান সমাজের আত্মচেতনাকে জাগ্রত করার এক সাহসী প্রচেষ্টা। একটি বিশেষ সময়ে, যখন বাংলার মুসলমানরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে নিজেদের স্থান নিশ্চিত করতে সংগ্রাম করছিল, নজরুল তখন তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এক পথপ্রদর্শকের মতো। তিনি শুধু সাহস দেননি, দিয়েছেন সৌন্দর্যের মাপকাঠিও।
ড. সুশীলকুমার গুপ্ত যথার্থই মন্তব্য করেছেন—
“বাংলা সাহিত্যে মুসলমান প্রবন্ধে নজরুলের সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায় বলে এটি খুবই মূল্যবান। নজরুলের সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ প্রাণবন্ত প্রবলতা, জড়তাশূন্য ও স্বভাব প্রনোদিত গতি এবং মুক্তির অকাঙ্খাজনিত বিদ্রোহ। তাঁর সাহিত্য তত্ত্বের ধারণাতেও এই লক্ষণগুলি পরিস্ফুট।”
নজরুল বিশ্বাস করতেন, সাহিত্য কেবল শব্দের খেলা নয়—তা হতে হবে জীবনের জীবন্ত প্রকাশ। তিনি সাহিত্যিকদের উদ্দেশ্যে বলেন—
“যে সাহিত্য জড়, যাহার প্রাণ নাই, সে নির্জীব সাহিত্য দিয়া আমাদের কোনো উপকার হবে না, আর তাহা স্থায়ী সাহিত্যও হইতে পারে না।”
এই নির্জীবতার বিপরীতে তিনি চেয়েছেন এক উচ্ছ্বল, প্রাণময়, গতিময় সাহিত্য। সাহিত্যিকের কলমে থাকা চাই জীবনের আনন্দ, চলমানতার স্বরলিপি, ও চেতনার ঝংকার। একথা বলার পেছনে তাঁর নিজস্ব জীবনদর্শনের ছাপ স্পষ্ট। তিনি মনে করতেন, সাহিত্যিকের দেহ-মনে যদি থাকে জড়তা, তবে তার রচনায় তা অনিবার্যভাবেই প্রতিফলিত হবে। তাই তিনি বলেছিলেন—
“সাহিত্যকে এই প্রাণের সোনার কাঠি দিয়া জাগাইবার যে জাদুশক্তি ইহা লাভ করিতে হইলে আমাদের তরুণ সাহিত্যিক সম্প্রদায়কে সর্বপ্রথম শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হবে। শরীর নীরোগ হইলে মনে আপনি একটা বিমল আনন্দ উছলিয়া পড়িতে থাকে।”
এই বক্তব্য নিছক স্বাস্থ্য-চিন্তা নয়, বরং একটি বৃহত্তর জীবনদর্শনের অংশ। শরীর ও চিত্তের মধ্যে সুসমন্বয় স্থাপনের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে সৃষ্টিশীলতা। ইউরোপের সাহিত্যিকরা খেলাধুলা ও দেহচর্চার মাধ্যমে চিত্তকে উজ্জ্বল করে তোলেন, ফলে তাদের সাহিত্যে থাকে দীপ্তি ও শক্তি। আর আমাদের সমাজে থেকে যায় সংকীর্ণতা, ভণ্ডামি ও কুসংস্কার, যার ফলে সাহিত্যে আসে দুর্বলতা ও ক্ষীণতা।
নজরুল মনে করতেন, সাহিত্য কেবল নিজ জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে তা পূর্ণতা পায় না। তাকে পৌঁছাতে হবে বিশ্বমঞ্চে, বিশ্বের পাঠকের হৃদয়ে। তবে সেই সর্বজনীনতা যেন নিজের জাতীয়তা বা সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে না আসে—বরং তার ভিত্তিতেই গড়ে উঠুক সেই বিশ্বমানবিক সাহিত্য।
এইভাবে, ‘বাংলা সাহিত্যে মুসলমান’ প্রবন্ধে নজরুল মুসলিম তরুণ সাহিত্যিকদের যে দিশা দেখিয়েছেন, তা আজও আমাদের সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে পথনির্দেশক হয়ে আছে। তিনি সাহিত্যকে দেখেছেন কেবলই শব্দের বুনট হিসেবে নয়, বরং জীবনের চলমান স্রোতের এক জীবন্ত ও মুক্ত অভিযাত্রা হিসেবে।
‘ছুঁৎমার্গ’ প্রবন্ধে নজরুল ইসলামের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে এক স্পষ্ট প্রতিবাদ—সামাজিক বর্ণবিভাজন ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে। তিনি আঙুল তুলেছেন সেই সাম্প্রদায়িক সংস্কারের দিকে, যেখানে হিন্দু ও মুসলমান—এই দুই ধর্মীয় গোষ্ঠী একই মানবসমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে ছুঁৎমার্গ ও অশুচিতার প্রাচীর তুলে। নজরুল গভীর বেদনা নিয়ে বুঝিয়েছেন, হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই একমাত্র প্রকৃত পরিচয়—তারা মানুষ। ধর্ম বা সম্প্রদায়ের পরিচয় মানুষের পরবর্তী, মৌলিক নয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, এই দুটি জাতির মধ্যে ধর্মীয় পরিচিতির চেয়ে মানবিক সংযোগ দুর্বল; বরং ছোঁয়াছুঁয়ির কৃত্রিম নিয়মেই এদের মধ্যে বিভেদের দেয়াল আরও শক্ত হয়ে ওঠে।
এই সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নজরুল বিশ্বজনীন সত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তাঁর বিশ্বাস, ধর্ম যদি সত্য হয়, তবে তা কেবল নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর সম্পত্তি হতে পারে না—তা হবে সবার, সর্বত্রের। তাই তিনি সংকীর্ণচিত্তের মানুষের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানান,
“হিন্দু হিন্দু থাক, মুসলমান মুসলমান থাক, শুধু একবার এই মহাগগন তলের সীমাহারা সৃষ্টির মাঠে দাঁড়াইয়া— মানব-! তোমার কণ্ঠে সৃষ্টির সেই আদিম বাণী ফুটাও দেখি। বল দেখি–‘আমার মানুষ ধর্ম।’ দেখিবে দশদিকে সার্বভৌমিক সাড়ার আকুল স্পন্দন কাঁপিয়া উঠিতেছে।”
এখানে নজরুল ধর্মের নিজস্বতা অস্বীকার করছেন না, বরং তিনি তার মধ্যে মানবিকতা, উদারতা ও সৌহার্দ্যের যে সার্বজনীন ব্যঞ্জনা, তাকেই প্রধান করে তুলতে চাইছেন। তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে এক বৈপ্লবিক মানবতাবাদের ভাষা, যেখানে মানুষ পরিচিত হবে তার মনুষ্যত্বের মাধ্যমে, জাতি বা সম্প্রদায়ের মাধ্যমে নয়।
‘উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন’ প্রবন্ধে নজরুল আরও একধাপ এগিয়ে অবহেলিত, নিপীড়িত জনসমষ্টির কথা তুলে ধরেছেন। সেই সমস্ত মানুষ, যারা সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থান করে এবং যাদের ‘ছোটলোক’, ‘দলিত’ বা ‘অস্পৃশ্য’ বলে সমাজ তাদের দূরে ঠেলে দিয়েছে—তাঁদের কথা ভোলেননি নজরুল। তিনি বুঝেছিলেন, সংখ্যায় এরা দেশের বৃহত্তর অংশ, যাদের শ্রম ও রক্তে সমাজের কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে। অথচ শ্রেণিগত ও বর্ণগত অহঙ্কারে উচ্চবর্গের মানুষ তাদের মানুষ বলেও গণ্য করেন না।
এই অবিচারের প্রতিবাদে নজরুল বলেছিলেন—
“কিন্তু যদি একবার আমাদের এই জনশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পার, তাহাদিগকেও মানুষ বলিয়া ভাই বলিয়া কোল দিবার তোমার উদারতা থাকে, তাহাদিগের শক্তির উন্মেষ করিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে তুমি শত বৎসর ধরিয়া প্রাণপণে চেষ্টা সত্ত্বেও যে কাজ করিতে পারিতেছ না, একদিনে সেই কাজ সম্পন্ন হইবে।”
এই বক্তব্যে নজরুল কেবল সামাজিক বিচার চাননি, তিনি চেয়েছেন নেতৃত্বের পরিবর্তন, শক্তির অভিমুখ বদলে যাক, যেন সমাজের প্রান্তিক মানুষরাই হয়ে ওঠে নবজাগরণের ধ্বজাধারী। এখানে তিনি রূঢ় সত্যটিকেই সামনে এনেছেন—আভিজাত্যের বাহ্যিক মোড়কে সমাজের প্রকৃত চালক হয়ে উঠবে না কেউ, যতদিন না সেই ‘উপেক্ষিত’ শক্তিকে মর্যাদা দিয়ে তার যথার্থ অবস্থান ফিরিয়ে দেওয়া হয়।
‘মুখবন্ধ’ প্রবন্ধে নজরুল মুখ খুলেছেন আমলাতন্ত্রের দুর্বৃত্তপনা ও শাসনতান্ত্রিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে। অসহযোগ আন্দোলনের আবহে গোটা দেশ যখন স্বাধীনতার দাবিতে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে, তখন তৎকালীন শাসকের দলদাস আমলারা জনগণের কণ্ঠ রোধ করার পাঁয়তারা শুরু করে। প্রশাসন বুঝে যায়—এই জেগে ওঠা জনসাধারণকে আর বেশিদিন বোকা বানিয়ে রাখা যাবে না। কিন্তু চিরকাল যারা আজ্ঞাবহ ছিল, তাদের পক্ষে সত্যভাষণের ভাষা মেনে নেওয়া সহজ নয়। তাই তারা শুরু করে ভয় দেখানো, হুমকি, দমন-পীড়ন।
কিন্তু নজরুল জানেন, জাগ্রত চেতনার পথ আটকানো যায় না। তাই তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উচ্চারণ করেন—
“জোর জবরদস্তি করিয়া কি কখনও সচেতন জাগ্রত জনসংঘকে চুপ করানো যায়? যতদিন ঘুমাইয়া ছিলাম বা কিছু বুঝি নাই, ততদিন যাহা করিয়াছ সাজিয়াছে; এতদিন মোয়া দেখাইয়া ছেলে ভুলাইয়াছ, এখনও কি আর ওরকম ছেলেমানুষি চলিবে মনে কর?”
এই প্রশ্নে রয়েছে প্রচণ্ড ব্যঙ্গ, আবার রয়েছে এক গর্জন—জনগণ আর শিশু নেই। আর নয় চুপ করে সহ্য, আর নয় মোয়ায় ভুলে থাকা। জনগণের ভিতরে যে বিদ্রোহ জন্ম নিয়েছে, তা আর কেবল স্বপ্ন নয়, তা সত্যের মশাল নিয়ে জ্বলতে শুরু করেছে। প্রশাসনের প্রতিটি অপচেষ্টা এখন তাদের কাছে বুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে।
এই তিনটি প্রবন্ধে নজরুল একাধারে সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক সংগ্রামের যে রূপরেখা এঁকেছেন, তা একশত বছর পরেও আমাদের চেতনায় প্রাসঙ্গিক, প্রজ্জ্বলিত। তাঁর কলমে তাই শুধুই প্রতিবাদ নয়—তা এক নিরস্ত্র বিপ্লব, এক তর্জনী নির্দেশ, যা এখনও আমাদের সমাজ, সাহিত্য ও রাজনীতিকে প্রশ্ন করে, নাড়া দেয়, জাগিয়ে তোলে।
‘রোজ-কেয়ামত বা প্রলয়দিন’ প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম কেবল ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক প্রলয়ের ধারণাকেই কেন্দ্রে রাখেননি; তিনি সেখানে যুক্ত করেছেন একটি বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গিও। নজরুল বোঝাতে চেয়েছেন, আধুনিক বিজ্ঞানের আলোচনাও আজ সেই মহাপ্রলয়ের সম্ভাবনা তুলে ধরছে, যার পূর্বাভাস আমরা ইতোমধ্যেই পাচ্ছি পৃথিবীর নানা প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে।
বিশেষত জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রেক্ষিতে নজরুল দক্ষিণ মেরুর ভয়াবহ ভবিষ্যতের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি লেখেন—
“এখন এই যে দক্ষিণ মেরুর আবহাওয়া এই রকমে ক্রমেই অসহ্য উষ্ণ হইয়া উঠিতেছে, ইহার পরিণাম কী? সুতরাং দক্ষিণ মেরুর এই অত্যধিক উষ্ণতার দরুন সেখানের ওই সহস্র সহস্র যোজন-ব্যাপী তুষারের মহাপর্বত সমূহ ভাঙিয়া গলিয়া যাইবে।”
এই বাক্যের মধ্যে নজরুলের বিজ্ঞানভাবনার গভীরতা ও বিশ্বদৃষ্টি প্রকাশ পায়। তিনি বুঝেছিলেন, প্রাকৃতিক ভারসাম্যের এই বিপর্যয় কেবল একটি ভৌগোলিক ঘটনা নয়, বরং তা বিশ্বব্যাপী বিপদের পূর্বাভাস। আজ যাকে আমরা বলি ‘গ্লোবাল ওয়ার্মিং’, সেই সংকটের ইঙ্গিত নজরুল তাঁর লেখায় আগেভাগেই তুলে ধরেছিলেন। তাঁর এই দূরদৃষ্টি কেবল সাহিত্যিক ভাবনায় সীমাবদ্ধ ছিল না; তা ছিল বাস্তব অভিজ্ঞতা ও যুক্তিবোধের উপর নির্মিত।
অপরদিকে, ‘বাঙালীর ব্যবসাদারি’ শীর্ষক প্রবন্ধে নজরুল উপহাসের সুরে ব্যঙ্গ করেছেন সেইসব ব্যবসায়ী বাঙালিদের, যারা স্বজাতির পরিচয় লুকিয়ে ইংরেজি বা খ্রিস্টীয় নাম ধারণ করে বাজারে নিজের পণ্য প্রচার করে চলেছেন। জাতিগত ও সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় বিসর্জন দিয়ে তারা যেন একরকম ভেকধারী বণিকে পরিণত হয়েছে। নজরুল এই প্রবণতার কড়া সমালোচনা করেন, কারণ এতে আত্মমর্যাদা হারিয়ে যায়, ব্যবসারও দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি হয়।
এই প্রসঙ্গে নজরুল কটাক্ষ করে বলেন—
“এই রূপে কৃষ্ণকে ক্রিষ্টো রূপে বাজারে বসাইয়া কতটা সুবিধা হয় জানিনা, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, ইহাতে অসুবিধাটাই হয় বেশি।”
এই একটি বাক্যে তিনি ব্যবসার নামে জাতিগত সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় মুছে ফেলার প্রবণতাকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন। একদিকে যেমন এ ধরনের ব্যবসায়িক কৌশলে জাতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাস অপমানিত হচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে বিদেশি সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণে নিজের শিকড় ভুলে যাচ্ছে বাঙালি সমাজ। নজরুলের বক্তব্য স্পষ্ট—ব্যবসার প্রসার যদি আত্মমর্যাদাহীনতায় ভর করে হয়, তবে তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।
এই দুই প্রবন্ধেই নজরুল দেখিয়েছেন তাঁর চিন্তার ব্যাপ্তি—একদিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন বিজ্ঞানের আলোকে, অন্যদিকে সংস্কৃতি ও জাতিসত্তা সংরক্ষণের প্রশ্নে উচ্চকণ্ঠ হচ্ছেন একজন জাতীয়তাবাদী চিন্তকের মতো। তিনি আমাদের মনে করিয়ে দেন, আত্মবিস্মৃতি যেমন ব্যক্তির জন্য আত্মঘাতী, তেমনি সমাজ ও জাতির পক্ষে তা ধ্বংস ডেকে আনে।
‘আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন’ প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম মানুষের জন্মগত স্বভাব ও সমাজবদ্ধ বিকৃতির মাঝে থাকা গভীর দ্বন্দ্বের কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, মানুষ জন্মসূত্রে চিরমুক্ত, স্বাধীন, এবং এক পবিত্র সত্তা। কিন্তু পরিবার, সমাজ ও সংস্কারের সংকীর্ণ জালে জড়িয়ে পড়ার পর ধীরে ধীরে তার সেই পবিত্রতা ও স্বাধীনতা ক্ষয়ে যেতে থাকে। এমন এক অন্তঃসারশূন্যতার শৃঙ্খলে বন্দি হয় সে, যাকে নজরুল ‘পরাধীনতার চাইতেও জঘন্য’ বলে আখ্যায়িত করেছেন।
বিশ্বজুড়ে বাঙালির নাম ও খ্যাতি থাকলেও, বাস্তবিক পরিসরে তারা যেন ধীরে ধীরে নিজেদের আত্মমর্যাদা হারিয়ে ফেলছে। এর পেছনে অন্যতম কারণ, বাঙালির ইংরেজ-চাকরি নির্ভর মানসিকতা। চাকরির প্রতি এই অতিরিক্ত নির্ভরতা বাঙালিকে কেবল একটি ‘নির্দেশ পালনের যন্ত্র’ করে তোলে—নিজের পায়ে দাঁড়ানোর আত্মবিশ্বাস, ব্যবসা-বাণিজ্যে সাহস, স্বাধীন উদ্যম সবই যেন হারিয়ে যায়। নজরুল এই প্রবণতাকে ধিক্কার জানিয়ে বলেন—
“আমরা দশ-পনেরো টাকার বিনিময়ে মনুষ্যত্ব, স্বাধীনতা অনায়াসে প্রভুর পায়ে বিকাইয়া দিব, তবু ব্যবসা বাণিজ্যে হাত দিব না, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে চেষ্টা করিব না। এই জঘন্য দাসত্ব আমাদিগকে এমন ছোটো হীন করিয়া তুলিতেছে।”
এই ভাষ্যে নজরুল কেবল অর্থনৈতিক দুর্বলতার দিকেই আঙুল তোলেননি, বরং তার অন্তর্নিহিত আত্মবিনাশের সংস্কৃতিকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। স্বাধীনতা হারিয়ে আত্মার গভীরে যে দীনতা বাসা বাঁধে, তা তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।
‘শ্যাম রাখি না কুল রাখি’ প্রবন্ধে নজরুল আলোচনায় এনেছেন বিহারের তৎকালীন শাসক লর্ড সিংহ বাহাদুরকে। একজন ভারতীয় হয়েও তিনি ব্রিটিশ লাটের পদলেহন করতে বাধ্য, অথচ নিজের জাতীয় জনগণের মনও রাখতে চান। এর ফলে তিনি পড়েন গভীর দ্বন্দ্বে—নিজ জাতির প্রতি দায়বদ্ধতা ও প্রভুদের আনুগত্যের মধ্যে। প্রজারা তাঁর কাছ থেকে আশাবাদী ছিলেন, তিনি অন্তত তাদের পক্ষে দাঁড়াবেন, কারণ তিনি এদেশীয়। কিন্তু লর্ড সিংহ বাহাদুর এমন পরিস্থিতির মধ্যে পড়েন, যেখানে বেশি নরম হলে প্রভুদের রোষে পড়তে হয়, আবার কঠোর হলে দেশের মানুষের প্রতিবাদে বিদীর্ণ হতে হয়। ফলে তিনি পড়েন দোটানার গভীরে— নিজে যেন এক চলমান প্রশ্নচিহ্ন হয়ে উঠেছেন: “শ্যাম রাখবেন, না কুল রাখবেন?” তাঁর অবস্থান এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, যেখানে ইংরেজরা তাঁকে নেটিভ শাসক বলে অবজ্ঞা করে, আর দেশবাসী তাঁর দূরত্ববোধে আহত হয়।
অন্যদিকে, ‘লাট প্রেমিক আলি ইমাম’ প্রবন্ধে নজরুল তীব্র ব্যঙ্গের সুরে তুলে ধরেছেন হায়দরাবাদের নিজাম-নিয়োজিত প্রধানমন্ত্রী স্যার সৈয়দ আলি ইমামের ভেতরের উপনিবেশিক আনুগত্যের নগ্ন প্রকাশ। লর্ড ও লেডি রিডিং-এর সম্মানে আয়োজিত এক ভোজসভায় আলি ইমাম তাঁর বক্তব্যে যেভাবে ব্রিটিশ শাসকদের প্রশস্তিগান গেয়ে গেছেন, তা একরকম উপনিবেশিক মনোবৃত্তির নগ্ন বহিঃপ্রকাশ। মন্টেগুর প্রশংসা করেছেন এই বলে যে, তিনি নাকি ভারতের মঙ্গলকামী ছিলেন; হার্ডিঞ্জের প্রশংসা করেছেন এই জন্যে যে, তিনি ভারতীয় সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে নাকি দেশপ্রেমিকতার নিদর্শন স্থাপন করেছেন। আর বিডিং-এর প্রশংসা করেছেন এই কারণে যে, তিনি লাট হতে এসে নাকি ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে নজরুল ক্ষোভভরে প্রশ্ন তোলেন—এইসব ‘লাটপ্রেম’ প্রদর্শনে দেশের জনগণের কী আসে যায়?
তিনি বলেন—
“রাজতন্ত্র, স্বেচ্ছাতন্ত্র বা আমলাতন্ত্রের মজাই হইতেছে এই যে, কর্তারা কেবল নিজের দিকটাই দেখেন। নিজেদের সুখ-সুবিধাটাই তাঁহাদের লক্ষ্য—বাকি সব চুলোয় যাক, তাঁহাদের সে দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই।”
এই বক্তব্যে নজরুল আসলে গোটা উপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থার এক নির্মম সত্যকে উন্মোচন করেছেন। রাজ্যশক্তি কেবল নিজের শাসনক্ষমতা টিকিয়ে রাখার দিকেই নজর রাখে—জনগণের দুঃখ, দুর্দশা কিংবা প্রতিক্রিয়া তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। আলি ইমামের ভোজসভা, প্রশংসা, লাটগান এসব কেবল একটি ‘মহল কেন্দ্রিক’ খেলা, যার সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোনও সখ্য নেই।
এই তিনটি প্রবন্ধে নজরুল স্পষ্ট করে দিয়েছেন—ভারতীয়দের আত্মপরিচয় হারানোর মূল কারণ কেবল উপনিবেশিক দাসত্ব নয়, বরং সেই দাসত্বকে মনেপ্রাণে মেনে নেওয়া, তাকে গর্বের বিষয় মনে করা, এবং নিজেদের জাতীয় সম্মান বিসর্জন দেওয়া। ব্যক্তি মাত্রেই যদি আত্মসম্মান হারিয়ে ফেলে, তবে জাতিও তার জেগে ওঠার স্বপ্ন বিস্মৃত হয়।
শিক্ষা বিষয়ক
কাজী নজরুল ইসলাম কেবল একজন বিদ্রোহী কবি কিংবা সাম্যবাদী গীতিকার ছিলেন না—তিনি একইসঙ্গে ছিলেন এক চিন্তাশীল সমাজসংস্কারক এবং শিক্ষাবিদ। তাঁর সাহিত্যকর্মের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে রয়েছে শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ, যেখানে তিনি শিক্ষা ও চেতনার সম্পর্ক, জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন এবং পরধর্মানুকরণবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরেছেন। এইসব প্রবন্ধে নজরুল জাতি গঠনের রূপরেখা কল্পনা করেছেন এমন এক সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে, যেখানে মানুষ চিন্তার স্বাধীনতা, আত্মমর্যাদা ও কর্মশীলতাকে সর্বোচ্চ স্থানে স্থান দেয়।
‘ভাব ও কাজ’ প্রবন্ধে নজরুল এক গভীর দার্শনিক তত্ত্বের বিস্তারে প্রবেশ করেছেন। তিনি বলছেন, যদিও ভাব ও কাজ দুটো শব্দ একই আত্মার দুই মুখ, তবু তাদের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক—একটি স্বপ্নময়, অপরটি বাস্তবের মাটিতে দাঁড়ানো। তাঁর মতে, ভাব একরকম সৌরভের মতো, যে সৌরভের কোনও পুষ্প নেই—এক উচ্ছ্বাসময় বিমূর্ততা, যাকে ছুঁয়ে দেখা যায় না। আর কাজ সেই ভাবকেই বাস্তবের দৃশ্যমানে রূপদান করে। কাজ ছাড়া ভাব নিছক কল্পনার খেলা। নজরুল তাই মনে করেন, ভাব যদি কর্মে রূপান্তর না হয়, তবে তার কোনও অর্থ নেই। সেই প্রেক্ষাপটেই তিনি বলেন—
“যিনি ভাবের বাঁশি বাজাইয়া জনসাধারণকে নাচাইবেন, তাঁহাকে নিঃস্বার্থত্যাগী ঋষি হইতে হইবে। তিনি লোকদিগের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও ভাবকে জাগাইয়া তুলিবেন মানুষের কল্যাণের জন্য, নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নয়।”
এই কথার মধ্যে নজরুল সমাজের সামনে এক নিঃস্বার্থ, কর্মমুখর, আদর্শবান চিন্তকের আদল তুলে ধরেছেন, যিনি নিজের ভাবনা দিয়ে জনগণকে প্রভাবিত করবেন, কিন্তু তা হোক নিঃস্বার্থভাবে, কেবল মানুষের মুক্তির জন্য।
‘সত্য-শিক্ষা’ প্রবন্ধে নজরুল বিদ্যাচর্চাকে কেবল বইয়ের পাতায় আবদ্ধ রেখে দেখেননি। তিনি শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিজাতীয় শাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর মতে, দু’চারটি স্কুল স্থাপন করলেই চলবে না, বরং দরকার একটি সুগঠিত, সংগঠিত, আত্মনির্ভরশীল জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন। রাগের মাথায় কয়েকটি ইংরেজ-বর্জিত বিদ্যালয় গড়ে তুলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। এমনকি অসহযোগ আন্দোলনের মৌসুম না এলেও—জাতীয় চেতনার কথা মাথায় রেখে বহু আগেই আমাদের নিজস্ব শিক্ষা-সংস্কৃতির ভিত গড়ে তোলা উচিত ছিল। এই প্রেক্ষাপটেই নজরুল অকপটে উচ্চারণ করেন—
“বিজাতীয় অনুকরণে আমরা ক্রমেই আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলিতেছি। অধিকাংশ স্থলেই আমাদের এই অন্ধ অনুকরণ হাস্যাস্পদ ‘হনুকরণে’ পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। পরের সমস্ত ভালো-মন্দকে ভালো বলিয়া মানিয়া লওয়া, আত্মা, নিজের শক্তি ও জাতীয় সত্যকে নেহাতই খর্ব করা হয়।”
এই বক্তব্যে নজরুল একদিকে যেমন উপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার আত্মঘাতী প্রভাব তুলে ধরেছেন, তেমনি অন্যদিকে জাতীয় আত্মপরিচয়ের অন্বেষায় নিজস্ব পথ গঠনের তাগিদ দিয়েছেন।
‘জাতীয় শিক্ষা’ প্রবন্ধে তিনি আরও তীব্রভাবে জাতীয় বিদ্যাচর্চার অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার দিকে আঙুল তুলেছেন। সেই সময় জনগণের মধ্যে একটি প্রবল শিক্ষানবেশ গড়ে উঠছিল—সরকারি বিদ্যালয়ের তুলনায় ভালো শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে অনেকেই জাতীয় বিদ্যালয় গড়ার উদ্যোগ নিচ্ছিলেন। কিন্তু নজরুল সাবধান করে দিয়েছেন—এই বিদ্যালয়গুলিকে যেন কেবল নাম পাল্টানো সরকারি বিদ্যালয়ে পরিণত না করা হয়। তাতে জাতীয় গৌরব আসে না, আসে না চিন্তাধারার কোনো স্বকীয়তা।
এই প্রসঙ্গে নজরুল তুলে ধরেছেন বন্দেমাতরম যুগের একটি ঘটনার দৃষ্টান্ত, যখন দেশি পণ্যের নামে বিদেশি পণ্যকে নতুন নামে বাজারে ছাড়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। দোকানদাররা কেবল বিলাতি জিনিসের লেবেল তুলে দেশীয় লেবেল সাঁটিয়ে দিচ্ছিলেন, কিন্তু আসল পণ্য রয়ে যাচ্ছিল আগের মতোই। এর প্রতিফলন ঘটছিল শিক্ষা ক্ষেত্রেও। এই অসাড় অনুকরণ প্রবণতার বিরুদ্ধেই নজরুল উচ্চারণ করেছেন—
“যদি আমাদের এই জাতীয় বিদ্যালয় ওই সরকারী বিদ্যাপীঠেরই দ্বিতীয় সংস্কার রূপে আত্মপ্রকাশ করে তাহা হইলে আমরা কিছুতেই উহাকে আমাদের জাতীয় বিদ্যালয় বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না, বা গৌরবও অনুভব করিতে পারি না।”
এই বক্তব্যের মাধ্যমে নজরুল কেবল বিদ্রোহ করেননি—তিনি ভবিষ্যতের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য একটি পরিশুদ্ধ মানদণ্ড নির্ধারণ করে গেছেন। তাঁর কাছে শিক্ষা মানে কেবল কিছু পাঠ্যবই পড়ানো নয়, বরং আত্মবিকাশ, জাতীয়তা, চেতনা, স্বাধীনতা ও মূল্যবোধের বিকাশ। তাঁর দৃষ্টিতে বিদ্যালয় মানে একটি রণাঙ্গন—যেখানে তরুণেরা গড়ে উঠবে মুক্তচিন্তায়, মানবতাবোধে ও নিজ জাতিসত্তার গর্বে।
কাজী নজরুল ইসলামের শিক্ষাসম্পর্কিত প্রবন্ধগুলোর অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ রচনা হল ‘জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে’। এই প্রবন্ধে তিনি অকপটে ও তীব্র ভাষায় জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও স্ববিরোধিতা তুলে ধরেছেন। তিনি লক্ষ করেছেন, যেখানে জাতীয় শিক্ষার মাধ্যমে জাতি গঠনের কথা ছিল, সেখানে বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন—কার্যত দেখা যাচ্ছে জাতীয় বিদ্যালয়গুলিতে ‘জাতীয়’ নামটিকে ব্যবহার করে কেবলমাত্র নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির পথ প্রশস্ত করা হচ্ছে। যে শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় চেতনা জাগাতে ছিল প্রতিশ্রুত, সেই ব্যবস্থায় আজ চলছে দুর্বৃত্তায়ন, এবং সেটাও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তরে—শিক্ষক নিয়োগে।
নজরুল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন, কাঁচা, অযোগ্য অধ্যাপকদের নিযুক্ত করার জন্য এক প্রকার সুপরিকল্পিত চাতুরী এবং পক্ষপাতিত্ব শুরু হয়েছে জাতীয় বিদ্যালয়গুলোতে। যাঁরা কেবলমাত্র ইংরেজের গোলামির ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে আমাদের বাহবা কুড়িয়েছেন, তাঁদের ‘জাতীয়’ আখ্যা দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনার সুযোগ করে দিতে হবে—এরকম কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। নজরুল দৃঢ় কণ্ঠে এই চক্রান্ত ও পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছেন।
এই সঙ্গে নজরুল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন—এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম কী, তার আদর্শই বা কী, কোন নীতিমালার ভিত্তিতে পাঠক্রম নির্ধারিত হচ্ছে, তার কোনও নির্ভরযোগ্য জবাব কি আছে? তার বক্তব্যে স্পষ্ট যে তিনি জাতীয় শিক্ষা বলতে কেবল ‘স্বদেশি’ লেবেল সাঁটানো কোনও ফাঁপা প্রতিষ্ঠান বোঝাতে চাননি। তিনি যে ধরনের শিক্ষার কথা ভাবছেন, তা হৃদয় ও মন, শরীর ও আত্মা—সমগ্র মানুষকে বিকশিত করতে সক্ষম। তিনি বলছেন—
“আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি এমন হউক, যাহা আমাদের জীবনশক্তিকে ক্রমেই সজাগ, জীবন্ত করিয়া তুলিবে। যে শিক্ষা ছেলেদের দেহ-মন দুইকেই পুষ্ট করে, তাহাই হইবে আমাদের শিক্ষা।”
এই উক্তি কেবল শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, বরং একটি জাতির উন্নয়নের মৌলিক ভিত্তি হিসেবেই চিহ্নিত হয়। তাঁর কাছে শিক্ষা মানেই আত্মজাগরণ, চিন্তার স্বাধীনতা ও কর্মোদ্যমের উৎস।
একই আত্মজাগরণের আহ্বান নজরুল ‘জাগরণী’ প্রবন্ধেও উচ্চারণ করেছেন। প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি কবির কণ্ঠে প্রেমিকের মতো ডাক দিয়েছেন এক কাল্পনিক চরিত্র ‘বকুল’কে—
“বকুল! জা-গো! জাগো বকুল, এই পল্লীমাঠের পথের পাশে মেঠো গানের সহজ সুরে জাগো।”
এই সরল কিন্তু চমৎকার পংক্তিতে তিনি যেন বাংলার নিস্তরঙ্গ পল্লির নিসর্গকে ডাকছেন জেগে ওঠার জন্য। কিন্তু এই ডাক কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে নয়—এ ডাক মূলত বাঙালির সুপ্ত, অলস ও আত্মনির্ভরতা হারানো জাতিচরিত্রের উদ্দেশে। সেই অলস প্রাণ, যে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হলেও কর্মে অনড়, যার হৃদয়ে বিপ্লবী চেতনা নেই, তাদের উদ্দেশে তিনি তীব্র আবেগে আহ্বান জানিয়েছেন—
“আমাদের এই শাশ্বত বাঙালির সুষুপ্ত, ঘুমে ভরা অলস প্রাণ জাগিয়ে তোলো তোমার জাগরণের সোনার কাঠি দিয়ে। তাদের ফুলের প্রাণে দাগ বসিয়ে দিয়ো তোমার মদির বাসের উন্মাদনার ছুরি হেনে।”
এই বাক্যে নজরুল তাঁর চিরপরিচিত সৃজনশীল উন্মাদনায় মিশিয়ে দিয়েছেন প্রেম, প্রত্যয়, বিপ্লব এবং দ্রোহের ধ্বনি। এ যেন এক ঐন্দ্রজালিক কবির ডাক—যে নিজের জাতিকে ঘুম পাড়ানি ছন্দে নয়, জাগরণের বিদ্যুৎঘন আবেগে জাগাতে চায়।
সার্বিকভাবে বলা যায়, এই দুই প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম কেবল শিক্ষা ও জাতীয় চেতনার তাত্ত্বিক আলোচনাই করেননি—তিনি বাস্তব সমস্যা ও নৈতিক বিচ্যুতিকে সামনে এনে এক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর গড়ে তুলেছেন। তাঁর প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি বক্তব্য পাঠকের হৃদয়ে এক প্রবল অনুরণন তোলে—কেননা তাতে রয়েছে সততা, সংবেদন এবং দেশপ্রেমের গভীর আকুতি।
‘রাজবন্দীর জবানবন্দী’: এক সাহসিক উচ্চারণের দলিল
কাজী নজরুল ইসলামের প্রাজ্ঞ ও তেজোদ্দীপ্ত রাজনৈতিক মননের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির মধ্যে অন্যতম হল তাঁর ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ‘রাজবন্দীর জবানবন্দী’। ১৯২৩ সালের ২৭ জানুয়ারি ‘ধূমকেতু’ পত্রিকায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে প্রবন্ধটি নজরুলের নিজের ছবি সংবলিত একটি পুস্তিকা আকারে আলাদা গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয় এবং ইতিহাসে এক প্রতিবাদী দলিলরূপে স্বীকৃত হয়। এটি নিছক একটি লেখা নয়—বরং এক আত্মপ্রত্যয়ী বিচারাধীন কয়েদীর কণ্ঠস্বর, যিনি আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন ঘোষণা করেছিলেন।
প্রবন্ধটির পটভূমি প্রস্তুত হয় আরও আগেই—১৯২২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর ‘ধূমকেতু’র দ্বাদশ সংখ্যায় নজরুল তাঁর অগ্নিসংবেদী কবিতা ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ প্রকাশ করেন। এই কবিতায় তিনি এক নতুন, দুর্বার, বিপ্লবী দেবীমূর্তির আহ্বান জানান, যিনি শৃঙ্খলিত ভারতবাসীকে মুক্ত করবেন। ব্রিটিশ শাসন এই কবিতার মধ্যে রাজদ্রোহ ও বিদ্রোহের উন্মাদনা খুঁজে পায় এবং ফলে নজরুলের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা রুজু হয়। সরকার তাঁকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে।
‘ধূমকেতু’ পত্রিকার দ্রুত জনপ্রিয়তা ও এর বিপ্লবী সুর সরকারকে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করে তোলে। কারণ এই সাময়িকী কেবলমাত্র সাহিত্যের প্রচার মাধ্যম ছিল না, বরং তা এক উন্মুক্ত রাজনৈতিক ঘোষণাপত্র, যা সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি সুস্পষ্ট সমর্থন জানাত এবং ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য জোরালো দাবি করত।
১৯২২ সালের ২৩ নভেম্বর কুমিল্লা থেকে পুলিশ নজরুলকে গ্রেফতার করে। সেদিনই তাঁকে নিয়ে আসা হয় কলকাতায়। ২৫ নভেম্বর তাঁকে আদালতে হাজির করা হয়, এবং ২৯ নভেম্বর মামলার শুনানির দিন ধার্য হয়। অবশেষে, ১৯২৩ সালের ১৬ জানুয়ারি দক্ষিণ কলকাতার পুলিশ কোর্টের বিচারক সিনহো মামলার রায় ঘোষণা করেন। বিচারে নজরুলকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তিনি সেই সময় প্রেসিডেন্সি জেলে ছিলেন বিচারাধীন বন্দী হিসেবে।
এই প্রেক্ষাপটে নজরুল আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যে জবানবন্দী পেশ করেন, তা কেবল এক কয়েদীর আত্মপক্ষসমর্থন নয়, বরং ভারতের উপনিবেশবাদবিরোধী ইতিহাসে এক সাহসিক উচ্চারণ, এক অগ্নিস্নানসম দ্রোহের অঙ্গীকার। তাঁর বক্তব্য ছিল যুক্তিনির্ভর, সাহিত্যিক গৌরবে মোড়া, এবং বিপ্লবের মর্মমন্ত্রে দীপ্ত।
এই প্রবন্ধে নজরুল তাঁর চিন্তা, স্বপ্ন, এবং মুক্ত ভারত নির্মাণের অদম্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। তিনি বলেছিলেন—
“আমি বিদ্রোহ করেছি, আমি বিদ্রোহ করব—এই নিপীড়িতের পাশে দাঁড়াতে আমি কসুর করিনি। আমার কলম থেকে রক্ত ঝরবে, তবু অন্যায়ের বিরুদ্ধে লিখতে আমি থামব না।”
এই ঘোষণায় উঠে আসে এক অবিনশ্বর প্রতিজ্ঞা—তিনি লিখবেন, কারণ সেটাই তাঁর অস্ত্র; তিনি কলম হাতে লড়বেন, কারণ সেটাই তাঁর যুদ্ধের পথ। তাঁর এই আত্মঘোষণাই পরবর্তীতে ভারতীয় যুবসমাজের জন্য অনুপ্রেরণার মশাল হয়ে ওঠে।
‘রাজবন্দীর জবানবন্দী’ কেবল নজরুলের রাজনৈতিক অবস্থানের বিবৃতি নয়, বরং তা একটি দার্শনিক বিপ্লবের ঘোষণা। এখানে উঠে আসে তাঁর বিশ্বাস, যে কবির কলম নিছক কাব্যকীর্তির জন্য নয়—তা ইতিহাস রচনার জন্য, সংগ্রামের জন্য, আর একটি নতুন ভারত নির্মাণের জন্য। এই প্রবন্ধে তাঁর প্রতিটি বাক্য যেন স্বাধীনতার আহ্বানে উজ্জ্বল মশাল।
অতএব, ‘রাজবন্দীর জবানবন্দী’ শুধু ভারতীয় উপনিবেশবিরোধী সাহিত্যের এক স্মারক দলিল নয়, বরং তা এক যুগচেতন, এক গোষ্ঠীস্বপ্নের ভাষ্য, যেখানে কবি নিজে হয়ে উঠেছেন ইতিহাসের অগ্রসেনানী।
— “আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজদ্রোহী! তাই আমি রাজকারাগারে বন্দি এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত।
একধারে রাজার মুকুট, আরধারে ধূমকেতুর শিক্ষা। একজন রাজা, হাতে রাজদন্ড, আরজন সত্য, হাতে ন্যায়দন্ড। রাজার পক্ষে রাজার নিযুক্ত রাজবেতনভোগী, রাজকর্মচারীরা। আমার পক্ষে সকল রাজার রাজা, সকল বিচাররকের বিচারক, আদি অনন্তকাল ধরে সত্য- জাগ্রত ভগবান।
আমার বিচারককে কেহ নিযুক্ত করে নাই। এ মহাবিচারকের দৃষ্টিতে রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, সুখী -দুঃখী সকলে সমান। এঁর সিংহাসনে রাজার মুকুট আর ভিখারির একতারা পাশাপাশি স্থান পায়। এঁর আইন– ন্যায়, ধর্ম। সে আইন কোনো বিজেতা মানব কোনো বিজিত বিশিষ্ট জাতির জন্য তৈরী করে নাই। সে আইন বিশ্ব মানবের সত্য-উপলব্ধি হতে সৃষ্ট ; সে আইন সর্বজনীন সত্যের, সে আইন সার্বভৌমিক ভগবানের। রাজার পক্ষে- পরমাণু পরিমাণ খন্ড সৃষ্টি ; আমার পক্ষে-আদি অন্তহীন অখন্ড স্রষ্টা।
রাজার পেছনে ক্ষুদ্র, আমার পেছনে-রুদ্র। রাজার পক্ষে যিনি, তাঁর লক্ষ স্বার্থ, লাভ অর্থ, আমার পক্ষে যিনি, তাঁর লক্ষ সত্য, লাভ পরমানন্দ। রাজার বাণী বুদ্, আমার বাণী সীমাহারা সমুদ্র। ….
যাক আমি বলছিলাম, আমি সত্য প্রকাশের যন্ত্র। সে যন্ত্রকে অপর কোনো নির্মম শক্তি অবরুদ্ধ করলে করতে পারে, ধ্বংস করলেও করতে পারে, কিন্তু সে যন্ত্র যিনি বাজান, সে বীণীয় যিনি রুদ্রবাণী ফোটান, তাঁকে অবরুদ্ধ করবে কে? সে বিধাতাকে বিনাশ করবে কে?
আমি ভগবানের হাতের বীণা। বীণা ভাঙলেও ভাঙতে পারে, কিন্তু ভগবানকে ভাঙবে কে? …
শুনেছি, আমার বিচারক একজন কবি। শুনে আনন্দিত হয়েছি। বিদ্রোহী কবির বিচার বিচারক কবির নিকট। কিন্তু বেলা শেষের শেষ খেয়া এ প্রবীন বিচারককে হাতছানি দিচ্ছে, আর রক্ত ঊষার নব-শঙ্খ আমার অনাগত বিপুলতাকে অভ্যর্থনা করছে, তাঁকে ডাকছে মরণ, আমায় ডাকছে জীবন; তাই আমাদের উভয়ের অস্ত-তারা আর উদয়তারার আলোর মিলন হবে কিনা বলতে পারি না।….
আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই; কেন না ভগবান আমার সাথে আছেন। আমার অসমাপ্ত কর্তব্য অন্যের দ্বারা সমাপ্ত হবে। সত্যের প্রকাশ পীড়া নিরুদ্ধ হবে না। আমার হাতের ধূমকেতু এবার ভগবানের হাতের অগ্নিমশাল হয়ে অন্যায় অত্যাচারকে দগ্ধ করবে। আমার বহ্নি এরোপ্লেনের সারথি হবেন এবার স্বয়ংরুদ্র ভগবান। অতএব মাভৈঃ ! ভয় নাই। ….
প্রেসিডেন্সি জেলঃ কলিকাতা
৭ই জানুয়ারী ১৯২৩ রবিবার-দুপুর
যদিও ‘রাজবন্দীর জবানবন্দী’ একটি বিচারাধীন কয়েদীর আত্মপক্ষসমর্থনের ভাষ্য, তবু তার পরতে পরতে নজরুলের সাহিত্যচেতনা ও আত্মপ্রকাশ অনুরণিত হয়েছে। এই জবানবন্দী নিছক একটি রাজনৈতিক দলিল নয়—এটি কবি নজরুলের অন্তর্গত দ্রোহ ও স্বাধীনতার সাধনার এক গভীর সাহিত্যিক নথি। তার ভাষা উগ্রতায় নয়, শাণিত আবেগে দীপ্ত; যুক্তি ও কল্পনার অপূর্ব সংমিশ্রণে তা পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করে। সেই সময়ের নিপীড়িত জাতির দুঃখ, অবদমন ও বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নজরুলের কলমে এমনভাবে সঞ্চারিত হয়েছে যে এই লেখাটি আজও নিঃসন্দেহে এক অনন্য সাহিত্যসৃষ্টি হিসেবে স্বীকৃত।
ঠিক তেমনি নজরুলের আর-এক সংগ্রামী গ্রন্থ ‘দুর্দিনের যাত্রী’, যা আশ্বিন ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ, অর্থাৎ অক্টোবর ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়, এক যুগবীক্ষণের প্রামাণ্য দলিল। এই গ্রন্থে সংকলিত সাতটি প্রবন্ধ হল—
১) আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল,
২) তুবড়ী বাঁশীর ডাক,
৩) মোরা সবাই স্বাধীন মোরা সবাই রাজা,
৪) স্বাগত,
৫) মেয় ভুখা হু,
৬) পথিক! তুমি পথ হারাইয়াছ,
৭) আমি সৈনিক।
এই লেখাগুলি মূলত ‘নবযুগ’ ও ‘ধূমকেতু’ পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু ‘যুগবাণী’, ‘রুদ্রমঙ্গল’ এবং ‘দুর্দিনের যাত্রী’তে পরিমার্জিত ও নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রবন্ধগুলিতে নজরুল একজন কবি, দেশপ্রেমিক ও জাতীয় অভিভাবকের মতো কথা বলেছেন। কোথাও তিনি হিন্দু-মুসলমান ভ্রাতৃত্বের মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন, কোথাও আবার সন্ত্রাসবাদ ও বিপ্লবের অনিবার্যতা নিয়ে যুক্তি সাজিয়েছেন। আবার কোথাও জাতিকে নবজাগরণের দীপ্ত আহ্বান জানিয়েছেন।
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ‘আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল’। এখানে ‘লক্ষ্মীছাড়া’ শব্দটি বাঙালির প্রচলিত গৃহস্থ-মনস্কতাকে উপহাস করে ব্যবহার করেছেন নজরুল। তিনি এই অভিধা দিয়েছেন সেই সব যুবকদের, যাঁরা বাধাবন্ধন ও সামাজিক অনিশ্চয়তার তোয়াক্কা না করে দেশমাতৃকার ডাকে জীবনকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। নজরুল মনে করেন, ইংরেজ শাসনকে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে গেলে কেবল পরিশীলিত বক্তৃতা বা আচারচর্চা যথেষ্ট নয়—প্রয়োজন বিপ্লবী উদ্যম ও আত্মবলিদান, প্রয়োজন এমন এক সাহসী যুবসমাজ, যারা ছন্দনাশ্রয়হীন, ভয়ের ঊর্ধ্বে, বিপদের মাঝেও নির্ভীক।
এই তরুণদের প্রতি নজরুলের আহ্বান জাগরণধ্বনির মতো প্রতিধ্বনিত হয়েছে তাঁর অগ্নিমন্ত্রে—
“তোমাদের জন্যে গৃহ নাই, তোমাদের জন্যে দয়া নাই, করুণা নাই, এই দুর্দিনে তোমাদের ঘরে ডেকে নেবার কেউ নেই, তোমাদের ডাক দিয়েছে ওই ঝড় বাদলের উতল হাওয়া আর মাটির মায়ের সিক্ত কোল। তোমাদের জন্যে কোনো গ্রহের বাতায়নে কালো চোখের করুণ কামনা ঝিলিক মারে না, তোমাদের অভাবে কারুর হৃদয় পীড়িত হয়ে ওঠে না।”
এই কথাগুলিতে ফুটে উঠেছে এক ভাঙনের যুগে কবির অচঞ্চল বিশ্বাস—যে জাতি তরুণদের নিঃস্ব করে, সেই জাতিই নবজাগরণের স্বপ্ন দেখতে পারে না।
এই প্রবন্ধে নজরুল কেবল বিদ্রোহের গান গাইছেন না—তিনি এক নতুন সৃষ্টির তপস্যার কথা বলছেন। তাঁর কণ্ঠে যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সৃষ্টিশীল আগুনের মন্ত্র: “এই অমঙ্গল অভিশাপ আর শনির জ্বালানো রুদ্র চুল্লির মধ্যে বসে, তোমাদের নবসৃষ্টির সাধনা করতে হবে। তোমাদের এই রুদ্র তপস্যার প্রভাবে সকল নবকাগ্নি ফুল হয়ে ফুটে উঠবে, যেমন ‘ইব্রাহিমের’ পরশে নমরুদের জাহান্নম ফুল হয়ে হেসে উঠেছিল।”
এই বাক্যে নজরুল যুগযন্ত্রণার মধ্যেই দেখেছেন নবজন্মের সম্ভাবনা। তাঁর চোখে বিপ্লব কেবল ধ্বংস নয়, তা গঠনেরও সূচনা।
অতএব, ‘দুর্দিনের যাত্রী’ কেবল রাজনৈতিক সময়ের ভাষ্য নয়, বরং তা কবির অন্তর্দৃষ্টিতে রচিত এক জাতীয় মহাকাব্য। তাঁর প্রবন্ধে ভাষা ও ভাব, কবিতা ও চিন্তা, যুক্তি ও আবেগ—সবই মিলে তৈরি হয়েছে এমন এক সাহিত্যিক রূপ, যা কালের গণ্ডি অতিক্রম করে আজও আমাদের প্রেরণা জোগায়।
তুবড়ি বাঁশির ডাক
তুবড়ি বাঁশি—এক অলৌকিক সুরবাহিত যন্ত্র, যেটি সাপুড়ের হাতে প্রাণ পায়। এই বাঁশির আহ্বানে এক অনিবার্য আকর্ষণে ছুটে আসে নাগ-নাগিনীর দল। কোনও প্রকার প্রতিরোধ তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। একবার মাত্র সেই সুর শুনলেই তারা আর স্থির থাকতে পারে না। গহন তটিনী-তীরের কেতকী কুসুমে লুকিয়ে থাকা বিষধর সাপও তখন কুন্ডলী ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসে, নাচে, উত্তেজনায় জারিত হয়, যেন তাদের প্রাণমজ্জাতেই ঢুকে পড়ে বাঁশির সুরের জাদু।
এই ‘তুবড়ি বাঁশি’ নজরুলের কাছে কেবল সাপখেলানোর একটি যন্ত্র নয়, বরং তা এক প্রতীকময় বিপ্লবের আহ্বান। আজকের দিন ‘ভাসান’—যা উৎসবের আবরণে স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গের ডাক বহন করে এনেছে। এই দিনেই নজরুল তাঁর কলমের বাঁশিতে সেই আহ্বান জাগিয়েছেন সমগ্র দেশবাসীর উদ্দেশে। সেই আহ্বানে লুকিয়ে আছে এক বিদ্রোহী প্রণোদনা, যা প্রতিটি নাগরিকের হৃদয়ে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে তুলতে চায়।
নজরুল যেন এই প্রবন্ধের মাধ্যমে বলছেন—এখনই সেই মুহূর্ত, যখন জাতির প্রত্যেকটি মানুষ, যার যতটুকু শক্তি আছে, সাহস আছে, রক্ত আছে, সমস্ত কিছু একত্র করে জাতিকে রক্ষা করতে হবে। স্বাধীনতা কেড়ে আনতে হবে। নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে এক বৃহত্তর ভবিষ্যতের জন্য।
এই প্রেক্ষিতেই তিনি উচ্চারণ করেছেন এক ঐতিহাসিক আহ্বান, যা একাধারে প্রতীকী ও আগ্নেয়—
“তোমাদের বিষ দাঁতের ছোবলে ছোবলে ধরণী জর্জরিত হয়ে উঠুক, তোমাদের অত্যুগ্র নিশ্বাসে নিশ্বাসে আকাশ তাম্রবর্ণ হয়ে উঠুক, বাতাসে জ্বালাদগ্ধ অগ্নি-দাহন হু-হু- হু- হু করে ছুটে যাক তোমাদের কর্কশ পুচ্ছে জড়িয়ে বসুমতীর টুটি টিপে ধরো।”
এই বাক্যে নজরুল সাপকে স্রেফ প্রাকৃতিক প্রাণী হিসেবে দেখেননি, বরং তাকে রূপ দিয়েছেন প্রতিরোধ ও প্রতিশোধের এক প্রতীক রূপে। এই প্রতীকে প্রতিস্থাপিত হয়েছে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এক বিপ্লবী চেতনা।
এই অনুপম রূপক-ভাষায় নজরুল বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, কেবল শান্তি ও অহিংসার মাধ্যমে নয়, বরং প্রয়োজনীয় সময়ে হিংস্র প্রতিরোধই হতে পারে জাতির মুক্তির পথ। সেই হিংস্র প্রতিরোধ যেন হয় সাপের ছোবলের মতো হঠাৎ, হিংস্র ও নির্ভুল।
তাঁর ভাষায় এ এক দাহনময় বিপ্লবের ডাক, যেখানে হিংস্র দখলদারদের হৃদয় হিম হয়ে যাবে বাঙালির উত্তপ্ত স্বদেশপ্রেমে। সেই অত্যাচারী শক্তিকে তিনি তুলনা করেছেন পশুর সঙ্গে, যারা সভ্যতা ও মানবতাকে গিলে খেতে এসেছে। নজরুল চান সেই পশুদের—অর্থাৎ ইংরেজ শাসকদের—টেনে আনা হোক ‘অজগরের মুখগহ্বরে’।
এইভাবে, ‘তুবড়ি বাঁশীর ডাক’ নজরুলের সাহিত্যিক কল্পনার এক অনন্য প্রকাশ—যেখানে বিপ্লব, প্রতিরোধ, প্রতীক ও কাব্য একসূত্রে বোনা। এটি কেবল একটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ নয়, বরং এক জাগরণের বাঁশি—যার সুর আজও যুগে যুগে প্রতিধ্বনিত হয় স্বাধীনতা ও স্বাভিমানকে কেন্দ্র করে।
মোরা সবাই স্বাধীন; মোরা সবাই রাজা
নজরুলের প্রবন্ধটির নামকরণে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অমর গানের ছায়া—“মোরা সবাই রাজা, আমাদের এই রাজার রাজত্বে।” এই অনুকরণ কেবল শব্দে নয়, ভাবনাতেও এক গভীর তাৎপর্য বহন করে। এখানে ‘রাজা’ শব্দটি কোনো সিংহাসনে বসা একচ্ছত্র শাসকের প্রতীক নয়, বরং এক একটি স্বাধীন আত্মার চিহ্ন, যে নিজের অধিকারে স্বনির্ভর এবং আত্মমর্যাদায় উদ্ভাসিত।
‘স্বরাজ’ শব্দটির মর্মার্থই হল—নিজের রাজত্ব, নিজেই নিজের অধিপতি। এই রাজত্বে কারো শাসন নেই, নেই কোনো পরাধীনতার শৃঙ্খল। সত্যিকারের স্বরাজ মানে অন্য কারো অধীনে নয়, বরং নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি, মনন ও বিবেকের শাসনে নিজেকে পরিচালিত করা। এ এক সর্বজনীন রাজত্ব—যেখানে প্রত্যেকেই রাজা, কেউ কারো প্রজা নয়।
নজরুলের দৃষ্টিতে স্বরাজ কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্ন নয়, এটি আত্ম-সচেতনতামূলক এক বিপ্লব। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, সত্যিকার স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বশর্ত হচ্ছে আত্মবিশ্বাস, আত্মচেতনা এবং সাহস। আমাদের হৃদয়ে যদি সেই সাহস জন্মে, যে সাহসে বুক ফুলিয়ে ঘোষণা করা যায়—”আমি রাজা, আমি স্বাধীন”, তাহলে কেউ আর আমাদের মনুষ্যত্ব বা অধিকার কেড়ে নিতে পারবে না।
স্বাধীনতার এই আহ্বান নজরুল উচ্চারণ করেছেন বজ্রকঠিন ভাষায়, যেখানে তিনি বলেন—
“জাগো অচেতন, জাগো! আত্মাকে চেনো! যে মিথ্যুক তোমার পথে এসে দাঁড়ায়, পিষে দিয়ে যাও তাকে, দেখবে তোমারই পতাকা-তলে বিশ্ব-শির লোটাচ্ছে।”
এই পঙ্ক্তির ভিতর নিহিত রয়েছে এক ভয়হীন আত্মঘোষণা—এমন এক সাহস যা শুধু জাতিকে নয়, প্রতিটি মানুষকে ব্যক্তিগত স্তরেও মুক্তির পথ দেখায়। এখানে ‘মিথ্যুক’ কেবল রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নয়, বরং প্রতীক—যে আমাদের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে, আমাদের আত্মাকে অপমান করে। আর পতাকা—তা স্বাধীনতার চিহ্ন, যা উঁচু হয়ে ওড়ে আত্মমর্যাদার শক্তিতে।
নজরুলের এই প্রবন্ধ কেবল একটি রাজনৈতিক লেখনী নয়, এটি এক মানসিক বিপ্লবের সঙ্কেত। তিনি জানতেন, কেবল বাইরের শৃঙ্খল ভেঙে দিয়ে স্বাধীনতা আসে না, যদি অন্তরের শৃঙ্খল অটুট থাকে। তাই তার আহ্বান—প্রথমে নিজেকে চিনো, নিজের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করো আত্মশক্তির ভিতরে।
এইভাবে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যিক ঐতিহ্যের অনুসরণে নজরুল সৃষ্টি করেছেন এক দ্রোহী ভাষ্যে অনন্য আত্মপ্রত্যয়ের দিগন্ত। তাঁর ভাষায় উঠে এসেছে সেই চিরন্তন ডাক—নিজেকে জানো, নিজেই নিজের অধিপতি হও।
স্বাগত : এই প্রবন্ধে কবি এক অনুপম আবেগে দেশের মহাবিপদের সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে স্বাগত জানিয়েছেন। দেশ তখন শ্মশানে পরিণত—চারদিকে জ্বলছে দাহশিখা, বাতাসে উড়ছে শবের ধোঁয়া, বাংলার আকাশ যেন ঋতুপর্ব ছেড়ে রুদ্রতাণ্ডবের চিত্রপটে পরিণত হয়েছে। এই বিষণ্ণ প্রেক্ষাপটে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐশ্বর্যময় কামনায় ভরা গান স্মরণ করেছেন— “বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল, পুণ্য হউক হে ভগবান!” এই স্তবগান যেন শ্মশানবুকে অঞ্জলি হয়ে উচ্চারিত, বাংলার ভস্মভূমিতে পবিত্রতার প্রত্যাশা।
কবি জানেন, এই অন্ধকার সময়ে পথ বাতলে দেওয়ার মতো কেউ নেই। দেশে এখনো অশান্তি, অস্থিরতা, দারিদ্র্য, অপমান, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, অবহেলা আর অনাচারের কালো ছায়া বিস্তার করেছে। এই শ্মশানে কেউ মায়ের স্নেহময় কোল পায় না, পিতার আশীর্বাদময় করস্পর্শ নেই, ভগিনীর স্নেহভরা দৃষ্টিও অনুপস্থিত। ঋষিসুলভ ধৈর্য নিয়ে নজরুল এক রূঢ় প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন—
“কেউ পথ দেখাতে নেই। অভাব, বেদনা, আঘাত, মার, বিদ্রুপের চাবুক-জ্বালা, অনাদর, অপমান, এই সপ্ত নরক হাঁ করে আছে গ্রাস করবার জন্যে। এই জাহান্নমের মধ্যে বসে পুষ্পের হাসি হাসতে পারবে?”
এই প্রশ্নের মধ্যে লুকিয়ে আছে এক ভয়ংকর বাস্তবতা। জাতির চিতায় আগুন জ্বলছে, আর সেই জ্বলন্ত শবসাধনার ভিতর দিয়েই দেশের শিবতুল্য চেতনাকে জাগাতে হবে। এ এক নিষ্ঠুর তপস্যা—যেখানে যুগ-যুগান্তরের অন্যায়, অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এক নতুন ভোরের জন্ম দিতে হবে। এখানেই নজরুলের দ্রোহী কবিসত্তা প্রকাশ পায়, যেখানে ধ্বংস আর অন্ধকারের ভিতর দিয়েই জন্ম হয় নতুন আলো, নতুন সৃষ্টির।
কবির আহ্বান এই মৃত্যু-গন্ধময় শ্মশানে দাঁড়িয়ে, যেন দেশবন্ধুর মতো নেতাদের কাছে—তারা যেন নেতৃত্ব দেন এই দুর্যোগকালীন সময়ে, যেন পুষ্পের হাসি ফুটে ওঠে অগ্নিময় ছাইয়ের ভিতর থেকেও।
এই প্রবন্ধ তাই কেবল একটি রাজনীতিকের প্রতি স্বাগত নয়, বরং তা এক পূর্ণাঙ্গ যুগচেতনার প্রকাশ—যেখানে শোক আর সংগ্রামের বুক ফুঁড়ে জেগে উঠছে নবজাগরণের সম্ভাবনা। এই লেখায় নজরুলের দ্রোহ, বেদনা ও উদ্দীপনার স্বর এক সঙ্গে মিশে গিয়ে রচনা করেছে এক অনন্য সাহিত্যিক আবেদনের জোয়ার।
মেয় ভুখাঁ হুঁ
নজরুল ইসলাম রচিত ‘মেয় ভুখাঁ হুঁ’ প্রবন্ধটি তাঁর প্রাজ্ঞ ও বিদ্রোহী মননের এক অনন্য প্রকাশ। এই রচনাটি ১৯২২ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর ধূমকেতু পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জনমানসে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। পরে এটি তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থ দুর্দিনের যাত্রী-তে সংকলিত হয়। প্রবন্ধটিতে কবি দেশমাতৃকাকে এক পাগলিনীর রূপে কল্পনা করেছেন, যিনি দেশের সন্তানদের সামনে দাঁড়িয়ে বুকভরা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠেন— “মেয় ভুখাঁ হুঁ”। এই আর্তনাদ শুধু শারীরিক ক্ষুধার প্রতীক নয়, বরং এর অন্তরালে রয়েছে দেশমাতার রক্তের তৃষ্ণা—এক অব্যক্ত মুক্তিচেতনা, যে মুক্তি আসতে পারে কেবল আত্মবলিদানের পথেই।
এই প্রবন্ধে ‘ভুখাঁ’ অর্থাৎ ‘ক্ষুধা’—তা কেবল খাদ্যের ক্ষুধা নয়, বরং তা স্বাধীনতার ক্ষুধা, আত্মমর্যাদার ক্ষুধা, শৃঙ্খল মুক্ত হবার অপরিসীম তৃষ্ণা। নজরুল দেখিয়েছেন, কীভাবে সেই তৃষ্ণা মেটাতে দেশের ছেলেরা স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, নিজেদের রক্ত দিয়ে জননীর ভাঙা কোলে পূর্ণতার আলো ফিরিয়ে এনেছেন। অন্নপূর্ণার ভৈরবী রূপ যেন তার সন্তানদের রক্তের আশায় উন্মত্ত, আর সেই রক্তই যেন তাঁর পরিত্রাণ।
প্রবন্ধে কবি লিখেছেন—
“পাগলী আবার হেঁকে উঠল, ‘মেয় ভুখাঁ হুঁ।”… হরিৎ বনের বুক চিরে বেরিয়ে এল রক্ত-কাপালিক। ভালে তার গাঢ় রক্তে আঁকা ‘অলক্ষনের তিলক রেখা।” বুকে তার পচা শবের গলিত দেহ । আকাশ খড়গ উৎক্ষিপ্ত করে কপালিক হেঁকে উঠল – “বেটী- রক্ত চায় !” তরুণের দল ভীম হুঙ্কার করে উঠল, “বেটী -রক্ত চায় ! বেটীরক্ত চায়!”
এই ভাষ্য যেন এক প্রাচীন তান্ত্রিক বলিদানের দৃশ্যকল্প। এখানে ‘রক্ত-কাপালিক’ এক প্রতীক, যে একাধারে বিপ্লব ও ধ্বংসের চেতনার বাহক। তাঁর কপালে অলক্ষণরেখা, বুকে মৃতদেহ, আর কণ্ঠে এক অশরীরী হুঙ্কার—সব মিলিয়ে এই দৃশ্য যেন মুক্তির জন্য এক রুদ্র নৃত্য।
এই যজ্ঞে নিজ মায়ের আরাধনার বলি হয়েছেন মায়ের নিজের সন্তানেরাই। কবি লিখেছেন—
“মহা উৎসবে পড়ে গেল ছেলেদের মধ্যে তার যজ্ঞ করবে। এবার মায়ের পূজার বলি হল মায়ের ছেলেরাই।”
এই শব্দগুলো শুধু চিত্রকল্প নয়, বরং এক ঐতিহাসিক সত্যের উপমা—যেখানে স্বাধীনতার জন্য, অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য, জাতির নবজাগরণের জন্য আত্মোৎসর্গই একমাত্র পথ। নজরুল এখানে বিপ্লবকে নৈতিক যুক্তিতে গ্রহণ করেছেন, সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতি সরাসরি সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন।
এই প্রবন্ধে নজরুল কেবল একটি রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশ করেননি, বরং রচনা করেছেন এক ঐতিহাসিক প্রতীকচিত্র, যেখানে জাতির নিঃস্বতা, জননীর আর্তনাদ ও যুবকদের বলিদান মিলেমিশে এক মহাসমর রূপ ধারণ করেছে। এটি নিছক একটি প্রবন্ধ নয়, এটি জাতীয় চেতনাকে ঝাঁকুনি দেওয়া এক বিদ্যুৎপ্রবাহ—যার শব্দে এখনও জেগে ওঠে স্বাধীনতার দুর্জয় শপথ।
পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ
এই প্রবন্ধে নজরুল ইসলাম দেশের বীর তরুণদের উদ্দেশে যে আহ্বান উচ্চারণ করেছেন, তা শুধু উত্তেজনার ভাষা নয়—তা এক অগ্নিস্নাত অনুপ্রেরণা, এক জীবনবোধের রণহুঙ্কার। দেশমাতৃকার পূজার জন্য যারা রক্তের পুষ্প অর্পণ করতে উদ্যত, যারা প্রয়োজনে হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত—তাদের হৃদয়ে সাহসের দীপ জ্বালিয়ে দিয়েছেন কবি, যেন তারা কোনও দিন দ্বিধাগ্রস্ত না হয়, ভীত না হয়, পথভ্রষ্ট না হয়।
তরুণ পথিকদের তিনি বারবার স্মরণ করিয়ে দেন—তোমাদের পথ ধরা হয়েছে রক্ত-আঁকা কণ্টকসঙ্কুল দুর্গম এক বনপথ। এই পথ ঘরের নয়, হাটের নয়—এ পথ আত্মবিসর্জনের, এক চিরপরিচিত বেদনার। যাঁরা মায়ের আরাধনায় নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত, তাঁদের চলার পথে ভয়-ভীতির কোনো স্থান থাকতে পারে না। সেই বীর পথিকদের উদ্দেশে নজরুল উচ্চারণ করেছেন—
“বল, মাভৈঃ! আমরা পথ হারাই না! আমাদের পথ কখনও হারায় না। বল, আমাদের এ পথ চির চেনা পথ—এই বনের বুকে রক্ত-আঁকা পথ। বল, ওরে রক্ত পথের পথিক! এই বনের পথই আমাদের চির-চেনা পথ। হাটের পথিকের পায়ে চলার পথ আমাদের জন্য নয়।”
এই ভাষ্য কেবল আত্মবিশ্বাসের আহ্বান নয়, বরং এক অস্তিত্ববাদী ঘোষণা। যারা ঘর হারিয়েছে, তারা বনের পথ জানে; যারা আত্মপরিচয় হারিয়েছে, তারা জাতির নবজন্ম দিতে পারে। এ প্রবন্ধে নজরুল চেয়েছেন—তরুণরা যেন জীবনবোধে কঠিন, সাহসে দুর্দমনীয়, আদর্শে অনমনীয় হয়।
প্রবন্ধের গভীরে কবি তুলে এনেছেন পুরাণের ভয়াবহ দৃশ্যের প্রতীকী ব্যবহার। তিনি স্মরণ করিয়েছেন রক্ত-পূজার মন্দিরের কথা, যেখানে দাঁড়িয়ে আছে রুদ্ররূপী ‘ভুখারিনি’, যার প্রসাদ রক্ত—যার উপাসনা বলি ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না। মন্দিরের দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে যুগযাত্রী পথিক, যার চোখে ঘুম নেই, হাতে অস্ত্র, বুকে বিদ্রোহ। দূরে শোনা যাচ্ছে ভৈরবের ভয়াল গান—
“তিমির হৃদয় বিদারণ, জলদগ্নি নিদারুণ।
জয় সংকট সংহর। শঙ্কর। শঙ্কর।”
এই দৃশ্য যেন এক অভিশপ্ত ঘোর রাত্রির, যেখানে দেবতাও আর্তনাদ করছেন, শিব নিজেই রক্ত-পাগলীর পায়ের চাপে যন্ত্রণায় কাতর। সেই বিভীষিকার মধ্যেও কবি আশার আলোক খোঁজেন। তিনি বলেন,
“রক্ত-পাগলি বেটির পায়ের চাপে শিব আর্তনাদ করে উঠল।
কাপালিকের রক্ত আঁখি দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।
আর দেরি নাই, ওই আসে রক্ত পূজার বলি।
ছেড়ে দে বেটি, ছেড়ে দে শিবকে, কল্যাণকে উঠে দাঁড়াতে দে।”
এ এক মহান প্রতীকের ভাষা—বিপ্লবের অন্ধকারে জন্ম নিচ্ছে নতুন দিনের সূর্য। রক্তের নদীর ভেতর দিয়েই জাতির পুনর্জন্ম সম্ভব। এই ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তিই নজরুলের কাব্যপ্রবাহের প্রাণ, তাঁর বিদ্রোহী চেতনার অক্ষয় চিহ্ন।
এই প্রবন্ধ কেবল সাহস জোগানোর ভাষা নয়, এটি এক অমর প্রহেলিকা—যেখানে আদর্শ, ত্যাগ, বেদনা, ক্রোধ এবং ভালোবাসা একই সঙ্গে ছায়াপাত করে। নজরুল এখানেই কবি, দার্শনিক এবং বিপ্লবী—তাঁর শব্দরথে উঠে আসা প্রত্যেকটি বাক্য যেন সময়কে ছেদ করে চলে যায় অনন্তে।
আমি সৈনিক : এই প্রবন্ধে নজরুল ইসলাম যেভাবে তাঁর বিদ্রোহী সত্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন, তা নিছক সাহিত্যিক ভঙ্গি নয়—বরং এক সুস্পষ্ট রাজনৈতিক অবস্থান। তাঁর কলম যেন সেই সময়কার নিস্তেজ বায়ুমণ্ডলে বজ্রের শব্দ তুলেছিল। কবির বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, তিনি শুধু আদর্শবাদী বা কল্পনাবিলাসী বিপ্লবী নন, বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন এক দার্শনিক, যিনি জানতেন—ঔপনিবেশিক শাসনের নির্মম শৃঙ্খল ছিন্ন করতে হলে করুণা নয়, প্রয়োজন প্রচণ্ড প্রতিরোধ।
ভারতবর্ষ তখন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে—একদিকে ছিল অহিংসার আশ্রমবাসী সাধনাপথ, অন্যদিকে ছিল তরুণ রক্তে আগুন জ্বালানো বিদ্রোহ। এই দ্বন্দ্বের মাঝে নজরুল স্পষ্টভাবে বেছে নিয়েছেন বিদ্রোহের পথ। তাঁর মতে, জাতিকে জাগ্রত করতে হলে চাই এমন একজন সেবক, যিনি নিছক করুণা বিলাবেন না, বরং প্রয়োজনে রুদ্ররূপ ধারণ করে শত্রুকে প্রতিহত করবেন। তিনি এই দায়িত্ব নারী কিংবা পুরুষ যেকোনো সংগ্রামী হৃদয়ের ওপরেই অর্পণ করতে প্রস্তুত, তবে শর্ত একটাই—সেবার সঙ্গে থাকতে হবে আগুনের ঔজ্জ্বল্য, বিদ্রোহের বলিষ্ঠতা।
কারণ, করুণা নিঃসন্দেহে মহত্তম গুণ, কিন্তু তা যদি কেবল কান্না ও সহানুভূতির আচ্ছাদন হয়ে থাকে, তবে তা শৃঙ্খল ভাঙার শক্তি নয়। আর সেই সময়ের ভারতের প্রয়োজন ছিল শৃঙ্খল-ভাঙার সাহসী হাত। নজরুল সেই সাহসী পুরুষত্মার সন্ধান করেছিলেন, যাঁর ভালোবাসা চোখের জলে ভিজে না, বরং জ্বলন্ত মশাল হয়ে ওঠে প্রতিরোধের প্রতীক। সেই আবেগভরা অথচ দৃপ্ত উচ্চারণেই তিনি বলেন—
“দেশকে যে নারীর করুণা দিয়ে সেবা করে, সে পুরুষ নয়, হয়তো মহাপুরুষ। কিন্তু দেশ এখন চায় মহাপুরুষ নয়। দেশ চায়, সেই পুরুষ যার ভালোবাসায় আঘাত আছে, বিদ্রোহ আছে। যে দেশকে ভালোবেসে শুধু চোখের জলই ফেলবে না, সে দরকার হলে আঘাতও করবে, প্রতিঘাতও বুক পেতে নেবে, বিদ্রোহ করবে।”
এই বক্তব্যে নজরুল কেবল এক সমাজ-সচেতন কবি হিসেবে নয়, বরং এক জাতি-সচেতন বিপ্লবী চিন্তাবিদ হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে, ভালোবাসা যদি নিস্তেজ হয়, তবে তা আত্মসমর্পণের নামান্তর। কিন্তু যে ভালোবাসা আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে দেয়, প্রতিকূলতার মাঝেও সৃজনশীল প্রতিরোধ গড়ে তোলে—সেই ভালোবাসাই উপযুক্ত মাতৃভূমির সেবা।
নজরুল এখানে প্রকৃত অর্থে গান্ধীর অহিংসার পথ থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছেন, এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিপ্লববাদী সংগ্রামের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল, জাতিকে স্বাধীন করতে হলে মোমবাতির আলো নয়, দরকার অগ্নিকুণ্ডের জ্বালা। যে আগুন ধ্বংস করে আবার নতুন করে গড়ে তোলে, সেই আগুনই প্রয়োজন জাতির পুনর্জাগরণের জন্য।
এভাবেই প্রবন্ধটি নিছক একটি মতবাদ নয়, বরং এক বিপ্লবী ভাষ্য—যা প্রজন্মকে ভাবিয়ে তোলে, জাগিয়ে তোলে, এবং চেতনার গভীরে এক বেদনার ভিতর থেকেও জন্ম দেয় সাহসের প্রতিশ্রুতি। এই প্রবন্ধে কবি এক সঙ্ঘর্ষময় প্রেমের রূপকল্প আঁকেন, যেখানে ভালোবাসা কেবল করুণার নয়—আঘাত, বিদ্রোহ ও আত্মোৎসর্গের এক মহান সংস্কার।
রুদ্রমঙ্গল : নজরুল ইসলাম সম্পাদিত প্রবন্ধ-সংকলন রুদ্রমঙ্গল প্রথম প্রকাশ পায় ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে, ‘ধূমকেতু’ পত্রিকার অনলবর্ষীয় সম্পাদকীয় প্রবন্ধসমূহের সমন্বয়ে। ঐ সময় কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আবহে, ২রা এপ্রিল ১৯২৬ তারিখে নগরী রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। এই পটভূমিতে নজরুল ২৬শে আগস্ট ও ২রা সেপ্টেম্বরের গণবাণী পত্রিকায় ‘মন্দির ও মসজিদ’ এবং ‘হিন্দু-মুসলমান’ শিরোনামে দুটি জ্বালাময় প্রবন্ধ লেখেন। রুদ্রমঙ্গল গ্রন্থে যে আটটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সেগুলির অধিকাংশই পূর্বে ‘ধূমকেতু’তে প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধগুলি হল—
১) রুদ্রমঙ্গল,
২) আমার পথ,
৩) মোহম,
৪) বিষবাণী,
৫) ক্ষুদিরামের মা,
৬) ধূমকেতুর পথ,
৭) মন্দির ও মসজিদ,
৮) হিন্দু-মুসলমান।
এই সংকলন কেবল একটি রাজনৈতিক ভাষ্য নয়; এটি হল নিপীড়িত শ্রেণির স্বপক্ষে উচ্চারিত এক সাহসী দ্রোহের দলিল। রুদ্রমঙ্গল প্রবন্ধে নজরুল শ্রমজীবী মানুষদের প্রশস্তিগাথা রচনা করেছেন। তিনি তাঁদের প্রতি সহানুভূতি, মমতা এবং মানবিক বোধের পরিচয় দিয়েছেন বারবার। এখানেই ফুটে উঠেছে তাঁর বাস্তব সমাজনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি, স্পষ্ট রাজনৈতিক চেতনা ও গভীর মানবতাবাদ।
নজরুল-সমালোচক ড. সুশীলকুমার গুপ্ত এই প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন— “এই সব প্রবন্ধের বাস্তববোধনিষ্ঠ রাজনৈতিক চেতনা, স্বভাবসিদ্ধ ভাবাবেগের প্রাবল্য ও গভীর মানবপ্রেম রচনাশৈলীর ত্রুটি ও উদ্দেশ্যপরতন্ত্রতা সত্ত্বেও পাঠকের মনকে দুরন্তভাবে আকর্ষণ করে ও নাড়া দেয়। বস্তুত এই সব রচনা যে রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা উদ্দীপনের জন্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল তা করতে এরা অনেক পরিমানেই সফল হয়েছিল – একথা মনে রাখলে এগুলির কতকটা সাহিত্যিক মূল্য ছাড়াও একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না।”
এই বক্তব্য যথার্থ, কারণ নজরুল এ প্রবন্ধগুলিতে কেবল প্রতিবাদ জানাননি, বরং ভবিষ্যতের বিপ্লবের ভাষ্য রচনা করেছেন। রুদ্রমঙ্গল প্রবন্ধে তিনি রক্তঝরা কণ্ঠে উচ্চারণ করেন এক বিপ্লবী আহ্বান। সেখানে নিশীথ অন্ধকারের মাঝে অগণিত মানুষের আলো জ্বালাবার চেষ্টা আবারও ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু তবুও সেই নিপীড়িত, অবহেলিত মানুষদের জাগাবার আকুল ডাক তিনি দেন—
“জাগো শক্তি! হে তোমার অবহেলিত পদপিষ্ট কৃষক হে আমার মুটে-মুজুর ভাইরা। তোমার হাতের এ লাঙ্গল আজ বলরাম স্কন্ধে হলের মতো ক্ষিপ্ত তেজে গগনের মাঝে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠুক, এই অত্যাচারীর বিশ্ব উপড়ে ফেলুক উলটে ফেলুক ! আনো তোমার হাতুড়ি ভাঙ্গে ঔ উৎপীড়কের প্রাসাদ-ধুলায় লুটাও অর্থ-পিচাশ বল দর্পীর শির। ছোড়ো হাতুড়ি, চালাও লাঙ্গল, উচ্চে তুলে ধরো তোমার বুকের রক্ত মাখা লালে লাল ঝান্ডা।”
এই উক্তির মাধ্যমে নজরুল তাঁর স্বপ্নের সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বিপ্লবের ভাষা ব্যবহার করেছেন। এটি শুধুমাত্র একধরনের আবেগপ্রবণ আহ্বান নয়, বরং একটি স্পষ্ট শ্রেণিসংগ্রামের রূপরেখা।
অন্যদিকে আমার পথ শীর্ষক প্রবন্ধে নজরুল নতুন এক যাত্রার প্রারম্ভ ঘোষণা করেন। এখানে তিনি নিজেকে ধূমকেতুর সারথি হিসেবে দেখেন— “জয় প্রলয়ংকর” এই ধ্বনি তুলে তিনি ধূমকেতুর রথে যাত্রা করতে চান। সেই যাত্রাপথে তাঁর একমাত্র পাথেয় সত্য। তিনি বলেন, মিথ্যার বিরুদ্ধে অবস্থানই তাঁর পথ; রাজশক্তির ভয় কিংবা জনমতের চাপে তিনি বিচলিত নন। তাঁর দৃপ্ত ঘোষণা— “অতএব যে মিথ্যাকে চেনে, সে মিছিমিছি তাকে ভয়ও করে না। যার মনে মিথ্যা সেই মিথ্যাকে ভয় করে।” এই আত্মবিশ্বাস থেকেই তিনি সত্যকে আপন করেন এবং ভয়ের অতীত হয়ে ওঠেন।
তিনি বিশ্বাস করেন, নিজের সত্যকে হৃদয়ে ধারণ করলে নিজ শক্তির উপর নির্ভরতা জন্মে, আর এই আত্মবিশ্বাসই মানুষের বৃহত্তর পরিবর্তনের রসদ। ধূমকেতু নিয়ে কেউ যদি আশঙ্কা করে যে এটি ঝগড়া-বিবাদ ঘটাবে, তবে নজরুল স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন— “ঝগড়া-বিবাদ আনবে না, তবে প্রলয় যদি আনে, তাহলে সেটার জন্যে দায়ি ধূমকেতুর দেবতা, – সারথি নয়।” এমন উচ্চারণে নজরুলের নির্ভীক আত্মদর্শনের প্রকাশ ঘটে।
তিনি আরও বলেন, ধ্বংস যদি আসে, তা যদি সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় হয়, তাহলে সেই ধ্বংসই কল্যাণের বার্তাবাহী হবে— “প্রলয় আনার যে দুর্দম অসম সাহসিকতা, ‘ধূমকেতু’ যদি তা না আনতে পারে তবে তাতে অমঙ্গলের চেয়ে মঙ্গলই আনবে বেশি।”
এইভাবে নজরুল তাঁর প্রবন্ধগুলিতে নিপীড়িত মানুষের মুখপাত্র হয়ে ওঠেন। কেবল সাহিত্যিক বাগ্মিতা নয়, বরং এক রাজনৈতিক-সামাজিক বোধসম্পন্ন নবজাগরণের ভাষা হয়ে ওঠে রুদ্রমঙ্গল। বাংলার প্রান্তিক মানুষ, কৃষক, শ্রমিক, মজুর, মুটেদের পক্ষ নিয়ে নজরুল যেভাবে কলম ধরেন—তা বাংলা সাহিত্যে এক দুর্লভ এবং অনন্য উদাহরণ। তাঁর ভাষা কখনও বজ্রের মতো, কখনও দীপ্ত সজীব আশ্বাসের মতো।
এই প্রবন্ধগুলি তাই কেবল সাহিত্য নয়, ইতিহাসেরও অংশ। এগুলি পড়লে বোঝা যায়, নজরুল কেবল কবি নন—একজন দুর্দমনীয় সমাজচেতনার ধারক ও বাহক। তাঁর ‘রুদ্রমঙ্গল’ তাই কেবল ধ্বংসের আহ্বান নয়, এক নবজাগরণের দীপ্ত রূপরেখা।
মোহম : ‘মোহররম’—এই শব্দটি ইসলামি চান্দ্র বছরের প্রথম মাসের নাম। আরবি ‘হরাম’ শব্দমূল থেকে উৎপন্ন এই শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থ নিষিদ্ধ বা পবিত্র। ইসলামি ইতিহাসে এই মাসটি একদিকে যেমন শান্তির প্রতীক, অন্যদিকে তেমনি তা গভীর শোক ও আত্মত্যাগের এক ঐতিহাসিক স্মারকও বটে। এই মাসেই কারবালার প্রান্তরে নবী মুহম্মদের প্রিয় দৌহিত্র ইমাম হোসেন আত্মোৎসর্গ করেছিলেন সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে, জুলুম ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এক অনন্য প্রতিবাদ হিসেবে। এই মহত্ আত্মত্যাগের স্মরণে বিশ্ব মুসলিম সমাজ মোহররম মাসে শোক পালন করে, রোজা রাখে, তাজিয়া তৈরি করে, মিছিল বের করে, মাতম করে।
তবে এই শোকানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কবি কাজী নজরুল ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অনেক গভীর, ব্যতিক্রমী ও আত্মসমালোচনামূলক। তাঁর মতে, আজ মুসলিম সমাজ মোহররম পালন করে একপ্রকার নিছক আচারগত অনুশীলনের মতো—যেখানে অন্তরের শ্রদ্ধা ও গভীরতা নেই, আছে কেবল অভিনয়, লোকদেখানো অশ্রুপাত, কর্কশ চিৎকার। সত্যিকার অনুভবের বদলে শোকানুষ্ঠান পরিণত হয়েছে এক ধরনের ‘ধর্মীয় নাট্যাভিনয়ে’। কবি ব্যথাভরে বলেন, মানুষ “হায় হোসেন!” বলে গলা ফাটিয়ে চেঁচায়, ফাতেমা (রা.)-র বুকফাটা মর্মযন্ত্রণাকে যেন আরও প্রগাঢ় করে তোলার প্রয়াস নেয়, অথচ এই অভিনয়ের মধ্য দিয়ে কি সত্যিই হোসেনের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে? নাকি সেই মহৎ আত্মোৎসর্গকে পরিণত করা হচ্ছে নিছক লোকদেখানো আবেগে, যাকে তিনি সরাসরি “আল্লাকে অপমান” বলেই মনে করেছেন।
কারণ, যে ব্যক্তি ধর্ম ও সত্যের জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁর জন্য শোক জানানো উচিত মর্যাদার সঙ্গে, আত্মসমালোচনার সঙ্গে, তাঁর পথ অনুসরণের সংকল্পে। যদি সেই শোক কেবল চিৎকার-চেঁচামেচি, ঢাকঢোল, বা লোকদেখানো মাতমে সীমাবদ্ধ হয়—যেখানে অন্তরের কোন অনুভব নেই, প্রতিবাদের কোন ধ্বনি নেই, আত্মশুদ্ধির কোন চেতনা নেই—তবে তা শহীদদের আত্মত্যাগকে অবমাননার শামিল।
এই মনোভাব থেকেই নজরুল বিস্ময়ে ও বেদনাভরে বলেন—
“তোমার ধর্ম নাই, অস্তিত্ব নাই, তোমার হাতে শমশের নাই, শির নাঙ্গা, তোমার কোরান পর – পদদলিত, তোমার গর্দানে গোলামির জিঞ্জির, যে শির আল্লার আরশ ছাড়া আর কোথাও নত হয় না, সেই শিরকে জোর করে সেজদা করাচ্ছে অত্যাচারী শক্তি আর তুমি করছ আজ সেই শহীদদের ধর্মের জন্য স্বাধীনতার জন্য শহিদদের-মাতমের অভিনয়! আপশোশ আপশোশ মুসলিম ! আপশোশ !!”
এই উক্তির মাধ্যমে নজরুল তাঁর জাতির নিদারুণ দুরবস্থার প্রতিচিত্র আঁকেন—যেখানে মুসলমানদের হাতে নেই আর সত্য প্রতিষ্ঠার তরবারি, কণ্ঠে নেই সাহসিকতার ভাষা, হৃদয়ে নেই আত্মমর্যাদার দীপ্তি। যে মুসলিম জাতি ছিল একদিন আল্লাহর আরশের সামনে মাথা নত করত কেবল, সেই জাতি আজ পদানত শাসকের জুলুমের সামনে। যে শিরে ছিল ঈমানের অহঙ্কার, সে শির আজ সেজদায় নত হয় জবরদস্তিতে। অথচ সেই অবনতির মুহূর্তেও তারা মাতম করে শহিদদের স্মরণে—যার মধ্যে নেই প্রতিবাদ, নেই শক্তির পুনরাবিষ্কার, নেই আত্মিক রূপান্তরের লক্ষণ। আছে কেবল ভণ্ডামি, আছে অভিনয়ের কৃত্রিমতা।
এই অবস্থাকে নজরুল শুধুই সমালোচনা করেননি; বরং তা থেকে উত্তরণের ইঙ্গিতও দিয়েছেন। মোহররম তাঁর কাছে নিছক কান্নার উপলক্ষ নয়, বরং আত্মশুদ্ধির, আত্মস্মরণের, এবং আত্মত্যাগের পথ অনুধাবনের এক তীব্র সংকেত। হোসেনের আত্মবলিদান যদি সত্যিই স্মরণ করতে হয়, তাহলে চাই তাঁর পথ অনুসরণের অঙ্গীকার—সত্যের জন্য দাঁড়াবার সাহস, জুলুমের বিরুদ্ধে কলম ও কণ্ঠস্বর তোলার সততা, এবং কেবল চিত্তবিনয় নয়, চেতনার জাগরণ।
এই দৃষ্টিভঙ্গিই নজরুলকে করেছেন কালজয়ী। তিনি শোককে করে তুলেছেন শক্তি, কান্নাকে রূপ দিয়েছেন বিদ্রোহে, এবং ইতিহাসকে ব্যবহার করেছেন ভবিষ্যতের পথ নির্দেশের জন্য। তাঁর লেখা আজও আমাদের মনে করিয়ে দেয়—মোহররম কেবল অতীতের স্মরণ নয়, বর্তমানের আত্মসমীক্ষা, ভবিষ্যতের প্রস্তুতির মাস। আর সেই প্রস্তুতি অভিনয়ে নয়, চাই অন্তরের গ্লানিমোচনে, চেতনার জাগরণে।
বিষ বাণী
কাজী নজরুল ইসলামের প্রবন্ধ ‘বিষবাণী’ তাঁর তীব্র দ্রোহ ও বৈপ্লবিক আহ্বানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই প্রবন্ধে কবি সরাসরি দেশের তরুণ সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন—তাঁরা যেন অন্তরে সঞ্চয় করে রাখে সেই বিষ, যা দাসত্ব ও পরাধীনতার শিকড় উপড়ে ফেলতে পারে। ঠিক যেমন একটি সাপ তার শরীরে ধারণ করে রাখে প্রাণঘাতী বিষ, তেমনি নজরুল তরুণদের বলছেন তাঁদের শরীর, মন, চিন্তা ও অস্তিত্বের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিতে কাল-বিষ। এই বিষ হল স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদার চেতনা, যা আত্মত্যাগ ও বিপ্লবের পথে চলার শক্তি যোগায়। তাঁর ভাষায় এই বিষ-সঞ্চয় কোনও নেতিবাচকতা নয়, বরং এটি হলো জ্বালাময় সাহস ও প্রতিরোধের প্রতীক।
নজরুল বলেন, তরুণদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কারণ এই বিষের এমন প্রখরতা থাকবে যে, শত্রুরা তাদের কাছে আসতে সাহসই পাবে না। যারাই কাছে আসবে, তারা যেন উগ্র বিষের দাহে ছারখার হয়ে যাবে। কবির ভাষায়—
“হে আমার তিক্ত-চিত ভুজগ তরুণ দল! তোমাদের ধরবে কে? মারবে কে? যে ধরতে আসবে, তার হাড়-মাংস খসে খসে পড়বে উগ্র বিষের দাহনে। কোন দুঃসাহসী বন্দী করবে তোমাদের? কারার লৌহদন্ড দারুণ বিষ-দাহনে খসে গলে পড়বে।”
এই রূপকটিতে নজরুল তরুণদের তুলনা করেছেন সাপের সঙ্গে—যে সাপ অহেতুক কামড়ায় না, কিন্তু যখন বাধ্য হয়, তখন তার বিষ হয়ে ওঠে মৃত্যুদানকারী। কবির বিশ্বাস ছিল, দেশের তরুণরাই স্বাধীনতার প্রকৃত বাহক, আর এই বিষের প্রতীকী শক্তি তাঁদের আত্মমর্যাদার অস্ত্র। এটি ভয় নয়, বরং ভয়ের অবসান ঘটাবার সাহসিকতা।
অন্যদিকে, ক্ষুদিরামের মা শীর্ষক প্রবন্ধে নজরুল এক আশ্চর্য সংবেদনশীল অথচ দীপ্তিময় দৃশ্যপট নির্মাণ করেছেন। এখানে বিদ্রোহ আর মাতৃত্ব এক অনন্য বন্ধনে যুক্ত হয়েছে। ইতিহাসে শহিদ ক্ষুদিরামের নাম আমাদের সকলেরই জানা, কিন্তু নজরুল তাঁর আত্মত্যাগকে শুধু একজন বিপ্লবীর মৃত্যু হিসেবে দেখেননি—তাঁর আত্মবলিদানকে করেছেন জাতির নবজাগরণের প্রতীক, মায়ের কোল থেকে উঠে আসা প্রতিবাদী সন্তানের প্রতিরূপ।
প্রবন্ধে বর্ণিত হয়েছে, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে ক্ষুদিরাম তাঁর মায়ের কাছে একটি গান গেয়েছিলেন—
“আঠারো মাসের পরে
জনম নেব মাসির ঘরে, মাগো,
চিনতে যদি না পার মা
দেখবে গলায় ফাঁসি
একবার বিদায় দেমা ফিরে আসি।”
এই গান যেন হয়ে ওঠে বাংলার প্রতিটি ঘরে জন্ম নেওয়া ক্ষুদিরামের প্রতিশ্রুতি। নজরুল বলেন, ক্ষুদিরাম মারা যাননি—তিনি ফিরে এসেছেন লক্ষ লক্ষ সন্তানের রূপে, যাঁরা আজ বাংলার ঘরে ঘরে। ফাঁসির দড়ি তাঁকে থামাতে পারেনি, কারণ মাতৃস্নেহের ক্ষুধা তাঁর এখনও মেটেনি। তাই তিনি ফিরে এসেছেন প্রতিটি জননীর কোলজুড়ে। তাঁর মৃত্যু জন্ম দিয়েছে আরও হাজার হাজার ক্ষুদিরামের। এখানে ‘মাসির ঘর’ মানে কেবল এক আত্মীয়র গৃহ নয়, বরং সেই প্রতীকী ভূমি, যেখানে প্রতিবাদ ও সাহসিকতার বীজ বপন করা হয়।
এই প্রসঙ্গে নজরুলের বক্তব্য গভীর দ্যোতনায় উদ্ভাসিত—
“ক্ষুদিরাম গেছে, কিন্তু সে ঘরে ঘরে জন্ম নিয়ে এসেছে কোটি কোটি ক্ষুদিরাম হয়ে। তোমারা চিনতে পারছ না, মা, তোমার মাথায় আবদ্ধ। ছেড়েদাও ছেড়েদাও আমাদের ক্ষুদিরামকে – তোমাদের ছেলেদের ছেড়ে দাও, ওরা আমাদের –আমাদের লক্ষ্মীছাড়ার দল।”
এই আহ্বানে শুধু দেশপ্রেম নয়, আছে মাতৃত্বের দৃষ্টিতে সাহসিকতার নতুন সংজ্ঞা। তিনি বলতে চান, মাতৃত্ব কেবল সন্তানের মঙ্গল কামনার সীমায় আবদ্ধ নয়, বরং তা বিপ্লব ও আত্মোৎসর্গের উৎস। মায়েরা যদি তাঁদের সন্তানদের কেবল ঘরের মাটির সঙ্গে বেঁধে রাখেন, তবে ক্ষুদিরামের মতো সন্তানের আত্মবলিদান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।
এই দুই প্রবন্ধে নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গি দুটি ভিন্ন কিন্তু পরস্পরসম্পর্কযুক্ত ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। বিষবাণীয় তিনি বিদ্রোহী তরুণদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, আর ক্ষুদিরামের মায় মাতৃমনের শক্তিকে সাহসিকতার উৎসে রূপান্তরিত করেছেন। এই দুই ধারায় তিনি দেখিয়েছেন, একটি জাতিকে জাগিয়ে তুলতে হলে চাই সাহসিকতা, চেতনা ও আত্মত্যাগের চর্চা, যা গড়ে ওঠে পরিবার থেকে, সমাজ থেকে এবং অন্তরের শক্তি থেকে।
নজরুলের ভাষা কখনও বজ্রের মতো কাঁপিয়ে তোলে, কখনও মায়ের মমতাভরা কোলের মতো জাগায় সাহস ও ভরসা। তাঁর কলমের বিষ ছিল না বিনাশের, ছিল মুক্তির ও নবজাগরণের, আর তাঁর মাতৃমন্দিরের আহ্বান ছিল আত্মোৎসর্গের পবিত্রতম ভাষ্য। এই প্রবন্ধদুটি সেই দুই ধারার সংমিশ্রণে হয়ে ওঠে এক অনন্য প্রতিরোধের মহাকাব্য।
ধূমকেতুর পথ
কাজী নজরুল ইসলামের প্রবন্ধ ‘ধূমকেতুর পথ’ তাঁর রাজনৈতিক বোধ, বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বাধীনতার জন্য অগাধ তৃষ্ণার বহিঃপ্রকাশ। এই রচনার মধ্য দিয়ে নজরুল কেবল একটি পত্রিকার দিকনির্দেশই দেননি, তিনি জানিয়েছেন সেই আগ্নেয় পথের কথা—যেখানে নেতৃত্ব দেবে ধ্বংস নয়, বরং নবসৃজনের এক অসীম আকাঙ্ক্ষা। এই প্রবন্ধের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের স্পষ্ট ও অনড় ঘোষণা। নজরুলের কাছে ‘ধূমকেতু’ কেবল একটি পত্রিকা নয়, এটি একটি আগুনজ্বলা রথ—যার সারথি নিজে, আর লক্ষ্য—ভারতবর্ষের পরাধীনতার শিকল ছিঁড়ে তাকে সম্পূর্ণ স্বরাজে প্রতিষ্ঠা করা।
এ দেশের বহু মানুষ, পাঠক ও শুভানুধ্যায়ী প্রশ্ন করেছিলেন—‘ধূমকেতুর পথ কী?’, ‘ধূমকেতু আসলে কী বলতে চায়?’ এই প্রশ্নের জবাব নজরুল দিয়েছেন প্রত্যয়ের সঙ্গে, নির্ভীক কণ্ঠে। তিনি বলেছেন—“ধূমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়৷” এখানেই ধূমকেতুর আসল অভিসন্ধি। আর এরই সূত্রে তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর সুস্পষ্ট অবস্থান:
“স্বরাজ টরাজ বুঝি না, কেননা ও কথাটার মানে এক এক মহারথি এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমানু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ হায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে।”
এই বক্তব্যে নজরুল কেবল রাজনৈতিক নেতাদের কৌশলী দ্ব্যর্থতার প্রতিবাদ জানাননি, বরং পরাধীনতার মূল শিকড়েই আঘাত হেনেছেন। ‘স্বরাজ’ শব্দটি অনেকের মুখে উচ্চারিত হলেও তার অন্তর্নিহিত অর্থ যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রয়োজনে পরিবর্তিত হয়েছে, তা কবি বুঝেছিলেন অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে। তাই তিনি সরাসরি ঘোষণা করেন—তাঁর কাছে ‘পূর্ণ স্বাধীনতা’ মানে হল একটি একবিন্দু জমিও বিদেশী শাসনের অধীনে থাকবে না, ভারতের অস্তিত্ব, অধিকার ও দায়িত্ব সমস্তটাই থাকবে ভারতবাসীর হাতে।
তবে কেবল এই উচ্চারণে তো স্বাধীনতা অর্জিত হয় না। নজরুলও তা জানতেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, কেবল আবেদন, প্রার্থনা কিংবা অহিংসার তাত্ত্বিক চর্চায় এ দেশে স্বাধীনতার সূর্য ওঠে না। তাঁর চোখের সামনে ছিল গান্ধিজীর নেতৃত্বে অহিংস আন্দোলনের দীর্ঘ সময়কাল—যেখানে সমগ্র ভারতবর্ষ বেদনায় কাতর, আকাঙ্ক্ষায় দীর্ণ, কিন্তু কার্যত স্বাধীনতা অধরা। সেই সময়েই নজরুল তুলে ধরেন এক ভিন্নতর কণ্ঠস্বর। তিনি বলেন, যদি সত্যিই আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে চাই, তবে প্রয়োজন এক সর্বাত্মক বিদ্রোহ—সকল বাধা, শৃঙ্খল, রীতিনীতি ও মিথ্যা নীতিবোধের বিরুদ্ধে।
এই বিদ্রোহ কেবল অস্ত্রধারী নয়, এটি চিন্তার, চেতনার, ও সাহসিকতার বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহ একদিকে যেমন বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে, তেমনি অন্যদিকে নিজের ভেতরের জড়ত্ব, কুসংস্কার ও দুর্বলতার বিরুদ্ধেও। নজরুল এই বিদ্রোহকে জাতীয় কর্তব্যের রূপ দিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস, ধ্বংস না হলে সৃজন আসে না—তাই ধূমকেতুর মত প্রকাশ্য ও বিস্ফারক বিদ্রোহের প্রয়োজন ছিল সে সময়ে।
এই বিদ্রোহই হল ‘ধূমকেতুর পথ’—এক এমন পথ, যা ভয়কে অস্বীকার করে, আপসকে প্রত্যাখ্যান করে, আর স্বাধীনতার জন্য অনিবার্য সর্বস্বত্যাগের আহ্বান জানায়। এই পথই হল ভারতের নবজাগরণের শাণিত রূপরেখা।
সারসংক্ষেপে বলা যায়, ‘ধূমকেতুর পথ’ প্রবন্ধে নজরুল নিজেকে কেবল একজন কবি, লেখক বা সম্পাদক হিসেবে নয়, একজন জাতির সারথি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন—যিনি ধ্বংসের শিখা হাতে ধরে আহ্বান জানাচ্ছেন নতুন স্বাধীন সূর্যোদয়ের। তাঁর ভাষা আগ্নেয়, কিন্তু সেই আগুনে পুড়ছে না মানুষ—বরং গলছে শিকল, পুড়ছে দাসত্ব। ধূমকেতুর বার্তা তাই আজও প্রাসঙ্গিক—যখনই অন্যায়, মিথ্যা, শোষণ বা নিপীড়ন মাথা তোলে, তখনই প্রয়োজন সেই ধূমকেতুর ঝলকানি, যার পথ অনুসরণ করেই সম্ভব এক সত্যিকার মুক্তির অভিযাত্রা।
মন্দির মসজিদ
১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে আগস্ট গণবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় কাজী নজরুল ইসলামের অন্যতম বিখ্যাত ও তাৎপর্যপূর্ণ প্রবন্ধ ‘মন্দির মসজিদ’। এই প্রবন্ধটি শুধু একটি সময়বিশেষে রচিত রাজনৈতিক বিবৃতি নয়—এটি একদিকে যেমন গভীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে, তেমনি নজরুলের ধর্মীয় চেতনা ও মানবিকতার সর্বোচ্চ প্রকাশও এতে নিহিত রয়েছে। এখানেই তাঁর অসাম্প্রদায়িক মানস ও মৌলিক চিন্তার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
একজন মুসলমান হিসেবে নজরুল তাঁর ব্যক্তিগত ও সাহিত্যিক জীবনে কখনোই ধর্মীয় গোঁড়ামি বা জাতিভেদপ্রথাকে সমর্থন করেননি। বরং বরাবরই তিনি ছিলেন সমাজের বঞ্চিত, নিপীড়িত ও প্রান্তিক মানুষের পক্ষের কণ্ঠস্বর। তাঁর দৃষ্টিতে মন্দির কিংবা মসজিদ কোনো পবিত্রতার প্রতীক নয়, যদি তা মানুষের মধ্যে বিভাজন ও হিংসা ছড়ায়। সেই কারণেই তিনি নিঃসঙ্কোচে উচ্চারণ করেন—“মন্দির ও মসজিদ শয়তানদের ঐ মন্ত্রনাগার।” এই উক্তি কেবল ধর্মস্থানের প্রতি বিষোদ্গার নয়, বরং সেইসব ধর্মান্ধদের প্রতি এক তীব্র ধিক্কার—যাঁরা ধর্মের নামে ঘৃণা, হিংসা ও রক্তপাত ছড়ায়।
নজরুল তাঁর কবিতাতেও বারবার এই বার্তাই দিয়েছেন—ধর্মের মূলস্বরূপ প্রেম, করুণা ও মানবতার মধ্যেই নিহিত, সেটি যদি হারিয়ে যায়, তবে মন্দির-মসজিদের নির্মাণ যত মহৎই হোক না কেন, তা হয়ে ওঠে নিষ্ঠুরতা ও অন্ধত্বের কেন্দ্র। তিনি মনে করেন, হিন্দুদের মন্দির কিংবা মুসলমানদের মসজিদ—দুই-ই হয়ে উঠছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বিশৃঙ্খলার মূল উৎস, যেখান থেকে ঘৃণার বীজ উপ্ত হচ্ছে সমাজে।
১৯২৬ সালের ২রা এপ্রিল কলকাতার বুকে ঘটে যায় ভয়াবহ এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, যা শুধু ধর্মীয় উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ ছিল না, ছিল এক নির্মম অমানবিক অধ্যায়ের সূচনা। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এমন এক বিভেদ, যার ফলে শহরের পথে পথে বইতে থাকে রক্ত, মৃতদেহ পড়ে থাকে রাস্তায়, অচল হয়ে পড়ে জনজীবন। নজরুল এই পরিস্থিতিতে গভীর বেদনায় মর্মাহত হন। তিনি উপলব্ধি করেন, যে দেশে ধর্মের নামে মানুষে মানুষে বিভেদ হয়, ঘর জ্বলে ওঠে প্রতিবেশীর ঘৃণায়—সেই দেশে স্বাধীনতার স্বপ্ন কেবল মরীচিকা। রাজনৈতিক স্বাধীনতা তখনই অর্থবহ, যখন মানুষের চেতনায় আসবে একতা, সহিষ্ণুতা ও ভালোবাসা।
এই অভিজ্ঞতা তিনি লিপিবদ্ধ করেন প্রবন্ধের এক অংশে, যেখানে বর্ণনা করেন নিজের চোখে দেখা সেই বিভীষিকার দৃশ্য—
“একস্থানে দেখিলাম, ঊনপঞ্চাশ জন ভদ্র-অভদ্র হিন্দু মিলিয়া একজন শীর্ণকায় মুসলমান মজুরকে নির্মম ভাবে প্রহার করিতেছে, আর একস্থানে দেখিলাম, প্রায় ওই সংখ্যাক মুসলমান মিলিয়া একজন দুর্বল হিন্দুকে পশুর মতো মারিতেছে। দুই পশুর হাতে মার খাইতেছে দুর্বল অসহায় মানুষ। ইহারা মানুষকে মারিতেছে যেমন করিয়া বুনো জংলি বর্বরেরা শূকরকে খোঁচাইয়া মারে।”
এই বিবরণ কেবল সংবাদভাষ্যে সীমাবদ্ধ নয়—এটি একসময়ের রাজনৈতিক ও মানবিক পরিস্থিতির চরম ব্যর্থতার দলিল। এখানে নজরুলের বর্ণনায় উঠে এসেছে সমাজের দুই বিপরীত মেরু—হিন্দু ও মুসলমান—যাঁরা উভয়েই যেন মানবতা বিস্মৃত হয়ে উঠেছেন নৃশংস হিংস্রতায়। আর এই হিংসার শিকার হয়েছে কেবল সাধারণ, নিরীহ, অসহায় মানুষ। নজরুলের দৃষ্টিতে এই দুই সম্প্রদায় যেন পরিণত হয়েছে আদিম বর্বরতায়, যারা মানুষের বুকে ঘৃণার ছুরি চালিয়ে আনন্দ খোঁজে।
এই প্রবন্ধে কবি একদিকে যেমন সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার মুখোশ ছিঁড়ে দেন, তেমনি আরেকদিকে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানান সত্যিকারের ধর্ম ও মানবিকতার প্রতি প্রত্যাবর্তনের। ধর্মের নামে রক্তপাত, বিভাজন ও শত্রুতা কখনোই ঈশ্বরের ইচ্ছা হতে পারে না—এই বার্তাই তিনি দিতে চেয়েছেন দৃপ্তভাবে। ধর্মের মর্মবাণী যদি হয় ভালোবাসা, তবে সে ভালোবাসার মুখোশ পরে ঘৃণার বিস্তার চলতে পারে না।
সার্বিকভাবে, ‘মন্দির মসজিদ’ প্রবন্ধে নজরুল ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা ও কূপমণ্ডূকতার বিরুদ্ধে এক নির্ভীক প্রতিবাদ রচনা করেছেন। এখানেই তাঁর কলম পরিণত হয় এক তীব্র ন্যায়বোধসম্পন্ন অস্ত্রে, যা ধর্মের নামে অশুভ শক্তিকে উন্মোচিত করে। এই প্রবন্ধ আজও প্রাসঙ্গিক—কারণ ধর্মের নামে যখনই সমাজে বিভেদ সৃষ্টি হয়, তখনই দরকার হয় এমন এক কণ্ঠস্বরের, যিনি বলবেন: ধর্ম নয়, মানুষই মুখ্য; ঈশ্বর নয়, মানবতাই সত্য। আর সেই কণ্ঠস্বরের নামই—কাজী নজরুল ইসলাম।
হিন্দু মুসলমান
১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর গণবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় কাজী নজরুল ইসলামের প্রবন্ধ ‘হিন্দু-মুসলমান’—যা কেবল একটি মুহূর্তের ভাষ্য নয়, বরং ভারতীয় উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ইতিহাসে এক অনন্য ঐতিহাসিক দলিল। এই রচনায় নজরুল প্রত্যাশা করেছিলেন এমন একটি জাতি, যেখানে হিন্দু ও মুসলমান কেবল সহাবস্থান নয়, বরং সৌহার্দ্য ও আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে উঠবে। তাঁর এই প্রবন্ধ তাই নিছক নীতিকথা নয়—এটি ছিল জাতির আত্মজিজ্ঞাসা ও পুনর্জাগরণের এক রূপরেখা।
এই প্রবন্ধে নজরুল জাতির হৃদয়ে গেঁথে দিতে চেয়েছেন এক অমূল্য মন্ত্র, যেটি আজও যুগান্তকারী
“এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান।
মুসলিম তার নয়নমণি হিন্দু তাহার প্রাণ।”
এই পংক্তিতে স্পষ্ট, নজরুল সাম্প্রদায়িক বিভেদের ধারক নন; বরং তিনি দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি, প্রেম ও সহাবস্থানকেই আদর্শ বলে মানতেন। তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক ফুলের দুটি কুসুমের মতো, যেগুলি একই বৃন্তে সমভাবে সৌন্দর্য ছড়িয়ে দেয়। একে ছাড়া অপরটি অপূর্ণ।
নজরুল মনে করতেন, হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে যে বিভেদ তা আসলে বাহ্যিক, আরোপিত এবং সংস্কারজাত। যদি অন্তরের ভিতর থেকে জাতপাতের ভেদরেখা মোচন না করা যায়, তবে কেবল রাজনৈতিক বা সামাজিক উপদেশে এই বিভেদ দূর হবে না। এই প্রবন্ধে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই রয়েছে কিছু গোঁড়া, যারা নিজেদের ধর্মীয় চিহ্নকে পরিণত করেছে অহংকারের হাতিয়ারে—আর সেই অহংকার থেকেই জন্ম নিচ্ছে বিবাদ ও হিংসা।
নজরুল অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় সমালোচনা করেন সেই সমস্ত ধর্মীয় চিহ্নগত গোঁড়ামিকে, যেগুলি হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিদ্বেষের বীজ রোপণ করছে। তিনি বলেন—
“হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্ব দুই-ই সওয়া যায় কিন্তু তাদের টিকিত্ব দাড়িত্ব অসহ্য। কেননা এই দুটোই মারামারি বাঁধায় । টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা পন্ডিত্ব। দাড়িত্ব মুসলমান তেমনি দাড়িত্ব ইসলামত্ব নয়। সেটা এই পান্ডিত্ব মোল্লার মারামারি। হিন্দু-মুসলমানের মারামারি নয়।”
এই বক্তব্যে নজরুল দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে চলমান দাঙ্গা ও বিভেদের মূল উৎস চিহ্নিত করেন—সেটি হচ্ছে তথাকথিত ধর্মীয় পাণ্ডিত্য ও গোঁড়ামি, যা কেবল মানুষের মধ্যে নয়, ধর্মের মধ্যেও বিভাজন সৃষ্টি করে। তাঁর মতে, হিন্দুত্ব বা ইসলাম স্বয়ং কখনো কারো বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু ‘টিকিত্ব’ ও ‘দাঁড়িত্ব’—অর্থাৎ হিন্দু ব্রাহ্মণ্য পাণ্ডিত্য ও মুসলিম মৌলবাদের এই রূপ দুটি সমাজে শুধু বিভেদই নয়, সংঘর্ষের বীজ ছড়িয়ে দেয়। নজরুল মনে করতেন, এগুলি ধর্ম নয়, বরং ধর্মের নামে চর্চিত এক প্রকার বিকার, যা সাধারণ মানুষকে একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয়।
এই প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম কেবল ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার সমালোচনা করেননি, বরং দিয়েছেন একটি নির্মল আদর্শ—যেখানে মানুষ আগে মানুষ, পরে তার ধর্মীয় পরিচয়। তাঁর কণ্ঠ ছিল এক ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের কণ্ঠ, যেখানে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও ধর্মীয় গোঁড়ামির কোনো স্থান নেই। নজরুলের ভাবনায় হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক ছিল হৃদয়ের সম্পর্ক, মাটির সম্পর্ক, দেশের সম্পর্ক—যে সম্পর্ক ধর্মের চেয়েও বড়।
আজকের সময়েও নজরুলের এই আহ্বান আমাদের জন্য এক অমূল্য দিশারী। কারণ ধর্মীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে, জাতপাত, গোঁড়ামি ও বিদ্বেষের শিকল ছিঁড়ে একটি মানবিক সমাজ গড়ার জন্য যে সাহসিকতা ও ভালোবাসা প্রয়োজন, তা এই প্রবন্ধে প্রতিটি পঙ্ক্তিতে অনুরণিত হয়েছে।
‘হিন্দু-মুসলমান’ প্রবন্ধে তাই নজরুল হয়ে ওঠেন কেবল একজন কবি নন—একজন দূরদর্শী সমাজচিন্তক, যাঁর কলমে ঝরে পড়ে সম্প্রীতির অমৃতবাণী। এই বাণী আজও আমাদের প্রয়োজন, কারণ এই বাণী মানুষকে মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেয়—ধর্ম নয়, ভালোবাসা দিয়ে পৃথিবী গড়ার প্রেরণা দেয়।
ধূমকেতু
১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে, বাংলা ১৩৬৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে, প্রকাশিত হয় ‘ধূমকেতু’ শিরোনামে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-সংকলন। কাজী নজরুল ইসলাম রচিত এই গ্রন্থটি কেবল তাঁর সাংবাদিক ও গদ্যচর্চার এক উজ্জ্বল নিদর্শন নয়, বরং তাঁর বিদ্রোহী মানস, সাম্প্রতিক সমাজ-রাজনীতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানবতাবাদী দর্শনের একটি রূপরেখাও বটে।
এই প্রবন্ধগ্রন্থে মোট একুশটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে, যেগুলির মধ্যে কিছু নজরুল-প্রণীত, আবার কিছু তাঁর নামে প্রকাশিত হলেও প্রকৃত রচয়িতা অন্য কেউ। সংকলনভুক্ত প্রবন্ধগুলি হল—
১) ধূমকেতুর আদি উদয়স্মৃতি
২) ধূমকেতুর পথ
৩) আমার ধর্ম
৪) মোহম
৫) মুশকিল
৬) লাঞ্ছিতা
৭) বিষ-বাণী
৮) নিশান-বরদার
৯) তোমার পণ কি
১০) ভিক্ষা দাও
১১) আমি সৈনিক
১২) বর্তমান বিশ্বসাহিত্য
১৩) মেয় ভুখা হুঁ
১৪) কামাল
১৫) ব্যর্থতার ব্যথা
১৬) আমার সুন্দর
১৭) ভাববার কথা
১৮) আজ চাই কি
১৯) নজরুল ইসলামের পত্র
২০) একখানি চিঠি
২১) চিঠির উত্তর
এই তালিকার মধ্য থেকে কিছু প্রবন্ধের উৎস অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, সেগুলি নজরুলের পূর্ববর্তী রচনাসমগ্র থেকে সংগৃহীত হয়েছে। যেমন— ‘মোহররম’ ও ‘বিষ-বাণী’ নামক প্রবন্ধদুটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল নজরুলের বিখ্যাত সংকলন ‘রুদ্রমঙ্গল’-এ। একইভাবে ‘আমি সৈনিক’ এবং ‘মেয় ভুখা হুঁ’—এই দুটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত ছিল তাঁর আরেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ‘দুর্দিনের যাত্রী’-তে।
তবে এই সংকলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ‘একখানি চিঠি’ রয়েছে, যা নজরুলের নিজের লেখা নয়। এটি রচনা করেছিলেন সাহিত্যিক ইব্রাহিম খাঁ। নজরুলের নামের সঙ্গে চিঠির বিষয়বস্তুর সম্পর্ক থাকলেও, প্রণেতার পার্থক্য এখানে বিশদভাবে উল্লেখযোগ্য।
এছাড়াও, ‘ব্যর্থতার ব্যথা’ প্রবন্ধটি গণবাণী পত্রিকায় ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। অন্যদিকে ‘আমার সুন্দর’ শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রথমবার প্রকাশিত হয় নবযুগ পত্রিকায়, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে।
তালিকাভুক্ত ‘নজরুল ইসলামের পত্র’ এবং ‘চিঠির উত্তর’—এই দুটি রচনার প্রকাশ ধূমকেতু পত্রিকায় ঘটেনি। ফলে এগুলিকে ধূমকেতু-প্রসূত না বলে সংকলনের প্রাসঙ্গিক সংযুক্তি হিসেবে ধরা যেতে পারে।
এখানে উল্লিখিত ‘ধূমকেতুর আদি উদয়স্মৃতি’ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ধূমকেতু পত্রিকার নবপর্যায়ে—২২শে আগস্ট, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে। এটি ছিল পত্রিকাটির পুনর্জাগরণ পর্বের এক স্মারক রচনা।
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ‘লাঞ্ছিতা’ প্রথম প্রকাশিত হয় ধূমকেতু পত্রিকার প্রথম বর্ষের ২০শে ডিসেম্বর, ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে। আর ‘নিশান-বরদার’ প্রবন্ধটি সেই একই বর্ষের ৩রা নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।
উপরোক্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে অনেকগুলিই পূর্ববর্তী আলোচনায় বিশ্লেষিত হয়েছে। প্রতিটি প্রবন্ধ নজরুলের ভাবধারার বিভিন্ন মাত্রা—প্রতিবাদ, প্রেম, ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি ও বিশ্বসাহিত্যের প্রতি তাঁর আগ্রহ—প্রকাশ করে। এই সংকলন নিঃসন্দেহে কাজী নজরুল ইসলামের গদ্যভাষার এক অনন্য শৈলীর দলিল, যেখানে কবিত্ব ও চিন্তাধারার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। এই রচনাগুলির মাধ্যমে আমরা নজরুলের কলমের ঔদ্ধত্য, আবেগ, বেদনা ও দায়িত্ববোধ—সমস্ত কিছুরই পরিচয় লাভ করি।
সার্বিকভাবে, ‘ধূমকেতু’ প্রবন্ধগ্রন্থটি একাধিক পত্রিকায় ও ভিন্ন ভিন্ন কালপর্বে প্রকাশিত রচনাগুলির এক সংহত ও সুনির্বাচিত সংগ্রহ—যা পাঠককে নজরুলচিন্তার বহুবর্ণ আয়নায় অনুরণিত করে তোলে।
তথ্যসূত্র :
- ১। গুপ্ত, ড. সুশীল কুমার: নজরুল চরিতমানস, দেজ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ, এপ্রিল, ২০১২,
- ৩। খান, আজহারউদ্দীন : বাংলা সাহিত্যে নজরুল, সুপ্রিম পাবলিশার্স,
- ৪। গুপ্ত, সুশীলকুমার : সাহিত্য সাধকচরিতমালা (ষোড়শখন্ড),বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন,
- ৫। আমদ, মুজফ্ফর : কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পঞ্চম মুদ্রণ, আগস্ট, ২০১২
- ১০। এই অধ্যায়ে প্রবন্ধ গ্রন্থের বাক্য, পদ, বক্তব্য নেওয়া হয়েছে যে বই থেকে, উক্ত বইটি হল কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী, প্রথম প্রকাশ, জুন, 2005।

 নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা
নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা