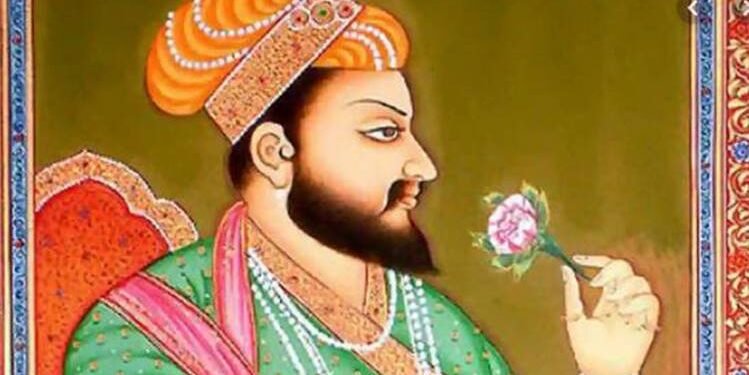সিন্ধুতে বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে থাট্টায় ১৩৫১ খ্রিস্টাব্দের ২০ শে মার্চ মুহাম্মদ বিন তুঘলকের আকস্মিক মৃত্যু ঘটলে তার সৈন্যবাহিনীতে বিশৃংখলা দেখা দেয়। নেতৃত্বের অভাবে সৈন্যদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয় এবং সৈন্যবাহিনীর বেতনভুক মােঙ্গল সৈন্যরা লুটতরাজ শুরু করে। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের কোনাে পুত্র সন্তান ছিল না এবং বারাণী বলেছেন যে তিনি কাউকে উত্তরাধিকারীও মনােনীত করে যান নি। ফলে দিল্লির সিংহাসনের উত্তরাধিকারের কোনাে নিশ্চয়তা না থাকায় এই বিশৃংখলা আরাে গুরুতর আকার ধারণ করে। এ রকম দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে সেনানায়ক ও আমীররা মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পিতৃব্য-পুত্র ফিরােজ শাহকে সিংহাসনে আরােহণের অনুরােধ জানায়। তাদের পীড়াপীড়িতে ও সাম্রাজ্যের শৃংখলা রক্ষার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরােজ শাহ সুলতান ফিরােজ শাহ তুঘলক উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরােহণ করেন। ফলে সৈন্যবাহিনীতে শৃংখলা ফিরে আসে। ইতােমধ্যে দিল্লিতে ওয়াজির খান জাহান আহম্মদ বিন আয়াজ পরলােকগত সুলতানের পুত্ররূপে পরিচয় দিয়ে ছয় বছর বয়সী একজন বালককে গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ উপাধি দিয়ে সিংহাসনে বসান। সুলতান ফিরােজ শাহ তুঘলক দিল্লির দিকে অগ্রসর হলে খান জাহান আত্মসমর্পণ করেন। ফিরােজ শাহ, খান জাহানকে সামানার গভর্নর নিযুক্ত করেন, কিন্তু সামানা যাওয়ার পথে তিনি নিহত হন।
১৩৫১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ফিরােজ শাহ তুঘলক সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনের প্রতি তার কোন লােভ ছিল না, সিংহাসনের জন্য তিনি উপযুক্তও ছিলেন না। তবে তাঁর সুদীর্ঘ ৩৭ বছরের রাজত্বকালে নিত্যপ্রয়ােজনীয় জিনিসপত্রের দাম কম ছিল, দেশে কোন দুর্ভিক্ষ বা মহামারী দেখা যায়নি, কোনাে বড় আকারের বিদেশী আক্রমণও ঘটেনি।
প্রায় দুই যুগ ধরে কিয়ামুল-মুলক খান জাহান আজম হুমায়ুন ওয়াজির হিসেবে ফিরােজ শাহের অধীনে দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ধর্মান্তরিত মুসলমান। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করে তিনি ওয়াজির খান জাহানের অধীনে নায়েব – ওয়াজির হয়েছিলেন। ফিরােজ শাহের রাজত্বকালে তিনি ওয়াজির পদে নিযুক্ত হন। তাঁর দক্ষতার জন্য ফিরােজ শাহ তাকেই ‘দিল্লির প্রকৃত মুসলমান’ রূপে অভিহিত করেন।
বাংলা অভিযান
বিজেতা ও সেনাপতি হিসাবে সুলতান ফিরােজ শাহ তুঘলক কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে স্বাধীন হয়ে যাওয়া কয়েকটি রাজ্য তিনি পুনর্দখলের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ১৩৫৩ – ৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলার স্বাধীন সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহের বিরুদ্ধে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। বাংলায় পৌঁছে ফিরােজ শাহ সে দেশের ওপর তার আইনগত অধিকার ও ইলিয়াস শাহের অত্যাচারের কথা উল্লেখ করে একটি ইশতেহার জারি করেন। বাংলার জনসাধারণকে নিজ পক্ষে আনার জন্য তিনি তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা দানেরও ঘােষণা দেন। ইলিয়াস শাহ ফিরােজ শাহের বাংলা আক্রমণের সংবাদ পেয়ে একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। ফিরােজ শাহ পান্ডুয়া দখল করে সেখানে অবস্থান করতে থাকেন। কিছুদিন পর ফিরােজ শাহ দিল্লি ফিরে যাবার ভান করে পিছু হটতে থাকলে ইলিয়াস শাহ দুর্গ থেকে বের হয়ে দিল্লি বাহিনীকে আক্রমণ করেন। উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং ইলিয়াস শাহ আবার একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। ফিরােজ শাহ তুঘলক একডালা দুর্গ অবরােধ করেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক শামস-ই-সিরাজ আফিফের মতে দুর্গের ভিতরের মুসলমান রমণীদের কান্না শুনে ফিরােজ শাহ দুর্গ দখল না করেই দিল্লি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ফিরােজ শাহ পান্ডুয়া ফিরে আসেন পরে তিনি দিল্লি প্রত্যাবর্তন করেন। নিরপেক্ষভাবে বলা যায় যে, ফিরােজ শাহ তুঘলকের প্রথম বাংলা অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল।
১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস শাহ মৃত্যুবরণ করেন। ১৩৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দে ফিরােজ শাহ আবার বাংলা দখলের উদ্দেশ্যে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাংলা আক্রমণ করেন। তাঁর সৈন্যবাহিনীতে ৭০,০০০ অশ্বারােহী, ৪৭০ টি হাতি, অনেক রণতরী এবং অসংখ্য পদাতিক সৈন্য ছিল। বাংলার সুলতান সিকান্দার শাহ পিতার মত একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অনেক দিন ধরে দুর্গ অবরােধ করেও ফিরােজ শাহ তা দখল করতে পারেন নি। দীর্ঘ দিনের নিস্ফল অবরােধে উভয় পক্ষেরই ধৈর্যচ্যুতি ঘটে এবং তাঁদের মধ্যে সন্ধি হয়। তাই দেখা যায় যে, ফিরােজ শাহ দুবার বাংলা আক্রমণ করলেও তা নিজ দখলে আনতে ব্যর্থ হন।
অন্যান্য রাজ্য আক্রমণ
বাংলা থেকে দিল্লি ফিরে আসার পথে ফিরােজ শাহ জাজনগর (উড়িষ্যা) আক্রমণ করেন। আগে জাজনগর দিল্লির বশ্যতা স্বীকার করেছিল এবং নিয়মিত কর হিসেবে দিল্লিতে হাতি পাঠাতাে। কিন্তু ফিরােজ শাহের দ্বিতীয়বার বাংলা অভিযানের সময় জাজনগরের রাজা বাংলার পক্ষে যােগদান করেছিলেন। দিল্লি বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আফিফের পিতা জাজনগরকে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী দেশরূপে বর্ণনা করেছেন। মুসলমানদের আক্রমণে ভীত হয়ে জাজনগরের রাজা পালিয়ে যান এবং পরে সন্ধি করতে বাধ্য হন। রাজা প্রতি বছর দিল্লির সুলতানকে কয়েকটি হাতি পাঠাতে অঙ্গীকার করেন। এবং সুলতান সন্তুষ্ট হয়ে দিল্লি ফিরে আসেন। পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দিরটি ধ্বংস করা হয় এবং ঐ মন্দিরের জগন্নাথদেবের মূর্তিটি দিল্লি নিয়ে আসা হয়।
১৩৬০-৬১ খ্রিস্টাব্দে ফিরােজ শাহ নগরকোট আক্রমণ করেন। মধ্যযুগের ভারতে নগরকোট ছিল এক দুর্ভেদ্য দুর্গ। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে বলা হয়েছে যে “নগরকোট নগরটি ছিল পাহাড়ের ওপর অবস্থিত এবং এর দুর্গটির নাম কাংড়া”। মুহাম্মদ বিন তুঘলক ১৩৩৭ খ্রিস্টাব্দে নগরকোট জয় করেছিলেন। কিন্তু তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে নগরকোটের রাজা স্বাধীনতা ঘােষণা করেন। ফিরােজ শাহের নগরকোট আক্রমণের এটাই ছিল প্রধান কারণ। নগরকোটের জ্বালামুখী মন্দির অতি প্রাচীন কাল থেকেই অত্যন্ত বিখ্যাত ছিল। এটা ছিল অত্যন্ত পুরনাে মন্দির এবং অসংখ্য হিন্দু প্রত্যেকদিন এ মন্দিরে পূজা করতে যেতাে এবং ধন-রত্ন উপহার দিতাে। ফিরােজ শাহ তুঘলকের আক্রমণের সংবাদ পেয়ে নগরকোটের রাজা দুর্গে আশ্রয় নেন। প্রায় ছয় মাস দুর্গ অবরােধের পর দুপক্ষের মধ্যে সন্ধি হয়। রাজা দুর্গের বাইরে এসে সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং সুলতান রাজাকে বহুমূল্যবান খেলাত প্রদান করেন। নগরকোটের মন্দির থেকে ফিরােজ শাহ ৩০০ মূল্যবান সংস্কৃত গ্রন্থ নিয়ে আসেন এবং আজউদ্দিন নামে তার এক সভাকবি দালাইল-ই-ফিরােজশাহী শিরােনামে ফার্সিতে অনুবাদ করেন।
সিন্দুর বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে মুহাম্মদ বিন তুঘলক প্রাণত্যাগ করেছিলেন। এর প্রতিশােধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে ফিরােজ শাহ তুঘলক এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ১৩৬১-৬২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু আক্রমণ করেন। শামস-ই-সিরাজ আফিফের মতে সিন্ধুর স্থানীয় নেতৃবর্গের বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ দমন করে সেখানে দিল্লির সুলতানের নিরঙ্কুশ আধিপত্য পুন:প্রতিষ্ঠা করা ছিল ফিরােজ শাহের সিন্দু অভিযানের মূল উদ্দেশ্য।
তিনি সিন্ধুর ‘জাম’ (শাসক) -এর রাজধানী থাট্টা অবরােধ করেন। সিন্দুর ‘জাম’ বাবিনিয়া তার বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে সুলতানকে প্রতিহত করতে থাকেন। মহামারীতে দিল্লি বাহিনীর তিন-চতুর্থাংশ ঘােড়া মারা যায় এবং সৈন্যবাহিনীতেও খাদ্যাভাব দেখা দেয়। এ অবস্থায় সুলতান গুজরাটের দিকে অগ্রসর হন। গুজরাটের শাসনকর্তা (গভর্নর) নিজামুল মুলক আমীর হােসেন ছিলেন সুলতানের ভগ্নিপতি। গুজরাটে এসে সুলতান আবার যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ইতােমধ্যে খান জাহানও দিল্লি থেকে অনেক সৈন্য ও বিপুল রণসম্ভার পাঠান। সিন্ধুর শাসক ভীত হয়ে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁকে দিল্লি নিয়ে আসা হয়। তবে সিন্ধুকে সাম্রাজ্যভুক্ত না করে পূর্ববর্তী শাসকের ভাই-এর হাতে এর শাসনভার ন্যস্ত করা হয়। ড. বানারসী প্রসাদ সাক্সেনার মতে সমগ্র দিল্লি সালতানাতের ইতিহাসে এটি ছিল সবচেয়ে অব্যবস্থিত সামরিক অভিযান।
জনহিতকরণ কার্যাবলী
বিজেতা ও সেনাপতি হিসাবে ফিরােজ শাহের সাফল্য অত্যন্ত সীমিত। তবে প্রজাহিতৈষী সুলতানরূপে তিনি ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করেছেন। সিংহাসনে আরােহণ করে তিনি বহুবিধ সংস্কার সাধন করেছিলেন। শাসনকাজে তিনি ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি শরিয়তের বিধি অনুসারে রাজকার্য পরিচালনা করতেন এবং সব সময়ই আলেমদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। মিশরের খলিফার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি দুবার খলিফার কাছ থেকে সনদ লাভ করেছিলেন। সুলতান ফিরােজ শাহ তুঘলক ছিলেন সুন্নি মুসলমান, শিয়াদের তিনি পছন্দ করতেন না। এটা বিস্ময়কর যে রাজপুত মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেও ফিরােজ শাহ অমুসলমানদের প্রতি তেমন উদারতা দেখাতে পারেননি। অন্য ধর্মাবলম্বীদের তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে উৎসাহিত করতেন। তবে তাদের ওপর তিনি অত্যাচার করেননি। তিনি হিন্দুদের উপর পুনরায় জিজিয়া কর আরােপ করেছিলেন।
জনগণের দুর্দশা দূর করার উদ্দেশ্যে তিনি মুহাম্মদ বিন তুঘলক কর্তৃক প্রজাদেরকে প্রদত্ত ঋণের টাকা মওকুফ করে দেন। পূর্ববর্তী সুলতানের আমলে ক্ষতিগ্রস্থ জনগণকে তিনি ক্ষতিপূরণ দান করেন।
সুলতান আলাউদ্দিন খলজীর সময় জায়গীর প্রথা রদ করা হয়েছিল। সুলতান ফিরােজ শাহ তা আবার প্রবর্তন করেন। আমীর ও কর্মকর্তাদের মনােতুষ্টির উদ্দেশ্যেই এটা করা হয়। সমস্ত সাম্রাজ্যকে জায়গীরে বিভক্ত করে কর্মকর্তা ও আমীরদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এ ব্যবস্থার ফলে সুলতানের কর্তৃত্ব সাময়িকভাবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও শেষ পর্যড় এটা সাম্রাজ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়েছিল।
সুলতান প্রজাদের কল্যাণের জন্য বেশ কিছু প্রশংসনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। কৃষির উন্নতিকল্পে তিনি বহু কর রহিত করেন। শামস-ই-সিরাজ আফিফের মতে সুলতান ২৩ ধরনের অবৈধ কর রহিত করেছিলেন এবং শরিয়তের বিধান অনুযায়ী ‘খারাজ’ বা ভুমি রাজস্ব (জমির ফসলের এক-দশমাংশ), ‘যাকাত’ বা গরীবদের সাহায্যার্থে সরকারি তহবিলে দান (২১/১%), ‘জিজিয়া’ বা অমুসলমানদের ওপর ধার্যকৃত কর ও ‘খামস’ বা খনিজ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ কর আরােপ করেছিলেন। এ ছাড়া সেচকর এবং যুদ্ধে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির এক-পঞ্চমাংশ প্রভৃতিও ছিল রাজ্যের আয়ের উৎস। পূর্বের বহু অবৈধ কর থেকে তিনি প্রজাদের মুক্তি দিয়েছিলেন। সুলতানের এসব ব্যবস্থার ফলে রায়ত ও চাষীদের অবস্থার উন্নতি ঘটে, নিত্যপ্রয়ােজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমে যায় এবং দেশে কখনাে অভাব দেখা যায় নি।
অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতির উদ্দেশ্যে সুলতান ফিরােজ শাহ তুঘলক আন্ত:প্রাদেশিক শুল্ক উঠিয়ে দেন। ফলে সাম্রাজ্যের সর্বত্র অবাধ বাণিজ্য পরিচালনায় সুবিধা হয়, শিল্প ও বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। তিনি মুদ্রানীতির সংস্কার করে এটাকে বিজ্ঞানসম্মত করেন। তিনি ‘আধা’ ও ‘বিখ’ নামে দুটি মুদ্রার প্রচলন করেন।
ফিরােজ শাহ তুঘলক বহু সেচ-খাল খনন করিয়েছিলেন যার ফলে কৃষির উন্নতি ঘটে ও বহু পতিত জমি আবাদ হয়। এগুলাের মধ্যে যমুনা খাল এখনও বিদ্যমান। তাঁর এসব ব্যবস্থার সুফল বর্ণনা করে আফিফ লিখেছেন যে প্রজাদের ঘর খাদ্য-শস্য, ধন-রত্ন, ঘােড়া এবং আসবাবপত্রে পূর্ণ ছিল। সবারই ছিল প্রচুর সােনা-রূপা। জনগণ সুখে-স্বাচ্ছন্দে জীবনযাপন করতাে।
নির্মাতা হিসাবেও ফিরােজ শাহ তুঘলক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি বহু শহর ও বাগান নির্মাণ করেছিলেন। জৌনপুর, ফতেহাবাদ, হিসার, বাদাউনের কাছে ফিরােজপুর ও দিল্লির কাছে ফিরােজাবাদ ইত্যাদি শহরগুলাে তিনি নির্মাণ করেছিলেন। তিনি বহু মাদ্রাসা, মসজিদ, প্রাসাদ, সরাইখানা, হাসপাতালও নির্মাণ করেছিলেন। আফিফের মতে ফিরােজ শাহ নয়টি প্রাসাদ ও সাতটি বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন। আলাউদ্দিন খলজীর নির্মিত ত্রিশটি বাগান তিনি সংস্কার করেছিলেন এবং নিজে ১২০০ নতুন বাগান তৈরি করেছিলেন। এসব বাগান থেকে খরচ বাদ দিয়ে রাজকোষে বছরে ১,৮০,০০০ তঙ্কা আয় হতাে। অশােকের নির্মিত দুটি স্তম্ভ সুলতান ফিরােজ শাহ দিল্লিতে নিয়ে আসেন এবং এগুলাের পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেন। এগুলাের একটি মীরাট ও অন্যটি খিজিরাবাদ থেকে তিনি নিয়ে এসেছিলেন।
সংস্কারমূলক কার্যাবলী
ফিরােজ শাহ বিচার ব্যবস্থারও সংস্কার সাধন করেন। পূর্ববর্তী আমলের অনেক নিষ্ঠুর প্রথা তিনি রহিত করেন। বিচারের ব্যাপারে সুলতান কোরআনের অনুশাসন মেনে চলতেন, মুফতি আইনের ব্যাখ্যা করতেন এবং কাজি শাস্তির হুকুম দিতেন। আগে শাস্তি হিসাবে অপরাধীর অঙ্গচ্ছেদ করা হতাে যা তিনি রহিত করে শাস্তির কঠোরতা হ্রাস করেন।
বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি একটি কর্মসংস্থান সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। কোতােয়াল বেকারদের তালিকা তৈরি করে পাঠাতেন এবং তাদের যােগ্যতা ও কর্মদক্ষতা অনুযায়ী তাদের চাকুরি বা জীবিকার ব্যবস্থা করা হতাে। সুলতান নিজে চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং জনসাধারণের উপকারার্থে দিল্লিতে বেএকটি দার-উশ-শিফা বা হাসপাতাল নির্মাণ করেন। সেখানে দেশ-বিদেশের দক্ষ চিকিৎসকদেরকে নিযুক্ত করা হতাে এবং রােগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করা এবং ওষুধ সরবরাহ করা হতাে।
দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য তিনি দিওয়ান-ই-খয়রাত বা সাহায্য ভান্ডার স্থাপন করেন। এখান থেকে বিশেষ করে মুসলমান বিধবাদের সাহায্য করা হতাে ও বিবাহযােগ্যা দরিদ্র মুসলমান মেয়েদের বিয়ের জন্য অর্থ সাহায্য করা হতাে। ফিরােজ শাহ তুঘলক সামরিক বিভাগেরও সংস্কার সাধন করেন। তিনি সামন্ত প্রথার ভিত্তিতে সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। সেনাধ্যক্ষদের জায়গীর দেওয়া হয়। যে সব সৈন্যকে জায়গীর দেওয়া হতােনা তাদেরকে কোষাগার থেকে নগদ অর্থে বেতন দেওয়া হতাে। সৈন্যরা নিজেদের ঘােড়া জোগাড় করতাে এবং এগুলাে আরিজ-ই-মমালিকের দফতরে তালিকাভুক্ত করা হতাে। সৈন্য বাহিনীর তত্ত্বাবধান ও দুর্নীতি দমন করা ছিল আরিজ-ই-মমালিকের দায়িত্ব। কিন্তু সুলতানের মহানুভবতা ও দয়ার ফলে সৈন্যবাহিনীতে দুর্নীতি প্রবেশ করে এবং সৈন্যবাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে। সৈন্যবাহিনীতে বৃদ্ধ ও অক্ষম সৈন্যদেরও ভর্তি করা হতাে। তাছাড়া দয়াপরবশ হয়ে সুলতান নিয়ম করেন যে কোনাে সৈন্য বৃদ্ধ হয়ে গেলে বা অক্ষম হয়ে পড়লে তার। স্থলে তার পুত্র, জামাতা বা ক্রীতদাসকে সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করা হবে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই সৈন্যবাহিনীর দক্ষতা নষ্ট হয়ে যায়।
ফিরােজ শাহের রাজত্বকালে দিল্লিতে ক্রীতদাসদের সংখ্যা খুব বেড়ে যায়। শামস-ই-সিরাজ আফিফের মতে দেশে মােট ১৮০০০ ক্রীতদাস ছিল। আমীরগণ রাজস্বের পরিবর্তে বা অন্য কোনাে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য উপহার হিসাবে সুলতানকে ক্রীতদাস পাঠাতেন। দাসদের প্রতি লক্ষ রাখার জন্য সুলতান একটি নতুন দপ্তর খুলেছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন যে ক্রীতদাসদের মাধ্যমে তিনি তার নিজের ও তার উত্তরাধিকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। ক্রীতদাসদের ভরণ-পােষণের জন্য রাজকোষ থেকে প্রচুর অর্থ খরচ করতে হতাে, অন্যদিকে রাজস্বের পরিমাণও হ্রাস প্রায়।
ফিরােজ শাহ তুঘলক, মুহাম্মদ বিন তুঘলকের মত অত বড় পন্ডিত না হলেও তিনি জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির সমাদর করতেন। তিনি সুফি-দরবেশ ও অন্যান্য পন্ডিত ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপােষকতা করেছিলেন। তিনি বহু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেশ-বিদেশের জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে ঐ সব মাদ্রাসায় নিয়ােগ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দিল্লির ফিরােজিয়া মাদ্রাসা তখনকার একটি বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে খ্যাতি অর্জন করেছিল। নগরকোট থেকে নিয়ে আসা ৩০০ সংস্কৃত গ্রন্থ তার আদেশে ফার্সিতে অনুবাদ করা হয়েছিল। তাঁর সময়ে এবং তারই পৃষ্ঠপােষকতায় জিয়াউদ্দিন বারাণীর ‘তারিখ-ই-ফিরােজশাহী’ ও শামস-ই-সিরাজ আফিফের ‘তারিখ-ই-ফিরােজশাহী’ নামের দুটি বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। অনেক পন্ডিত মনে করেন যে, তিনি ‘ফুতুহাত-ই-ফিরােজশাহী’ ও ‘সিরাত-ই-ফিরােজশাহী’ গ্রন্থ দুটি রচনা করেছিলেন। শামস-ই-সিরাজ আফিফের মতে সুলতান পন্ডিত ব্যক্তিদের ভাতা হিসাবে বছরে ৩৬ লক্ষ তঙ্কা ব্যয় করতেন।
তুঘলক বংশের পতনে তাঁর দায়িত্ব
রাষ্ট্র নায়ক হিসেবে ফিরােজ শাহ তুঘলক ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং তুঘলক বংশের পতনের জন্য তিনি বহুলাংশে দায়ী ছিলেন। প্রথমত, তিনি সাম্রাজ্যের হৃত প্রদেশগুলাে উদ্ধার করার কোনাে চেষ্টা করেননি। ফলে ক্রমেই সাম্রাজ্য সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং দূরবর্তী প্রদেশগুলােতেও কেন্দ্রের কর্তৃত্ব ধীরে ধীরে কমে আসে। দ্বিতীয়ত, জায়গীর প্রথার পুন:প্রবর্তন আমীর ও কর্মচারীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। বংশগতভাবে সৈন্য নিয়ােগের ফলে একদিকে যেমন সৈন্যবাহিনীর দক্ষতা হ্রাস পায় তেমনি বংশগতভাবে কর্মচারী নিয়ােগের ফলে কেন্দ্রীয় শক্তির অবনতির সুযােগে প্রাদেশিক কর্মচারীরা স্বাধীন হয়ে পড়ে। তৃতীয়ত, বিশাল ক্রীতদাস বাহিনীর ভরণপােষণ রাজকোষকে ক্রমশ শূন্য করে ফেলে এবং রাজ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে প্রজাদের স্বার্থে ও তাদের উন্নতি কল্পেই ফিরােজ শাহ এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু জনহিতকর এসব কাজই তাঁর বংশের ও সালতানাতের পতনকে তরান্বিত করেছিল। ড. রমেশচন্দ্র মুজুমদার বলেছেন যে ফিরােজ শাহের দীর্ঘ রাজত্বকালে দেশে শান্তি, সমৃদ্ধি ও পরিতৃপ্ত অবস্থা বিরাজ করলেও তাঁর নীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাবলী যে বহুল পরিমাণে দিল্লি সালতানাতের পতনের সহায়ক হয়েছিল সে সম্পর্কে কোনাে সন্দেহ নেই। নেপােলিয়ন বােনােপার্ট বলেছিলেন যে, প্রজারা যখন রাজাকে একজন দয়ালু ব্যক্তিরূপে অভিহিত করে তখন বুঝতে হবে যে তাঁর রাজত্বকাল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। ফিরােজ শাহ তুঘলক সম্পর্কে নেপােলিয়নের এ উক্তিটি যথাযথভাবে প্রযােজ্য।
সমসাময়িক ঐতিহাসিকরা ফিরােজ শাহের উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন। তাঁদের মূল্যায়ণ ফিরােজ শাহের চারিত্রিক গুণাবলী ও তার শাসনপদ্ধতি সম্পর্কে অতিশয়ােক্তি রয়েছে সন্দেহ নেই। বারাণী ও আফিফ সুলতানকে ন্যায়পরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, দয়ালু প্রভৃতি গুণের আধাররূপে বারাণীর মতে মুহাম্মদ ঘােরীর মৃত্যুর পর এরকম বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতাে বিনয়ী, দয়ালু, সত্যবাদী, বিশ্বাসী ও ধার্মিক সুলতান আর দিল্লির সিংহাসনে বসেন নি। তবে ঐতিহাসিকদের অতিশয়ােক্তি বাদ দিলেও ফিরােজ শাহ যে একজন প্রজাহিতৈষী, ধর্মভীরু ও দয়ালু সুলতান ছিলেন তা অস্বীকার করা যায় না। দীর্ঘ ৩৭ বছর রাজত্ব করার পর ফিরােজ শাহ তুঘলক ১৩৮৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।
পরিশেষে বলা যায় দীর্ঘ ৩৭ বৎসর ব্যাপী রাজত্বকালে ফিরােজ শাহ তুঘলক সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃক্মখলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। তিনি দুবার বাংলা আক্রমণ করেও স্বাধীন হয়ে যাওয়া প্রদেশটিকে দিল্লির অধীনে ফিরিয়ে আনতে পারেননি। অন্যান্য সামরিক অভিযানেও তিনি তেমন সাফল্য অর্জন করেননি। তাঁর রাজত্বকাল বিভিন্ন সংস্কারমূলক কাজের জন্য খ্যাতি অর্জন করে। জনকল্যাণে তিনি বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে ইতিহাসে প্রজাহিতৈষী শাসক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। তাঁর সামরিক ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ও অন্যান্য অনেক পদক্ষেপই প্রত্যক্ষ ও পরােক্ষভাবে তুঘলক বংশের শাসনের পতনে সাহায্য করেছিল বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন।
‘নবজাগরণ’ অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপ্লিকেশনটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।
![]()
‘নবজাগরণ’ এর টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।
‘নবজাগরণ’ এর ফেসবুক পেজে লাইক করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

 নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা
নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা