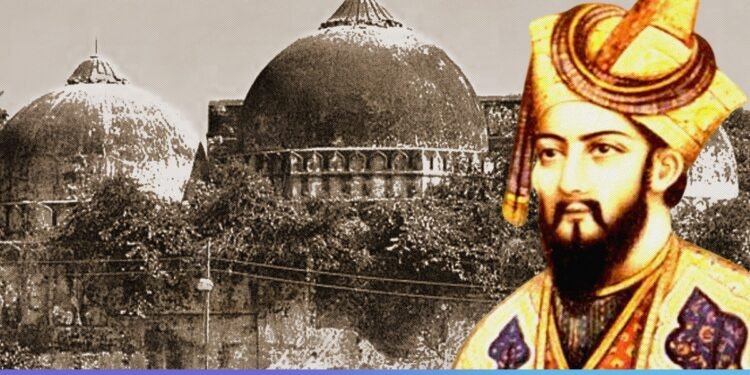বাবরি মসজিদ বিতর্ক নিয়ে দীর্ঘ কয়েক বছর মামলা চলার পর এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চের রায় বের হয়েছিল ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১০। এই রায় সন্তুষ্ট করতে পারেনি। ভারতীয় জনতার কোনও অংশকেই। পৌনে তিন একর জমি নিয়ে মামলা। এলাহাবাদ কোর্ট রায় দিয়েছিল তিনভাগ করে দাও। দুইভাগ হিন্দুদের এবং একভাগ মুসলিমদের। আমরা তাে জানি জমি ভাগ বাটোয়ারা হয়ে যাওয়া মানেই বিতর্ক ও দ্বন্দ্বের ইতি। কিন্তু হল কই। বাবরি মসজিদ কি রামমন্দির ভেঙে তৈরি করা হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর ভারতীয় জনতা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুঁজে পায়নি। সেদিন অন্যতম বিচারপতি ডি ভি শর্মা জানিয়েছিলেন, বাবরি মসজিদ ই রামচন্দ্রের জন্মস্থান। কিসের ভিত্তিতে বিচারপতি এমন বক্তব্য রেখেছিলেন তা আমাদের অজানা। বিচারপতির এমন বক্তব্যের পেছনে কি কোনও নৃতাত্বিক বা ঐতিহাসিক গবেষণার সমর্থন ছিল? কিংবা ছিল প্রত্নতাত্বিক গবেষণার সমর্থন? পুরােটাই অনুমান, বিশ্বাস আর ভাবাবেগের ফসল। বিচারপতি সুধীর আগরওয়াল যেমন বলেছিলেন, ‘দ্য ফেথ অ্যাণ্ড বিলিফ অফ হিন্দুস ইজ দ্যাট লর্ড রাম ওয়াজ বর্ন অ্যাট দিস সাইট।’ হ্যাঁ, সেদিন এটাই ছিল এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের ভিত্তি। এই সমস্ত কিছুরই নির্মোহ জবাব নির্ভর করছিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারের ওপর। অবশ্য সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যে তার রায়ে (৯ মে ২০১১) এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়কে ‘অদ্ভুত’ আখ্যা দিয়ে বিতর্কিত ভুখণ্ডটিতে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ জারি করেছিল। তাই এই সংকটকালে আধুনিক গণতান্ত্রিক-ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের বিচারব্যবস্থার প্রাজ্ঞতা নির্ভর করছিল সুপ্রিম কোর্টের সুবিবেচনার ওপর। কিন্তু রামমন্দির নির্মাণের পক্ষে রায় দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সেই সুবিবেচনা আজ গেল কোথায়? তারাও তাে দেশের সাম্প্রদায়িক শক্তির কাছে বিকিয়ে গেল। এই রায়ের পেছনে কোনও প্রত্নতাত্বিক বা নৃতাত্বিক গবেষণা বা ইতিহাসের সমর্থন খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।
স্বভাবতই এই রায় বহু ধর্ম, জাতপাত ও অঞ্চল বিভক্ত ভারতে এক বিপজ্জনক নজির স্থাপন করেছে। অর্থাৎ আইন, নৈতিকতা, সংবিধান এবং মানবিক মূল্যবােধ উপেক্ষা করে যদি অপেক্ষাকৃত দুর্বল সম্প্রদায়ের কোনােকিছু জোরপূর্বক দখল করা যায়, সেক্ষেত্রে বিচার বিভাগ সংখ্যাগুরু ও সবলের পক্ষে তাদের বিশ্বাসের অযুহাত দিয়ে ওই অন্যায়কে মান্যতা দিতে পারে! এই ধরনের পরিস্থিতি দেশে অশান্তি ও সন্ত্রাস সৃষ্টির উপাদান হিসেবে যে কাজ করতে পারে, তা বলার জন্য সমাজবিজ্ঞানী হবার দরকার পড়ে না। পাশাপাশি এই রায় কুঠারঘাত করল দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইতিহাস চেতনার উপরও। ইতিহাস আর পুরাণে তফাৎ থাকল কই। বিশ্বাস অনুসারে যদি রামচন্দ্রকে মেনেও নেওয়া যায়, কিন্তু কোন স্থানে তার জন্ম সে সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা যায় কি? বিশ্বাসের বস্তুর আবার জন্মস্থানের বাস্তব অস্তিত্ব থাকে নাকি? স্বভাবতই সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের এহেন রায় ভারতীয় বিচারব্যবস্থার অবক্ষয়কেই প্রকটিত করে।
একথা এখনও ভুলে যায়নি কেউ যে, এই সুপ্রিম কোর্টই এই বিশ্বাসবাদের ভিত্তিতে রায় দান তাে দূরস্থান তার বিচারই চলে না বলে রায় দিয়েছিল ১৯৯৩-৯৪ সালে। যখন ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ভাঙার পর তৎকালীন নরসিমা রাও-এর কংগ্রেস সরকার রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে মত জানতে চেয়েছিলেন যে, কোনও হিন্দু মন্দির ভেঙে বাবরি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল কিনা? সুপ্রিম কোর্টের তাতে স্পষ্ট ঘােষণা ছিল: ‘কোনও পৌরাণিক বিষয়ে বিচার করা তার এক্তিয়ারে পড়ে না। তারপরও যদি সুপ্রিম কোর্ট সেই ‘রামলালা বিরাজমান’ তত্ত্বের ভিত্তিতে রায় দেন সেটি কি সর্বোচ্চ আদালতের বিরুদ্ধে বা তার লংঘন নয়? বিচারব্যবস্থাকে হাইজ্যাক করার এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কি হতে পারে? তাছাড়া আমাদের দেশের সংবিধানে বিজ্ঞানকে ভিত্তি করার পক্ষে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে ৫১ নং ধারায়। যেখানে বলা হয়েছে: বিজ্ঞানমনস্কতা ও তার প্রসারে দেশের সকল নাগরিক ও সংস্থাকে সংবিধান নির্দেশ দিচ্ছে। তেমন অবস্থায় কোনও কোর্ট যদি বিশ্বাসবাদ বা পৌরাণিক ধারণার ভিত্তিতে রায় দেন তবে তা কি সংবিধান লংঘন নয়? ‘রামলালা বিরাজমান’ বিশ্বাসের ভিত্তিতে রায় দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট কি সেই কাজটিই করেননি?
(২)
১৯৮৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি বাবরি মসজিদ এর তালা খুলে দেবার পর যখন বিতর্ক চরমে ওঠে তখন ভারতীয় প্রত্নতাত্বিক বিভাগ অযােধ্যায় একটি সর্বেক্ষণ চালান ১৯৮৮ সালে। তাতে ২০০০ খ্রিস্টপূর্বের আগে অযােধ্যায় কোনও বসবাসের অস্তিত্ব তারা খুঁজে পাননি। যে স্থানে বাবরি মসজিদ ছিল, তার এবং আশেপাশের স্থানে একাদশ ও পঞ্চদশ শতকের মধ্যে কোনাে জনবসতি ছিল এমন প্রমাণ কোনাে ঐতিহাসিকও দিতে পারেননি। অতএব যেখানে কোনাে জনবসতি ছিল না সেখানে বাবরি মসজিদ তৈরী হওয়ার প্রায় সওয়া ৩০০ বছর পর অর্থাৎ ১৮৫৫ সালে কোন্ ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে হিন্দুত্ববাদীরা ঐ জায়গাটা রামের জন্মভূমি হিসেবে দাবী করেন? অর্থাৎ মুঘল সম্রাট বাবরের আগে ভারতে রামমন্দির ছিলই না তাে মন্দির ভাঙবে কে? তাছাড়া বাবর ১৫২৬ সালে দিল্লি দখল করেই ১৫২৮ সালে প্রথমেই দিল্লিতে মন্দির না ভেঙে কেন অযােধ্যায় গিয়ে মন্দির ভাঙেন তারও তাে একটা জবাব চাই? প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ রামশরণ শর্মা দেখিয়েছেন, ১৬ শতকের আগে এদেশে রামমন্দির বা রাম পূজার প্রচলন ছিল না। ১৬ শতকে তুলসীদাস (১৫৩২-১৬২৩) হিন্দি রামায়ণ ‘রামচরিতমানস’ রচনা করেন সরযূ নদীর তীরে বসে। মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরী করা হলে নিশ্চয়ই তিনি তা শুনতে পেতেন, তা উল্লেখও করতেন। কিন্তু ‘রামচরিতমানস’-এর কোথাও সেকথার উল্লেখ নেই। ‘রামচরিতমানস’ রচিত হওয়ার পর থেকে দেশে শুরু হয় রামপূজা। ১৫৯৫-৯৬ সালে আবুল ফজল তার ‘আইন-ই-অযােধ্যা’ গ্রন্থে অযােধ্যায় রামের বাসস্থান ছিল বলেছেন, রামের জন্মভূমি বলেননি। উল্লেখ্যযােগ্য যে, অযােধ্যাতে যে দুজন ইহুদি নবীর কবর রয়েছে সে সম্পর্কেও তিনি বলেছেন। রামের জন্মভূমিতে মসজিদ করা হয়েছে, এরকম কোনও ইঙ্গিত এর মধ্যে নেই। ১৬০৮ থেকে ১৬১১ সালের মধ্যে উইলিয়াম ফিঞ্চ অযােধ্যাতে এসেছিলেন। উনি বলেছেন যে, এখানে রামের দূর্গ ও বাড়ি আছে। উনি রামকোট (দূর্গ) ও স্বর্গদ্বারের কথা বলেছেন, কিন্তু রামের জন্মের কোনও কথা বা মন্দিরের কথা বলেননি। ১৬৯৫-৯৬ সালে সুজন রায় ভান্ডারী তাঁর বই (খুলসাৎ-ই-তওয়ারিখ) সমাপ্ত করেন, যার মধ্যে ভারতের তীর্থক্ষেত্রগুলাের ভৌগােলিক বিবরণ আছে। অযােধ্যা যে রামচন্দ্রের বাসস্থানের জন্য পুণ্যতীর্থ সে কথাও বলেছেন। ইহুদিদের কবরের কথাও বলেছেন। কিন্তু এরমধ্যে রামজন্মভূমি বা রামমন্দিরের কোনও কথা নেই। ১৭৫০-৬০ সালে রাইচতুরাম তাঁর বই (‘চাজার গুলশান’) শেষ করেন, যার মধ্যে ভারতের ভৌগােলিক বর্ণনা রয়েছে। যদুনাথ সরকার এর কিছু অংশ অনুবাদ করেছিলেন। এতে অযােধ্যাকে রাজা দশরথের ছেলে রামচন্দ্রের জন্মস্থান বলে ধরা হয়েছে। কিন্তু রামের জন্মস্থান বা রামমন্দির নিয়ে নিশ্চিত করে কোনও কথা বলা নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বাবরি মসজিদ তৈরী (সম্ভবত ১৫২৮-২৯ সালে বাবরের সেনাপতি মীর বাকি বাবরি মসজিদ তৈরী করেন, তৈরী করার পর এতে একটি শিলালেখ লাগানাে হয়, যার থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়) হবার ২০০ বছরের মধ্যে কোনও ইঙ্গিত সমকালীন লেখার মধ্যে নেই যে, ঠিক কোথায় রামচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল এবং মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ তৈরী করা হয়েছিল এ রকম কোনও ইঙ্গিতও নেই। এ পর্যন্ত হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান কারও লেখাতেই এটা পাওয়া যায় না।
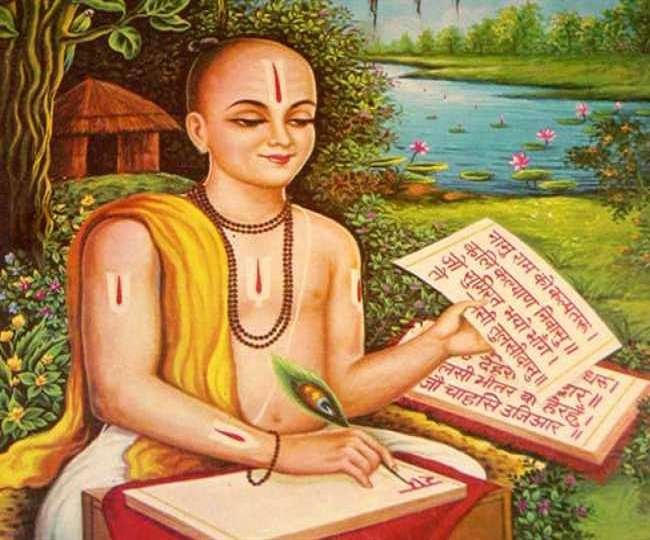
১৭৮৯ সালে জার্মান জেসুইট পাদ্রী জোসেফ টিফেন থালারের বই পন্ডিত জে. বারনুলি ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করে বার্লিন শহর থেকে প্রকাশ করেন (Description historique et geographic de l’Inde). এই দুর্গেও রামদুর্গের কথা বলা হয়েছে কিন্তু রামমন্দিরের কোনও উল্লেখ নেই। মসজিদ তৈরী হবার প্রায় ২৫০ বছর পরেও স্থানীয় লােকের মনে বিশ্বাস ছিল না যে, ওখানে একটা রামমন্দির ছিল। এরও ২০ বছর পর এই বিশ্বাস জন্মাতে থাকে। ১৮১০ সালে ফ্রান্সিস বুকানন অযােধ্যায় এসে মন্দির ভাঙার কথা শােনেন। অবশ্য বুকাননের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট নয় যে, তিনি মন্দির ভেঙে বাবরি মসজিদ তৈরী করা হয়েছিল, এটা বলছেন।
স্থাপত্য এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে বাবরের ধ্যান-ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় ‘বাবরনামা’ গ্রন্থ থেকে। ১৫৮৯ খ্রিস্টাব্দে আকবরের রাজত্বকালে ‘বাবরনামা’র একটি ফরাসি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। সেই গ্রন্থে অবশ্য মসজিদের কোনও উল্লেখ নেই। তবে একথা সত্য, দীর্ঘদিন ধরেই বাবরি মসজিদ এর সঙ্গে এদেশের মুসলমানদের একটা অন্তরের যােগ ছিল। মসজিদটি ভারতীয় মুসলমানদের উপাসনা সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই দেখতে হবে এই মসজিদটি সম্পর্কে অন্য আর কোনও তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা।
এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করতে হয়, শিখ গুরু নানকের (১৪৬৯-১৫৩৯) কথা। বাবর যে সময় ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, নানক তখন জীবিত। বাবর যে লুণ্ঠন, যে অত্যাচার চালিয়েছিলেন, নানক তার প্রত্যক্ষদর্শী। একা নানক নন, তার সর্বক্ষণের সঙ্গী মারদানাও প্রত্যক্ষ করেছেন তা নানক তার বিভিন্ন রচনায়, গানে বাবরের এই অত্যাচারের কথা উল্লেখ করেছেন। শিখ ধর্মগ্রন্থ ‘গ্রন্থসাহিব’-এ নানকের ওই সব গান ও রচনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মানুষের ওপর বাবরের ওই অত্যাচারের প্রতিবাদ করার ফলেই নানক এবং মারদানা বাবরের সেনাদের হাতে বন্দি হন। কিন্তু বন্দি নানকের চোখমুখের ভাব দেখে অবাক তুর্কি সেনারা তাঁকে বাবরের সামনে হাজির করলে তিনি অবাক হন। মুগ্ধ বাবর বলে ওঠেন—‘ওই ফকিরের চোখেমুখে আমি যেন ঈশ্বরকে দেখলাম।’ মুগ্ধ সম্রাট জিজ্ঞাসা করেন, হে ফকির আমি তােমার জন্য কি করতে পারি। নানক বলেন, এই যে সমস্ত সাধারণ মানুষকে আপনি বন্দি করেছেন তাদের মুক্তি দিন। তারা মুক্ত হলেই আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হব। নানকের কথায় বাবর সেদিন সব বন্দিকে মুক্তি দিয়েছিলেন। অবশ্যই নানক এবং মারদানাকেও।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে নানক অযােধ্যায় যান। বাবরি মসজিদও দেখেন। তিনি কিন্তু মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়ার কোনও উল্লেখ কোথাও করেননি। যে নানক বাবরের অত্যাচারে প্রতিবাদ করে বন্দি পর্যন্ত হয়েছিলেন, তিনি মন্দির ভেঙে মসজিদ হলে নিশ্চয়ই তার উল্লেখ করতেন, প্রতিবাদ করতেন। বাবর একবার ভ্রমণে গিয়ে একটা জৈন মূর্তি ভেঙেছিলেন, এ কথাও ‘বাবরনামা’তে উল্লেখ রয়েছে। সত্যিই বাবর যদি মন্দির ধ্বংস করতেন নিশ্চয়ই তার ‘বাবরনামা’তে তা উল্লেখ করতেন।
মুঘল বংশের শাসকগণ হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি স্থাপনের নিমিত্ত এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে নতুন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। বাবরই প্রকৃতপক্ষে তার সূচনাকারী। বাবর অমুসলমানদের প্রতি যে কতখানি সহনশীল মনােভাব পােষণ করতেন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর রচিত একটি গােপন ‘শেষ ইচ্ছাপত্র’ বা ‘অসিয়তনামা’য়, যেটি তিনি তাঁর পুত্র হুমায়ুনের জন্য রেখে গিয়েছিলেন। পুত্র হুমায়ুনের প্রতি বাবরের উপদেশ—‘শেষ ইচ্ছাপত্র’ সংক্রান্ত দলিলটি ভূপালের রাজ্য গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। ‘দ্য ইন্ডিয়ান রিভিউ’-এ দলিলটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়, অনুবাদক সৈয়দ মাহমুদ। বাংলা অনুবাদে সেটি দাঁড়ায়, “হে আমার পুত্র, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ ভারতবর্ষে বাস করে; রাজার রাজা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এই দেশের শাসনভার তােমার হাতে ন্যস্ত করেছেন। সুতরাং তােমার কর্তব্য হল :
১. তােমার মনকে ধর্মীয় সংস্কার দ্বারা প্রভাবিত হতে দেবে না এবং সকল শ্রেণির মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি ও ধর্মীয় আচারাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে সকলের প্রতি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করবে;
২. বিশেষ করে গােহত্যা থেকে বিরত থাক, এর ফলে ভারতের জনগণের হৃদয়ে তুমি স্থান করে নিতে পারবে। এর দ্বারা তােমার সঙ্গে এদেশের মানুষ কৃতজ্ঞতা রজ্জতে আবদ্ধ হবে;
৩. তুমি কখনও কোনও সম্প্রদায়ের উপাসনালয় ধ্বংস করবে না এবং সবসময় ন্যায়বিচারের প্রতি অনুরক্ত থাকবে, যাতে রাজার সঙ্গে প্রজাদের সুসম্পর্ক বজায় থাকে এবং এই ভূখণ্ডে শান্তি ও সন্তুষ্টি বিরাজ করে।
৪. অত্যাচারের তরবারির চেয়ে ভালবাসা ও কর্তব্যপরাণয়তার তরবারি দিয়ে ইসলাম প্রচার অধিক সাফল্য অর্জন করবে।
৫. শিয়া ও সুন্নিদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ সবসময় উপেক্ষা করে চলবে, তা না হলে এগুলাে ইসলামকে দুর্বল করে দেবে।
৬. তােমাদের প্রজাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে বছরের বিভিন্ন ঋতুর বৈচিত্র্যের সঙ্গে তুলনা করবে, তাহলে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকবে।”১
বাবরের এই উপদেশ বা ‘শেষ ইচ্ছাপত্র’-তে আমরা একজন ধর্মনিরপেক্ষ ও দুরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রশাসককে দেখতে পাই। সাম্প্রতিককালে ভারতের অযােধ্যায় রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ নিয়ে যে বিতর্কের ঝড় সমগ্র ভারতের রাজনীতিতে অশুভ প্রভাব বিস্তার করেছে এবং এর ফলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক হিংসাত্মক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে সম্রাট বাবরের ঐ নির্দেশনামা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিচার করা প্রয়ােজন। মৌলবাদী হিন্দুদের বিশ্বাস যে, যে স্থানটিতে বাবরি মসজিদ অবস্থিত সেটি ছিল রামের জন্মস্থান এবং পূর্বে ওখানে একটি মন্দির ছিল। তাদের ধারণা যে, সম্রাট বাবরের নির্দেশে কিংবা তার সময়কালে ওই মন্দিরটি ভেঙে ফেলা হয় এবং ওখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়, সেটিই হল বাবরি মসজিদ । যেহেতু রাম হলেন ঈশ্বরের অবতার, তার জন্মস্থানে যে মন্দিরটি ছিল সেটা যদি পুনঃনির্মাণ করা যায় মসজিদটি ভেঙে দিয়ে, তাহলে একটা বিরাট পুণ্যের কাজ হবে। বিশ্বহিন্দু পরিষদ এই আন্দোলনের প্রবক্তা। কিন্তু হিন্দু মৌলবাদীদের এই দাবি ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পরিপন্থী। প্রথমত, রাম কোনও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব নন; দ্বিতীয়ত, হুমায়ুনের প্রতি বাবরের নির্দেশনামা যেটি একটি ঐতিহাসিক দলিল, সেটিতে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, বাবর মােটেই হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন না। তিনি সকল ধর্মের প্রতি সহনশীল মনােভাব পােষণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। বস্তুত ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আনুমানিক চোদ্দ শতক থেকে এই উপমহাদেশের ধর্ম ও সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে বিদ্যমান রক্ষণশীলতার পাশে এক আধ্যাত্মিক মানবতাবাদী ও সমন্বয়ধর্মী এবং পরমতসহিষ্ণুতার ধারার উন্মেষ ঘটেছিল, সেটা আঠার শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের প্রথমদিক পর্যন্ত এই মহাদেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় প্রতিফলিত হয়।
শাসকরা কেমন হবেন, এই বিষয়েও বাবরের একটি স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তিনি ‘ভাল’ ও ‘ন্যায়পরায়ণ’ শাসকদের প্রশংসা করতেন এবং ‘অত্যাচারী’ শাসকদের অপছন্দ করতেন। এই কারণে তিনি কয়েকজন মুসলমান শাসকের নিষ্ঠুরতা ও অপশাসন তীব্র ভাষায় নিন্দা করেন। কিন্তু বাবর নিজেও সমালােচনার উর্ধ্বে ছিলেন না। অবশ্য শাসক হিসেবে তার বর্বর আচরণের দৃষ্টান্ত শুধু বিরলই ছিল না, তার প্রকাশ সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই ঘটেছে। প্রতিপক্ষরা যাতে বাবরের কোনও ক্ষতি করতে না পারে তার জন্যে তাদের মনে বাবর ভীতি সঞ্চার করতেন। কিন্তু যারা বাবরের বিরােধিতা না করে আত্মসমর্পণ করত, তাদের সঙ্গে তিনি সহৃদয় আচরণ করতেন। এমনকি পরাজিত আফগানদের প্রতিও তিনি দয়া প্রদর্শন করেন। নীতিগতভাবে বাবর নির্বিচারে হত্যা ও সম্পত্তি ধ্বংসের বিরােধী ছিলেন। নিরীহ মানুষদের সম্পত্তি নষ্ট করার জন্যে বাবর সৈনিকদের শাস্তিও দেন। তাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার অত্যাচারের দৃষ্টান্ত থেকে তার চরিত্রের বিচার করলে ভুল হবে। তুলনায় তার ঔদার্যবােধের ও মানবিক আচরণের উদাহরণ অনেক বেশী পাওয়া যায়। শত্রুদের প্রতি তিনি ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শনও করেন। বাবরের চরিত্রে আত্ম-জাহির করার ভাব ছিল না। নম্রতা তার চরিত্রকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল।
(৩)
অযােধ্যার বিতর্কিত ধর্মস্থানটিই ভগবান রামের জন্মস্থান, বাবর সেটি ভেঙে ১৫২৮ সালে মসজিদ বানিয়েছেন—এই তাে রাম ভক্তদের দাবি। কিন্তু এ নিয়ে মামলা তাে শুরু হয়েছে, ১৮৮৫ সালে প্রথম। তাহলে এই এতদিন ধরে রাম জন্মভূমি কোনও ইস্যু হল না কেন? রামের মতাে ভগবানের জন্মস্থান যদি বেদখল হয়ে গিয়ে থাকে তা ওই ৩৫৭ বছর ধরে যাঁরা বসে বসে দেখলেন তারা তবে কেমন রাম ভক্ত? আসলে, রাম জন্মস্থানটি ততদিন কোনও ইস্যুই ছিল না—একথা বললে কি কোনও বাহুল্য বলা হয়?
১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজ শাসকরা যখন অনেকটা অনিশ্চয়তা বােধ করতে শুরু করেন তারপরেই এই জাতির ঐক্যকে ভাঙতে নানা পরিকল্পনা ও গবেষণার আশ্রয় নেন। তারই এক কৌশল হিসাবে পুরাণের অযােধ্যার সঙ্গে মিলিয়ে ওই বিতর্কিত মসজিদটিকে রাম জন্মভূমি বলে দাবি করিয়ে দীর্ঘস্থায়ী হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে প্ররােচিত করা হয়নি, একথাই বা কে বলতে পারে?
মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়ার তত্ত্ব সরকারিভাবে প্রথম প্রকাশ করেন শ্রীমতি সুষান বেভারিজ, তার “মেমােয়ার্স অফ বাবর’ গ্রন্থে (তিন খণ্ডে প্রকাশিত)। যা ছিল ‘বাবর নামা’র অনুবাদ। শ্রীমতি বেভারিজ একজায়গায় লেখেন, Presumably the order for building the mosque was given during Babar’s stay in Oudh in 934 A.H. (1528 AD), at which time he would be impresed by dignity and sanctity of the ancient Hindu shrine it (at least in part) displaced and like the obedient follower of Muhammad he was in intolerence of another faith, would regard the substution of a temple by a mosque as dutiful and Wozrty’. এই সমস্তটাই তাে শ্রীমতি বেভারিজের কল্পনাপ্রসূত। এই কল্পনাকেই তিনি তত্ত্ব এবং তথ্য রূপে হাজির করতে চেয়েছিলেন। এই রচনা প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালে। যখন ভারতবর্ষ ছিল গণআন্দোলনে উত্তাল। বুঝে নিতে হয় না শ্রীমতি বেভারিজ হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরােধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই অনুমানকে তত্ত্ব হিসেবে উপস্থিত করতে চেয়েছিলেন।
এবার রামায়নের কথায় আসা যাক। ধরে নেওয়া হয় ৬০০০ শ্লোক থেকে এটা হয়েছে। ২৪ হাজার শ্লোক। চারটি পর্যায়ে বেড়েছে। শেষ পর্যায়টি ১১০০ সালে লেখা। মনে করা হয় প্রথম পর্যায়টি লেখা হয়েছিল ২৪০০ বছর আগে। কিন্তু দশরথের অযােধ্যা কোথায় ছিল এ রামায়ন থেকে পাওয়া যায় না। রামায়ণ সম্পূর্ণই মহাকবি বাল্মীকির কপােলকল্পিত মহাকাব্য। এই মহাকাব্যে যে রামের কথা বলা হয়েছে তিনি যদি ঐতিহাসিক চরিত্রও হন, তবুও তার সময়ের অযােধ্যা যে আজকের অযােধ্যা, তার কোনও প্রমাণ নেই। উল্লেখ্য আমাদের পাঠ্য বইতে রয়েছে, ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস শুরু হয়েছিল খ্ৰীষ্ট জন্মের তিন হাজার বছর আগে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে সিন্ধু উপত্যকায়। কিন্তু অয্যোধ্যা মামলার বিচারকেরা রায় দিয়েছেন যে, বর্তমান কলিযুগের আগে, এমনকি দ্বাপর যুগেরও আগে, অর্থাৎ অন্তত ১৭,০০,০০০ বছর আগে ত্রেতাযুগে সরযু নদীর তীরে ভারতীয় সভ্যতার মহান সুচনা হয়েছিল!
বি বি লাল, যিনি এক সময়ে ছিলেন ভারতীয় প্রত্নতাত্বিক বিভাগ-এর ডিরেক্টর জেনারেল এবং সেই সঙ্গে বিশ্বমানের পুরাতত্ত্ববিদ, তিনি পুরাতত্ত্ব বিভাগের উৎখননের ব্যাপক এক কর্মসূচি নিয়েছিলেন। দশ বছর ধরে সে কাজ চলেছিল। জায়গাগুলি ছিল অযােধ্যা, নন্দীগ্রাম, চিত্রকূট, ভরদ্বাজ আশ্রম ইত্যাদি। খােড়াখুঁড়ি করে বিস্তর প্রাচীন দ্রব্যাদি আবিস্কৃত হল সত্য, কিন্তু সবগুলাে বস্তুই বড়জোর খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতকের, তার আগেকার কোনও নিদর্শনই পাওয়া গেল না। সংঘ পরিবারের দাবি হচ্ছে রাম জীবিত ছিলেন অন্তত খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে। কিন্তু পুরাতাত্ত্বিক খননে দেখা গেল যে, অযােধ্যায় লােকবসতির শুরু মহাভারত যুদ্ধেরও অনন্ত শতবর্ষ পরে—অর্থাৎ এই অযােধ্যা যদি রামের জন্মভূনি হয়, তবে তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরবর্তীকালের মানুষ হয়ে যাচ্ছেন। বি বি লাল নিজের মনােভাবটি ব্যক্ত করেছেন খুব খােলামেলা এবং আন্তরিক ভাষায—“রামায়ণের কাহিনী যে এত পরেকার অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতকের হতে পরে, সে তথ্য অনেককেই ব্যথিত করেছিল, এমনকি স্বীকার করা ভাল যে, আমি নিজেও ব্যথিত হয়েছিলাম। কিন্তু নিষ্ঠাবান পুরাতত্ত্ববিদ হিসেবে পথিবীর কাছে নতি স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। গত শতকের আশির দশকের শেষের দিকে এই সব তথ্য যখন বি বি লাল প্রকাশ করলেন, তখন একটি বিশেষ মহল তাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। বি বি লাল তখন একটা জরুরি প্রশ্ন তােলেন। তিনি দেখালেন যে, তখন থেকে পঁয়ষট্টি বছর আগে ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী উপনিষদ ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থের সাক্ষ্য থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, রামচন্দ্রের কাল খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতকের আগেকার হতে পারে না। তারপর তিনি প্রশ্ন করেছেন, ‘But not even a little finger was raised then. Why should be a furore now when archaeology comes out with a similar result?”—পেছনে যে একটা বড় রকমের রাজনীতির খেলা চলছে সরল পুরাতত্ত্ববিদ এ কথাটা জানতেন না বলেই ১৯৮৯ সালে প্রশ্নটা তুলেছিলেন।২ বি পি সিংহ আর একজন পুরাতত্ত্ববিদ। তিনিও রামচন্দ্রে ঐতিহাসিকতত্ত্বে বিশ্বাসী। তিনি বলেছেন, অযােধ্যার লােকবসতির প্রথম পর্যায়টা যদি খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের হয়ে থাকে, তবে রামচন্দ্রের কাল তাে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক হবে, কারণ রামায়ণের বিবরণে রামচন্দ্রের পূর্ব-পুরুষদের যে তালিকা রয়েছে, তাদের জন্য কিছুটা সময় তাে ছেড়ে দিতেই হয়। অপর আর একজন ঐতিহ্যবাদী পুরাতত্ত্ববিদ হলেন আর জি গৌর। তিনি অযােধ্যার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে বি বি লালের বক্তব্য নিঃসংশয়ে মেনে নিয়েছেন। তবে রামায়ণের কাল যে মহাভারতের চাইতে অনেক প্রাচীন, এই ঐতিহ্যগত ধারণার তিনি সমর্থক। তাই তিনি মনে করেন, Gradually the whole episode of Rama along with his geograghical surroundings was transferred from the land of Saptasindhu and transplanted in the region of Ayodhya’ অর্থাৎ মূল ঘটনাটা আদৌ অযােধ্যার নয়ই। আর যদি রামচন্দ্রকে অযােধ্যারই সন্তান বলে মানতে হয়, তবে রামায়নের কাহিনীর আরও বহু ব্যাপার ছাঁটাই করতে হয় এবং মেনে নিতে হয় রামচন্দ্র কৃষ্ণের পরে জন্মেছিলেন।
২৮০০ বছর আগে অযােধ্যার প্রথম উল্লেখ রয়েছে অথর্ব বেদে। কিন্তু সেটাও বলা হয়েছে কল্পনার শহর, দেবতার শহর এবং তা থেকে আলাের ছটা বেরােত। ২৩০০ বছর আগে বৌদ্ধ পালি গ্রন্থে (সংযুক্ত নিকা) অযােধ্যার কথা বলা হয়েছে, তবে তার অবস্থান। গঙ্গা নদীর ওপর, সরযু নদীর ওপরে নয়। পালি গ্রন্থগুলিতে অনেকগুলি নদীর নাম আছে, এমন নয় যে যেকোন নদীকেই গঙ্গা বলা হত। ২৭০০ বছর আগে চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ লিখেছিলেন যে গঙ্গার দেড় কিলােমিটারের মধ্যে অযােধ্যা আছে। তার মতে অযােধ্যার বৌদ্ধ শ্রমণের সংখ্যা তিন হাজার, অ-বৌদ্ধের সংখ্যা খুবই কম। দেড় হাজার বছর আগে ফা-হিয়েন বলেছিলেন, অযােধ্যা মৌর্যদের একটা তীর্থ। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার অযােধ্যা জৈনদেরও তীর্থক্ষেত্র ছিল। পরে মহাবীর এসেছিলেন, এবং কয়েকজন তীর্থঙ্করের জন্ম হয়েছিল এখানে। কিন্তু জৈনরা স্পষ্টভাবে এর স্থান নির্দেশ করেননি। রামের অযােধ্যার কথা শােনা যায় গুপ্তযুগ থেকে। অযােধ্যা থেকে শিলমােহর, মুদ্রা বা শিলালেখ যা পাওয়া গিয়েছে তাতে গুপ্তযুগের আগে রাম দশরথের অযােধ্যার কোন হদিশ পাওয়া যায় না।
অযােধ্যা তীর্থক্ষেত্র হিসেবে ‘বিষ্ণু স্মৃতি’ (পরিচ্ছদ ৮৫) লেখা হয়েছিল আনুমানিক ৩০০ খৃষ্টাব্দে। এবং তীর্থের তালিকার মধ্যে এটিই সর্বপ্রথম রচিত। এতে ৫২টি তীর্থের কথা আছে, অযােধ্যার নাম নেই। ১০০০ সালে গড়বাল রাজার মন্ত্রী ভট্ট লক্ষ্মীধর তার ‘কৃত্য কল্পতরু’তে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তালিকা দিয়েছেন। তার মধ্যে অযােধ্যা বা রামের জন্মস্থানের কোন উল্লেখ নেই। অনাদিকাল থেকে হিন্দুদের যে বিশ্বাসের কথা বলা হচ্ছে, তুলসীদাসের লেখায় অযােধ্যা যে তীর্থ সেটা বলা হয়নি। বরং হিন্দুদের সবথেকে বড় তীর্থ বলে তুলসীদাস অভিহিত করেছেন প্রয়াগকে।
১৪২০ সালে বৃহস্পতি মিশ্র যে তীর্থের তালিকা দিয়েছেন, তার মধ্যে অযােধ্যা নেই। আকবরের রাজত্বকালে সেনাপতি টোডরমল কাশীর পণ্ডিতদের নিয়ে যে তীর্থপরিক্রমা দেখান তার মধ্যে অযােধ্যার উল্লেখ নেই। সুতরাং ১৬ শতকে গড়ে ওঠা বাবরি মসজিদ যেখানে, ঠিক সেইখানেই রাম ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, এই দাবি একেবারেই অসৎ ও উদ্দেশ্যপ্রণােদিতও বটে।
(৪)
এর নেপথ্যে রয়েছে উপমহাদেশের রাজনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণের ইতিহাস। দেশভাগের অনিবার্য ফল হিসেবে ভারতে হিন্দুত্ববাদী চেতনা সক্রিয় হয়। এরই জেরে ১৯৪৯ সালের ২২ ডিসেম্বর এক রাত্রিতে একদল সাধু জোরপূর্বক বাবরি মসজিদে রামলালার মূর্তি রেখে আসেন। এক্ষেত্রে কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির একটি বড় ভুমিকা ছিল। এটা ঠিক যে ১৯৪৯ সালের ২২-২৩ ডিসেম্বরের আগে বাবরি মসজিদে কোন রামলালার মূর্তি ছিল না। ১৯৪৮ সালে ফৈজাবাদ বিধানসভার উপনির্বাচনে সােসালিস্ট প্রার্থী আচার্য নরেন্দ্র দেবকে হারানাের জন্য কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী গােবিন্দবল্লভ পন্থ যে হীন পদ্ধতি নিয়েছিলেন, তাতেই রামভক্তদের সংখ্যাবৃদ্ধি হয় এবং তারা উত্তেজিত হয়।।
১৯৪৯ সালের ২৯ নভেম্বর ফৈজাবাদের এসপি জেলাশাসককে জানান যে, আযােধ্যায় জোর গুজব যে, হিন্দুরা গােপনে বাবরি মসজিদে রামের মূর্তি ঢােকাবে। জেলাশাসক এসপি-র পাঠানাে খবরে কোনও গুরুত্ব দেননি। ২২-২৩ ডিসেম্বর রাতে ৫০-৬০ জন রামভক্ত গােপনে মসজিদে রামের মূর্তি বসিয়ে পুজো করতে শুরু করে। রামভক্তরা বলে, মূর্তি ওখানে বরাবরই ছিল। মুসলমানরা বলে, মূর্তি হিন্দুরা ঢুকিয়েছে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী গােবিন্দবল্লভ পন্থ পুলিশ দিয়ে এই বেআইনি কাজ বন্ধ না করায় ভারতের রাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তাকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অনুরােধ জানান। সর্দার প্যাটেল তঁার চিঠিতে শ্রীপন্থকে লেখেন, কয়েক হাজার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর মুসলমানরা যখন এদেশকে নিজের দেশ বলে ভাবতে শুরু করেছে, তখন নতুন করে তাদের মনে আঘাত করে সমস্যা সৃষ্টি করা উচিত নয়। দুর্গা দাশ সম্পাদিত ‘সর্দার বল্লভভাই প্যাটেন্ লেটার’এ ওই চিঠিটা রয়েছে। চিঠিটা হুবহু মনে নেই, তবে বয়ানটা এইরকম ছিল। চিঠিটা পেয়ে উত্তরপ্রদেশ সরকার ফৈজাবাদের জেলাশাসককে ওই মূর্তিটি বের করে দিতে বলেন। জেলাশাসক ওই নির্দেশ পালন করেনি। উত্তরপ্রদেশ সরকার বাবরি মসজদ চত্বর বিতর্কমূলক ঘােষণা করে গেটে তালা লাগিয়ে দেয়। ১৯৫০ সালের জানুয়ারীতে আদালত রামের মূর্তি সরানাের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং পূজোর অনুমতি দেয়, কিন্তু বাবরি মসজিদে নামাজ পড়া বন্ধ হয়। মসজিদে রামের মূর্তি ঢােকানাের পর একের পর এক মামলা শুরু হয়।
গান্ধীজির মৃত্যুর পর জওহরলাল নেহরু এবং সর্দার প্যাটেল কংগ্রেস সােসালিস্ট পার্টিকে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে থাকতে দিতে অস্বীকার করেন। সােসালিস্টরা দল না ভেঙে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যায়। সােসালিস্ট নেতা আচার্য নরেন্দ্র দেব কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে ফৈজাবাদ কেন্দ্র থেকে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি কংগ্রেস থেকে পদত্যাগের পর বিধানসভা থেকেও পদত্যাগ করেন এবং উপনির্বাচনে সােসালিস্ট দলের প্রার্থী হন। কংগ্রেস হাইকমাণ্ড আচার্য নরেন্দ্র দেবকে হারানাের মতাে প্রার্থী খুঁজে পায় না। কারণ আচার্য নরেন্দ্র দেব ছিলেন কংগ্রেস সােসালিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি, সারা ভারত কিষাণ সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রাক্তন সদস্য এবং লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। স্বাধীনতার প্রাক্কালে গান্ধীজি আচার্য নরেন্দ্র দেবকে কংগ্রেস সভাপতি ও জয়প্রকাশ নারায়ণকে সাধারণ সম্পাদক করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জওহরলাল নেহরু ও সর্দার প্যাটেলের আপত্তিতে গান্ধীজির ইচ্ছা কার্যকর হয়নি। যাইহােক, গােবিন্দবল্লভ পন্থ আচার্য নরেন্দ্র দেবকে হারানাের দায়িত্ব নেন। সেই দায়িত্ব পালনও অভিনব।
অযােধ্যা ফৈজাবাদ বিধানসভার মধ্যে পড়ে। কংগ্রেস প্রথমে পােস্টার দেয়, এই কেন্দ্রে রামভক্ত হনুমানের শিষ্য নির্বাচন প্রার্থী। পরের পােস্টারে কংগ্রেস প্রার্থী হনুমানের শিষ্য রামের পদধূলি নিচ্ছে। তৃতীয় পােস্টারে রামভক্ত হনুমানের শিষ্যের নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বী একজন নাস্তিক। পরের পােস্টারে কংগ্রেস প্রার্থী রামভক্ত হনুমানের শিষ্য মােহান্তের বিরােধী প্রার্থী একজন নাস্তিক। তারপর মােহান্তের অযােধ্যায় ও ফৈজাবাদে বিজয়ীর বেশে আগমন। কোথাও প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আচার্য নরেন্দ্র দেবের নাম থাকে না। অর্থাভাবে সােসালিস্ট পার্টি কংগ্রেসের পােস্টার প্রচারের মােকাবিলা করতে পারে না। নির্বাচনে এক অজ্ঞাত মােহান্তের কাছে আচার্য নরেন্দ্র দেবের পরাজয়ে সারা ভারত স্তম্ভিত হয়। নির্বাচনে জেতার জন্য কংগ্রেসের নোংরা রাজনীতির নিন্দা করে, এই নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করে এম এন রায় ভারতের গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা হারান এবং দেশে বিজ্ঞানভিত্তিক চেতনা সৃষ্টির জন্য র্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট পার্টি তুলে দিয়ে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সৃষ্টিতে উদ্যোগী হন। নির্বাচনে জেতার জন্য কংগ্রেস ফৈজাবাদে যে নােংরা রাজনীতি চালু করে, সম্ভবত তা থেকেই বাবরি মসজিদ এর জায়গায় রামমন্দির গড়ার ভাবনার জন্ম দিয়েছিল। বিজেপি পরে এই ভাবনার নেতৃত্ব দেয়।৩
যাইহােক ১৯৪৯ সালে মূর্তি সরানাে অসম্ভব হলে স্থিতাবস্থা বজায় রেখে মসজিদের গেট তখন থেকে তালাবন্ধ করা হয়। এরপর ১৯৮৬ সালে সেই তালা খুলে দেওয়া হয়—
রাজনৈতিক মহলের অনেকেরই ধারণা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সচিবালয়ের হাত ছিল এতে। অরুণ নেহেরুর কথায় রাজীব এটা করিয়েছিলেন হিন্দু ভােট অটুট রাখার লক্ষ্যে। ফল কি হলাে? ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ গুড়িয়ে দেওয়া হল। তখনকার প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও বললেন, আমরা মসজিদ পুনর্নির্মাণ করব। তারপর তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। কোনও চেষ্টাই করেননি। এইতাে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতা!
স্মর্তব্য যে, এইসমস্ত সময়টা জুড়েই কিন্তু জমির মালিকানার প্রশ্নে পুরানাে রায় বহাল থাকে। কোর্ট পুরানাে রায় খারিজ করতে পারেন, তাতে আপত্তি বা অবাকের কিছু থাকে না। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে রচিত আইনই ভিত্তি হতে পারে সেই রায় পরিবর্তনে, ধর্মীয় বিশ্বাস বা আবেগ সেই ভিত্তি হতে পারে না। অথচ সেই আবেগ দিয়েই আইনের প্রশ্নকে নাকচ করা হল। আবেগই দেশের আইনকে প্রভাবিত করল। এটা ভারতের মত দেশের পক্ষে এক মারাত্মক প্রবণতা।
(৫)
ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে, স্থানটিতে কয়েক শতাব্দী প্রাচীন বাবরি মসজিদ ছিল। সেটা ভাঙল কিছু দুর্বৃত্তরা। তারা আইন তুলে নিল নিজের হাতে। এক কথায় অপরাধী তারাই অপরাধীর অপরাধের বিচার হল না, উল্টে তারা বাবরি মসজিদের জমিটাই পেয়ে গেল রামমন্দির নির্মাণের জন্য! এতে তাে প্রকারন্তরে বাবরি মসজিদ ভাঙাকে আইনসিদ্ধ করা হল! ‘মন্দির ভেঙে মসজিদ হয়নি’ আবার ‘বাবর কবে মসজিদ তৈরী করান তার কোন প্রমাণ নেই’, অথচ মসজিদ ছিল এ কেমন কথা? যে জিনিসটা কয়েক শতাব্দী থেকে ২৭ বছর আগে পর্যন্ত ছিল তার অস্তিত্ব কেন প্রমাণিত হল না, অথচ যে বিষয়টি শুধুমাত্র কিছু মানুষের বিশ্বাসের স্থানে ছিল, কখনও তার অস্তিত্ব মানুষ চোখে দেখেনি, তারই অস্তিত্ব প্রমাণ হয়ে গেল!
অথচ ভারতীয় প্রত্নতাত্বিক বিভাগ ২০০২ সালের খননে (রিপাের্ট বেরিয়েছিল ২০০৩এ) নাকি বাবরি মসজিদের তলায় অন্য একটা প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন পেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে খননের জালিয়াতির বিষয়টি সংক্ষেপে উল্লেখ করা দরকার। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগকে লখনউ কোর্ট যেদিন খননকার্যের নির্দেশ দিল, সেদিনই পুরাতত্ত্ব বিভাগে সর্বোচ্চ পদের পরিবর্তন হলাে। নতুন ডাইরেক্টর জেনারেল হলেন সংস্কৃতি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব। মনে রাখা দরকার তখন বিজেপি-জোট সরকারে আছে এবং সেই সরকারের উপ প্রধানমন্ত্রী এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী দুজনেই বিজেপি-র সর্বোচ্চ কমিটির নেতা এবং প্রধান অভিযুক্ত। এই বদলির সঙ্গে সঙ্গে মসজিদের নিচে মন্দির পাওয়া নিশ্চিত হয়ে গেল!
খোঁড়াখুঁড়ির জন্য বরাত দেওয়া হলাে যে ঠিকাদারকে তিনি বিশ্বহিন্দু পরিষদের লােক। ১২ মার্চ ২০০২ থেকে ৫০ জন মজুর নিয়ােগ করা হলাে, তার মধ্যে একজনও মুসলিম নেই। ফলে স্পেশাল বেঞ্চের আবার নির্দেশ টিম গঠন ও মজুর নিয়ােগে যেন উভয় সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রতিনিধি থাকে। এই আদেশও অগ্রাহ্য করা হলাে। ২৭ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত মজুর বাড়ানাে হলাে মুসলিম ৭ বা ৯ এবং হিন্দু ৩৬ জন। ভি এইচ পি নিয়ােজিত এই মজুরেরা ঠিকাদারের নির্দেশে মুসলিম সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিছু দেখলেই তা ছুঁড়ে দিচ্ছে আবর্জনা স্তুপে। এর একমাত্র সহজবােধ্য উদ্দেশ্য মসজিদ বলে প্রমাণ হতে পারে এমন সবকিছুকেই নষ্ট করে ফেলা। ফলে ১০ এপ্রিল হাইকোর্ট আবার নির্দেশ দেয় আরও বেশি মুসলিম মজুর নিয়ােগ করার জন্য কিন্তু কে শুনবে তার কথা।
তারপর ২৪ এপ্রিল একটা প্রাথমিক রিপাের্ট কোর্টে জমা পড়ল। এর উপাদানগুলাে ও এই এলাকা থেকে পাওয়া অন্যান্য জিনিসগুলাে একজন ঐতিহাসিক পরীক্ষা করেন। তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জিনিস যা নথিভুক্ত, তা হয় বাবরি মসজিদের সঙ্গে যুক্ত অথবা অনেক বছর আগেকার মুসলিম বসতির সঙ্গে সম্পর্কিত। অথচ রিপাের্ট বেরােল পুরাে উল্টো—ওখানে একটি প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন মিলল! ২০০৩-এর রিপাের্টে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ পুরাতাত্ত্বিক বিজ্ঞানের সমস্ত স্বীকৃত পদ্ধতি, অনুসন্ধানের নিয়ম, প্রাপ্ত নিদর্শনগুলিকে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ও পরীক্ষার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা—এ সমস্তকেই বুড়াে আঙ্গুল দেখিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের খুশি করা মন্দিরতত্ত্বকেই সার্ভে রিপাের্টে জুড়ে দেয়। কাল নির্ণয়ের জন্য সুশৃঙ্খলভাবে প্রত্যেকটি স্তর থেকে কাবনের মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহ। করা, জৈব পদার্থের উপস্থিতি দেখার জন্য মাটির পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানাে, প্রত্ন সম্পদ সমূহের স্তর ও পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী সুশৃঙ্খল বিশ্লেষণ, এর কোনটাই করা হয়নি। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ সংগ্রহের অত্যন্ত বুনিয়াদী দুটি পদ্ধতি—স্তরবিন্যাস এবং প্রাপ্ত পুরাবস্তুর যথাযথ নথীকরণ—কোনটারই তােয়াক্কা করা হয়নি। তাই ঐতিহাসিক ইরফান হাবিবের নেতৃত্বে একদল বুদ্ধিজীবী যেমন প্রত্নতাত্ত্বিক সূরজ ভান, আইনজীবী রাজীব ধাওয়ান ও অর্থনীতিবিদ প্রভাত পট্টনায়ক ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের রিপাের্টের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁদের মতে, এই রিপাের্ট সম্পূর্ণভাবে অপেশাদারি ও পক্ষপাতিত্বমূলক।
প্রথমত, খননকার্যে খুঁজে পাওয়া পশুদের হাড়ের কোনাে পরীক্ষা করা হয়নি। ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার আলগাভাবে স্বীকার করা হয়েছে—“বিভিন্ন পর্বের স্তর থেকে পশুর হাড় পাওয়া গেছে। অথচ মূল রিপাের্টে কোথাও আদৌ সেই হাড়ের বর্ণনা নেই, পরীক্ষা নেই। কোন প্রাণী তা চিহ্নিত করা হয়নি। কোন পরিখায় ও কোন স্তরে এই হাড় পাওয়া গেছে তার তালিকা নেই। বিশেষ করে যেসব হাড়ে ক্ষতের চিহ্ন আছে, তার তালিকা নেই। উদ্দেশ্য স্পষ্টই। কারণ, সর্বত্র সব স্তরে পশুর হাড়ের উপস্থিতি মন্দিরের অস্তিত্বের পক্ষে যথােপযুক্ত প্রমাণ নয়। নিশ্চয়ই মন্দিরে বসে পশু খেয়ে হাড় জমিয়ে রাখা হয় না। হাড় জৈব পদার্থ ও তা কার্বন পদ্ধতিতে সময় নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা করাও সম্ভব। বিস্ময়কর যে, বাবরি মসজিদ স্থলে পাওয়া হাড় কার্বোনেট করা হয়নি। সেক্ষেত্রে হাড়ের সময় নির্ণয় করেই বলে দেওয়া যেত কবে থেকে সে সব হাড় ওখানে আছে, অর্থাৎ ওই সময় মন্দিরের সম্ভাবনা আছে কিনা। অর্থাৎ মূল রিপাের্টে কাল নির্ণয়ের কোনও চেষ্টা নেই। শুধু হাবিবরা যখন বলেছেন, এমন নমুনা মন্দির তত্ত্বের পরিপন্থী, তখন শােনা গেল স্বরাজ প্রকাশ গুপ্তর কণ্ঠ—কেন, ওঁরা জানেন না মন্দিরে আগেও বলি হত, এখনও হয়। ঠিক গুপ্তজি, কিন্তু রামের (অথাৎ বৈষ্ণব) মন্দিরে বলি? শােনাও পাপ!
দ্বিতীয়ত, মাটি খুঁড়ে মেঝের স্তরের তলাতেই মধ্যযুগের (অথাৎ মুসলিম যুগের) উজ্জ্বল মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে, এটা মন্দিরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। কারণ তা মধ্যযুগীয় সুলতানি আমলের বা পাঁচ-ছ’শাে বছরের বেশি পুরানাে নয়। কিন্তু কোনরকম ‘Thermo-Luminescence’ পরীক্ষা ছাড়াই কালাে ও হালকা রঙের মৃৎপাত্র NBP বা Northern Black Polished Ware’-কে ঠেলে ১০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের বলে উল্লেখ করে দেওয়া হল এবং রিপাের্টের ২৬৮-২৬৯ পাতায় ‘ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার’ বর্ণনায়। ষষ্ঠ পর্ব হয়ে গেল আদি মধ্যযুগীয়, যাতে মৃৎপাত্রগুলিকে সুলতানি আমলেরও আগের বলে দেখানাে যায়।
তৃতীয়ত, একইভাবে চুনের সঙ্গে গুঁড়াের মিশ্রণে তৈরী মেঝের যে প্রমাণ মিলেছে তা ইসলামীয় রীতিতে তৈরী এবং এর ব্যবহারকাল অনুমানের দড়িকে যথেচ্ছ প্রলম্বিত করলেও ১২০০ খ্রীঃ আগে পাঠানাে যাবে না। একটাও প্রাক্-মুঘল মন্দির দেখানাে যাবে না যেখানে চূণ-সুরকির মেঝে ছিল। অথচ রিপাের্ট একে মন্দিরের মেঝে বলে চালিয়ে দিল। রিপাের্ট চারটি স্তম্ভ-ভিত্তির কথা বলেছে যা নাকি মন্দিরের বিশাল স্থাপত্যের বাহক। এবং এই বিশাল স্থাপত্যটি অবশ্য মন্দির। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ যাকে স্তম্ভ-ভিত্তি বলছে তা আসলে একাধিক ক্যালক্রিট পাথর, যা মাটির প্রলেপ দেওয়া ইটের ভগ্নাংশের ওপর রয়েছে। কাদামাটির প্রলেপ দেওয়া ইটের ভগ্নাংশ কি করে ছাদের ওজনবাহী স্তম্ভের ভার বইতে পারে, তা রিপাের্ট-লেখা খননবিদরাই জানেন। Fill Material-কে Cultural Material বলে চালিয়ে দেওয়া হল। এমনকি স্তম্ভ-ভিত্তিগুলাের কোন সুনির্দিষ্ট আকারও নেই, কোনটা চতুষ্কোণাকৃতি, কোনটা আয়তাকার, কোনটা বৃত্তাকার। সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য পুরাবিভাগ খনন এলাকার Isometric পরিমাপ নিয়েছে যাতে মনে হয় এগুলাে সারিবদ্ধভাবে অবস্থান করছে। এইরকম সমতাহীন স্তম্ভের ওপর মন্দির বানানাের নক্সা কেন গুপ্তোত্তর যুগের (৭-১০ খ্রীঃ) নক্সা থেকে আলাদা এবং বাবরি মসজিদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, তার কোন ব্যাখ্যা নেই।
চতুর্থত, বৃত্তাকার মন্দির ছিল বলে বলছে রিপাের্ট। এটা নাকি শৈব ও বৈষ্ণব মন্দিরের আদলের সঙ্গে তুলনীয়। অথচ ইসলামীয় স্থাপত্য রীতিতে এইরকম বৃত্তাকার দেওয়াল ও আকার অত্যন্ত সুবিদিত। বাবরি মসজিদের ভেতর একটা কালাে সিস্ট পাথরের স্তম্ভ ছিল, সেটা মন্দির প্রেমিক করসেবকরা গুঁড়িয়ে দেন। এছাড়া খুঁড়ে অলংকৃত পাথর, লেখাযুক্ত পাথরের চাই, লতানাে নকযুক্ত পাথর, আমলক, অর্ধবৃত্তাকৃতি পিলাস্টার সহ পদ্ম ফুলের না যা পাওয়া গিয়েছে, তা সামগ্রিক বিচারে খুবই সামান্য এবং তা যে অন্য জায়গা থেকে এনে এখানে নির্মাণে পুনর্ব্যবহার করা হয়েছিল তা স্পষ্ট।
পঞ্চমত, তাছাড়া ভূগর্ভস্থ ভগ্নাবশেষ থেকে রামমন্দিরের অস্তিত্বের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ছােট বড় মূর্তির ভগ্নাবশেষগুলির কোনটাই রাম-সীতার নয়। রাম জন্মভূমি হলে দশরথের যে প্রাসাদের অস্তিত্বের কোনও চিহ্ন মেলেনি। এইভাবে একদিকে মন্দির তত্ত্বের সরাসরি বিরুদ্ধে যায় এমন সব প্রমাণই ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ আড়ালে লুকোতে চেয়েছে। আর সুপ্রিম কোর্টও তাে এই পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ নিয়ে কোনও প্রশ্ন তুললেন না।
অথচ ঐ রিপাের্টেই যে ভগ্নাংশগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে তা হিন্দুর বদলে বৌদ্ধ বা জৈন মন্দিরও হতে পারে। কালের নিয়মে জরাজীর্ণ হয়ে বহু বৌদ্ধ স্থাপত্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তিও কিছু কিছু ধ্বংস করেছিল। অনেক হিন্দু মন্দিরও কালের গ্রাসে গুরুত্বহীন হয়ে ধ্বংস হয়েছিল। এককালে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে বৌদ্ধ বা হিন্দুরা ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিল, যেটা বিবেকানন্দসহ বহু মনীষী স্বীকার করেছেন। এক্ষেত্রে ঐসব অঞ্চলে বৌদ্ধ বা হিন্দু মন্দির নব মুসলিমদের কাছে তার প্রয়ােজনীয়তা হারিয়েছিল। কালক্রমে সেগুলি জরাজীর্ণ হয়ে ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছিল। সেই ধ্বংসাবশেষ ব্যবহার করে হয়ত পরে মুসলিম স্থাপত্য গড়ে উঠেছিল। বাংলার কয়েকটি প্রাচীন ইসলাম ধর্মীয় সৌধের প্রত্নসাক্ষ্যেও অ-ইসলামীয় অলংকরণ ব্যবহৃত হওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। বহুকাল পরের মানুষদের এরকম মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক যে সে যুগে প্রাক-ইসলামীয় ধর্মস্থান ধ্বংস করেই ওই সব অলংকরণগুলি আহৃত হয়ে ইসলামীয় সৌধে ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু বাংলার সহযানী বৌদ্ধদের দলে দলে ইসলাম ধর্মগ্রহণের প্রেক্ষাপটটাই এই রকম ঘটনার অন্যরকম অথচ অতি যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছে।
আমরা দেখেছি যে সহজযানীদের পূর্বসূরী বৌদ্ধ বজ্রযানীদের মধ্যে বুদ্ধদেবের নানা শক্তিরূপের দ্যোতক হিসাবে বহু বৌদ্ধদেবদেবীর উদ্ভব ও তাদের পূজার ব্যাপক প্রকাশ ঘটেছিল। ওই সব দেবদেবী যে সব বৌদ্ধ মন্দির বা মঠে পূজিত হতাে সেগুলি নানা বৌদ্ধ প্রতীক চিহ্নেও সজ্জিত হতাে। বজ্রযানীদের সূচনার আমলে তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণে সেই অলংকরণগুলি নির্মিত হতাে বাংলায় দুষ্প্রাপ্য উচ্চমূল্যের পাথর দিয়ে। কিন্তু সহযানী আমলে বাংলার বৌদ্ধদের মূল অংশের লােকেদের মধ্য থেকে মূর্তিপূজার অবসান হয়ে যাওয়ায় ওই সমস্ত বজ্রযানী বিগ্রহ ও সৌধগুলি পরিত্যক্ত হয়ে ধ্বংসােন্মুখ অবস্থায় চলে গিয়েছিল বলেই মনে হয়। কিন্তু ২/১টি ক্ষেত্রে ব্যাতিক্রম ছাড়া সেগুলি বর্ণহিন্দুদের দেবালয়ে পরিবর্তিত না হওয়াই স্বাভাবিক। এই সব পরিত্যক্ত সৌধগুলির অধিকাংশের অবস্থান নিশ্চিতই সহযানী অধ্যুষিত গ্রামাঞ্চলেই ছিল। আর সেগুলি গ্রামের চারণভূমির মতাে গ্রামবাসীদের সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তাই কোনও গ্রামের সহযানী ইসলাম ধর্মী হয়ে যাওয়ার পর প্রাথমিক পর্যায়ে যে সব ইসলাম ধর্মৰ্চারণের জন্য সৌধের প্রয়ােজন দেখা দিয়েছিল তা সেই সব ব্যবহার্য অথচ পরিত্যক্ত বজ্রযানী সৌধগুলি মেটাতাে। এগুলিতে কিছু ইসলামী চিহ্নযুক্ত করেই বৌদ্ধ/জৈন সৌধগুলিকে ইসলামীয় করে নেওয়া হতাে।
আবার কোনও নির্মিয়মান ইসলামী সৌধের অলংকরণে ধ্বংসপ্রাপ্ত অ-ইসলামীয় সৌধগুলির অলংকারগুলি বা সৌধের অংশ বিশেষ সংযােজন করে নিত। কে বলতে পারে যে ভারতে মসজিদ সমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ আদিনা মসজিদে (পাণ্ডুয়া : নির্মাণ ১৩৭৫ খ্রীঃ) যে সব বৌদ্ধ অলংকরণ চিহ্ন রয়েছে সেগুলি কয়েকশত বৎসর পূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দু রাজাদের পরিত্যক্ত রাজধানী পাণ্ডুয়া থেকে এভাবেই সংগৃহীত হয়নি? এ কথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়ােজন যে কোনও প্রাচীন ইসলামীয় সৌধে অ-ইসলামীয় অলংকরণের অবিস্থিতি অনিবার্যভাবে প্রমাণ করে না যে সেই সৌধটি নির্মাণে নিকটবর্তী কোনও অ-ইসলামীয় ধর্মস্থানের—যেখানে তখনও ধর্মাচরণ চলছিল—তাকে ধ্বংস করেই সেই সব অলংকরণ আহৃত হয়েছিল।
ইসলাম ধর্মীয় সৌধে হিন্দু মন্দিরের অংশবিশেষ ব্যবহারের আরও একটি পরিপ্রেক্ষিতও আলােচনা প্রয়ােজন। যদিও বাংলায় ইসলাম ধর্মগ্রহণকারীদের একটা বড় অংশই বৌদ্ধ সহজযানীরা ছিল, তবু বাংলার গ্রামাঞ্চলে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বিচার অস্পৃশ্য বা জল-অচল শূদ্র জাতির লােকেদের একটা উল্লেখযােগ্য অংশও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অতলান্ত ঘৃণা-বিদ্বেষঅত্যাচার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ও ইসলামের ধর্মীয় সাম্যের আকর্ষণে সে ধর্ম গ্রহণ করেছিল। এরকম ব্রাত্যজন অধ্যুষিত গ্রামে মুষ্টিমেয় বর্ণ হিন্দুরও অধিষ্ঠান ছিল। সে সব গ্রামে তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ের অবস্থিতি নিশ্চিতই ছিল। কিন্তু এরকম মন্দির কোনও ব্যক্তি বিশেষের পারিবারিক বংশানুক্রমিক সম্পত্তি ছিল বলেই সে সব মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ বা পূজার্চনা সেই সব পরিবারের অর্থানুকূল্যেই সাধিত হতাে। কিন্তু সে রকম কোনও পরিবারের আর্থিক অবস্থার বিপর্যয় ঘটলে তাদের পক্ষে আর মন্দিরের ব্যয় সংকুলন সম্ভবপর হতাে না। ফলে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী এরকম মন্দিরের স্বত্বাধিকারীরাই মন্দির পরিত্যাগ করে বিগ্রহকে নদী বা জলাশয়ে বিসর্জন দিতেন। তুর্কী আগমনের বহু শত পূর্ব থেকেই বাংলায় তথা ভারতে এরকম অজস্র পরিত্যক্ত মন্দির বা বিগ্রহের অস্তিত্ব ছিল এবং আজও আছে। ইসলাম ধর্মগ্রহণকারী ব্রাত্যজনদের অধ্যুষিত গ্রামেও এরকম পরিত্যক্ত মন্দির বা বিগ্রহের অবস্থানও স্বাভাবিক ঘটনা। এখন ইসলাম ধর্মগ্রহণকারী সেখানকার একদা ব্রাত্য মানুষদের ওই রকম পরিত্যক্ত মন্দির বা বিগ্রহের প্রতি কি মনােভাব পােষণ করা স্বাভাবিক? ব্রাত্য জীবনে যারা কখনও সে সব মন্দিরে প্রবেশাধিকার পায়নি, ব্রাহ্মণদের বিধানে যে সব মন্দিরে দেবতাদের পূজা দেওয়ার অধিকার তাদের ছিল না—তাদের কাছ থেকে কি সেই সব পরিত্যক্ত মন্দির বা বিগ্রহের প্রতি কোনাে ধর্মীয় মােহ আশা করা সঙ্গ ত? তাই ওই ধর্মান্তরিত ব্রাত্যজনেরা যখন তাদের নতুন ধর্মের প্রয়ােজনে কোনও সৌধ নির্মাণ করেছিল, তখন তাতে ওই পরিত্যক্ত মন্দিরের অংশ বা বিগ্রহ সংযােজিত করেছিল। মনে রাখা প্রযােজন যে পর্বতহীন গাঙ্গেয়বঙ্গে পাথরের বড়ই অভাব ছিল এবং যা পাওয়া যেত সেগুলি হতাে দুর্মূল্য। যার পরিবর্ত হিসাবে মন্দির বা বিগ্রহের পাথর ব্যবহৃত হয়েছিল, তারা তা করেছিল সেগুলির প্রস্তর মূল্যের জন্যই হিন্দু ধর্মীদের মনে আঘাত করার জন্য নয়, তাদের উপহাস করার জন্যও নয়। পাশাপাশি স্মরণ রাখতে হবে যে বাংলার মানুষরা। সুফী সন্তদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। আর তৎকালীন জগতে বিশ্বমানবতাবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা সুফীদের পক্ষে ভিন্নধর্মীদের ধর্মস্থান ধ্বংস করার প্ররােচনা দেওয়ার অভিযােগ করা এক ঐতিহাসিক বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়।
এ বিষয়ে আরও কিছু বলা দরকার। সেকালে ঝড়-খরা-বন্যা-ভূচাল-মহামারী হলে লােকে বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে যেত। রাজস্ব বা সামন্ত পীড়নেও পালাত। এভাবে পাকা মন্দির মসজিদ পরিত্যক্ত হত। তাছাড়া পাথুরে মন্দির-মসজিদ হলে স্থানীয় লােক অর্থাভাবে মেরামত করতে পারত না বলে এক সময়ে সেগুলাে জীর্ণ হয়ে ভেঙে পড়ত। হিন্দুদের হাজারাে বিশ্বাসে সংস্কারে নিয়ন্ত্রিত জীবন। কাজেই ভাঙা মসজিদের বা মন্দিরের পাথরের উপযােগ নেই তাদের কাছে। কিন্তু মুসলিমদের সে-সংস্কার ছিল না বলে ওরা পরিত্যক্ত বা জীর্ণ মন্দিরের পাথর উত্তরভারতের অনেক মসজিদে ব্যবহার করেছে। তুর্কি-মুঘলরা শাসন-প্রশাসন চালিয়েছে হিন্দু দিয়েই, তাছাড়া গােটাভারত কখনও তুর্কী-মুঘল অধিকারেও ছিল না। হিন্দু প্রজা রইল, তার পেশা রইল, তার পারিবারিক জীবন রইল, সামাজিক জীবন রইল, তার শাস্ত্র ও শাস্ত্রাচার রইল, লক্ষ লক্ষ ঘরে গৃহ দেবতা রইল, গাঁয়ে-গঞ্জে শহরে-বন্দরে মন্দিরও রইল। কয়েকটি মসজিদে কয়েক টুকরাে মূর্তি অঙ্কিত পাথর দেখেই কি বলা যায় যে তুর্কী-মুঘলরা মন্দির ভেঙেছে? হ্যা মন্দিরও ওরা ভেঙেছে, বিদ্রোহী হিন্দু ধনী-মানী-মহাজন-জমিদার-সামন্তকেও হয় এককভাবে অথবা স্ববংশে হত্যা অবশ্যই ওরা করেছে প্রশাসনিক প্রয়ােজনে, আজও করতে হয়। পাকিস্তানে মসজিদে সৈন্যরা সবুট ঢুকে লােক হত্যা করেছিল। ১৯৭১-এ এরাই বাংলাদেশের রমনা কালীমন্দির ভেঙেছিল। এই সেদিন (প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সময়ে) শিখ স্বর্ণমন্দিরে সবুট সৈন্য প্রবেশ করে নরহত্যা করেছে। রাজারা এমন কাজ করেই। তাই সমস্ত মন্দির ও মঠের ক্ষতি সাধনের জন্য মুসলিম কার্যকলাপকে দায়ী করলে স্বাভাবিক ধ্বংসের বিষয়টি এবং হিন্দু মতবাদের অসহিষ্ণুতাকে উপেক্ষা করা হবে।
অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওই ধরনের ক্ষতিসাধনে মুসলিমদের দায়ী করা হয়েছিল যুদ্ধকালীন কার্যকলাপ থেকে; যখন এরকম হয়নি, তখনও তার উদ্দেশ্য ধরা উচিত বিজয়ীর ধর্মীয় উৎসাহের জন্য নয়। তাছাড়া ইতিহাসের উৎসাহী বর্ণনার মধ্যে ধর্মীয় উৎসাহ ছাড়া আরও বেশি কিছু রয়েছে। মন্দির ধ্বংস করার ও ‘আল্লাহর আবাসস্থল তৈরি করার’ অতিরঞ্জিত বর্ণনায় একটা প্রচারের মূল্য ছিল। এতে মধ্য এশিয়া থেকে লােক সংগ্রহ করার সুবিধা হত ধর্মের গৌরব ও জাগতিক ধন পাবার সম্ভাবনা দেখিয়ে। জাঁকজমকপূর্ণ ভাষায় রচিত ‘ফতেনামা’ (বিজয়কাহিনী) তৈরি করা হয়েছিল এজন্যই।
(৭)
তাছাড়া সুলতানরা পূর্বতন রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যও মন্দির ধ্বংস করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন অথাৎ পরাজিত হিন্দু রাজাদের শাসনের বৈধতা নষ্ট করে তাদের সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করার জন্য। হিন্দু রাজন্যবর্গের বৈধতা যুক্ত থাকত রাজকীয় মন্দিরের সঙ্গে যেখানে অধিষ্ঠিত থাকত রাজবংশের রাষ্ট্রদেবতার মূর্তি। সেই মন্দিরগুলিই আক্রান্ত হত, যার ফলে পরাজিত হিন্দুরাজারা তাদের ঈশ্বর প্রদত্ত বৈধতা হারিয়ে ফেলে নিজেদের চিরতরে বিধ্বস্ত বােধ করতেন ও মাথা তুলে দাঁড়াবার সাহস ও মানসিকতা হারিয়ে ফেলতেন। যে সব হিন্দু মন্দির এইভাবে রাজবংশের রাজকীয় মন্দিরের মর্যাদা লাভ করেনি সেগুলি সুলতানী শাসনে আক্রান্ত হয়নি। খাজুরাহাের বিখ্যাত মন্দির যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।
প্রসঙ্গক্রমে মীরজুমলা কর্তৃক কোচবিহারের রাজমন্দিরটি ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা যায়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আর এম ইটন ‘এসেজ অন ইসলাম অ্যান্ড ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি’ গ্রন্থে অত্যন্ত বিস্তারিত ও প্রামাণ্য তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যে, ওই সব মন্দির ধ্বংস বা অপবিত্র করার পেছনে রয়েছে বিজয়ী রাজা কর্তৃক পরাজিত রাজার কুলদেবতার মন্দির ধ্বংস করার প্রেরণা। যার ফলে পরাজিত রাজা যে কেবল তার জাগতিক ক্ষেত্র থেকেও উৎসাদিত হলেন তাই নয়, তিনি তাঁর পারত্রিক ক্ষেত্র থেকেও উৎখাত হলেন। এ দ্বারা আরও প্রমাণিত হলাে যে, যে রাজা তাঁর কুলদেবতাকে রক্ষা করতে অসমর্থ তাঁর রাজত্ব করার কোনােও নৈতিক অধিকার নেই। আর এই রাষ্ট্রনৈতিক প্রথা ইসলাম ধর্মী শাসকদের আবিষ্কার বা আমদানি করা নয়। প্রাক ইসলাম যুগের তথাকথিত হিন্দু ভারতেই তার প্রচলন ছিল।
ষষ্ঠ শতকে রচিত ‘বৃহৎ সংহিতায়’ বলা হয়েছে, যদি কোনও মন্দিরে দেববিগ্রহ ভেঙে যায় বা ভেঙে দেওয়া হয়, কোনও ফাটল দেখা দেয় বা কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাহলে তা রাজা ও দেশের অনিবার্য ধ্বংসের বার্তা ঘােষণা করে। এই বিশ্বাস হিন্দুরাজাদের মানসিকতায় দৃঢ়ভাবে প্রােথিত থাকার ফলে এক হিন্দু রাজা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য হিন্দু রাজার রাষ্ট্র দেবতার বিগ্রহ ও মন্দির ধ্বংস বা কলুষিত বা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে ষষ্ঠ শতক থেকে। এ সমস্ত বিবেচনা করেই বলা যায় যে এ মন্তব্যটি অত্যন্ত সঠিক যে পরাজিত রাজার রাজমন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস করার প্রেরণা কোনও বিশেষ ধর্মানুসারীদের অপর ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ থেকে আসেনি। এটা ভারতে প্রচলিত রাষ্ট্রতত্ত্বেরই প্রবাহমান ধারার একটি বিশেষ অংশ।
এটা ঠিক যে, মুসলিম আগমনের প্রাথমিক যুগে মুসলিম শাসকদের কেউ কেউ কিছু মন্দির ধ্বংস করেছিলেন মন্দিরে সঞ্চিত ধনদৌলতের লােভে বা সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্যে। সেকাজ তাে ভারতে পাঠান-মুঘল শাসন প্রবর্তিত হওয়ার আগে হিন্দু শাসকরাও করতেন। বাংলার কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্মের মূলােৎপাটনের জন্য এমন কোনও প্রচেষ্টা ছিল না যা তিনি করেননি। তিনি বুদ্ধগয়ার পবিত্র বােধিবৃক্ষ (যে বৃক্ষের তলায় বসে দিব্যজ্ঞান লাভ করেছিলেন বুদ্ধদেব) কেটে জ্বালিয়ে দেন। পাটলিপুত্রতে বুদ্ধদেবের পদচিহ্নের নিদর্শন সম্বলিত পাথর খন্ডটি ভেঙে টুকরাে টুকরাে করে দেন। বহু বৌদ্ধশালা ও বৌদ্ধভিক্ষুকদের তিনি দেশত্যাগ করতে বাধ্য করেন। অবশ্য ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, শশাঙ্কের এরূপ ধ্বংস সাধনের কারণ বৌদ্ধ বিদ্বেষ নয়; প্রকৃত কারণ বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হর্ষবর্ধনের এতদঞ্চলে আক্রমণ। “বৌদ্ধধর্মের রাজকীয় মুখপাত্র তখন হর্ষবর্ধন, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শশাঙ্ক; রাষ্ট্রক্ষেত্রে উভয়ে উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং উভয়েই সংগ্রামরত। এই অবস্থায় শশাঙ্কের পক্ষে গয়ার বােধিদ্রুম কাটিয়া পােড়াইয়া ফেলা, বুদ্ধপ্রতিমাকে অন্য মন্দিরে স্থানান্তরিত করা এবং সেই স্থানে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা, কুসীনারার একবিহার হইতে ভিক্ষুদিগকে তাড়াইয়া দিয়া বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা; পাটলিপুত্রে বুদ্ধপদাঙ্কিত একটি প্রস্তরখন্ডকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করা প্রভৃতি কিছুই অস্বাভাবিক নয়।”৪
তবে শশাঙ্ক যে একেবারে বৌদ্ধ বিদ্বেষী ছিলেন না তা শ্রী রায় একেবারে অস্বীকার করেননি। “য়ুয়ান-চোয়াঙ (হিউয়েন সাঙ ভারতেদ্দেশে ভ্রমণকাল ৬০০-৬৪৫খ্রীঃ) হয়তাে শশাঙ্কের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি কিন্তু বলিতেছেন, শশাঙ্ক ছিলেন নিদারুণ বৌদ্ধ-বিদ্বেষী এবং তিনি বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদসাধনেও সচেষ্ট হইয়াছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি কী কী অপকর্ম করিয়াছিলেন, তাহার একটি নাতিবৃহৎ তালিকাও দিয়াছেন। য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণের পরিণতির—অর্থাৎ দূরারােগ্য চর্মরােগে শশাঙ্কের মৃত্যুকাহিনীর—একটু ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মঞ্জুশ্রীমূলকল্প-গ্রন্থেও আছে; এবং খুব আশ্চর্যের বিষয়, মধ্যযুগীয় ব্রাহ্মণ্যকুল-পঞ্জীতেও আছে। বৌদ্ধ-বিদ্বেষী শশাঙ্কের প্রতি বৌদ্ধ লেখকদের বিরাগ স্বাভাবিক, কিন্তু বহুযুগ পরবর্তী ব্রাহ্মণ্যকুলপঞ্জীতে তাহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া একটু আশ্চর্য বই কি।…কিন্তু তাঁহার বিবরণ সর্বদা মিথ্যা এবং শশাঙ্কের বৌদ্ধ-বিদ্বেষ ছিল না একথা বলিয়া শশাঙ্কের কলঙ্কমুক্তির চেষ্টাও আধুনিক ব্রাহ্মণ্য মানুষের অসার্থক প্রয়াস।”৫ অষ্টম শতকে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানকালে কুমারিল ভট্টও বৌদ্ধ নির্যাতনের স্বপক্ষে রীতিমত শাস্ত্রীয় নির্দেশ জারি করেছিলেন। ‘বৌদ্ধ মাত্রই বধ্য’-এই মতের প্রচার করেছিলেন তিনি।
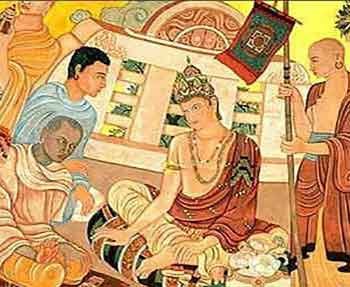
এছাড়া আদি মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসে হিন্দু রাজাদের নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্বসংঘাতের ফলে মন্দির বিনষ্ট হওয়ার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় আর এম ইটনের ‘এসেজ অন ইসলাম অ্যান্ড ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি’ (দিল্লি, ২০০২) নামক গ্রন্থে:
১. পল্লব রাজবংশের রাজা প্রথম নরসিংহবর্মন (৬৩০-৬৬৮) চালুক্যদের রাষ্ট্রদেবতা মন্দিরের মূল বিগ্রহ গণেশ মূর্তি ৬৪২ সালে লুণ্ঠন করেন।
২. চালুক্য রাজা ৬৯৩ সালে উত্তর ভারতে অভিযান চালিয়ে পরাজিত রাজাদের মন্দির থেকে গঙ্গা ও যমুনার দেবীমূর্তি লুণ্ঠন করেন।
৩. অষ্টম শতকে কাশ্মীর রাজ ললিতাদিত্যের (৬৯৯-৭৩৬) রাজ্যে হানা দিয়ে পাল রাজারা কাশ্মীরে রাজাদের রাষ্ট্রদেবতা রামস্বামী নামক বিষ্ণু মূর্তিকে ভেঙে দেন।
৪. অষ্টম শতকে পাণ্ড্য রাজা শ্রীবল্লভ সিংহল আক্রমণ করে তাঁর রাজধানীতে একটি সােনার বুদ্ধমূর্তি লুণ্ঠন করে নিয়ে যান।
৫. দশম শতকের গােড়ার দিকে প্রতিহার রাজা হেরম্বপদ কাংড়ার শাহী রাজাকে হারিয়ে সােনার বিষ্ণুমূর্তি লুণ্ঠন করেন।
৬. দশম শতকের মাঝামাঝি ওই বিষ্ণুমূর্তি আবার ছিনিয়ে নেন চান্দেলা রাজ যশােবর্মন এবং সেটাকে খাজুরাহের লক্ষ্মণ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন।
৭. একাদশ শতকের প্রথম দিকে চোল রাজা প্রথম রাজেন্দ্র (১০১৪-১০৪২) বিভিন্ন রাজমন্দির থেকে বিভিন্ন দেবমূর্তি লুট করেন।
৮. একাদশ শতকের মাঝের দিকে চোল রাজ রাজাধিরাজ (১০১৮-১০৫৪) চালুক্য রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে চালুক্য রাজবংশের রাষ্ট্র দেবতা দ্বারপালিকা বিগ্রহ বিধ্বস্ত ও মন্দির পুড়িয়ে দেন।
৯. ওড়িশার সূর্যবংশী গজপতি বংশের রাজা কপিলেন্দ্র ১৪৬০ সালে তামিল রাজাদের রাজত্বে যুদ্ধাভিযান চালিয়ে বহু শৈব ও বৈষ্ণব মন্দির বিধ্বস্ত করেন।
১০. বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায় ১৫১৪ সালে উদয়গিরির রাজাকে যুদ্ধে হারিয়ে বালকৃষ্ণ মূর্তি তাঁর রাজধানীতে নিয়ে যান।
১১. ছয় বছর পর ওই কৃষ্ণদেব রায় গান্ধারপুর দখল করে রাজবিগ্রহ ভিট্টলকে বিজয়নগরে নিয়ে যান।
১২. দশম শতকের গােড়ার দিকে রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় ইন্দ্র তাঁর শত্রুপক্ষীয় প্রতিহার রাজার রাষ্ট্রদেবতার কলাপ্রিয় মন্দির ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে নিজেই বিস্তারিতভাবে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন।
(৮)
মুসলিম শাসকরা ওইসব হিন্দুশাসকদেরই অনুসারী ছিলেন। সােমনাথের মন্দির বারবার লুণ্ঠিত এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল সেখানে সঞ্চিত অঢেল ধনসম্পদের লােভেই। হিন্দু মন্দির ধ্বংস করার উদ্দেশ্য আর যাইহােক না কেন, হিন্দুদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা নিশ্চয় নয়। কেননা কী করে আমরা ভাবতে পারি যে, কোনও সম্প্রদায়ের হৃদয় জয় করা যায় তাদের মন্দির ধ্বংস করে? এই ধ্বংস প্রক্রিয়া তাদের মনে ইসলাম সম্বন্ধে প্রেম নয়, বরং ঘৃণারই উদ্রেক করতে পারে। তাহলে এ ধরনের কার্যকলাপের উদ্দেশ্য তাদের মন্দির ধ্বংস করা নিশ্চয় নয়, নিশ্চয়ই অন্য কোনও অভিপ্রায় ছিল। এটা লক্ষ্যণীয় যে, সাধারণত কেবলমাত্র শত্রুপক্ষের এলাকার মন্দিরগুলিই ধ্বংস করা হয়েছে। মন্দিরগুলি ষড়যন্ত্র বা বিদ্রোহের কেন্দ্র না হয়ে দাঁড়ালে সম্রাটের নিজের এলাকার মধ্যে কখনওই তা ধ্বংস করা হত না। শত্রুর এলাকার মন্দির ধ্বংস করা যেন জয়ের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে কোনও মুসলিম শাসক মসজিদ নির্মাণের জন্য মসজিদ ভেঙেছেন এমন নজির পাওয়া যায়। আসলে কোনও মুসলিম শাসকের পক্ষে তার ধর্মবিশ্বাসের জায়গাটা যতই দুর্বল হােক, জবরদখল করা জায়গায় কিংবা কারও ধর্মস্থান ভেঙে মসজিদ নির্মাণের কথা ভাবাই সম্ভব ছিল না। কারণ,ইসলামে এই কাজটা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তবুও কোনও বিকারগ্রস্ত নামধারী মুসলিম শাসক যদি এ কাজ করেও থাকেন, তাহলে যত বিলম্বেই হােক মুসলমানরা সেই ভুল শুধরে নিতে সম্মত হবেই।
কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বাবরের অন্যতম সেনাধ্যক্ষ মীর বাকি মসজিদ নির্মাণের জন্য কারও জমি জবর দখল করতে যাবেন কেন? তখনকার নিয়ম অনুযায়ী যিনি বিজয়ী হিসেবে শাসকের সিংহাসনে বসতেন দেশের সমস্ত জমির মালিকানা তাে তার উপরই বর্তাতাে। তিনি বরং অন্যদের জমি দান করবেন। অন্যের জমি দখল করতে যাবেন কোন দুঃখে!তাও আবার মসজিদ নির্মাণের জন্য। মীর বাকি রামমন্দিরই বা ভাঙতে যাবেন কেন? মন্দিরে অঢেল ধনসম্পদ সঞ্চিত থাকলে অবশ্য অন্য কথা। কিন্তু সেই লােভে তিনি শুধু মন্দিরটাই ভাঙবেন। সেখানে কিছুতেই মসজিদ নির্মাণের কথা ভাববেন না। জোর করে দখল করা স্থানে গড়ে ওঠা মসজিদে নামাজ পড়া ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। সুতরাং কোন মুসলিমের পক্ষে জবরদলকৃত জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা সম্ভব নয়। হয়ত কোনও মন্দিরের ধ্বংসস্তুপ হিসেবে ওই বিতর্কিত জমিটা পড়ে ছিল বহুকাল। দেশের নতুন শাসক হিসেবে বাদশাহ বাবরের সম্মতি ক্রমে ওই জমিতে মসজিদ নির্মাণ এবং জমির বাকি অংশকে কবরস্থান হিসেবে ব্যবহার করার অনুমতি মীর বাকি দিতেই পারেন।
আর এম ইটন উল্লিখিত বিবরণ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, তুর্কি মুসলমান শাসকদের ভারতে আসার আগে থেকেই হিন্দু মন্দিরগুলি হিন্দুরাজাদের রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যার ফলে অগণিত দেবমূর্তি ও মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। তাই যারা ভাবেন, তুর্কি আক্রমণকারীরা ভারতে তাদের রাজ্য বিস্তারের জন্য প্রথম মন্দির ধ্বংস প্রথা চালু করেন, তাদের ভাবনা মােটেই ইতিহাসসম্মত নয়। সুলতানী শাসনকালে লিপিবদ্ধ না হওয়ায় মন্দির কলুষিত ও ধ্বংসের ঘটনার প্রকৃত সংখ্যা জানা যায় না। তবে বিখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক রিচার্ড এম ইটনের অন্য এক লেখায়৬ জানা গেছে, পাঁচ শতাব্দীর বেশী সময়ে (১১৯২-১৭২৯) আশিটি মন্দির মুসলিম সুলতানদের দ্বারা কলঙ্কিত বা বিধ্বস্ত হওয়ার প্রামাণ্য ঐতিহাসিক বিবরণী পাওয়া যায়। হিন্দুত্ববাদীদের মতে, এই সংখ্যা প্রায় ৬০,০০০ এর মত!! অধ্যাপক ইটনের তালিকায় দিল্লির তুর্ক-আফগান শাসকদের রাজ্য বিস্তারের ২০০ বছরের (১১৯২-১৩৯৪) ইতিহাসে মন্দির ধ্বংস করার ২৪টি ঘটনার বিবরণ উল্লিখিত রয়েছে যা শুরু হয়েছিল ১১৯৩ সালে মহম্মদ ঘােরী কর্তৃক আজমীরে পরাজিত রাজপুত রাজার রাজকীয় মন্দির লুণ্ঠনের মাধ্যমে। পরবর্তী ২০০ বছরের পরিধিতে (১৩৯৪-১৬০০) অধ্যাপক ইটন শত্রু রাজাদের মন্দির ধ্বংসের ঘটনার ইতিহাস তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালিয়ে ৩১ টি মন্দির বিধ্বস্ত করার তালিকা প্রস্তুত করেছেন।
দিল্লির সুলতানরা হিন্দুরাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে রাজ্য বিস্তার করেছিলেন বলেই ভারতীয় প্রথা বা ঐতিহ্য অনুযায়ী তারা বিভিন্ন মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তার বা প্রতিষ্ঠার সময় মুঘল সম্রাট বাবর, হুমায়ুন, আকবর (১৫২৬-১৬০৫) মূলত আফগান সুলতানদের পরাজিত করে গদিয়ান হয়েছিলেন বলেই এই তিন মুঘল সম্রাট হিন্দু মন্দিরের ধ্বংস ঘটাননি—এটাই প্রামাণ্য ইতিহাসে পাওয়া যায়। বাবরের নির্দেশে বাবরি মসজিদ গড়ার (অযােধ্যার প্রাচীন রামমন্দির ধ্বংস করে) সাম্প্রদায়িক কল্প কাহিনী ভিত্তিহীন হিন্দুত্ববাদী প্রচার। আজ পর্যন্ত প্রামাণ্য ঐতিহাসিক গবেষণায় কোথাও পাওয়া যায় না যে, বাবর কোনও মন্দির ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ তৈরী করেছিলেন। দুই ব্রিটিশ ঐতিহাসিক উইলিয়াম রাসব্রুক ও স্ট্যানলি লেনপুল বাবরের যে দুটি প্রামাণ্য জীবনী রচনা করেছেন, তাতে বাবর কর্তৃক মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়ার কোনও বর্ণনা নেই আর রামমন্দির তাে দূরস্থান! যেটা প্রথমেই বলা হয়েছে। আকবর-পরবর্তীকালে মুঘল বাদশাহরা পূর্বতন সুলতানী সাম্রাজ্যের বাইরে গিয়ে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে গেলে হিন্দু রাজাদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। তার ফলে মন্দির ধ্বংসের ঘটনা আবার ঘটতে থাকে। এইভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণকালে ও আঠারাে শতকের সঙ্কটের সময়ে ১৬০০ থেকে ১৭৬০ সাল পর্যন্ত। মুঘলদের বিনষ্ট করা ২৫টি মন্দির গবেষক ইটনের মন্দির ধ্বংসের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
তুর্ক-আফগান সুলতানরা ও পরবর্তীকালে বাদশাহরা ভারতীয় মুসলিম রাষ্ট্র দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার পর মন্দির ধ্বংস নয়, বাস্তবত হিন্দুমন্দির রক্ষণাবেক্ষণ ও নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। গজনীর মাহমুদকে হিন্দু মন্দির লুণ্ঠনকারী হিসেবে চিত্রিত করা হলেও, পারস্যের নবজাগরণের অন্যতম প্রতিনিধির মর্যাদাতেই তিনি পন্ডিতদের বসবাসের জন্য এক আবাসকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ‘তুজুক-ই-ফাহানগিরিতে’ বলা হয়েছে, “হিন্দুদের উপর ইসলাম চাপিয়ে দেবার জন্য উলেমাদের পরামর্শ ইলতুৎমিস গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন।” শেরশাহ পর্যন্ত ঐ অভিমত বলবৎ ছিল। ফিরােজ শাহ তুঘলক মুসলিম কট্টরবাদীদের হাত থেকে এক হিন্দু ফার্সিনবিশের জীবন রক্ষা করেছিলেন। ফিরােজ শাহ তুঘলক ও সেকেন্দার লােদির সময়ে বহু সংস্কৃত কাব্যের ফার্সি অনুবাদ করানাে হয়।
অ-মুসলমানদের নিয়মমাফিক পুজো করার প্রচুর স্বাধীনতা ছিল এবং তাদের মন্দিরগুলিও পুরানাে পবিত্রতা ধরে রেখেছিল। বেরিলি থেকে মথুরা যাওয়ার পথের এক শহরে কানিংহাম লক্ষ্য করেন, এক পুরানাে মন্দির যেটা ১০০০ সালের পরে তৈরি হয়নি এবং যার তীর্থযাত্রীদের তারিখ দেওয়া দলিল আছে এবং তিনি ১২৪১-১২৯০ সালের মধ্যে কম করে পনেরােটা শিলালেখ পেয়েছিলেন।৭ নতুন মন্দির নির্মাণেও স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। দিল্লির পুরানাে কেল্লায় প্রাপ্ত এবং পারসিক ও সংস্কৃতে লেখা একটি শিলালিপির ভগ্নাংশ নির্মিত মন্দিরের ভরণপােষণের জন্য বার বিঘা জমি দেবার কথা নথিভুক্ত করেছে। মন্দিরটি শ্রীকৃষ্ণকে উৎসর্গ করা হয়েছিল।৮ আরও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ফিরােজ তুঘলকের সময়ে যেখানে দিল্লিতে তাঁর পূর্বসূরিদের সময়ে তৈরি নতুন মন্দিরগুলির কথা বলা হয়েছে। “হিন্দুরা ও মূর্তি পূজাকারীরা …নতুন মন্দিরগুলি শহরে ও চারপাশে তৈরি করেছে।” “মালিয়া গ্রামে একটি পুষ্করিণী আছে যেখানে ওরা মূর্তি পূজার মন্দির তৈরি করেছে এবং বিশেষ কয়েকটি দিনে হিন্দুরা ওখানে ঘােড়ায় চড়ে অস্ত্র নিয়ে যেতে অভ্যস্ত …ওরা হাজারে হাজারে সমবেত হয় এবং মূর্তিপূজা করে।”৯ ফিরােজ তুঘলক স্বীকার করেছেন যে ঐ ধরনের মূর্তির আবাস সালিহপুর এবং কোহনা গ্রামে তৈরি করা হয়েছে ও পূজা নিয়মিত করা হচ্ছে। এটাতে জৈনদের তিনটি মূর্তি পাওয়া গিয়েছে যাদের প্রতিষ্ঠা তারিখ দেওয়া হয়েছে বিক্রম সংবৎ ১৩৩৫/১২৭৮ সাল।১০ ফিরােজ খলজীর যে স্বীকৃতি নীচে দেওয়া হল সেটা স্পষ্ট প্রমাণ করবে যে এমনকি রাজধানীতেও হিন্দুরা ধর্মীয় স্বাধীনতা ভােগ করত। “প্রতিদিন হিন্দুরা ..আমার প্রাসাদের নীচ দিয়ে যায় শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়ে যমুনার পাড়ে মূর্তিপূজা করার জন্য …আমার নাম যখন খুৎবাতে পড়া হচ্ছে ইসলামের রক্ষক বলে, ভগবান ও তার নবীর এই শত্রুরা আমার চোখের সামনে গৌরবের সঙ্গে তাদের ধনদৌলত প্রদর্শন করছে এবং আমার রাজধানীর মুসলিমদের মধ্যে বিত্ত নিয়ে বাস করছে। তারা ঢােলক ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজায় এবং তাদের হিন্দু আচার চালিয়ে যায়।”১১
কাশ্মীরের শাসক জয়নাল আবেদিন হিন্দুদের মন্দির নির্মাণ করেন, হিন্দু উৎসবে যােগদান ও গােহত্যার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। সুলতানশাহীকালে হিন্দুদের বসন্ত, হােলি ও দীপাবলি উৎসবে মুসলিম রাজন্যরা যােগ দিতেন। একটি সংস্কৃত শিলালিপিতে দেখা যায়, মহম্মদ বিন তুঘলক ১৩২৬ সালে বিদার জেলার মঙ্গলার্থে একটি বিখ্যাত শিবমন্দির সংস্কারের জন্য রাজকোষ থেকে প্রচুর অর্থ মঞ্জুর করে এক পদস্থ মুসলিম কর্মচারীকে দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। ইবন বতুতার বিবরণে পাওয়া যায় (দিল্লির ওরিয়েন্টাল বুকস কর্তৃক ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত এইচ এ আর গিবন অনুদিত ইবন বতুতার ‘Travels in Asia and Africa 1324-1354′), হিন্দু রাজা সুলতানকে জিজিয়া দান করলেই যে কোনও স্থানে স্বাধীনভাবে মন্দির নির্মাণ করতে পারতেন। মধ্যপ্রদেশের কতিহাগড়ে পাওয়া ১৩২৮ সালের একটি লিপি থেকে জানা যায়, মহম্মদ বিন তুঘলক একটি গাে-মঠ নির্মাণ করেছিলেন। সমসাময়িক একটি জৈন রচনা অনুযায়ী, তিনি শত্ৰুঞ্জয় মন্দির পরিদর্শন করে জৈন সংঘের একজন নেতার উপযােগী আরাধনামূলক কাজ করেন।১২ রাজকোষের আর্থিক সমৃদ্ধির জন্য কাশ্মীরের হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরগুলির দেবদেবীর সােনা রুপার নির্মিত মূর্তিগুলি গলিয়ে ফেলার পরামর্শ (এই পরামর্শ দিয়েছিলেন সুলতানের হিন্দু ব্রাহ্মণ মন্ত্রী) দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখান করে কাশ্মীরের সুলতান শিহাব-অল-দিন (রাজত্বকাল ১৩৫৫-১৩৭৩)। মন্দিরগুলি উপযুক্তভাবে সুরক্ষিত করার নির্দেশনামাও জারি করেছিলেন তিনি।
মুলতানে প্রসিদ্ধ আদিত্য মন্দির ধ্বংস হলে ‘কুয়ামিতা’ বংশীয় মুসলমান শাসকরা তা পুননির্মাণ করেন। অথচ মুলতান তখন ‘কুব্বাতুল ইসলাম’ অথাৎ ‘ডােম অফ ইসলাম’ নামে অভিহিত ছিল। মুলতানে মুসলমানেরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। বিস্ময়ের ঘটনা, ফিরােজ তুঘলকও যে দিল্লীর সন্নিকটবর্তী অঞ্চলে কয়েকটি নতুন মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, সেতথ্যও আজ ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে স্বীকৃত। রাজধানী দিল্লীতে যে হিন্দুরা ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে পূজা-অর্চনা করতেন, তা জালালউদ্দিন খলজীর বক্তব্যেই পাওয়া যায়।
(৯)
আর মুঘল সম্রাটরা রাজত্বের শুরু থেকেই তাদের সাম্রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত হিন্দু মন্দিরকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করতেন যার সুরক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। তারা এমনকি মন্দিরের পুরােহিতের ভরণপােষণ ও নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠায় পৃষ্ঠপােষকতাও করেছেন। তাদের প্রতিষ্ঠিত গােবিন্দ দাস মন্দির তার উজ্জ্বল উদাহরণ। পরবর্তীকালে জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের ও রথযাত্রা উৎসবের দেখাশােনার কাজে বিশেষভাবে নিযুক্ত ছিলেন মুঘল সম্রাটের প্রতিনিধি হিসেবে ওড়িশার মনসবদার। পুরীর মন্দিরের পুরােহিতরা মুঘল শাসকদের পুরীর মন্দির ও জগন্নাথদেবের মূর্তির রক্ষক হিসেবে গণ্য করতেন—ঔরঙ্গজেবের শাসনকালেও এটা লক্ষ্য করা গেছে। ড. বি.এন. পান্ডে তাঁর গবেষণামূলক রচনা ‘ইসলাম অ্যান্ড ইন্ডিয়ান কালচার’ গ্রন্থে বহু তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যে, ঔরঙ্গজেব মােটেই হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন না। অপ্রিয় কাজ তিনি করতে বাধ্য হয়েছেন আইন-শৃঙ্খলগত কারণে, কারও প্রতি বিদ্বেষবশত নয়। প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌম শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করলে, ঔরঙ্গজেব কেন, কোনও কালেই কোনও শক্তিই মন্দির বা মসজিদ ধ্বংস করতে কুণ্ঠিত হয় না।
প্রাচীন বা মধ্যযুগে ঘটে যাওয়া এমন ঘটনার মীমাংসা খুঁজতে যাওয়া আধুনিক যুগে অসম্ভব—ভারতের দীর্ঘ বিচিত্র ইতিহাসে অঘটনের কোনও শেষ নেই, কোন সম্প্রদায়ের উপর কবে কে অত্যাচার করেছে, এই চাপানউতােরের শেষ খুঁজে পাওয়া ভার। রক্তাক্ত ইতিহাস নিয়ে টানাটানি করে সংশােধনের চক্রব্যুহে ঢােকা বােকামি ছাড়া কিছু নয়। খেয়াল রাখতে হবে উত্তর ভারতের অযােধ্যাসহ আশেপাশের এলাকায় একসময় বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল দাপট ছিল। বৌদ্ধরা হিন্দু পুরাণকথা এবং দেবদেবী মানত না। তবে মহাযান বৌদ্ধদের প্রচুর সংখ্যক দেবদেবী ছিল। এইসব দেবদেবীর মূর্তি ও মন্দিরও ছিল। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ সাক্ষ্য দেয় একসময় বৌদ্ধরা ভারতভূখণ্ডের বেশিরভাগ জায়গা থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু শাসকদের দ্বারা বিতাড়িত হয়েছিল। তখন মহাযান বৌদ্ধদের মন্দির এবং দেবদেবীদের হিন্দুকরণ ঘটিয়ে ফেলা হয়। সেই কারণেই মাটির তলায় খনন কার্য চালিয়ে ঐতিহাসিক নিদর্শন খুঁজতে গেলে যেসব প্রত্নতাত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায় সেগুলির সবই হিন্দু নিদর্শন হবে এমন কোনও গ্যারান্টি নেই।
অবশ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিত্তিতে কোন বিশেষ ভূমিখণ্ডকে কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায় নিজেদের বলে দাবি করতেই পারে। কিন্তু সেই দাবি আদালতে গ্রাহ্য হলে দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে বাধ্য। তেমনটা ঘটলে শুধু বৌদ্ধরা কেন, সাঁওতাল, কোল, ভিল, মুণ্ডা ইত্যাদি আদিবাসীরাও এমন অনেক ধর্মস্থানকেই তাদের বলে দাবি করে বসতে পারে, যেগুলি বাস্তবে এখন তাদের নয়। এরকম সম্ভাবনাকে কাল্পনিক মনে করার কোনও কারণ নেই। ভারতের এমন কিছু কিছু ধর্মস্থান আছে যেগুলি প্রকৃত মালিকদের হাত থেকে কার্যত জবর দখল হয়ে গেছে বলে বিশেষ করে সাঁওতাল আদিবাসী এবং বৌদ্ধরা দাবি করে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, সাঁওতালদেরও পুরাণকথা এবং দেবদেবী হিন্দু পুরাণকথা এবং দেবদেবীদের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা। প্রাচীন ভারতে একদা অপেক্ষাকৃত উন্নত সংস্কৃতির উদগাতা সাঁওতালরা আর যাই হােক, হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুরাগী নয় মােটেই। কিন্তু তাই বলে তারা যদি দাবি করে পাহাড় পর্বত এবং অরণ্যের গহন এলাকায় তাদের কোনও কোনও ধর্মস্থান হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদীরা জবরদখন করে মন্দির বানিয়ে ফেলেছে, এখন সেই ধর্মস্থান তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হােক, তাহলে তেমন দাবি কি মেনে নেওয়া সম্ভব হবে? ভারতভূমিতে সাঁওতালরা এখন প্রান্তিক মানুষ বলে যদি এরকম দাবি করেও সেটাকে আমলই দেওয়া হবে না। যে মথুরা নিয়ে এত হইচই, সেখানে তাে বৌদ্ধদের উৎখাত করেই ব্রাক্ষ্মণ্য সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।১৩ পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের নীচে বৌদ্ধ স্কুপ থাকার সম্ভাবনা নিয়ে অনেকেই আলােচনা করেছেন। বিবেকানন্দ এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন, “ভারতবর্ষের এই যে সব সন্ন্যাসীর মঠ-ফঠ দেখতে পাচ্ছিস তা বৌদ্ধদের অধিকারে ছিল। হিন্দুরা সেই সকলকে তাদের রঙে রাঙিয়ে নিজস্ব করে বসেছে।..প্ররীর জগন্নাথ মন্দির আসলে ছিল বৌদ্ধমঠ।”১৪ এখন বৌদ্ধরা যদি পুরীতে উৎখননের দাবি তােলেন এবং আদালতের নির্দেশে ভারতীয় প্রত্নতাত্বিক বিভাগ সেখানে ভুল করেও বৌদ্ধ স্থাপত্যের দু-একটি টুকরাে পেয়ে যায়, তাহলে কি সেক্ষেত্রে বৌদ্ধদের প্রাধান্য মেনে নেওয়া হবে? পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া থেকে শুরু করে বাঁকুড়া হয়ে বর্ধমান পর্যন্ত বিস্তৃত জৈন সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলি পরবর্তীকালে অনেকক্ষেত্রেই শৈবকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সে সব আবার গুণে গুণে জৈনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে?১৫
এমন বহু ঘটনা ইতিহাসের সাক্ষ্যবাহী। তাছাড়া অযােধ্যার ইতিহাস দেখলে দেখা যাবে যে, অযােধ্যা বিভিন্ন যুগে নানা ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের কাছে পুণ্যভূমি বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে, বিশেষভাবে কোনও একক সম্প্রদায়ের নয়। যেটা পূর্বেই বলা হয়েছে। হিঙয়েন সাঙের সময় তাে অযােধ্যায় শতাধিক বৌদ্ধ মঠ ছিল। হিন্দু মন্দির ছিল দশটি। এখন হিন্দু মন্দিরগুলির অস্তিত্ব তাে বিদ্যমান, কিন্তু বৌদ্ধ মঠগুলি গেল কোথায়? সেগুলি কি জরাজীর্ণ হয়ে ধ্বংসাবশেষে পরিণত হল? না সেগুলি ধ্বংস করা হয়েছে? এক্ষেত্রে তাহলে আমরা কি সিদ্ধান্ত নেব? ইতিহাস কি আমাদের অতীতের পুননির্মাণের অধিকার দেয়? আমরা তাে আর অত্যাধুনিক এই কলকাতার পরিবর্তে সুতানুটি-গােবিন্দপুর ফিরে পেতে চাইব না। সমস্ত ধ্বংসের পর যেটা নবনির্মিত হয়েছে, সেটাকে মান্যতা দেওয়াই তাে সভ্যতা।
কিন্তু একদা যদি কখনও প্রমাণিত হয় যে, অযােধ্যার ধর্মস্থানটি আগে হিন্দুদেরই ছিল। এবং সেটি ভেঙেই বাবর ওই মসজিদ বানিয়েছেন। হতেও বা পারে। কারণ, মুঘল আমলে বহু কিছু প্রাচীন স্থাপত্য দখল হয়েছে, যেমন তারও আগে হিন্দু আগ্রাসনে বহু বৌদ্ধ স্থাপত্য দখল হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে—এগুলি তাে সব ইতিহাসেই বলা আছে। যেটা পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু তার সত্যটি আসলে কি—তা নির্ধারণে তাে নির্মোহ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও নির্মোহ বিচার প্রয়ােজন। তার সঙ্গে বিশ্বাসবাদের কোনও সম্পর্ক নেই।
তার চেয়েও বড় কথা হল, ৫০০ বছর আগেকার স্থান-কাল-পাত্র আর আজকের ভারত কি এক? অভিন্ন ভারত রাষ্ট্র বলে কিছু ছিল না তখন। তখনকার কৃতকর্মের দায় বর্তমান প্রজন্ম নেবে কেন? বা নিতে যাবে কেন? আর সেই সময়কার কোনও ঘটনার বিচার স্বাধীন ভারতের কোর্ট করবে কিসের ভিত্তিতে? দেশে কি ওই অযােধ্যায় ধর্মস্থানটির ২.৭৭ একর ছাড়া বা তার সংলগ্ন ৬৭ একর জমি খণ্ডটি ছাড়া আর মন্দির নেই? না, আরেকটি নতুন মন্দির নির্মাণের কোনও স্থান নেই? নতুন ভারতকে জটিল ভাবাবেগে অশান্ত করা ছাড়া সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের মানে কি?
তথ্যসূত্রঃ
১. দ্য ইন্ডিয়ান রিভিউ, আগস্ট ১৯২৯, পৃ. ৪৯৯।
২. সুজিৎ চৌধুরী, রামজন্মভূমির পুরাতত্ত্ব, আজকাল, ২ এপ্রিল ২০০২, কলকাতা।
৩. নিরঞ্জন হালদার, বিজেপি কী বলছে?’, ১৯৮৯, কলকাতা।
৪. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস-আদিপর্ব, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩,পৃ. ৫০৬।
৫. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৫-৫০৬।
৬. R M Eaton, “Temple desecration in pre-modern India, Forntline : 22 December, 2000 & 5 January, 2001.
৭. কানিংহাম রিপাের্টস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০৬।
৮. রিপাের্টস অফ দ্য আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, ১৯০৯-১০, পৃ. ১৩১।
৯. এ বি এম হাবিবুল্লাহ, ফাউন্ডেশন অফ মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া, ওরিয়েন্টাল বুক ডিপাে, এলাহাবাদ, ১৯৭৬, পৃ. ২৭৩-২৭৪। ১০. রিপাের্টস অফ দ্যা আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, ১৯২৩-২৪, পৃ. ৯২।
১১. এ বি এম হাবিবুল্লাহ, ফাউন্ডেশান অফ মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া, ৩য় সংস্করণ, ওরিয়েন্টাল বুক ডিপাে, এলাহাবাদ, ১৯৭৬, পৃ. ২৭৪।
১২. দ্রঃ- হীরালাল, ডেসক্রিপ্টিভ লিস্টস অফ ইনক্রিপশনস ইন সেন্ট্রাল প্রভিনসেস অ্যান্ড বেরার, নাগপুর, ১৯১৬, পৃ. ৫০।
১৩. ইন্দ্রজিৎ চৌধুরি, প্রত্নতত্ত্বও যখন রাজনীতির হাতিয়ার, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০-০৯-২০০৩, কলকাতা। ১৪. বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নবম খন্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ২৮।
১৫. ইন্দ্রজিৎ চৌধুরি, প্রাগুক্ত, কলকাতা।

 নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা
নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা