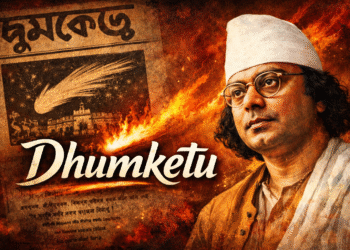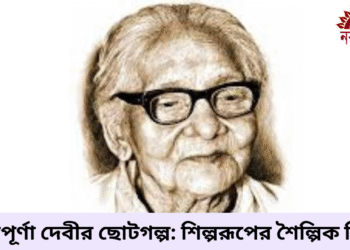লিখেছেনঃ আবদুস সাত্তার
আধুনিক আরবী সাহিত্যে বিদেশী শব্দ বিশেষ করে ফরাসী শব্দ ব্যবহার শুরু করলেন এভাবে। ফরাসী শব্দের ব্যবহারে ঘোর আপত্তি তুললেন আধুনিক আরবী সাহিত্যের প্রথম সারির অন্যতম রূপকার ডক্টর তাহা হোসাইন। যদিও তিনি ফরাসী মহিলা বিয়ে করেছিলেন তথাপি তিনি আরবী সাহিত্যে ফরাসী শব্দের ব্যবহার পদ্ধতিকে তুলনা করলেন সুন্দরী নারী দেহে ক্ষতচিহ্ন স্বরূপ। তখন মিশরের ‘আল হেলাল’ পত্রিকার জাঁদরেল সম্পাদক জুরজী জায়দান ডক্টর তাহা হোসাইনের এই যুক্তি খণ্ডন করলেন এই বলে যে, মিশরীয় সামাজিক তথা দৈনন্দিন জীবনে যে সব ফরাসী শব্দ পরিচিত এবং ব্যবহৃত হয়ে আসছে সে সব সাহিত্যে ব্যবহার করলে দোষের কিছু নেই। অনেকেই জুরজী জায়দানকে সমর্থন করলেন এবং এ ব্যাপারে ‘আল হেলাল’ পত্রিকায় সম্পাদকীয় নিবন্ধও প্রকাশিত হলো। তাদের যুক্তির সঙ্গে আরও যুক্ত ছিল, আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা যদি সাহিত্যে দেখা দিতে পারে তবে বিদেশী বহুল প্রচলিত এবং জানা শব্দ ব্যবহারে আপত্তি থাকার কথা নয়। বলা যায়, এই সময়ে আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করার পক্ষপাতিত্ব নিয়ে এগিয়ে আসেন মাহমুদ তাইমুর আহমুদ তাইমুর প্রমুখ খ্যাতিমান আরবী কথা শিল্পীগণ। বাংলা সাহিত্যের বেলায়ও জুরজী জায়দানকে সমর্থন করে, বলা যায়, কাজী নজরুল ইসলামও কেবল সেইসব শব্দই ব্যবহার করেছেন যে গুলো আমাদের কাছে খুবই পরিচিত এবং আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।
এখানে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ না করে পারছি না। অষ্টম শতাব্দীতে যখন আরব শাসক সুলতান মাহমুদ ইরান দখল করেন তখন ইরানীরা ইসলাম গ্রহণ করেন বটে তবে তাদের সাংস্কৃতিক ধারা অব্যাহত রয়ে যায়। আস্তে আস্তে ইরানীদের প্রাচীন ভাষা পাহলবী ‘দারী’ বা আধুনিক ফারসী ভাষায় রূপ লাভ করে। এমনকী পাহলবী ভাষার হরফ আরবী হরফে পরিবর্তন করা হয় এবং ইরানীদের আলাদা সম্মান প্রদর্শনের জন্য আরবীর চেয়ে বাড়তি আরও চারটি হরফ ফারসী ভাষায় সংযোজন করা হয় যেমন টে, পে, ঢে, ইয়ে ইত্যাদি। কিছু সংখ্যক ইরানী এসব মনে প্রাণে গ্রহণ করলেও অনেকে ভিতরে ভিতরে প্রতিবাদে মুখর হয়। কিন্তু রাজশক্তির কাছে তারা মাথা তুলে দাঁড়াতে সমর্থ হয়নি। আরও প্রতিবাদের শিকার হতে হয় যখন ফেরদৌসীর মতো কবিরা আধুনিক ফারসী সাহিত্যে আরবী শব্দের প্রচলন ঘটাতে শুরু করেন। ফেরদৌসীর মতো অন্যান্যরাও যখন একই পথ অবলম্বন করেন। তখন এই পদ্ধতি সহনীয় হয়ে ওঠে। অবশ্যি সাহিত্যের এই নব দিগন্তের সূচনায় রাজশক্তির ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জানা গেছে, সুলতান মাহমুদ সাহিত্য ও শিল্পের খুবই সমঝদার ছিলেন এবং তার রাজদরবারে পণ্ডিত, দার্শনিক, সঙ্গীতজ্ঞ ছাড়াও কেবল কবিদের সংখ্যাই ছিল চারশত।

ফারসী সাহিত্যের সূচনা পর্বের ফেরদৌসী থেকে শুরু করে রুমী, জামী, খৈয়াম, আনওয়ারী নিজামী, সাদী, হাফিজ, আত্তার, আমির খসরু, জেবুন্নেসা পর্যন্ত এবং তাদের পরবর্তী কবিদের থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর আধুনিক সময়ের কবি সাহিত্যিকরাও তাদের কাব্য কর্ম এবং সাহিত্য কর্মে অবলীলা ক্রমে আরবী শব্দ ব্যবহার করেছেন। এবং এ জন্য ফারসী সাহিত্যে যত আরবী শব্দের প্রয়োগী রীতি লক্ষ্য করা যায় অন্য কোনো ভাষায় এতটা লক্ষ্য করা যায় না। একমাত্র নজরুল ইসলামই বাংলা সাহিত্যে ব্যতিক্রমধর্মী কাজ করেছেন। ফারসী কবিদের মতো আরবী শব্দের প্রয়োগ করে তিনি বাংলা সাহিত্যের বাগানে বসরার গোলাপ ফুটিয়েছেন, সু-ঘ্রাণে মাতোয়ারা করেছেন এবং সাহিত্যের গলায় পরিয়েছেন জহরতের মালা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, প্রখ্যাত ফারসী কবি এবং সঙ্গীত জগতের ম্রাট আমির খসরু দেহলবী ফারসী সাহিত্যে প্রথম সারির কবিদের অন্যতম কবি। ফারসী ভাষা ছাড়া তিনি উর্দু ও হিন্দী ভাষায়ও প্রচুর কবিতা লিখেছেন। হিন্দী ভাষায় কবিতা লিখতে গিয়ে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে হিন্দী কবিতার শরীরে আরবী-ফারসীর জরির ঝলমলে শব্দে পোশাক পরিয়ে সুদৃশ্য ও আকর্ষনীয় করে তোলেন। তাঁর কবিতার কিছু অংশের উদ্ধৃতি দিচ্ছি,
হিন্দু বাচ্চেরা বনিগর আজব হসন ধরতা হ্যায়,
দর অক্তে সুমন গুফতন মুহফুল ঝরতা হ্যায়,
গুফতম বিয়াকে বর লবে তু বুসে বগীরম
গুফতে আরে রাম ধরম নষ্ট করতা হ্যায়।
[আশ্চর্য সুন্দর রূপ ধরেছে ও হিন্দু শিশুগণ
প্রতিটি মুহূর্তে যেন কথায় সে ফুল ঝরে শুধু
মন বলে, ‘চুমো দিই আশ্চর্য ফুলের সমারোহে।
ওরা বলে, আরে রাম! ধর্ম নষ্ট হয়েছে এবার]’
উপরের হিন্দী কবিতার চার লাইনের স্তবকে ‘আজব’ (আশ্চর্য), ‘হুসন’ (সুর), “অ’ (সময়) ইত্যাদি আরবী শব্দ এবং ‘গুফতন’ ‘গুফতম’ ‘গুফতে (মূল ‘গুফত’ থেকে যার অর্থ কথা, বলা ইত্যাদি), দর’ (প্রতি) ইত্যাদি ফারসী শব্দ। বলা আবশ্যক কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনার ঝড় ওঠে এবং কিছু সংখ্যক পাঠক-পাঠিকা এর সমর্থনে উচ্চকণ্ঠ হন এবং কিছু সংখ্যক পাঠক-পাঠিকা প্রতিবাদী কণ্ঠে সোচ্চার হয়ে বলেন, আরে রাম! রাম! আমাদের ধর্ম নষ্ট হয়েছে।’
সত্য কথা চিরদিনই সত্য। সত্য কথা কোন ধর্মকে কোনোদিন নষ্ট করতে পারে। আমির খসরু রচিত বহু হিন্দী গজল আছে, যে সব গজলের প্রাণ শক্তিকে সঞ্জীবিত রেখেছে প্রচুর আরবী-ফারসী উর্দু শব্দ। বলা যায়, কাজী নজরুল ইসলামও বাংলা সাহিত্যে আরবী ফারসী-উর্দু শব্দ ব্যবহার করে আমির খসরু দেহলভীর মতো সমালোচনার কাঠগড়ায় দাড়িয়ে ছিলেন কিন্তু বৃহৎ জনগোষ্ঠীর রায়ে তিনি বিজয়ীবাংলা সাহিত্যের ধর্ম নষ্ট করেননি। বরং আমরা এই নব পর্যায়কে অভিনন্দন জানিয়ে ‘বুসা’ বা চুমো দিতেই আগ্রহী।
ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নজরুল সাহিত্যে যেসব ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্যে শতকরা ৬০% ভাগ আরবী শব্দ। আরবী শব্দের ‘মাদ্দাহ’ বা মূল অন্বেষণ না করে, অবশ্যি এসবের কোনো প্রয়োজনও পড়েনি, শব্দটি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যেভাবে প্রচলিত ঠিক সেভাবেই ব্যবহার করেছেন। ব্যাকরণবিদরা শব্দের ‘তালিল’ করে নিতে পারেন। অর্থাৎ কোনটা ‘এলেম’ ‘বিশেষ্য কোনটা ফায়েল’ (কর্তা) কোনটা ম’ফোল (কর্ম) কোনটা ‘আমর’ (আদেশ), কোনটা ‘তাসনীর’ (ক্ষুদ্রায়তন) ইত্যাদি নির্ণয় করতে কোনো অসুবিধা হয় না।’
কিছু আরবী শব্দের সঙ্গে ফারসী শব্দের সমন্বয় ঘটে এক নবরূপ লাভ করেছে যেমন ‘আব-ই-হায়াত’ ‘আব-ই-কাওসার’, ‘আব-ই-জমজম’, ‘আমল নামা’, ‘কবরস্তন’, ‘কোহিনূর’ ‘খোশ খবর’, ‘খোশ নসীব’, ‘খেয়ালী’ (খেয়াল+ই), ‘গোলাম খানা’, ‘তখত তাউস’, ‘বদ নসীব’ ইত্যাদি। শব্দগুলোর অর্থ ইতিপূর্বে বলা হয়েছে বলে এখানে আর পুনরাবৃত্তি ঘটালাম না।
আরবী শব্দ এবং আরবী-ফারসী সমন্বয়জনিত কারণেই নজরুল সাহিত্যে আরবী শব্দের প্রয়োগ অধিক মাত্রায় অর্থাৎ শতকরা ৬০% ভাগ। আরও মজার কথা এই, যেসব আরবী শব্দ ফারসী সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে উর্দু কবি সাহিত্যিকরাও সে সব উর্দু সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন। একারণে নজরুল সাহিত্যে ফারসী শব্দের গড়পড়তা শতকরা ৩০% ভাগ এবং উর্দু শব্দের সংখ্যা শতকরা ১০% ভাগেরও কম।
ফারসী শব্দের ব্যাপারে আরও একটি বিষয় উল্লেখের দাবী রাখে। কিছু সংখ্যক ফারসী শব্দ আছে যেগুলো বাংলায় এসে ছোটখাট হয়েছে অর্থাৎ নিজস্ব শরীর থেকে কিছু অংশ প্রত্যাহার করে বাংলার সঙ্গে বাংলাজাত হয়েছে। অথচ ফারসী ভাষায় সেগুলো পুরোপুরিই ব্যবহৃত হয়। এ ধরণের শব্দ সংখ্যা অনেক। এখানে কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করছি যেগুলো নজরুল ইসলাম বাংলাজাত করে তার সাহিত্য-কর্মে ব্যবহার করেছেন। যেমন,
১. আন্দাজ— মূল ফারসীর পুরো শব্দ ‘আনদা তান।’ এর অর্থ নিক্ষেপ করা, মারা, খোলা, গুলি করা ইত্যাদি। বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দটির ভিন্নরূপ লক্ষ্য করবার বিষয়, যেমন ‘তীরন্দাজ’, ‘গোলন্দাজ’, ‘বরকন্দাজ’ ‘খোনান্দজ’ ইত্যাদি। ‘আন্দাজ’-এর আভিধানিক অর্থ নিরূপণ, পরিমাপ, অনুমান ইত্যাদি।
‘নাইকো পাইক’ ‘বরকন্দাজ’ নাই পুলিশের ডর। [সাম্য]
২. আলু— মূল ফারসীর পুরো শব্দ ‘আলুদান’। এর অর্থ ধারণ করা, বহন করা, আয়ত্তে রাখা ইত্যাদি। যেমন দয়ালু, দুধালো, জোরালো, নিদালু প্রভৃতিতে ‘আলু’ যুক্ত হয়ে বিশেষ্যপদ যেমন দয়া, দুধ, জোর, নিদ ইত্যাদি এক নবরূপ ধারণ করেছে এবং ‘আলুদান’ শব্দটিও লেজ বিহীন হয়ে কেবল ‘আলু’ হয়েছে। ‘আলু’ এর সাধারণ অর্থ মিষ্টি আলু, লাল আলু, গোল আলু ইত্যাদি।
৩. কার— মূল ফারসীর পুরো শব্দ ‘কারদান’। এর অর্থ ‘কারক’ (যে করে অর্থে) ধারক ইত্যাদি। নেক, বদ, জেনা, রোজ ইত্যাদি বিশেষ্য পদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রূপ লাভ করেছে নেককার, বদকার, জেনাকার, রোজকার, ইত্যাদি। বিশেষ্যপদের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় শব্দটির আদি রূপ নেই।
৪. খানা— মূল ‘খানা’। এর অর্থ স্থান, বাড়ী জায়গা, ইত্যাদি বিশেষ্যপদের সঙ্গে যুক্ত হলে এরূপ দাঁড়ায়। যেমন চিড়িয়াখানা, ডাক্তারখানা, পায়খানা, জেলখানা, কসবীখানা, দপ্তরখান, দস্তরখানা, তাড়িখানা, জিন্দানখানা, ইত্যাদি। বন্দী শামের জিন্দানখানা, হিন্দের বদখত।
৫. খোর — মূল ফারসীর পুরোশব্দ ‘খোরদান’। এর অর্থ খাওয়া, পান করা। বিশেষ্যপদের সঙ্গে যুক্ত হলে অর্থ দাঁড়ায় সেই ব্যক্তি যে খায় কিংবা পান করে। যেমন মদখোর, ঘুষখোর, হারামখোর, আদমখোর, গাঁজাখোর ইত্যাদি এবং মূলশব্দের লেজুড়ও খসে পড়ে।
‘খামখা’ তুমি মরছ কাজী ব্যস্ত তোমার শাস্ত্র ঘেঁটে,
মুক্তি পাবে মদখোরের এই আল-কিমিয়ার পাত্র চেটে!
৬. গার— মূল ফারসীর পুরো শব্দ ‘গার-ই’। এর অর্থ বৃত্তি-ব্যবসায় ইত্যাদি। বিশেষ পদের সঙ্গে যুক্ত হলে শেষের ‘ই’ বা ‘ইয়ে’ ওঠে যায় এবং শব্দ গুলো এরূপ দাঁড়ায়, যেমন যাদুগর, কারিগর ইত্যাদি। আবার এই মূল ফারসী ‘গার-ই’ বা ‘গারি’ শব্দের অপভ্রংশ ‘গিরি’ যার অর্থও বৃত্তি, ব্যবসায় বা ইংরেজীতে যাকে বলা হয় ‘প্রফেশন’। বিশেষ্য পদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এরূপ দাঁড়ায়, যেমন মুনশীগিরি, বাবুগিরি, কেরানীগিরি, মৌলবীগিরি ইত্যাদি।
৭. গো— ফারসীর পুরো শব্দ ‘গুফতান’। এর অর্থ বলা, কওয়া ইত্যাদি। বিশেষ্য পদের সঙ্গে যুক্ত হলে কেবল ‘গো’ অংশটুকু থাকে বাকী অংশ হাওয়া হয়ে যায়। যেমন ‘কানুনগো।’ সিলেটে ‘গো’ অর্থটি, টা, খানা, খানি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন দুই বন্ধুতে সিগারেট বিনিময়ের সময় বলেন, আপনার গো রাখুইন আমার গো খাইন।
৮. গির — মূল ফারসীর পুরোশব্দ ‘গিরিফতান’। এর অর্থ লওয়া, দখল করা, আয়ত্তে আনা ইত্যাদি। বিশেষ্যপদের সঙ্গে যুক্ত হলে কেবল গির টুকু থাকে বাকী অংশ অস্তহিত হয়ে যায়। যেমন আলমগীর, জাহাঙ্গীর, রাহুগীর।
৯. দান— মূল ফারসী ‘দান’। এর অর্থ শস্য কণা, খাদ্য কণা। ‘দান’ শব্দটি মূল ফারসী ‘দানিস্তান’-এরও অন্তর্গত। যখন শব্দটি কোনো বিশেষ্য পদের তখন এর অর্থ দাড়ায় জানা, বোঝা কিংবা কোনো কিছু রাখার পাত্র বা আধার। যেমন আতরদান, ছাইদান, কদরদান, পানদান ইত্যাদি।
১০. দার— মূল ফারসীর পুরো শব্দ ‘দাশতান’। এর অর্থ ধারণ করা। বিশেষ্য পদের সঙ্গে যুক্ত হলে ‘দার’ টুকুই থাকে আর সব কিছু উহ্য হয়ে যায়। অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন থানাদার, হানাদার, অংশীদার, চটকদার ইত্যাদি।
১১. পছন্দ— মূল ফারসীর পুরো শব্দ ‘পছন্দিদান’। এর অর্থ পছন্দ করা, মনোনীত করা। এই শব্দ কোনো বিশেষ্যপদের সঙ্গে যুক্ত হলে কেবল ‘পছন্দ’ টুকুই থাকে ‘দিদান’ উহ্য হয়ে যায়। অর্থ ঠিকই থাকে যেমন দিল পছন্দ, বিবি পছন্দ ইত্যাদি।
১২. পরস্ত—মূল ফারসীর পুরো শব্দ ‘পরস্তিদান’। এর অর্থ উপাসনা করা, পূজা করা ইত্যাদি। বিশেষ্য পদের সঙ্গে যুক্ত হলে ‘পরস্তিদান’ কেবল ‘পরন্ত’ হয় বোতপরন্ত, গোরপরও, বিবিপরস্ত ইত্যাদি।
১৩. পোশ— মূল ফারসীর পুরো শব্দ ‘পাশিদান’। এর অর্থ ছড়ান, বিলি করণ, ছিটানো ইত্যাদি। বিশেষ্যপদের সঙ্গে যুক্ত হলে ‘পাশিদান’ অন্যরূপ ধারণ করে কেবল পাশ হয় এবং এর অর্থ দাঁড়ায় যে বস্তু দ্বারা ছিটানো হয়। যেমন ‘গোলাপ পাশ’। সাদা মেঘের ‘গোলার পাশে ঝরিছে গোলাব পানি। [গীতি শত দল]
১৪. পোশ— মূল ফারসীর পুরো শব্দ ‘পোশিদান’। এর অর্থ পরিধান করা, আবৃত করা, ঢাকা ইত্যাদি। বিশেষ্য পদের সঙ্গে যুক্ত হলে ‘পোশিদানে’র কেবল ‘পোশ’ থাকে। তখন এর অর্থ দাঁড়ায় যে পরিধান করে কিংবা যে বস্তু দ্বারা আবৃত করা হয়। যেমন ‘বালাপোশ’, তক্তপোশ, খাঞ্চাপোশ, পাপোশ ইত্যাদি।
‘চোখের পানির ঝালর ঝুলানো হামির ‘খাঞ্চাপোশ’।
১৫. বর— মূল ফারসীর পুরো শব্দ ‘বরদান’। এর অর্থ ধারণ করা, বহন করা ইত্যাদি। বিশেষ্য পদের সঙ্গে যুক্ত হলে ‘দান’ অন্তর্হিত হয় এবং তখন অর্থ দাঁড়ায় ‘বহনকারী’, যেমন ‘রাহবর’।
১৬. বরদার—মূল ফারসীর পুরোশব্দ ‘বরদাস্তান’। এর অর্থ ধারণ করা, বহন করা ইত্যাদি। বিশেষ্য পদের সঙ্গে যুক্ত হলে বারদারই থাকে। বাকী অংশ উহ্য হয়ে যায় এবং অর্থ দাঁড়ায় ধারণকারী, বহনকারী ইত্যাদি। যেমন ‘নিশানবরদার’, হুকুমবরদার, তল্পিবরদার। আমরা ‘হুকুমবর্দার’ তার পাইয়াছি ফরমান। [নিত্য প্রবল হও]
১৭. বাজ— মূল ফারসীর পুরো শব্দ ‘বাখতান’। এর অর্থ খোলা, ভান করা ইত্যাদি। শব্দটি বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হলে ‘বাখতান’ সম্পূর্ণ আড়ালে হয়ে নতুন শব্দ ‘বাজ’-এ পরিণত হয়। তখন এর অর্থ দাঁড়ায় খেলার নায়ক কিম্বা ভানকারী। যেমন ‘চালবাজ’, ‘ধড়িবাজ’, ‘ফাঁকিবাজ’ ইত্যাদি। যে যত ভণ্ড ‘ধড়িবাজ’ আজ সেই তত বলবান। [ফরিয়াদ]
১৮. নবীশ— মূল ফারসীর পুরোশব্দ ‘নবীশতান’। এর অর্থ লেখা, নকল করা ইত্যাদি। বিশেষ্য পদের সঙ্গে যুক্ত হলে কেবল ‘নবীশ’ থাকে বাকী অংশ লোপ পায়। তখন এর অর্থ দাঁড়ায় লেখক বা নকলকারী। যেমন খানবীশ, নকলনবীশ মহানবীশ ইত্যাদি।
এমনি ধরণের উদাহরণ আরও অনেক দেওয়া যায়। আমার এইসব শব্দের উদ্ধৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, অনেক আরবী-ফারসী শব্দ বাংলার সাথে মিশ্রিত হয়ে সে সব শব্দের মূল বা ‘খাদ্দাহ্’ হারিয়ে আলাদাভাবে নতুনরূপ ধারণ করেছে উপরের শব্দসমূহ তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। কাজী নজরুল ইসলাম এইসব শব্দ সম্পর্কে ছিলেন অত্যধিক সচেতন এবং ব্যাকরণরীতি অবলম্বন করেই তিনি শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন। প্রমাণ, তাঁর কাব্যের উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট।
আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নজরুল কাব্যে উর্দুশব্দের সংখ্যা শত করা ১০% ভাগেরও কম। এর কারণ প্রধানত এইটাই যে, উর্দু সাহিত্যে আরবী ও ফারসী শব্দের প্রাচুর্য লক্ষ্য করবার মতো। ফলে উর্দু শব্দের শতকরা হার কম।
আরও বলে রাখা ভালো যে, কিছু কিছু ফারসী শব্দ মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদারূপ নিয়ে সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাংলাজাত হয়ে আছে। দু’চারটে উদাহরণ এইরূপ,
জোতদার—সংস্কৃতঃ জোএ>জোও>জোততা>জোত
+ফারসী দার’= জোতদার।
ফাঁকিবাজ— সংস্কৃত ফক্ষিকা>ফাকিয়া>ফাঁকি
+ফারসী ‘বাজ’ ফাঁকিবাজ।
গাঁজাখোর—সংস্কৃত গঞ্জিকা>গাঞ্জা>গাঁজা
+ফারসী ‘খোর’= গাঁজাখোর।
শিক্ষানবিশ—সংস্কৃত শিক্ষা+ ফারসী নবিশ=শিক্ষানবিশ।
গোলন্দাজ-সংস্কৃত গোলকা>গোলআ>গোল
+ফারসী আন্দাজ=গোলন্দাজ।
এ ধরণের শব্দও নজরুল সাহিত্যে বহু জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন,
ওরে ফাঁকিবাজ, ফেরেববাজ
আপনারে আর দিসনে লাজ
গরু ঘুষ দিয়ে চাস সওয়াব? [শহিদী ঈদ]
তিন
কাজী নজরুল ইসলাম তার সমগ্র সাহিত্যে যে সব আরবী-ফারসী-উর্দুবা অন্যান্য শব্দ ব্যবহার করেছেন সেইসব শব্দের আবর্তন-বিবর্তন এবং বাংলায়ন আমরা ইতিপূর্বে আলোচনায় লক্ষ্য করেছি। শব্দ শব্দই এবং শব্দকে আমরা মুক্তাখণ্ড, উপলখণ্ড অথবা পাথরের চকচকে নুড়ির সঙ্গে তুলনা করতে পারি। হাজার হাজার বছরের আবর্তন-বিবর্তনের স্রোতোধারার ঘর্ষণে হয়তো শব্দগুলোর গা থেকে অসমান বস্তু অন্তর্হিত হয়ে আরও চকচকে আকার ধারণ করেছে- অর্থের কোনো অসঙ্গতি ঘটে নি। ব্যাকরণবিদ বা ভাষার রূপকারদের হাতে পড়ে শব্দের সঙ্কোচন হয়তো ঘটেছে কোথাও কোথাও কিন্তু সেই শব্দের গা থেকে আসল নির্যাস বের করতে আমাদের কোনো কষ্ট হয় নি।
আমরা এবারে নজরুল ইসলাম যেসব আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দ ব্যবহার করেছেন সেই শব্দগুলো আরবী-ফারসী-উর্দু ভাষার কবি সাহিত্যিকদের হাতে কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তার একটা ছোটখাট ফিরিস্তি পেশ করছি। এখানে বলে রাখা ভালো যে, কোনো কোনো নজরুল গবেষকের মতে (ইচ্ছাকৃতভাবে নাম উল্লেখে বিরত রইলাম) নজরুল ইসলাম আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দ ব্যবহার করেছেন আরবী-ফারসী-উর্দু কবিদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে এবং নজরুল সাহিত্যেও তাদের প্রভাব বর্তমান। কথাটি যে কত অযৌক্তিক এবং ঢালাও মন্তব্যের পরিচয়বাহী তা নিম্নের উদ্ধৃতিসমূহই প্রমাণ করবে।
১ দিল (ফা’)- অন্তর, হৃদয়, প্রাণ, মন ইত্যাদি। এই ‘দিল’ কবি নজরুল ইসলাম বহু কবিতায় ব্যবহার করেছেন। একটি উদাহরণ, হায় সাহারার প্রখর তাপে/ পরান কাঁপে, ‘দিল’-কাবাব। [বুলবুল]
মওলানা রুমীর কবিতায় ‘দিল’ আছে এই ভাবে,
‘দিল’ বদস্ত আর কে হজে আকবরাস্ত
আজ হাজারা কাবা এক ‘দিল’ খোশতরান্ত।
কাবা বুনো গাহে খলিলে আজরাস্ত
‘দিল’ গুজারো গাহে জলিলে আকবরাস্ত।
[মানুষের হৃদয় জয় করা হজে আকবরী, হাজার কাবার চেয়ে একটি হৃদয় অনেক বড়। কাবা তৈরী করেছেন আজরের পুত্র ইবরাহীম খলিলুল্লাহ এবং মানুষ তৈরী করেছেন স্বয়ং আল্লাহতায়ালা, আর মানুষের হৃদয়ই আল্লাহর বিহারভূমি।]
মওলানা রুমীর আর একটি কবিতায় ‘দিল’ আছে এইভাবে,
দস্ত দর তসবীহ ওয়া ‘দিল’ দর গাউওয়া খার।
ইঁ চানিন তাসবীহ্ কে দারাদ আসার
[হাতে তাসবীহ এবং হৃদয়ে গাভী ও গাধার চিন্তা, এ ধরনের তাসবীহুতে কান আসর করতে পারে?]
কবি ইকবালের ‘দিল’ এইরূপ,
আঁ ফকর কে বে তেগে সদ্ কিশওয়ার ‘দিল’ গীরদ,
আজ শওকতে দারা বেহ আজ ফররে ফরীদুঁ বেহ।
[যে হৃদয় বিনা তরবারিতে শত শত দেশ জয় করে, সে হৃদয় দারার ঐশ্বর্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং ফরীদ বাদশাহর জাঁক জমকের চেয়েও অনেক বড়।]
আর একজন উর্দু কবি তাঁর ‘দিল’ উৎসর্গ করেছেন এই ভাবে,
ম্যায় ‘দিল’ মুরশিদ কে দিয়া নজরানা সমকার,
ঔর ইশক জ্বালায়া মুঝে পরওয়ানা সমজার।
[আমার হৃদয় আমি উপহার স্বরূপ আমার প্রভুকে দিলাম। এবং নিজে প্রেমের আগুন জ্বালালাম নিজেকে পতঙ্গ সাব্যস্ত করে।]
২. খোশবু (ফা) সুঘ্রান, সুগন্ধি। কাজী নজরুল ইসলাম এই ‘খোশবু’ ছড়িয়েছেন তার কাব্য-কর্মের সর্বত্র। একটি মাত্র উদাহরণ,
যে দেশের বাতাসে আছে নবীজির দেহের ‘খোশবু’, [জুলফিকার]
পারশ্যের বুলবুল কবি হাফিজের ‘খোশবু’ এইরূপ,
ইয়ারে আগার ইয়ারে নাদারাদ ইয়ারে হরগেজ ইয়ার নিস্ত
গুলে আগার ‘খোশবু’ নাদারাদ দিদারে কাবেল নিস্ত।
[বন্ধু যদি বন্ধুসুলভ ব্যবহার না করে তবে সে বন্ধুর অনুপযুক্ত। আর ফুলে যদি সুঘ্রাণ না থাকে তবে সে ফুল দেখারও অনুপযুক্ত।]
মহাকবি ইকবালের মাত্র এক জায়গায় ‘খোশর এরকম,
সাদকাত সাফ নেহী হো সাকতা বানাতিউ কি অসুলো সে,
‘খোশবু নেহী আ সাকতি কাগজে কে ফুলো সে।
[সত্য কোনোদিন ভাওতাবাজি দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না, কাগজের ফুল থেকে কোনোদিন সুঘ্রাণ আসে না।]
৩ ইশক (আ)— প্রেম, প্রণয়। নজরুল-সাহিত্য ‘ইশকে’ ভরা। গুলবাগিচা, থেকে মাত্র একটি লাইন, ‘হৃদয়ে লইয়া ইশক আল্লার আগে চল বাজে বিষাণ।’
কবি হাফিজের আল্লার ‘ইশক’ ছাড়া মানবতাবাদী ইশক’ এইরূপ,
চুনা কাহাত শোদ আর দামেস্ক,
কেহু ইয়ারাহ্ ফরামুশ জারদান্দ ‘ইশক’।
[দামেস্ক শহরের ভিতরে এতো যে দুর্ভিক্ষ অথচ মানুষের অন্তরে প্রেম আছে, মানবতাবোধ আছে।]
কোনো কোনো ফারসী কবিতার পেছনে সুন্দর-সুন্দর কাহিনী আছে। কবি হাফিজের এই দুই লাইন কবিতার অন্তরালেও একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী আছে। কবি হাফিজের দীওয়ানের দুটি লাইনে যেমন ‘আগার আ তুর্কে সিরাজী বদস্ত আরাদ দিলে মারা/বখালে হিন্দুয়াশ বখশাম সমরখন্দ ওয়া বোখারা’ [প্রাণ যদি মোর ফিরে দেয় সেই তুর্কী চাওয়ার মনচোরা/একটি কালো তিলের লাগি বিলিয়ে দেব সমরখন্দ ও বোখারা’- কাজী নজরুল ইসলাম অনুদিত।] খ্যাতি যখন তুঙ্গে তখন একদল লোক তখনকার দুর্ধর্ষ সম্রাট চেংগিজ খানের কাছে গিয়ে বললো, ‘হে সম্রাট, আপনি এত কষ্ট করে রাজ্য জয় করেন আর কবি হাফিজ রূপসী নারীর গালের তিলের বিনিময়ে সমরখন্দ ও বোখারার মতো সম্পদশালী রাজ্য বিলিয়ে দিচ্ছেন।’
চেংগিজ খান তো শুনে অবাক সঙ্গে সঙ্গে পাইক বরকন্দাজ পাঠালেন কবিকে ধরে আনার জন্য। কবি মেসওয়াক করতে করতে হাম্মামখানায় যাচ্ছিলেন গোসল করতে, ঠিক সেই অবস্থায়ই তাকে রাজ দরবারে হাজির করা হলো।
চেংগিজ খানের ছিল এক চীনা বেগম। তিনি ছিলেন খুব বিদুষী এবং কবি হাফিজের খুব ভক্ত। হাফিজকে এই অবস্থায় দেখে তিনি বাদশাহকে বললেন, ‘জাঁহাপনা একি করেছেন? এত বড় একজন খ্যাতিমান কবি, তাকে এ অবস্থায় হাজির করিয়েছেন? আগে তাকে পরিধানের কাপড় দিন অতঃপর কোনো অভিযোগ থাকলে বলুন।’
বাদশাহ ভাবলেন তাই তো! সম্রাজ্ঞীর কথাই ঠিক। সম্মানীয় ব্যক্তিকে অসম্মান করা অন্যায়। তাঁকে উত্তম পোশাক প্রদান করে অতঃপর বললেন, ‘কি কবি সাহেব, আমি এত কষ্ট করে রাজ্য জয় করি আর আপনি নাকি সমরখন্দ ও বোখারার মতো আমার প্রিয় রাজ্য নারীদেহের সৌন্দর্যময় তিলের বিনিময়ে বিলিয়ে দিয়েছেন?
হাফিজের জবাব, জাহাপনা, ব্যাকরণে ভুল করেছেন। আমি বিলিয়ে দিয়েছি এমন তো কোনো কথা নেই। কবিতার প্রথমইে আছে ‘আগার’ অর্থাৎ ‘দিতে পারি’ কিংবা ‘দিব’, দিয়েছি বলে তো বলা হয়নি।’
চেংগিজ খান নিজের ভুলের জন্য হেসে ফেললেন এবং বললেন, সময় উপযোগী দু’চারটে মিসরা লিখুন না?’
সঙ্গে সঙ্গে কবি হাফিজ উপরে উল্লেখিত দুটো লাইন লিখে দিলেন। বাদশাহ্ এতে খুশী হলেন এবং কবিকে পুরস্কৃত করলেন। চীনা বেগমও এতে আনন্দিত হলেন।
উল্লেখ্য, চেংগিজ খান যখন চীন দখল করেন তখন চীন রাজপরিবার থেকে উপঢৌকন হিসেবে এই মহিলাকে দেওয়া হয়েছিল।
আওরঙ্গজেব কন্যা প্রখ্যাত ফারসী মহিলা কবি জেবুন্নেসা মখফীর একটি ছত্রে ‘ইশক’ ব্যবহার করা হয়েছে এইভাবে,
দুরে আবুলাগ কাসিমে দিদ মজুদ,
মগর ‘ইশকে’ বুতানে সো মলুদ।
[চোখের পানি কি চমৎকারভাবে জমা হয়ে আছে; এসব তো চোখের পানি নয় বরং প্রেমই জমা হয়ে আছে।]
উপরের দুটো লাইনের অন্তরালেও সুন্দর কাহিনী আছে। একবার এক রাজকুমার আবেগপ্রবণ অবস্থায় আয়নায় মুখ দেখছিলেন। হঠাৎ তার চোখ থেকে এক ফোঁটা পানি আয়নায় পড়ে এবং বিস্মিত হয়ে রাজকুমারের চোখে সুদৃশ্য হয়ে ধরা পড়ে। রাজকুমার মুহূর্তের মধ্যে কবি বনে যান এবং আবেগের বশে লিখে ফেলেন ‘দুররে আবোগ কাসিমে দিদ মজুদ।’ ওই পর্যন্তই। হাজার চেষ্টা করেও মিল সহকারে দ্বিতীয় লাইন আর তিনি লিখতে পারেন নি।
কি আর করবেন? আর এক লাইন না হলে যে মিসরা হয় না-অন্ততঃ দুই লাইনের কবিতা। তিনি ওই একটি লাইন জানিয়ে দিয়ে সারা শহরময় ঢোল পিটিয়ে বলার ব্যবস্থা করলেন এই বলে যে, যিনি মিল সহকারে পরবর্তী লাইন লিখে দিতে পারবেন তাঁকে পুরস্কৃত করা হবে।
জেবুন্নেসা প্রাসাদের বারান্দায় পায়চারী করছিলেন। এমন সময় ঢোলকের দল ওখান দিয়ে যাচ্ছিল ওই লাইন নিয়ে শোরগোল করতে করতে। জেবুন্নেসা তাদের ডাকলেন এবং ব্যাপারটি জানতে পেরে ওই লাইনের সঙ্গে মিলিয়ে লিখে দিলেনঃ ‘মগর ইশকে বুতানে সো মলুদ।’
তখনকার বিচারক কবিদের রায়ে জেবুন্নেসা পুরস্কৃত হলেন এবং পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য নির্দিষ্ট দিনে তাঁকে ডাকা হলো। জেবুন্নেসা পুরস্কার আনতে আর যাননি। বরং চার লাইন কবিতা লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যেমন,
দর সুখন মখফী আম সো
বুয়ে দর বরগ-এ গুল,
হরকে দিদান মায়েল দারাদ
দর সুখন বিনাদ মারা।
[আমি তো লুকিয়ে আছি আমার এ কাব্যের ভিতরে, যেমন লুকিয়ে থাকে সুঘ্রাণ সে গুলাবের মাঝে, গুলাব নির্যাস যদি পাবার কামনা কেউ করে সে যেন আমার কাব্য আত্মার আকুতি দিয়ে পড়ে।]
কবি ইকবাল ‘ইশক’ নিয়ে ‘শিকওয়াহ’ করেছেন এইভাবেঃ
ইশক কো, ইক কী আশিফতা-সরী কো ছোড়া?
রসমে সলমান ও উবায়সে করনী কো ছোড়া?
[প্রেম, প্রেম-আচরণ এবং প্রেমের মত্ততা কি ছেড়ে দিয়েছি। ছেড়ে দিয়েছি কি সোলমান ও ওয়ায়েসকরনীর সেই প্রেমের রীতিনীতি?]
উপমহাদেশ খ্যাত ফারসী ও উর্দু কবি গালিব এর ‘ইশক’ একটু ভিন্ন স্বাদের?
ইশক মুঝকো নেহী, ওহশাত-ই সহী,
মেরী ওহশাত, তেরী শোহরত ই সহী।
মগর কাতায়া না কি জিয়ে তাল্লুক হম সে
কুছ নেহী তো ওহশাত-ই সহী।
(আমার প্রেম না থাক, যন্ত্রণাই যথেষ্ট; আমার যন্ত্রণা, তোমার খ্যাতিই যথেষ্ট; তথাপি আমাকে বিচ্ছিন্ন করো না তুমি। কিছুই না থাক, আমার যন্ত্রণাই যথেষ্ট।]
৪. বুলবুল (কা) কোকিল। কাজী নজরুল ইসলাম তার সমগ্র সাহিত্যের বাগানে বুলবুলের মিষ্টি গান ছড়িয়েছেন। একটি মাত্র উদাহরণঃ ‘হৃদয়ে মোর খুশীর বাগান/বুলবুলি তায় গায় সদাই’
কবি শেখ সাদীর বুলবুল কি রকম দেখা যাকঃ
বুলবুল মুশদায়ে বাহার ব ইয়ার,
খবরে বদ ব বোফে শোম গুজার।
[কোকিলের ধর্ম মিষ্টি গান গেয়ে বন্ধুদের পরিতৃপ্ত করা। পেচকের ধর্ম অন্ধকারে খারাপ সংবাদ ছড়ানো।]
পারশ্যের বুলবুল কবি হাফিজ ‘বুলবুল’ এর সঙ্গে কাঁদতে চেয়েছেন বন্ধুত্ব করার জন্য। ব্যতিক্রমধর্মী কণ্ঠ এইরূপঃ
ব নালে বুলবুল আগার ব আমানত সর ইয়ারিস্ত,
কেহ মা দুম্ব আশেক জারায়েম ও কর মা জারিস্ত।
[বুলবুল তুমি কাঁদো, কাঁদো আমার বন্ধুত্ব যদি চাও, আমরা দু’জনেই কাতর প্রেমিক, কান্নাই আমাদের একমাত্র সম্বল।]
মহাকবি ইকবালের ‘বুলবুল’ পাখাহীন অবস্থায়ও আকাশে উড়তে আগ্রহী, সম্মুখে তার গতি :
কওমে আওয়ারা ইনাঁ-সাব হ্যায় ফির সুয়ে হিজাজ,
লে উড়া বুলবুল বে পরকো মজাকে পরওয়াজ।
[দিশে হারা জাতি হিজাজের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে, পক্ষবিহীন বুলবুল, সেও আকাশে উড়ে যেতে চায়।]
৫ মঞ্জিল (আ)—গন্তব্যস্থান, বসতিস্থান আবাসভূমি ইত্যাদি। কাজী নজরুল ইসলামের বহু কবিতায় ‘মঞ্জিল’ তার আর্তির মধ্যে। একটি উদাহরণঃ
‘আসবে সেজন এ মঞ্জিল/এই সে মাসে।’ [মরু ভাস্কর]
ইসলাম পুর্ব-যুগের ‘সাবআ মু’আল্লাকা’ খ্যাত কবি ইমরাউল কায়েস-এর, মঞ্জিল তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল তার প্রিয়ার জন্য এই সেই মঞ্জিল ।
কিফানবে মিন্ জিকরী হাবিবিন ওয়া ‘মানজিলি’
বি সিক্তেল আলওয়া বায়নাদ দুখুল ফা হাওমালী।
[বন্ধু দাঁড়াও, আমার প্রেয়সী ও তার বসতিস্থান স্মরণ করে কেঁদে নিই। হাওমল ও দুখুল এর মাঝখানে বালির ভিটি এখনো পড়ে আছে। কবি হাফিজ তার ‘মঞ্জিল’ খুঁজেছেন প্রিয়ার রাস্তার উপর। যেমন,
ইয়াদ বাদ আঁকেহ সো গোয়ে তোয়াম মঞ্জিল বোদ,
দিক্হ রা রোশনী আজ খা দরতে বোদ।
[মনে পড়ে তোমার পথের মাথায় ছিল আমার বসত, আমার চোখে এখন সেই মাটি চমক খেলে।]
দার্শনিক কবি ইকবাল বহুস্থানে ‘মঞ্জিল’ -এর কথা বলেছেন। একটি মঞ্জিল এই রকম,
মঞ্জিলে দহরমে উটো কে হুদী খাঁ গয়ে,
আপনি বগলোঁ মে দবায়ে হয়ে কুরআঁ গয়ে।
[বসতিস্থান থেকে হুদী মানে যারা উটের গান গাইত তারা চলে গেলো। তারা চলে গেলো বগলের নীচে কোরান দাবিয়ে রেখে।]
৬. জোশ (ফা. উ.)—উৎসাহ, উদ্দীপনা, প্রেরণা।
নজরুল-কাব্যে ‘জোশ’-এর কথা অনেক স্থানেই আছে। তার ইসলামী ‘জোশ’ এইভাবে ব্যক্ত করেছেনঃ
নাহি সে উমর খাত্তাব, নাহি সে ইসলামী
‘জোশ করিল জয় যে দুনিয়া, আজ নাহি সে সিপাহী।’
মওলানা রুমী তার ‘জোশ’-এর কথা বলেছেন এইভাবে,
মান চে গুইয়াম দর দিলে মান ‘জোশে’ নিস্ত,
বা কে গুইয়াম দরজাহা এল গোশে নিস্ত।
[আমি আমার আসার কথা, উত্তেজনার কথা কার কাছে বলবো যদি পৃথিবীতে শোনার মত একটি কানও না থাকে।]
৭. জওহর (আ, ফা-গওহর) মূল্যবান পাথর, মনি, মুক্তো ইত্যাদি। নজরুল ইসলাম ‘জওহর’ বা ‘গওহর’ দিয়ে তৈরী করেছেন তাঁর কাব্যের প্রাসাদ। একটি মাত্র উদাহরণ,
‘পানি কওসর
মণি ‘জওহর’
আনি জিবরাইল আজ হরদম দানে ‘গওহর’
টানি’ মালিক উল-মৌত জিঞ্জির বাধে মৃত্যুর দ্বার লৌহর।
মহাকবি শেখ সাদী ‘গওহর’-এর চিরত্বগুণ রক্ষা করেছেন এইভাবে,
সংগে বদ ‘গওহর’ আগার কাসায়ে জরি শেকান্দ,
কিমতে সংগে নাইয়াফ জাইয়াদ ও জর কম না শওয়াদ।
[যদি শক্ত পাথর দিয়ে মুক্তোখণ্ড অথবা সোনার পিয়ালা ভেঙ্গে ফেলা হয় তবু মুক্তো বা স্বর্ণের দাম কমে না। এবং স্বর্ণ স্বর্ণই থাকে। পাথরও কোনোদিন সোনা হয়।]
মহাকবি ইকবালও ‘জওহর’ ছড়িয়েছেন তাঁর কাব্যের সর্বত্র। ‘পচ-চি-বায়দ কর্দ’ (অতঃপর কিংকর্তব্য) কাব্যগ্রন্থের দুটি লাইনে ব্যবহৃত ‘জওহর’ কি ঔজ্জ্বল্যই দিচ্ছে,
মুমিন আজ আযম ও তওফকুল কাহির আস্ত,
গর না দারাদ ইঁ দু’ ‘জওহর’ কাফির আস্ত।
[মুসলমান বিজয়ী হয় তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও নির্ভরশীলতার জন্যে। এই দুই গুণ সম্পন্ন মুক্তো যদি না থাকে তবে সে কাফের মানে অবিশ্বাসী।]
৮. আব জম জম (ফা, আ) মন্দাকিনী ধারা, মক্কার পবিত্র কুপ (নহরে জম জম)। কাজী নজরুল ইসলামের ‘আব জম জম’ খুব কষ্টে অর্জিত। যেমন,
‘আব জম জম’ আনলে এরা,
আপনি পিয়ে কলসী বিষের।’
মহাকবি ফেরদৌসীর ‘আব জম জম’ এইরূপ,
আবে জম জম করদা বুদাম আবে সুরা কায়কোরাম,
পাদশাহী করদা বুদাম পাসবানী কায় কোরাম।
[যে একবার ‘আবে জম জম’-এর পানি পান করেছে সে কোনোদিন নর্দমার পানি খাবে না। যে একবার বাদশাহী করেছে সে কখনো চৌকিদারী করতে যাবে ।]
৯. জহর (ফা)—বিষ। নজরুল ইসলাম ‘জহর’ কিনেছেন জহরতের বিনিময়ে। যেমন, ‘জহর’ নিয়ে জহরত দেয়া নও বণিকের নও খেলা। ফারসী কবি ও সঙ্গীত সম্রাট আমির খসরু দেহলভী ‘জহর’-এর ক্রিয়া অনুভব করেছেন এইভাবে,
তন্ দুরন্তি গার না বাশাদ শহদ শকর ‘জহর’ আস্ত,
মাশুক আগার খোশ না বাশাদ বস্তার গুলখারে আন্ত।
[স্বাস্থ্য যদি ভালো না থাকে তখন মধুও মিষ্টি বিষের মতো মনে হয়। প্রেমিকা যদি খুশী না থাকে তবে ফুলের বিছানা কাটার মতো মনে হয়।]
একটি জনপ্রিয় উর্দু গজলে ‘জহর’ আছে এইভাবে,
দুনিয়া মে হম আয়ে তো জিনাহী পারে গা,
দুনিয়া আগার জহর’ কা পিয়ালা হায়।
তো পিনাহী পারে গা।
[দুনিয়াতে যখন এসেছি তখন জীবিত থাকার চেষ্টা করতেই হবে। দুনিয়া যদি বিষের পাত্রও হয় তবু তা পান করতেই হবে।]
১০. খাহেশ<খায়েশ (ফা)-ইচ্ছা, অভিলাষ, আশা, আকাঙ্খা ইত্যাদি। নজরুল ইসলামের ‘খায়েশ’ নিঃস্বার্থ, তিনি কেবল স্বদেশে ‘নওরোজে’র মেলা দেখতে চান। যেমন,
তখত তাউস কোহিনূর কারো নাই ‘খায়েশ’,
নওরোজের এই সে দেশ।
কবি গালিব তাঁর খাহেশ’ বিবৃত করেছেন চিরন্তন সূত্রেঃ
দুনিয়া কি ‘খাহেশ’ ইনি
কেহ্ হর ‘খাহেশ’ পে দম নিকলে,
বহুত আরমাঁ নিকলে মেরে
ফির ভি কম নিকলে।
[দুনিয়ার আশা-আকাঙ্খা এত যে, একটি আশা পূর্ণ করতে গিয়ে জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। অজস্র আশা পূর্ণ হয় অথচ মনে হয় কিছুই হয় নি মানে খুব কম হয়েছে।]
১১. মসজিদ (আ)-উপাসনালয় (মুসলিমদের), নামাজ-ঘর। নজরুল ইসলাম বহু ‘মসজিদ’ তৈরী করেছেন তাঁর কাব্যকর্মের মোড়ে মোড়ে। কিন্তু আল্লার শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের একটি হৃদয়ের চেয়েও ‘মসজিদ’ অনেক ছোট। যেমন, কবি বলেছেন,
নহে ঐ এক হিয়ার সমান
হাজার কা’বা হাজার ‘মসজিদ’।
উমর খৈয়ামের বরাত দিয়ে জনৈক উর্দু কবি মসজিদের স্থান উল্লেখ করেছেন এইভাবে,
সাকী শারাব পিলে দে হম মসজিদ মে বৈঠ কর,
ইয়া ও জাগা বাতা দে জাঁহা পর খুদা না হ্যায়।
[হে সাকী, আমাকে মসজিদে বসে পান করতে দাও,
না হলে এমন স্থানের কথা বলে দাও, যেখানে খোদা নেই।]
আর একজন উর্দু কবি বলেছেন,
মসজিদ তোড়ো মানদের তোড়ো
ইয়ে তু মুজাক্কার হায়,
মগর কেসি কা দিল না তোড়ো
ইয়ে খাস খুদা কা ঘর হায়।
(মসজিদ ধ্বংস করো, মন্দির ধ্বংস করো, এটাতো পৌরুষ দীপ্ত কাজ। কিন্তু কারো মন ভঙ্গ করো না, কারণ মানুষের মন আল্লাহতায়ালার খাস ঘর।]
১২. আবহায়াত (ফা, আ.)—জীবন সার, জীবন রস, জীবন পানি। নজরুল ইসলাম রাসুলে করীমের মারফত ‘আব হায়াত’ বিলিয়েছেন সারা দুনিয়ার মানবতাপাত্রে। যেমন,
হায় সিকান্দার খুঁজলে বৃথাই ‘আবহায়াত’ এই দুনিয়ায়,
বিলিয়ে দিল আমার নবী, সে সুধা মানব সবায়।
পারশ্যের কবি হাফিজের ‘আবহায়াত’ এইরূপ,
সাকীম খিজিরাস্ত ও মি আবহায়াত,
তৌবা আজ মি চু কুনাম হায়হাতা হাত।
[আমার সাকী হচ্ছে খিজির এবং আমার পানীয় হচ্ছে ‘আব হায়াত’। তৌবা করি শারাব ছেড়ে দেব, কিন্তু আফসোস তা হয় না বরং উল্টোটা হয়ে যায়।]
১৩. মাল্লা (আ) নাবিক, মাঝি।
নজরুলের তরী কখনো ডুববার নয়। কারণ এ তরীর কাণ্ডারী মানে চালক হচ্ছেন সরওয়ারে কায়েনাত আহমদ (সঃ) এবং মাঝি মাল্লারাও পাকা। যেমন,
এ তরীর কাণ্ডারী আহমদ
পাকা সব মাঝি ও মাল্লা।
মাঝিদের মুখে সারিগান
শোন ঐ লা শরীক আল্লাহ্।
উপমহাদেশের প্রখ্যাত কবি গালিব ‘মাল্লা’দের সতর্ক করে দিয়েছেন এইভাবে,
বে ফিকর না হো মাল্লা সাহেল কি
কিনারে আ কর,
হাজারো কিশতিয়া ডুব গয়ী ইস
সাহেল সে টাকা কর।
[হে মাঝি, কিনারে এসেও নিশ্চিন্ত হয়ো না, কারণ কিনারের ধাক্কা খেয়েও বহু নৌকা ডুবে গেছে।]
১৪. মুল্লা, মোল্লা (আ) জ্ঞানী, পণ্ডিত, বিজ্ঞজন।
কাঠমোল্লাদের উপর ক্ষিপ্ত নজরুলের সাবধান বাণী,
মৌ-লোভী যত মৌলবী আর ‘মোল-লা’রা কন হাত নেড়ে,
দেবদেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও পাজিটার জাত মেরে!
দার্শনিক কবি ইকবালের ‘মুল্লা’ এই রকম,
ব-বন্দ-ই-সুফী ও মুল্লা আসীরী,
হায়াত আয হিকমত-ই-কুর আঁনা-গারী
[তুমি সুফী ও মুল্লার ফাদে বন্দী আছ—পবিত্র কুরআনের জীবন থেকে তুমি সরে পড়েছ।]
১৫. সিজদা (আ)—নত হওয়া নামাজে ব্যবহৃত ‘সিজদা’। ‘মরু-ভাস্কর’ গ্রন্থে নজরুল ইসলামের ‘সিজদা’ এই রকম,
পড়ছে ঝুঁকে অধোমুখে ‘সিজদা’ করার লাগি সব,
সেদিন হতে শুনছি কেবল নতুনতর ‘সালাত’-রব।
কবি হাফিজ-এর ‘সিজদা’ এইরূপ,
ব ম্যায় ‘সুজ্জাদা’ রাঙি কোন গারাত পীরে মগা গোয়েছ,
কে সালেক বেখবর নাবুদ জরাও রসমে মঞ্জিল হা।
[কামিল পীর যদি জায়নামাজে শারাব ঢালতে বলেন, তাই ঢালো। কারণ, তিনি সিজদার আসল মানে জানেন এবং আসল মঞ্জিলে যেতে যা দরকার সে সম্পর্কে তার জ্ঞান আছে।]
একটি জনপ্রিয় উর্দু গজলে ‘সিজদা’ আছে এইভাবে,
জেয়সী ‘সিজদো’ সে আল্লাহ কো নেহি মিলতা,
হর জাগা মে ঝুঁকানে সে কিয়া ফায়দা।
[যে সিজদায় আল্পাকে পাওয়া যাবে না,
দুনিয়া জোড়া মাথা নত করেও কোনো লাভ নেই।]
১৬. আসমান (ফা)—আকাশ।
নজরুল-কাব্যের বহু ‘আসমানের’ একটি এইরূপ,
আরাস্তা আজ জমীন ‘আসমান’
হুরপরী সব গাহে গান।
কবি ইকবালের ‘আসমান’ এ রকম,
দু’আ ইহ কর কি খুদাওন্দে আসমা’নো যমীঁ
করে ফির উস্ কি যিয়ারতসে শাদমাঁ মুঝকো।
[এই প্রার্থনা করো, যেন স্বর্গমত্যের প্রভু খুদাতায়ালা তার দর্শন দ্বারা আমাকে আবার আনন্দময় করে তোলেন।]
১৭. ফেরেশতা (আ)—স্বর্গীয় দূত।
নজরুল-কাব্যে ফেরেশতা বহুবার আবির্ভূত হয়েছেন। এক স্থানে এই ভাবে,
‘ফেরেশতা’ সব সওদা খুশীর
বিলায় নিখিল ভুবন মাঝে।
কবি গালিব ‘ফেরেশতা’কে দেখিয়েছেন এই ভাবে,
মুহব্বত আগ যায় যো পথর কে সিনে সে জ্বলতে,
বাশার কিয়া? ফেরেশতো ইনহি সোলে সে জ্বলতে।
[প্রেম হচ্ছে এমন আগুন যা পাথরের ভিতর থেকেও বের হয়ে আসে। মানুষ কি? ফেরেশতারাও মানুষের স্ফুলিঙ্গে জ্বলে যায়।]
১৮. ফুল (উর্দু)—পুষ্প।
বিভিন্ন ফুলের সমারোহে নজরুল ইসলাম তাঁর কাব্যের বাগান সাজিয়েছেন। তার অনন্য একটি ফুল,
‘সাহারাতে ফুটলো রে ‘ফুল’
রঙ্গিন গুলে লালা।
সেই ফুলেরই রৌশনীতে
ত্রিভুবন উজালা।
কবি ইকবাল ফুলের দল দিয়ে হীরক খণ্ডও কাটতে চান,
ফুল কি পাত্তি সে কাট সাকতা হ্যায় হীরে কা জিগর।
[ফুলের দল দিয়ে হীরকের অন্তরও কাটা যায়]
১৯. ফরমান (ফা)—আদেশ।
নজরুল কাব্যে বহু সৎকর্মের ফরমান আছে। একটি ফরমান এই,
মানুষ হইয়া মানুষের পূজা মানুষেরই অপমান,
তাই মহাবীর খালেদেরে তুমি পাঠাইলে ‘ফরমান’।
প্রখ্যাত ফারসী অন্ধ কবি রোদকীর ‘ফরমান’ খুবই চমৎকার,
খিরমন্দ গুইয়াদ খিদ পাদশাহ আস্ত,
কি বরহাস আম ফরমান বাস্ত।
[মানব দেহের শাসক হচ্ছে জ্ঞান, এই জ্ঞানই আদেশ দান করে দেহ শাসন করতে।]
২০. তৌহিদ (আ)—একত্ববাদ।
বহু জায়গায় নজরুল ইসলাম তৌহিদের বাণী ঘোষণা করেছেন। একটি নমুনা,
এই তৌহিদ-একত্ববাদ বারে বারে ভুলে এই মানব,
হানাহানি করে, ইহারাই হয় পাতাল তলের ঘোর দানব।
মহাকবি ইকবালও তৌহিদের ঘোষণা করেছেন বারবার। একটি উদাহরণ,
মশক তৌহিদ কা হর দিল বঠায়া হমনে,
যেরে খঞ্জর ভি ইহ পয়গাম সুনায়া হমনে।
প্রতিটি হৃদয়েই তৌহিদের ছবি এঁকেছি, খঞ্জরের নীচে থেকেও এই পবিত্র বাণী শুনেয়েছি।
২১. গুল (ফা)—ফুল, পুষ্প।
নজরুল ইসলাম তাঁর কাব্য-মাঠ গুলে গুলজার অর্থাৎ ফুলে ফুলময় করেছেন। ‘বুলবুল’ থেকে একটি নিদর্শন,
গোপনে চৈতী হাওয়ায় ‘গুল’ বাগিচায় পাঠালে লিপি,
দেখে তাই ডাকছে ডালে কু কু বলে কোয়েল ননদী।
কবি হাফিজ তার ‘দীওয়ান’ সাজিয়েছেন ‘গুল’-এর বাহার দিয়ে,
গুল বে রোখ ইয়ারে খোশ না বাশাদ,
বি বাদাহ বাহারে খোশ না বাশাদ।
[গোলাপ ছাড়া প্রিয়ার মুখ ভালো লাগে না।
গোলাপ ছাড়া বসন্ত কাল নিরর্থক।]
উর্দু কবি জোশ মলিহাবাদী ‘গুল’ প্রস্ফুটিত করেছেন নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে। যেমন,
মেটা দো আপনি হাঝি কো আগার কুছ মর্তবা চাহে,
যেয়মে দানা খাক মে মেলকার গুলে গুলজার হো যায়ে।
[যদি কোনো ফললাভ চাও তবে সাধনার মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করো। যেমন বীজ মাটিতে মিশে গিয়ে ফুলে ফুলময় করে তোলে।]
উর্দু কবি মীর তকী মীরও ‘গুল’-এর আসলরূপ প্রদর্শন করেছেন,
নিকাল যাতি হায় খোশবু তো ‘গুল’ বেকার হোতা হায়।
[সুঘ্রাণ বেরিয়ে গেলে ফুল নিরর্থক হয়ে পড়ে।]
২২ খঞ্জর (ফা)—ছুরি, বল্লম, তরবারী, ছোরা।
নজরুল ইসলাম অশুভ খঞ্জরের কথা বহুবার উল্লেখ করেছেন। যেমন,
কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙ্গালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের ‘খঞ্জর’।
কবি ইকবাল পাশ্চাত্য সভ্যতার মারাত্মক খঞ্জরের কথা বলেছেন এভাবে,
তুমহারী তাহযীব আপনে খঞ্জরমে আপহী খুদকশী করেগী,
জো শাখে নাযুক পে আশইয়ালা বনে গা নাপায়দার হোগা।
[তোমাদের সভ্যতা তোমাদেরই ছোরায় আত্মহত্যা করবে।
দুর্বল শাখায় যে বাসা তৈরী করা হয় তা খুবই ক্ষণস্থায়ী।]
২৩. শমশের (ফা)—তরবারী।
নজরুল ইসলাম বহুবার ‘শমশের’-এর ঝিলিক দেখিয়েছেন। বীর খালেদের ‘শমশের’ এইরূপ,
খোদার হাবিব বলিয়া গেছেন অসিবেন ঈশা ফের,
চাই না মেহদী, তুমি এস বীর হাতে নিয়ে শমশের।
মহাকবি ইকবাল আত্মবিস্মৃত মানুষকে ডাক দিয়েছেন এভাবে,
তু শামশীরে যে নিয়ামে খুদ বিরূ আ’,
বিরূ আ’ আয নিযামে খুদ বিরূ আ’
[হে তরবারী, তুমি নিজের খাপ থেকে বাইরে আসো, তুমি বাইরে আসো, নিজের খাপ থেকে বাইরে আসো]
২৪. বান্দা (ফা)—চাকর, গোলাম, দাস।
নজরুল ইসলামের ‘বান্দা’ বন্ধন ছিঁড়ে বাইরে আসতে চায়,
চির অবনত তুলিয়াছে আজ গগনে উচ্চ শির,
‘বান্দা’ আজিকে বন্ধন ছেদি ভেঙেছে কারা-প্রাচীর।
কবি ইকবাল বান্দা ও বাদশাহকে এক কাতারে দাঁড় করিয়েছেনঃ
এক হী সফমে খড়ে হো গয়ে মাহমুদ ও আয়াজ,
কোই ‘বান্দা’ রাহা আওর না কোই বান্দা নওয়াজ।
[একই কাতারে পাশাপাশি দাড়িয়েছে মাহমুদ ও আয়াজ, এখন আর কোনো তফাৎ নেই, কে চাকর, কে বাদশাহ।]
২৫. জিঞ্জির (ফা)—শিকল।
নজরুল ইসলামের ‘জিঞ্জির’ বড় শক্ত। যেমন,
টানি’ মালিক উল মৌত ‘জিঞ্জির’ বাঁধে মৃত্যুর দ্বার লৌহর।
শেখ সাদীর ‘জিঞ্জির’ও লক্ষ্য করবার মতো,
পায়ে দর ‘জিঞ্জিরে’ পে দোস্ত আ,
বেহু কেহু ব বেগানে দর দোস্ত।
[বন্ধুর কাছে আবদ্ধ থাকা শত্রুর বাগানে ভ্রমণ করার চেয়ে উত্তম।]
২৬. আতশআতশী (ফা)—আগুন, অগ্নি
নজরুল ‘আতশ’ জ্বেলেছেন বহু কবিতায়। একটি নমুনা,
জিবরাইলের আতশী পাখা সে ভেঙে যেন খান খান,
দুনিয়ার দেনা মিটে যায় আজ তবু জান আনচান।
কবি গালিব-এর ‘আতশ’ এইরূপ,
ইশক পর জোর নেহী, হ্যায় য়েহ, ওহ্ ‘আতশ’,
জো লাগায়ে নহু লাগে ঔর বুজায়ে নহু বুজে।
[প্রেমের উপর কোন জোর জবরদস্তি নেই, এটা সেই আগুন যে আগুন জ্বালালে জ্বলে না এবং নিভাতে চাইলেও নেভে না।]
২৭. সাকী (আ)—শরাব পরিবেশক।
নজরুল বহুবার ‘সাকীর’ পেয়ালায় আমাদেরকে কাব্যরস পান করিয়েছেন। যেমন,
বন্ধু গো ‘সাকী’ আনিয়াছ নাকী বরষের সওগাত।
কবি হাফিজের ‘সাকী’ এভাবে হাজির,
সাকী, ব নূরে বাদাহ্ বর আফরোজ জামে মা,
মুতরেব বেও কেহ কার জাহাঁ শব্দ ব কামে মা।
[হে সাকী, সুরার ঝলক দিয়ে পাত্র উজ্জ্বল করো, হে জ্ঞানী, বলল, দুনিয়ার সব আকাঙখা কি আমাদের পূর্ণ হয়েছে?]
কবি গালিব ‘সাকী’কে দেখেছেন এভাবে,
নাহ্ হায়রত চশমে ‘সাকী’ কী,
নাহ্ সুহবত দওরে সাগর কী।
[সাকীর চোখ আর ঘুরে ঘুরে কারও চোখে বিস্ময় জাগায় না; সুরাপাত্র ঘুরে ঘুরে কারও তৃষ্ণা মেটায় না।]
২৮. তন (ফা)—শরীর, দেহ।
নজরুল ইসলামের কাব্যের ‘তন’ শৌর্যবীর্যে ভরা। যেমন,
হাকে ঘন ঘন বীর—
হবে জুদা তার ‘তন’ শির,
আজ যে বলিবে নাই বেঁচে হজরত -যে নেবেরে তারে গোরে
আমির খসরু দেহলভীর ‘তন’ এর আকাঙ্খ এইরূপ,
মান তু শুদাম তু, মন শুদী, মান ‘তন’ শুদাম
তু জান শুদী,
তা কস্ নাহ গোয়দ বাদ আজ ঈমান দীগরম
তু দীগরী।
[আমি যদি তুমি হই, তুমি আমি হই। তাহলে আর কেউ বলতে পারবে না যে, তুমি আর আমি ভিন্ন।]
২৯, আরজু (ফা) ইচ্ছা, অভিলাষ, আশা।
নজরুলের ‘আরজু’ এইরূপ,
যে নাম নিয়ে এসেছি দুনিয়ায়
সেই নাম নিতে নিতে মরি এই ‘আরজু’। (সঙ্গীতাঞ্জলী)
উর্দু কবি আলতাফ হোসেন আলি ‘আরজু’ পেশ করেছেন এভাবেঃ
যো হ্যায় গরজ উসকে নয়ে জিসতাজু।
লাখো আগার দিল হ্যাঁয় তো লাখো আরজু।
[প্রত্যেকেই কমবেশী ভিন্ন মত পোষণ করে,
যদি সহস্র প্রাণ থাকে তবে সেখানে সহস্র আশা।]
৩০. দুশমন (ফা)—শত্রু।
নজরুল ঈদের আনন্দে দোস্ত দুশমন এক করে ফেলেছেন,
শয়তান আজ ভেশতে বিলায় শরাব-জাম,
দুশমন-দোন্ত এক জামাত।
উর্দু কবি আলতাফ হোসেন হালী ‘দুশমন’ কে ছাড়তে চান না :
জান যব তক নাহ হো বদন সে জুদা,
কোই দুশমন নাহ্ হো ওতন সে জুদা।
[যে পর্যন্ত প্রাণ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়,
সে পর্যন্ত কোনো শত্রু যেন মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়।]
আলতাফ হোসেন হালীর সমসাময়িক এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রখ্যাত কবি আসাদুল্লাহ গালিবের ‘দুশমন’ও কম প্রিয় নয়। যেমন,
রফিকোসে রকীব আচ্ছে’ যো দুশমনি সে নাম লেতা হায়,
ফুলো সে খার বেহতর যো দামান্দ থাম্ লেতা হায়।
[বন্ধুর চেয়ে সেই শক্ত ভালো যে শক্রতার জন্যও অন্ততঃ স্মরণ করে।
ফুলের চেয়ে কাঁটা ভালো, যে কাঁটা আঁচল টেনে ধরে।]
৩১. মরদ, মর্দ (ফা) পুরুষ, নর মানব।
নজরুল ইসলামের মর্দ কেমন শক্তিশালী,
ওদের কল্লা দেখে আল্লা ডরায়, হল্লা শুধু হল্লা।
এক মুর্গির জোর গায়ে নেই, ধরতে আসেন
তুর্কী তাজী ‘মর্দ’ গাজী মোল্লা। [কামাল পাশা]
উর্দু কবি আলতাফ হোসেন হালী নারী পুরুষের দ্বন্দ্ব নিরুপণ করেছেন এভাবে,
এয়সা না হো মর্দ ঔর আওরত মে রাহে বাকী নাহ ফারাক,
তা’লিম পা কার আদমী বানানা তুমহি জিয়ানা নাহীঁ।
[এমনও যদি হয় যে, নারী-পুরুষে কোনো তফাৎ না থাকে,
তবে তা হবে শিক্ষার মাধ্যমে সভ্যতার দিকে ধাবিত হওয়া।]
দার্শনিক কবি ইকবালের ‘মর্দ’ এর নমুনাও লক্ষ্য করবার মতো,
নিশানে মর্দে মুমিন বাতু গোয়ম,
চু মর্গ আয়াদ তবসসুম বর লবে উস্ত।
[বিশ্বাসী পুরুষদের লক্ষণ বলবো,
যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখনও তার মুখে মৃদু হাসি থাকে]
৩২. হেনা (আ. হিন্না থেকে)—মেহেদী।
নজরুল ‘হেনা’র শিল্পকর্মে তার কাব্য সাজিয়েছেন এভাবে,
সেই মুহূর্তে ‘হেনার’ সুবাস আনিল চন্দ্রালোক।
উর্দু কবি আলতাফ হোসেন হালী, হেনার আসলরূপ দেখিয়েছেন এ ভাবে,
সুর্থে রূহ হোতা হায় ইনসাঁ ঠোকর খানে কে বাদ,
রংগ লাতি হায় হেনা পত্থর পর পিস জানে কে বাদ।
[মানুষ উজ্জ্বল প্রাণের অধিকারী হয় আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পর,
মেহেদী রং প্রাপ্ত হয় পাথরের সঙ্গে পিষ্ট হওয়ার পর।]
৩৩. সিয়া (ফা) কালো রং এর কালি। (উর্দুতে সিয়াহী ব্যবহৃত হয়)।
নজরুল এর ‘সিয়া’ এ ভাবে চিহ্নিত,
বুঝলে ভাই ঐ নীল সিয়াটা শক্রদের,
দেখতে নারে কারু ভালো,
তাইতো কালো রক্তধারার বইছে শিরায় স্রোত ওদের।
উর্দু কবি দাগ সিয়া <সিয়াহী ব্যবহার করেছেন এ ভাবে,
ইশকে বাজী মেঁ কারামত নাহ হো কিয়া মা’নী,
যিসকো দিল চাহে মুলাকাত নাহ হো কিয়া মা’নী,
লিখতা হোঁ জিগর খুন সে ‘সিয়াহী’ নাহ সমঝানা,
মরতা হোঁ তেরী হিজর মেঁ জিন্দা নাহু সমঝানা।
[প্রেমের খেলায় আশ্চর্য লাভ না থাক, তাতে কি?
যাকে প্রাণ চায় তার সঙ্গে দেখা না হোক তাতে কি?
বুকের রক্ত দিয়ে লিখেছি কালি কিনা জানি না,
তোমার বিছিন্নতায় মৃতপ্রায়, জীবিত কিনা জানি না।]
৩৪. শামা (ফা)—বাতি, মোমবাতি।
নজরুল ইসলাম শামার আলোকে বহুবার আমাদের চোখ ঝলসে দিয়েছেন যেমন,
‘আমার হৃদয় ‘শামা’দানে জ্বালি মোমের বাতি।’ [জুলফিকার]
উর্দু কবি দাগ এর ‘শামা’ আমাদের চিন্তামগ্ন করে,
যো জ্বালাতা হ্যায় কেসী কো ওহুতী জলতা হায় জরুর,
শামা ভী জ্বল যাতী হায় পরোয়ানা জ্বল জানে কে বাদ।
[যে জালায় সেও নিশ্চিতভাবে দগ্ধ হয়,
পতঙ্গ জ্বলে পুড়ে যাওয়ার পর মোমবাতিও জ্বলে নিভে যায়।]
৩৫, খাক (ফা)—মাটি।
নজরুলের কাব্য-বৃক্ষ সরস খাক কেন্দ্র করেই বেড়ে উঠেছে,
‘যদিই পাই তায় তোমার বোস্তার খুশবুদার ‘খাক’ ধুল খোড়া।’
কবি ইকবাল দেশের মাটির প্রতিটি কণাকেই দেবতা বলে উল্লেখ করেছেন অবশ্যি এটা ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্য করে বলা,
পাখর কি মুরতোঁ মেঁ সমঝা হ্যায় তু খুদা হায়,
খাকওয়াতান কা মুঝকো হর যররা দেওতা হ্যায়।
[তোমাদের ধারণা, পাথরের মুর্তিতে খোদা আছেন,
আমার কাছে স্বদেশের প্রতিটি ধুলিকণায় দেবতাস্বরূপ]
৩৬. জুদা (ফা)—পৃথক, বিছিন্ন।
নজরুল-কাব্যে ‘জুদা’র খবর বহু আছে। মওলানা রুমী ‘জুদা’র করুণ পরিণতি উপলব্ধি করেছেন এ ভাবে,
বেশনু আয ন’য় চুঁ হেকায়েত মী কুনাদ,
ওয়ায জুদাইহা শেকায়েত মী কুনাদ।
[শোননা, বশী কি কাহিনী বর্ণনা করছে, আসলে সে বিচ্ছিন্নতার করুণ অভিযোগের কথা শোনাচ্ছে।]
৩৭. মউত (আ)—মৃত্যু।
নজরুল বহুবার, মউতকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। হজরত আলি (রাঃ) মৃত্যুকে মধুর মতো মনে করেছেন,
আল ‘মাউতু’ আহলি ইনদানা মিনাল আসাল,
নাহনু বানু দাববাত আসহামেল জামাল।
নাহনু বানুল ‘মাউতু’ ইজাল মাউতা নাজাল
তানহী ইবনে উফফান বিল মারফেল আছাল
ওয়াদ -য়ু আলাই না শায়েখনা ছুম্মা বেহাল।
[মধুর চেয়ে মিষ্টি মৃত্যু আজ আমাদের কাছে,
আমরা দাববার গোত্র, উটের চালনা জানা আছে।
যখনি সে মৃত্যু আসে আমরা মৃত্যুর পুত্র হই,
উফফান গিয়েছে মারা এ খবর দ্রুতবেগে বই
নেতাকে ফিরিয়ে দাও, এই দাবী আর কিছু নয়।
কবি গালিব মউত ‘টেনে’ নিয়েছেন তাঁর জীবন কাব্যে এ ভাবে,
কয়েদে হায়াতও বন্দে গম্ আসল মে দোনা এক হায়।
মউত সে পহলে আদমী গম, সে নাজাত পায়ে কিঁয়ু?
[আয়ুর মেয়াদ আর দুঃখের বন্ধন আসলে তো একই,
মৃত্যুর আগে মানুষ দুঃখ থেকে ত্রাণ পাবে কি করে?]
৩৮. বদল (আ)—পরিবর্তন, প্রতিদান।
নজরুল-কাব্যে বহুবার ‘বদল’-এর আবির্ভাব ঘটেছে। একটি মাত্র উদাহরণ,
বদলাবে তকদীর আমার/ঘুচিবে সকল অন্ধকার।’ [নতুন চাঁদ] ‘বদল’ থেকে বদলাবে’।
হজরত আলি (রাঃ)-এর ‘বদল’এ কি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ,
ফাকুম বি ইলমিন ওয়ালা তাবগি লাহু ‘বাদলা’ন,
ফান্ নাসু মাওতা ওয়া আহলেল ইলমু আহয়িয়া।
(জ্ঞানের সে অন্বেষণে কখনো চেয়োনা প্রতিদান,
জ্ঞানীরা জীবিত আর বাকী সব মৃতের সমান।]
৩৯. খোদ (ফা)—জিন, আপন। (খোদ থেকে খুদী, উর্দু)
নজরুলের আত্মজ্ঞান বড় স্পষ্ট,
খোদকে যদি চিনতে পারিস চিনবি খোদাকে।
ইকবালের খুদীতত্ত্বও কম উপদেশ পূর্ণ নয়।
খুদীকো কর বুলন্দ ইতনা কি হর তকদীর সে পহলে,
খুদা বান্দেসে খোদ পুছে বতা তেরী রিযা কিয়া হায়।
[নিজেকে এত উন্নত করো যে প্রত্যেক ভাগ্যনির্ধারণের আগে খোদা
যেন মানুষকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমার মনের বাসনা কি?]
৪০. মুহব্বত (আ)—প্রেম, ভালোবাসা, প্রণয়।
নজরুল ইসলাম প্রেমের জয় গান গেয়েছেন সর্বত্র একটি নমুনা,
‘মুহব্বত মেরা ফস্ গয়ি’। [বনগীতি]
একজন উর্দু কবি তাজমহল দেখে গরীবদের ‘মুহব্বত’ এর কথা এভাবে বলেছেন,
এক শাহানশাহ্ নে দৌলত কা সহারা লেকর
হম গরীবে কী ‘মুহব্বত’ কা উড়ায়া হায় মজাক।’
(এক শাহানশাহ অঢেল ধনভাণ্ডারের সুযোগ নিয়ে
আমাদের মতো সামান্য লোকের প্রেমকে উপহাস করেছেন।]
কবি ইকবালের প্রার্থনায় ‘মুহব্বত’ এ ভাবে,
ইস দওরকী জুলমত মে হর কলবে পরেশাঁ কো,
ওহ দাগে মুহব্বত দে জো চাঁদকো শরমা দে।
[বর্তমান কালের অন্ধকারে প্রত্যেকটি হৃদয়ে এমন ব্যাকুলতা
জাগিয়ে দাও, চাঁদকেও লজ্জা দেয় এমন প্রেমের কলঙ্ক দাও।]
উপরে মাত্র প্রায় অর্ধশত আরবী-ফারসী উর্দু শব্দের ব্যবহার এবং প্রতিটি শব্দের মাত্র একটি করে উদাহরণ নজরুল কাব্য থেকে পেশ করেছি। সেই সঙ্গে বিশ্বের তাবৎ আরবী উর্দু ফারসী সাহিত্যের খ্যাতিমান কবিরা শব্দসমূহ কিভাবে ব্যবহার করেছেন সে সব থেকেও মাত্র একটি করে উদাহরণ আহরণ করেছি। নজরুল ইসলাম শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন মাত্র। তিনি শব্দের অন্তর্ভুক্ত কোন পংক্তির ভাবধারা অনুসরণ করেছেন কিংবা কাব্যের মূল ভাব অনুকরণ করে নিজের নামে আত্মসাৎ করেছেন এমন কথা আশা করি কেউ বলতে পারবে না। তবে যদি কেউ বলেন যে, নজরুল ইসলাম আরবী ফারসী উর্দু শব্দ ব্যবহার করতে গিয়ে সেসব ভাষার কবি-সাহিত্যিকদের দ্বারাই অনুপ্রাণিত ও প্রভাবান্বিত হয়েছেন, তবে তাঁদের ধারণা যে কত অযৌক্তিক এবং অপ্রতুল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ সম্পর্কে পরে বলছি।
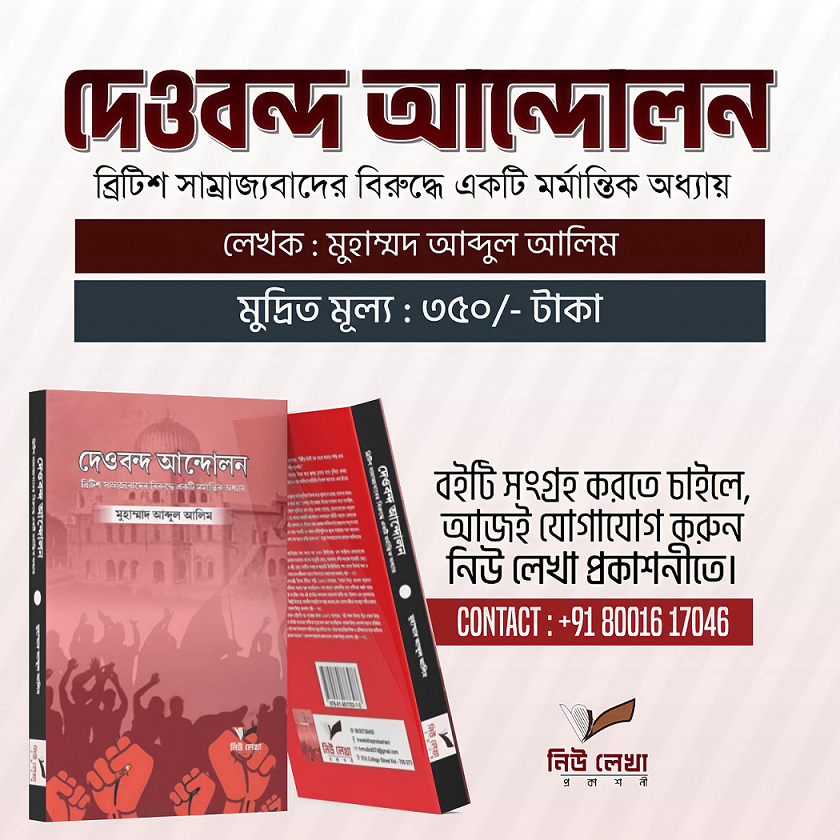
আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষাও সাহিত্যের উদ্ভবজনিত প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার করা এখানে আমার উদ্দেশ্য নয়। এ ব্যাপারে আমি কিছু বলবোও না। শুধু এইটুকুই যোগ করতে চাই যে আরবী ভাষার শব্দগুলো আমরা পেয়েছি ফারসীর মাধ্যমে এবং সেই সঙ্গে ফরাসী শব্দও। অষ্টম শতাব্দীতে যখন আরবগণ ইরান দখল করেন তখন ইরানীরা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাদের মূল ভাষা পাহলবী থেকে আর একটি নতুন ভাষার নবরূপ পরিগ্রহ করে। সেই ভাষাই ‘দারী’ বা আধুনিক ফারসী ভাষা। শুধু নতুন ভাষাই জন্ম লাভ করলো না পাহলবী ভাষার হরফ পাল্টিয়ে আরবী হরফ প্রবর্তন করা হলো এবং আরবী হরফের চেয়ে আরও চারটি হরফ বাড়িয়ে দেওয়া হলো। এ সম্পর্কে আগে সামান্য ইংগিত দেওয়া হয়েছে। ফেরদৌসীর মতো বিশ্বখ্যাত কবিরা তখন এগিয়ে আসলেন ফারসী ভাষা ও সাহিত্যকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার জন্য তাঁদের অমর অবদান সন্নিবেশিত করে।
পাহলবী ভাষা পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ভাষা। এই ভাষার প্রাচীন কবি মহামানব জরোথুস্ত্র এবং তার প্রবর্তিত ধর্মের মহাগ্রন্থ ‘জেন্দ’ ও ‘আবেস্তা’ এবং দুটো মিলিয়ে ‘জেন্দাবেস্তা’। এই পাহলবী ভাষা থেকেই উদ্ভব ঘটেছে সংস্কৃত ভাষার প্রথম গ্রন্থ বেদ। উর্দু ভাষার উদ্ভব অনেক পরে।
ইরানীরা যখন সিন্ধু অববাহিকা বেয়ে এই উপমহাদেশে আসা শুরু করেন তখন তাঁদের সাহিত্য ভাণ্ডারতো আনেনই সেই সাহিত্যভাণ্ডারের সঙ্গে আনেন প্রচুর আরবী শব্দ। মুলত ও আমাদের আরবী শব্দের সঙ্গে পরিচয় ঘটে ফারসীর মাধ্যমেই।
এই উপমহাদেশে যখন মুসলিম শাসন কায়েম হয় তখন ফারসী ভাষা রাজভাষার মর্যাদা লাভ করে এবং দীর্ঘদিন তা অব্যাহত থাকে। ফলে ফারসীর প্রচলন এ দেশে একটা আভিজাত্যের লক্ষণ হয়ে দাঁড়ায়। তখন থেকেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আরবী ফারসী ও উর্দু শব্দের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটে। মধ্যযুগের কবি সাহিত্যিকদের রচনা সম্ভারে তার প্রমাণ রয়েছে যথেষ্ট পরিমানে। বিশেষ করে পুঁথি সাহিত্যে। শুধু যে মুসলিম কবি সাহিত্যিকরাই তাদের সাহিত্যকর্মে আরবী ফারসী উর্দু শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়ে স্বস্তি পান তাই নয় অনেক হিন্দু কবি সাহিত্যিকদের মধ্যেও এই প্রবণতা লক্ষণীয় হয়ে দাঁড়ায়। এমন কি কোনো কোনো হিন্দু পণ্ডিত সাহিত্যিক আরবী ও ফারসী ভাষা রপ্ত করে গ্রন্থও রচনা করেন। রাজা রামমোহন রায় তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। অনেক হিন্দু পরিবারেরও ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল। যেমন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার। এই ঠাকুর পরিবারের দ্বারকানাথ ঠাকুরই ‘দীওয়ান ই-হাফিজে’র প্রথম সার্থক অনুবাদক। দ্বারকানাথ ঠাকুরকে বলা হতো ‘হাফিজ-ই-হাফিজ।’ অর্থাৎ কবি হাফিজকে তিনি সম্পূর্ণ আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন।
আরব ইরান, দুরান প্রভৃতি পশ্চিমী দেশ থেকে যেসব সুফী দরবেশ এবং মুসলিম প্রবক্তা এদেশে আগমন করেছিলেন তারা কেবল ইসলামের অমিয়বাণী, শুভ শিক্ষা বিস্তার করেই ক্ষান্ত হন নি, তাঁরা এদেশেই রয়ে গেলেন এ দেশকে ভালোবেসে এবং এদেশের মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে। এখানেই শেষ নয়। বহু হিন্দু তখন ইসলামের শান্তির বাণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলামের শাস্তির ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। তাদের মধ্যে তখন দেখা দেয় নব উদ্দীপনা এবং নতুন প্রেরণা। ইসলাম গ্রহণ করেই তারা ক্ষান্ত হয় নি, ইসলামী ঐতিহ্যপ্রীতি এবং সেই সঙ্গে আরবী ফারসী উর্দু চর্চার প্রচলনও তাদের মধ্যে ব্যাপক আকারে দেখা যায়।
পশ্চিমী দেশসমুহ থেকে ইসলাম প্রচার এবং ইসলামী শাসন কায়েম করার জন্য যারা এদেশ আগমন করেছিলেন তাদের রক্তধারায় ছিল আভিজাত্যের লক্ষণ এবং শেখ সাদী যার বর্ণনা দিয়েছেন, ‘বার ওজিদা হাস্তে শুইয়া জবু তাজা নামে নাদ’ বলে। অর্থাৎ উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন বংশাবলীর রক্ত ধারার মধ্যে একটা সজীব উন্নতমনা স্বভাব থাকে। সেই উন্নতমনা স্বভাবত কিছুসংখ্যক মানুষ এদেশে বৈবাহিক সুত্রে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে থাকেন। বংশ পরম্পরায় তারা বাইরে বাঙ্গালীপনা বজায় রাখলেও পারিবারিক জীবনে আরবী উর্দু-ফারসীর চর্চা পরিহার করতে পারেন নি। এমনকি অনেক পরিবারে ছিল দ্বিভাষিতার লক্ষণ। কারণ তাঁরা বাইরে বাংলায় কথা বলতেন কিন্তু ঘরে অর্থাৎ পারিবারিক জীবনে ব্যবহার করতেন ফারসী কিংবা উর্দু। আর এই ফারসী উর্দুর সঙ্গে ছিল প্রচুর আরবী শব্দ।
কাজী নজরুল ইসলামের পারিবারিক জীবনে বংশপরম্পরায় ছিল আরবী ফারসী উর্দুর চর্চা। তাদের রক্তধারায় যে নামে ‘নাদ’ প্রবহমান ছিল তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন নজরুল। পবিত্র হাদিসে আছে, ‘কুল্লু শাইয়েন ইয়ারজুয়ু ইলা আসলেহী’। অর্থাৎ সবকিছু তার মূলের দিকে ধাবিত হয়। নজরুল ইসলামও তার মূলের দিকে ধাবিত হয়েছেন। ফলে নিজস্ব ধর্ম, ঐতিহ্যপ্রীতি স্বাজাত্যবোধ ইত্যাদি রক্ষা করতে গিয়েই তাঁর রচনায় প্রচুর আরবী ফারসী উর্দু শব্দের মুক্তো দিয়ে সাহিত্যের মালা তৈরী করেছেন। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায়, নজরুল আরবী ফারসী উর্দু শব্দ ব্যবহার করতে গিয়ে এসব ভাষার কবিদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হননি এবং তাদেরকে অনুসরণও করেননি। তিনি অনুসরণ করেছেন নিজেকে তাঁর বিবেককে এবং এদিকে ধাবিত করেছে তাঁর আসলবন্ধু মানে রক্তধারা। তিনি নিজেই নিজের অনুসারী।
‘নবজাগরণ’ অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপ্লিকেশনটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।
![]()
‘নবজাগরণ’ এর টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।
‘নবজাগরণ’ এর ফেসবুক পেজে লাইক করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

 নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা
নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা
![নজরুল-কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দঃ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা [পর্ব ১]](https://nobojagaran.com/wp-content/uploads/2022/10/pngtree-about-the-celebration-of-indian-poet-kazi-nazrul-islam-jayanti-png-image_6297945-750x375.png)