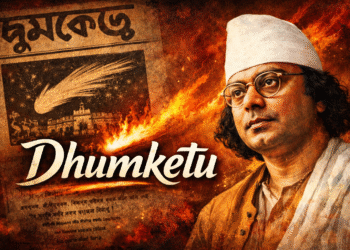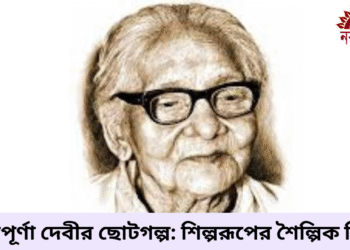সাহিত্যে পীর-মাহাত্ম্যঃ- বাংলা সাহিত্যে পীর মাহাত্ম প্রচার উপলক্ষে সত্যপীর পাঁচালী রচনায় হিন্দু ও মুসলমান পুঁথিকারগণ আত্মনিয়ােগ করেছিলেন। সত্যপীর পাঁচালী ছাড়া বাংলা সাহিত্যে পাঁচালী রচিত হয়েছে মানিক পীরকে কেন্দ্র করেও। মধ্যযুগে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হায়াত মাহমুদের ‘আম্বিয়া বাণী’ কাব্যের বন্দনা অংশে মানিকপীর ও শাহাপীরের কেরামতির ইঙ্গিত আছে,
“মানিকপীর শাহাপীর বান্দা দুই ভাই।
মারিয়া গােঠের গাবী দিয়াছে জীয়াই।”
মানিকপীরের অবির্ভাব সম্পর্কে সুকুমার সেন বলেন, “সত্যপীর যেমন জোড়াতালি দেবতা মানিক পীর ঠিক তেমন নয়। মানিক সুফীদের স্বীকৃত পীর। তিনি অনেকটা যীশুর স্থানীয়। কখনও কখনও তিনি যীশুর (‘ইশা’ নবীর) সঙ্গে অভিন্ন। মানিক পীরের নামে মানিক (মাণিক্য) শব্দের কোনাে সংস্পর্শ নাই। ইহা আসিয়াছে মানিকী (manichee গ্রিক manikhaios) হইতে। ইনি ইরানের লােক ছিলেন এবং খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতাব্দে জরথুস্ত্রীয় ও খ্রিস্ট সংমিশ্রণে নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করিয়াছিলেন। সুফীরা মানিকীকে পীর বলিয়া এবং যীশুর মতাে দয়ালু ও ব্যাধিনিবারক মহাপু(ষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।”১০১ এছাড়াও বাংলা সাহিত্যে পীর গােরাচঁাদ, মােবারক গাজী, জাফর খাঁ গাজী, বড় খাঁ গাজী, একদিল শাহ, পীর বরদশাহ, ইসমাইল গাজীর ন্যায় প্রমুখ পীরগণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে কাব্য রচনা করেছেন অসংখ্য কবি।
যেসব কবিপীর একদিল শাহের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে কাব্য রচনা করেছিলেন তাদের মধ্যে পুঁথিকার শাহ শরফুদ্দিন প্রাচীনতম। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তার গ্রন্থে খ্যাতনামা পীর একদিল শাহ সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করেছেন এক মনােজ্ঞ বিবরণী।১০২ একদিল শাহর মাজার পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসতের নিকটবর্তী আনােয়ারপুরের কাজীপাড়ায় অবস্থিত। প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্ত উপলক্ষে সাতদিনব্যাপী মেলা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে। সেই মেলায় বহু লােক সমাগম হয়। জনশ্রুতি এরূপ যে, একদিল শাহ মােগল-সম্রাট হুমায়ুনের রাজত্বকালে আগমন করেন আনােয়ারপুরে। পরবর্তীকালে মােগল-সম্রাট জাহাঙ্গীর তাকে ২২৫২ বিঘা জমি লাখরাজপুরে দান করেন।
শাহ শরফুদ্দিনের লেখা ‘একদিল শাহের পুঁথি’ পালাগান হিসেবে গীত হত। বেশ বড় পুথি, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৩৮। “হাতের লেখাটি পুরান ছাঁদের থাকিলেও দেখিতে বড়ই মনােহর, একরূপ অলঙ্কৃতই বলা যায়। প্রথম পৃষ্ঠাটি হাতের ঘষায় অস্পষ্ট কিন্তু অন্যত্র সব স্থলেই সুস্পষ্ট।”১০৩ পুঁথিতে কবির ভণিতা প্রায় একই ধরনের –
“রচীয়া ত্রিপদি ছন্দ
পাচালি করিণু বন্দ
ভরসা একদিলের পাত্র।
সাহা সরব্দি ভণে
ভাবিয়া একদিল মােনে
বােলাে আৰ্ধা জদি মােনে লএ৷৷”১০৪
গবেষকের মতে, কবি হেয়াত মামুদের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন পুঁথিকার শাহ শরফুদ্দিন।১০৫ পুথির রচনা-নিদর্শন-
“চন্দ্র সুজ্জ তারা উদএ একস্থান
বিদরিয়া গেল তবে জমীন আসমান।।
প্রর্জা লােক ক্রন্দন করে ধুলাএ লােটায়া।
আনজার করিয়া একদিল জাবেন ছাড়ীয়া ।।
আমরা রহিব ঘরে কার পানে চায়া।
গড়াগড়ী কান্দে প্রজা না ধরে পরান।
অনাথ করিয়া পাব একদিল দেওয়ান।।”১০৬
পীর একদিল শাহের মাহাত্মজ্ঞাপক পুঁথির অপর রচয়িতা সৈয়দ হেলু মীরা শাহ। পুঁথি নকলের তারিখ ১২০৩ বঙ্গাব্দ, ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দ। পুথিকার সৈয়দ হেলু মীরা শাহ যে এর বহু পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন তা সহজেই অনুমেয়। গবেষক বলেন,
“একদিল শাহ বাংলার ইতিহাসগত চরিত্র। জন-দরবারে এই পুঁথি পালাওয়ারীভাবে গীত হইত প্রত্যেক পালার এক একটি স্বতন্ত্র নাম উল্লেখ হইতে এই কাহিনির সর্গ-ভাগ বুঝা যায়। প্রথম খাফের পালা, তৎপর জনমের পালা, এইরূপ পালা দেখা যায়। কলমী পুথিটির হরফ-চেহারা খুব পুরান আমলের হইলেও অতীব সুন্দর।”১০৭
কবির ভণিতা ঠিক পাতায় পাতায় না থাকলেও দুই-চার পাতা অন্তরই আছে। একটি ভণিতা এরূপ –
“রচে হেলু মিয়া এহি একদিলের জনম।
বাড়িতে লাগিল বিবির প্রথম জৈবন।।”১০৮
আমিরউদ্দিন বসুনিয়া সম্ভবত অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। মাতৃভাষা বাংলার ন্যায় আরবি ভাষায়ও তার অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল। সেইসাথে তিনি কবিত্ব প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সাহিত্যচর্চায় তার শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব পবিত্র কুরআন শরিফের ‘আমপারা’ অংশের স্বচ্ছন্দ কাব্যানুবাদ। কুরআন শরিফের পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদের কৃতিত্ব ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের প্রাপ্য। তার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে। এর বহু পূর্বে আমিরউদ্দিন বসুনিয়ার ‘আমপারা’র কাব্যানুবাদ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ সম্পর্কে সমালােচকের উক্তি,
“গ্রন্থখানি কাঠের অক্ষরে ছাপা হয়েছিল। তারিখ জানা না গেলেও মুদ্রণরীতির প্রাচীনত্বের কারণে গ্রন্থখানি প্রাচীন বলেই মনে হয়। এর একখণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে রথিত (নম্বর ৫০২) আছে।”১০৯
পুঁথিকার শাহ বকশউল্লাহ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে জীবিত ছিলেন। রংপুর জেলার লালবাড়ি পরগণার পাটকলাই মৌজার অধিবাসী ছিলেন তিনি। তার লেখা পুঁথির নাম ‘একদিল শাহ’। পুঁথির রচনাকাল সম্পর্কে সঠিক কোনাে তথ্য জানা যায় না এ কারণে যে, পুঁথির ভিতরে কোথাও কোনাে সন তারিখ দৃষ্টিগােচর হয় না। তবে পুঁথির ভাষা বিচারে দেড় শতাধিক বছরের পুরনাে হাতের লেখা পুঁথি বলে সংগ্রাহকের মনে হয়েছে।১১০ পুঁথির বেশ কয়েকস্থানে ‘নিরঞ্জন’ নামে ভণিতা হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ভাষার নিদর্শন হিসেবে পুঁথির মধ্যভাগের অংশ বিশেষ উল্লেখ্য-
“দুই বাচ্চা বােলে মাও জানিলাও সমাচার।
তােমার কারণ পাঠাইলাঙ একদিল খােনকার।।
বােল দেখি গিয়ে নাকী একদিল গুণমুনী।
এমন সুনিএ তবে বােলেন হরনি।
সমকালের আরেক পুঁথিকার শেখ আসমতুল্লাহ। তার পুঁথির নাম ‘ফুলমতী বিবির কেচ্ছা’। পুঁথিতে কবির ভণিতা— ‘কহে কবি আসমতুল্লা আজীর নন্দন। পুথিটি আদ্যন্ত খণ্ডিত। পুঁথি রচয়িতার নিবাস ছিল রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার রাণীপুকুর গ্রাম। গবেষকের মতে, কবি আঠারাে শতকের শেষভাগে ছিলেন বলিয়া মনে হয়।১১১ পুঁথির শুরু –
“উড়িয়া তাহাক লএয়া সাগরে ফেলা।।
উড়িয়া ২ পাড়ে রথের উপারে।
চুর্ণ হয়া পড়ে রথ পায়া পদভরে।।”১১২
এ কালের আর এক পুঁথিকার ফকির মুহম্মদ। তিনি মানিকপীরের পাঁচালির রচয়িতা।১১৩
অন্যান্য কবি : আঠার শতক
মুহম্মদ আলী রাজা (১৬৯১-১৭৬৭) প্রণীত রােমান্টিক প্রণয় কাহিনি সমৃদ্ধ ‘তামিম গােলাল’ এক সময়ে খুব খ্যাতি অর্জন করেছিল। ফারসি উৎস থেকে গৃহীত কেচ্ছা অবলম্বনে কাব্যটি রচিত। তার ‘মিছির জামাল’ আর একটি রােমান্টিক প্রেম কাহিনিমূলক কাব্য। তিনি ফটিকছড়ি থানার বখতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবি আলী রাজা (১৬৯৫-১৭৮০) একজন তাত্ত্বিক ও সাধক হিসেবে সুবিখাত। তিনি চট্টগ্রাম জেলার আনােয়ারা থানার ওসখাইন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্থানীয়ভাবে কানু ফকির নামে সুপরিচিত। আলী রাজা ‘আগম’, জ্ঞানসাগর’, ‘সিরাজ কুলুব’, ‘যটচক্র ভেদযােগ’, ‘ধ্যানমালা প্রভৃতি বহু কাব্য রচনা করেন। বস্তুত ‘জ্ঞান সাগর’ ও ‘আগম’ একই পুস্তকের দুই নাম। এসব কাব্যে সুফী দর্শন, বৈষ্ণব তত্ত্ব ও যােগশাস্ত্রীয় তত্ত্ব আলােচিত হয়েছে। ‘জ্ঞানসাগর’ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হতে প্রকাশিত হয়েছে। আলী রাজার বহু রচনা এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে সংক্ষিত আছে। তিনি অসংখ্য পরমার্থ সঙ্গীতের রচয়িতা। আলী রাজার দুটো শ্যামা সঙ্গীতও পাওয়া যায়। কবি হৃদয়ের চেয়ে ভক্ত হৃদয়ের প্রকাশ ঘটেছে এই দুটি গীতে। গান দুটিতে দেবী কালিকার নানা ঐধর্য বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণনাভঙ্গী অনাড়ম্বর, কিন্তু ‘তত্ত্বরূপী নবীন যৌবনী’। এই বাক্যাংশের ব্যবহারে আলাদা দ্যুতি প্রকাশিত হয়েছে সমগ্র সঙ্গীতে।
মােহাম্মদ মুকীম (১৭০০-১৭৭৫) আঠার শতকের শক্তিশালী কবিদের অন্যতম। তিনি কবি আলী রাজার শিষ্য ছিলেন। তার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে কবি শ্রদ্ধাভরে লিখেছেন, ‘মন মাের লীন জান তান প্রেম রসে’। মােহাম্মদ মুকীম তার ‘গুলে বকাওলী’ গ্রন্থে তাঁর পূর্ববর্তী সমসাময়িক কবিদের নাম উল্লেখ করে মুসলিম বাংলা সাহিত্যের এক অন্ধকার যুগের উপর যে আলােকসম্পাৎ করেছেন, তার তুলনা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বিরল। কবির আত্মবিবরণীর এই অংশ মূল্যবান-
“মুকিম মােহাের নাম জ্ঞানহীন অতি।
চাটিগ্রাম রাজ্যে জান আমার বসতি।।
জন্মভূমি নােয়াপাড়া গ্রাম মনােহর।
কুলশীল নরগণ সাধু সদাগর।।
নােয়াপাড়া নাম জান নবীন সদায়।
নব মুখ নব ভােগ নব যুব রায়।” (ফায়দুল মুকতদী’)
মােহাম্মদ মুকীম চট্টগ্রাম জেলার নােয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই গ্রামে নব্য বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা কবি নবীনচন্দ্র সেনও জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মােহাম্মদ মুকীমের কাব্যগ্রন্থগুলি হল ‘গুলে বকাওলী’, ‘কালাকাম’, ‘মৃগাবতী’, ‘আইয়ুব নবীর কথা’ ও ‘ফায়দুল মুকতাদী’।
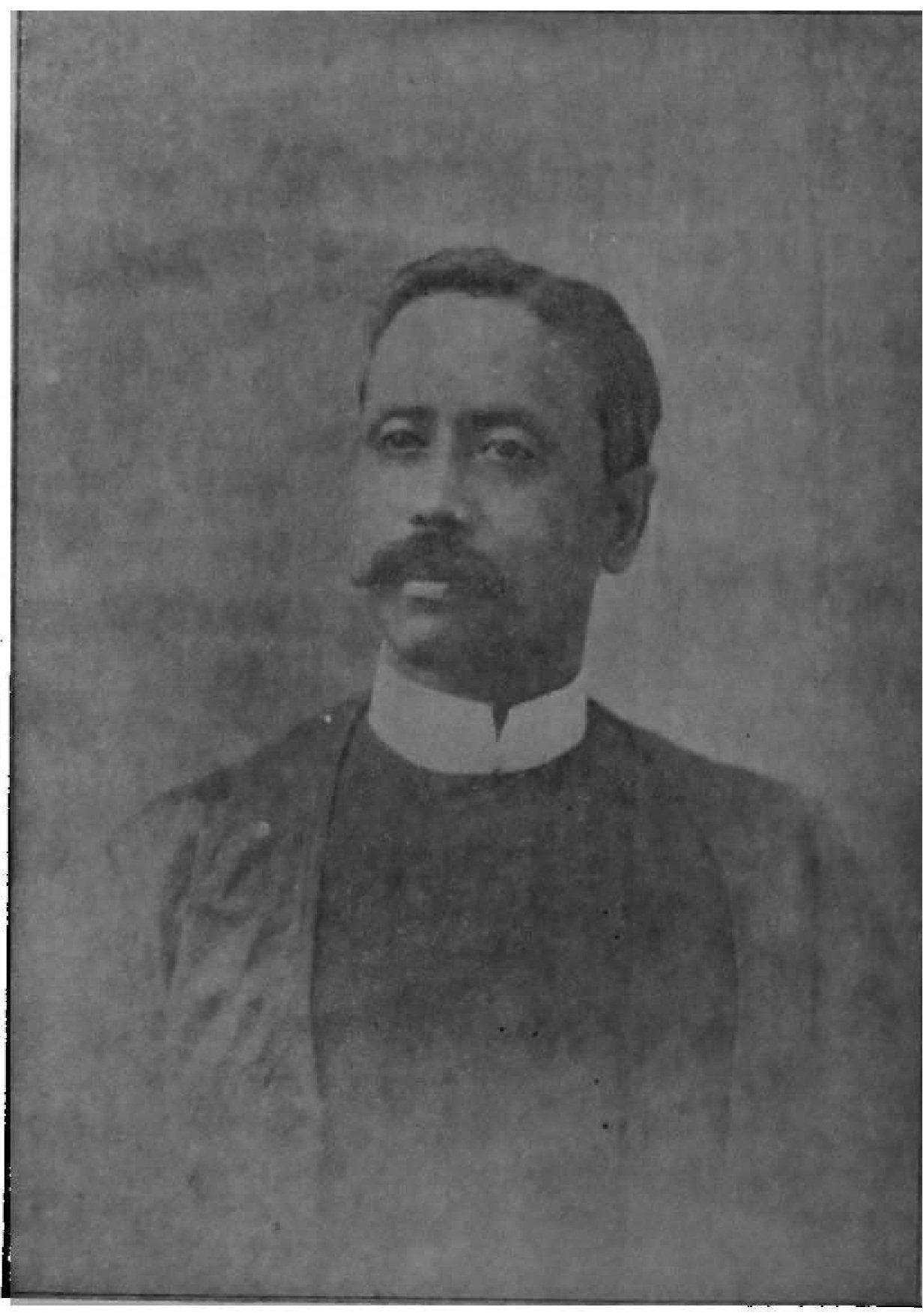
‘গুলে বকাওলী’ ফারসি গ্রন্থ অবলম্বনে লেখা মােহাম্মদ মুকীমের স্বতঃস্ফূর্ত রচনা এবং এতে তিনি প্রয়ােজনবােধে স্বকপােলকল্পিত কিছু নতুন বিষয় সংযােজিত করেছেন। মােহাম্মদ মুকীম এ কাব্যে ছন্দ-শাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, সংগীত এবং হিন্দু ও মুসলমানি শাস্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কাব্যে জ্ঞানের বিষয়কে তিনি কুশলতার সঙ্গে প্রয়ােগ করেছেন, সেই সূত্রে তাকে কবি আলাওলের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কবির অন্যান্য কাব্যগুলাে ধর্মীয় বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে এক ‘ফায়দুল মুকতদী’ ছাড়া অন্যান্য তিনটি পাণ্ডুলিপি অনাবিষ্কৃত থাকায় এ ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। ধর্মীয় বিষয় মােহাম্মদ মুকীমের ‘ফায়দুল মুকতাদী’র দেহগঠনে সহায়ক হয়েছে। তার ভাষার নিদর্শন হিসেবে খানিকটা অংশ উদ্ধৃত হল—
“প্রেমরস কাব্য কথা সুগন্ধি শীতল।
কালাকাম ভাঙি কৈলু পয়ার নির্মল।।
মৃগাবতী নামে তার পরীর নন্দিনী।
মিত্র জনে শুনে সেই অপূর্ব কাহিনী।
মােরে আজ্ঞা দিলা পীর রচিতে পয়ার।
দেশী ভাষে রঙ্গ কথা লােকে বুঝিবার।।
আয়ুব নবীর কথা আছিল কিতাবে।
পয়ার না কৈলু তাহে মন্দ কহে সবে।।”
বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত সুখছড়ি গ্রামের কবি নওয়াজিস খানের (১৬৩৮-১৭৬৫) ভণিতায় একাধিক কাব্যের উল্লেখ রয়েছে। তার যেসব কাব্যগ্রন্থ পাওয়া গেছে তার মধ্যে ‘গুলে বকাওলী’, ‘গীতাবলী’, ‘বয়ানাত’, ‘প্রক্ষিপ্ত কবিতা’, ‘পাঠান প্রশংসা’ ও ‘জোরওয়ার সিংহ কীর্তি’ শীর্ষক রচনা অন্যতম। এগুলাের মধ্যে ‘গুলে বকাওলী’১১৪ পূর্ণাঙ্গ আখ্যানকাব্য। ‘পাঠান প্রশংসা’ ও ‘জোরওয়ার সিংহ কীর্তি’ প্রশস্তিমূলক ক্ষুদ্র কাব্য। বয়ানাত’ ও ‘প্রক্ষিপ্ত কবিতা’ উদ্দেশ্যপূর্ণ খণ্ড রচনা এবং ‘গীতাবলী’ হচ্ছে ভাবাত্মক গান। গ্রন্থগুলাের কোনােটারই সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়নি। সবগুলাে পাণ্ডুলিপিই ছিন্ন ও খণ্ডিত। অধিকাংশ গ্রন্থে নওয়াজিসের ভণিতা রয়েছে এবং রচনার স্টাইল লক্ষ করে গবেষকগণ এসব কবি নওয়াজিসের লেখা বলে সাব্যস্ত করেছেন। প্রথাগতভাবে ‘গুলে বকাওলী’র শুরুতে কবি ব্যক্তিগত পরিচয় দিয়েছেন— সৌভাগ্যক্রমে এই অংশটুকু আবিষ্কৃত হয়েছে। অন্য লেখার নাম ভণিতা ছাড়া বিশেষ কোনাে তথ্য পাওয়া যায়নি।
কবি নওয়াজিস খানের প্রপিতামহের পিতা ছিলিম মােড়ল গৌড় থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে আগমন করে বসতি স্থাপন করেন। কবির পিতার নাম মুহম্মদ ইয়ার খােন্দকার এবং তিনি চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার সুখছড়ি গ্রামে স্থায়ীভাবে আবাসগৃহ নির্মাণ করেন। ইয়ার খন্দকারের তিন পুত্রের মধ্যে নওয়াজিস মধ্যম। তিনি তিন পুত্রকেই সুশিক্ষা দিয়েছিলেন এবং বিদ্যবত্তায় পারদর্শী করেছিলেন।
স্থানীয় জমিদার শ্ৰীযুক্ত বৈদ্যনাথ রায়ের নিকট থেকে কবি নওয়াজিস ‘গুলে বকাওলী’ রচনার আদেশ ও প্রেরণা লাভ করেছিলেন। কবির পীর ছিলেন আতাউল্লাহ। তিনি সুফী মতে দীক্ষিত হয়েছিলেন। ‘গুলে বকাওলী’র হামদ ও নাত অংশে এবং ‘গীতাবলী’ ও ‘বয়ানাতে’ সুফী মতানুসারে আধ্যাত্মতত্ত্বের উল্লেখ পরিলথিত হয়। এছাড়াও ভারতীয় দেহতত্ত্বের সঙ্গে কবি নওয়াজিসের বিশেষ পরিচয় ছিল।
কবির অনুসৃত কাব্য ফারসি ‘গুলে বকাওলী’ থেকে নেওয়া হয়েছে বলে অনেকে যথার্থভাবেই মত ব্যক্ত করেছেন। উর্দুতে ‘গুলে বকাওলী’ লিখিত হয়েছিল, কিন্তু তা অনেক পরে, উনিশ শতকের গােড়ার দিকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের উদ্যোগে। মুন্সী নেহালচান্দ লাহােরী ‘মজহাবে ইশক’ নামে ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে উর্দু গদ্যে এবং দয়াশংকর নসীম ‘মসনবী গুলজারে নসীম’ নামে উর্দু পদে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে কাহিনিটি রচনা করেন। কবি নওয়াজিস খান এদের আগে আবির্ভূত হন। হিন্দী ভাষায় ‘গুলে বকাওলী’র কোনাে প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। আরব-পারস্যেও এর কাহিনি প্রচলিত ছিল না। কাহিনিটি একান্তভাবে ভারতীয়। এ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের দুটি ফারসি ‘গুলে বকাওলী’র সন্ধান পাওয়া গেছে। অযােধ্যায় নবাবের গ্রন্থাগারের ক্যাটালগে জনৈক প্রিঙ্গার সাহেব ‘গুলে বকাওলী’র একটি পাণ্ডুলিপির কথা বলেছেন। এর রচনাকাল ১৬২৫। ক্যাটালগে উল্লেখ থাকলেও এই পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া যায়নি। মুন্সী নেহালচান্দ লাহােরী এ মর্মে স্বীকৃতি দিয়েছেন যে, তিনি শেখ ইজ্জতুল্লাহ্ বাঙ্গালীর রচিত ফারসি ‘তাজুলমুলক’ ‘গুলে বকাওলী’র অনুসরণে উর্দু অনুবাদ করেন। শেখ ইজ্জতুল্লাহ বাঙালি ছিলেন এবং তার কাব্যের রচনাকাল ১৭২২ খ্রিঃ। মনে হয় তিনি কোনাে এক হিন্দী গ্রন্থের অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু গ্রন্থটির কোনাে সন্ধান পাওয়া যায়নি।
নওয়াজিশ খানের ‘গুলে বকাওলী’ কাব্যের রচনাভঙ্গির স্বচ্ছলতা এবং সহজ পারিপাট্য পরিলক্ষিত হয়। আখ্যানকাব্যের অন্যান্য কবির মতই তার বর্ণনারীতি বিবৃতিধর্মী। তবে নওয়াজিস খানের প্রকাশভঙ্গি প্রাণহীন ও পরিচর্যাহীন নয়। বরং ছন্দেঅলংকারে-ধ্বনিসুষমায় কাব্যিক রসাস্বাদন লাভ করা যায়। তার বর্ণনায় কৃত্রিমতা ও জড়তা নেই, একথা এক বাক্যে স্বীকার করতে হয়। কতক ঘটনা, ভাব এবং পরিবেশ বর্ণনায় তিনি শৈল্পিক চারুতা ও সৌকর্যের পরিচয় দেন। বকাওলীর রূপ, বকাওলী ও রূহু আফজার সাজসজ্জা, পাত্র-পাত্রীর প্রেম-মিলনের আনন্দঘন মুহূর্ত ইত্যাদি বিষয়ে কবির লেখনিতে মুন্সীয়ানার চিহহ্ন ফুটে উঠেছে। টঙ্গির নিভৃতকক্ষে ঘুমন্ত বকাওলীর যে রূপ কবি তাজুলমুলুকের চোখ দিয়ে দেখেন, তা অন্য রােমান্টিক কবিদের বর্ণনার তুলনায় অভিনব নয়, কিন্তু আভাহীনও নয়। কবির রূপচর্চায় পরিচ্ছন্ন সৌন্দর্যবােধ এবং প্রসন্ন বিলাসাবেগ প্রকাশিত হয়েছে। সুললিত ধ্বনিবিন্যাসে কবির লিপিকুশলতা ধরা পড়ে—
“খঞ্জন নিন্দিত আঁখি পলক ঘন ঘন।
অঞ্জনে রঞ্জিত দেখি জাগাএ মদন।।
চরণ দুটির চিত্র সৌন্দর্যের সাথে ধ্বনিসৌন্দর্য প্রকটিত হয়েছে। বিবাহের সময় বকাওলীর রূপসজ্জার বর্ণনা এরূপ –
“প্রথমে কোড়াই কেশ দিয়া চতুর্সম।
বান্ধিল পাটেল জাদে খোঁপা মনােরম।।
তাহাতে মুকুতা ছরা করিল শােভন।
চন্দ্রিমা উদিত জেন বিদারিয়া ঘন।।
সীতিপাতি মধ্যেত সিন্দুর বিরাজিত।
জেন প্রকাশিত হইল প্রভাত উদিত।।
রত্নের চিকলি বিন্দি ললাটেত শােভা।
বাল্যচন্দ্রে পাইল কিবা পূর্ণচন্দ্র প্রভা।…
যােগাল শ্রবণে দিল রত্নের কুণ্ডল।
আলেখা ফণির মুখে মাণিক্য উজ্জ্বল।।”
এখানে কবির রূপকল্পনা এবং বাণী বন্ধন প্রশংসার যােগ্য। তার সুর ও ছন্দজ্ঞানও প্রশংসার দাবী করতে পারে। ভাবপূর্ণ মুহূর্তের বর্ণনায় নওয়াজিস প্রধানত কথকতার ভূমিকা গ্রহণ করেন, চিত্ররীতির অনুসরণ করেননি। তার ‘বয়ানাত’ ধর্মীয় বিষয়ের উপর লিখিত একটি শাস্ত্রীয় গ্রন্থ। কবি নওয়াজিসের একটিমাত্র শ্যামা সঙ্গীতের সন্ধান পাওয়া গেছে। তার প্রথম লাইন—
“তােমার পদে লইলু শরণ। জননী মাই কালি।”
আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে লেখা এই ছােটো গীতে পাই কবি হৃদয়ের উদার অসাম্প্রদায়িক মনােভাব ও শ্রদ্ধাশীল ভক্তিপ্রবণ চিত্তের নির্মল প্রকাশ।
মুহম্মদ খানকে উত্তরকালে অনুসরণ করেন কবি মুহম্মদ ইয়াকুব। চব্বিশ পরগণার বসিরহাটের অন্তর্গত জিকিরপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন তিনি। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে তিনি হুগলির বালিয়া পরগণায় কয়েক বছরের জন্য প্রবাসী জীবনযাপন করতেন। এখানেই তার সঙ্গে শাহ গরীবুল্লাহর পরিচয় হয়ে থাকবে। কারবালার বিয়ােগান্ত ঘটনাশ্রয়ী ‘জঙ্গনামা’র প্রথমাংশ গরীবুল্লাহর রচনা ও শেষাংশ রচনা করেন মুহম্মদ ইয়াকুব। এই ‘জঙ্গনামা’য় উপমা ও চিত্রকল্পের বয়ন-দক্ষতা লক্ষণীয়। কবি মুহম্মদ ইয়াকুব লিখেছেন,
“ইমামের লহু গেল আসমানের উপরে।
আসমান উপরে লহু ছিটকায় লাগিল।।
সিন্দুরিয়া মেঘ হইয়া আসমানে রহিল।
আজি তক সেই মেঘ উঠে যে আসমানে।।”
চট্টগ্রামের কক্সবাজারের রামু অঞ্চলের কাজী শেখ মনসুর ‘সিরনামা’ বা ‘শ্রীনামা’ (১৭০৩) রচনা করেন। কাব্যটি ফারসি ‘আসরারুল মুসা’ কাব্যের বাংলা সার সংকলন। কাব্যটি নয়টি ‘ফসল’ বা ‘বাবে’ বা অধ্যায়ে কবি তার ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত তত্ত্বকথা বয়ান করেছেন। আর এক মনসুর ‘শমসের গাজীনামা’ রচনা করেন। ত্রিপুরাবাসী বাঙালি কবি শেখ সাদী রচনা করেন। ‘গদা-মালিকা সংবাদ’ (১৭১২)। এটি অনুবাদমূলক বলে কবি দাবি করেন—ফারসী বাঙ্গালা করি করিলু রচন।১১৫ সতের শতকের কবি শেখ শেরবাজ রচিত মল্লিকার হাজার সওয়াল কাব্যের অনুকরণে এ পুঁথিটি লেখা হয়। দুটি কাব্যেরই মূল ভাব রােমান্টিক। রুম-রাজকুমারী মালিকার এক হাজার প্ররে উত্তর দিলেন তুরস্ক হতে আগত আবদুল হালিম নামে এক ‘গদা’ বা দরবেশ। ফলে উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ‘গদা’ ও মালিকা বহুদিন রুম-রাজসিংহাসনে বসে সুখে রাজশাসন করেন। কাব্যটি উপাখ্যান হলেও এতে প্রাত্তরচ্ছলে নানারকম ধর্মতত্ত্ব প্রকাশের বিশেষ প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কবি সাদীর ছন্দপ্রকরণ শিথিল ও উপমা প্রয়ােগ গতানুগতিক। তবে কবি প্রকৃত একজন ধার্মিক ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। গ্রন্থে কবি কলিকাল সম্বন্ধে কয়েকটি সত্য কথা বলেছেন। ধূমপান যে কলিযুগে প্রসারিত হবে সে সম্পর্কে তাঁর বাণী—“তামাকু তু করিবেক ভুবন বিনাশ।” মুহম্মদ নকী অষ্টাদশ শতকের শেষপাদের লােক। তিনি চট্টগ্রাম জেলার অধিবাসী ছিলেন। মুহম্মদ নকী কবি নওয়াজিশ খানের শিষ্য ছিলেন। চট্টগ্রামের ত্রাহিরাম নামক এক হিন্দু জমিদারের আদেশে মুহম্মদ নকী তার তৃতীনামা’ কাব্যটি ফারসি গ্রন্থ থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন।
চট্টগ্রামের মুহম্মদ বাকির আগা অষ্টাদশ শতকের শেষপাদের লােক। তাঁর ‘গুলজারে ঈশক’ কাব্যটি ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়। কাব্যের কাহিনি রােমান্টিক। হরিণীবেশী রুহ আফজার সঙ্গে চীনের রাজকুমার রিজওয়ান শাহের প্রণয়জীবনের রােমান্টিক কাহিনিকে এ কাব্যে রূপায়িত করা হয়েছে। শমসের আলীর জন্ম চট্টগ্রামের সুলতানপুর গ্রামে। তিনি ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় আরাকানে গমন করেন এবং সেখানেই তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে। তিনি রােসাঙ্গে অবস্থানকালে ‘রিজওয়ান শাহ উপাখ্যান’১১৬ কাব্য রচনা করেছিলেন। তিনি কোনাে রােসাঙ্গ-রাজ অমাত্যের অনুগ্রহ লাভ করতে পারেননি। কাব্যটি রােমান্টিক উপাখ্যানমূলক। কাব্যটির তিন-চতুর্থাংশ কবি শমসের আলীর রচিত। বাকি এক চতুর্থাংশ আসলাম, হাকিম আলী ও সেদমত আলীর রচিত বলে অনেকে মনে করেন। কাব্যে বর্ণিত স্থান খােরাসান ও পারস্য দেশ হলেও বাংলার নানা প্রচলিত কাহিনি এতে স্থান পেয়েছে। চরিত্রগুলি বাঙালি হিন্দুর নামাঙ্কিত। যেমন—চন্দ্রাবতী,হীরালাল, চিত্রপ্রভা ইত্যাদি। শমসের আলীর ভাষা সংস্কৃতানুগ, ললিতমধুর ও ছন্দঝঙ্কৃত—
“ভুরু ধনু যুগ মধ্যে কটাক্ষর বান
ইন্দ্রধনু নহে সেই ধনুক সমান।।”
কবি মােহাম্মদ মুকীমের আত্মকথায় উল্লেখিত পূর্বসুরি কবি পরায়ল নামের লেখ্য রূপ পরাগল সম্রাট হােসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খান তিনি নন, যাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমের ‘পরাগলী মহাভারত রচনা করেছিলেন। তিনি আঠার শতকের কবি ছিলেন। তার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। তাঁর রচিত ‘শাহ পরীর কেচ্ছা’ নামক একটি পুঁথির পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। কেচ্ছাটি কবি নিযামীর (১১৪০-১২০৭) ফারসি কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত।১১৭ শাহ পরীর কেচ্ছা’ কাব্যটি রােমান্টিক বিষয়ের উপর কল্পিত। রােকাম শহরের শাহপরীর সঙ্গে রাজকুমার রূপবানের সাক্ষাৎ ও তাদের প্রেম নিয়ে রচিত এটি। কুমিল্লার নারানয়া গ্রামের মুহম্মদ রফিউদ্দিন ‘জেবলমুলুক শামারুখ’ (১৬৭৩) কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি তার পূর্বসূরি সৈয়দ মুহম্মদ আকবরের কাব্যের অনুসরণে লেখা। কাব্যটির কাহিনি রােমান্টিক। দৈত্যদানাের সঙ্গে যুদ্ধ করে জেবলমুলুক ও শামারুখের মিলনের কাহিনি এখানে ব্যাখ্যাত হয়েছে। কবির ভাষা পরিমার্জিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ—
“কোকিল করে গান, মােহজ্ঞান রঙ্গে।
সুধামৃত শুনি গীত, পুলকিত অঙ্গে।।”
মােহাম্মদ মুকীমের আত্মকথায় উল্লেখিত পূর্ববর্তী কবি গিয়াসক নামটি গিয়াস খান নামের বিকৃত রূপ। চট্টগ্রাম নিবাসী কবির পিতার নাম দরিয়া খান। তিনি রাজপাত্র বা পদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। গিয়াসের পিতামহের নাম ছিল বুধা খান। কবির পীর ছিলেন বুরহানউদ্দিন। আঠার শতকের কবি গিয়াস খান হামজা বিজয়’, ‘লালমতি সয়ফুলমুলুক’ নামক দুটি কাব্য ও কিছু পদ রচনা করেছিলেন। মুহম্মদ কাসিমের (১৭৩০-১৮০০) জন্মস্থান নােয়াখালি জেলার যুগদিয়া নামক গ্রাম, পিতা শাহ আজিজ। মুহম্মদ কাসিমের তিনটি কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলাে হল-“হিতােপদেশ’, ‘সুলতান জমজমা’ ও ‘সিরাজুল কুলুব’। সুফীতত্ত্বের বিষয়কে কেন্দ্র করে আরবি গ্রন্থ ‘বুরহানুল আরেফীন’-এর অনুবাদের মাধ্যমে কবি ‘হিতােপদেশ’ কাব্য রচনা করেছেন। হজরত ঈসার (আঃ) অনুগ্রহে সুলতান জমজমার পুনর্জীবনের কাহিনি ব্যক্ত হয়েছে ‘সুলতান জমজমায়’। গ্রন্থটি আহমদ আলী সিবরাজপুরীর উর্দু গ্রন্থ ‘কিসাস-ই-শাহ জমজমা’ অবলম্বনে রচিত।১১৮ ‘সিরাজুল কুলুব’ গ্রন্থে বিসমিল্লার বয়ান, নামাজতত্ত্ব, রােজাতত্ত্ব, হাদিস তত্ত্ব, জিকিরের মাহাত্ম্য, রসুলের কথা, হাশর-বেহেস্তের বিবরণ ইত্যাদি বিষয় আলােচিত হয়েছে।১১৮ মুহম্মদ কাসিম জনকল্যাণের দিকে নজর রেখে শাস্ত্রীয় বিষয়ে নীতিবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাই তাঁর কাব্য রচনার প্রয়াস উদ্দেশ্যমূলক ও নীতিবাহক হয়ে পড়েছে। সেই কারণেই শিল্পের লালিত্য তাতে অনুপস্থিত।
১৫০৪ সালে রচিত কবি কুতবনের কাব্য ‘মৃগাবতী’র কাহিনি বাংলাতেও অনুদিত হয়েছে। পাঁচজন মুসলমান ও দু’জন হিন্দু কবি সতের থেকে উনিশ শতকের মধ্যে এই কাব্যের অনুসরণে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে বাংলায় কাব্য রচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছেন কবি দ্বিজ পশুপতি এবং তার কাব্যগ্রন্থ ‘চন্দ্রাবলী’ বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এতে কাহিনির উল্লেখযােগ্য পরিবর্তন ছাড়াও বিভিন্ন চরিত্রের নতুন নামকরণ হয়েছে। মৃগাবতী’ কাহিনি নিয়ে রচিত বাংলায় অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে—কবি দ্বিজ রামের মৃগাবতী চরিত্র’, কবি মােহাম্মদ খাতের-এর মৃগাবতী যামিনীভান’, কবি করিমুল্লার যামিনী ভান’ বা মৃগাবতী’ (কাব্যটি ১৯৮৪ সালে ড. আবদুল আউয়াল কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে) এবং কবি ইবাদুল্লার ‘কুরঙ্গভান’। এঁরা কেউই সৈয়দ আলাওল বা কাজী দৌলতের মতাে শক্তিশালী কবি ছিলেন না। কিন্তু বাংলা কাহিনিগুলিতে নামধাম ও ঘটনাসমূহ যেমনভাবে পাওয়া যাচ্ছে, তাতে মনে হয় সে বাঙালি কবিগােষ্ঠী কুতবনের কাব্য থেকে উপাখ্যানটি সরাসরি গ্রহণ করেননি। তারা পরবর্তীকালের কোনাে না কোনাে কাব্য বা লােকমুখে প্রচারিত গল্পের সাহায্য নিয়েছিলেন। তাছাড়া মুহম্মদ মুকীমও (১৭০০-১৭৭৫) বাংলা ‘মৃগাবতী’ কাব্য লেখেন বলে জানা যায়। তাঁর কাব্যের পাণ্ডুলিপি আজও পাওয়া যায়নি।
‘মৃগাবতী’ কাব্যের আরেক বাংলা-অনুবাদক আবদুল আলীম। এই কাব্য সংগ্রহ সম্পর্কে অধ্যাপক আবু তালিব বলেন-
“বর্তমান শতকের গােড়ার দিকে পুঁথি-রসিক আবদুল মহিদ চৌধুরী সুয়াতা দরগাহের খাদিম আবদুল কাদির চৌধুরীর কাছে একটি কলমী পুঁথির অনুলিপি রেখে যান।…আবদুল কাদির সাহেব কপিটি তার কন্যা রাণীর কাছে গচ্ছিত রাখেন। আলােচ্য পুঁথির সংগ্রাহক আয়ুব হােসেন সাহিত্যবিনােদ ঘটনাক্রমে পুঁথিখানির সংবাদ পেয়ে আবদুল কাদির চৌধুরীর কন্যা রাণীর কাছ থেকে উক্ত পুঁথিখানি সংগ্রহ করে স্থানীয় শারদীয় বর্ধমান পত্রিকায় তার কাহিনিটি প্রকাশ করেন (১৩৯১ সাল/১৯৮৪)।
এ থেকে জানা যায়, সর্বপ্রথম পুঁথিখানি ১৬ বােশেখ ১১৮১ সালে/১৭৭৪ খ্রিঃ অনুলিখিত হয়। পরে মহিদ চৌধুরীর পিতা সেই কপি থেকে ১২১১ সালে/১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে আর একটি কপি করেন। প্রথম কপিটি করেন তার আব্বা। সর্বশেষে মহিদ চৌধুরী স্বয়ং তার আব্বার অনুলিখিত কপি থেকে এটি কপি করেন (১৬ ফাল্গুন, ১৩১৬ সাল/১৯০৯)। পূর্বোক্ত শারদীয় বর্ধমান পত্রিকায় টীকা-টিপ্পনি সহযােগে তারই একটি অনুলিপি প্রকাশিত হয়। এই হলাে আবদুল আলীম রচিত মৃগাবতী কাব্য সংগ্রহের সংক্ষিপ্ত ইতিকথা।”১১৯
‘মৃগাবতী’ কাব্যের বাংলা অনুদিত কাব্যগুলির সাহিত্যিক মূল্য খুব বেশী নয়। তবে ‘মৃগাবতী’ কাব্যের কাহিনি বিভিন্ন কারণে বিশিষ্ট। এতে মানবীয় ঘটনা ও রূপকথার সমাবেশ ঘটেছে। রূপকথামূলক আবহ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে মৃগাবতীর মৃগারূপী ভূমিকা, মৃগাবতীর ও তার সখীদের রহস্যময় স্নানকেলি ও পীরূপ ধারণের ক্ষমতা, রাক্ষস ও নরখাদকের প্রসঙ্গ, পীর মনুষ্যরূপ গ্রহণের দৃশ্য এবং মৃগাবতীর প্রতি আসক্ত, ব্যর্থ প্রেমিকের আকাশপথে পরিভ্রমণ ও রাজকুমারের সঙ্গে লড়াইএর। শুধুমাত্র এই অবাস্তব ঘটনাগুলির প্রতি গুরুত্ব আরােপ করলে এ কথা মনে হতে পারে যে, সমগ্র কাহিনিটিই অলৌকিক।
রূপকথার অবতারণার মধ্য দিয়ে কবির সমকালীন লােকমানসেরই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। জনসাধারণ রূপকাহিনি শুনতে আগ্রহী ছিল। বিভিন্ন লােককথায় অলৌকিক ঘটনার প্রাচুর্য থেকেই এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে। কিন্তু এ কাহিনি বাস্তবের ভিত্তিতে গঠিত। কাহিনির আধ্যাত্মিক রূপক ও রূপকথার উপাদান কোথাও এর মানবীর গুণকে ব্যাহত করেনি। গণপতি, রুক্মিণী, মৃগাবতী, রাজকুমার ও দেবী রায় বাস্তব পরিবেশে স্থাপিত, রক্তমাংসে গড়া, জীবন্ত মানব-মানবী।
হাবুত রােয়াজা-র আসল নাম হাবুত, রােয়াজা পদবি, আরাকানি রাজকর্মচারীর পদবি। কবি হাবুত রােয়াজা দক্ষিণ চট্টগ্রাম, বর্তমান কক্সবাজার জেলার লােক ছিলেন। তিনি বা তার পূর্বপুরুষ আরাকানের রাজাদের কর্মচারী ছিলেন বলে রােয়াজা পদবি বংশানুক্রমিক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। উল্লেখ্য যে, দক্ষিণ চট্টগ্রাম ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ অবধি আরাকানের অধিকারভুক্ত ছিল। কবি হাবুত রােয়াজা আঠার শতকের লােক ছিলেন। তাঁর কোনাে রচনা আবিষ্কৃত হয়নি। চট্টগ্রামের কবি ও সাধক পুরুষ জান মােহাম্মদ রচনা করেন ‘নামাজনামা’। এতে বিভিন্ন প্রকার নামাজের নিয়ম, তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ্য, উনিশ শতকে বাংলা হরফ না-জানা শিক্ষিতদের পড়ার জন্যে আরবি হরফে বাংলা পুঁথি লেখা শুরু হয়। কবি জান মােহাম্মদের এতে ঘাের আপত্তি ছিল। তিনি বলেন,
“আর এক কথা কহি শুন বন্ধুজন
আরবি আঙ্গুলে যদি বাঙ্গালা লিখন
বুঝিসুঝি কর্ম কৈলে পাপ ঘােরতর
সত্তর নবীর বধ তাহার উপর।”১২০
তিনি আঠার শতকের শেষ ভাগের লােক ছিলেন বলে মনে করা হয়।
নাসির মােহাম্মদ ও ফাজিল নাসির একই ব্যক্তি। কবির পূর্ণ নাম ফাজিল নাসির মােহাম্মদ। নামটি দীর্ঘ হওয়ায় তিনি ভনিতায় ফাজিল নাসির রূপে উল্লেখ করেছেন। তিনি চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত সুলতানপুর মৌজার জমিদার ওয়াহিদ মােহাম্মদ চৌধুরীর আগ্রহে ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে রাগমালা রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থের নাম ‘ধ্যানমালা’। রাগ-তালের বইয়ের মধ্যে ফাজিল নাসির মােহাম্মদের ‘ধ্যানমালা’ সর্বশ্রেষ্ঠ। কবির পীরের নাম জান মােহাম্মদ-
“সর্বশাস্ত্রে অবধান রূপে নব পঞ্চবান
শ্ৰীযুত জান মােহাম্মদ।
মান্য গুরু শিরােমনি জ্ঞানের সমুদ্র জানি
পুনি পুনি প্রণামি সে পদ।”১২১
তাহির মাহমুদ আঠার শতকের একজন পদকার কবি ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। চট্টগ্রামের প্রাচীন সংগীত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ‘রাগতালনামা’য়১২২ কবি তাহির মাহমুদের কিছু পদ আবিষ্কৃত হয়েছে। নােয়াখালী জেলার ফেণী মহকুমার অন্তর্গত বেদরাবাদ পরগণার অধিবাসী ছিলেন অখ্যাতনামা কবি মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাক। তিনি রচনা করেন ‘সয়ফুলমূলক লালবানু’ (১৭৭০)। নর-নারীর প্রেমই এই উপাখ্যান-কাব্যের উপজীব্য। শেখ সােলায়মান রচিত ‘নসিয়তনামা’য় স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক সম্পর্ক, দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণিত হয়েছে। এটি ফারসি থেকে বাংলায় অনুদিত। নােয়াখালির ভুলুয়া গ্রাম ছিল কবির নিবাস—
“ভুলুয়া শহর জান দিব্য এক স্থান
শেখ সােলেমান নাম তাহাত প্রধান।”
কবি আঠার শতকের শেষার্ধে এ গ্রন্থ রচনা করেন।
কবি মােহাম্মদ মুকীমের আত্ম পরিচিতিতে তার পূর্বসূরি কবিদের তালিকায় কবি আলী মােহাম্মদের নামােল্লেখ দেখা যায়। ‘হায়রাতুল ফিকাহ’ নামে তার একটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। ফারসি গ্রন্থ অবলম্বনে এটি লিখিত। এতে ইসলামি ধর্মাচরণ সম্বন্ধে বহু প্রর্ণ ও তার উত্তর রয়েছে।১২৩ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ তার একটি হেঁয়ালিও আবিষ্কার করেছিলেন –
“দিবসেতে বৃদ্ধ যুবা হএ একবার।
মনুষ্যে ভক্ষণ করে চর্ম নাহি তার।।
সেইতান জননীর আদ্যনাম রতি।
ত্রিপুরারি নাম ধরে তান নিজ পতি।।
কহে আলি মােহাম্মদে ছি অলি অনুসন্ধি।
মুখে বুঝিব কিবা পণ্ডিত হএ বন্দী।।”১২৪
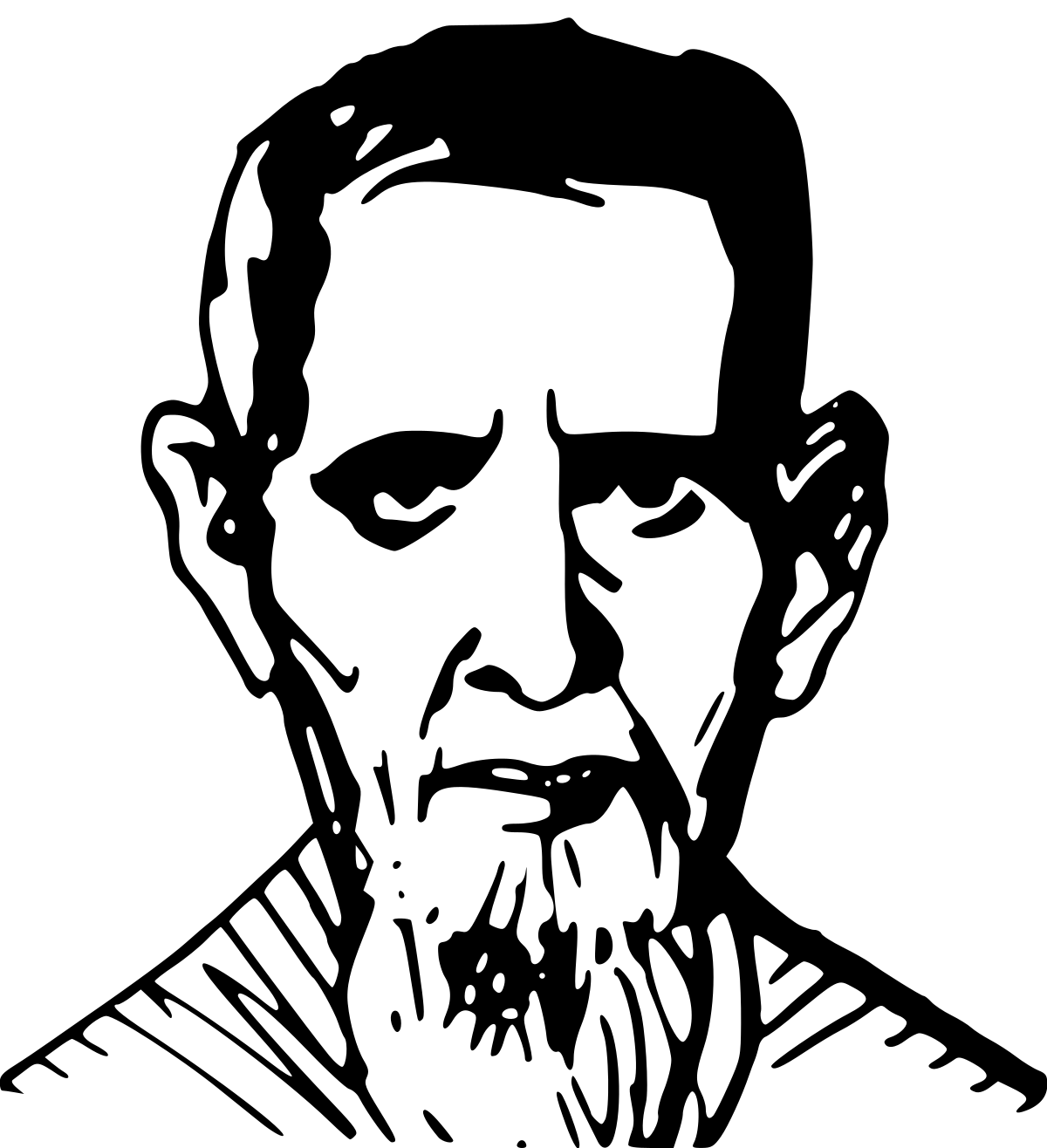
শাহাপরী মল্লিকজাদা’ ও ‘হাসান বানু’ প্রণয়ােপাখ্যান রচয়িতা মুহম্মদ আলী (১৭৭৩-এ জীবিত)। তিনি তিনটি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনা করেন। চট্টগ্রামের আজিমনগরের অন্তর্গত ইদিলপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। সৈয়দ নূরুদ্দিন (১৭৩০১৮০০) রচনা করেন ‘দাকায়েকুল হাকায়েক’ (১৭৯৬), “রাহাতুল কুলুব’ (১৭৪৬), ‘বুরহানুল আরেফীন’ বা ‘হিতােপদেশ’ (১৭৬৯) এবং ‘মুসার সওয়াল’ নামে চারটি গ্রন্থ। পণ্ডিতগণ সৈয়দ নুরুদ্দীনকে এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলে উল্লেখ করেন। ‘দাকায়েকুল হাকায়েক’-এ ইসলাম ধর্মীয় আচার আলােচিত হয়েছে ‘রাহাতুল কুলুব’-এ কিয়ামতের কথা, পিতা-মাতার হক, স্বর্গ-নরকের কথা, নামাজ রােজার কথা এবং মদ্য পানের কুফল ইত্যাদি আলােচিত হয়েছে। ‘বুরহানুল আরেফীন’ কাব্যের মূল বিষয় সুফীতত্ত্ব। ‘মুসার সওয়াল’ কাব্যে প্রগ্ন-উত্তরের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তা সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ ও তার নবী হযরত মুসার (আঃ) মধ্যে কথােপকথন বিবৃত হয়েছে। কবি জীবন মুহম্মদ তিনটি কাব্য রচনা করেন কামরূপ কুমার’, কুমারী কালাকাম’ ও ‘বানু হােসেন-বাহরাম গাের’। প্রথম দুটি কাব্য আজও অজ্ঞাত। জীবন মুহম্মদের কবিমানস উচ্চাঙ্গের শিল্প ভাবনায় পরিশ্রুত। বাক্য বিন্যাস, অলঙ্করণ ও বর্ণনাগুণে কবির কাব্য রসােত্তীর্ণ হয়েছে। কবি কেমন পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে এই পংক্তি হতে—
“কাঞ্চল বসন – চারু সুশােভন
আঞ্চল জড়িত মুতি।
সাজাইল কন্যা – ত্রিজগৎ ধন্যা
বিলেপি আমােদ অতি।”
সৈয়দ নাসির ‘বেনজীর বদর-ই-মুনীর’ (১৭৮৪-৮৫) শীর্ষক একটি কাব্য রচনা করেন। উর্দু কবি মীর হাসান দেহলভীর ‘সিহরুল বয়ান’ গ্রন্থের অনুসরণে কবি তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছেন। এতে যুবরাজ বেনজীর ও রাজকুমারী বদর-ই-মুনীরের প্রেম কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। মীর হাসানের গ্রন্থের দ্বিতীয় বাংলা অনুবাদক হলেন হাওড়া জেলার জালালদি নিবাসী কামরুদ্দিন। তিনি বিশ শতকের প্রথমার্ধে এটা রচনা করেন। চট্টগ্রামের কবি বালক ফকির রচনা করেন ‘ফায়দুল মুকতাদী’। মুসলিম জীবনের নিত্য করণীয় বিষয়ক গ্রন্থ ‘ফায়দুল মুকতাদী’। কাজী শিহাবউদ্দিন আঠার শতকের শেষভাগে ফারসিতে ফায়দুল মুকতাদী’ লেখেন। বালক ফকির সেটাই বাংলায় অনুবাদ করেন। বালক ফকিরের পীর ছিলেন ‘জ্ঞানসাগর’ প্রণেতা আলী রাজা।১২৫ দক্ষিণ রাঢ়ের তাজপুরের কবি আরিফ রচনা করেন ‘লালমনের কেচ্ছা’। কাব্যটিকে ‘সত্য নারায়ণের পুঁথি’ বা ‘সত্যপীরের পাঁচালী’ বলে ধারণা করা হয়। এ কাব্যের কাহিনিটি হচ্ছে, লালমন ও হােসেন শাহ বাদশাহর ভুলের জন্য সত্যপীরের রােষ ও তার পরিণামে উভয়ের অশেষ দুর্গতি। শেষ পর্যন্ত উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে সত্যপীরের মসজিদ তৈরি করে, ফলে উভয়ের মিলন সম্ভব হয়। কাব্যটি রােমান্টিক। নানা কারণে এ কাব্যে অলৌকিকতার প্রভাব দেখানাে হয়েছে। কাব্যের ভাষা প্রায় বিশুদ্ধ বলা চলে। কবি সম্ভবত আঠার শতকের শেষ পাদের লােক। এ অনুমানের ভিত্তি এই যে, আরিফের রচনায় শাহ গরীবুল্লাহ ও সৈয়দ হামজার প্রভাব নেই।
দানিশ নামের কয়েকজন কবির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। মুহম্মদ মুকীম তার ‘গুলে বকাওলি’ কাব্যে মুহম্মদ দানিশের নাম উল্লেখ করেছেন, যিনি আঠার শতকের মধ্যভাগে চট্টগ্রামের সুলুকবহরের অধিবাসী ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল আরব আলি। মুহম্মদ দানিশ ধার্মিক ও সৈয়দ আলাওলের সমকক্ষ পণ্ডিত ছিলেন। মুহম্মদ মুকীমের সঙ্গে তার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল এবং মুকীম সে সূত্রে মুহম্মদ দানিশের বাড়ি গিয়ে তার সঙ্গে কাব্যালােচনা করতেন। তিনি উপদেশাত্মক পঞ্চতন্ত্র সম্বন্ধীয় কাব্যগ্রন্থ ‘জ্ঞানবসন্তবাণী’ লেখেন। এ কাব্যটির পাণ্ডুলিপি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগ্রহ করেছিলেন। কাব্যটি ২য় থেকে ২৩শ অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল। মুহম্মদ দানিশ আরবি বা ফারসি কোনাে গ্রন্থ অবলম্বন করে তার কাব্যটি রচনা করেছিলেন। কাব্যটির সংক্ষিপ্ত রূপ—এক রাজপুত্র অজ্ঞাতনামা রাজকুমারীর প্রেমে উন্মত্ত হয়ে উঠলে তার চিত্ত উপশমের জন্য তার হিতৈষীরা নারীর চারিত্রিক দোষ ও নারী প্রেমের বিকার-অসারতা দেখাবার জন্য একটার পর একটা গল্প বলেছে। গল্পগুলাে সুন্দর ও নীতিগৰ্ভ। পড়তে পড়তে ‘আলেফ লায়লা’, ‘পঞ্চতন্ত্র’, ‘পুরুষ পরীক্ষা’, ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’, ‘বত্রিশ সিংহাসন’ এবং শেখ সাদীর গুলিস্তাঁ বােস্তার কথা মনে পড়ে।
মুহম্মদ দানিশ কাব্যাদর্শে ছিলেন মুহম্মদ খান ও সৈয়দ আলাওলের অনুসারী। তাই তাঁর কাব্যে এঁদের কাব্যকলার অনুরণন শুনতে পাই। মুহম্মদ দানিশ ‘লগ্নিকা ছন্দে’ নায়িকার রূপ ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে—
“বিমল ললাট বাল্য শশী
হেরি বলিহার দেবী শচী।
নিকলংক মুখ পূর্ণিমা চান্দ
ভাবক বান্ধিতে জোলক ফাণ্ড।
বক্রতা যুগল ভ্রু বিষম
রতিপতি চাপ না হয় সম।
পূর্ণ দেবাসন সুলােচনা
বাজে বনে গেল শশি-বাহনা।
দন্ত মুক্তপাঁতি তড়িত হাস
সুধামুখী সুধা বলিয়ে ভাষা
কমল অধর কুসুম দল
তাম্বুল বিহীন ধিক ধবল।
উরু সুগঠ কদলিকা ফুল
চম্পক কলিকা বিংশ অংগুল।”
মুহম্মদ দানিশের এ ধরনের বর্ণনায় আলাওলের প্রভাব সুস্পষ্ট।
আলাওলের ‘সিকান্দরনামা’র ভণিতা-রীতির অনুকরণ দেখা যায় মুহম্মদ দানিশের ভণিতায় –
“আইস গুরুমণি দেঅ সুরা
‘জীন’ বধ বাণী রচি পুরা।
হানাতি দানিশে সিঞ্চে অমৃত
রসিকে পান করে জানি হিতা।”
মুহম্মদ দানিশের এরূপ কবিত্বের ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় তার কাব্যের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। সর্বোপরি কবির কাব্যে যেসব কাহিনি বর্ণিত হয়েছে সেগুলি এযুগেও সুখপাঠ্য। মুহম্মদ দানিশ যে তার কাব্যকে ‘জ্ঞানবৃদ্ধি বাণীর পুস্তক’ বলে উল্লেখ করেছেন, তাতেও অত্যুক্তি নেই।
অপর কবি মােহাম্মদ দানেশ কয়েকটি পুঁথি রচনা করেন। পুঁথিগুলি হল ‘চাহার পরবেশ’, ‘হাতেম তাই’, ‘গুল সানুবর’ এবং ‘নূর-উল-ইমান’। তার ভাষা পুঁথির ভাষা হলেও তাতে আধুনিকতার ছোঁয়া রয়েছে। ঐতিহ্যমূলক বিষয়-ব্যবহারে শুধু নয়, পরিবেশ সৃষ্টিতেও যে মােহাম্মদ দানেশ সচেষ্ট ছিলেন তার পরিচয় দুর্লভ নয়। যেমন কবি মােহাম্মদ দানেশ লিখেছেন—
“দরজার দারােয়ান খাড়া নকিব চোপদার।
দেওয়ালে দেওয়ালে দেখি ফানুস বেলােয়ার।।
গালিচা দুলিচা কত গেদা সামিয়ানা।
শাটিন মখমল শােভে জরির বিছানা।।
পান-দান পিক-দান কত গােলাব-পাশ।
সুবাসে মহিত মন হইল উদাস।।”
(চাহার দরবেশ মােহাম্মদ দানেশ)
লক্ষণীয় যে, উদ্ধৃত এই স্তবকে রচয়িতার বর্ণনা-কৌশল যেমন মূর্ত হয়ে উঠেছে, তেমনি মুসলিম পরিবেশ এনে দিয়েছে নতুনত্বের আস্বাদ। কবি মােহাম্মদ দানেশের বর্ণনা-দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে উপমা ও চিত্রকল্পের যুগপৎ ব্যবহার-দক্ষতাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উপমা ও চিত্রকল্প এমনিভাবে বহু শক্তিমান মুসলিম কবির রচনায় সমভাবে হাত মিলিয়েছে।
মােহাম্মদ আকিল সম্বন্ধে খুব বেশী জানা যায় না। তবে তিনি আঠার শতকে বর্তমান ছিলেন বলে অনুমান। তাঁর কাব্যের নাম ‘মুসানামা’। হযরত মুসা (আঃ) তুর পর্বতে বসে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কাছে প্রর্ণ করে জগৎ ও জীবনের নানা গভীর তত্ত্ব জেনে নিতেন। এই সমস্ত বিষয় কাব্যটিতে ব্যক্ত হয়েছে। এই প্রণোত্তর পয়ার ছন্দে সার্থকভাবে প্রকাশ করায় আকিলের এই দক্ষতা প্রশংসার্হ। কৃষ্ণদাস কবিরাজের তত্ত্ব ব্যাখ্যানের সঙ্গে এর তুলনা চলে। কাব্যটিতে পাপ-পুণ্য সম্পর্কেও বর্ণনা দান করা হয়েছে। নারীর মাহাত্ম্য সম্পর্কেও কবির বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে—
“শরীরের অর্ধ অঙ্গ ঘরের রমণী।
দুই হস্তে দুনিয়াতে ভাবের ভাবিনী।।
নারী না থাকিলে পুরুষ কিছু না হএ।
নারীপুরুষ এক জানিআ নিশ্চিএ।।”
আকিলের শব্দ প্রয়ােগে প্রাচীনত্বের চিহ্ন বর্তমান, তা এই বর্ণনায় স্পষ্ট। মহসিন আলী সম্বন্ধেও আমরা খুব বেশি জানতে পারিনি। তবে আঠার শতকের এই কবির একটিমাত্র কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়, কাব্যটি হল ‘মােকাম মঞ্জিল’ কথা।
মধ্যযুগে নাথ সাহিত্যের খ্যতিমান স্রষ্টা ছিলেন শুকুর মাহমুদ (১৬৮০-১৭৫০)। কেউ কেউ কবির নাম শুকুর মােহাম্মদ (মুহম্মদ) বলেও উল্লেখ করেছেন। কবির পিতা শেখ আনার (আনােয়ার) ফকির, নিবাস ছিল রাজশাহীর রামপুর-বােয়ালিয়ার কাছে বালুরঘাটের সিন্দুরকুসুম গ্রাম। মুহম্মদ এনামুল হক তাঁকে ত্রিপুরার কবি বলে মনে করেন। ইসলাম, নাথ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম মতের সাথে সুপরিচিত এই কবি নিষ্ঠার সঙ্গে নাথ সাহিত্য রচনা করেছিলেন। তার একমাত্র কাব্য ‘গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস’। এটি একটি ঐতিহাসিক কাহিনি কাব্য। আঠার শতকের গােড়ার দিকে (১৭০৫) এ কাব্য রচিত হয়। ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী শুকুর মাহমুদের পুঁথি দিনাজপুর থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। পুঁথিটি শতাধিক বছরের পুরাতন। ত্রিপুরার রাজা গােপীচন্দ্র ও তার স্ত্রী রাণী ময়নামতীকে নিয়ে নাথ সাহিত্যে যে কাহিনি প্রচলিত আছে শুকুর মাহমুদের কাব্যের বিষয়ও উক্ত কাহিনি। পুরাণ শুনে শুনে কবি এ কাব্য রচনা করেন। কাব্যে বর্ণিত ময়নামতীর প্রখরা রূপটি আমাদের মুগ্ধ করে।
রূপকের অন্তরালে ভাব প্রকাশের যে হেয়ালিপূর্ণ রীতি চর্যাপদে দেখা যায় (১২০০ সালের পূর্বে রচিত) তার ছায়া নাথ সাহিত্যে (যেমন- শ্যামদাসের ‘মীন চেতন’ ও শেখ ফয়জুল্লাহর ‘গােরক্ষ বিজয়’) বিশেষ করে শুকুর মাহমুদের কাব্যেও দেখা যায়। গুপিচন্দ্রের ‘সন্ন্যাস’-এ বলা হয়েছে—
“ভরিল এন্দুরে নাও বিড়াল কান্ডারী।
শুতিয়া আছেন ব্যঙ্গ ভুজঙ্গ প্রহরী।।
বদল প্রসব হইল গাই হইল বাঞ্জা।
বাছুরেক দোহাএ তাহার দিন তিন সাঞ্জা।।”
কিছু চর্যার সঙ্গে এই উদাহরণের যথেষ্ট ভাবগত ঐক্য লক্ষ করা যায়। চর্যাপদের অনেক কবি নাথ সম্প্রদায়েরও গুরু ছিলেন। এছাড়া বাংলার জনসমাজের সাংস্কৃতিক জীবনে সহজিয়া বৌদ্ধ মতাদর্শের প্রভাব রাতারাতি বিলীন হয়ে যাবার মত বিষয় ছিল না। এসব কারণেই সম্ভবত লােকমুখে প্রচলিত কাব্য বা দুপ্রাপ্য কোনাে পুঁথি থেকে নাথ সাহিত্যের কবিদের উপর চর্যাগীতির কোনাে বিশেষ অংশের প্রভাব পড়া সম্ভব হয়েছিল। শুকুর মাহমুদও এর ব্যতিক্রম ছিল না।
উপমার ব্যবহারে শুকুর মাহমুদ দক্ষ ছিলেন। রাজা গুপিচন্দ্রের স্ত্রী ময়নামতীর গ্রীবাকে তিনি ‘হংসরাজের গ্রীবা’র সঙ্গে তুলনা করেছেন। রাণীদের রূপের বর্ণনা তিনি এভাবে করেছেন—
“বার বৎসরের সবে তের নাহি পুরে।
যৌবনের ভারে নারী হাটিতে না পারে।।”
গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস যাত্রার আয়ােজনে রাণীদের (রাজা গুপিচন্দ্রের চার স্ত্রীর কথা উল্লেখিত হয়েছে। গ্রিয়ার্সন সংগৃহীত গীতে আছে ছয় কুড়ি বা ১২০ স্ত্রী ও নগেন্দ্রনাথ বসু সংগৃহীত গীতে আছে শত স্ত্রীর উল্লেখ) মনঃকষ্টের কথায় রয়েছে। আধুনিকতার ছোঁয়া। যেমন—
“পতি যাবে যুগী হইয়া ঘর রব কারে লৈয়া
চারি রাণী খাইব গরল।।”
রাজা গুপিচন্দ্রের যুদ্ধসজ্জার বর্ণনাও আধুনিকতার ছোঁয়া রয়েছে—
“হস্তী ঘােড়া সাজে আর মহা মহা বীর
সাজিল অপার সৈন্য আঠার উজির।
বাষট্টি নাজির সাজে তেষট্টি শিকদার।”
এভাবে কবির রচনা অনুপম কাব্যগুণে পল্লবিত হয়ে নানা লােকরঞ্জনে সহায়ক হয়েছে।১২৬
মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, আব্দুস সামাদ আঠার শতকের শেষপাদের কবি। তাঁর বাড়ি চট্টগ্রামের সুলকবহর। তিনি পারস্যের বিখ্যাত কবি শেখ সাদীর ‘গুলিস্তা ও বােস্তা’ থেকে প্রেমমূলক কাহিনিগুলি বাংলায় অনুবাদ করেন।১২৭ অজ্ঞাতনামা কবি জাফর, তিনি একটি মর্সিয়া শ্রেণির কাব্য রচনা করেছিলেন, কাব্যটি ‘শহীদ-ই-কারবালা’। কাব্যটিতে কবির স্বাভাবিক কবি প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে। আঠার শতকের কোনাে এক সময়ে কাব্যটি রচিত হয়। আঠার শতকের আর এক কবি ছিলেন সিলেটের আব্দুল হামিদ। সংগ্রাম হােসেন নামে তিনি একটি কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যে কারবালা প্রান্তরে ইমাম হােসেনের (রাঃ) করুণ মৃত্যুবরণ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। কাব্যের ভূমিকায় কবি আব্দুল হামিদ ‘মক্তুল হােসেনকে’ আদর্শ বলে উল্লেখ করেছেন। কবি শেখ আশরাফ মধ্যযুগে এদেশে বাংলা ভাষার মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষা দানের সহায়ক গ্রন্থ ‘কিফায়াতুল মুসলেমিন’ (১৭৮৮) রচনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বিভিন্ন নামাজের ফজিলত বর্ণনা করাই এ কাব্যের উদ্দেশ্য। এ গ্রন্থে শবে কদর নির্ণয় সম্পর্কে কিছু বিরল তত্ত্ব ও তথ্য শেখ আবুল হাসানের বরাত দিয়ে পরিবেশন করা হয়েছে। পয়লা রমজান মঙ্গলবার হলে শবে কদর হবে সাতাইশে রমজান, বুধবার হলে হবে বাইশে, বৃহস্পতিবার হলে হবে পঁচিশে, শুক্রবার হলে হবে ছাব্বিশে এবং শনিবার হলে শবে কদর হবে তেইশে রমজান। কবি আঠার শতকের গােড়ার দিকে বর্তমান ছিলেন।
কবি এতিম আলমের কাব্যের নাম আবদুল্লাহর ‘হাজার সওয়াল’। কাব্যটি আরবি ফারসি কাহিনির পল্লবিত বাংলা রূপান্তর। ইহুদি রাজা আবদুল্লাহর ইসলামধর্ম গ্রহণের কাহিনি এখানে বর্ণিত হয়েছে। আঠার শতকের শেষার্ধে রচিত হয় ‘মল্লিকদার পুঁথি’, পুঁথি খণ্ডিত। গল্পাংশ দেখে মনে হয় এর কাহিনি মৃগাবতী উপাখ্যান ধরনের। কবি অজ্ঞাতনামা, পুস্তকটি অমুদ্রিত। কবি বলেন—
“ফারসি ভাষে ন বুঝে লােক বুঝিতে কারণ
পঞ্চালির ছন্দে তবে করিল রচন।”১২৮
কবি হাজী আলী আঠার শতকের প্রথমার্ধে ফারসি গ্রন্থ অবলম্বনে রচনা করেন ‘মওতনামা’। এতে জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত যা ঘটতে পারে তার বর্ণনা আছে। কবি রামু অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন।১২৯ আঠার শতকের প্রথম দিকে নােয়াখালি-ফেনি অঞ্চলের ভূস্বামী শামসের গাজীর কীর্তিকাহিনি নিয়ে এই শতকের একেবারে শেষপাদে ‘শামসের গাজীনামা’ রচনা করেন কবি শেখ মনােহর। চরিত কাব্যে এক জমিদারের জীবনী বিধৃত হওয়া একটা নতুন ব্যাপার। আঞ্চলিক ইতিহাসের কিছু মিশ্র বিবরণ ব্যতীত এর মধ্যে অন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই।১৩০
আকবর আলী সম্ভবত আঠার শতকের শেষপাদে চট্টগ্রামে বর্তমান ছিলেন।১৩১ তাঁর গ্রন্থগুলি হল হাদিসের কথা, চোরার হেকায়েত, সখিনার বারমাস, হানিফার বারমাস ইত্যাদি। কবির দুটি পদও সংগৃহীত হয়েছে। প্রথম পদ আহমদ শরীফ সংকলিত মুসলমান কবির ‘পদসাহিত্য’ গ্রন্থের ১৪৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে। দ্বিতীয় পদ মিলেছে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংকলিত ‘প্রাচীন পুঁথির বিবরণ’ (১ম খণ্ড, পৃ. ৩০) হতে। এই দুটি শ্যামা সংগীতের (‘শলখা’ ও ‘মালিনী’ নামাঙ্কিত) মধ্য দিয়ে ভক্ত হৃদয়ের আকুতি ফুটে উঠেছে। এই আকুতির আন্তরিকতা আরও তীব্র হয়েছে ‘সে পদ নি পাব নিরে’ পদাংশে, প্রাঞ্জল ভাষায় ঘটেছে তার প্রকাশ।১৩২
আঠার শতকের শেষপাদে আবদুল আলিম রচনা করেন মােহাম্মদ হানিফার লড়াই’। আবদুল আলিমের চেয়েও শক্তিশালী কবি ছিলেন নজর আলী। তাঁর রচিত একটি অখণ্ড পুঁথি পাওয়া গেছে। পুঁথিটি ১০৪ পত্রে সমাপ্ত। কবির আবির্ভাবকাল অজ্ঞাত। উত্তরবঙ্গের কবি আবদুস সােবহান। তাঁর মুদ্রিত কাব্যের নাম ‘ইমাম সাগর’, এটি সাধু ভাষার রচিত। আঠার শতকের শেষপাদে কবি এটা রচনা করেন। সেকালের পাঠকদের করুণ রসের চেয়ে বীর রসে আকর্ষণ ছিল। পদাবলী ও রাগতালনামা রচয়িতা চম্পা গাজীর নিবাস চট্টগ্রামের সতরপটুয়া গ্রাম। পিতা আবদুল কাদির। চম্পা গাজী পণ্ডিত ও হাড়িদের সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন। তিনি কাজী বদিউদ্দিনের বাংলা শিক্ষক ছিলেন।১৩৩ কাজী বদিউদ্দিন আঠার শতকের লােক, নিবাস ছিল চট্টগ্রামের পটিয়া থানা সংলগ্ন বাহুলী গ্রাম। তিনি কায়দানী কেতাব’ ও ‘সিফাত-ই-ইমান’ প্রভৃতি বাংলা কাব্যের প্রণেতা। ‘কায়দানী কেতাব’ শরিয়ত বিষয়ক গ্রন্থ। এখানে প্রয়ােত্তরে ওজু-নামাজ প্রভৃতির নিয়মাবলী আলােচিত হয়েছে। সিফাত-ই-ইমান ইসলামি বিধাস বা আকিদা বিষয়ক গ্রন্থ। এখানে কবির আত্মপরিচয় ও শিক্ষকদের নাম আছে। আরাকান রাজ্যের কবি আবদুল গণি রচনা করেন ‘ফালনামা’। ভাগ্যনির্ণয় পদ্ধতি ও দুর্ভাগ্য এড়ানাের উপায় ফালনামায় বর্ণিত। বাংলা ফালনামা ফারসি-উর্দু গ্রন্থের অনুবাদ বলে দাবী করা হয়। যেমন আবদুল গণি বলেছেন,
“কিতাবেতে দেখি ফালনামা বিবরণ
করিলু বাঙ্গালা ভাষা পয়ার বন্ধন।”১৩৪
রংপুরের কবি বুরহানউল্লাহ আঠার শতকে রচনা করেন ‘কেয়ামতনামা’ (১৭৪৭)।১৩৫
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালােচনা করলে লক্ষ করা যায় যে, যতই সময় পেরিয়েছে বাংলা সাহিত্যচর্চা ততই এগিয়েছে। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকের আগে বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চার নিদর্শন সামান্যই পাওয়া যায়। মধ্যযুগের সূচনার পর বাঙালি কবিদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’র (১৩৫০) কবি বড়ু চণ্ডীদাস প্রাচীনতম বলে অনেকে বিবেচনা করেন। তারই সমকালীন ছিলেন শাহ মুহম্মদ সগীর (১৩৩৯-১৪১৯)। এ সময় হতে মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপােষকতাই শুধু নয়, মুসলিম সাহিত্যিকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যচর্চা নতুন গতি লাভ করেছিল। কৃত্তিবাস, মালাধর বসু প্রমুখের সাহিত্যচর্চার পেছনেও মুসলিম শাসকদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপােষকতা ছিল। পরবর্তীতে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে আমরা ক্রমান্বয়ে স্ফীত হতে দেখি। পূর্ববর্তী শতাব্দী থেকে পরবর্তী শতাব্দীগুলােতে বিষয় বৈচিত্র্যে যেমন অগ্রগতি এসেছিল, তেমনি গ্রন্থাদির সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বেড়েছিল।
পুরাে মধ্যযুগ ধরেই অগণিত হিন্দু কবিদের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক মুসলিম কবি বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়ােগ করেছিলেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যথার্থই বলেছেন,
“মধ্যযুগের সাহিত্য কিংবা সংস্কৃতির ইতিহাস রচনা তৎকালীন মুসলমান কবি ও লেখকদের আলােচনা ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না।…মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের দান হিন্দুর অপেক্ষা কোনও অংশেই হীন নহে, বরং সাহিত্যে বিমানবতা এবং বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য আমদানীতে মুসলমান কবিগণ হিন্দুদিগকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন।”১৩৬
মুসলমান কবিদের সবচেয়ে বড় অবদান কাহিনি কাব্য বা ‘রােমান্টিক’ কাব্যধারার প্রচলন। পুরাে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বৌদ্ধ-হিন্দু রচিত বাংলা সাহিত্য যেখানে ‘দেব-দেবী নির্ভর’, দেব চরিত্রই যেখানে প্রধান, মানুষ যেখানে দ্বিতীয়িক বিবেচ্য— সেখানে মুসলমান-রচিত কাব্য-সাহিত্যে মানুষই হয়ে ওঠে প্রধান। সামগ্রিকভাবে বিষয়বস্তুর দিক থেকে মুসলমানদের সাহিত্য হিন্দুদের সাহিত্য থেকে বহুলাংশে স্বতন্ত্র (ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক কারণে) বৈচিত্র্যমণ্ডিত ও কৌতূহলােদ্দীপক কাব্যধারা এভাবেই মধ্যযুগে মুসলমান বাঙালির দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। কাহিনি কাব্য ও ‘ধর্মীয়-সাহিত্য’ যদিও তাদের হাতে প্রাধান্য লাভ করেছে, তবু হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি-সমন্বয়মূলক সাহিত্যও রচিত হয়েছে বহুল পরিমাণে, এমনকি চৌতিশা এবং জ্যোতিষ ও সঙ্গীতশাস্ত্রীয় কাব্যও রচিত হয়েছে।
মধ্যযুগের এসব কাব্যে উপমা ও চিত্রকল্পের ব্যবহারে কোথাও কোথাও আমরা সৃজন ক্ষমতার বিচ্ছুরণ লক্ষ করি বটে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, মুসলিম কবিরা বর্ণনা, উপমা ও চিত্রকল্পের ব্যবহারে গতানুগতিক পদ্ধতিকেই অনুসরণ করেছেন। বিশেষত বর্ণনা ও উপমা সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা লক্ষণীয় হলেও, চিত্রকল্পের ব্যবহার-কৌশল তেমন দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। কিন্তু শক্তিমান মুসলিম কবিরা নতুনত্ব সৃষ্টির প্রয়াসও যে করেননি এমন নয়। এই নতুন প্রয়াসের পথ ধরেই সেই পঞ্চদশ শতক হতে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলা কাব্য নানাভাবে পরিপুষ্ট হয়েছে।
কাহিনি-বর্ণনা, ভাষা, শিল্প ভাবনা ও উপমা সৃষ্টিতে প্রাগাধুনিক মুসলিম কবিরা ক্রমান্বয়েই দক্ষতা দেখিয়েছেন। পঞ্চদশ শতকের কবি শাহ মুহম্মদ সগীর ও জায়েনউদ্দিন, ষােড়শ শতকের কবি সৈয়দ সুলতান, হাজী মুহম্মদ, সাবিরিদ খান, বাহরাম খান, শেখ ফয়জুল্লাহ, মুজাম্মেল এবং সপ্তদশ শতকের কবি সৈয়দ আলাওল, দৌলত কাজী, আবদুল হাকিম, আবদুন নবী, শেখ মুত্তালিব প্রমুখ কবিরা কি কবিত্বশক্তি কি লালিত্যময় ভাষাবৈশিষ্ট্য সবকিছুতেই তাদের অভিনবত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। আঠার শতকের শক্তিমান কবি শাহ গরীবুল্লাহর রচনায়ও আমরা লক্ষ করি—
“আল্লার কুদরতে বাদশার ঘরেতে
ফরজ হইল এক, চঁাদের ছুরত
ইউসুফ মূরত রূপেতে নাহিক সীমা।।
হৈল সাদী গীত সবে খােসালাত
রশেষ কাপড় জামা।”
সৌন্দর্য বর্ণনায় নয়, রূপকের ব্যবহারেও প্রাগাধুনিক মুসলিম কবিরা ছিলেন বিশেষ সচেষ্ট। শিল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রেও তারা স্বতন্ত্র ধারার বুনিয়াদ রচনা করে গেছেন। কবি সৈয়দ হামযা ‘হাতেম তাই’ কাব্যে লিখেছেন—
“বসিয়া পানির ধারে
যে কেহ পিয়াসে মরে
তার বড়া নাই আভাগিয়া।।
দেখাকে না দেখা ভাল
দেখে যদি জান গেল
তবে কাম নাহি দেখা দিয়া।।”
এরপর উনিশ শতকের প্রারম্ভ থেকেই নতুন যুগের সূচনা। বাংলা সাহিত্যে এক নতুন উপলব্ধি এই যুগের বাহন। নবযুগ তথা আধুনিক যুগের সেই নতুন উপলব্ধিতে গতি সঞ্চার করে গদ্য চর্চা। প্রবন্ধ সাহিত্যের উন্মেষ ঘটে গদ্যে এবং কাব্যগীতির ধারায় গীতি কবিতায় মননধর্মী রূপায়ণ এই নবযুগেরই সাহিত্য বৈশিষ্ট্য। উনিশ শতকের শেষপাদ তথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) থেকে এই যুগের ব্যাপক প্রচার-প্রসার শুরু হয়। তবে এই যুগকে তার সৃষ্টির বিশালতায় পূর্ণ করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করেছে মুসলিম বাংলা সাহিত্যের প্রাগাধুনিক যুগ। এই প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, নতুনের ঐশ্বর্য সৃষ্টির প্রেরণা আসে মুখ্যত অতীতকে তথা প্রাগাধুনিক যুগকে তার স্বমহিমায় গৌরবান্বিত করার প্রবণতার মধ্য দিয়ে।
বাকি পর্বগুলি পড়ুন,
১. মধ্যযুগে মুসলিম কবিদের অবস্থান ও বাংলা সাহিত্যে কাব্যচর্চার ক্রমবিকাশ [পর্ব ১]
২. মধ্যযুগে মুসলিম কবিদের অবস্থান ও বাংলা সাহিত্যে কাব্যচর্চার ক্রমবিকাশ [পর্ব ২]
৩. মধ্যযুগে মুসলিম কবিদের অবস্থান ও বাংলা সাহিত্যে কাব্যচর্চার ক্রমবিকাশ [পর্ব ৩]
৪. মধ্যযুগে মুসলিম কবিদের অবস্থান ও বাংলা সাহিত্যে কাব্যচর্চার ক্রমবিকাশ [পর্ব ৪]
৫. মধ্যযুগে মুসলিম কবিদের অবস্থান ও বাংলা সাহিত্যে কাব্যচর্চার ক্রমবিকাশ [পর্ব ৫]
তথ্যসূত্রঃ
- ১১১. মুফাখখারুল ইসলাম, কলমী পুথি জরীপ, বাংলা একাডেমি পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৭৫, ঢাকা, পৃ. ৭৩।
- ১১২. মুফাখখারুল ইসলাম, কলমী পুঁথি জরীপ, প্রাগুক্ত, ১৩৭৫, পৃ. ৭১।
- ১১৩. আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, খণ্ড-২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৩।
- আরও বহু পীর পাঁচালীর সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন- ষােল শতকে শেখ ফয়জুল্লাহ লেখেন ইসমাইল গাজীর চরিত ও মাহাত্ম্য কথা। জাফর খাঁ গাজীর মাহাত্ম কথা কেউ লিপিবদ্ধ করেননি বটে, তবে বন্দনাংশে পশ্চিমবঙ্গের কবিগায়েনরা এখনও তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। শান্তিপুরের কবি মােহাম্মদ মােজাম্মেল হকের (১৮৬০-১৯৩২) ‘দরাফ খাঁ গাজী’ নামে কিংবদন্তি নির্ভর একটি পুস্তিকা আছে। বহু কিংবদন্তির নায়ক বদর পীর আরব দেশ থেকে আগত। সতের শতকের কবি মােহাম্মদ খানের বংশ পরিচিতি অংশে বদর পীরের উল্লেখ রয়েছে। শাহ বদিউদ্দিন মাদারকে নিয়ে কবি আবদুর রহিম রচনা করেছিলেন শাহ মাদারের নিকট শাহ মালেকের ‘সওয়াল’ নামের পুঁথি।। আবদুল মজিদ খান শাহ সুলতান বলখির অলৌকিকবহুল চরিতকথা রচনা করেছিলেন। বসিরহাটের হাড়ােয়ার পীর গােরাচঁাদ ওরফে সৈয়দ আব্বাস আলিকে নিয়ে কবি শেখ লাল শাহ এবং শেখ জয়েনউদ্দিন লেখেন “গােরাচঁাদ পুঁথি। মেদিনীপুর জেলার হিজলীর শাসক তাজ খান মসনদ-ই-আলাকে নিয়ে ‘মছলন্দীর গীত’ রচনা করেন কবি জয়েনউদ্দিন। হাড়ােয়ার আর এক পীর ছিলেন পেয়ার শাহ। লাল শাহ পেয়ার শাহকে নিয়ে লিখেছিলেন পেয়ার শাহ চরিতকথা। সতের শতকের পীর মুবারক গাজীকে নিয়ে ফকির মুহম্মদ লিখেন মােবারক গাজী পুঁথি। কলিমুদ্দিন গায়েনও লেখেন গাজী সাহেবের গান বা মােবারক গাজীর উপাখ্যান। এছাড়াও আমিরউদ্দিন ও শাহ মােহাম্মদ খােন্দকার রচনা করেন যথাক্রমে মনসুর হল্লাজ চরিত ও শাহ কলন্দর চরিত। এ সমস্ত পীর সকলেই ছিলেন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। দেখুন-আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, খণ্ড-২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৫-৭৩।
- ১১৪. রাজিয়া সুলতানা সম্পাদিত, গুলে বকাওলি, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭০। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে দেখুন- এ এম হাবিবুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যে উপাখ্যান গুলে বকাউলী, সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৬৪, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আরও দেখুন-রাজিয়া সুলতানা, নওয়াজীস খান ও গুলে বকাওলী, বাংলা একাডেমি পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৭২, ঢাকা।
- ১১৫. আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৩১৩। আরও দেখুন- ক্ষেত্র গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫।
- ১১৬. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, কবি শমসের আলীর ‘রেজওয়ান শাহ উপাখ্যান’, বাংলা একাডেমি পত্রিকা, ১৪০৩, ঢাকা।
- ১১৭. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা, খণ্ড-২, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬।
- ১১৮. মাহে নও পত্রিকা, ফাল্গুন ১৩৫৮, ঢাকা। আরও দেখুন-মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩। আজহার ইসলাম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৫।
- ১১৯. সাহিত্যিকী পত্রিকা, রাজশাহী বিথবিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, ১৩৯৮, রাজশাহী, পৃ. ৬৯-৭০ আরও দেখুন-আবদুল করিম, বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০।
- ১২০.পুঁথি পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬।
- ১২১. আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, খণ্ড-২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।
- ১২২. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, রাগতালনামা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৭।
- ১২৩. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা, খণ্ড-২, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮।
- ১২৪. অবসর, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩১৪।
- ১২৫. আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, খণ্ড-২, পৃ. ৩৩২-৩৩।
- ১২৬. কবি শুকুর মাহমুদের কাব্যকৃতি সম্বন্ধে জানতে দেখুন-খন্দকার মাহমুদুল হাসান, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১২৩-১২৫, মাহবুবুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০-৬১। আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, খণ্ড-১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২-৬৩। ক্ষেত্র গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮, আজহার ইসলাম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮১। শুকুর মাহমুদের পাঁচালী ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালীর সম্পাদনায় একটি (১৯২৫), দীনেশচন্দ্র সেন, বিধের ভট্টাচার্য ও বসন্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় একটি (১৯২৪) এবং এ কে এম যাকারিয়ার সম্পাদনায় অন্য একটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৪ সালে। এছাড়া দুর্লভ মল্লিকের ‘গােপীচন্দ্রের সন্ন্যাস’ শিবচন্দ্র শীলের সম্পাদনায় প্রকাশিত (১৩৮০)। এই কবি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায়নি। তার পুথির অনুলিপি কাল ১৮০০ সাল, কলকাতার এন্টালি থেকে সংগৃহীত। এতে আখ্যান পল্লবিত নয়, তবে যােগতত্ত্বের ব্যাখ্যার প্রবণতা খুব বেশি। তাছাড়া নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও বৈকুণ্ঠনাথ দত্তের সম্পাদনায় ভবানী দাসের ‘ময়নামতীর গান’ ১৩২১ সনে ঢাকা সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়। অপর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় কলকাতা বিধবিদ্যালয় হতে। পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন ও মুদ্রণের জন্য পাণ্ডুলিপি তৈরি করে দিয়েছিলেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। আর সম্পাদক হিসেবে ছাপা হয়েছিল দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখের নাম। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ এক্ষেত্রে প্রবঞ্চিত হয়েছিলেন (ভূমিকা নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত, ‘ময়নামতীর গান’)। দেখুন আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, খণ্ড-১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২।
- ১২৭. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা, খণ্ড-২, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬। আরও দেখুন- আজহার ইসলাম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ), প্রাগুত্ত(, পৃ. ৩৮৮।
- ১২৮. পুঁথি পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৬-২৭।
- ১২৯. পুঁথি পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩২-৩৪।
- ১৩০. ক্ষেত্র গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩-৯৪।
- ১৩১. আহমদ শরীফ, মুসলমান কবির পদসাহিত্য, ঢাকা, ১৯৬১, পৃ. ১৬০। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, কতিপয় প্রাচীন শ্যামা সংগীত, সােনার বাংলা পত্রিকা, ১৯ আথিন ১৩৫৮, পৃ. ১০।
- ১৩২. কিন্তু বৈষ্ণব পদকর্তা আর একজন আকবর আলী আছেন। তিনি শ্রীহট্টবাসী ও বিংশ শতাব্দীর লােক। তিনি এস্কে দিওয়ানা’, ‘ফানায়ে জান’ ও ‘যৌবন বাহার’ নামে তিনটি বই লেখেন। এগুলি বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। আকবর আলীর উনত্রিশটি বৈষ্ণব পদ সংগৃহীত হয়েছে। দেখুন- যতীন্দ্রমােহন ভট্টাচার্য, বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-১২ ও ৩৫২-৫৫।।
- ১৩৩. আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, খণ্ড-২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১। আরও দেখুন-পুঁথি পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫২।
- ১৩৪. আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, খণ্ড-২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৬-৭৭।
- ১৩৫. আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, খণ্ড-২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০০।
- ১৩৬. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা, খণ্ড-২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭০।
‘নবজাগরণ’ অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপ্লিকেশনটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।
![]()
‘নবজাগরণ’ এর টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।
‘নবজাগরণ’ এর ফেসবুক পেজে লাইক করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

 নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা
নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা
![মধ্যযুগে মুসলিম কবিদের অবস্থান ও বাংলা সাহিত্যে কাব্যচর্চার ক্রমবিকাশ [পর্ব ১]](https://nobojagaran.com/wp-content/uploads/2021/06/watch-4638673_1920-750x375.jpg)