রাজনৈতিক একতাঃ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে গুপ্ত যুগ বা সাম্রাজ্যই শেষ সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। পরবর্তীকালে হর্ষবর্ধনের পুষ্যভূতি, গুর্জর-প্রতীহার, পাল, রাষ্ট্রকূট ও চোল সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল বটে, কিন্তু আয়তন, স্থায়িত্ব ও মানমর্যাদার দিক দিয়ে এদের কোনটি গুপ্ত সাম্রাজ্যের সমকক্ষ নয়। গুপ্তদের শাসনামল প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। অশােকের সাম্রাজ্যের মতাে বিশাল না হলেও সভ্যতার ক্ষেত্রে গুপ্তগণ উল্লেখিত শক্তির তুলনায় অনেক বেশি অগ্রসর। উত্তর-পশ্চিম ভারত বা সুদূর দাক্ষিণাত্যে প্রত্যক্ষভাবে শাসন সম্প্রসারণে তারা সফল হননি; বৈদেশিক আক্রমণ ও গৃহবিবাদে তাঁদের রাজ্যটি শেষ পর্যন্ত ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়- এ হেন দুর্ভাগ্য ও দুর্বিপাক সত্ত্বেও গুপ্তগণ দুইশত বৎসর যাবত আর্যাবর্তে একতার উৎসরূপে কাজ করেন।
গুপ্তদের গৌরব রাজ্যের বিশালতা ওপর নির্ভর করে না; বরং উন্নত শাসন ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক ঐক্যের চেতনাই এর অন্যতম আকর্ষণ। দয়া-মায়া, সদ্বিবেচনা ও সহৃদয়তার সাথে দৃঢ়তা মিশ্রিত এমন সুশাসনের দৃষ্টান্ত আগে আর কোনদিন দেখা যায়নি।
সাহিত্যঃ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে গুপ্ত যুগের স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁদের দান অবিস্মরণীয়। অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টি এবং সংস্কৃত ভাষার উৎকর্ষের জন্য গুপ্ত যুগ সুবিখ্যাত। সমুদ্রগুপ্ত নিজে উচ্চশ্রেণীর কবি এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কিংবদন্তীর রাজা বিক্রমাদিত্য হলে তাঁরা ছিলেন সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বৈদেশিক রাষ্ট্র ও লেখকগণের মধ্যে পারস্পরিক ভাব বিনিময় গুপ্ত রাজ্যে সাহিত্য-প্রতিভা বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। সম্রাট অশােকের সময় থেকে সংস্কৃত চর্চার প্রমাণ পাওয়া যায়; তবে গুপ্তদের শাসনকালে এটি রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পায়। সমুদ্রগুপ্তের সভাসদ বীরসেন বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। হরিষেণ রচিত এলাহাবাদ প্রশস্তির ভাষা অত্যন্ত উন্নতমানের এবং উপভােগ্য। গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রায়ও সংস্কৃত বর্ণমালার ব্যবহার লক্ষণীয়। মহাকবি কালিদাস দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় থেকে ‘রঘুবংশ’, ‘মেঘদূত’, ‘কুমারসম্ভব’, ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম্’ ও ‘মালবিকাগ্নিমিত্র’ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ‘রঘুবংশ’ মহাকাব্য সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সামরিক প্রতিভার স্বাক্ষর; ‘কুমার সম্ভব’ হিন্দুদেবতা শিবের প্রতি গুপ্তদের ভক্তি-পুস্পাঞ্জলি, ‘মেঘদূত’ চমৎকার গীতিকবিতা, ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নাটকগুলাের অন্যতম এবং ‘মালবিকাগ্নিমিত্র’ পুষ্যমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্রের জীবন-কাহিনী অবলম্বনে রচিত একটি ঐতিহাসিক নাটক। এই যুগে অপর যে সকল কবি, সাহিত্যিক ও নাট্যকারের দানে প্রাচীন সাহিত্য ভান্ডার সমৃদ্ধ তাঁদের মধ্যে ‘মুদ্রারাক্ষস’ প্রণেতা ‘বিশাখদত্ত’, ‘মৃচ্ছকটিক’ প্রণেতা শূদ্রক, ‘শব্দকোষ’ বা অভিধান লেখক অমরসিংহ, বৌদ্ধ লেখক বসুবন্ধু ও দিগনাগ, জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট, বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্ত প্রধান। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীনকালে যে উচ্চমার্গীয় নাট্যসাহিত্য লেখা হতাে ‘মৃচ্ছকটিক’ তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। বিশাখদত্ত রচিত ‘মুদ্রারাক্ষস’ এবং ‘দেবী চন্দ্রগুপ্তম’ নাটকের কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।
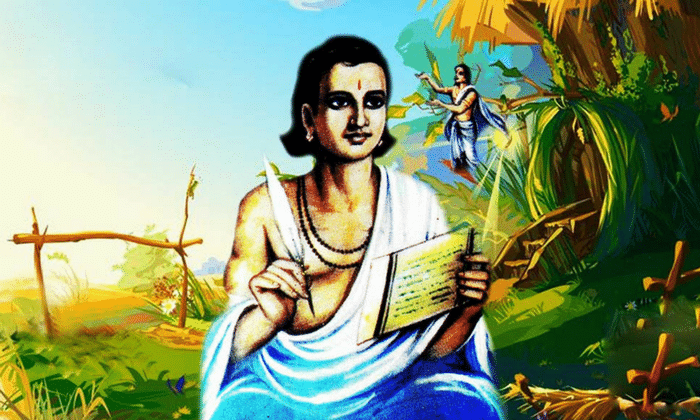
গুপ্ত যুগ ধর্মীয় সাহিত্যের ইতিহাসেও গুরুত্বপুর্ণ।এই যুগেই মহাভারত ও পুরাণগুলাে সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন হয়। এগুলাে নব-সম্পাদনা ও রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধ ধর্মের বিপরীতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি জনগণকে। আকৃষ্ট করা। যাহােক, কিংবদন্তী, গল্প, ধর্মোপদেশ, নীতিমালা ও আধ্যাত্মিক দর্শন ছিল পৌরাণিক সাহিত্যের প্রধান সম্পদ। ব্রাহ্মণগণ সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এগুলােকে নতুন করে সহজ সংস্কৃতে পরিবেশন করেন। আজকাল আমরা বিষ্ণুপুরাণ, গরুড়পুরাণ ও স্কন্ধপুরাণ প্রভৃতি যেসকল সাম্প্রদায়িক পুরাণ দেখতে পাই সেগুলােও তখন জন্মগ্রহণ করে; বিবর্তনবাদের ধারা অনুসরণ করে স্মৃতি বদলে যায় এবং মনুসংহিতা ও যাজ্ঞবল্ক্য বর্তমান আকারে প্রকাশিত হয়।
গণিত, বিজ্ঞান, ভূগােল, জ্যোতির্বিদ্যা
গুপ্তযুগের অপর একটি গৌরবের দিক হচ্ছে গণিত, বিজ্ঞান, ভূগােল ও জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতি। এ সকল বিষয়ের প্রধান দিকপাল ছিলেন আর্যভট্ট। অনেকেই তাঁকে ‘ভারতীয় নিউটন’ বলে আখ্যা দেন। তিনি প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে মন্তব্য করেন যে, পৃথিবী আপন মেরুদন্ডের ওপর থেকে সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে। তিনি আহ্নিক গতি ও বার্ষিকগতিও আবিষ্কার করেন। সংখ্যা গণিতে ‘0’ (শূন্য) সংখ্যার প্রচলনের মাধ্যমে অঙ্কশাস্ত্রে বৈপ্লবিক যুগের সূচনা তাঁর অন্যতম কীর্তি। এই যুগে দশমিক পদ্ধতির আবিষ্কারের ফলে মানব জাতির অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। পরবর্তীকালে আরবজাতি এই উপমহাদেশ হতে শূন্য ও দশমিকের ব্যবহার শিখে তা ইউরােপে প্রচার করেন। বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞান যে অসম্ভবকে সম্ভব করেছে শূন্যের প্রচলন তার অন্যতম প্রধান কারণ। তাই একথা বলা অমূলক নয় যে, গণিত শাস্ত্রে জগৎ প্রাচীন ভারতের কাছে একান্তভাবেই ঋণী। বরাহমিহির (৫০৫-৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে) গ্রিক বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। তিনি গ্রিসের শিল্প ও যন্ত্রবিদ্যা হতে কতগুলাে শব্দ চয়ন করে ভারতীয় ভাষায় ব্যবহারের মাধ্যমে একে যথেষ্ট শক্তিশালী ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপযােগী করেন। তাঁর রচিত ‘পঞ্চসিদ্ধান্ত’ ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাসে দিক নির্দেশক। বাগভট্ট নামে একজন পন্ডিত চিকিৎসাশাস্ত্রে বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। চিকিৎসাবিদ্যায় সেকালে ভারত এতােটাই এগিয়েছিল যে, শব-ব্যবচ্ছেদ তখন প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য অবশ্য শিক্ষণীয় পাঠ ছিল বলে জানা যায়।
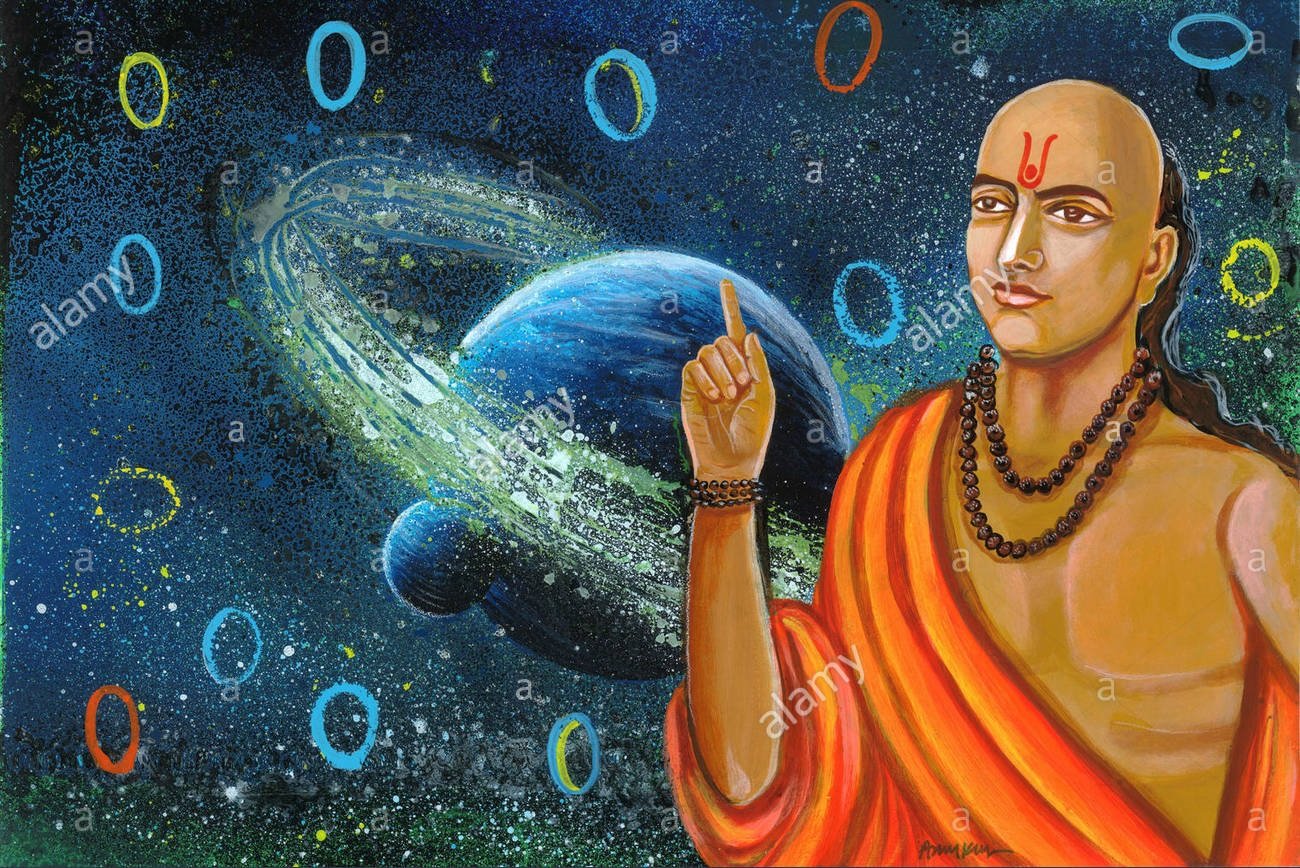
শিক্ষা-দীক্ষা
গুপ্ত যুগে ভারতে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়। নালন্দা, তক্ষশীলা, উজ্জয়িনী, সারনাথ এবং অজন্তা তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। এ সকল স্থানের শিক্ষাকেন্দ্রগুলােতে বিষয়ভিত্তিক পড়াশােনার অগ্রগতি লক্ষ করা যায়। বিহারের নালন্দা বিহারে মহাযান বৌদ্ধমতের ওপর বিশেষভাবে পড়ানাে হতাে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে অবস্থিত তক্ষশীলা ছাত্র ছিলেন বিখ্যাত পন্ডিত পাণিনি, কৌটিল্য, চরক প্রমুখ। এছাড়া গুজরাটে বল্লভী এবং অন্যান্য অসংখ্য স্থানে নানা ধরনের শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এসব স্থানে ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন, ধর্ম এবং জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান আহরণ করতাে। গুপ্ত শাসকগণ এবং বড় বড় ব্যবসায়ীরা ছিলেন শিক্ষার পৃষ্ঠপােষক।
সঙ্গীত ও শিল্পকলা
সমুদ্রগুপ্ত কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসংগীতের প্রতি অতিশয় অনুরাগী ছিলেন। তাঁর কাছে উৎসাহ পেয়ে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গান-বাজনার আসর বসে এবং গায়ক ও বাদ্যকরেরা সঙ্গীতে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করে। এছাড়া শিল্পকলার ক্ষেত্রে গুপ্তযুগের অগ্রগতি উল্লেখযােগ্য। এই যুগকে ভারতীয় শিল্পকলার ‘উৎকর্ষের যুগ’ বলা যেতে পারে। মথুরা, বারাণসী ও পাটলিপুত্র ছিল শিল্পকলার প্রধান কেন্দ্র। স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলাএই তিনটি পরস্পর ঘনিষ্ট মাধ্যমে গুপ্তযুগীয় শিল্পকলার প্রসার ঘটে।
খ্রিস্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে উত্তরপ্রদেশের কঁসি জেলার দেওঘরে গুপ্তদের নির্মিত প্রস্তর মন্দির আজও বর্তমান। এর দেয়ালের খােপে ভারতীয় ভাস্কর্যের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ নমুনা আছে।কানপুর জেলায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ের একটি ইট নির্মিত মন্দির রয়েছে। এছাড়া বারাণসীর নিকটবর্তী সারনাথের বিধ্বস্ত ভাস্কর্যের চিহ্নাদি গুপ্তযুগের সুদৃশ্য সারনাথ প্রস্তর মন্দিরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে, গুপ্তযুগেই সর্বপ্রথম মন্দিরের চূড়া উঁচু করে তৈরি করা শুরু হয়। এছাড়া এ যুগের মন্দির স্থাপত্যে দ্রাবিড় রীতি ও নাগর রীতির লক্ষণীয় প্রভাব বিদ্যমান। সেকালের শিল্পী ও কারিগরেরা শিল্পের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় ধাতব শিল্পে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে দিল্লিতে একটি লৌহস্তম্ভ স্থাপিত হয়। এটি ২৩ ফুটের অধিক উঁচু, অতিশয় মসৃণ এবং বর্তমান বিশ্বেরও বিস্ময়। হাজার বছরের রােদ, বৃষ্টি, ঝড় এতে কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। স্তম্ভটি সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সােনালী বর্ণে রঞ্জিত হয়ে ওঠে এবং বেলা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে এর ঔজ্জ্বল্য বেড়ে যায়। গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রাগুলাে স্বর্ণ শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এ যুগের চিত্রকলার অভূতপূর্ব বিকাশ অজজুর গুহার গায়ে দেখা যায়। গুপ্তযুগের চিত্রকলা ধর্মীয় বিষয়কে অতিক্রম করে মানুষের জীবনের নানাদিক নিয়ে রচিত হয়েছিল। গৌতম বুদ্ধের জীবনকে অবলম্বন করেও বহু প্রাচীর চিত্র আঁকা হয়। অজন্তা ছাড়া বাগ গুহার চিত্রগুলাের বিষয়বস্তু বিশেষ করে নর-নারীর দৈহিক সৌন্দর্য বিশেষ উল্লেখ্য। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল শিল্প বিশেষজ্ঞ গুপ্ত চিত্রকলার ভূয়সী প্রশংসা করেন। সাধারণত রেখা বিন্যাস ও বর্ণসমাবেশের ওপরেই চিত্রশিল্পের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। এই উভয় ক্ষেত্রেই গুপ্ত চিত্রকলা ছিল অতুলনীয়। সবকিছু মিলে সঙ্গীত, চিত্রকলা ও শিল্পকলায় গুপ্তযুগের গৌরব বিশেষভাবে উল্লেখযােগ্য।
গুপ্ত শাসনব্যবস্থা
কেবল সামরিক শক্তির সাহায্যে সাম্রাজ্য স্থাপনই নয়, গুপ্তগণ সেই সাম্রাজ্যে সুদৃঢ়, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুবিন্যস্ত শাসনব্যবস্থা প্রণয়নের কৃতিত্বেরও দাবিদার। গুপ্তদের শাসনব্যবস্থা পূর্ববর্তী ঐতিহ্য ও শাসনরীতির ধারা অনুসরণ করেই রচিত হয়। তাদের শাসনব্যবস্থা ছিল সুদক্ষ, জনহিতকর ও পক্ষপাতহীন। জনসাধারণের নিরাপত্তা ও মঙ্গল সম্পর্কে গুপ্ত রাজাগণ সর্বদাই সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। গুপ্ত শাসন কাঠামােয় রাজতন্ত্রের নিরংকুশ প্রাধান্য ছিল। সম্রাট পদ ছিল বংশানুক্রমিক। রাজাই ছিলেন সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করার মতাে কোন ধরনের ব্যবস্থা রাজ্যে ছিল না। তবে রাজা সুষ্ঠুভাবে শাসন পরিচালনা করার জন্য মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সাহায্য নিতেন। মন্ত্রীপদও অনেক ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিক হয়েছিল। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে ‘মহাবলাধিকৃত’ (সেনাপ্রধান), ‘মহাপ্রতীহার’ (রাজপ্রাসাদের রক্ষীবাহিনীর প্রধান), ‘মহাদন্ডনায়ক’ (প্রধান সেনাপতি),‘মহাসান্ধিবিগ্রহিক’ (যুদ্ধ ও সন্ধি বিষয়ক কর্মকর্তা) প্রমুখ গুরুত্বপুর্ণ ছিলেন।

গুপ্ত শাসন কাঠামােতে প্রাদেশিক শাসনের ব্যবস্থা ছিল। সমগ্র সাম্রাজ্যকে কয়েকটি দেশ’ বা ‘ভূক্তি’তে বিভক্ত করা হয়েছিল। এগুলাে আবার ‘বিষয়’ বা জেলায় বিভক্ত ছিল। সর্বনিম্নস্তরে ছিল ‘গ্রাম’। গুপ্তযুগে ‘বিষয়’ বা জেলার শাসনে একটি উল্লেখ্যযােগ্য পরিবর্তন ঘটে। বিষয়ের শাসনকাজে পরামর্শ দেয়ার জন্য বিষয়ের অধিষ্ঠান অধিকরণে একটি পরিষদ থাকতাে। এই পরিষদে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিরা থাকতেন। নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ, প্রথম কুলিক, প্রথম কায়স্থ সমন্বয়ে গঠিত হতাে এই পরিষদ। এভাবে শাসনকাজে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের সুযােগ সৃষ্টি করা হয়। এই অবস্থাকে গুপ্তযুগের অন্যতম গৌরব। হিসেবে অনায়াসে চিহ্নিত করা যেতে পারে।
গুপ্ত শাসনব্যবস্থার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলাে হচ্ছে সুনিয়ন্ত্রিত রাজস্ব ও পুলিশ ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, সামরিক সংগঠন ইত্যাদি। তবে গুপ্ত শাসনব্যবস্থার প্রধান প্রশংসার দিক হচ্ছে এর বিকেন্দ্রীকরণ নীতি ও প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা।
গুপ্ত সংস্কৃতি : ‘ধ্রুপদী’ পর্ব
সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে গুপ্ত শাসনকাল ছিল ভারতের এক গৌরবময় যুগ। সর্বক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব অগ্রগতি এই যুগকে মহিমান্বিত করেছে। এ কারণে অনেকেই গুপ্ত সংস্কৃতি তথা গুপ্ত যুগকে ‘ক্ল্যাসিক্যাল’ যুগ বা ধ্রুপদী’ যুগ বলে অভিহিত করেন। কেউ বলেন, গুপ্তযুগ ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ। এ সময়ে আধুনিক হিন্দু ধর্মের উত্থান ও রূপান্তর ঘটে। রাজ পৃষ্ঠপােষকতার অভাবে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের পতন শুরু হয়। কেউ আবার গুপ্তযুগের সভ্যতাকে ‘দরবারি সভ্যতা’ হিসেবেও অভিহিত করেন। ঐতিহাসিক বার্ণেট গুপ্ত যুগকে পেরিক্লিসের যুগের সাথে তুলনা করেন। সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবেচনায় উভয় যুগের। মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।
গুপ্ত যুগে ভারতের সাথে বহির্বিশ্বের যােগাযােগ বৃদ্ধি পায়। এতে করে সাংস্কৃতিক সমন্বয় ঘটে যা গুপ্ত সংস্কৃতিকে ঋদ্ধ করে। ঐতিহাসিক কোয়েডেস দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গুপ্ত শাসন ও সংস্কৃতির সুস্পষ্ট প্রভাবের। কথা উল্লেখ করেছেন। গুপ্ত মুদ্রায়ও বহির্বিশ্বের প্রভাব দেখা যায়। এভাবে বাইরের সংস্কৃতি ও সভ্যতার। সাথে আদান-প্রদান গুপ্ত সংস্কৃতিকে উচ্চমার্গীয় মর্যাদা দান করেছে। বিশেষ করে গ্রিস, রােম, চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শৈল্পিক প্রভাব গুপ্ত সংস্কৃতিকে নব-বৈশিষ্ট্য দান করেছিল।
এতদসত্বেও অনেকেই গুপ্তযুগকে ‘স্বর্ণযুগ’ বা ‘ক্ল্যাসিক্যাল যুগ’ বলার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের মতে, গুপ্ত শাসনব্যবস্থার প্রশংসার দিক থাকলেও এর ছিল কতগুলাে দুর্বল দিক। প্রদেশ ও জেলায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ফলে স্থানীয় শাসনকর্তারা ক্ষমতালােভী হয়ে পড়েন এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের সর্বভারতীয় আবেদন ক্রমেই ভেঙ্গে যায়। এছাড়া নগরগুলাের ধ্বংসােনুখ অবস্থা জনসাধারণের তীব্র দারিদ্র্য, উচ্চ শ্রেণীর জন্য বিনােদন সাহিত্য- লােক সংস্কৃতির অভাব-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও জাতিভেদ প্রথার বিস্তার, স্থাপত্য-ভাস্কর্যে উচ্চ শ্রেণীর লােকের রুচির প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি কারণে গুপ্তযুগকে প্রশ্নাতীতভাবে ‘ক্ল্যাসিক্যাল যুগ’ বা ‘স্বর্ণযুগ’ বলা চলে না। তবুও সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি মেনে নিয়ে একথা বলা যেতে পারে যে, গুপ্ত যুগের সামগ্রিক অগ্রগতি ছিল অসাধারণ। শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, শাসনব্যবস্থা, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে গুপ্তযুগের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বা গৌরব প্রাচীন ভারতের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে।
শেষে বলা যায় গুপ্তযুগের নানাবিধ গৌরব এই যুগকে ধ্রুপদী ‘সংস্কৃতির যুগ’ হিসেবে পরিচিতি এনে দিয়েছে। ধর্মীয়ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র থাকলেও সাধারণভাবে উদারনীতি অনুসরণ, সংস্কৃত সাহিত্যের দৃষ্টান্তমূলক অগ্রগতি সাধন, শিক্ষাক্ষেত্রে পৃষ্ঠপােষকতা, শিল্পকলায় উৎকর্ষ অর্জন এবং বহির্বিশ্বের সাথে সাংস্কৃতিক যােগাযােগ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে গুপ্তযুগকে আলােকিত করেছে। এই গৌরব এতােটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, রাজনৈতিক সংহতি, সুশাসন এবং গুপ্তদের সাংস্কৃতিক মহিমা সমগ্র ভারতে তাে বটেই, এমনকি বহির্বিশ্বেও ছড়িয়ে পড়েছিল। সর্বোপরি প্রাচীন ভারতে দ্বিতীয়বারের মতাে সুসংগঠিত, সুবিন্যস্ত এবং গুরুত্বপুর্ণ শাসনব্যবস্থা গুপ্তদের হাতেই রচিত হয়।
আরও পড়ুন,
১। সাতবাহন রাজবংশঃ ইতিহাস ও তার রাজনৈতিক মূল্যায়ন
২। হিন্দু মন্দির ধ্বংস ও ভারতে মুসলিম প্রশাসনঃ একটি ঐতিহাসিক পুনর্মূল্যায়ন
৩। মুহাম্মদ বিন তুঘলক কি পাগল ছিলেনঃ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ
৪। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক ও তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাঃ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ
৫। মৌর্য সাম্রাজ্যের উদ্ভব ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যঃ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা

 নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা
নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা




