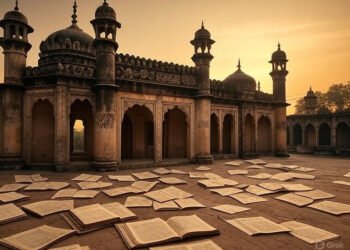লিখেছেনঃ রোমিলা থাপার
ভারতীয় ইতিহাসের ব্যাখ্যায় সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব প্রসঙ্গে যখন কথা হয়, তখন সাধারণত অনেকেই ধরে নেন যে প্রাচীন যুগ নিয়ে যারা লিখেছেন তাদের উপরে এই ধরনের প্রভাব হয় একেবারেই নেই অথবা থাকলেও তা খুব একটা প্রাসঙ্গিক নয়। অথচ ভারতীয় ইতিহাসের অনুশীলনে ও ব্যাখ্যায় সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব মোটেই শুধু মধ্যযুগীয় ও আধুনিক যুগের ইতিহাসেই আবদ্ধ থাকেনি; মূলতঃ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণের ফলে প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে চেতনা ও তার ব্যাখ্যাও বিকৃত হতে পারে। ইদানীংকালের সাম্প্রদায়িক ভাবধারা পরীক্ষা করে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তা প্রাচীন ইতিহাস থেকে বুদ্ধিগত সমর্থন খুঁজছে। হিন্দু সাম্প্রদায়িকেরা যেমন প্রাচীনকালে একটি আদর্শ হিন্দু-সমাজের চিত্র খাড়া ক’রে তুলতে চেষ্টা করেন এবং ভারতবর্ষের সব দুর্ভাগ্যের জন্যে ‘মুসলমান’দের আগমনকে দায়ী করেন, ঠিক তেমনি সাম্প্রদায়িক মুসলমানেরাও মধ্যযুগের গোড়ার দিক (অর্থাৎ একাদশ বা ত্রয়োদশ শতক) থেকে বিভেদনীতির উৎস সন্ধান এবং প্রমাণের চেষ্টা করেন।
আমরা অনেক সময় ভুলে যাই যে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা সমসাময়িক মতবাদপ্রসূত হ’তে পারে। এ কথা অল্পদিন আগেও ঐতিহাসিকদের মতামত সম্বন্ধে বিশেষভাবে খাটতো কারণ তখন ইতিহাস রচনা ছিলো (এবং এখনো অনেক ক্ষেত্রে তাই আছে) বিশ্লেষণের বিশেষ চেষ্টা না ক’রে শুধুমাত্র ঘটনাপরম্পরা সাজিয়ে যাওয়া। ঐতিহাসিকরা তাদের নিজন্য পছন্দ অনুযায়ী ঘটনাগুলি বাছাই করতেন এবং তাদের নির্বাচনের ধরন থেকে তাদের পক্ষপাত বোঝা যায়। যেসব উৎস থেকে ঐতিহাসিক তার তথ্য সংগ্রহ করেন, সেগুলির কোনটিকে তিনি কতটুকু মুল্য দেন এবং প্রামাণিকতার বিচার বিশ্লেষণ করে যাচাই করতে তিনি কতটা রাজী, তার দ্বারাও ঐতিহাসিকের ভাষা প্রভাবিত হয়।
প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা বুঝতে হলে প্রথমে বোধ হয় বিগত কয়েকটি শতকে ইতিহাস-প্রণয়নে সমসাময়িক চিন্তাধারার প্রভাব বিচার করা উচিত। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে আধুনিক রচনা ও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চা শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং তখন থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মতবাদের দিক দিয়ে তিনটি প্রধান ধারা লক্ষ্য করা যায়ঃ প্রাচ্যবাদী, হিতবাদী ও জাতীয়তাবাদী।
পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ইয়োরোপ ও এশিয়ার মধ্যে রীনিচ্যের প্রসারের ফলে বহু ইয়োরোপীয় পণ্ডিত এবং ধর্ম প্রচারক এশিয়ার সংস্কৃতি বিষয়ে ক্রমশঃ আগ্রহশীল হয়ে উঠলেন । ভারতবর্ষের ক্ষেত্র এই আগ্রহের সূচনা দেখি ভাষাচর্চায়— বিশেষতঃ সংস্কৃত ও পারসিক ভাষা শিক্ষার মধ্যে। এই ভাষাচর্চা নতুন উদ্যমে শুরু হলে আঠারো শতকের শেষে রয়াল-এশিয়াটিক সোসাইটির গোড়াপত্তনের পর থেকে। যাকে ধ্রুপদী ইতিহাস বলে, সেবিষয়ে আলোচনাগুলি লিপিবদ্ধ হলো সুবিন্যস্তভাবে। এ কাজ প্রধানত যে পণ্ডিতরা করতেন তাঁদের প্রাচ্যবাদী বা ভারততত্ত্ববিদ (ওরিয়েন্টালিস্ট বা ইন্দলজিস্ট) বলা হতো। তাঁদের মধ্যে যারা সংস্কৃত অধ্যয়ন করেছিলেন তারা আর্য-ভাষীদের সংস্কৃতির রীতিমত ভক্ত হয়ে উঠলেন । তারা এক ইন্দো-ইয়োরোপীয় দেশখণ্ড এবং সংস্কৃত ও গ্রীক সংস্কৃতির বংশগত ঐক্য সম্বন্ধে মতের প্রচলন করলেন। আর্যদের তারা একই ধরনের ভাষা-ভাষী— একটি গোষ্ঠী হিসেবে না দেখে একটি জাতি হিসেবে দেখতে লাগলেন এবং ভারতবর্ষে আর্য সংস্কৃতির ইয়োরোপে গ্রীক সংস্কৃতির চারিত্রিক রূপান্তরের মধ্যে পারস্পরিক যোগ খোঁজার চেষ্টা চলতে লাগল। প্রাচ্যবাদীরা বৈদিক যুগের অকুণ্ঠ গুণগান করতে লাগলেন সাম্প্রদায়কতা ও প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনা এবং তাদের ধারণা হলো প্রাচীন ভারতে মোটামুটি একটি আদর্শ সমাজব্যবস্থা ছিল । সেই ব্যবস্থার মধ্যে যে সব ছন্দ ছিল তা প্রচ্ছন্ন রেখে তারা তার গৌরব কীর্তনই বেশি করে করতে লাগলেন। তাদের এই ধারণার সঙ্গে গোঁড়া হিন্দুদের মতের পুরোপুরি মিল হলো, কারণ হিন্দুরা এমনিতেই বেদ ও বৈদিক নর মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী ছিলেন।
যে সব ভারতীয় ঐতিহাদিক পরে এই চিন্তাধারার অবলম্বন করেন, তাঁরা প্রাচ্যবাদীদের প্রাচীন ভারতীয় সমাজের মাহাত্ম্য-কীর্তনের পেছনে যে উদ্দেশ্যগুলি কাজ করেছে তা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। সবচেয়ে স্পষ্ট যে কারণটি তা হলো বেশির ভাগ প্রাচ্যবাদী পণ্ডিত তাদের নিজেদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন এবং শিল্পবিপ্লবের ফলে ইয়োরোপে যে সব ঐতিহাদিক পরিবর্তন ঘটেছিল, তার সম্বন্ধে তারা সবিশেষ সন্দিহান ছিলেন । এর ফলে তারা অন্যত্র রামরাজ্য খুঁজে বেড়াতেন এবং বেশির ভাগই প্রাচ্যের প্রাচীন সভ্যতায় তা আবিষ্কার করতেন । আদর্শরূপে চিত্রিত প্রাচীন ভারতের সঙ্গে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করার এরকম একটি দৃষ্টান্ত হলেন ম্যাকসমূলার, যিনি নিজের নামটি সংস্কৃত ক’রে মোক্ষমূলর-এ রূপান্তরিত করেছিলেন। এই ধরনের আদর্শীকরণ অনেক সময় আধুনিক ভারতের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হতো। ম্যাকসমুলার যদি তাঁর জীবনকালে উনিশ শতকের ভারতবর্ষকে সচক্ষে দেখে যেতেন তা হ’লে তার প্রতিক্রিয়া কী হ’তো এ চিন্তা ‘ কৌতূহল জোগায়। প্রাচ্যবাদীদের লেখা অনেক ভারতীয়কে প্রভাবিত করেছিল এবং উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে অনেকগুলিই (যথা আর্য সমাজ) বৈদিক সংস্কৃতির আদর্শকে ভারতীয় ঐতিহ্যে ভিত্তি বলে প্রচার করতো। পাশ্চাত্যজগতেরও কোনো কোনে চিন্তাধারার ওপর এই মতামতের যে ছাপ পড়েছিলো তা রোমান্টিক আন্দোলন বা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে বোঝা যায় । গোবিনে (যিনি উগ্র জাতীয়তাবাদী দার্শনিকদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ) ‘আর্যজাতি’ ও ভারতের বর্ণবিন্যাস সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ধারণার ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে তাঁর চিন্তা-ধারার প্রবর্তন করেন। এইজাতীয় ধারণা পরিণতি লাভ করলো বিংশ শতকের জার্মানিতে হিটলারের মতবাদে।
অন্য একটি কারণেও প্রাচ্যবাদীরা প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতিকে সমর্থন করার চেষ্টা করতেন, তা হ’লো হিতবাদীদলের সঙ্গে বিতর্কে তারা ক্রমশ পরাজিত হচ্ছিলেন। হিতবাদীরা হ’লেন উনিশ শতকের বিশেষ প্রভাবশালী একদল ব্রিটিশ দার্শনিক। তারা সুনিশ্চিত জানতেন যে ব্রিটিশদের আগমন ভারতবর্ষের পক্ষে দৈবানুগ্রহবিশেষ, কারণ ব্রিটিশ শাসন ও আইনের ফলে ভারতবর্ষের অনগ্রসরতা দূর হবে। সঙ্গে সঙ্গে এযাবৎ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে যে সব স্বেচ্ছাচারী শাসকরা রাজত্ব করেছেন তাদের ধারাও শেষ হবে এবং ভারতবর্ষের মানুষ রাজনৈতিক চেতনা লাভ করবে। হিতবাদীদের মধ্যে জেমস মিল ভারতীয় ঐতিহাসিক চিন্তাধারার ওপরে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তার “ব্রিটিশ-ভারতের ইতিহাস’’-এর সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক বোধহয় তা এক হিসেবে ভারতীয় ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার সূচনা করেছিলো এবং পরে দ্বিজাতিতত্ত্বের ঐতিহাসিক সমর্থন জুগিয়েছিল। ঐতিহাসিকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ভারতীয়
ইতিহাসকে তিনটি পর্বে ভাগ করার রীতি প্রচলন করেন। এই তিনটি অধ্যায় হলো হিন্দু সভ্যতা, মুসলমান সভ্যতা এবং ব্রিটিশ সভ্যতা ( বিচিত্র হলো, খৃষ্টান সভ্যতা নয় )।
মিল্ যে এরকম একটি কাঠামো জোর ক’রে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন তা তার হিতবাদী দর্শনের চিস্তাগত ও রাজনৈতিক পটভূমি থেকেই বোঝা যায়। বিস্ময়ের ব্যাপার হ’লো এই যে, পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিকরা এই পর্ব-বিভাগ নির্বিচারে মেনে নিয়েছিলেন । একেবারে এখনকার কথা বাদ দিলে এই পর্ব-বিভাগের যৌক্তিকতা বিচারের কানো চেষ্টাই ভালভাবে করা হয়নি। মিলের লেখা ছিলো সাধারণভাবে স্বীকৃত সর্ধপ্রথম ভারতের ইতিহাস এবং এর প্রভাব এতোই বেশি যে এখনো অনেকে তার মূল ধারণাগুলিতে বিশ্বাস করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক ভারতীয় ইতিহাসকে অতীত,মধ্য এবং আধুনিক যুগে বিভক্ত করেন বটে, কিন্তু এই বিভাগের মূলেও আছে মিলের মতবাদ, অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশগুলির ধর্মের পরিবর্তন। ভারতীয় শাসন বিভাগের আমলাদের প্রাথমিক পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত ছিলো মিলের ইতিহাস এবং উনবিংশ শতকের ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের অধিকাংশই এই শ্রেণী থেকে এসেছিলেন। মিলের ইতিহাসের আর একটি দিক হ’লো। হিন্দু সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিরূপতা। তিনি একে বর্ণনা করেছেন পশ্চাদমুখী এবং প্রগতি ও যুক্তির পরিপন্থী হিসেবে । তিনি যার নাম দিয়েছেন “মুসলমান সভ্যতা” সে-বিষয়ে তিনি একটু বেশি সহানুভৃতিশীল ছিলেন, যদিও সে সম্পর্কেও তিনি কখনো-কখনো বিরূপ সমালোচনা করতে ছাড়েন নি । এর ফলে প্রাচ্যবাদীদের একটি অংশ এবং পরবর্তাকালের ভারতীয় ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ কিছুটা বাধ্য হয়েই ‘হিন্দুসভ্যতা’র সমর্থন করেছেন, যদিও তার জন্যে তাদের প্রাচীন অতীতকে অতিরিক্ত গৌরব দান করতে হয়েছে।
বিশ শতকের গোড়ার দিকের ভারতীয় ঐতিহাসিকরা জাতীয় আন্দোলনের দ্বারা স্বভাবতঃই প্রভাবিত হয়েছিলেন। নিজেদের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক না বললেও তাদের ভারতীয় ইতিহাসের ব্যাখ্যায় প্রায়ই জাতীয়তাবাদী মনোভাবের ছাপ থাকতো । তারা প্রাচ্যবাদীদের রচনাবলির ওপর আরো বেশি ক’রে নির্ভর করতেন এবং আবার শুরু হলো প্রাচীন ভারতের (এখন থেকে যা প্রায়ই ‘হিন্দু ভারত’ ব’লে অভিহিত হতে লাগলো) গুণগান। প্রাচ্যবাদীদের কাজের তাই দু’ধরনের ফলাফল দেখা যায়ঃ অতীত ভারতের পুনরাবিস্কারের পথিকৃৎ হিসেবে তারা জাতীয়তাবাদীদের অতীত সম্বন্ধে আগ্রহের ভিত্তি স্থাপন করেন; এরই সঙ্গে আবার ভারতীয় সংস্কৃতিকে সমর্থন কারে তারা অতীতের অন্ধ পুজারীদের হাতে অস্ত্র যোগান।
অতীতের গৌরবগান নিশ্চয়ই কিছুদূর পর্যন্ত ন্যায্য ছিল, কারণ সব জাতীয় আন্দোলনেই তা দেখা যায়। এই ধরনের আন্দোলনে দেশজ ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা স্বাভাবিক এবং অনেক ক্ষেত্র দেশজ ঐতিহ্য বলতে ঐতিহাসিক সংস্কৃতি আদি নিদর্শন বোঝায়। জাতীয়তাবাদের সঙ্গে যেখানে আছে ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা, অতীতপুজা সেখানে বর্তমানের লাঞ্ছনার মধ্যে সান্তনা আনে। ফলে যাঁরাই অতীতের সমালোচনা করেন, তাদের প্রায় সর্বদাই জাতীয়তাবাদবিরোধী ব’লে মনে করা হয়। অতীত মাহাত্ম্যকীর্তনের একটি প্রতিক্রিয়া হ’লোঃ প্রথম যুগের ভারতীয় সমাজে কোনোরকম দ্বন্দ্ব বা বিরোধের, বিশেষত সামাজিক-অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় বিরোধের অস্তিত্ব স্বীকার করার অনিচ্ছা । ধর্মশাস্ত্র প্রমুখ তত্ত্বগ্রন্থগুলিকে প্রাচীন ভারতের বাস্তবচিত্র বলে গ্রহণ করা হ’লো এবং এর ফলে সেযুগের জীবনকে একেবারে আদর্শ ব’লে ধ’রে নেওয়া হলো । ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহের পেছনে যে সমস্ত লক্ষ্য বা অভিপ্রায় কাজ করে, সেগুলির বিশ্লেষণ করা আধুনিক ইতিহাসচর্চার একটি প্রধান অঙ্গ। কিন্তু এই ধরনের বিশ্লেষণের কোনো চেষ্টা আগেকার ঐতিহাসিকরা করেন নি । আগেকার দিনের অধিকাংশ ঐতিহাসিক আসতেন ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ পরিবার থেকে, কারণ এই সব বর্ণের লোকেরাই প্রধানত সেযুগে সংস্কৃতচর্চার সুযোগ পেতেন। সুতরাং সংস্কৃত উপাদানগুলির সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ বিশেষ হ’তোনা । বিদেশী শাসন থেকে মুক্তিলাভ, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি যেসব মূল্যবোধ জাতীয় আন্দোলনের পক্ষে অপরিহার্য ছিলো, অতীতযুগের তাদের সন্ধান চলতে লাগলো এবং অতীতেও তাদের অস্তিত্ব ছিলো একথা ধরে নেওয়া হ’লো। উদাহরণম্বরূপ বলা যায়, বিদেশী শাসনের প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাওয়া খুবই কঠিন ছিলো, কেননা উত্তরভারতের ইতিহাসে খৃষ্টপূর্ব ৬০০ সাল থেকে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বারবার বিদেশী আক্রমণ ও অধিকারের নিদর্শন আছে।
জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা হ’লো তারা কেউই মিলের পর্ব-বিভাগ সম্বন্ধে কোনো রকম প্রশ্ন তোলেননি। অংশত এর কারণ হ’লো সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসকে প্রায় সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে রাজনৈতিক ও রাজবংশের ইতিহাপচর্চায় নিমগ্ন থাকা। ত্রয়োদশ শতকের পর থেকে মুসলমান রাজবংশের সংখ্যা খুব বেড়ে যায়, তাই কেবল রাজবংশের ইতিহাসের কথা ভাবলে এ যুগকে “মুসলমানযুগ’’ বলে মনে হতে পারে। কিন্ত এই ধরনের পর্ব-বিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে অতীতের গুণগান মূলত হিন্দুযুগের গুণগান হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে দুই যুগের মধ্যে পৃথকীকরণ আরো বেশি অনড় হয়ে ওঠে।
বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদের সূচনার ফলে এই ব্যবধান আগে বেড়ে গেলো। হিন্দুশক্তির পতনের জন্যে মুলমানদের আগমনকে সহজেই দায়ী করা চলে; এর জন্যে বিশেষ বুদ্ধি খাটাতে হয় না। তুর্কিরা কী করে এত সহজে তাদের ক্ষমতা স্থাপন করলেন তা সেযুগের সমাজ বিশ্লেষণ করে বোঝার চেষ্টা করা অল্পই হয়েছে। “মুসলমান যুগ’’-কে অধপতনের যুগ বলে ধরে নেওয়া হলো এবং মনে করা হলো যে তার দুর্বলতার জন্যেই ব্রিটিশশাসন স্বাভাবিক নিয়মে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। তাছাড়া, একথাও বলা, হতো যে মুসলমান যুগে হিন্দু এবং মুসলমান এই দুই ‘জাতির’ উদ্ভব হয়েছিল এবং আধুনিক জাতীর রাষ্ট্রব্যবস্থায় এর একমাত্র পরিণতি হতে পারে সমগ্র দেশকে হিন্দু ও মুললমান অধিকৃত দুটি ভিন্ন রাষ্ট্রে ভাগ করা। একথা বিশেষ ভেবে দেখা হলো না যে ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং জাতি সমার্থক নয়। উনিশশো তিরিশ চল্লিশের দশকের সাম্প্রদায়িক নীতির ফলে এই ব্যাখ্যা ও বিভেদ আরো তীব্র হয়ে ওঠে । পাকিস্তান সৃষ্টির ফলে কিন্তু সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকদের সমস্যার কোনো সমাধান হলোনা । বাস্তবে মুসলমান সংস্কৃতির সঙ্গে আজও হিন্দু সাম্প্রদায়িকদের যুঝতে হচ্ছে। কাজেই তাঁরা চেষ্টা করেন হয় তাকে তুচ্ছ করতে, অথবা তার বিদেশীয়ানাকে বড়ো করে তুলতে।
আমরা এতক্ষণ ভারতীয় ইতিহাসের পর্ব-বিভাগের সূত্রপাত বিষয়ে আলোচনা করলাম । এখন “হিন্দযুগ’ এই পরিভাষাগুলির যৌক্তিকতা বিচার করে দেখা যেতে পারে ।
মনে করা হয় যে, খৃষ্টপূর্ব ১০০ সাল থেকে ১২০০ শ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে যুগ তা হলো হিন্দুযুগ, কারণ তখন সমস্ত উপমহাদেশের শাসক-বংশগুলি হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলো । কিন্তু রাজবংশের ইতিহাসের ভিত্তিতেও এ যুগকে হিন্দুযুগ মনে করা সঠিক নয়, কারণ মৌর্য, ইন্দো-গ্রীসিয়, শক, কুষাণ প্রভৃতি বহু প্রধান রাজবংশই অহিন্দু ছিলো । অনেক রাজাই ছিলেন বৌদ্ধ, এবং হিন্দুবিদ্বেষী না হলেও তাঁরা সচেতনভাবে নিজেদের বৌদ্ধ বলে পরিচয় দিতেন। তাহলে কি আমরা মনে করবো যে খ্রষ্টপূর্ব ৫০০ সাল থেকে ৩০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একটি বৌদ্ধযুগ-ও ছিলো? আজকের ভারতে যদি যথেষ্ট সংখ্যক বৌদ্ধ থাকতেন, তাহলে হয়তো এ ধারণাটি-ও স্বীকৃতি পেতো ।

পর্ব-বিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু কথাটির প্রকৃত অর্থ কি, এপ্রশ্নও তোলা যেতে পারে। ভারত সম্পর্কিত প্রাক ইসলামীয় উপাদানসমূহে কথাটি পাওয়া যায় না। হিন্দ্ ( ইন্ডিয়া ) দেশে যাঁরা বাস করতেন তাদের বর্ণনা করার জন্যে প্রথমে আরবরা এবং পরে অন্যরা এটি ব্যবহার করতেন । অর্থাৎ “হিন্দু” সংজ্ঞাটি গোড়ায় হিন্দুরা নিজেরা বা ব্যবহার করেন নি, এটি ছিলো একটি বিদেশী শব্দ যা পরে হিন্দুরা গ্রহণ করেছেন । আজকের দিনে আমরা যাকে হিন্দু বলে স্বীকার করি, অতীত যুগে তার প্রায় কোনো পরিচয়ই মিলবে না। আজকের অর্থে হিন্দুর উন্মেষ ঘটে গুপ্তযুগের পরে, পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দে। প্রাকমুসলমান যুগের ভারত বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীগুলি যে নিজেদের হিন্দু বা কোনো ঐক্যবদ্ধ ধর্মসম্প্রদায় বলে মনে করতেন না তার প্রচুর প্রমাণ প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক উপাদান থেকে পাওয়া যাবে। বৌদ্ধদের নিজস্থ ধর্সসংগঠনের যে রূপ ছিলো তা সম্পূর্ণ আলাদা। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক হিন্দুধর্মের, বিশেষত ভক্তি- সম্প্রদায়ের লক্ষণগুলি বিশেষভাবে মধ্যযুগেই দেখা দিলো, যদিও সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকরা এ যুগকে অবক্ষয়ের যুগ বলে মনে করেন।
গোড়ার দিকে, অর্থাৎ সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত নিজেদের মুসলমানদের থেকে পার্থক্য নির্দেশের জন্য হিন্দুরা যে পরিভাষা ব্যবহার করতেন তারও আলোচনা করা উচিত। লক্ষণীয় হ’লো আজকের দিনে সেযুগের ইতিহাস লেখার সময় আমরা আরব, তুর্কি এবং পারসিক সকলকেই একসঙ্গে “মুসলমান” ব’লে অভিহিত করি। কিন্তু আকরগ্রন্থগুলিতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যস্ত এইসব বিভিন্ন লোকদের বর্ণনায় “মুসলমান” শবের ব্যবহার বিরল। সেযুগের আকর-গ্রন্থে ধর্মীয় পরিভাষা ব্যবহার না ক’রে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সংজ্ঞার্থ ব্যবহার করা হ’তো। যেমন তুর্কিদের বলা হতো তুরস্ক এবং আরবদের বলা হ’তো যবন। পশ্চিম এশিয়া বা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে আগত গ্রীক, রোমীয়, আরব নির্বিশেষে সকলকেই যবন বলার রীতি ছিলো । সংস্কৃতি ‘‘যবন” কথাটি প্রাকৃত যৌনা থেকে গৃহীত এবং যোনা কথাটি এসেছে “অয়োনিয়া’’ থেকে। কারণ পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে সর্বপ্রথম এবং ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক স্থাপিত হয় আয়োনীয় গ্রীকদের।
তুর্কি, পারসিক এবং আরবদের বর্ণনায় ‘ম্লেচ্ছ’ শব্দটিও ব্যবহার করা হ’তো । এই শব্দটিও প্রাচীন এবং ঋগ্বেদে সর্বপ্রথম এর উল্লেখ পাওয়া যায়। যেসৰ লোক অনার্য্ ভাষা-ভাষী ছিলেন এবং আর্য্ সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিলোনা প্রধানত তাদের সন্বন্ধেই শব্দটি ব্যবহৃত হ’তো । সুতরাং উত্তর ও মধ্যভারতের বিভিন্ন অংশের অনার্য্ ভাষী উপজাতিগুলিই ছিলো প্রথম ‘গুচ্ছ’। পরে শব্দার্থের প্রসার ঘটায় সব বিদেশীদের ক্ষেত্রেই কথাটি ব্যবহৃত হ’তে লাগলো। এখানেও ‘ম্লেচ্ছ’ শব্দটি ধর্মীয় পরিভাষা নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সাংস্কৃতিক অর্থে ব্যবহৃত হ’তো। সুতরাং আরব ও তুর্কিদের যখন ‘ম্লেচ্ছ’ বলা হ’তো তখন তাদের ভিন্ন সংস্কৃতিসম্পন্ন বলেই বোঝানো হতো। এবং তার। রাজনৈতিক শক্র বা মিত্র উভরই হতে পারতেন । ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গে আরব, পারসিক এবং তুর্কিদের বাণিজ্য ও যুদ্ধের মাধ্যমে যে রকম ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো তাতে বিরূপ ধর্মীয় মনোভাব থেকে থাকলে তা নিশ্চয়ই সেষুগের ঐতিহাসিক আকরগ্রস্থ-গুলিতে প্রকাশ পেতো। এই উপমহাদেশে তু্র্কিরা রাজনৈতিক ক্ষমতায় প্রতিঠিত হবার পরই প্রথম ধর্মের ভিত্তিতে স্বাতন্ত্র্য –নির্দেশের সুচনা হয়। হিন্দুধর্মের নিজন্ব গঠন যেরকম ছিলো, তাতে তার পক্ষে ভিন্ন ধর্মের লোকেদের শুধুমাত্র ধর্মীয় সত্তা হিসেবে দেখা সম্ভব ছিলোনা।
পরিশেষে বিচার্য যে মিলের পর্ব-বিভাগ যদি কেবল পরিবর্তনশীল বংশাবলীর ইতিহাসের ভিত্তিতে রচিত হয়, তাহ’লেও তা সমর্থনযোগ্য কিনা। ভারতের ইতিহাসকে শুধু গাঙ্গেয় উপত্যকাকেন্দ্রিক বংশধারার বিবরণমাত্র বলে মনে করলে এরকম একটি পর্ব-বিভাগ হয়তো ব্যবহার করা যায়। ত্রয়োদশ শতকের গোড়া পর্যন্ত সত্যিই এ অঞ্চলের রাজবংশগুলি মোটামুটিভাবে হিন্দুই ছিলো এবং তারপর থেকে এখানে একের পর এক মুসলমান রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। কিন্তু সমগ্র উপমহাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এরকম পর্ব-বিভাগ মেনে নেওয়া যায়না। খুব ওপর ওপর দেখলেও সমস্যা দেখা দেবেঃ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে মুললমান রাজবংশগুলি স্থাপিত হয়েছিলো । যেমন আরবরা সিদ্ধুদেশ জয় করে সেখানে অষ্টম শতকেই তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। একাদশ শতকে পাঞ্জাবের একটি অংশ তুর্কি অধিকারভুক্ত হয় এবং ত্রয়োদশ শতকে উত্তর ভারতের বিরাট এলাকা জুড়ে তারা আধিপত্য বিস্তার করেন। দাক্ষিণাত্যে প্রথম মুসলমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় চতুর্দশ শতকে। সুদূর দক্ষিণে মুসলমানের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় আরও বহু পরে। সুতরাং মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার কোনো একটি বিশেষ তারিখ দেওয়া যায় না। অধিকাংশ পাঠ্যতালিকায় খুব শিথিলভাবে কাল-নির্ণয় করা হয় ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ অথবা ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ যদিও এই তারিখটি কেবলমাত্র উত্তর ভারতের একটি অংশের সম্বন্ধে ব্যবহার করা যায়।
ভাষাগত প্রমাণের ওপর নির্ভর ক’রে বহিরাগত একটি আর্যজাতি অস্তিত্বের কথা বলেছিলেন। তাদের মতে এই জাতি উত্তর-ভারতে এসে পাঞ্জাব ও গাঙ্গেয় উপত্যকায় বসবাস করতে শুরু করে, এবং যে সভ্যতা গড়ে তোলে তার বিষয়ে আমরা বৈদিক সাহিত্যের মাধ্যমে জানতে পারি। গত তিরিশ বছরে এমন অনেক প্রত্বতাত্ত্বিক তথ্য আমাদের গোচরে এসেছে যার ফলে আর্যসংস্কৃতি বিষয়ে আমরা নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য হয়েছি। এই সমস্যাটির অন্য কতকগুলি অংশও খুঁটিয়ে বিচার করার ফলে সমস্যাটি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অনেক বদলে গেছে। যেমন একটি স্পষ্ট ও পৃথক আর্যজাতির অস্তিত্ব প্রমাণ করা এখন খুব কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনুরূপ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে আর্যসংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ বলে মনে করা এবং ধরে নেওয়া যে দেশজ সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ ঢেকে দিয়ে এই সংস্কৃতি তার ওপর আরোপিত হয়েছিলে। এ সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য অর্থপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় একমাত্র যখন আমরা মনে করি যে ‘‘আর্য’’ কথাটি একই ভাষাভাষী একটি গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, নৃতাত্বিক অর্থে, কোনো জাতির বিষয়ে নয়। আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে যে বৈদিক সাহিত্যে আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণ প্রতিফলিত হয়েছে, অবশ্য যদি কখনোই এ দুটি সম্পূর্ণ-ই পৃথক সত্তা হ’য়ে থাকে।
আজ পর্যন্ত যেসব স্বীকৃত ইতিহাস গ্রন্থ লেখা হয়েছে তাতে এই ধরনের সাম্প্রতিক গবেষণার প্রভাব খুবই বিরল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিপরীত ধারার প্রতিই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, যার ফলে যারা আর্যসভ্যতার গৌরব কীর্তন করতে চান তাদের সুবিধে করে দেওয়া হয়েছে। আর্যসংস্কৃতির গুরুত্ব বাড়িয়ে দেবার জন্য হরপ্পার সভ্যতাকে পর্যন্ত আর্য বলে প্রমাণ করার চেষ্টা কো হয়, যদিও প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য এর সম্পূর্ণ বিপক্ষে। ভারতবর্ষকে আর্যদের বাসভূমি বলে প্রতিপন্ন করারও চেষ্টা হয়ে থাকে। এর ঐতিহাসিক যাথার্থ্য যাই হোক না’কেন, আসলে এর উদ্দেশ্য হলো একটি ভুয়ো জাতীয় অহমিকাকে প্রশ্রয় দেওয়া। এবং যে আর্যসংস্কৃতিকে কেউ কেউ ভারতীয় সভ্যতার মূল বলে মনে করেন তাকে সম্পূর্ণ দেশজ বলে প্রমাণ করা। নিঃসন্দেহে এঁদের পক্ষে স্বীকার করা খুবই কষ্টকর যে বৈদিক সভ্যতা মূলত এবং সম্পূর্ণত ভারতীয় ছিলোনা। আর্যসস্কৃতির যে পরিমাণ গুণগান করা হয় তার ফলে ঠিক সে পরিমাণে ভারতীয় ইতিহাসের হিন্দু ব্যাখ্যার শক্তিবৃদ্ধি করা হয়। বৈদিক সাহিত্যে যে সভ্যতার কখা আছে তা যে প্রধানত দেশজ একথা তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া যায়। কিন্ত এর পর উচিত ছিলো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিত্তিতে প্রাক-বৈদিক সভ্যতাগুলির অনুশীলন করে বৈদিক সভ্যতার উদ্ভবে তাদের কতটা অবদান আছে তার পর্যালোচনা করা। যারা জোর করে বলার চেষ্টা করেন যে ভারতীয় ইতিহাসে আর্যসংস্কৃতির বিশেষ প্রাধান্য ছিলো, তারা প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন এবং সাহিত্যিক উপাদানগুলিরও যথোচিত বিশ্লেষণ করেননা। সবচেয়ে শোচনীয় হলো যে, আর্য জীবনযাত্রার বর্ণনাও পুরোপুরি ঠিক হয়না । যেমন আর্যরা কোনো উপলক্ষে গোমাংস খেতেন না বা মদ্যপান করতেন না, একথা বলার অর্থ হলো সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যকে একেবারেই অস্বীকার করা।
আর্যসমস্যা ছাড়াও অন্য কয়েকটি সমস্যা সম্বদ্ধেও আমাদের পূর্ণ-বিবেচনা প্রয়োজন। গুপ্ত আমলের স্বর্ণযুগের তত্ত্বটি পরস্পর বিরোধিতায় ভরা। একথা বলা হয় যে, তা ছিলো হিন্দু নবজাগরণের যুগ, অথচ সেষুগের প্রধান শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন মেলে বৌদ্ধ চিত্রকলায় ও ভাস্কর্যে যা বৌদ্ধমঠগুলির অনুপ্রেরণায় নির্মিত হয়েছিল । বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই কৃতিত্ব ছিলো অংশত দেশজ এবং অংশত বিশ্বজনীন। প্রথমদিকের ঐতিহ্য, অর্থাৎ চরক, শুশ্রুত, আর্যভট এবং কিছু পরে বরাহমিহিরের কাজের ধারা থেকে একথা বোঝা যায়। যদিও অহিংসাকেই হিন্দু ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ অবদান বলে মনে করা হয় তবুও সমুদ্রগুপ্তের গৌঁরব-কীর্তনের প্রধান ভিত্তিই হলো তার সামরিক বিজয়। হিন্দু নবজাগরণের প্রধান নিদর্শন তাহলে রয়েছে কালিদাসের রচনায়, প্রথমদিকের পুরাণগুলিতে এবং গুপ্তরাজাদের মুদ্রা ও শিলা-লিপিগুলিতে, যা থেকে মনে হয় তারা হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাহলে এই হিন্দু জাগরণকে কি ‘স্বর্ণযুগে’র অপরিহার্য অংশ ব’লে মনে করা যায়?
প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস-সম্পর্কে এমন অনেক ধারণা প্রচলিত আছে যেগুলি সরাসরিভাবে সাম্প্রদারিক না হলেও সহজেই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিলে যেতে পারে। এর কারণ এই ধারণাগুলির ঐতিহাসিক যথার্থ্য প্রায় কখনোই বিচার করা হয়না । এরকম একটি ধারণা হলো ভারতীয় সংস্কৃতির আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস। আজকের দিনে কথাটি ধরে নেওরা হয়েছে যে ভারতীয়রা সর্বদাই আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক চিন্তায় নিমগ্ন থেকেছেন এবং দৈনন্দিন জীবনের পার্থিব ব্যাপারকে তুচ্ছ করেছেন। কিন্তু এই ধারণাটি মোটামুটি সাম্প্রতিক, কারণ উনবিংশ শতকের লেখকরা এটিকে ব্যাপকভাবে প্রচলিত করেন। প্রাচীন ভারতে যাঁরা রামরাজ্য অনুসন্ধান করতেন এবং যাঁরা বিশ্বাস করতেন যে এই ধারণাটির ফলে ভারতীয়রা দৈনন্দিন জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলি (অর্থাৎ যন্ত্রশিল্পের প্রচলন, প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি এবং বিদেশী শাসন থেকে মুক্তিলাভ) সম্বন্ধে উদামীন হয়ে পড়বেন, তারাই এই মতবাদের প্রবক্তা। ভারতীয় পণ্ডিতরা এই ধারণাটিকে সোৎসাহে স্বাগত জানালেন কারণ এর ফলে তাদের পরাধীনতার গ্লানি শান্ত হলো । খুব কম লোকেই প্রশ্নটিকে যথার্থভাবে আলোচনা করতে বাজি ছিলেন। আধ্যাত্মিকতা ঠিক কাকে বলে, এবং সমগ্র সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে তা কি বুঝায়? বেশিরভাগ লোক মনে করতেন ভারতীয় সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক উপাদানের অর্থ ছিলো নিশ্চিত অবকাশের সুযোগে অনন্তের ধ্যান করা। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা তো ভারতীয় সংস্কৃতির একচেটিয়া ছিলোনা। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা বলতে যা বোঝায় তা অন্য অনেক প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যেও পাওয়া যায় এবং ঐতিহ্য অনুগামী বহু সমাজেই তার পরিচয় মেলে। একথায় বিস্মিত হবার কিছু নেই যে, প্রাচীন ভারতীয়রা কখনোই নিজেদের নিকট বা দূরের প্রতিবেশীদের চেয়ে বেশি অধ্যাত্মবাদী বলে মনে করতেন না। গ্রীক, চীনা, আরব ইত্যাদি অন্যান্য বিশিষ্ট সভ্যতাসম্পন্ন দেশ থেকে যে সব পর্যটকরা ভারতে আসতেন তারাও এখানে কোনো অসাধারণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আধ্যাত্মিক লক্ষণ দেখতে পান নি। আরো তাৎপর্যপূর্ণ একটি প্রশ্ন হলো সমাজের কোন্ শ্রেণী আধ্যাত্মিক কার্যকলাপে অর্থাৎ অনন্তের ধ্যান, অতীন্দ্রীয় ভাব, আর দার্শনিক চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন? স্বভাবতই তারা সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প । সমগ্র আর্য সম্প্রদায়ের খুবই ছোটো একটি অংশ উপনিষদের অনুশাসনগুলি মেনে চলতেন। এমন কি, ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলিও ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠী রচনা করেছিলেন। এই ধরনের সাহিত্য যে আজও টিকে আছে তার মানে এই নয় যে সমাজের সব লোকই পুরোহিত এবং ঋষি ছিলেন। বৈদিক সাহিত্যই প্রমাণ করে দেয় যে সেই সম্প্রদায়ের লোকেরা দৈনন্দিন জীবনের পার্থিব ব্যাপারগুলি সম্বন্ধে যথেষ্টই অবহিত ছিলেন। খ্রীষ্টাব্দের প্রথম কয়েকটি শতকে বহু নতুন ধর্মীয় সম্প্রদায় ও দার্শনিক চিন্তাধারা বেশ সক্রির ছিলো; অথচ এই যুগের সৃষ্টিশীল সাহিত্য, যেমন কালিদাসের নাটক থেকে, রাজসভায় অধ্যাত্মবাদের বিশেষ কোনো অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায় না। হিন্দু অধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে সবচেয়ে খাঁটি কথা বোধহয় হিন্দু ঐতিহ্য থেকেই জানা যায়। এখানে মানুষের চতুর্বর্গ সম্বন্ধে বলা আছে, তা হলো ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ। এর মধ্যে কেবল শেষোক্ত অবস্থারই লক্ষ্য বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতা । সুতরাং পার্থিব সম্পদ ও সুখকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং— চতুরাশ্রমের মধ্যে সুসামঞ্জস্য ও সংগতিই তার লক্ষ্য।
ভারতীয় সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক ভিত্তির আর একটি দিক হলো অহিংসা। জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীর অহিংস নীতির অনুষঙ্গে এই দিকটি বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। ভারতীয় দর্শনচিস্তায় অহিংসাতত্ত্বের দীর্ঘ ইতিহাস আছে। বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শনের মূল ও হিসেবে এই চিন্তা প্রথম তাত্ত্বিক স্বীকৃতি পায়। অবশ্য দর্শন হিসেবে অহিংস ভারতের একচেটে সম্পত্তি নয়। প্রথম দিকের খ্রীষ্টধর্ম একই মত প্রচার করেছিলো, যদিও তার তুলনায় বৌদ্ধশিক্ষায় এর গুরুত্ব অনেক বেশী ছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে বেশিদিন টে’কেনি। অহিংসার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক তাৎপর্যের মধ্যে তফাৎ করা দরকার। কার্যতঃ হিংসা-নীতি কতটা পরিহার করা হতো, সে-বিষয়ে অল্পই প্রমাণ আছে। আক্রমণ প্রায়ই হিংসাত্মক রূপ নিতো। ভারতীয় ঐতিহ্যে অনেক বড়ো বড়ো ঘটনাই হিংসার সঙ্গে জড়িত। মহাভারতের যুদ্ধ ও ভগবদ্গীতা তার উদাহরণ।
এর একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হলেন সম্রাট অশোক, যাঁর চরিত্রের অসাধারণত্ব শুধুমাত্র ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক পটভূমিকাকে ছাপিয়ে উঠেছে। অত্যন্ত নির্দয় সামরিক অভিযানের পর তিনি ধীরে ধীরে অহিংসার পথ গ্রহণ করেন এবং তার চাইতেও বড়ো কথা, তিনি অহিংসাভিত্তিক একটি রাজনীতির সূচনা করেন। কিন্তু সমস্ত বিশিষ্ট ক্ষমতাবান ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্যে একমাত্র তিনিই এই নীতির প্রচলন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধেও অনেক বিচিত্র পরম্পর-বিরোধী মত আছে। একদিকে যেমন অহিংস নীতির জন্যে তাঁর প্রশংসা করা হয়, অন্যদিকে মৌর্যসাম্রাজ্যের পতনের জন্যেও অনেকে তাঁকে দায়ী করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে এই সমালোচনা শোনা যায় যে অহিংসা-নীতির ফলে দেশ সামরিকভাবে দুর্বল ও নিস্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলো এবং উত্তর-পশ্চিম থেকে আগত আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে নি। অজাতশক্র, চন্দ্রগুপ্ত, মৌর্য, কণিষ্ক সমুদ্রগুপ্ত হর্ষ, দ্বিতীয় পুলকেশিন্, মহেন্দ্রবর্মন, পল্লব, রাজেন্দ্র চোল প্রমুখ প্রথমদিকের ভারতীয় ইতিহাসের মহাবীররা বিজেতা বলেই বীরের সম্মান পেয়েছেন। ভিনসেপ্ট স্মিথের অনুকরণে বছরের পর বছর ইতিহাসের হাজার হাজার ছাত্র সমুদ্রপ্তকে ভারতের নেপোলিয়ন আখ্যা দিয়ে এসেছেন— রাজা এবং উপজাতীয় সর্দারদের একের পর এক পরাজিত ও উচ্ছেদ করেছিলেন বলে তার যশোগান করেছেন। এর মধ্যে অহিংসার স্থান কোথায় তা বোঝা শক্ত।
আর একটি প্রসঙ্গেও দৃষ্টিভঙ্গির অসঙ্গতি দেখা যায়। বেশির ভাগ প্রচলিত ইতিহাসের বইতে গজনীর মামুদ মন্দির ও প্রতিমা ধ্বংস-কারীরূপেই চিত্রিত হয়েছেন । ধরে নেওয়া হয় যে এই কাজের সহজ ব্যাখ্যা হ’লো তিনি মুসলমান। ইসলামধর্ম প্রতিমা পুজার বিরোধী, তাই শুধু একজন মুসলমানই মন্দির ও প্রতিমা ধ্বংস করতে পারেন। এ কথাও ধরে নেওয়া হয় যে, সব মুদলমান শাসকই প্রতিমা ধ্বংস করতে উদ্যত থাকতেন, যদি না অন্য কোনো বাধা এসে তাঁদের নিবৃত্ত করতো। মামুদের ব্যবহারের অন্য কোনো কারণ খোঁজবার বিশেষ চেষ্টা করা হয়না। হিন্দুরাজাদের মধ্যেও কেউ কেউ মন্দির ও প্রতিমা ধ্বংস করেছিলেন কিনা এই প্রশ্নটি উঠলেই অবশ্য অন্য ধরনের যৌক্তিকতা খোঁজা হয়। একাদশ শতকে কাশ্মীরে হর্ষ নামক একজন রাজার কথা জানা যায়, অত্যন্ত সগঠিতভাবে মন্দির ধ্বংসের কাজে লেগেছিলেন। কলহনের রাজতরঙ্গিনী থেকে জানা যায় যে হর্ষ ‘‘দেবোৎপাটননায়ক” (আক্ষরিক অর্থে, যিনি দেবতাদের উৎপাটিত করার কাজে নিযুক্ত হয়েছেন) নামে বিশেষ একজন কর্মচারীকে নিযুক্ত করেছিলেন যার প্রধান কাজ ছিলো মন্দির লুঠ করা। একথা বলা যায় না যে, তিনি স্বভাবতই একজন কালাপাহাড় ছিলেন— আসলে তার মন্দির লুঠের উদ্দেশ্য ছিলো অর্থসংগ্রহ, যা তিনি অন্য কাজে ব্যবহার করতেন।
এতক্ষণ পর্যন্ত যেসব মন্তব্য করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য শুধুই সাম্প্রদারিক দৃষ্টিভঙ্গির নিন্দা করা নয়। এই মন্তব্যর পেছনে দুটি প্রধান অভিপ্রার আছে। প্রথমতঃ ইতিহাসের দাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা হলো নিম্নমানের ইতিহাস রচনা। প্রত্যক্ষভাবে সাম্প্রদায়িক না হয়েও যেক্ষেত্রে মানসিক জড়তার ফলে প্রচলিত মতগুলিই গ্রহণ করা হয়, সেক্ষেত্রেও ইতিহাস রচনা নিম্নমানের হবে। ইতিহাস হ’লো একটি অগ্রগামী বিদ্যা যাতে নতুন গবেষণার রীতি এবং বিশ্লেষণের কৌশল ব্যবহার করা হয়। ইতিহাস রচনার ধারা পর্যবেক্ষণ করলে এইসৰ কৌশলের পরিবর্তন পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে।’ প্রচলিত ধারণাগুলি সর্বদাই যাচাই করা উচিত এব সাক্ষ্য-প্রমাণ দুর্বল হলে তাদের বর্জন করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় কারণ সাম্প্রতিক পরিস্থিতি। মিথ্যা ইতিহাস রাজনীতিমূলক উপকথা রচনায় সাহায্য করছে—ঐতিহাসিকরা তাঁদের অধীত বিদ্যায় এই অধঃপতন মেনে নিতে পারবেন না। যেহেতু ঐতিহাসিকরা সচেতনভাবে অথবা অচেতনভাবে চিন্তার দিক দিয়ে রাজনৈতিক বিশ্বাসের জনক হতে পারেন, সেজন্য ইতিহাসের বিশ্লেষণ রাজনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বলাভ করে।
প্রাচীন ভারতের ইতিহাসচর্চায় আজকাল ক্রমশ নানাধরনের নতুন অনুসন্ধান পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয়েছে, নতুন ধরনের উপাদান কাজে লাগানো হচ্ছে। এই পরিবর্তন শুধু প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের ক্ষেত্রেই আবদ্ধ নয়, সব প্রাচীন সভ্যতার চর্চাতেই এই পদ্ধতি অনুসৃত। এর কারণ হলো সমাজবিজ্ঞান, বিশেষ করে নৃতত্ত্ববিদ্যা ও প্রত্নতত্ত্ব গবেষণার অগ্রগতি। তাছাড়া সব ধরনের সমাজের সুষ্ঠু আনুক্রমিক-চর্চার ফলে প্রাচীন সমাজের ঐতিহাসিক অনুশীলনে নতুন পরিপ্রেক্ষিত দেখা দিয়েছে।
এসবের ফলে সাহিত্যিক উপাদানের বিশ্লেষণী অনুশীলনে অনেক উন্নতি হয়েছে প্রাচীন অতীতের ওপর নতুন আলোকপাত করে। এই ধরনের বিশ্লেষণে অনেক প্রশ্ন ওঠে। প্রথমত, যে পুঁথিটি উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে তা কী তত্ত্বমূলক আলোচনা, না বাস্তব অবস্থার বর্ণনা? ধর্মশান্ত্রগুলি উপাদান হিসেবে ব্যবহার করার সময় এই প্রশ্নটির বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা আছে। যদি সর্বদাই একথা মনে রাখা হয় যে প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রগুলি আইনের দলিল এবং এগুলি সবসময় বাস্তব পরিস্থিতির বর্ণনা না করে ব্যবহারের, ওচিত্য বিচার করে, তাহলে প্রাচীন ভারতের সমাজচর্চা আরো অনেক সঠিক হবে। জাতিভেদ প্রথার বর্ণনায় ধর্মশস্ত্র গুলিতে যে বর্ণবিভাগের আলোচনা আছে, তা একসময় প্রামাণিক ব’লে ধ’রে নেওয়া হ’তো। সমাজবিজ্ঞানের আলোয় এই বিশ্বাসের এখন পুনর্মুল্যায়ন হচ্ছে।
দ্বিতীয়ত উপাদানগুলিকে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা দরকার। কোনো একটি বিশেষ উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে কি সমগ্র সমাজের প্রতিফলন পাওয়া যায়, না বিশেষ একটি গোষ্ঠীর? প্রাচীন সাহিত্যের যেটুকু নিদর্শন পাওয়া যায়, তার বেশির ভাগই রাজা, প্রধান পুরোহিত, ‘মঠ-বিহার, সমৃদ্ধ বণিক প্রমুখ সমাজের অভিজাত শ্রেণীদের সম্পর্কে । ফলে সমাজের ওপরতলার বিষয়েই অনেক বেশি খবর আমরা পাই। তাছাড়া, অধিকাংশ ঐতিহ্যানুসারী পুরানো সমাজে ওপরতলার লোকেরাই কেবল শিক্ষালাভের সুযোগ পেতেন এবং সেই কারণে একমাত্র তারাই পারতেন সাহিত্যের মাধ্যমে তাদের কাজকর্মের বিবরণ রেখে যেতে । উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে কালিদাসের নাটক থেকে রাজা ও রাজসভার সদস্যদের চমৎকার ঐতিহাসিক বর্ণনা মেলে কিন্তু সমগ্র ভারতীয় সমাজের সবশ্রেণীর লোকই যে তার নাটকের চরিত্রদের মতো কাজ করতেন, এরকম ভাবা, অত্যন্ত অনৈতিহাসিক হবে। তাই সমগ্র ছবিটি পেতে গেলে অন্য ধরনের উপাদান খোজা এবং ব্যবহার করা উচিত।
আদি যুগের বৌদ্ধ সাহিত্য ব্রাহ্মণ্যসাহিত্যের উৎকৃষ্ট পরিপূরক, কারণ তাতে প্রতিফলিত হয়েছে সমাজের অপর এক অংশের কার্য-কলাপ, কেননা উপাদানগুলি বিচ্ছিন্নভাবে যেহেতু সমাজের বিশেষ গোষ্ঠীর সংস্কৃতির প্রতিফলন, সেজন্য তা একদেশদর্শী হতে বাধ্য। নানাধরনের উপাদান সর্বদা ব্যবহার করার চেষ্টা যে কতটা জরুরি তা এ থেকেই বোঝা যায় যে, শুধু ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির উপকরণের ওপর নির্ভর করলে সম্রাট অশোকের রাজত্বের বিবরণ কিছুই পাওয়া যেতো না। পুরাণের রাজবংশ তালিকায় তাকে শুধু একজন মৌর্য রাজা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তার শাসনের বিষয় আমরা জানতে পেরেছি ব্রাহ্মণ্যসাহিত্য থেকে নয়, তার নিজের শিলালিপি এবং বৌদ্ধ উপাদান থেকে।
ব্রাহ্মণ্যসাহিত্যে চার্বাক ও লোকায়তদর্শনও বিস্ময়করভাবে প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। বস্তুবাদী দর্শনের ধারার অস্তিত্বের প্রমাণ আমরা বৌদ্ধ, জৈন ও আজীবিক সাহিত্যে এবং দু-একটি শিলালিপি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে পেয়েছি।
প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিকদের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্পূর্ণ প্রাথমিক উৎস হলো প্রত্নতত্ত্ব। প্রত্নতাত্বিক খননকার্য-প্রণালী আজ এতদূর উন্নত হয়েছে যে প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য ইতিহাস রচনায় নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য হতে পারে। দুঃখের বিষয় প্রাচীন ভারত নিয়ে যে সব ঐতিহাসিকরা কাজ করেছেন তারা এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান খুব কমই ব্যবহার করেছেন। সাহিত্যিক উপাদানে প্রধানত সমাজের অভিজাত শ্রেণীর জীবনযাত্রার কথা জানা যায়, কিন্ত প্রত্নতত্ত্ব থেকে শুধু ওপর তলাকার নয়, সাধারণ মানুষের জীবনের কথাও আমরা জানতে পারি। খননকার্যের দ্বারা বাসস্থান, শহর প্রভৃতি পুরাকীর্তিগুলির পুনরুদ্ধারের ফলে সর্বস্তরের মানুষের কথা জানা যায়। সাহিত্য থেকে এখনে পর্যন্ত প্রধানত রাজবংশতালিকা এবং রাজাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্নতত্ত্বে রাজাদের নাম নিয়ে ব্যস্ত নয়। হরপ্পার বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকদের সম্বন্ধে আমরা আজ এতো খবর জানতে পেরেছি যে তাদের দৈনন্দিন জীবনের ছবি পুনরুদ্ধার করা খুব শক্ত নয় যদিও তাদের একজন শাসকের নামও আমরা জানিনা। প্রত্নতত্ত্ব তাই প্রমাণ করেছে যে রাজবংশতালিকা কারো-কারো মনে কৌতূহল জাগালেও অতীতের প্রকৃত অনুসন্ধানে তার গুরুত্ব অল্পই। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান এইভাবে প্রাচীন ইতিহাসের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে।
প্রত্নতত্ত্বের একটি গুরুত্ব হলো তা আমাদের জ্ঞানের ফাঁকগুলি ভরিয়ে দিতে সাহায্য করে। প্রাচীন সাহিত্যে যে সব কাল্পনিক গল্প আছে তাদের ওপরে নির্ভর করে নয়, প্রত্নতত্ত্বের বাস্তব উপাদানের ভিত্তিতেই আমরা আজ সুদূর অতীতে ভারতীয় ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করতে পারছি। আরো গুরুত্বপূর্ণ হলো যে ভারতসভ্যতার ভিত্তি— হরপ্পা এবং হরপ্পা পরবর্তী সস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আজ স্পষ্টতর হয়েছে। ইন্দো-গাঙ্গেয় উপত্যকায় আর্যসভ্যতার আবির্ভাব কোনো সাংস্কৃতিক মরুভূমিতে ঘটেনি। তৎকালে প্রচলিত ও পূর্ববর্তী সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে একে আজ বিচার করতে হবে।
প্রত্নতত্ত্বের তথ্য হলো খননকার্যের দ্বারা প্রাপ্ত কীর্তিগুলি এবং সেই তথ্যের আলোতে সাহিত্যিক উপাদান গৃহীত বা বর্জিত উভয়ই হতে পারে। গাঙ্গেয় উপত্যকার আদি বাসস্থানগুলি থেকে যে ধরনের চিত্রিত ধূসর মাটির বাসন পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে আমাদের এই ধারণাই হয়, যে তারা ছিলেন বেশ সাদাসিদে মানুষ, (নাগরিক) সভ্যতার পালিশবিহীন আদিম কৃষিজীবী। বৈদিক সাহিত্যে যে অতিরঞ্জিত ছবি আমরা পাই তার অনেকখানিই বোধ হয় সাহিত্যিক কল্পনা। হস্তিনাপুরের খননকার্যের ফলে অবশ্য সাহিত্যিক উপাদানের বিলক্ষণ সমর্থন পাওয়া গেছে । মহাভারতে যে প্লাবন ও ধ্বংসের কথা বর্ণিত আছে, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে তার প্রমাণ মেলে । কৌশাম্বীতে সবচেয়ে পুরোনো যে অবশেষ পাওয়া গেছে তা হস্তিনাপুরের বন্যার সমকালীন। কৌশাম্বীতে যে রাজধানী স্থানাস্তুরিত করা হয়েছিল এটি তার একটি ইঙ্গিত। মৌর্যযুগ সম্পর্কেও সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলি অনেক জায়গায় বেশ মিলে যায়।
প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যের আর একটি ফল হ’ল পরিসংখ্যান। মাটির বাসন, পুঁতি ও নানাধরনের ছোটখাটো যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিষ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। মৃৎকার্য যেমন সংখ্যাতাত্বিক অনুসন্ধানের উৎকৃষ্ট ভিত্তি। শুধু যে মাটির বাসনের আকার ও প্রকৃতি থেকে জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তথ্যলাভ করায় তা নয়, বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ ধরনের মৃৎশিল্পের প্রাধান্য থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য বা লোকপ্রচারণের প্রমাণ মেলে । মৌর্যদের ঠিক পূর্ববর্তাকালে এবং মৌর্যযুগে উত্তরাঞ্চলের বিখ্যাত সুমসৃন কালো মাটির বাসন বা সেযুগে বিলাস সামগ্রীরূপে ব্যবহৃত হ’তো তা যেসব অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে তার এলাকা এবং মৌর্যসাম্রাজ্যের প্রকৃত পরিধি মোটাগুটি এক। মুদ্রা নিয়েও উৎকৃষ্ট সংখ্যাতাত্ত্বিক গবেষণা সম্ভব।
শিলালিপিচর্চাকে সাধারণত প্রত্নতত্ত্বের অংশ হিসেবে দেখা হয় যদিও তা হ’লো প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসের সংযোগস্থল। কোনো বিশেষ-যুগের তথ্য সন্ধানে সাহিত্যিক উপাদানের তুলনায় শিলালিপি সাধারণত অনেক বেশি সঠিক খবর দেয়। শিলালিপি নাতিদীর্ঘ হ’তে বাধ্য কারণ তা প্রস্তুত করা যথেষ্ট কঠিন। সুতরাং প্রশস্তিগুলি বাদ দিলে অধিকাংশ শিলালিপিতে অল্পকথায় জরুরি খবর দেওয়া থাকে। উপাদান হিসেবে সাহিত্যের তুলনায় শিলালিপির আরো একটি সুবিধে হলো একবার খোদাই হ’য়ে গেলে তার আর কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়। সাহিত্যের পুনর্লিখন বা সম্পাদনা কিন্তু বন্থ শতাব্দী ধরে চলতে পারে এবং এখানে নানারকম পরিবর্তন বা পরিবর্ধন খুবই সম্ভব। শিলালিপিতে শুধু রাজনীতি প্রসঙ্গে সংবাদ পাই না, অনেক সময় তার চাইতেও বেশি খবর জানা যায় সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে। গুপ্ত-পরবর্তী যুগের ভূদান বিষয়ক শিলালিপিগুলি আইনসম্মত দলিল ব’লে অত্যন্ত মূল্যবান উপাদান এবং এগুলির ফলে সমগ্র যুগটি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বদলে যেতে পারে। উদাহরণন্বরূপ বলা যায় যে বহুদিন পর্যন্ত মনে করা হ’তো এইসময়ে বর্ণভেদপ্রথা আরো কঠোর ছিলো এবং তুর্কি ও আফগান আক্রমণের যুগে ভারতের দুর্বলতার এটি একটি বড়ো কারণ। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে বেশি কঠোর হয়ে ওঠা দূরে থাক, এযুগে বর্ণাশ্রম প্রথা যথেষ্ট শিথিল ছিলো।
প্রত্নতত্ত্বের বোধহয় প্রধান সুবিধা হলো ঐতিহাসিককে তা বাধ্য করে রাজবংশ ও রাজ-সম্পর্কিত ঘটনার নিষ্ফল গবেষণা ছেড়ে সমগ্র সমাজের অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণের দিকে যেতে। স্থাবর ভগ্রাবশেষ নিয়েই প্রত্নতত্ত্বের কারবার, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য পরিবর্তনের মধ্যে। ফলে প্রাচীন অতীতের সামাজিক কাঠামো, অর্থনীতি এবং প্রযুক্তিবিদ্যায় পরিবর্তন প্রভৃতি বহু উপেক্ষিত দিকগুলি প্রত্নতত্ত্ব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাজবংশের ইতিহাস সামগ্রিক ইতিহাসের ছোটো একটি অংশমাত্র।
সাহিত্যিক উপাদানের বিশ্লেষণ বা প্রত্নতত্ত্ব থেকে নতুন তথ্যের সন্ধান এমনিতে যথেষ্ট নয়। প্রাথমিক উৎস সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে গবেষণার বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতাও (শিক্ষা আর চেতনা উভয় অর্থেই প্রাসঙ্গিক) বিচার করে দেখতে হবে। রাজবংশের ইতিহাসের মূল কথা বংশতালিকা নয়, তা হলো ক্ষমতার সংজ্ঞা এবং বণ্টন। রাজাই কি ক্ষমতার কেন্দ্রে ছিলেন, নাকি বিভিন্ন ছোটো ছোটো সংগঠন এবং দপ্তরের মাধ্যমে তার বিকেন্দ্রীকরণ হতো? যদি প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্রের তথ্যটি, অথবা প্রাচীন ভারতীয় রাজার সর্বাঙ্গীণ প্রজারঞ্জনের ধারণাটির সমালোচনা করতে হয়, তাহলে সঠিক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের সাহায্যে তা করতে হবে। কোনোক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক কাঠামো বিষয়ে সঠিক ও সম্যক জ্ঞান ছাড়া ক্ষমতার নীতি নির্ধারণ করা যায়-না। ক্ষমতার নীতি বণ্টন বিষয়ে বুঝতে হলে সবচেয়ে বেশি দরকার অর্থনৈতিক বণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান- শ্রম ও উৎপাদন, রাজস্ব আদায়ের এই দুটি ভিত্তি সম্বন্ধে উপলব্ধি। অর্থনীতিবহির্ভূভ অন্যান্য কারণগুলিরও (যথা ধর্মমোহ) গুরুত্ব আছে, কিন্ত একই পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলি বিচার্য। সামাজিক কাঠামো বুঝতে গেলে বর্ণভেদ প্রথার বিবর্তন অনুসন্ধান করতে হবে। বর্ণাশ্রমধর্মের নীতি অনুযায়ী সত্যিই কি সমাজ জীবন চলতো? তা’হলে এতো ক্ষত্রিয় রাজার আবির্ভাব হয়েছিল কী করে ? নীতি এবং বাস্তবের মধ্যে ফারাকের এটি একটি মাত্র উদাহরণ। অথবা এই ফারাক কি কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যাপারেই ছিলো ? বর্ণাশ্রম প্রথার গড়ন ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যাপারে মিল ছিলো ?
এর চাইতেও, গুরুত্বপূর্ণ হ’লো নানাধরনের গোষ্ঠীর মধ্যে এনিয়ে ভারতীয় ঐতিহাসিকরা অল্পই কাজ করেছেন।সব সমাজেই সংঘাত ও বিরোধের প্রকাশ থাকে, কিন্তু প্রাচীন ভারতের ক্ষেত্রে এগুলি প্রায় কখনোই সঠিকভাবে নিরূপিত বা আলোচিত হয়নি। প্রায়ই বিরোধগুলি এড়িয়ে চলার একটি ঝৌক দেখা যায়, অবশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা মধ্যযুগে আসি। তখন আবার কোনো কোনো ঐতিহাসিক প্রাণপণে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের তালিকা নির্ণয়ে এবং সেগুলির গুরুত্ব উল্লেখ করতে উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। কিন্তু ১২০৬ সালের পরবর্তী ধর্মভিত্তিক হিন্দু-মুসলমান বিরোধগুলিও ঠিক মতো বুঝতে গেলে আগেকার বিরোধের চরিত্র জানা দরকার। প্রাচীন যুগে সিংহাসন দখল, রাজহত্যা এবং যুদ্ধ ইত্যাদি রাজনৈতিক বিরোধের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। বাকি সমাজের ওপর এদের কী ধরেনের প্রভাব পড়তো? ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে নিশ্চয়ই অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বও দেখা দিতো। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মতবিরোধ থেকেও নিশ্চয়ই তাদের নিজেদের ধরনের সংঘর্ষ বাধতো বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে খানিকট। অসহিষ্ণুতা না থাকলে সম্রাট অশোকের পক্ষে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রচার করার এত দরকার হতো না। ব্রাহ্মণ ও চার্বাকবাদীদের যে মতপার্থক্যের ফলে সমস্ত ব্রাহ্মণ্য দার্শনিক সাহিত্য থেকে চার্বাক চিন্তার সব চিহ্ন মুছে ফেলা হয়েছিলো, সে বিরোধের স্বরূপ কী ছিলো? বিশেষ বিশেষ ধর্মের প্রতি কেন বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠী আকৃষ্ট হতেন, যেমন বৌদ্ধধর্মের প্রতি বণিকসম্প্রদায় ও রাজ-পরিবারের মহিলারা? সমগ্র ভারত ইতিহাসে অধিকাংশ জৈনরা কেন বণিকসম্প্রদায় থেকে আসতেন? বিরোধের মূলে কি এইসব হেতু ছিলো?
বিরোধ কখন সংঘর্ষের আকার ধারণ করতো, এ প্রশ্নটিও সমান প্রাসঙ্গিক। আর্যদের সঙ্গে দস্যু ও পাণিদের বিরোধ কী ধরনের ছিলো? প্রচলিত মতানুযায়ী সত্যিই কি তা বর্ণভিত্তিক ছিলো, না তা সাংস্কৃতিক বিরোধের ফলে ঘটেছিল? আদিবাসীদের সঙ্গে যাদের বহিরাগত মনে করা হ’তো, তাদের বিরোধের চরিত্র কি? গ্রীক সিথিয়ানরা কীভাবে ব্রাত্যক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হলেন, ভারতীয়সমাজে কীভাবে তারা মিশে গেলেন? আরব ও তুর্কিদের সম্বন্ধে প্রাক-ত্রয়োদশ শতকের ভারতীয়দের ঠিক কী ধারণা ছিলো ?
এই ধরণের প্রশ্ন তোলার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র বুদ্ধির খেলা নয়। একমাজ এইসব প্রশ্নের ভেতর দিয়েই ইতিহাস চর্চা অর্থপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে । দু’ভাবে এই প্রশ্ন গুলির প্রাসঙ্গিকতা বোঝানো যায়। প্রথমত, ভারত ইতিহাসে প্রত্যেক যুগ সম্বন্ধেই- এই ধরনের প্রশ্ন উঠতে পারে এবং ওঠা সঙ্গত। সমাজ বিবর্তনের প্রতিস্তরেই এগুলি সঙ্গত প্রশ্ন। ভারত ইতিহাসের যথার্থ ধারাবাহিকতা এইসব প্রশ্নের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা থেকেই ধরা পড়বে। দ্বিতীয়ত, অতীতের নানাসময় সম্বন্ধে ধারণার ওপরে এগুলি আরো স্পষ্ট আলোকপাত করবে। তার ফলে আমরা লাভ করবো অতি মূল্যবান তুলনামূলক বিচারের অন্তর্দৃষ্টি এবং ভারত ইতিহাসের ধারা নির্ণয়ে কোন কোন হেতু প্রধান এবং কোনগুলি অ-প্রধান ছিলো তা বুঝতে পারবো। একমাত্র তখনই ভারতীয় ইতিহাসের ওপর ইসলামীয় প্রভাবের সঠিক চরিত্রটি আমাদের বোধগম্য হবে এবং সেইসঙ্গে ভারত-অতীত সৃজনের পেছনে যত ধরনের শক্তি কাজ করেছে তাদের সম্বন্ধেও সত্য ধারনা জন্মাবে।

 নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা
নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা