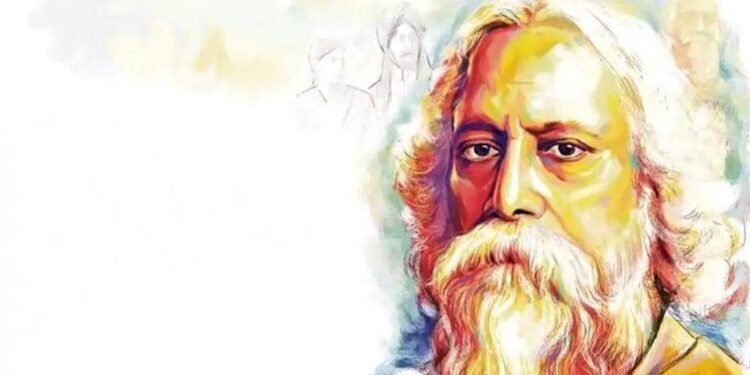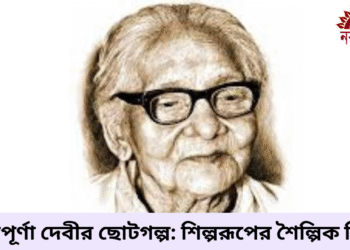হিন্দু-মুসলমান সমস্যা আমাদের সমাজ জীবনের অন্যতম প্রধান দুরারােগ্য ব্যাধি। ভারতীয় উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক কলহের ঘটনা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। বিবেকবান নাগরিকদের সঙ্গে সহৃদয় সাহিত্যিক সমাজ এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন বারবার। রবীন্দ্রনাথের নানা রচনায় হিন্দু-মুসলমান সমস্যার বহুমাত্রিক আলােচনা আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বুঝেছিলেন যে, মুসলমানেরা এদেশের মাটিতে জন্ম গ্রহণ করে এবং এদেশেরই মাটিতে শেষ শয্যা গ্রহণ করে এদেশকে আপনার করে নিয়েছে। ইংরেজদের মতাে তারা কেবল বাণিজ্যের মুনাফা লুঠতেই আসেনি। তাই হিন্দুদের মত মুসলমানদেরও নিজস্ব স্বাতন্ত্রের অধিকার আছে। তবে তা নিশ্চয় উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্যসম্ভাবনাকে স্বীকার করেই।
হিন্দু-মুসলিম বিভেদের কারণে রবীন্দ্রনাথ কতটা দুঃখিত, মর্মাহত ও উদ্বিগ্ন ছিলেন তার পরিচয় ইংরাজ ও ভারতবাসী প্রবন্ধে পাওয়া যায়। তিনি মুসলিম রাজাদের অত্যাচারী ও প্রজাপীড়ক বললেও তাদের অনেক প্রশংসাও করেছেন। মুসলিমদের প্রতি কখনও কখনও বিরূপ হলেও তাদের অনাত্মীয় বলে দূরে ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার মানসিকতা বিশ্বকবির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়নি। ‘ইংরাজের আতঙ্ক’ নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলিম অনৈক্যের জন্য মূলত ইংরেজকেই দায়ী করেছেন। তিনি মনে করেন উভয় সম্প্রদায়কে আলাদা করে রাখা যেন ইংরেজদের অলিখিত নীতি।
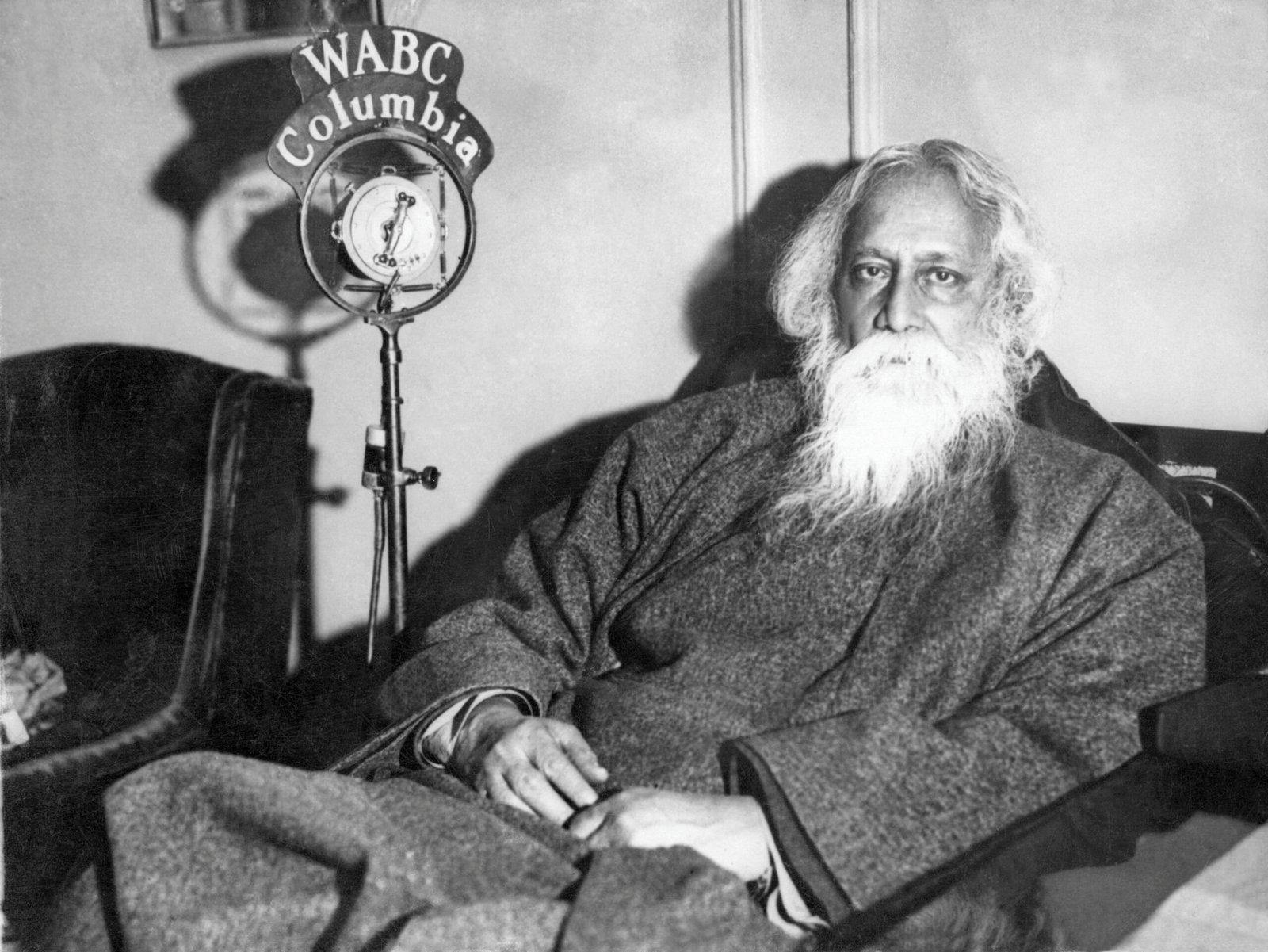
রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে আলােচনা করেননি, এর সমাধানের কথাও ভেবেছেন। তিনি বলেছেন। শিক্ষার দ্বারা, সাধনার দ্বারা এই সমস্যাকে দূর করতে হবে। ডানার চেয়ে খাঁচা বড় এই সংস্কারকে বদলে ফেললেই হিন্দু-মুসলমানের মিলন হবে। যে ধর্মমােহ আমাদের মিলতে দেয় না, সেই মােহ থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে। ধর্মীয় সংহতি যারা চায় না, অসম্প্রীতির ধূলি-ধূসরতা যাদের কাম্য ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ তারা জানে না। ‘আত্ম পরিচয়’-এর পাতায় এদের সম্পর্কেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,
“সকল মানুষেরই “আমার ধর্ম’ বলে একটা জিনিস আছে। কিন্তু সেটিকে সে স্পষ্ট করে জানে না। সে জানে, আমি খ্রিস্টান, আমি বৈষ্ণব, আমি মুসলমান, আমি শাক্ত ইত্যাদি। কিন্তু, সে নিজেকে যে ধর্মাবলম্বী বলে জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিশ্চিন্ত আছে, সে হয়তাে সত্য নয়। নাম গ্রহণে এমন একটা আড়াল তৈরি করে দেয়, যাতে নিজের ভিতরকার ধর্মটা তার চোখেও পড়ে না। তাই তার পুজো-সাধনা-অনুধ্যান সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সে ভুলে যায় তার মধ্যকার ব্রহ্মশত্তিকে, যে শক্তি সকলের মধ্যেই বিরাজমান। ধর্মের ভুল পথে তখনই সে হাঁটতে শুরু করে।”
রবীন্দ্রনাথ ভুল পথে হাঁটা ধর্মের ধ্বজাধারীদের বিরুদ্ধে সেজন্য তীব্র জেহাদ ঘােষণা করেছেন (‘ধর্মমােহ’ পরিশেষ) এভাবে,
“হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি
ধর্মমূঢ়জনেরে বাঁচাও আসি।।
যে পূজার বেদী রক্তে গিয়েছে ভেসে।
ভাঙ্গো ভাঙ্গো, আজি ভাঙ্গো তারে নিঃশেষে,
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানাে,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলােক আনাে।”
সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে ক্ষুব্ধ ও বেদনাহত রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত এক ভাষণে (৮ বৈশাখ ১৩১৩) জানাচ্ছেন, এ কি হলাে ধর্মের চেহারা? এই মােহযুদ্ধ ধর্মবিভীষিকার চেয়ে সােজাসুজি নাস্তিকতা অনেক ভালাে। ঈশ্বরদ্রোহী পাশবিকতাকে ধর্মের নামাবলী পরালে সে কি বীভৎস হয়ে ওঠে তা’ চোখ খুলে একটু দেখলেই বেশ দেখা যায়। ‘ধর্মমােহ’ কবিতায় আমরা আরাে শুনতে পাই —
“ধর্মের বেশে মােহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।”
যারা এই তথাকথিত ধার্মিকদের ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে শান্তির বাণীর গিল্টি দিয়ে ধর্মীয় বীভৎসতাকে ঢাকতে চায় অগ্নিজ্বালা বিদ্রুপে সেই নকল ধার্মিকদের দগ্ধ করে রবীন্দ্রনাথ বলছেন –
“ঐ দলে দলে ধার্মিক ভীরু
কারা চলে গীর্জায়।
চাটুবাণী দিয়ে ভুলাইতে দেবতায়,
দীনাত্মাদের বিশ্বাস, ওরা ভীত প্রার্থনা-রবে
শান্তি আনিবে ভবে।
পাকার লােভ বক্ষে রাখিয়া জমা,
কেবল শাস্ত্র মন্ত্র পড়িয়া লবে বিধাতার ক্ষমা।”
বিধাতা এই ফাঁকা-ভক্তির অপমান কখনাে সইবেন না। কল্যাণ শক্তির তেজে ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত করে নূতন আলােকে নূতন দেশে নূতন জীবন বিকশিত হবে। রবীন্দ্রনাথ বজ্রবাণীর আশীর্বাদ চেয়েছেন যাতে করে তিনি শিশুঘাতী নরঘাতী বীভৎসতার উপর ধিক্কার হানতে পারেন। কিন্তু যতাে অন্ধকারই আজ আমাদের জীবনকে ঘিরে থাকুক না কেন, অন্ধকার বিলীন হবেই নূতন জীবনের আলােকে। রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বাস অম্লান রেখেছিলেন তার অন্তরে। মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বের উপর তার বির্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল অন্তহীন। আধুনিক কাল তার ক্ষণিকের কালাে আবরণ দিয়ে মানুষের যথার্থ স্বরূপকে যতােই ঢাকবার চেষ্টা করুক না কেন, মহাকবির কালজয়ী দৃষ্টি সেই আবরণ সরিয়ে মানুষের মহান সত্তাকে সহজেই দেখেছিল।
‘ধর্মের অধিকার’ শীর্ষক আলােচনায় সংশ্লিষ্ট বিষয়টি আরও প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে “ধর্মের দোহাই দিয়ে কোন জাতি যদি মানুষকে পৃথক করতে থাকে, একশ্রেণীর অভিমানকে আর এক শ্রেণীর মাথার উপর চাপিয়ে দেয় এবং মানুষের চরমতম আশা ও পরমতম অধিকারকে সঙ্কুচিত ও শত খণ্ড করে তবে সে জাতিকে হীনতার অপমান থেকে রক্ষা করতে পারে এমন কোন সভাসমিতি কংগ্রেস-কনফারেন্স, এমন কোন রাষ্ট্রনৈতিক ইন্দ্রজাল নেই।…এই বিকারেই গ্রীস ও রােমের পতন হয়েছে এবং আমাদের দুর্গতির কারণও রয়েছে তথাকথিত ধর্মাচরণের মধ্যে।”
ধর্ম রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল মানুষ হিসেবে মানুষকে দেখা নিয়ে। মানবাত্মার মুক্তি নিয়ে। এই মুক্তিকেই তিনি দীর্ঘজীবনব্যাপী তাঁর সৃজনের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছিলেন। আলােয় আলােয় এই আকাশে, ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে, সর্বজনের মনের মাঝে তিনি মুক্তি দেখেছেন, যেখানে কোনও সংকীর্ণতার স্থান নেই। সীমার মধ্যে অসীমকে তুলে আনতে চেয়েছিলেন বলেই তাে ইঙ্গিত করলেন।
“আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
দেখতে আমি পাইনি
বাহির পানে চোখ মেলেছি।
হৃদয় পানে চাইনি।”
মানবতার মহামন্ত্রে দীক্ষিত রবীন্দ্রনাথকে তার দীর্ঘজীবনে ধর্মীয় অন্ধকার প্রত্যক্ষ্য করতে হয়েছে। প্রথম জীবনে উপনিষদে আশ্রয় গ্রহণ করার পর মানুষের জীবন, মানবিক পৃথিবীর পরিণতি, জীবনের লক্ষ্য ও সাধনা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে রবীন্দ্রনাথের যে দার্শনিক প্রত্যয় গড়ে ওঠে, তাই তাকে আজীবন পথ প্রদর্শন করেছে। ঝড়-ঝঞা মথিত পৃথিবীর অনেক আলােড়ন ও বিব্ধ উচ্ছ্বাস প্রত্যক্ষ্য করার পরও তার ওই ধ্যান-ধারণার কোনও রূপান্তর ঘটেনি।
রবীন্দ্রনাথ সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন ধর্মের জন্য যদি মানুষকে মারতে হয়, সে ধর্ম মিথ্যে। ধর্মের দোহাই দিয়ে যদি মানুষ মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে, এক শ্রেণীর অভিমানকে যদি আরেক শ্রেণীর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, মানুষের অধিকারকে যা সঙ্কুচিত করে, তবে তা না মানাই শ্রেয়। শান্তিনিকেতনে একটি ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বললেন,
“এ কি হল ধর্মের চেহারা? এই মােহমুগ্ধ ধর্মবিভীষিকার চেয়ে সােজাসুজি নাস্তিকতা অনেক ভালাে। ঈশ্বরদ্রোহী পাশবিকতাকে ধর্মের নামাবলী পরালে যে কী বীভৎস হয়ে ওঠে তা চোখ খুলে একটু দেখলেই বেশ বােঝা যায়।”
সারা পৃথিবী জুড়ে ধর্মের নামে যে হিংসা, মানুষে মানুষে বিভাজন ও তা বজায় রাখার যে খেলা চলে রবীন্দ্রনাথের মিলন সাধনার মন তাতে বারবার হোঁচট খায়। এই অশুভ শক্তিকে, মৌলবাদী ধর্মীয় সংঘাতকে চিহ্নিত করে খােলামেলা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, যা থেকে আজও আমরা সতর্ক শিক্ষা নিতে পারি।
“একদিন যারা, মেরেছিল তারে গিয়ে
রাজার দোহাই দিয়ে
এ যুগে তারাই জন্ম নিয়েছে আজি,
মন্দিরে তারা এসেছে ভক্ত সাজি
ঘাতক সৈন্যে ডাকি
‘মারাে মারাে’ ওঠে হাঁকি।
গর্জনে মিশে পূজামন্ত্রের স্বর—
মানবপুত্র তীব্র ব্যাথায় কহেন, হে ঈর।
এ পানপাত্র নিদারুণ বিষে ভরা দূরে ফেলে দাও,
দূরে ফেলে দাও ত্বরা।”
ধর্মের বিকৃতি, যা একশ্রেণীর মানুষের স্বার্থরক্ষার ধ্বজা তা-ই যুগে যুগে মানুষের অত্যাচারের হাতিয়ার হয়ে এসেছে। শােষণের ধারা অব্যাহত রাখতে মানব ইতিহাস মৌলবাদীদের হুঙ্কারে ঢাকা পড়ে গেছে। অনুন্নত দেশগুলিতে জাতিতে জাতিতে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এই মৌলবাদকেই আশ্রয় করে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্থান, ইরান, তুরস্ক, শ্রীলঙ্কা, জাপান, সিঙ্গাপুর, ভারতবর্ষ—সর্বত্র সাম্প্রদায়িকতার জিগির রক্তে ভিজিয়ে দেয় মাটি। ঐতিহ্যময় হাজার বছরের ইতিহাস মুহূর্তে ধসে যায় কামানের গােলায়, শাবল-গাঁইতিতে। বিধে আজ ধর্মীয় অরাজকতা প্রধান হয়ে উঠেছে এ কারণে যে, এই ধর্মতরল দিয়ে মানুষের বিচারবুদ্ধি ভাসিয়ে নেওয়া যায়। ফলে ধর্মীয় মৌলবাদ আজ আবি। ইউরােপ একদিন তরবারি হাতে ধর্ম প্রচারে নেমে পড়েছিল। ধর্মপ্রচারকে গূঢ় বাণিজ্যের স্বার্থেও বেঁধে নিয়েছে।
রবীন্দ্রনাথ ভারত-ইতিহাসের মূলগত বৈশিষ্ট্য যে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য তা যেমন ধরতে পেরেছিলেন, তেমনি বুঝেছিলেন,
“ভারতীয় ঐতিহ্যের মূল প্রণােদনা ঐক্যমূলক। যেখানে পলিটিকস্ নাই সেখানে আবার ‘হিট্রি কিসের’-এ ধরনের কুসংস্কার ইয়ােরােপে চলতে পারে বটে, তবে ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়”, একথা রবীন্দ্রনাথের অজানা ছিল না। তাই তিনি স্পষ্ট ভাষায় লিখেছিলেন, “ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী, এ কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন সে উত্তর আছে ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লথের অভিমুখীন করিয়ে দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে। নিঃসংশয়রূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যােগকে অধিকার করা।”
এই যে ঐক্যবােধ, এই যে এককে প্রত্যক্ষ্য করা ও ঐক্য বিস্তারের চেষ্টা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তা ভারতবর্ষের স্বভাবের মধ্যেই নিহিত। তিনি ভারতের ইতিহাস সম্যক উপলব্ধি করেই বুঝেছিলেন যে, সমাজে দ্বান্দ্বিক প্রতিক্রিয়া থাকবেই, এমনকি ‘কাটাকাটি খুনাখুনি’ও থাকবে। ছিলও, কিন্তু এই সংঘর্ষই ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়, এই কাটাকাটি খুনােখুনিই যে ভারতবর্ষের প্রধানতম ব্যাপার, তাহা নহে। রবীন্দ্র-ভাবনার সামগ্রিকতায় যদি তাকে দেখি তাহলে তর্কাতীতভাবে যা এই মহান দ্রষ্টা ও চিন্তানায়কের জীবনদর্শন থেকে উঠে আসে, তা হল ভারতবর্ষ আবিষ্কার। পণ্ডিতি মন নিয়ে তার রচনা পড়লেই রবীন্দ্রভাবনার অনুধ্যানী পাঠক হওয়া যায় না। যিনি দীর্ঘকালব্যাপী ভেবেছেন, ভাবনার মধ্যেও হয়েছে পর্ব থেকে পর্বান্তর, প্রেক্ষিত হিসেবে জটিল এই দেশে ও পৃথিবীতে ঘটেছিল নানা তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন, তার সামনে উপস্থিত হয়েছে নানা সমস্যা, নিজের মতাে করে তার সমাধানও ভেবেছেন—এমন একজন মানুষকে বুঝতেও বিশেষ বােধের দরকার। এই মননের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চিন্তা অনুধ্যান করলে মানতেই হয়, রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস পাঠের পর এবং অভিজ্ঞতার নিরিখে সঙ্গতভাবেই বুঝেছিলেন যে ভারতবর্ষের ইতিহাসের মূল সুর সংঘর্ষ নয়, সামঞ্জস্য। প্রজ্ঞার সঙ্গে সংবেদনশীলতার মিশ্রণে তার সম্প্রীতিভাবনা উদ্ভাসিত, যা বর্তমানের সংকটকালেও ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক।
হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক এবং মুসলিম প্রসঙ্গ রবীন্দ্রকাব্যে যথেষ্ট না হলেও গৌণ নয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক আলােচনায় তাঁর বিশেষ মানসিকতার ও পরিবর্তিত মানসিকতার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। অবশ্য বঙ্গভঙ্গ বিরােধী আন্দোলন ও পরবর্তীকালে বক্তৃতা ও প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কিত ধারণায় অনেক পরিণত রূপ প্রত্যক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের ধারাবাহিকতা আলােচনায় দেখা যাবে যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কিত চিন্তা পরিণত হওয়ার পূর্বেই তার কবিতায় মুসলিম প্রসঙ্গ চিত্রিত হয়েছে। মূলত রবীন্দ্রনাথের ঘটনাপ্রধান রচনাতেই মুসলিম প্রসঙ্গ আনীত হয়েছে। এবং এই জাতীয় কবিতাগুলির অধিকাংশই সংকলিত হয়েছে ‘কথা ও কাহিনী’ কাব্যে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-কবিতায় মুসলমান প্রসঙ্গ কোনও আকস্মিক বিষয় নয়।
১৩০৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় তার ‘সতী’ সংলাপ-কবিতা—কবিতাটি মুসলিম প্রসঙ্গ যুক্ত। ‘রবিজীবনী’কার প্রশান্ত পাল ‘রবিজীবনী’ গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে জানিয়েছেন, ‘সতী’ কাব্যনাট্য মারাঠি গাথা অবলম্বনে রচিত। বিনায়ক রাওয়ের কন্যা অমাবাঈকে বিবাহরাত্রে বিজাপুরের যবন রাজ অপহরণ করে। পিতা বিনায়ক এবং বাগদত্ত বর শিবাজি দস্যুরক্তপাতে প্রতিশােধ গ্রহণের প্রতিজ্ঞা করেন এবং দীর্ঘকাল পরে রণক্ষেত্রে পিতা-কন্যার সাক্ষাৎ হয়। যবনস্বামী পিতার হস্তে নিহত হয়েছে। অমাবাঈ পিতাকে সম্বােধন করলে পিতা বিনায়ক তাকে ‘কুলকলঙ্কিনী’ রূপে তিরস্কার করেন। অমাবাঈ তার পুত্রের কাছে প্রত্যাবর্তনে উন্মুখ হলে পিতা তাকে ‘শােণিত তর্পণে’ প্রায়শ্চিত্ত করার কথা বলেন। পিতা তার স্বামীকে দস্যুরূপে অভিহিত করলে অমাবাঈ সতী ধর্মের সমুজ্জ্বলতার কথা বলে উচ্চারণ করে—
“যবন ব্রাহ্মণ
সে ভেদ কাহার ভেদ? ধর্মের সে নয়
অন্তরের অন্তর্যামী যেথা জেগে রয়
সেথায় সমান দোঁহে”।
অমাবাঈ নিজেকে পরিপূর্ণা সতীরূপে ঘােষণা করে বলেছে,
“পূর্ণ ভক্তি ভরে
করেছি পতির পূজা হয়েছি যবনী
পবিত্র অন্তরে নহি পতিত রমণী”।
কিন্তু অমাবাঈ-জননী রমাবাঈ যবনী-পাতকিনী’ কন্যার বিরুদ্ধে ধিক্কার বাক্য উচ্চারণ করলে অমাবাঈ বজ্রকণ্ঠে উচ্চারণ করে—
“উচ্চ বিপ্রকুলে জন্মি তবুও যবনে
ঘৃণা করি নাই আমি, কায়বাক্যে মনে
পূজিয়াছি পতি বলে, মােরে করে ঘৃণা
এমন সতী কে আছে?”
শেষ পর্যন্ত ‘সমাজের চেয়ে হৃদয়ের নিত্যধর্ম সত্য চিরদিন’-একথা ঘােষিত হলেও ধর্মান্ধতার হাত থেকে অমাবাঈকে রক্ষা করা সম্ভব হল না। নিত্যধর্মকে সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা গেল না। কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর কবিগুরু ‘রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে ‘সতী’ সংলাপ- কবিতাটিকে স্বজাতির নৃশংসতার চিত্ররূপে গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথের নিরপেক্ষ দৃষ্টির প্রশংসা করেছেন। এ কবিতায় শুধুই নিত্যধর্ম নয়, পতিধর্ম ও সতীধর্মের কথাও উচ্চারিত হয়েছে, এমনকি সাম্প্রদায়িকতা, সতীমঠ ইত্যাদির ঘােষণাও অনুপস্থিত নয়। কাব্যনাট্যটি আদ্যন্ত নাটকীয় এবং কাহিনীটি মারাঠি গাথানির্ভর হলেও মননভাবনা রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজাত।
১৩০৬ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ মুসলিম প্রসঙ্গ যুক্ত বেশ কয়েকটি কবিতা লেখেন। ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ৩০ আর্থিন বন্দী বীর, ১ কার্তিক মানী, ২ কার্তিক প্রার্থনাতীত দান, ৬ কার্তিক শেষ ভিক্ষা, ৯ কার্তিক হােরিখেলা, ৪ অগ্রহায়ণ বিচারক লিখিত হয়। ছটি কবিতাই ‘কথা ও কাহিনী’ কাব্যে সংকলিত। আলােচ্য কবিতাসমূহ মূলত রাজপুত ও শিখ বীরত্ব বিষয়ক।
‘বন্দী বীর’ কবিতায় মুঘল-শিখের যুদ্ধে শিখের বীরত্ব ও মুঘলের নৃশংসতা অঙ্কিত হয়েছে। পাঞ্জাবে গুরুমন্ত্রে নবজাগ্রত শিখ বাহিনীর সঙ্গে মুঘল বাহিনীর যুদ্ধ শুরু হল। ‘মরন আলিঙ্গণে’ মুঘল-শিখ পরস্পরকে আঁকড়ে ধরল—
“দংশন ক্ষত শ্যেন বিহঙ্গ
যুঝে-ভুজঙ্গ সনে।…
‘জয় গুরুজির’ হাঁকে শিখ বীর
সুগভীর নিঃস্বনে।।
মত্ত মােগল রক্ত পাগল।
‘দীন দীন’গরজনে।”
এই যুদ্ধে শিখ বীর বান্দা বন্দী হলেন। শিখ বন্দীদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে যুদ্ধে জয়ী মুঘল দিল্লিতে ফিরে গেল। সাত দিনে সাতশত বন্দী ঘাতকের হাতে প্রাণ হারালেন। ‘সতী’ কবিতায় ধর্মান্ধ হিন্দুদের নৃশংসতা ও ‘বন্দী বীর’ কবিতায় মুঘলের নৃশংসতা কবি সত্যের খাতিরেই চিত্রিত করেছেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় পরে নৃশংসতা চিত্রিত করে কবি নিরপেক্ষ মানসিকতার পরিচয় রেখেছেন।
‘মানী’ কবিতায় ঔরঙ্গজেব বন্দী রাজপুতবীর সিরােহীপতির আত্মসম্মানজ্ঞানে খুশি হয়ে তাঁকে অচলগড়ে রাজত্ব করার অনুমতি দেন। সিরােহীপতিকে রাজসভায় আনার আগে মাড়ােয়ার রাজ যশােবন্ত বন্দীর সম্মান রক্ষার জন্য বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের প্রতিশ্রুতি চাইলে ঔরঙ্গজেব হেসে বললেন—
“তােমার মুখে এমন বাণী
শুনিয়া মনে শরম মানি
মানীর মান করিব হানি
মানীরে শােভে হেন কাজ।”
এই কবিতার প্রধান উদ্দেশ্য হল, নির্ভীকতার মাধ্যমে রাজপুতবীর কিভাবে শত্রুকে জয় করতে সমর্থ হল সে কথা বর্ণনা করা। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই কবিতায় ঔরঙ্গজেবকে প্রবঞ্চক হিসেবে অঙ্কিত করা হয়নি। প্রার্থনাতীত দান’ কবিতায় শিখ বীর তরুন সিংহের নির্ভীকতা চিত্রিত হয়েছে। সুহিদগঞ্জের মাটি শিখ রক্তে বিত হল। পাঠান নবাব বন্দী শিখবীর তরুন সিংহকে ক্ষমা করতে চাইলেন, বিনিময়ে ‘বেণীটি’ কেটে দিতে হবে। কিন্তু শিখের পথে বেণীচ্ছেদের মত অধর্ম আর নেই। তাই—
তরুন সিংহ কহে, “করুণা তােমার
হৃদয়ে রহিল গাঁথা—
যা চেয়েছে তার কিছু বেশী দিব
বেণীর সঙ্গে মাথা।
‘শেষ ভিক্ষা’ কবিতায় শিখ গুরু গােবিন্দ সিংহের চরিত্র মাহাত্ম্য চিত্রিত হওয়ার পাশাপাশি পাঠানদের বীরত্বের প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়েছে। যুদ্ধে হেরেও ছলনার আশ্রয় নিয়ে ভুনাগরাজার রাণী বিজয়ী পাঠান কেশর খাঁকে কিভাবে বধ করলেন ‘হােরি খেলা’ কবিতায় তা চিত্রিত হয়েছে। বিচারক কবিতায় দেখানাে হয়েছে—বিচারকের কাছে মান পদ নয়, ন্যায় শাস্ত্রই বড়। হায়দার আলির সঙ্গে মারাঠাদের যুদ্ধের প্রসঙ্গও এই কবিতায় উঠে এসেছে।
তাছাড়া ‘বলাকা’ কাব্যগ্রন্থে ‘তাজমহল’ ও ‘শাজাহান’ নামে দুটি কবিতা আছে। ‘শাজাহান’ কবিতায় জীবনযৌবন কালস্রোতে ভেসে যায়, তবুও চঞ্চল অপূর্ণ জীবন পূর্ণতায় অভিলাষী। আর ‘তাজমহল’ কবিতায় ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের বিগত হয়ে ওঠার বক্তব্যই প্রকাশিত। দুটি কবিতাই তাত্ত্বিক কবিতা। ‘বলাকা’র পর রবীন্দ্র কাব্যে মুসলিম প্রসঙ্গ যুক্ত কোন কাব্য বা কবিতা আর পাওয়া যায় না।
কবি সুফিয়া কামাল আমাদের জানাচ্ছেন, ‘মহুয়া’ কাব্যের ‘পরিচয়’ কবিতাটি কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জোড়াসাঁকোয় তাঁর সাক্ষাতের স্মৃতির অনুষঙ্গ বহন করে।১
১৯৩৯ সালে পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক বিরােধ প্রকট আকার ধারণ করলে রবীন্দ্রনাথ ‘মর্মান্তিক দুঃখে’ লিখেছিলেন—
“হে বিষয়ী, হে সংসারী, তােমরা যাহারা
আত্মহারা, যারা ভালােবাসিবার বিপথ হারায়েছ,
হারায়েছ আপন জগৎ,
রয়েছে আত্মবিরহী গৃহকোণে,
বিরহের ব্যথা নেই মনে…
লক্ষ্মীর মন্দিরে আমি আনিয়াছি নিমন্ত্রণ জানায়েছি
সেথাকার তােমার আসন অন্যমনে তুমি আছ ভুলি।
জড় অভ্যাসের ধূলি আজি নববর্ষে পুণ্যক্ষণে
যাক উড়ে, তােমার নয়নে দেখা দিক—
এ ভুবনে সর্বত্রই কাছে আসিবার
তােমার আপন অধিকার।”২
রবীন্দ্রনাথ ১৩৪৭-এর ১২ ভাদ্র আবুল মনসুর এলাহি বখশকে শান্তিনিকেতন থেকে যে অটোগ্রাফ-কবিতা উপহার দিয়েছিলেন তারও বিষয়বস্তু কিন্তু ধর্মীয় সংঘাতের বিরােধিতা। এই কবিতায় কবি বলেছিলেন—
“যে করে ধর্মের নামে
বিদ্বেষ সঞ্চিত
ঈশ্বরকে অর্ঘ্য হতে
সে করে বঞ্চিত।”
কবিতাটি ‘শীষমহল’ পত্রিকায় প্রথম মুদ্রিত হয় ১৩৪৮-এর আর্কিন সংখ্যায়। পরে ‘স্ফুলিঙ্গ’ কাব্যে ৩২৮ নং কবিতা হিসেবে সংকলিত।
পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক-কেন্দ্রিক অনেক প্রবন্ধ বা ছােটগল্প রচনা করলেও, তাঁর কবিতায় মুসলিম অনুষঙ্গ কিংবা হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক তেমন উজ্জ্বলভাবে আসেনি।
আসলে রবীন্দ্র-মানস ক্রমশ হিন্দু মুসলমান সমস্যা ও সম্পর্ক বিষয়ে সচেতন হয়েছে। মারাঠি, শিখ ও রাজপুত বীর গাথায় মুসলমান হিন্দুর প্রতিপক্ষ রূপে চিত্রিত হলেও রবীন্দ্রনাথই কিন্তু সেই ব্যক্তি যিনি বঙ্গভঙ্গ বিরােধী জাগরণের কালে মুসলমান সহিসের হাতে রাখি বেঁধে মিলনের আবেগতপ্ত ভাষণ দিয়েছেন। তিনি ক্রমশ ইতিহাসবােধের দ্বারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, হিন্দু-মুসলমান ‘স্বতন্ত্র’ নয়—“বিরুদ্ধ’ তাদের বিরুদ্ধাচরণের জন্য ইংরেজের উপর দায়িত্ব না চাপিয়ে সমাজদেহে তার কারণ অন্বেষণ করতে হবে। তার চিন্তায়—“দেশের কর্মশক্তিকে একটি বিশেষ কর্তৃসভার মধ্যে বদ্ধ করিতে হইবে। অন্তত একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানকে আমরা এই সভার অধিনায়ক করিব—তাহাদের নিকট নিজেকে সম্পূর্ণ অধীন, সম্পূর্ণ নত করিয়া রাখিব। তাহাদিগকে সম্মানিত করিয়া দেশকে সম্মানিত করিব।” তিনি লক্ষ্য করেছেন—
১. হিন্দু মুসলমানের পার্থক্যটাকে আমরা সমাজে কুশ্রীভাবে বেআব্রু করে রেখেছি।
২. বাংলাদেশে নিম্নশ্রেণির মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণ নিম্নশ্রেণির প্রতি হিন্দু ভদ্রসমাজের সম্পর্ক রাখা।
৩. সমস্ত বিরােধের মূলে অশিক্ষা, আন্তরিকতার অভাব, শিক্ষাহীনতা, অন্ধ আচারনিষ্ঠা, বিচার ও বুদ্ধিহীনতা। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে, হিন্দু-মুসলমান উভয়েই ‘ভারতভাগ্যের শরিক’। উভয় সম্প্রদায়ের সমকক্ষতা, ঐক্য একমাত্র সম্ভব শিক্ষার প্রসারের দ্বারা শিক্ষার মাধ্যমে বৌদ্ধিক ও আত্মিক উন্নতি এবং মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটে।
‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাস প্রথম বিযুদ্ধ চলাকালীন রচিত হলেও, এর প্রোয় বিধাযুদ্ধ নেই, রাজনৈতিক প্রোপট হিসাবে এসেছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূত্র ধরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী বিরােধী স্বদেশি আন্দোলন, যা ছিল মূলত ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের বৃহত্তর আন্দোলনেরই অঙ্গ। উপন্যাসটি ১৩২২ সালের বৈশাখ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ‘সবুজপত্র’-এ প্রকাশিত হয় এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩২৩ বঙ্গাব্দে। এর কিছুদিন পূর্বে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ঘটনা ব্রিটিশ শাসকের বঙ্গবিভাগের ঘােষণা (৩০ আশ্বিন, ১৩১২/১৬ অক্টোবর, ১৯০৫)। এই ঘােষণা বাঙালি মানসে যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল, তারই বহিঃপ্রকাশ বিভিন্ন প্রতিবাদ আন্দোলনে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই আন্দোলনে শামিল হয়ে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের অচ্ছেদ্য ঐক্যের কথা তুলে ধরেন। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন –
“বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক হে ভগবান।”
গানটির অপর অংশে যাওয়া যাক —
“বাংলার প্রাণ, বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবােন —
এক হউক এক হউক,
এক হউক হে ভগবান।।”
গানটি তখনকার দিনে বাংলার ঘরে বাইরে সকলের মুখে। প্রাণের গভীর থেকে উঠে আসছে এই গানটি। এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি আমাদের লক্ষ করার বিষয়। রবীন্দ্রনাথ এই গানটিতে বাংলার প্রকৃতি ও বাংলার মানুষকে এক বন্ধনে গ্রোথিত করেছেন। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মিলন, আর এই সূত্র ধরেই মানুষে মানুষে সম্প্রীতি।
‘বাংলার জল’ মন্ত্রগানটি রচনা করা ছাড়াও, “৩০শে আর্কিন কলিকাতায় যে ‘রাখিবন্ধন’ উৎসব অনুষ্ঠিত হইল, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ সর্বসাধারণের সহিত মিলিয়া অংশ গ্রহণ করিলেন প্রাতে ‘বন্দেমাতরম্’ সম্প্রদায় পরিচালিত শােভাযাত্রার পুরােভাগে। তিনি ছিলেন। গঙ্গাঘাটে তিনি বাংলাদেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া বাংলার মাটি’র মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন। আপামর জনের হস্তে ‘রাখিবন্ধন’ করিয়াছিলেন। ঐদিন অপরাহ্নে কলকাতায় ফেডারেশন হলের প্রতিষ্ঠার পর যে বিপুল জনতা মিছিল করে বাগবাজারের পশুপতিনাথ বসুর বাড়ির দিকে যায়, সেই মিছিলেও তিনি অংশ নেন। জনতার কণ্ঠে উচ্চারিত হয় তাঁরই নবরচিত সঙ্গীত-
ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে…
ততই মােদের বাঁধন টুটবে।
এদের যতই আঁখি রক্ত হবে..
ততই মােদের আঁখি ফুটবে।।
‘বুলবুল’ পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যায় (চৈত্র ১৩৪৩) রবীন্দ্রনাথের একটি ভাষণ ‘উদ্বোধন’ শিরােনামে প্রকাশিত হয়। এটি ‘বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের চন্দননগর অধিবেশনের উদ্বোধন বক্তৃতা’। এই ভাষণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি আলােকচিত্রও ছাপা হয়। এই সংখ্যাতেই ‘কলস্রোতা’ নামে সম্পাদকীয় মন্তব্য বিভাগে ‘রবীন্দ্রনাথ ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা’ উপশিরােনামে রবীন্দ্রনাথের কবিতা-সংবলিত যে কথাগুলাে মুদ্রিত হয়, নিচে তার সম্পূর্ণই উদ্ধৃত করছি।
“গত ৬ই মার্চ (১৯৩৭) মুসলিম স্টুডেন্ট ফেডারেশানের ভ্রাম্যমাণ দল শান্তিনিকেতন পরিভ্রমণে গিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতন ও শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের সহিত ভাববিনিময় ও আলাপ আলােচনা দ্বারা বাংলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি সুনির্দিষ্ট পথ নির্ধারণই ছিল ইহাদের উদ্দেশ্য।”
বিশ্বভারতীর ছাত্ররা ইহাদিগকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করেন। রবীন্দ্রনাথ অসুস্থতা সত্ত্বেও ইহাদের সহিত ভারতবর্ষ ও ইউরােপের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলােচনা করেন। তিনি বলেন মুসলমান ছাত্রগণ মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতন গিয়া যদি একটি সংস্কৃতিগত ভাবধারা সৃষ্টি করিতে পারেন তবে উহাতে দেশের বিশেষ উপকার হইবে।
সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে আলােচনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বলেন জীবনের শেষভাগে দেশের এইরূপ বিকৃত মনােভাব প্রতি মুহূর্তেই আমাকে পীড়া দিতেছে। যদি আমার দ্বারা এই সমস্যা সমাধানের কোনােরূপ সাহায্য হয়, আমি চেষ্টার ত্রুটি করিব না।
তােমরা কাজে অগ্রসর হও। দেশ রইল, আর রইলে তােমরা দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা।অতঃপর রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখিয়া ছাত্রদের উপহার দেন-
‘তােমার আমার আত্মার মাঝে
ঘন হলাে কাঁটার বেড়া
কখন সহসা রাতারাতি
স্বদেশের অশ্রুজলে
তারেই কি তুলিব বাড়ায়ে
ওরে মূঢ় ওরে আত্মঘাতী!
ওই সর্বনাশটাকে ধর্মের দামেতে করাে দামী
ঈশ্বরের করাে অপমান
আঙিনা করিয়া ভাগ দুই পাশে তুমি আর আমি
পূজা করি কোন শয়তান!
ও কাটা দলিতে গেলে দুই দিকে ধর্ম-ধ্বজী দলে
ধিক্কারিবে। তাহে ভয় নাই,
এ পাপ আড়ালখানা উপাড়ি ফেলিব ধূলিতলে
জানিব আমরা দোঁহে ভাই।
দুই হাত মেনে নাই, এতকাল ধরে তাই
বারবার বিধাতার দান ব্যর্থ হল, অবশেষে আশীর্বাদ কাছে এসে
অভিশাপ হল অবসান।।
তবুও মানবদ্রোহে স্পর্ধাভারে সমারােহে
চলাে যাই অন্ধতার পথে,
এই কথা জেনে যেয়াে –
বাঁচাবে যে মূঢ়কেও
হেন শক্তি নাই এ জগতে।।”
আত্মার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার যে কাঁটাগাছ জমেছে, তাকে উৎপাটন করতে হবে এবং নির্ভকিভাবে উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পরকে ভাই বলে গ্রহণ করতে হবে, কবি এ কবিতায় সেই আশা লালন করেছেন।
বাঙালির জীবনধারা লক্ষ করে তিনি হতাশ হয়েছেন। ব্যঙ্গের সুরে বলেছেন (মানসী, দুরন্ত আশা)
“ভদ্র মােরা, শান্ত বড়াে,
পোেষ-মানা এ প্রাণ
বােতাম-আঁটা জামার নীচে
শান্তিতে শয়ান।
দেখা হলেই মিষ্ট অতি
মুখের ভাব শিষ্ট অতি,
অলস দেহ ক্লিষ্টগতি—
গৃহের প্রতি টান।
তৈল-ঢালা স্নিগ্ধ তনু
নিদ্রারসে ভরা, মাথায় ছােটো বহরে বড়াে
বাঙালি সন্তান।”
ইউরােপ-ফেরত যুবক রবীন্দ্রনাথ বাঙালির এ জীবন-ধারা পছন্দ করতে পারেননি। শান্ত, পােষ-মানা, অলস, ক্লিষ্টগতি, তৈলচিকন দেহ, নিদ্রারসে মগ্ন, মাথায় ছােট এবং বহরে বড় এ-এক অথর্ব জাতি বলে তার মনে খেদ জন্মেছে। জাতি হিসেবে বাঁচতে হলে ক্ষতি প্রগতি, নির্ভীক, ঝঞা-উপেক্ষাকারী জীবন কবির আদর্শ। তাই আরব জাতির জীবন তিনি পছন্দ করেছেন। তিনি আরব দেশে যাননি, তবু বেদুইন জীবনের গতি এবং বৈশিষ্ট্য তাঁকে আকৃষ্ট করে। পরিণত বয়সে বিভ্রমণ করে বহু দেশের বহু আদর্শ তিনি পছন্দ করেছেন, তার প্রশংসা করেছেন কিন্তু সাতাশ বছর বয়সে কেন তিনি বেদুইন হতে চেয়েছেন তা দুর্বোধ্য নয়। ‘দুরন্ত আশা’ কবিতায় উপরােক্তৃত কবিতাংশই তার প্রমাণ।
নানা কারণে, নানাভাবে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে আরব, পারস্য, ইরাক, মিশর, তুরস্ক, এসব দেশ রবীন্দ্র-হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক করেছিল। মনে হয়, এ কবিতা লেখার আগে রবীন্দ্রনাথ কোনাে আরব-দেশ ভ্রমণ করেছেন। তবু লিখলেন-
“ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুয়িন।
চরণতলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন।
ছুটেছে ঘােড়া, উড়েছে বালি,
জীবনস্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয়তলে। বহ্নি জ্বালি
চলেছি নিশিদিন।
বর্শা হাতে, ভরসা প্রাণে,
সদাই নিরুদ্দেশ
মরুর ঝড় যেমন বহে
সকল-বাধা-হীন।”
ইউরােপের নানাদেশ—আমেরিকা, সােভিয়েত রাশিয়া (১৯৩০), চীন ইত্যাদি কবি রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণ করেছেন, কিন্তু ভারতের একান্ত সীমান্তবর্তী প্রতিবেশী আরব পারস্য ভ্রমণ হয়নি—১৯৩২ সালে সত্তর বছর বয়সে তিনি গেলেন ইরানে বা পারস্যে। ইরানি সুফি কবিদের কাব্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন গভীর অনুরাগী—তুরস্কের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত সমর্থন জানিয়েছিল। অথচ ঐ স্বাধীন দেশগুলি কবির ভ্রমণ তালিকার বাইরে ছিল। অজ্ঞাত কারণে রবীন্দ্রনাথ আরব্য জীবনকে ভালােবেসেছিলেন, ইরাক ভ্রমণের সময় তিনি যে বেদুইন জীবন প্রত্যক্ষ্য করলেন, তার প্রায় অর্থ-শতাব্দী পূর্বে লিখেছিলেন ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন।
‘সােনার তরী’ কাব্যের ‘বসুন্ধরা’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, তিনি পৃথিবীর সর্বমানুষের সঙ্গে স্বজাতি সম্বন্ধে বাঁচতে চান। নিজেকে তিনি প্রসারিত করে দিতে চান উদয়সমুদ্র হতে অস্তসিন্ধু-পানে। সেখানেও কবি আরব সন্তানদের মতাে দুর্দম, তাতারদের মতাে নির্ভীক এবং পারসিকদের মতাে পুষ্পবিলাসী হবার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন-
“ইচ্ছা করে মনে মনে স্বজাতি হইয়া থাকি
সর্বলােকসনে দেশে দেশান্তরে উষ্ট্রদুগ্ধ করি পান
মরুতে মানুষ হই আরব-সন্তান দুর্দম স্বাধীন
দ্রাক্ষাপায়ী পারসিক গােলাপকাননবাসী, তাতার নির্ভীক
অর্থারূঢ়, …।”
এই স্বপ্নময় রােমান্টিক অনুভূতির বাস্তব পরিচয় কবি লাভ করেন ১৯৩২ সালে পারস্য ভ্রমণের সময় ।
পাশাপাশি এমন একটা দৃষ্টান্ত আমরা তুলে ধরতে পারি যেখানে দেখতে পাই কবি হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সীমা অতিক্রম করে এক মিলনাত্মক পরিণতিতে পৌঁছেছেন। পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থের ‘শুচি’ কবিতা স্মরণ করেন যেখানে—
“রামানন্দ বললেন, প্রভাতেই যাব এই সীমা ছেড়ে
দেব আমার অহঙ্কার দূর করে তােমার বিপ্ন লােকে।”
তারপরেই জোলা কবীরের সঙ্গে গুরু রামানন্দের সেই অতুলনীয় সাক্ষাকার—কবীর ব্যস্ত হয়ে বললেন,
“প্রভু, জাতিতে আমি মুসলমান,
আমি জোলা, নীচ আমার বৃত্তি।”
উত্তরে রামানন্দের কথাটা স্মরণ করি—
“রামানন্দ বললেন, এতদিন তােমার সঙ্গ পাইনি বন্ধু
তাই অন্তরে আমি নগ্ন,
চিত্ত আমার ধূলায় মলিন।”
রামানন্দ চরিত্র-মাহাত্মে প্রমাণ করেছিলেন ধর্মের উদ্দেশ্য মানুষে মানুষে মিলন। সেখানে জাতপাত তুচ্ছ। চিত্তজাগ্রত হলেই অন্তরের অন্ধকার দূর হয়, আর প্রেমই সেই আলােক উৎস, যার ধারায় স্নাত হলে সকল বিরােধে এক পরম সামঞ্জস্য যুক্ত হয়। পরিণতপ্রজ্ঞা রবীন্দ্রনাথ যখন সেই ভাবনায় উত্তীর্ণ হন, তখন আমাদের কানে অনেকদিন আগে উচ্চারিত তারই কণ্ঠস্বর যেন নতুন করে ধ্বনিত হয়ে উঠে—
“এসাে ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন
ধরাে হাত সবাকার।”
আমরা বুঝতে পারি যে পারিপার্থিকতার গণ্ডি ছাড়িয়ে কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কেমন করে এক বিরাট উত্তরণে সামিল হয়েছেন, যেখানে সম্প্রীতি ও মিলনের ভাবনা জাতিধর্মের সংকীর্ণ সীমা ছাড়িয়ে এক অসীম সামঞ্জস্য ও প্রেমচেতনায় নিজেকে বিস্তৃত করে দিয়েছে।
‘পুনশ্চ’ কাব্যের ‘মুক্তি’, ‘প্রেমের সােনা’ বা ‘স্নান সমাপন’ কবিতায়ও আচারের সীমা অতিক্রম করে সত্যধর্মের সন্ধানের পরিচয় আছে। ঐ সন্ধান জ্ঞানের পথে নয়, প্রেমের পথে। ‘রঙরেজিনী’ কবিতায় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শংকরলালের পাগড়িতে লেখা ছিল— “তােমার শ্রীপদ মাের ললাটে বিরাজে। রাজসভায় যাওয়ার আগে পাগড়ি রং করতে দেওয়া হলে রঙরেজিনী আমিনা তরুণ বয়সের চপলতাবশে একটি ছত্র যােগ করেছিল – পরশ পাই নে তাই হৃদয়ের মাঝে। – হৃদয়ের সঙ্গে যােগ থাকলে সব সাধনাই নিষ্ফল।
‘পুনশ্চ’ কাব্যের মানবপুত্র’ ও ‘শিশুতীর্থ’ কবিতা মানব-স্বীকৃতির আর এক তাৎপর্য উঠে এসেছে। ‘মানবপুত্র’ কবিতাটিতে মহামানব খ্রিস্টকে মানুষের একান্ত আপনজন হিসেবে দেখানাে হয়েছে, যিনি মৃত্যুর পাত্রে নিজের মৃত্যুহীন প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, এবং কবির ধারণায় এখনাে শেষ হয়নি তার নিরবচ্ছিন্ন মৃত্যুর মুহূর্ত। কারণ,
“সেদিন তাকে মেরেছিল যারা
ধর্মমন্দিরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে,
তারাই আজ নূতন জন্ম নিল দলে দলে,
তারাই আজ ধর্মমন্দিরের বেদির সামনে থেকে
পূজামন্ত্রের সুরে ডাকছে ঘাতক সৈন্যকে বলছে ‘মারাে মারাে’
মানবপুত্র যন্ত্রণায় বলে উঠলেন ঊর্ধ্বে চেয়ে, হে ঈশ্বর, হে মানুষের ঈশ্বর,
কেন আমাকে ত্যাগ করলে।”
খ্রিস্ট এখানে রাষ্ট্রিক ষড়যন্ত্রের এবং মারণাস্ত্রের দ্বারা বিপন্ন সকল মানুষের প্রতীক হয়ে উঠেছেন। তবে ষড়যন্ত্র, অন্যায়-বিরােধ, যুদ্ধের বিভীষিকা—এই সংকটের মধ্য দিয়েও মানুষের চরম অভিব্যক্তি লাভের কথা বলা হয়েছে। ‘শিশুতীর্থ’ কবিতায়। এ-কবিতায় ব্যবহৃত ‘সার্থকতার তীর্থ’, ‘প্রেমের তীর্থ’, শক্তির তীর্থ’,—এগুলি এই অভিব্যক্তিরই তীর্থায়ন।
রীতিনীতি, আচারের বন্ধনের চেয়ে মানুষের মূল্যই রবীন্দ্রনাথের কাছে বেশি। ‘পত্রপুট’-এর পনেরাে-সংখ্যক কবিতায় নিখিলমানবের কাছে তাঁর প্রার্থনা-
“হে চিরকালের মানুষ, হে সকল মানুষের মানুষ
পরিত্রাণ করাে
ভেদচিহের তিলক পরা
সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।
হে মহান্ পুরুষ, ধন্য আমি, দেখেছি তােমাকে
তামসের পরপার হতে
আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা।”
এমনি করে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক, আচার-বিচার-মূলক সঙ্কীর্ণ ধর্মের গণ্ডি কাটিয়ে এগিয়ে চললেন কবি কবির চিত্ত ধীরে ধীরে যেন এক নব মানবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করল, যে মৌলিক মানবধর্ম সমস্ত দেশকাল জাতি ধর্ম ও সম্প্রদায়ের বাইরে অথচ তারই অন্তরের বস্তু। এই সাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ বলিষ্ঠ মানবধর্মে অনুপ্রাণিত হয়েই কবি পরবর্তীকালে লিখলেন-
“ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত।
দেবালয়ের মন্দিরদ্বারে,
পূজা-ব্যবসায়ী ওদের ঠেকিয়ে রাখে।
ওরা দেবতাকে খুঁজে বেড়ায়
তার আপন স্থানে সকল বেড়ার বাইরে
সহজ ভর্তির আলােকে, নক্ষত্রখচিত আকাশে,
পুষ্পখচিত বনস্থলীতে,
দোসর-জনার মিলন-বিরহের
গহন বেদনায়।… কবি আমি ওদের দলে—
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন, দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।
পূজারি হাসিমুখে মন্দির থেকে বাহির হয়ে আসে,
আমাকে শুধায়, “দেখে এলে তােমার দেবতাকে?”
আমি বলি, না। অবাক হয় শুনে বলে, জানা নেই পথ?’
আমি বলি না। প্র করে, কোনাে জাত নেই বুঝি তােমার ?
আমি বলি, ‘না’।”
সমস্ত ‘জাত’ চলে গেলে যে ‘জাত’ থাকে সেটা শুধু মানুষ। কবি এখন সেই আদিম মানবের জাতিতে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন, আর কোনাে জাত তার নেই, আর কোনাে জাতিতে কবি বিশ্বাসও করেন না। মানুষের মধ্যেই আছেন কবির দেবতা। শুধু তাই নয়, মানুষের মধ্যে যারা অবজ্ঞাত, হীন, পতিত, অন্ত্যজ, তাদের মধ্যেই কবি তার দেবতার অস্তিত্ব অনুভব করেন সবচেয়ে গভীর, সবচেয়ে সত্যভাবে।
“যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তােমার রাজে
সবার পিছে, সবার নিচে
সব-হারাদের মাঝে।”
এমনি করে সকল গণ্ডি, সমস্ত সম্প্রদায়, সর্বপ্রকার বিভেদ ও বৈষম্যের ঊর্ধ্বে এই যে সর্বৰ্মানুষের ঈশ্বর, কবি তারই সাধনা, তারই আরাধনা করেছেন এবং তাকে খুঁজে পেয়েছেন মানুষের মধ্যে। একদিকে ভিতরে আপন অন্তর্জগতের চিন্ময়লােকে এবং অপর দিকে বাইরে সর্বমানবের মিলন রসে। তার ভাষায়,
“আমার মন যে সাধনাকে স্বীকার করে তার কথাটা হচ্ছে এই যে, আপনাকে ত্যাগ না করে আপনার মধ্যেই সেই মহান পুরুষকে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্র আছে—তিনি নিখিলমানবের আত্মা।”
বিশ্বের সঙ্গে ঐক্যের অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের কাছে তত্ত্বমাত্র নয়—তত্ত্ববিচারের চেয়ে উপলব্ধিকেই তিনি বড়াে করে দেখেছেন। আবার বিশ্বের সঙ্গে ঐক্যের চেতনা যেমন আধ্যাত্মিক অনুভূতিরূপে তেমনই আবার কতকটা বিজ্ঞানভিত্তিক ভাবনার আকারেও প্রকাশিত হয়েছে। ‘নৈবেদ্য’ এর একটি চতুর্দশপদী (২৬ সংখ্যক) স্মরণীয় –
“এ আমার শরীরের শিরায় শিরায় যে প্রাণ-
তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায় সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ববিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তানে লয়ে নাচিয়ে ভূবনে,
সেই প্রাণ চুপে চুপে বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রােমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে, বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু সমুদ্রদোলায় দুলিতেছে
অন্তহীন জোয়ার-ভাটায়।
করিতেছি অনুভব, সে অনন্ত প্রাণ অঙ্গে অঙ্গে
আমারে করেছে মহীয়ান।।
সেই যুগযুগান্তের বিরাট স্পন্দন আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্তন।।”
‘নৈবেদ্য’র চতুর্দশপদীগুলিতে ভারতবর্ষের অচলায়তনিক ধর্মসাধনা, আচারের মরুবালিরাশি, বদ্ধজ্ঞানের কূপমণ্ডুকতাকে বিদ্ধ করেছেন কবি। যেমন,
ক) বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয় (৩০)
খ) তব পূজা না আনিলে দণ্ড দিবে তারে (৪১)
গ) যে ভক্তি তােমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে (৪৫)
ঘ) এ দুর্ভাগা দেশ হতে হে মঙ্গলময় (৪৮)
ঙ) চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির (৭২)
‘পলাতকা’র ফঁাকি’ কবিতায় বিলাসপুরের রুক্মিনী নামে হিন্দুস্থানি স্ত্রীলােকের প্রতি কবিতার কথকের স্ত্রীর স্নেহানুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। পরিশেষে’র ‘জলপাত্র’ কবিতায় চণ্ডালিকা’ নৃত্যনাট্যের মূল ভাব প্রকাশ পেয়েছে। এক ‘নিম্নজাতীয়া’ নারীর কাছে ‘উচ্চজাতীয় মানুষের জলপ্রার্থনা বর্ণশাসিত সমাজে অপরাধবিশেষ। নারী তাই বলেছে-
“প্রভু, তুমি পূজনীয়।
আমার কী জাত জান তাহা হে জীবননাথ।
তবুও সবার দ্বার ঠেলে কেন এলে কোনাে দুখে
আমার সম্মুখে! ভরা ঘট লয়ে কঁাখে মাঠের পথের বাঁকে
তীব্র দ্বিপ্রহরে আসিতেছিলেম ধেয়ে আপনার ঘরে।
চাহিলে তৃষার বারি
আমি হীন নারী তােমারে করিব হেয়।
সে কী মাের শ্রেয়!”
‘সেঁজুতি’ কাব্যগ্রন্থের ‘পরিচয়’ কবিতায় কবি জানালেন যে তিনি মানুষের লােক। এ মানুষ কোনাে বিশেষ বর্ণ বা সম্প্রদায়ের মানুষ নয়, এ মানুষ নির্বিশেষে মানুষ। কবি বললেন-
“সেতারেতে বাঁধিলাম তার,
গাহিলাম আরবার, ‘মাের নাম এই বলে খ্যাত হােক
আমি তােমাদেরই লােক,
আর কিছু নয়—
এই হােক শেষ পরিচয়।”
তবে মানুষের মধ্যে অমানুষও আছে। তারাই সৃষ্টি করে নানা অসাম্য। তারাই ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়গত শ্রেণিভেদ সৃষ্টি করে। এরা শােষক, অত্যাচারী। রবীন্দ্রনাথ এদের ‘মানুষ জন্তু’ বলে সম্বােধন করেছেন।
আসলে মানুষের অন্তরে বিরাজিত সার্বজনীন মানবসত্তার প্রতি গভীর বিশ্বাস থেকেই তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র সকল মানুষকে ভালােবেসেছিলেন। এই সার্বজনীন প্রেমই হল ধর্মবােধ। মানুষ আজ এই ধর্মবােধ উপলব্ধি না করে সংকীর্ণ ধর্মীয় মৌলবাদের শিকার হয়ে হারিয়েছে তার মানবিক চেতনা ও মূল্যবােধ। চারদিকে আজ মানুষ-জন্তুর হুংকার, মনুষ্যত্বের পরাভব পীড়নে-শােষণে মানুষ আজ অবহেলার ধুলােয় গড়াগড়ি যায়। মুখে শান্তির বুলি আওড়ালেও ক্ষমতার মদমত্ততার ভয়ংকর প্রকাশ এখানে ওখানে। ধ্বংস, রণ-রক্তপাতে মানবসভ্যতা আজ চরম সংকটাপন্ন। এই বিপন্ন কালীয় মুহূর্তে মানব-সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আজ রবীন্দ্রনাথের মনুষ্যত্বের বাণীকে উপলব্ধি করতে হবে, তাকেই গ্রহণ করতে হবে সভ্যতার সঞ্জীবনী মন্ত্ররূপে। তারই সুরে সুর মিলিয়ে আমরা যেন বলতে পারি—
“সকল জীব সুখিত হােক,
নিঃশত্রু হােক,
সুখী হয়ে কালহরণ করুক।
সকল জীব দুঃখ হতে প্রমুক্ত হােক,
সকল জীব যথালব্ধ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হােক।
সেই সঙ্গে এও বলতে পারি,
দুঃখ আসে ত আসুক, মৃত্যু হয়ত হােক,
ক্ষতি ঘটে তাে ঘটুক—মানুষ
আপন মহিমা থেকে বঞ্চিত না হােক, সমস্ত দেশকালকে ধ্বনিত করে বলতে পারুক ‘সােহহম্।” ‘রিলিজিয়ন অফ ম্যান’-এর পরিশিষ্টাংশে (পরিশিষ্ট ‘এক’ ও ‘তিন’) রবীন্দ্রনাথ-
বিশ্বভারতী কোয়াটার্লি’ (ইংরেজি) থেকে ক্ষিতি তিমােহন সেনের দুটি প্রবন্ধ সন্নিবেশ করেছেন—‘দ্য বাউল সিঙ্গার্স অফ বেঙ্গল’ আর ‘দাদু অ্যান্ড দি মিস্টরি অফ ফর্ম’। তার ইংবেজি ‘গীতাঞ্জলি’ প্রকাশিত হওয়ার পর ইউরােপের সমালােচকদের কেউ কেউ ‘গীতাঞ্জলি’-র মূলে খ্রিস্টান ভাবনার প্রত্যক্ষ্য প্রভাব আছে বলে মন্তব্য করেছিলেন। সম্ভবত তারই প্রত্যুত্তরস্বরূপ ভারতে যে ঐ ভাবনার দ্বারা দীর্ঘকাল ধরে প্রবাহিত হয়ে আসছে এটি বােঝাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ কবীরের একশােটি দোহা ও ভজন ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। মধ্যযুগের সাধকগােষ্ঠীর সঙ্গে তিনি অন্তরের মিল অনুভব করেছেন—সেকথা প্রত্যক্ষ্য ভাবে বা পরােক্ষ ভাবে বলেছেনও। বাউলদের ভাবের সঙ্গে তার ভাবের মিল তাে ছিলই। এই মিলের মূল কোথায়? ‘রিলিজিয়ন অফ ম্যান’ থেকে কিছু অংশ “একদিন ব্রাহ্মণ রামানন্দ তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে চলে গিয়ে আলিঙ্গন করলেন নাভা চণ্ডালকে, মুসলমান জোলা কবীরকে, রবিদাস চামারকে। সেদিনকার সমাজ তাকে জাতিচ্যুত করলে। কিন্তু তিনি একলাই সেদিন সকলের চেয়ে বড়াে জাতিতে উঠেছিলেন যে জাতি নিখিল মানুষের। সেদিন ব্রাহ্মণমণ্ডলীর ধিক্কারের মাঝখানে একা দাঁড়িয়ে রামানন্দই বলেছিলেন সােহহ্ন সেই সত্যের শক্তিতেই তিনি পার হয়ে গিয়েছিলেন সেইদ্র সংস্কারগত ঘৃণাকে যা নিষ্ঠুর হয়ে মানুষে মানুষে ভেদ ঘটিয়ে সমাজস্থিতির নামে সমাজধর্মের মূলে আঘাত করে।”
হিন্দু-মুসলমানের মিলনের বাণী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক কবিতা-গান রচনা করেছেন। ভারতমাতার দুই সন্তানকে মায়ের দুঃখ ঘােচানাের জন্য লড়াই করতে হবে একত্রে। দলাদলি নয়, ভালােবাসাই মূল কথা। প্রেম দিয়ে জয় করতে হবে সকল বিভেদের নি। যার ধর্ম যাই থাকুক শ্রদ্ধা দিয়ে জয় করতে হবে অপর ধর্মকে। ঐক্যের সুরে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সকলকে আহ্বান জানিয়ে বলতে হবে—
“দাঁড়া দেখি তােরা আত্মপর ভুলি,
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজুলি,
প্রভাত গগনে কোটি শির-তুলি
নির্ভয়ে আজি গাহরে।।
বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে,
রােমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে,
দশদিক সুখে ভাসিবে।”
এরপর যখন ভাইয়ে ভাইয়ে পরস্পর প্রাণের সঙ্গে প্রাণের বাঁধন লাগে তখন –
“মান-অপমান গেছে ঘুচে।
নয়নের জল গেছে মুছে
নবীন আশে হৃদয় ভাসে
ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে।।”
আজকের এই কঠোর সংগ্রামের দিনে ভাইয়ের পাশে ভাইকে দাঁড়িয়ে ভারতমাতার সম্মান রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটে গেল বাবরি মসজিদ ও রাম মন্দিরকে অবলম্বন করে। এই সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে কিছু কিছু ধর্মীয় সংস্থা। বাবরি মসজিদ থাকবে না রাম মন্দির থাকবে—এ বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মৌলবাদী ধর্মীয় নেতাদের প্রতি আমাদের বিনীত অনুরােধ তারা রবীন্দ্র রচনাবলি পাঠ কন, তাহলে সমস্যা সমাধানের পথ নিদের্শ পেতে অসুবিধা হবে না। অবশ্য তারা যদি আপন আপন ধর্মের গণ্ডির মধ্যে নিজেদের না রাখেন। স্বধর্মের মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে পরধর্মের প্রতি যদি সম্মান প্রদর্শনে কুণ্ঠা বােধ না করেন তবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে অসুবিধা হয় না। প্রত্যেককে চিন্তা করতে হবে মানুষ বড় না ধর্ম বড়। চণ্ডীদাসের কথা স্মরণ করুন ‘সবার উপরে মানুষ সত্য’। এ সত্য উপলব্ধি করতে পারলে পরধর্মসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পাবে, ফলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ রােধ করা যাবে।
মানবতার সাধক রবীন্দ্রনাথ। স্বধর্মে ও স্বধর্ম পালনে তিনি একনিষ্ঠ ও একাগ্রতার পরিচয় দিয়েছেন। সংস্কারের আবহাওয়ায় লালিত হয়েও তাকে অতিক্রম করে চলে এসেছেন সংস্কৃতির উজ্জ্বল ভূমিতে, অন্ধতা বিসর্জন দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন বাস্তব ও বিজ্ঞানবুদ্ধির আলােক তীর্থে। তার মানুষের ধর্ম তাই মনুষ্যত্বের ধর্ম, যেখানে প্রাণের অবারিত প্রকাশ, যেখানে নেই সংকীর্ণ জাতীয়তা ও সংস্কারের কালাে চেতনা। হৃদয়কে যে তিনি বড় ঠাঁই দিতেন, তার স্বাক্ষর মৌলানা জিয়াউদ্দীনের স্মৃতি চারণায়?
“কত সে গভীর প্রেম সুনিবিড় অকথিত কত বাণী,
চিরকাল তরে গিয়েছে যখন।
আজিকে সে কথা জানি।”
রােমা রোঁলা রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দিতে গিয়ে যে কথা বলেছেন তাও স্মরণযােগ্য –
“We serve truth alone which is free, with no frontiers, with no limits, with no prejudices of race or caste, we work for it (humanity), but for it as a whole. We do not recognise nations, we recognise the people as one and Universal.”
রবীন্দ্রনাথের শিরায়-উপশিরায় প্রবাহিত হয়েছে মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালােবাসা। মানুষের উপর বিশ্বাস হারানাে তাই তার কাছে ‘পাপ’। সন্ত্রাস-অসম্প্রীতির সংঘাত পৃথিবীর বুকে যুদ্ধের নির্মমতাকেই অবশ্যম্ভাবী করে তােলে। রবীন্দ্রনাথ মহাযুদ্ধের বিভীষিকায় যন্ত্রণাকাতর হয়েছেন। জাপানের চীন আক্রমণ, ইতালির সঙ্গে আবিসিনিয়ার লড়াই, সােভিয়েত রাশিয়ার ফিনল্যান্ড আক্রমণ, স্পেনের গৃহযুদ্ধ কবিকে পীড়িত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন তিপ্পান্ন, তখন প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা বাজে। রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। যুদ্ধ ঘােষণার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে কবি বলেন, “সমস্ত ইউরােপে আজ মহাযুদ্ধের ঝড় উঠেছে। কত দিন ধরে গােপনে গােপনে এই ঝড়ের আয়ােজন চলছিল? অনেকদিন থেকে। আপনার মধ্যে আপনাকে যে মানুষ কঠিন করে বন্ধ করেছে, আপনার জাতীয় অহমিকাকে প্রচণ্ড করে তুলেছে, তার সেই অবরুদ্ধতা আপনাকেই আপনি একদিন বিদীর্ণ করবেই করবে।” বিশ্ববিধাতাকে উদ্দেশ্য করে সাপ্তাহিক উপাসনায় কবি বলেন,
“স্বার্থের বন্ধনে জর্জর হয়ে রিপুর আঘাতে আহত হয়ে মরছে মানুষ, বাঁচাও তাকে। বিপাপের যে মূর্তি আজ রক্তদেখা দিয়েছে, সেই বিপাপকে দূর করাে। বিনাশ থেকে রক্ষা করাে।”
১৯১৪-এর আগস্টে সংঘটিত মহাযুদ্ধ কবির মনকে গভীরভাবে আলােড়িত করেছিল। জার্মানের সঙ্গে বেলজিয়ামের মরণপণ লড়াই যখন চলছে তখন বেলজিয়ামের বীরত্ব-যুদ্ধনৈপুণ্য কবিকে প্রভাবিত করেছিল। জার্মানদের অগ্রগতি রােধ করার ঘটনা স্মরণে রেখেই কবি লেখেন-
“বাধা দিলে বাধবে লড়াই,
মরতে হবে পথ জুড়ে কী করবি লড়াই, সরতে হবে।
লুট করা ধন করে জড়াে,
কে হতে চাস সবার বড়াে
এক নিমেষে পথের ধুলায় পড়তে হবে,
নাড়া দিতে গিয়ে তােমায় নড়তে হবে।
বলাকা কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় সংখ্যক কবিতাতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল মানবসভ্যতার উপরে ঘনিয়ে আসা দুর্যোগের ইঙ্গিত-
“এবার যে ওই এল সর্বনেশে গাে।
বেদনায় যে বান ডেকেছে রােদনে যায় ভেসে গাে।
রক্ত মেঘে ঝিলিক মারে,
বজ বাজে গহন-পারে,
কোন্ পাগল ওই বারে বারে উঠছে অট্টহেসে গাে।।
এবার যে ওই এল সর্বনেশে গাে।”
স্বার্থান্বেষী, লােভী মানুষ দিনের পর দিন অপেক্ষাকৃত দুর্বল মানুষের উপর শােষণ-পীড়ন অব্যাহত রেখেছে। সেই পাপ আজ তার ভয়াবহ মূর্তি নিয়ে পৃথিবীর সর্বত্র আত্মপ্রকাশ করেছে। বিলুপ্ত হয়েছে মানবমহিমা। উদারনৈতিক মানবতাবাদী কবির কাতরােক্তি ধ্বনিত হয়েছে ‘বলাকা’র ৩৭ সংখ্যক কবিতায়—
“ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি? মাথা করাে নত।
এ আমার এ তােমার পাপ।
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহু যুগ হতে জমি বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লােভীর নিষ্ঠুর লােভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্ত ক্ষোভ,
জাতি-অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,
বিধাতার বক্ষে আজি বিদীরিয়া
ঝটিকার দীর্ঘাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।
১৯১৭ সালে রাশিয়ায় নভেম্বর বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এইবিপ্লব একাধারে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বচ্ছ, মানবিক ও যুক্তি নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এই মহান বি-বকে স্বাগত জানিয়েছিলেন ‘বিজয়ী’ কবিতা রচনা করে। কবিতাটি ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় ১৯১৮ সালে৩ প্রকাশিত হয়। পরে ‘পূরবী’ কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়। ঐ কবিতায় উচ্ছ্বসিত আবেগে কবি লিখলেন?
“মশাল তাদের ক্ষুদ্রজ্বালায় উঠল জ্বলে—
অন্ধকারের ঊর্ধ্বতলে বহ্নিদলের রক্তকমল
ফুটল প্রবল দম্ভভরে,
দূর গগনের স্তব্ধ তারা মুগ্ধ ভ্রমণ তাহার পরে।
ভাবল পথিক—এই যে তাদের
মশাল শিখা নয় সে কেবল দন্ডপলের মরীচিকা।
ভাবল তারা—এই শিখাটাই ধ্রুব জ্যোতির তারার সাথে
মৃত্যুহীনের দখিন হাতে জ্বলবে বিপুল বির্বতলে।
ভাবল তারা এই শিখারই ভীষণ বলে
রাত্রিরাণীর দুর্গ প্রাচীর দগ্ধ হবে,
অন্ধকারের রুদ্ধকপাট দীর্ণ করে
ছিনিয়ে লবে। নিত্যকালের বিত্তরাশি
ধরিত্রীকে করবে আপন ভােগের দাসী।”
অর্থাৎ কবি তার অন্তদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেলেন, যারা এতকাল ভেবেছিল নিত্যকালের ‘বিত্তরাশি’ ছিনিয়ে নিয়ে ‘ধরিত্রীকে আপন ভােগের দাসী করবে’ তারা এখন পরাজিত। মহেরের বিশ্ব যেন লুঠ করেছে’—এই ভেবে যারা অট্টহাসি হাসছিল, তাদের সে হাসি এখন স্তব্ধ। কারণ,
“শূন্যে নবীন সূর্য জাগে
ওই যে তাহার বিধা-চেতন কেতন-আগে
জ্বলছে নূতন দীপ্তিরতন তিমির-মথন শুভ্ররাগে
মশালভস্ম লুপ্তিধুলায় নিত্যদিনের সুপ্তি মাগে।
আনন্দলােক দ্বার খুলেছে,
আকাশ পুলকময়জয় ভূলােকের, জয় দ্যুলােকের,
জয় আলােকের জয়।”
কবি আন্তর্জাতিক অবস্থা সম্পর্কে, সাধারণ ধারণা সম্বল করে রুশ বিপ্লব সম্পর্কে তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন ‘অ্যাট দ্যা রুশ রােডস’ প্রবন্ধে।৪
রাশিয়ায় ভ্রমণে গিয়ে রাশিয়ার শ্রমজীবী, কৃষিজীবী মানুষের উন্নতি দেখে কবি অভিভূত হয়েছেন আর ব্যথিত হয়েছেন। ভারতবর্ষের বৃহত্তম মানব সাধারণের দুর্গত জীবনের কথা ভেবে। আর এই বেদনা থেকেই তিনি আরও বেশি আস্থা স্থাপন করলেন সাধারণ মানুষের শক্তির অভিব্যক্তিতে। দেশের অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যবাদ বিরােধী মুক্তিসংগ্রাম, শাসকশ্রেণির শােষণ নিপীড়নে কবিচিত্ত অতিমাত্রায় বেদনার্ত হয়ে পড়ল। ‘ওরা কাজ করে’ কবিতায় সমগ্র বিধব্যাপী মানবতার অপমানের মধ্যেও প্রত্যক্ষ করলেন তিনিঃ
“বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে
যুগ যুগান্তর হতে মানুষের নিত্য প্রয়ােজনে
জীবনে মরণে
ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল
ওরা মাঠে মাঠে বীজ বােনে, পাকা ধান কাটে
ওরা কাজ করে। নগরে প্রান্তরে।”
কবি সুস্পষ্ট অভিমত দিলেন, স্বার্থলােভী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইতিহাসের পাতায় তথ্য হিসাবে স্থান পাবে ঠিকই কিন্তু ‘জ্যোতিষ্কলােকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন থাকবে না তার।
যারা কাজ করে দেশে দেশান্তরে শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে’ তারাই মানব সভ্যতার ইতিহাসে আদৃত হবে। কবি আমৃত্যু মানুষের বিশেষ করে নিপীড়িত, অত্যাচারিত মানুষের প্রতি বিধাস রেখেছেন আর অপেক্ষা করেছেন ‘নবজীবনের আশ্বাসে’ ভরপুর ‘মানব-অভ্যুদয়’-এর জন্য। হানাহানি নয় শান্তিই তার বাণী। ওটাই মানুষের ধর্ম।
এ-কথা বিদিত যে, বৌদ্ধসংস্কৃতি মূলত অহিংসা ও করুণার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রসাহিত্যেও দেখি এই অহিংসা ও কণার মহিমা বিশেষভাবে কীর্তিত হয়েছে। এইজন্যেই তাে ‘হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে তিনি বুদ্ধদেবের পুনরাবির্ভাবকে এমন বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন—নতুন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী। শুধু তাই নয়, পশুহিংসাও রবীন্দ্রনাথের হৃদয়কে পীড়িত করেছে। গীতগােবিন্দের কবি জয়দেব বুদ্ধচরিত্রকে দুটিমাত্র বাক্যদ্বারা বর্ণনা করেছেন –
“নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহ শ্রুতিজাত,
সদয়হৃদয়দর্শিত পশুঘাতম্।”
‘রাজর্ষি’ ও ‘বিসর্জন’ গ্রন্থে পশুবলির নিষ্ঠুরতাকে যেভাবে অঙ্কিত করা হয়েছে তার থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে অহিংসা নীতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ কত গভীর। বাল্মীকি প্রতিভা’ নাটকে ব্যাধের শরে ক্রোঞ্চপাখির মৃত্যুতে বাল্মীকির হৃদয়ে যে গভীর করুণার সঞ্চার হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা থেকেই তার আন্তরিকতা স্পষ্ট অনুভব করা যায়।
অহিংসা ও করুণার পরে ত্যাগের মহিমা। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ চিরকালই ত্যাগধর্মের উপাসক। ‘তেন তক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, উপনিষদের এই বাণী ছিল তাঁর অন্যতম মূলমন্ত্র—
“নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান।
ক্ষয় নাই তার, ক্ষয় নাই।”
এই কথা রবীন্দ্রনাথের মতাে করে আর কেউ বলতে পারেননি। এইজন্যই তাে তিনি মহাত্যাগী তথাগতকে আহ্বান করে বলেছেন –
“এসাে দানবীর দাও ত্যাগকঠিন দীক্ষা,
মহাভি, লও সবার অহঙ্কার ভিক্ষা।।”
ভারতবর্ষের পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ব্যাকুলচিত্তে বুদ্ধদেবকে সম্বােধন করে বলেছেন—
“ওই নামে একদিন ধন্য হল দেশে দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।
সেই নাম আরবার এদেশের নগরে প্রান্তরে দান করাে তুমি।
বােধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থক হােক, মুক্ত হােক মােহ-আবরণ,
বিস্মৃতির রাত্রিশেষে এ ভারতে তােমার স্মরণ
নবপ্রাতে উঠুক কুসুমি।”৫
তাছাড়া ‘কথা’ কাব্যের ‘শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা’, ‘মস্তক বিক্রয়’, ‘মূল্যপ্রাপ্তি’, ‘নগরলক্ষ্মী’, ‘পূজারিণী’ প্রভৃতি রচনায় বুদ্ধদেবের দ্বারা অনুপ্রাণিত ত্যাগের মহিমা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা নেই। এই যে ত্যাগের কথা বলা হল, তার লক্ষ হচ্ছে বিধমৈত্রী। বিমানবের মৈত্রী প্রতিষ্ঠার মধ্যেই ব্যক্তিগত সংকীর্ণ স্বার্থত্যাগের সার্থকতা। এই বিধমৈত্রীর সাধনাই যে তথাগতের জীবনব্রতের মূলবস্তু, একথা বলাই নিষ্প্রয়ােজন। আর যে রবীন্দ্রনাথ তার রুদ্রবীণার ঝঙ্কার দিয়ে আর্য-অনার্য, হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান, পূর্ব-পশ্চিম সকলকে আহ্বান করেছেন –
“মার অভিষেকে এসাে এসাে ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা সবার পরশে পবিত্র-করা।
তীর্থনীরে, আজি ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।”
যে রবীন্দ্রনাথ সর্বমানবের কল্যাণবার্তা নিয়ে বহুবার বিপ্রদক্ষিণ করেছেন, তাঁর জীবনসাধনারও মূল লক্ষ যে বিধমৈত্রী, তা আজ সর্বজনবিদিত। এই লক্ষগত সমতাও বুদ্ধদেবের প্রতি তার শ্রদ্ধা ও অনুরাগের অন্যতম প্রধান হেতু, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।
এছাড়া সামাজিক তথা সাম্প্রদায়িক ধর্ম মানুষের নিত্য ধর্মকে কিরূপে অবমাননা করে তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,
“হিন্দুর কুয়াে থেকে মুসলমানে জল তুললে তাতে জল অপবিত্র করে। এটা বিষম মুশকিলের কথা। কেননা, পবিত্রতা হল আধ্যাত্মিক রাজ্যের আর কুয়াের জলটা হল বস্তুরাজ্যের। যদি বলা যেত, মুসলমানকে ঘৃণা করলে মন অপবিত্র হয় তা হলে সে কথা বােঝা যেত কেননা, সেটা আধ্যাত্মিক মহলের কথা। কিন্তু মুসলমানের ঘড়ার মধ্যে অপবিত্রতা আছে বললে তর্কের সীমানাগত জিনিসকে তর্কের সীমানার বাইরে নিয়ে গিয়ে বুদ্ধিকে ফাঁকি দেওয়া হয়।”৬
এমনি করে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক আচার-বিচারমূলক সঙ্কীর্ণ ধর্মের গণ্ডি কাটিয়ে এগিয়ে চললেন কবি কবির চিত্ত ধীরে ধীরে যেন এক নব মানবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করল, যে মৌলিক মানবধর্ম সমস্ত দেশকাল জাতি ধর্ম ও সম্প্রদায়ের বাইরে অথচ তারই অন্তরের বস্তু। এই সাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ বলিষ্ঠ মানবধর্মে অনুপ্রাণিত হয়েই কবি পরবর্তীকালে লিখলেন,
“ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত।
দেবালয়ের মন্দিরদ্বার,
পূজা-ব্যবসায়ী ওদের ঠেকিয়ে রাখে।
ওরা দেবতাকে খুঁজে বেড়ায় তার আপন স্থানে
সকল বেড়ার বাইরে
সহজ ভক্তির আলােকে,
নক্ষখচিত আকাশে,
পুষ্পখচিত বনস্থলীতে,
দোসর-জনার মিলন-বিরহের
গহন বেদনায়।”৭
এই যে মৈত্রীর আদর্শ, তার মূলে রয়েছে সর্বমানবের ঐক্যের তত্ত্ব। এই ঐক্যতত্ত্বকে রবীন্দ্রনাথ কতখানি গুরুত্ব দান করতেন, তা তার এক ও অবর্ণ ব্রহ্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যায় তথা তার গদ্য ও পদ্য রচনায় বহুস্থলেই সুস্পষ্ট হয়ে আছে। তার দৃষ্টিতে ভারতীয় সংস্কৃতির মূলেই ছিল এই ঐক্যের সাধনা –
“হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা-ওঙ্কারধ্বনি
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি।
তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।” [১লা বৈশাখ (১৩৪৫)]
নববর্ষের দিন এক-প্রবন্ধে কবি তাঁর প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করে অমিয় চত্র(বর্তীকে লেখেন ‘আমাদের জীবনের শেষ পর্বে মানুষের ইতিহাসে এ কী মহামারীর বিভীষিকা দেখতে দেখতে প্রবল দ্রুতগতিতে সংক্রামিত হয়ে চলেছে – দেখে মন বীভৎসতায় অভিভূত হােলাে। এক দিকে কী অমানুষিক স্পর্ধা, আর একদিকে কী অমানুষিক কাপুরুষতা! মনুষ্যত্বের দোহাই দেবার কোনাে বড়াে আদালত কোথাও দেখতে পাইনে।…
এই বিশ্বব্যাপী আশঙ্কার মধ্যে আমরা আছি ক্লীব নিস্ক্রিয়ভাবে দৈবের দিকে তাকিয়ে—এমন অপমান আর কিছু হতে পারে না—মনুষ্যত্বের এই দারুণ ধিক্কারের মধ্যে আমি পড়লুম আজ ৭৮ বছরের জন্ম বৎসরে।”৮ রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। শুধু যুদ্ধের বিরুদ্ধে নয়, যুদ্ধ সংঘটনের পেছনের ক্রিয়াশীলতাকে রবীন্দ্রনাথ এত তীব্র ঘৃণা ও ত্রোঁধে আক্রমণ করলেন, সমকালীন মননে তার কোনাে তুলনা নেই। কবি বললেন—
“শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ মাঝে
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিনী
ভয়ঙ্করী। দয়াহীন সভ্যতা নাগিনী
তুলিছে কুটিল ফণা চক্ষু নিমিষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।”
যুদ্ধের বিরুদ্ধে এত তীব্র ঘৃণা, প্রচণ্ড ক্রোধ ও প্রতিক্রিয়া সমকালীন বাংলা কাব্যের আর কারাে কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে কিনা সন্দেহ। কয়েকদিন পরে যেদিন বুলান নগরীর পতন হয় সেই দিনই কবি অমিয়বাবুকে এক পত্রে তাঁর এই কবিতা রচনা সম্পর্কে লিখেছেন (কালিম্পঙে, ২৪মে, ১৯৪০) “…তুমি জানাে আমার অনেক কবিতা দুর্যোগের ফসল। দুর্দিনের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ আমার কলমের স্বভাব— যে চেম্বারলেনের ছাতার বাঁটে তৈরী নয়। লক্ষ্মীর চেলারা দুঃসময়ের কাছে ঘেবড়ে যায়, কিন্তু সরস্বতীর চেলা তাকে ডিঙিয়ে যায় কিম্বা তার ফুটোয় বাঁশির আওয়াজ তুলে উদ্বিগ্ন হওয়ার দীর্ঘাস ডুবিয়ে দিতে থাকে।৯
মানবিক সৃজনীশলতায় আস্থাশীল রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন সকল বিপর্যয় কেটে গিয়ে একদিন মানুষের মুক্তি আসবেই। সেই আসন্ন সুপ্রভাতের জন্য কবির মঙ্গল-আকাঙ্খর কোন শেষ নেই। এই মাঙ্গলিক চিন্তা দিয়ে তিনি পথভ্রষ্ট মানবিকতার শত্রুর চিত্ততলে জ্বেলে দিতে চান চেতনার মঙ্গলদীপ, প্রার্থনা করেন—যেন বিভ্রান্ত মানবসমাজের বন্দী-দৃষ্টি খুলে গিয়ে জ্বলে ওঠে আলােকের সূর্য-উৎস—
“আলােকের পথে, প্রভু, দাও দ্বার খুলে —
আলােক-পিয়াসী যারা আছে আঁখি তুলে,
প্রদোষের ছায়াতলে হারায়েছে দিশা,
সমুখে আসিছে ফিরে নিরাশার নিশা।
নিখিল ভুবনে তব যারা আত্মহারা
আঁধারের আবরণে খোঁজে ধ্রুবতারা,
তাহাদের দৃষ্টি আনাে রূপের জগতে —
আলােকের পথে।”
কোনাে ঘটনার আপাত সত্যকেই রবীন্দ্রনাথ চরম সত্য বলে বিশ্বাস করেননি। যুদ্ধের ক্ষেত্রেও নয়। যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে বসেও তিনি ধ্বংসকেই শেষ কথা বলে মনে করেননি। তাঁর জীবনের সর্বশেষ মহত্তম ভাষা সভ্যতার সংকট প্রবন্ধে তিনি মানবমহিমার প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাসের কথা ঘােষণা করেছেন। বলেছেন, বিনাশের শক্তিই মানব ইতিহাসের শেষ কথা হতে পারে না। গভীর আশা প্রকাশ করেছেন এই বলে “আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তুপ! কিন্তু মানুষের উপর বির্বাস হারানাে পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তাে আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিমানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিধাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি!” অনেক আগে লেখা ‘শিশুতীর্থ’ কবিতায় ছিল এরই পূর্বাভাস।
রবীন্দ্রনাথ যে সভ্যতার সঙ্কট দেখেছিলেন, আজকের সঙ্কট তার তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে ঘনীভূত। আজও কি মানুষের প্রতি বিশ্বাস রাখা সম্ভব? সম্ভব যদি না হয়, তাহলে বিশ্বাস হারালে পাপ বলে কেন ধিক্কার দেব? তিনি যে সুস্থ আশাবাদী প্রসন্ন জগতে জন্মেছিলেন, সেই তুলনায় পরবর্তী জগৎ জরাজীর্ণ। সেখানে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন আমাদের কী হদিশ দিতে পারে? অন্নদাশঙ্কর মনে করেন, এরজন্যে আমাদের তাকাতে হবে আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক দিকে এবং এমন মানবতত্ত্ব খুঁজে নিতে হবে যা আমাদের এই সঙ্কটকালের অভিজ্ঞতার মােকাবিলা করতে পারে। তাই যথার্থ মানবিকবাদের জন্য প্রয়ােজন শক্ত দার্শনিক কাঠামাের, প্রয়ােজন ভিত্তি হওয়ার মতাে দৃঢ় মানবতত্ত্বের এবং সেই সঙ্গে প্রয়ােজন গুরুত্বপূর্ণ সুপরিকল্পিত কর্মপন্থার। কর্মপন্থাহীন মানবতন্ত্র শূন্যগর্ভ বাক্য।
অন্নদাশঙ্কর মনে করেন, গােষ্ঠীবদ্ধ হলে মানবিকবাদ আর মানবিকবাদ থাকে না। যেমন সাম্প্রদায়িক হলে ধর্ম আর ধর্ম থাকে না। তিনি কথাটি জোরের সঙ্গে বলেছেন :
“ধর্মের বেলায় যেমন সাম্প্রদায়িকতা, মানবিকবাদের বেলাও তেমনি মতবাদ নিয়ে গােষ্ঠীবদ্ধতা।”১০
কঠিন বিশ্বসঙ্কটের মুখে মানবিকবাদ যে কিছু পরিমাণে অসহায়, রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের দিকে তাকিয়ে অন্নদাশংকরের একথা মনে হয়েছে। তিনি বলেছেনঃ
“ধর্মের মতাে মানবিকবাদও পারমাণবিক মহাযুদ্ধের দিনে অসহায়। যদি না মানুষ হিংসা প্রতিহিংসার দৃষ্টান্ত ভেদ করতে শেখে।”
অন্নদাশঙ্কর ১৯৬১ সালে রচনা করেন ‘সভ্যতার সঙ্কট ও রবীন্দ্রনাথ’ প্রবন্ধটি। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি সচেতন থেকেছেন ঊনবিংশ শতাব্দী, বিংশ শতাব্দী থেকে সমকাল ও উত্তরকাল পর্যন্ত। শুধু তাই নয়, তার লেখনীতে উঠে এসেছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের কাল পরিক্রমণ ও জীবনবােধের সাথে সাথে উভয় দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের নানা ঘটনার তথ্যসূত্র। “সভ্যতার সঙ্কট” রবীন্দ্রনাথের কাছে কেবল ভারতীয় সভ্যতার সঙ্কটের ব্যাখ্যা নয়, তা হয়েছে সমগ্র পৃথিবীর সভ্যতার সঙ্কটের কথা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্কটের মুখােমুখি দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ কোনােদিনই উভয় সভ্যতার বিভেদ চাননি, চেয়েছেন উভয়ের সমন্বয় ও মিলন। এই সমন্বয়ী চেতনায় বিশ্বাসী হয়ে অন্নদাশঙ্করও লিখলেন ‘সভ্যতার সঙ্কট ও রবীন্দ্রনাথ’ প্রবন্ধটি। প্রবন্ধের প্রথমেই অন্নদাশঙ্কর লিখেছেন,
“কবি যদি আরাে দশ বছর বাঁচতেন ও আশি বছর বয়সে না লিখে নব্বই বছর বয়সে তাঁর শেষ জবানবন্দী ‘সভ্যতার সঙ্কট’ লিখতেন তাহলে আর যেই হােক ইংরেজ হত না তার ‘Villian of the piece’ শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ মহামানবের আবির্ভাব কামনা করে নবযুগের জন্যে গভীর আশা প্রকাশ করলেন পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণের পূর্ব মুহূর্তে। ১ বৈশাখ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে লেখা ‘শেষ লেখা’ কাব্যের ‘ওই মহামানব আসে’ কবিতায় উচ্চারণ করেছন মানব অভ্যুদয়ের চিরায়ত বাণীঃ
“ওই মহামানব আসে,
দিকে দিকে রােমাঞ্চ লাগে মর্ত্যধুলির ঘাসে ঘাসে। …
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব নব জীবনের আধাসে।
জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়,
মন্দ্ৰি উঠিল মহাকাশে।”
এখানে ‘মহামানব’ কোনাে মহাপুরুষ বা মহান ব্যক্তি নয়। এই মহামানব হল বিশ্বমানব বা সর্বমানব। এই মহামানব যদি বিশ্বমানব বা সর্বমানব বা মানবকুল বা মানুষের সংগ্রামশীল সত্তা বা নিখিল মানবের জাগ্রত বিবেক হয় এবং তার যদি অভ্যুদয় ঘটে তাহলে সভ্যতার সঙ্কট মােচন হবে। অন্নদাশঙ্কর মনে করেন, মহামানব যদি জাগে তবে সঙ্কট মােচন হবে বইকি। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ‘সভ্যতার সঙ্কট’ তার কোনাে আশাভঙ্গের কথা হয়ে দাঁড়ায়নি, বরং তা হয়েছে তার মানবিক মিলনের দৃষ্টিভঙ্গির ফসল।
মানুষকে বাদ দিয়ে তিনি সাহিত্যের কথা চিন্তাও করতে পারেননি। ভাষা ও ছন্দ কবিতায় মানব-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথের কি অপূর্ব পরিচয়! –
“মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বন্ধ চারিধারে,
ঘুরে মানুষের চতুর্দিকে।
অবিরত রাত্রিদিন
মানবের প্রয়ােজনে প্রাণ তার হয়ে আসে ক্ষীণ।
পরিস্ফুট-তত্ত্ব তার সীমা দেয় ভাবের চরণে
ধূলি ছাড়ি, একেবারে ঊর্ধ্ব মুখে অনন্ত গগনে উড়িতে
সে নাহি পারে সঙ্গীতের মতন স্বাধীন
মেলি দিয়া সপ্তসুর সপ্তপক্ষার্তি ভারহীন।…
মানবের জীর্ণ বাক্য মাের ছন্দে দিবে নবসুর
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
ভাবের স্বাধীন লােক, পক্ষ বান অর্থরাজ সম
উদ্দাম সুন্দর গতি, সে আশ্বাসে ভাসে চিত্ত মম। ..
গাবে যুগে যুগান্তরে সকল গম্ভীর কলম্বনে
দিক হতে দিক-দিগন্তরে-মহামানবের স্তব গান
ক্ষণস্থায়ী নবজন্মে মহৎ মর্যাদা করি দান।”
রবীন্দ্রনাথ পূর্বে অবশ্য সন্ত্রাসের লাল মেঘ প্রত্যক্ষ করেছিলেন ইতিহাস থেকে জেনেছিলেন তার প্রােথিত শিকড়টিকে। তাই আমরা দেখতে পাই, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে, বঙ্গভঙ্গের পর সশস্ত্র বিল্পবীরা যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হল তখন লক্ষবিহীনভাবে ‘সন্ত্রাসবাদী’ কার্যকলাপে মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। সে মানুষ যেমন সাগর পাড়ের তােঙ্গ—তেমন ভারতীয়ও। মানুষের এই বেমানান-বেসামাল মৃত্যুকে রবীন্দ্রনাথ সহজে মেনে নেননি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজির নেতৃত্বে অহিংস আন্দোলনের পাশাপাশি সহিংস আন্দোলনের ধারাও ছিল অব্যাহত। মানবতার জয়গান যিনি চান, তিনি মানুষের মৃত্যুকে এভাবে মেনে নিতে পারেননি। প্রতিরােধ, প্রতিবাদের তাে ভিন্ন মত, ভিন্ন পথ থাকতে পারে। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের আসল রূপ প্রত্যক্ষ করে সংশয়দীর্ণ মানসিকতা নিয়ে জীবনের উপান্তে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে ব্যক্ত করেন তার অনুভব এবং তােলেনঃ-
“আমি যে দেখেছি গােপন হিংসা কপটরাত্রি ছায়ে—
হেনেছে নিঃসহায়ে।
আমি যে দেখেছি—প্রতিকারহীন, শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথাকুটে।।…
যাহারা তােমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলাে,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছাে ভালাে?”১১
সন্ত্রাসের সঙ্গে যারা যুক্ত প্রকৃতপ েতারা নির্দিষ্ট কোনও ভূখণ্ডের নাগরিক হতে পারে না। সেই সূত্রে কখনােই তাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হতে পারে না —‘সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে। বস্তুত এই সন্ত্রাসের বিপরীতে ‘ঈশােপনিষদ’-ই রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ঈশাবাস্যমিদং সর্ব’ (এই জগতের সব কিছুই ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত) ঈশােপনিষদের এই বাণীটিই হয়ে উঠেছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। একটি গানে আসা যাক—
“তুমি ধন্য ধন্য হে, ধন্য তব প্রেম
ধন্য তােমার জগত রচনা।”
গানটিতে তিনি বলেছেন,
“তােমার প্রেমে তুমি ফুল ফুটালে
তােমার অমৃতরসে তুমি চন্দ্র বিকশিত করলে
সাগরকে গভীর বাণী শেখালে
নদী-কল্লোলে মধুগীতি তুললে
মানবহৃদয়ে প্রেমের অমৃতসুধা ঢেলে দিলে।”
এই একটি গানের মধ্যেই তার পরিপূর্ণ জীবনদর্শন পাওয়া যায়, সবকিছুই ঈশ্বরপ্রেমে আচ্ছাদিত হয়ে আছে—একেবারে ঈশােপনিষদের ফসল। আর, এখান থেকেই তাঁর গানে মিলন ও সম্প্রীতিবােধ। ‘মিলন’ শব্দটিকে সংকীর্ণ ও ব্যাপক, উভয় অর্থেই গ্রহণ করা যায়। সম্প্রীতির ক্ষেত্রেও তাই। রবীন্দ্রনাথ যখনই আমাদের প্রসঙ্গ, তখনই অর্থটি হবে ব্যাপক। অতএব মিলনই বলি বা সম্প্রীতি বলি, তার অর্থটি হবে ‘অহং’ বর্জন। বস্তুত রবীন্দ্র-জীবনই হল এই ‘অহং’ বর্জনের সাধনা। তাঁর গানে গানে এই সত্যটি খুঁজে পাওয়া যায়—“আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তােমার গান’, ‘কেন বাণী তব নাহি শুনি নাথ হে’ ইত্যাদি। দ্বিতীয় গানটির শেষের দিকে ‘আভােগ’ পর্বে তিনি বলছেন, ‘অহংকার চূর্ণ কর, প্রেমে মন পূর্ণ কর। গানটিতে রয়েছে জীবন-দেবতার প্রতি কবির পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং সর্বকল্যাণবাদে আত্মাহুতি। এই হল তার জীবনের বেদমন্ত্র এবং তার সঙ্গীতে মিলন ও সম্প্রীতিবােধের উৎস। মন্দিরের পূজায় ধর্ম নেই, আছে মানুষের সেবায়। আর, এই দর্শনটি থেকেই উৎসারিত তার মিলন ও সম্প্রীতিবােধ। তাই রবীন্দ্রনাথের প্রেমধর্মের স্রোতােধারা যে দিকেই প্রবাহিত হয়েছে, সেখানেই সােনার ফসল ফলেছে।
ঘরে ভালাে হও, সেই ভালােত্ব আপনা থেকেই বাইরে ছড়িয়ে পড়বে। অথাৎ যথার্থ স্বাদেশিকতার পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটবে আন্তর্জাতিকতায়, স্বদেশের প্রতি প্রীতির রূপান্তর ঘটবে বিপর্যায়ের সম্প্রীতি বােধে। রবীন্দ্রনাথের হৃদয় উৎসারিত এই বাণী সমগ্র পৃথিবী শুনেছিল। ভারতে ও ভারতের বাইরে মানুষে মানুষে সম্প্রীতির ডাক দেওয়া হয়েছিল নিচের গানের মধ্য দিয়ে—
“কলুষ কল্মষ বিরােধ হউক নির্মল হউক নিঃশেষে
চিত্তে হােযত বিঘ্ন অপগত নিত্য কল্যাণ কাজে।”
ওই গানটিতে আরও বললেন—
“স্বরতরঙ্গিয়া গাও বিহঙ্গম পূর্ব-পশ্চিম বন্ধু সঙ্গম—
মৈত্রী বন্ধন পুণ্য মন্ত্র পবিত্র বিসমাজে।”
সুতরাং, সংকীর্ণ অর্থে দেশপ্রেম নয়, বিস্তীর্ণ অর্থে বিপ্রেম ও মানবপ্রেম, এই হল রবীন্দ্রসাধনা। অথচ মানব সভ্যতা আজ বিপন্ন। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এমনকি মানবিক আশ্রয়ও আজ বিশুদ্ধ নয়। প্রাচীন বা মধ্যযুগে হানাহানি, অসংহতি ছিল না, এমন নয়। কিন্তু তার রূপ ছিল স্বতন্ত্র। অসভ্য অসংস্কৃত একদল মানুষ বর্বর হতে পারে কিন্তু আজ আমরা যখন একবিংশ শতাব্দীর মানুষ, তখন এই নৃশংসতা মূঢ়তা কাম্য নয়। তবু তা ঘটেছে। দেশপ্রেমের ছদ্মবেশে, মানব হিতৈষীর মুখােশে শুধু সর্বনাশই জন্ম নিচ্ছে, যার প্রতিরােধ এখনই দরকার।
ত্রয়ােদশ শতকে তুর্কি আক্রমণের সময়, অষ্টাদশ শতকে বর্গির আক্রমণের সময় এমনই বিচ্ছিন্নতা, অসংহতি আমাদের দেশে দেখা গিয়েছিল। সেই ভুল পুনরাবৃত্ত হােক, কোনাে সচেতন বুদ্ধিমান মানুষ চাইতে পারে না। এই জন্য আমাদের সেই দর্পণের মুখােমুখি হওয়া দরকার, যেখানে নিজের প্রতিবিম্বর খুঁত ধরা যাবে। যেখান থেকে জেনে নেওয়া যাবে, যথার্থ পথ কী? সেই দর্পণের নাম রবীন্দ্রনাথ। ঐক্যকামী ভারতবর্ষের মর্মকথা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়—“ভারতবর্ষে যে কেহ আছে, যে কেহ আসিয়াছে, সকলকে লইয়া আমরা সম্পূর্ণ হইব।” এই ভারতবােধই রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ববােধে উত্তীর্ণ করেছিল। তাই জীবনের গােধূলিবেলায় উচ্চারণ করেছিলেন।
“আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি।”
জীবনের প্রত্যুষেও বলেছিলেন।
“হৃদয় আজি মাের কেমনে গেল খুলি।
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।”
তাহলে রবীন্দ্র-জীবনের একমাত্র সাধনা ও সাধ হল, মানুষে মানুষে ঐক্য ও মিলন ঘটানাে। শুধু বাঙালি বা ভারতীয় হওয়া নয়, বিশ্ববাসী হওয়া দরকার। তবে যে কোনাে বড় কাজ করতে গেলে আগে ছােটো জায়গায় তার প্রয়ােগ বাঞ্ছনীয়। নিজেকে, পরিবারকে, সমাজকে এবং দেশকে সর্বাগ্রে ভালােবাসতে হবে।।
রবীন্দ্রনাথ বারবার তার লেখায় অতীত ভারতবর্ষের মহিমা তুলে ধরেছেন। হতে পারে, একালে সেই আদর্শ অস্তমিত কিন্তু নতুন করে ঐক্যচেতনা তাে গড়ে তােলা যায়। পুরাতন যদি গৌরবের হয়, বর্তমানকে কেন আমরা কলঙ্কিত করব? তাই রবীন্দ্রনাথ যেমন অতীতকে চিত্রিত করেছেন, তেমনি বর্তমানের ত্রুটি দেখিয়ে ভবিষ্যতের সুন্দররূপও কল্পনা করেছেন। সভ্যতার সংকট দেখেও ‘মানুষের প্রতি বির্বাস হারানাে পাপ’ বলতে দ্বিধা করেননি। এ শুধু তার কথা নয়, এ তাঁর বিশ্বাস। দুঃখের তপস্যায় যে জীবনকে কবি দেখেছেন জেনেছেন তার পরিণাম দুঃখের নয়, আনন্দের আর আনন্দের শেষ কথাই তাে পূর্ণতা, অখণ্ডতা। তার জন্মদিন কবিতায় কবির সেই পরম প্রীতি ও বিশ্বাস ধ্বনিত হয়েছে –
“মানুষের দেবতারে ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা
বর্বর মুখবিকারে তারে হাস্য হেনে যাব,
ব’লে যাব—এ প্রহসনের মধ্যঅঙ্কে অকস্মাৎ হবে
লােপ দুষ্ট স্বপনের নাট্যের কবর রূপে বাকি শুধু রবে
ভস্মরাশি দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।
বলে যাব, দূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শার্ধত অধ্যায়।”
‘ঐকতান’ কবিতায় কবি নিজেকে ‘পৃথিবীর কবি’ বলে সম্বােধন করলেন। বংশ, পরিবার, জাতি, ধর্ম, দেশকে কেন্দ্র করে মানুষের যে সীমাবদ্ধ পরিচয় গড়ে ওঠে সেটার মধ্যেই বিদ্বেষ ও হিংসার বীজ সংগুপ্ত থাকে। সাম্প্রতিককালে অমর্ত্য সেন তার ‘আইডেন্টিটি অ্যাণ্ড ভায়ােলেন্স’ বইতে সেকথাই ব্যাখ্যা করেছেন। এই সীমাবদ্ধ পরিচয় রবীন্দ্রনাথ কখনাে স্বীকার করেননি। ‘ঐকতান’ কবিতায় কবি বলেলেন,
“আমি পৃথিবীর কবি,
যেথা তার উঠে যত ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি—
এই স্বরসাধনায় পৌছিল না বহুতর ডাক
রয়ে গেছে ফাঁক।
কল্পনায় অনুমানে ধরিত্রীর মহা একতান,
কত না নিস্তব্ধ ক্ষণে পূর্ণ করিয়াছে মাের প্রাণ।”
তারপরেই তাঁর মানসভ্ৰমণ।
নানা দেশে প্রকৃতির বিচিত্র রূপ দর্শন,
নানা দেশের নানা কবির সঙ্গে সমগােত্রীয়তা অনুভব,
“দুর্গম তুষারগিরি অসীম নিঃশব্দ নীলিমায়
অশ্রুত যে গান গায়,
আমার অন্তরে বার বার।
পাঠায়েছে নিমন্ত্রণ তার।
দক্ষিণ মেরুর ঊর্ধ্বে যে অজ্ঞাত তারা
মহাজনশূন্যতায় দীর্ঘ রাত্রি করিতেছে সারা,
সে আমার অর্ধরাত্র অনিমেষ
চোখে অনিদ্রা করেছে স্পর্শ অপূর্ব আলােকে।
সুদূরের মহাবী প্রচণ্ড নিৰ্বর মনের গহনে মাের পাঠায়েছে স্বর।
প্রকৃতির ঐকতানস্রোতে নানা কবি ঢালে গান নানা দিক হতে—
তাদের সবার সাথে আছে মাের
এই মাত্র যােগ সঙ্গ পাই সবাকার,
লাভ করি আনন্দের ভােগ
গীতভারতীর আমি পাই তাে প্রসাদ—
নিখিলের সঙ্গীতের স্বাদ।”
আজ আমরা নতুন শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে, এই অস্বাভাবিক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে বেরিয়ে রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে মানবতার উত্তরণের পথ খুঁজব। স্বার্থপরতার আবহকে অতিক্রম করে, ‘সবকিছু নিজের জন্য’—একথা ভুলে আগামীতে একসাথে পা ফেলব আর মানুষ হয়ে মানুষের জন্য, সকলের জন্য জীবন হবে ধন্য’—এটাই অঙ্গীকার হওয়া উচিত।
তথ্যসূত্রঃ
- ১. দ্বিজেন শর্মা, আঁখিজল মুছাইলে, জননী’, আমার একাত্তর ও অন্যান্য, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৮০-৮১।
- ২. প্রভাতকুমার মুখােপাধ্যায়, রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রবেশক, খণ্ড-৪, বিভারতী, পৃ. ১৮৫।
- ৩. প্রবাসী, মার্চ-এপ্রিল (চৈত্র ১৩২৪), কলকাতা।
- ৪. মডার্ন রিভিউ, জুলাই ১৯১৮।
- ৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বুদ্ধদেবের প্রতি’, সারনাথে মুলগন্ধকুটিবিহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রচিত, ১৯৩১।
- ৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘শিক্ষা’ ‘শিক্ষার মিলন।
- ৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পত্রপুট’-১৫।
- ৮. প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৭, কলকাতা।
- ৯. কবিতা, আর্বিন, ১৩৫০, কলকাতা।
- ১০. অন্নদাশংকর রায়, প্রবন্ধ সমগ্র, খণ্ড-৪, মিত্র ও ঘােষ, কলকাতা, ২০০৪, পৃ.৩১।
- ১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘প্রথম’ পরিশেষ।
‘নবজাগরণ’ অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপ্লিকেশনটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।
![]()
‘নবজাগরণ’ এর টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।
‘নবজাগরণ’ এর ফেসবুক পেজে লাইক করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

 নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা
নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা