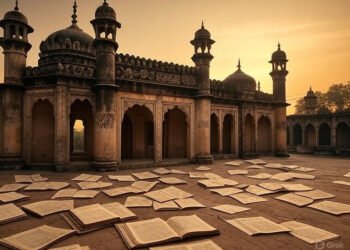ভারতবর্ষ সম্প্রীতির দেশ। যুগে যুগে ভারতবর্ষ পৃথিবীকে সহিষ্ণুতার বাণী, শান্তি ও সংহতির বাণী প্রচার করে এসেছে। ভারতবর্ষ বহু শতাব্দী ধরে যে বােধটিকে লালন করে এসেছে তা হল সহাবস্থানের বােধ—আপন গৃহাঙ্গণে যে প্রতিবাদী ধর্মকে স্থান দিয়েছে আর বহিরাগত ধর্মের সঙ্গে নিজের দেওয়া-নেওয়া গড়ে তুলেছে এবং অন্যের উদ্ধত চ্যালেঞ্জকে নিজের সহিষ্ণুতা দিয়ে বশীভূত করেছে। ভারতের প্রধান ধর্মগুলি—হিন্দুধর্ম, জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ইসলাম ধর্ম, শিখ ধর্ম ও খ্রিস্টান ধর্ম—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পারস্পরিক সহমর্মিতা বজায় রেখে এই ভারততীর্থে সহাবস্থান করে এসেছে। মাঝে মাঝে সম্প্রদায়গত সহাবস্থানে ব্যাঘাত ঘটেছে বিরােধ কখনও কখনও সমুচ্চও হয়ে উঠেছে এবং যার ফলে একদিন অপ্রত্যাশিত দেশবিভাগ মেনে নিতে হয়েছে। তবে এটা ঠিক যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস বিরােধ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্যের কথা যত না বলে তার থেকে অনেক বেশি করে বলে সম্প্রীতির কথা, সংহতির কথা, পারস্পরিক আদান-প্রদানের কথা। ভারতে প্রাচীনকাল থেকে যদি আমরা এর ইতিহাস খুঁজি তবে দেখব যে, বৈষয়িক জীবনের প্রতিটি স্তরে সমঝােতা ও সম্প্রীতির উজ্জ্বল দিকগুলির উপস্থিতি। এই সহিষ্ণুতার কথায় ভারতবর্ষের দার্শনিকরা তাদের দর্শনে বারবার প্রকাশ করেছেন। এই একই কথাই প্রকাশিত হয়েছে সাধারণ মানুষের মন ও মানসিকতায়। কিন্তু পাদ প্রদীপের নীচে যেমন অন্ধকার থাকে, তেমনি ভারতীয় ভাবনার বিপরীতে সমাজচেতনায় জাত-পাত, উচ্চ-নিচ ভেদ, লিঙ্গবৈষম্য সাম্প্রদায়িকতা ভারতের মাটিতে আজও বর্তমান। এ সবই ভারতের উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায়। কিন্তু কে কার কথা শােনে! দেশনেতা হিসেবে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সারাজীবন ধরে বৈষম্য ও অশান্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন এক অন্য জাতের জাতীয়তাবাদী নেতা, যিনি দৃষ্টিভঙ্গিতে ও মননে প্রকৃত অর্থেই ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ। তিনি সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গেই প্রয়াসী হয়েছিলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার মতাে দুরুহ কাজে। এই ক্ষেত্রে তিনি তাঁর রাজনৈতিক দীক্ষা গুরু চিত্তরঞ্জন দাশেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন, তারই দৃষ্টিভঙ্গি ও মনন অনুযায়ী গড়ে তুলেছিলেন। নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র যক্তিগতভাবে নিষ্ঠাবান ধর্মবিধাসী ছিলেন। আর সেই নিষ্ঠা থেকেই তিনি মনে করতেন, ধর্ম হল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয়। তিনি এই প্রত্যয়ে দৃঢ় ছিলেন যে, ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয়টিকে সমষ্টিগত আচরণের ক্ষেত্রে টেনে আনা যায় না, বা ব্যক্তিগত বিশ্বাস দ্বারা সমষ্টিগত আচরণের ত্রুটিকে নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা অনুচিত। ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস সত্ত্বেও তার রাজনীতিতে ধর্মের কোনও ভূমিকা ছিল না। আর এই ধর্মনিরপেক্ষ তার নীতি অবলম্বনের সঙ্গেই তিনি নিজেকে নিয়ােজিত রেখেছিলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার কাজে। এক্ষত্রে নেতাজী সুভাষচন্দ্র যে নতুন কোনও তত্ত্ব দিয়েছিলেন, বা এই সকল প্ররে তিনি তাত্ত্বিকভাবে নতুন কিছু সংযােজন করেছিলেন, তা নয়। কিন্তু তত্ত্বকে বাস্তবে রূপায়ণের ক্ষেত্রে তিনি আন্তরিকভাবেই প্রয়াসী হয়েছিলেন, তার কাজের মাধ্যমে প্রত্যয়কে বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। আর এখানেই নিহিত আছে বর্তমান আলােচনার প্রাসঙ্গিকতা।
সাম্প্রতিককালে ভারতে ধর্মকে কেন্দ্র করে নানা কলহ-বিরােধ-প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে, হয়তাে বা উত্তরােত্তর বাড়ছে। কিন্তু এই যে ধর্ম-কলহ, এর মূলে যে কেবল মৌলবাদী ধর্মান্ধতা তা নয়, এর পেছনে রয়েছে ধর্মকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির ষড়যন্ত্র। সেইজন্যই আশঙ্কটা আরাে গভীর। ভবিষ্যৎ ভারতের অখণ্ডতা ও জাতীয় সংহতিকে রক্ষার প্রৰ্বেভারতবাসীমাত্রই তাই চিন্তিত। এই সংকটময় অবস্থায় আমরা সঙ্গত কারণেই সুভাষচন্দ্র বসুর চিন্তা-ভাবনার কথা স্মরণ করতে পারি। কারণ তিনিই আমাদের বিপ্লবী জাতীয় নেতা যিনি তার সারা জীবনব্যাপী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, বিশেষ করে আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠন ও পরিচালনার মধ্য দিয়ে দেখিয়ে গেছেন কীভাবে দেশ ও জাতির স্বার্থে সর্ব ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন গড়ে তােলা যায়। সুভাষচন্দ্র টোকিও ইম্পিরিয়াল বিধবিদ্যালয়ে তাঁর প্রদত্ত ভাষণে (নভেম্বর ১৯৪৪) বলেছেন,
“ভারতবর্ষের বাইরে যেখানে ব্রিটিশ প্রভাব নেই সেখানে ভারতীয়দের মধ্যে কোনও বিভেদও নেই। পূর্ব-এশিয়ায় ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনে এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে জাতি, ধর্ম বা শ্রেণীর কোনও প্রা নেই। একমাত্র ভারতবর্ষেই, যেখানে ব্রিটিশের প্রভাব ও অধিকার রয়েছে। সেখানেই এইসব বিভেদ লক্ষ্য করবেন।”
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, কিন্তু সমগ্র আন্দোলনটি কখনওই ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল না। ধর্মনিরপেক্ষ এক ধারাও স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রায় প্রথম থেকেই অব্যাহত ছিল। খ্যাতনামা বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও হেমচন্দ্র কানুনগাে প্রথম থেকেই বি-বী রাজনীতির সঙ্গে হিন্দুধর্মের মিশ্রণের ঘােরতর বিরােধী ছিলেন। তারাই বি-বী রাজনীতির মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ ধারাটির সূত্রপাত করেছিলেন। ভারতের বাইরে ভারতের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লব প্রচেষ্টায় যাঁরা রত ছিলেন, তারা রাজনীতির ধারে কাছে ধর্মকে ঘেঁষতে দেননি। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধ্যে গান্ধী অসাম্প্রদায়িক হওয়া সত্ত্বেও প্রতিনিয়ত হিন্দুধর্মীয় অনুষঙ্গগুলিকে ব্যবহার করেছেন, সচেতনভাবে নেতৃত্বের প্রধান অংশটি হিন্দুত্বের সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনকে যুক্ত করেছিলেন, ফলে ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শ বহুক্ষেত্রেই বাধাগ্রস্ত হয়েছে। অন্যদিকে চরিত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে ভারতের বামপন্থীরা প্রথম থেকে রাজনীতি থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন রেখেছিল। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে ধর্মনিরপেক্ষ যে ধারাটি প্রায় প্রথম থেকেই ছিল, সেই ধারার অন্যতম সার্থক প্রতিনিধি ছিলেন আপসহীন স্বাধীনতা সংগ্রামী সুভাষচন্দ্র বসু।

রাজনীতি-জীবনের প্রথম থেকেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু চেয়েছিলেন, ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক করে রাখতে। তিনি মনে করতেন, কোনও অজুহাতেই এই দুটি বিষয়কে মিশিয়ে ফেলা উচিত হবে না। তার প্রয়াসের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় তার বিভিন্ন ভাষণে, বিবৃতিতে, প্রবন্ধে, চিঠিপত্রে ও অন্যান্য লেখায়। ১৯২৮-র ৩ মে পুনায় অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন,
“সাম্প্রদায়িক ক্ষত আরােগ্যের জন্য প্রয়ােজন হলে জোড়াতালি ব্যবস্থার নিন্দা না করেও আমাদের সাম্প্রদায়িক গােলযােগের জন্য গভীরতর কোনও প্রতিকার আবিষ্কারের প্রয়ােজনীয়তার উপর আমি গুরুত্ব আরােপ করতে চাই। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের পরস্পরের রীতি, আদর্শ এবং ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়ােজন, কারণ সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ঠতা সাম্প্রদায়িক শান্তি এবং ঐক্যের পথ প্রস্তুত করবে। আমি মনে করি যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্যের মূল ভিত্তি হলাে সাংস্কৃতিক পুনর্মিলন।…সাংস্কৃতিক সৌহার্দ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সহজ করতে ধর্মনিরপেক্ষ এবং বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণের প্রয়ােজন। সাংস্কৃতিক অন্তরঙ্গতার পথে বড় বাধা ধর্মোন্মত্ততা এবং ধর্মোন্মত্ততার প্রতিকার হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষ এবং বৈজ্ঞানিক শিার চেয়ে উৎকৃষ্টতর আর কিছু নেই। এই ধরণের শিক্ষা অন্য একটি দিক থেকেও প্রয়ােজনীয়, কারণ এই শিক্ষা আমাদের অর্থনৈতিক চেতনা জাগ্রত করে। অর্থনৈতিক চেতনার উন্মেষ ধর্মোন্মত্ততার মৃত্যু ডেকে আনে। একজন মুসলমান কৃষক এবং একজন মুসলমান জমিদারের মধ্যে যতটা মিল তার চেয়ে ঢের বেশি মিল একজন মুসলমান কৃষক এবং একজন হিন্দু কৃষকের মধ্যে। তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ কোথায় নিহিত আছে জনসাধারণকে শুধু সেই শিক্ষা দিতে হবে…।”
এই বক্তৃতায় আমরা পাচ্ছি সম্পূর্ণ আধুনিক মননের অধিকারী সুভাষচন্দ্রকে। সাংস্কৃতিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি জোর দিচ্ছেন ধর্মনিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণের উপর।
১৯২৯ সালের ৩০ মার্চ রংপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনে তাঁর সভাপতির অভিভাষণে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বাংলার সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সম্প্রীতির ঐতিহ্য সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন,
“একমাত্র সত্যই আমাদের আদর্শ এবং বাংলার কৃষ্টি, সভ্যতা, সাহিত্য এবং ধর্মে অনুপ্রবেশ ঘটা সত্ত্বেও কেন যে সর্বদাই নিজের স্বাতন্ত্র অগ্ন রেখে নবাগতদের সত্যকে আত্মীকরণ করেছে, এর থেকেই তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।…যেমন ধর্মে তেমনই সাহিত্যে বাংলা বিভিন্ন রূপে নিজেকে প্রকাশ করেছে। তার বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম এবং ভারতচন্দ্র, কাশীরাম, কৃত্তিবাস এবং রামপ্রসাদ চিন্তা এবং কৃষ্টির ক্ষেত্রে বাংলার অভিনব আবিষ্কারের উল্লেখযােগ্য উদাহরহণ হয়ে আছে। বাংলা তার সাহিত্যে মুসলমানদের অবদানের কথা বিস্মৃত হয় না এবং এই ক্ষেত্রে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অবিচ্ছেদ্য ঐক্য গড়ে উঠেছে, অতীতে তা অনেক ঝড়ঝা অতিক্রম করেছে। এক কথায় আজকের বাংলা জাতিধর্ম নির্বিশেষে বিধাজনীনতার সন্তান।..বাংলার ধর্ম, দর্শনে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধর্মের নব জাগরণ প্রতিফলন হলে এবং ভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচারে হিন্দু এবং মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হলাে।”
তাছাড়া তার কাছে ঐক্যের বিষয়টা ছিল একটা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলেছেন, জনগণকে সেভাবে শিক্ষা দিতে হবে—তাদের এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে যাতে তারা মনে করে যে, তারা একটা জাতি। জাতিগত এই আকাঙ্খই দেশে আনে ঐক্য ও সমৃদ্ধি।
খিলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতার পর হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। বাংলার অনেক নেতা এবং বুদ্ধিজীবী এই সময় মুসলমানদের সম্বন্ধে বিরূপ মনােভাব পােষণ করতেন। কিন্তু সুভাষ বসু কখনও সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপট বিসর্জন দেননি। হিন্দু ও মুসলমানকে সর্বাগ্রে ভারতীয় হিসাবেই তিনি বিবেচনা করতেন। উচ্চমধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দু নেতার পথে এটা কিন্তু সে যুগে মস্ত বড় ব্যাপার। সর্বভারতীয় রাজনীতির স্বার্থে তিনি মুসলমানদের সঙ্গে যােগাযােগ রেখে চলতেন। এই পরিস্থিতিতে মুসলমান জনগণের কাছে সুভাষ বসুর একটা বির্বাসযােগ্যতা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়।
কলকাতা কংগ্রেসে (১৯২৮) অনেক মুসলমান নেতা তার পাশে আসেন। তাদের মধ্যে পাঞ্জাবের বিখ্যাত নেতা ডাঃ আলমের নাম উল্লেখ করা যায়। মুসলমান যুবকদের উপর তার অসামান্য প্রভাব ছিল। ডাঃ আলম সুভাষচন্দ্রকে ভবিষ্যতের নেতা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া ডাঃ আনসারি, সাইফুদ্দিন কিচলু প্রভৃতি ব্যক্তিরা সুভাষচন্দ্রের দিকেই বেশি ছিলেন। যদিও এঁরা গান্ধীজিকে শ্রদ্ধা করতেন তবু সুভাষ বসুই হচ্ছেন এঁদের ভবিষ্যৎ নেতা। সুতরাং বলা যায়, সুভাষ বসু কলকাতার কংগ্রেসেই মুসলমান সমাজে তার প্রতিষ্ঠার উদ্বোধন করলেন নির্দিষ্ট পথে ও সংগ্রামের লক্ষ্য। এই সংগ্রামের লক্ষ্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। এখন এই সব শ্রমিক সংগঠনগুলিতে বিপুল সংখ্যক মুসলমানদের সংস্পর্শে সুভাষচন্দ্র এসেছিলেন। সুভাষচন্দ্রকে মুসলমান শ্রমিকরাও সে ভাবে পেলেন। ১৯২৯-র ২১ জুলাই হুগলি জেলা ছাত্র সম্মেলনে তিনি চেয়েছেন, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার। তাঁর বক্তব্য ছিল, নতুন ভারতকে গড়তে হবে সেই সাম্য আর উদারতার ভিত্তিতেই।
বিখ্যাত অমরাবতী ভাষণে (১৯২৯-র ১ডিসে.) তিনি বলেছিলেন,
“সমাজে, রাজনীতি ক্ষেত্রে, আর্থিক ব্যাপারে সর্বত্র এবং সর্ব বিষয়েই প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমান অধিকার দিতে হইবে, ইহাতে বৈষম্য রাখিলে চলিবে না।”
সাম্প্রদায়িক মানসিকতার গভীরে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির মৌলিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্ভব। তার মতে,
“একজন মুসলমান কৃষক এবং একজন মুসলমান জমিদারের মধ্যে যতটা মিল তার চেয়ে ঢের বেশি মিল একজন মুসলমান কৃষক এবং একজন হিন্দু কৃষকের মধ্যে। তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ কোথায় নিহিত আছে জনসাধারণকে শুধু সেই শিক্ষা দিতে হবে এবং একবার এই কথাটা বুঝতে পারলে তারা আর সাম্প্রদায়িক বিবাদে নিজেদের খুঁটি হিসাবে ব্যবহার করতে দিতে রাজি হবে না।”
সুভাষচন্দ্রের কাছে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও ছিল একটা বড় কথা। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সংখ্যালঘুর অধিকারের স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে তিনি সাম্প্রদায়িক সমস্যার অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন। এমনকি ঐক্যের স্বার্থে তিনি সংখ্যালঘুদের কিছু সুযােগ-সুবিধা দেওয়ারও পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি সমর্থন করেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ‘বেঙ্গল প্যাক্ট’কে—তাতে মুসলমানদের জন্য চাকরিতে কিছু সুবিধে ছিল। সুভাষচন্দ্রের মতে, এভাবে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণের মধ্য দিয়েই তাদেরকে বৃহত্তর জাতীয় স্রোতের সঙ্গে একাত্ম করে নিতে হয়।
হরিপুরা ভাষণে (১৯৩৮) তিনি সমস্ত ভারতবাসীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন যাতে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ অন্ন থাকে। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন, অভিন্ন স্বার্থ ও লক্ষ্যর দ্বারাই সাম্প্রদায়িক বিভেদকে দূর করতে হবে। মুসলমানদের তাে বটেই অন্যান্য সংখ্যালঘুদের প্রতিও সুবিচার করা হবে আমাদের লক্ষ্য। কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষার জন্য লীগ নেতা জিন্নার সঙ্গে বােঝাপড়ার চেষ্টা করেছেন। ওই বছরের ১৪ই মে তারিখে তিনি জিন্নাকে যে ‘নােট’ পাঠান, তাতে তিনি জানিয়েছিলেন যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্খর কথা মনে রেখেই ভারত-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তিনি বলেছিলেন,
‘It is obvious that the Musalmans of India, through minority in the whole country, form a very considerable part of the population and their wishes and desires must be considered in any scheme affecting India.’
আমরা জানি যে, ১৯ শতকের শেষ লগ্ন থেকেই গাে-হত্যার বিষয়টি কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। গাে-হত্যা সাম্প্রদায়িকতার প্রধান কারণ নয়, কারণ নিহিত ছিল অন্যত্র। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তথা সেই সময়কার পরিবেশে গাে-হত্যা ক্রমেই একটি বিশেষ তাৎপর্য লাভ করছিল। একদিকে গাে-হত্যাকে কেন্দ্র করে মুসলিমদের একাংশের উত্তেজক বক্তব্য অন্যদিকে হিন্দু সমাজের গাে-সংরক্ষণী সভা, গাে-হত্যা নিবারক সমিতি প্রভৃতির ততােধিক উগ্র কর্মকান্ড—এ দুয়ের টানাটানিতে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছিল। এই প্রেক্ষিতে গাে-হত্যা সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যের সারবত্তা অনুধাবন করা যায়। তিনি বলেছিলেন,
“মুসলমানরা গরুর শত্রু নয়। মুসলমানদের বাড়িতে গরুর যথেষ্ট যত্ন হয়, কোনও কোনও ক্ষেত্রে হিন্দুর বাড়ির থেকেও। বাংলার মুসলমান কৃষক হিন্দু কৃষকের মতই গরুকে ভালবাসে, কারণ সে জানে দুধ ও চাষবাস তা ছাড়া সম্ভব নয়।”
হিন্দু মহাসভার জনসমাবেশে একথা বলার সময় সুভাষচন্দ্র অবশ্যই জানতেন যে, তার বক্তব্যের অপব্যাখ্যা হতে পারে, তার জনপ্রিয়তার ক্ষতি হতে পারে। তা সত্ত্বেও কিন্তু তিনি পিছপা হননি। এটি সুভাষচন্দ্রের চরিত্রের একটি দীর্ঘমেয়াদী বৈশিষ্ট্য। তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে তিনি বিশ্বাসের সঙ্গে কোনও আপােষ করার পক্ষপাতি ছিলেন না।
আরও বলা দরকার যে, হিন্দু ও মুসলমানকে আনুষ্ঠানিক বিচ্ছিন্ন করার যে প্রচেষ্টা ইংরেজ নানা আইনের মাধ্যমে ১৯০৯, ১৯১৯, ১৯৩৫-এ করেছে নেতাজী সুভাষচন্দ্র এ বিষয়ে বেশ শংকিত ছিলেন। তাই প্রথম থেকেই এই ভেদবুদ্ধির রাজনীতি ও কর্মকান্ডের তিনি ছিলেন বিরােধী। এ প্রসঙ্গে একটি তথ্য আমরা উল্লেখ করতে পারি। ১৯৪০ সালে রামগড় কংগ্রেস অধিবেশনের সময় সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে একটি সম্মেলন হয় যেখানে হিন্দু-মুসলমানদের নিয়ে গঠিত একটি অস্থায়ী সরকার গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র বুঝেছিলেন উভয় সাম্প্রদায়কে ভারতীয় হিসেবে একতাবদ্ধ করার পথ যদি খুঁজে বের করা যায় তাহলে দেশ স্বাধীন হতে পারে না। অথবা যথার্থ স্বাধীনতা আসতে পারে না।
সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনীর প্রসঙ্গে আসতে পারি। এই বাহিনীতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ব্যাপারটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। আজাদ হিন্দ বাহিনী ছিল সম্প্রীতি সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির এবং জাতীয়তাবাদী রাজনীতি থেকে ধর্মকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখার ক্ষেত্রে তার আন্তরিক প্রয়াসের মূর্তরূপ। সমস্ত রকম সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল এই আজাদ হিন্দ বাহিনী।
১৯৪৩-র ২ জুলাই সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে পৌঁছেই যেন এক আশ্চর্য যাদুমন্ত্রে মােহিত করে ফেলেছেন বিপুল জনতা ও আজাদ হিন্দ ফৌজকে। তার প্রথম ভাষণেই একটা শিহরণ দেখা দিল। তার কথাগুলাে প্রতিধ্বনি হল কণ্ঠে কণ্ঠে। সংগ্রামের ডাক শুনে সবাইয়ের মধ্যে উচ্ছ্বাসের বন্যা বয়ে গেল, মনে রইল না ভাষা-বর্ণ-ধর্মের কথা। দেখতে দেখতে গড়ে উঠল যেন এক ক্ষুদ্র ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের প্রবাসী মানুষকে নিয়ে তিনি গড়ে তুললেন এক অভিনব সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান ও এক সেনাদল—অন্য সব পরিচয় মুছে গেল, শুধু রইল অখন্ড ভারতের সংগ্রামী স্বপ্নেরঙীন জাতীয়তাবােধ। কিন্তু শুধু যুদ্ধ-প্রস্তুতি দিয়ে নয়, নানাভাবেই সুভাষচন্দ্র এনেছেন এই একাত্মতা। সেনাবাহিনীর মধ্যে বৈষম্য দূর করার জন্য তিনি বেতনের একটা কাঠামাে তৈরি করলেন—একজন সৈনিক পেতেন ৪০টাকা, মেজর ১২০ টাকা, আর সুপ্রীম কমান্ডার ২৫০ টাকা। পদোন্নতির ক্ষেত্রে জাতি-ধর্ম প্রভৃতির কোনও গুরুত্ব না দিয়ে যােগ্যতাকেই একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছিল।
সমস্যা ছিল জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে। কিন্তু গাওয়ার সুবিধের কথা ভেবে ‘জনগণ’ গানটাকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। জাতীয় পতাকা নিয়েও গ্রহণ করা হয়েছিল নতুন পরিকল্পনা। কংগ্রেস যে জাতীয় পতাকা নিয়েছিল তার রঙ-প্রকৃতি রক্ষা করেও মাঝখানে চিত্রটাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল সেটা অহিংসার প্রতীক বলে। তার বদলে গ্রহণ করা হয়েছিল উল্লম্ফরত বাঘের ছবি।
আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের অন্যতম আবিদ হাসান তাঁর ‘স্মৃতিকথা’য় লিখেছেন,
“আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনারা পরস্পরের প্রতি সম্বােধনের সময় চিরাচরিত প্রথাই অনুসরণ করতেন। মুসলমানরা পরস্পরকে “আসসালামাে আলাইকুম, শিখরা সৎ শ্ৰী আকাল’, হিন্দুরা কখনও ‘নমস্কার’, কখনও বিশেষ করে রাজপুতরা ‘জয় রামজি কি’। এটা ছিল সাধারণ মানুষের ভাষা। আমরা ভাবলাম, তাহলে ‘জয় হিন্দুস্তান কি’ বললেই তাে হয়। এই চিন্তা থেকেই বেরিয়ে এল “জয় হিন্দ।” কথাটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এইচ তােয়ে এই সময় সামরিক গােয়েন্দা দফতরে কর্মরত অফিসার। পরবর্তীকালে তিনি তার ‘দ্য স্প্রিংগিং টাইগার’ গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, ‘জয় হিন্দ’ সম্বােধন প্রচলিত হবার পর এক সিপাহী মন্তব্য করেন, ভারতবর্ষে আমাদের নানা ধর্ম, অনেক ঈশ্বর। কিন্তু এখানে শুধু একটাই—জয় হিন্দ।”
নেতাজী সুভাষচন্দ্র যাবেন গ্রিস ভ্রমণে। জানানাে হল, তিনি একজন মাত্র সঙ্গী নিতে পারেন। কেননা সাবমেরিনে সােজা হয়ে বসার জায়গা নেই। ছােট্ট কেবিন, দাঁড়ানাে বা পায়চারি করা তাে দূরের কথা। জার্মানির বড় বড় রাজনীতিকরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সকলকে হতচকিত করে তিনি আবিদ হাসানকে সঙ্গী নির্বাচন করলেন। নেতাজীর ব্যক্তিগত দেহরক্ষী ছিলেন উত্তরপ্রদেশের আজমগড় জেলার সাহাবুদ্দিনপুর গ্রামনিবাসী নিজামুদ্দিন। তিনি সুভাষচন্দ্রের গাড়ীর চালকও ছিলেন।

১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে তখন সবে অস্থায়ী সরকার গঠন হয়েছে। সিঙ্গাপুরে তখন চেট্টিয়ার সম্প্রদায়ের একটি মন্দির ছিল। তারা ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। মন্দির কর্তৃপক্ষ নেতাজিকে আমন্ত্রণ জানান এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। নেতাজি মন্দির কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেন, তাঁর মন্ত্রীসভায় হিন্দু, মুসলমান, শিখ সব সম্প্রদায়ের লােকেরাই আছেন। সুতরাং তাদের সকলকে নিয়েই তিনি মন্দিরে প্রবেশ করবেন। গোঁড়া হিন্দু চেট্টিয়ারদের আপত্তি ছিল, কিন্তু নেতাজীর ব্যক্তিত্বের কাছে তাঁরা তাঁদের মত বদল করতে বাধ্য হলেন। নেতাজী সেদিন সর্ব ধর্মর্সমন্বয়ের এক অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করেছিলেন।
ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রর্ণ আর সামাজিক বিপ্লবের প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গি জড়িত। যখন কোনও অভ্যুত্থান ঘটেছে তখন যে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তাতে সম্প্রদায় ও শ্রেণীর ব্যবধান ভেঙে গেছে। যেমন ঘটেছে ১৮৫৭তে, পরে ১৯৭১-এ। আজাদ হিন্দ ফৌজ যখন যুদ্ধ করছিল তখন সেই বাহিনীতেও সাম্প্রদায়িকতার স্থান ছিল না। পাছে বিভাজন দেখা দেয় সেভয়ে ধর্মকে দূরে রাখা হয়েছিল। সুভাষ বসু খুবই অসন্তুষ্ট হতেন যখন ধর্মকে রাজনীতিতে আনবার চেষ্টা করা হতাে। গান্ধীজির সঙ্গে ওইখানে তার মৌলিক ব্যবধান।
আবিদ হাসান স্মরণ করেছেন যে, একবার তারা কয়েকজন মিলে সর্বধর্ম সমন্বয়ের একটি প্রার্থনা সঙ্গীত রচনা করে সুভাষবসুকে গেয়ে শুনিয়েছিলেন। আবিদ হাসান লিখেছেন,
“ভাল প্রার্থনা মানে? শােনাে, একটি কথা তােমাকে খুব স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি। আমাদের কাজকর্মের সঙ্গে কিছুতেই ধর্মকে মেশাতে দেব না আমি। তুমি ওদের ধর্মের নামে এক করতে চাও? তাই যদি হয়, তা হলে একদিন ধর্মের নামেই ওরা আবার আলাদা হয়ে যাবে।”
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আজ আর আমাদের মধ্যে উপস্থিত নেই কিন্তু আছে তার আদর্শ, তার নীতি, তার শিক্ষা সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সম্প্রীতি সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি এবং এই ঐক্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় তার আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং রাজনীতি থেকে ধর্মকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখার ক্ষেত্রে তার নিরলস প্রয়াস—যথাযথভাবে এই শিক্ষা গ্রহণ ও এই পথ অনুসরণের মাধ্যমেই এক প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ ভারত গড়ে তােলা সম্ভবপর। কিন্তু আজকে ভারত সরকার যেভাবে দেশকে পরিচালনা করছেন তার উদ্দেশ্য আমাদের কাছে খুবই স্পষ্ট। তাদের এই বিভাজনকামী কার্যকলাপ সুভাষচন্দ্রের উদারনৈতিক ও সংহতিমূলক ভাবনা ও তার প্রয়ােগ দিয়েই প্রতিহত করা জরুরী হয়ে পড়েছে।
‘নবজাগরণ’ অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপ্লিকেশনটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।
![]()

 নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা
নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা