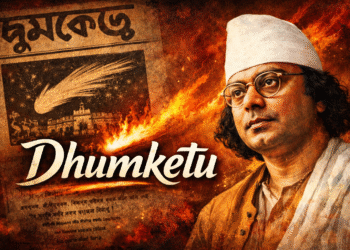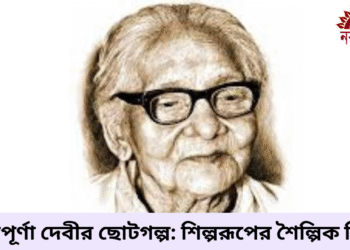লিখেছেনঃ মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম
মহৎ ঔপন্যাসিক মাত্রই মানবতার পথপ্রদর্শক। সাহিত্য মানেই মানুষের কথা, তার জীবনযাপন, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-সংঘর্ষ, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের এক জটিল বুনট। প্রকৃত সাহিত্যস্রষ্টারা যুগে যুগে মানবতার জয়গান গেয়েছেন, তুলে ধরেছেন মানুষের অন্তর্লীন আবেগ, তার স্বপ্ন ও সংগ্রামের আখ্যান। টলস্টয়, ফ্লবেয়ার, তুর্গেনিভ, লরেন্স, গোর্কি, মার্সেল প্রুস্ত, এমিল জোলা, মঁপাসাঁ, বালজাক প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য ঔপন্যাসিক তাঁদের নিজ নিজ পরিসরে থেকেও মানবতার এক অভিন্ন সত্যকে ধারণ করেছেন। জীবন ও সমাজের গভীরতম বাস্তবতাকে তাঁরা সাহিত্যের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, যেখানে মানুষই প্রধান চরিত্র—তার লড়াই, আশা-নিরাশা, ভালো-মন্দের দ্বন্দ্ব, ইতিহাসের ঘূর্ণিপাকে তার টিকে থাকার চেষ্টা।

বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে বাংলা উপন্যাসেও তার সুগভীর প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। বিশেষত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় যে গভীর পরিবর্তন আসে, তার প্রতিফলন তখনকার সাহিত্যেও লক্ষ্য করা যায়। যুদ্ধ-উত্তর ইউরোপের মতো বাংলা সমাজেও নেমে আসে এক ধরণের অস্তিত্বের সংকট। অর্থনৈতিক টানাপোড়েন, উপনিবেশিক শাসনের দুঃসহ যন্ত্রণা, মূল্যবোধের টানাপোড়েন, আস্থার সংকট—এসব কেবল ব্যক্তিজীবনেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং সমাজব্যবস্থার ভেতরেও সৃষ্টি করেছিল অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা। নীতিনৈতিকতার অবক্ষয়, শ্রেণিসংগ্রামের তীব্রতা, সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব—এসবই তৎকালীন উপন্যাসে গভীর বাস্তবতার সঙ্গে উঠে আসে।
তখনকার বাংলা কথাসাহিত্যের লেখকেরা এই পরিবর্তনের অভিঘাতকে বাস্তবের আলোয় দেখাতে সচেষ্ট হন। সাহিত্য আর নিছক কল্পনার জগৎ হয়ে থাকেনি, বরং সমাজের বাস্তব চিত্রায়ণে এক শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাস, শরৎচন্দ্রের আবেগময় সমাজচিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তববাদী কাহিনি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অর্থনৈতিক সংকটের গভীর বিশ্লেষণ—এসবই বাংলা উপন্যাসকে এক নতুন গতিপথের দিকে নিয়ে যায়।
বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়কালে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি, জীবনদর্শন ও সমাজভাবনারও তীব্র প্রভাব পড়ে বাংলার শিক্ষিত মানুষের চেতনায়। পাশ্চাত্যের অস্তিত্ববাদ, শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্ব, সাম্যবাদী আদর্শ, জাতীয়তাবাদ—এসবই তৎকালীন বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল। বাংলা উপন্যাসের চরিত্ররা আর নিছক গল্পের অবয়বে সীমাবদ্ধ থাকেনি; তারা হয়ে উঠেছিল সমাজের প্রতিনিধি, মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের প্রতিচিত্র।
এই ধারায় নজরুল ইসলামও ব্যতিক্রম নন। তাঁর সাহিত্য, বিশেষত উপন্যাসে, মানবতাবাদ এক শক্তিশালী অবস্থান নেয়। বিদ্রোহ ও মানবপ্রেমের অপূর্ব সংমিশ্রণে তিনি রচনা করেছেন এক অনন্য সাহিত্যভুবন, যেখানে অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর কলম ধারালো হয়েছে, ভালোবাসা ও সাম্যের পক্ষে তিনি বজ্রনির্ঘোষ তুলেছেন। তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পেও যুদ্ধোত্তর মানবতার সংকট, দারিদ্র্য, সামাজিক অবক্ষয়ের বিষয়বস্তু প্রবলভাবে প্রতিফলিত হয়। সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ থেকে শুরু করে নারীর স্বাধীনতা, শ্রমজীবী মানুষের অধিকার—সবকিছুর সপক্ষে তিনি লিখেছেন, সমাজকে নতুনভাবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি উপহার দিয়েছেন।
বাংলা উপন্যাস তাই নিছক বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং তা হয়ে উঠেছে মানুষের ইতিহাসের এক প্রামাণ্য দলিল। সমাজের পরিবর্তন, মূল্যবোধের বিবর্তন, সংকটের মুখে মানুষের লড়াই—এসবই বাংলার উপন্যাসের আত্মা। মহৎ সাহিত্য মানেই মানবতার চিত্রণ, আর এই মানবতার অগ্নিশিখাই যুগে যুগে সাহিত্যের অন্ধকার পথকে আলোকিত করে রেখেছে।
কার্ল মার্কসের সমাজতান্ত্রিক দর্শন, রুশ বিপ্লবের অভিঘাত এবং ফ্রয়েড-ইয়ুং-এর মনোবিশ্লেষণী তত্ত্ব বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বিশ্বজুড়ে যে নবজাগরণের ঢেউ উঠেছিল, তা শুধু রাজনীতি ও অর্থনীতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং মানুষের মানসিক গঠনের গভীরতম স্তরেও পরিবর্তন এনেছিল। বাংলার ঔপন্যাসিকরাও এই পরিবর্তনের ধারাকে আত্মস্থ করেছিলেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপান্তর কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ব্যক্তিমানুষের মনোজগৎ, তার চিন্তাভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত।
নজরুলও এই নতুন যুগের ভাবনায় সমানভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। যদিও কবি ও সংগীতস্রষ্টা হিসেবেই তিনি অধিক পরিচিত এবং স্বীকৃত, তবে তাঁর ঔপন্যাসিক পরিচয়ও বিশেষভাবে মনোযোগের দাবি রাখে। অনেকে মনে করেন, ঔপন্যাসিক হিসেবে নজরুলের সাফল্য কিছুটা প্রশ্নসাপেক্ষ, কারণ তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম, এবং গদ্যের ক্ষেত্রে তিনি সে অর্থে ধারাবাহিক ছিলেন না। তবে তাঁর চিন্তার গভীরতা, মানবিকতা ও অন্তর্দৃষ্টি—এসব বিচার করলে তাঁর উপন্যাসত্রয় ‘বাঁধন হারা’, ‘‘মৃত্যুক্ষুধা’’ ও ‘‘কুহেলিকা’’ বাংলা সাহিত্যে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।
এই তিনটি উপন্যাসের ভেতর দিয়েই নজরুল বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। ‘বাঁধন হারা’ প্রেম ও মানবিক সম্পর্কের এক জটিল বিশ্লেষণ। সেখানে শুধুমাত্র প্রেম নয়, বরং সামাজিক বাধানিষেধ, মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও নিয়তির বিপরীতে তার সংগ্রামের কথাও উঠে এসেছে। একদিকে এটি একটি প্রগতি-চেতনাসম্পন্ন উপন্যাস, যেখানে সামাজিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে একজন ব্যক্তিমানুষের স্বাধীন সত্তার আর্তি ধ্বনিত হয়েছে, অন্যদিকে এখানে প্রেম ও মানবিক সম্পর্কের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
‘‘মৃত্যুক্ষুধা’’ একদিকে বাস্তববাদী, অন্যদিকে গভীরভাবে মনস্তাত্ত্বিক ও মানবিক। এটি শুধুমাত্র দরিদ্র মানুষের দুঃখগাথা নয়, বরং সামন্ততন্ত্র, শ্রেণিবিভেদ ও অর্থনৈতিক শোষণের কঠোর সমালোচনাও। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়কালের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট, দরিদ্র কৃষকের জীবনসংগ্রাম এবং তারই পাশাপাশি এক ধরণের অস্তিত্ববাদী বেদনা—এসব কিছু মিলিয়ে এটি বাংলা উপন্যাসের এক স্মরণীয় সৃষ্টি।
‘কুহেলিকা’ তুলনামূলকভাবে এক ভিন্ন মাত্রার উপন্যাস। এখানে সমাজ, রাজনীতি ও মনস্তত্ত্বের এক জটিল মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসটি নিছক কাহিনিনির্ভর নয়; বরং এর ভেতর দিয়ে লেখকের চিন্তাভাবনা, আদর্শ ও দর্শনের এক বিশেষ প্রতিফলন ঘটেছে। ইউরোপে সেই সময়ে ফ্রয়েড ও ইয়ুং-এর মনোবিশ্লেষণ তত্ত্ব সাহিত্যকে নতুনভাবে ভাবতে শিখিয়েছিল। ব্যক্তি মানুষের অবচেতন মন, তার অজানা ইচ্ছা, স্বপ্ন ও মানসিক দ্বন্দ্ব—এসব বিষয় নজরুলও তাঁর এই উপন্যাসে অন্বেষণ করেছেন। ফলে, এটি নিছক কাহিনি নয়, বরং ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্বের এক দার্শনিক ব্যাখ্যা।
ফলে নজরুলকে কেবল বিদ্রোহের কবি কিংবা গানের স্রষ্টা হিসেবে দেখলে তাঁর সাহিত্যকর্মের ব্যাপ্তি খাটো করে দেখা হবে। তাঁর উপন্যাসত্রয় বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে এক স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে আছে, যা আজও প্রাসঙ্গিক এবং পাঠকের মননে গভীর রেখাপাত করে চলেছে।
নজরুল ইসলামের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই এক বিতর্ক সামনে আসে—তিনি কি সত্যিই উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন? কেউ কেউ মনে করেন, নজরুলের উপন্যাস বাংলা কথাসাহিত্যে তেমন গভীর প্রভাব ফেলতে পারেনি, কিংবা তাঁর সৃষ্টি কোনো চিরস্মরণীয় অধ্যায়ের সংযোজন ঘটায়নি। ড. সুশীলকুমার গুপ্ত তাঁর ‘নজরুল চরিত মানস’ গ্রন্থে লিখেছেন, “কারো কারো মতে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে নজরুল বিশেষ কোনো কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হননি।” এই মতের পক্ষে কিছু যুক্তি থাকলেও এটাও সত্য যে, তাঁর উপন্যাসে যে তীব্র মানবতাবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে, তা একেবারেই উপেক্ষণীয় নয়।
নজরুলের রচিত তিনটি উপন্যাস—বাঁধন হারা, ‘মৃত্যুক্ষুধা’ ও ‘কুহেলিকা’—বিশ শতকের তৃতীয় দশকে প্রকাশিত হয়। এই সময় বাংলা উপন্যাস ইতিমধ্যেই বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এক পরিণত রূপ পেয়েছে। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাংলা উপন্যাসের যে ধারা শুরু হয়েছিল, তা বিশ শতকের প্রথমভাগে এসে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান পায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যসাধনায় বাংলা উপন্যাস তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও শক্ত ভিত্তি গড়ে তোলে।
বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের প্রথম সুসংগঠিত কাঠামো নির্মাণ করেন। তাঁর উপন্যাসে একদিকে ঐতিহ্যগত ভাবধারা, অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে আধুনিকতার ছোঁয়া দেখা যায়। তিনি সমাজজীবনের নানা সমস্যা ও সংকটের পাশাপাশি জাতীয়তাবাদী চেতনারও বিস্তার ঘটান। বিশেষ করে, ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে তাঁর উপন্যাসে রাজনৈতিক চেতনার যে প্রকাশ ঘটে, তা পরবর্তী সাহিত্যিকদের প্রবলভাবে প্রভাবিত করে।
রবীন্দ্রনাথ বাংলা উপন্যাসকে আরও উচ্চতর স্তরে পৌঁছে দেন। তিনি কেবল জাতীয়তাবাদ বা সামাজিক সমস্যার আলোচনা করেননি, বরং ব্যক্তি মানুষের জটিল মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ, সম্পর্কের টানাপোড়েন, প্রেম-বিরহ এবং মানবতাবাদের গভীরতর উপলব্ধিকে উপন্যাসের কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে রাজনৈতিক চেতনার পাশাপাশি এক দার্শনিক ভাবনাও পরিস্ফুট হয়, যা বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে এক অনন্য সংযোজন।
অন্যদিকে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসকে একেবারে সাধারণ মানুষের জীবনের কাছাকাছি নিয়ে আসেন। তাঁর উপন্যাসে গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, দুঃখ-দুর্দশা, শ্রেণিসংগ্রাম ও সমাজের নানা অসঙ্গতির বাস্তবচিত্র ফুটে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে জাতীয়তাবাদের ভিত্তি তৈরি করেছেন, রবীন্দ্রনাথ যেখানে মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সংযোজন ঘটিয়েছেন, সেখানে শরৎচন্দ্র সাধারণ মানুষের আবেগ-অনুভূতিকে উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য করেছেন। ফলে, তাঁর সাহিত্য বাংলা উপন্যাসের একটি স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি করেছে।
এই পরিপ্রেক্ষিতেই নজরুলের উপন্যাসগুলির মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। সংখ্যার বিচারে নজরুলের উপন্যাস সামান্য, কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক থেকে তা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর উপন্যাসে একদিকে রয়েছে সমাজের প্রতি বিদ্রোহ, অন্যদিকে রয়েছে গভীর মানবিক বোধ। বাঁধন হারা, ‘মৃত্যুক্ষুধা’ ও ‘কুহেলিকা’—এই তিনটি উপন্যাসেই আমরা নজরুলের সেই সমাজচিন্তা, দ্রোহ এবং মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ দেখতে পাই।
বাঁধন হারা উপন্যাসে নজরুল সমাজের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তোলেন। এখানে তিনি স্বাধীনচেতা এক নারীর চরিত্র অঙ্কন করেন, যিনি প্রচলিত সামাজিক বিধিনিষেধকে অস্বীকার করে নিজস্ব জীবনবোধের ভিত্তিতে পথ চলতে চান। বাংলা সাহিত্যে এমন চরিত্র তখনও পর্যন্ত বিরল ছিল।
‘মৃত্যুক্ষুধা’ উপন্যাসে নজরুল চরম দারিদ্র্যের করুণ চিত্র এঁকেছেন। এখানে শুধু অর্থনৈতিক দারিদ্র্য নয়, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের দারিদ্র্যও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ক্ষুধার্ত মানুষের আর্তনাদ, দারিদ্র্যের অভিশাপে নিষ্পেষিত সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রাম এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য।
‘কুহেলিকা’ উপন্যাসে নজরুল সমাজের ভণ্ডামি, কুসংস্কার এবং ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। এখানে তিনি বাঙালি সমাজের সেই রূপটিকেই তুলে ধরেছেন, যেখানে সংস্কারের নামে মানুষের উপর শোষণ ও নিপীড়ন চলে। এই উপন্যাসে নজরুলের বিদ্রোহী সত্তার এক উজ্জ্বল প্রকাশ দেখা যায়।
অতএব, নজরুলের উপন্যাসকে শুধু সংখ্যা বা প্রভাবের বিচারে মূল্যায়ন করলে তার যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হবে না। তাঁর উপন্যাসে যে মানবতাবাদী চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে, সেটিই তাঁর কথাসাহিত্যের প্রধান শক্তি। নজরুল তাঁর উপন্যাসের মাধ্যমে শুধু কাহিনি নির্মাণ করেননি, বরং সমাজের রুগ্ন চিত্র তুলে ধরে মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্ববোধ ও ন্যায়ের আহ্বান জানিয়েছেন। ফলে, তাঁর উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে এক স্বতন্ত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।
তিরিশের দশকের অন্তিম পর্যায়ে পাশ্চাত্যের প্রকৃতিবাদ, ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব এবং মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বাংলা কথাসাহিত্যে এক নতুন ধারা সৃষ্টি করে। সমাজ, রাষ্ট্র, মনস্তত্ত্ব ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনশীল রূপ নিয়ে সাহিত্যিকদের মধ্যে এক নতুন ভাবনার জাগরণ ঘটে। এই নবযুগচেতনা পরবর্তীকালে কল্লোল যুগের ঔপন্যাসিকদের সাহিত্যকর্মে গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়। বাংলা সাহিত্যে তখন এক অস্থির, রূপান্তরমুখী যুগের সূচনা হয়েছে—যেখানে ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব, আদর্শগত সংঘাত এবং নীতির টানাপোড়েন এক জটিল বাস্তবতার জন্ম দিয়েছিল।
এই আলোড়নের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান না করেও নজরুল তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে বাংলার মাটি ও মানুষের আবেগ, যন্ত্রণা, সংগ্রাম ও মানবতাবোধকে বিশ্বসমাজের বৃহত্তর মানবিক চেতনার সঙ্গে সংযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর কবিতা ও গান যতটা জনপ্রিয়তা ও প্রভাব সৃষ্টি করতে পেরেছিল, তাঁর উপন্যাসগুলি হয়তো সেই মাত্রায় পৌঁছাতে পারেনি, কিন্তু তাতে যে মানবিক মূল্যবোধের এক অনন্য স্পর্শ রয়েছে, তা অনস্বীকার্য।
সাহিত্যতাত্ত্বিক মুহাম্মাদ মজিরুদ্দিন যথার্থই উল্লেখ করেছেন— “আঙ্গিকগত স্খলনে এবং সৃষ্টির স্বল্পতায় ঔপন্যাসিক নজরুল অত্যুজ্জ্বল না হলেও ঐতিহাসিক কালানুসারে তাঁর সৃষ্টি শ্রবণীয় এবং ব্যত্যয়ধর্মী।” (নজরুল গদ্য সমীক্ষা) অর্থাৎ, নজরুল সংখ্যার বিচারে বিশাল উপন্যাস-ভাণ্ডার রেখে যাননি, তাঁর রচনার আঙ্গিক ও কাঠামো কখনো কখনো শৈল্পিক শৃঙ্খলার সীমানা অতিক্রম করেছে, কিন্তু তাঁর সৃষ্টির অন্তর্নিহিত আবেদন, তাঁর মানবিক দর্শন এবং সামাজিক উপলব্ধি আজও প্রাসঙ্গিক।
কল্লোল যুগের লেখকদের মধ্যে অনেকেই তখন আন্তর্জাতিক সাহিত্যচিন্তার প্রভাবগ্রস্ত ছিলেন। ইউরোপের আধুনিক সাহিত্যধারা, সমাজতান্ত্রিক চেতনা, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং রাজনৈতিক মতবাদ তাঁদের রচনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু নজরুল ছিলেন খানিকটা স্বতন্ত্র ধারার পথিক। তিনি কল্লোল যুগের পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের মতো আদ্যন্ত দেশজ কাহিনি নির্মাণের পথে অগ্রসর হননি, আবার সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য সাহিত্যধারার অনুগামীও হননি। বরং, তিনি এক উত্তাল রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বাংলা ও বাঙালির চিরন্তন আবেগ, সংগ্রাম ও মানবিক আকাঙ্ক্ষাকে তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরেছিলেন।
নজরুলের স্বল্পসংখ্যক উপন্যাস— ‘বাঁধনহারা’, ‘মৃত্যুক্ষুধা’ ও ‘কুহেলিকা’—এই তিনটি রচনা তাঁর সাহিত্যপ্রবণতার স্বাতন্ত্র্য বোঝাতে যথেষ্ট। সংখ্যার দিক থেকে এগুলি হয়তো বাংলা উপন্যাসের বিশাল ভাণ্ডারে নগণ্য, কিন্তু ভাবের গভীরতা ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে এগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের সংকট, ব্যক্তির অবদমন, প্রেম ও দ্রোহ, সামাজিক শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—এসব উপাদান তাঁর উপন্যাসগুলিকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলেছে।
যে সময় নজরুল উপন্যাস লিখছেন, সে সময় বাংলা উপন্যাসের ধারার ইতিমধ্যেই এক বিশাল রূপান্তর ঘটে গিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে বাংলা উপন্যাসে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে, রবীন্দ্রনাথ সেই জাতীয়তাবাদী ভাবনার সঙ্গে আধুনিক গণতান্ত্রিক চেতনার সংমিশ্রণ ঘটান, আর শরৎচন্দ্র গ্রামবাংলার সমাজজীবনের দ্বন্দ্ব, মানবিক অনুভূতির টানাপোড়েন ও চিরায়ত প্রেমের আখ্যান নির্মাণ করেন। সেই ধারাবাহিকতায় নজরুলের উপন্যাসও তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বভাবধর্ম অনুযায়ী মানবতার বাণীকে তুলে ধরেছে।
তাই বলা যায়, উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে নজরুলের অবদান হয়তো পরিমাণগতভাবে বৃহৎ নয়, কিন্তু তিনি তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে মানবিক আবেগ, সামাজিক সচেতনতা এবং ন্যায়ের জন্য সংগ্রামের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর উপন্যাসগুলো বাংলা কথাসাহিত্যের মূলধারায় হয়তো তেমন বিশাল স্থান পায়নি, কিন্তু তাঁর সাহিত্যিক মানবতাবাদী চেতনা পাঠকের হৃদয়ে আজও গভীর অনুরণন তোলে।
‘বাঁধনহারা’ : বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রোপন্যাস
নজরুল ইসলামের প্রথম উপন্যাস ‘বাঁধনহারা’, যা বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রোপন্যাস হিসেবে পরিচিত, একটি গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টিকর্ম হিসেবে চিহ্নিত। এটি প্রথম ১৩২৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে তৎকালীন জনপ্রিয় পত্রিকা মোসলেম ভারত-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। উপন্যাসটির পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ)। নজরুল তাঁর এই সৃষ্টিকে উৎসর্গ করেছিলেন খ্যাতনামা সুরকার নলিনীকান্ত সরকারকে, যিনি তখনকার সময়ে বাংলা সঙ্গীতের এক প্রতিষ্ঠিত নাম ছিলেন।
‘বাঁধনহারা’ শুধুমাত্র নজরুলের প্রথম উপন্যাস নয়, বরং এটি বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন ধারার সূচনা করেছিল। ইংরেজি সাহিত্যের অষ্টাদশ শতকের প্রখ্যাত লেখক রিচার্ডসনের পামেলা উপন্যাসের মতো ‘বাঁধনহারা’ও একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নিজেদের অবস্থান প্রতিষ্ঠা করেছে। যদিও শিল্পগত দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু সমালোচনা হতে পারে, তবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পত্রোপন্যাসের প্রথম রচনা হিসেবে এর গুরুত্ব অপরিসীম।
নজরুল ইসলামের সাহিত্যকর্মে বরাবরই তিনি তাঁর সময়ের সমাজ ও মানুষের যন্ত্রণা, দুঃখ-দুর্দশা, এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে গভীরভাবে অনুসন্ধান করেছেন। ‘বাঁধনহারা’ উপন্যাসটিতে এই সব দিকের প্রতিফলন ঘটে। এখানে তিনি কেবল একটি কাহিনি রচনা করেননি, বরং একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন, যেখানে সামাজিক বৈষম্য, ধর্মীয় সংকীর্ণতা, এবং মানবিক মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। উপন্যাসটি, যেমনটি তার নাম থেকেই প্রতিভাসিত, একটি মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং সামাজিক বাঁধন থেকে বেরিয়ে আসার চিত্র তুলে ধরে।
নজরুলের লেখায় কখনওই কেবল কাহিনির অগ্রগতি উদ্দেশ্য নয়, বরং তিনি যে গভীর দর্শন ও মানবিক চেতনাকে তুলে ধরেন তা উপন্যাসের মূল শক্তি। ‘বাঁধনহারা’ উপন্যাসে তাঁর সেই চেতনাই লক্ষণীয়, যা সমাজের সংকট, মানুষের অধিকার, এবং ন্যায়পরায়ণতার প্রশ্নকে সমালোচনার মুখে দাঁড় করিয়েছে। এটি সেই সময়ে, যেখানে ভারতীয় সমাজ একটি পরিবর্তনের সন্ধানে ছিল, সেই পরিবর্তনকে একটি সাহিত্যিক রূপ দেওয়ার একটি চেষ্টা ছিল।
বাঙালি সাহিত্যের ইতিহাসে, বিশেষ করে উপন্যাসের ক্ষেত্রে, ‘বাঁধনহারা’ একটি অমোচনীয় স্থান অধিকার করেছে। এটি কেবল একটি সাহিত্যকর্ম নয়, বরং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের এক দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত। আর তেমনই, বাংলা সাহিত্যকে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও সাহসী পথ প্রদর্শন করেছে।
নজরুল ইসলামের ‘বাঁধনহারা’ উপন্যাসটি বাংলার সাহিত্যজগতে এক অনন্য মর্যাদা লাভ করেছে। এটি একটি পত্রোপন্যাস, যার মধ্যে মোট আঠারোটি পত্রের সমন্বয়ে পুরো কাহিনির গড়ন তৈরি হয়েছে। এই পত্রগুলি লিখিত হয়েছে একাধিক লেখক এবং লেখিকার দ্বারা, যারা হলেন— নূরুল হুদা, রবিয়ল, রাবেয়া, সোফিয়া, মাহবুবা, মনুয়র, রকিয়া, এবং আয়েশা। প্রতিটি পত্র ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে লেখা হয়েছে— করাচী সেনানিবাস, সালার, বাঁকুড়া, শাহপুর, বীডন স্ট্রীট, কলকাতা, শোভান বোগদাদ প্রভৃতি। পত্রগুলির মধ্যে ঘটনার বিন্যাস এবং উত্তর-পত্রের মাধ্যমে উপন্যাসের কাহিনি ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।
এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নূরুল হুদা, যাকে বলা যেতে পারে এক ধরনের ‘বাঁধনহারা’ পুরুষ, যিনি নিজের অন্তর্গত দৃষ্টিভঙ্গি, চেতনা এবং জীবনদর্শনের সঙ্গে বাঁচেন। তার এই ‘বাঁধনহারা’ জীবন সম্পর্কে ব্যাপক বিশ্লেষণ এবং আলোচনার মধ্যে আসেন মিস্ সাহসিকা বোস, একজন ব্রাহ্ম মেয়ে, যিনি উপন্যাসের এক গুরুত্বপূর্ণ স্ত্রীরূপ চরিত্র। তিনি নূরুল হুদার জীবনকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং এর সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। সাহসিকা বোস, তাঁর বর্ণনায় নূরুল হুদার চরিত্রের কষ্ট, দ্বন্দ্ব এবং অস্থিরতার প্রতি এক গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন।
উপন্যাসের মূল চরিত্র নূরুল হুদা, সাহসিকা বোস, রবিয়লের মা রকিয়া এবং অভিমানী মাবা—প্রত্যেকেই মানবতাবাদী ব্যক্তিরূপে চরিত্রায়িত। সাহসিকা বোস, নূরুল হুদার অন্তর্দৃষ্টি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন, এবং তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন— “সৃষ্টির আদিম দিনে এরা সেই যে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে আর তারা ঘর বাঁধলো না। ঘর দেখলেই এরা বন্ধন-ভীতু চখা হরিণের মতন চমকে ওঠে। এদের চপল চাওয়ায় সদাই তাই ধরা পড়বার বিজুলি গতি ভীতি নেচে বেড়াচ্ছে। এরা সদাই কান খাড়া করে আছে, কোথায় কোন গহনপারের বাঁশী যেন এরা শুনছে আর শুনছে। যখন সবাই শোনে মিলনের আনন্দধারা, এরা তখন শোনে বিদায়-বাঁশীর করুণ গুঞ্জরণ। এরা ঘরে বারে বারে কাঁদন নিয়ে আসছে, বারে বারে বাঁধন কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে। ঘরের ব্যাকুল বাহু এদের বুকে ধরেও রাখতে পারে না। এরা এমনি করে চিরদিনই ঘর পেয়ে ঘরকে হারাবে আর যত পরকে ঘর করে নেবে। এরা বিশ্বমাতার বড় স্নেহের দুলাল, তাঁর বিকেলের মাঠের বাউল-গায়ক-চারণ-কবি যে এরা। এদের যাকে আমরা ব্যথা বলে ভাবি, হয়তো তা ভুল। এ ক্ষ্যাপার কোনটা যে আনন্দ কোনটা যে ব্যথা তাই চেনা দায়। এরা সারা বিশ্বকে ভালবাসছে কিন্তু হায় তবু ভালবেসে আর তৃপ্ত হচ্ছে না। এদের ভালবাসার ক্ষুধা বেড়েই চলেছে। তাই এরা অতি সহজেই স্নেহের ডাকে গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ায় কিন্তু স্নেহকে আজো বিশ্বাস করতে পারলো না এরা তার কারণ ঐ বন্ধন ভয়।” (নজরুল রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশঃ ১১ জৈষ্ঠ্য ১৩৭৩, ২৫ মে, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা-৭৯২)
এ বর্ণনা থেকে স্পষ্ট যে, উপন্যাসের চরিত্রগুলি শুধু ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব বা সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তারা মানবিক চেতনা এবং এর সীমাবদ্ধতা, আশা-নিরাশা, ভালোবাসা-দ্বন্দ্বের গভীর তলদেশে প্রবাহিত। নজরুলের রচনায় যে মানবতাবোধ প্রতিফলিত হয়, তা শুধুমাত্র চরিত্রের মনের স্নেহ বা দুর্বলতার প্রতিফলন নয়, বরং মানুষের প্রকৃতির একটি চিরকালীন অনুসন্ধান।
এভাবেই ‘বাঁধনহারা’ উপন্যাসটি নজরুল ইসলামের সাহিত্যিক দক্ষতা ও চিন্তার গভীরতার এক দৃষ্টান্ত। এটি কেবল একটি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে মানবতাবাদ এবং তার অপ্রতিরোধ্য আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে না, বরং সমাজ, সম্পর্ক এবং স্বাধীনতার একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গিও উপস্থাপন করে।
নূরুল হুদা এবং রবিয়ল—এই দুটি চরিত্রের সম্পর্ক ছিল সত্যিকার অর্থেই এক বন্ধুত্বপূর্ণ এবং অগাধ বিশ্বাসে আচ্ছাদিত। একে অপরের অন্তরঙ্গ সঙ্গী, সহায়ক এবং জীবনের নানান বাধা-বিপত্তিতে পরস্পরের পাশে থাকা, এমন গভীর বন্ধন তাদের ছিল। নূরুল হুদা, পিতৃহীন এবং মাতৃহীন, রবিয়লের পরিবারে আশ্রয় পায়। সেখানে সে পায় অবিশ্বাস্য ভালোবাসা এবং স্নেহ। রবিয়লের মা রকিয়া তার প্রতি গভীর মায়া ও ভালোবাসা অনুভব করতেন, যেন সে তার নিজের সন্তান। নূরুল হুদা একদিকে রবিয়লদের পরিবারের আস্থার পাত্র হয়ে উঠল, অন্যদিকে, রবিয়লের পরিবারের মধ্যে একটি অদ্ভুত সম্পর্কের সূচনা হল—নূরুল হুদা এবং মাহবুবার মধ্যে। মাহবুবা, রবিয়লের নিকটাত্মীয়, তার সঙ্গে নূরুল হুদার সম্পর্ক ক্রমশই গভীর হতে থাকে। তাদের সম্পর্ক এক অদৃশ্য সুরে বাঁধা ছিল, যেন একে অপরের আত্মা মিলে গেছে।
যখন তাদের বিবাহের সব প্রস্তুতি চলে, তখনই এক অপ্রত্যাশিত মোড় আসে। একদিন, নূরুল হুদা এক পলকেই, কাউকে কিছু না জানিয়ে, যুদ্ধে চলে যায়। এমন এক সিদ্ধান্ত, যা সবাইকে চমকে দেয় এবং মর্মাহত করে তোলে। সে তার জীবনের স্নেহ এবং প্রেমের বাঁধনে আবদ্ধ হতে চায়নি, সত্ত্বেও তার এই আচরণে মাহবুবা এবং তার মা আয়েশার হৃদয়ে বিশাল আঘাত আসে। আঘাতের পর আঘাতে আচ্ছন্ন হয়ে আয়েশা তার কন্যা মাহবুবাকে নিয়ে ফিরে চলে যান পিত্রালয়ে। একদিকে, যেখানে এই ঘটনা রবিয়লের পরিবারের মধ্যে শোকের অন্ধকার নিয়ে আসে, সেখানে অন্যদিকে, মাবার আত্মাভিমানী মন তাকে কেবলমাত্র মুক্তির দিকে নিয়ে যায়।
এই সময়ে নূরুল হুদা করাচী সেনানিবাস থেকে বোগদাদ পর্যন্ত একাধিক চিঠি লেখে রবিয়লদের পরিবারকে। তার চিঠিগুলোর মধ্যে একটি নিরব দুঃখবোধ ছিল, যেন সে জানত তার পদক্ষেপে সবাই কষ্ট পাবে, কিন্তু তার মনে এক অদৃশ্য আকাঙ্ক্ষা ছিল—মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। একান্ত এই আকাঙ্ক্ষা তাকে সবার স্নেহ থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছিল। রবিয়ল, রাবেয়া, রকিয়া, মনুয়র—এরা সকলেই প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল, যেন নূরুল হুদার ছিন্ন জীবনকে একত্রিত করে স্নেহের বন্ধনে বাঁধা যায়, কিন্তু তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।
অবশেষে, আয়েশা তার কন্যা মাহবুবাকে বীরভূমের এক বৃদ্ধ জমিদারের সাথে বিবাহ দেয়, যা তার জন্য একটি অসম্ভব কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল। তবে, এক অদ্ভুত অনুভূতির মধ্যে, মাহবুবা সেই সম্পর্ক থেকে মুক্তি পায় এবং একদিন বিধবা হয়ে তীর্থভ্রমণের জন্য বেরিয়ে পড়ে। এর কিছুদিন পর মনুয়র এবং সোফিয়ার বিয়ে হয়। সোফিয়া গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তার জীবন সঙ্কটে চলে আসে। একই সময়ে, নূরুল হুদা জানতে পারে যে মাহবুবা, তার প্রিয় স্থানগুলোতে তীর্থভ্রমণ করার উদ্দেশ্যে বোগদাদ আসতে চায়। কিন্তু নূরুল হুদা তাকে বাধা দেয় না, কারণ সে জানে তার জীবনের মহত্ব এই সম্পর্কের বন্ধনে আটকা পড়ে যাবে। মাহবুবা, জানে যে, তার জীবন যদি বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তবে তার মুক্তি অমোচনীয় হয়ে যাবে—তাহলে সে নিজেই নূরুল হুদাকে এমন পথে পাঠিয়েছিল।
অবশেষে, উপন্যাসের শেষ চিঠিতে নূরুল হুদা লেখে, “আমার ‘বাঁধন-হারা’ জীবননাট্যের একটা অঙ্ক অভিনীত হয়ে গেল। এরপর কি আছে, তা আমার জীবনের পাগ্লা নটরাজই জানেন। আশীর্বাদ করো তোমরা সকলে, আবার যখন আসবো রঙ্গমঞ্চে — তখন যেন আমার চোখের জলে আমার সকল গ্লানি, সকল দ্বন্দ্ব-দ্বিধা কেটে যায়— আমি যেন পরিপূর্ণ শান্তি নিয়ে তোমাদের সকলের চোখে চোখে তাকাতে পারি।” (নজরুল রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশঃ ১১ জৈষ্ঠ্য ১৩৭৩, ২৫ মে, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা-৮০৬)
এভাবেই, ‘বাঁধনহারা’ উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রই এক গভীর মানবিক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়—মুক্তি এবং প্রেমের মধ্যে পার্থক্য কী? তাদের মধ্যে কি এক অনুভূতিহীনতা বা মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা মানবিক সম্পর্কের সব সীমাকে অতিক্রম করে? নূরুল হুদার জীবন ও তার অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম যেন একটি চিরন্তন সত্য—যা সকলকে বুঝতে শেখায়, কখনও কখনও জীবন নিজে থেকে নিজের পথে চলে যায়, আর সেই পথ কখনো সহজ নয়, তবে তা একটি অনন্ত পথেই পৌঁছায়।
নূরুল হুদা জীবনের গভীরে ডুবে থাকা এক বিচিত্র মানবসত্তা, যিনি দুঃখকেই জীবনের একমাত্র সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সুখের প্রতি তার বিশ্বাস ছিল নিছক একটি মিথ্যা, যে মিথ্যাকে পেছনে ফেলে তিনি চিরকাল দুঃখকে বরণ করে নিতে চেয়েছিলেন। তার জীবনের চেতনায় এই দুঃখের রংই ছিল একমাত্র রং, যা তাকে নীরব দানে অভিভূত করে রেখেছিল। তিনি বন্ধু মনুয়রকে লেখা একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, “যদি দুঃখই না পাওয়া গেল জীবনে, তবে সে জীবন বে- নিমক, বিস্বাদ। এই বেদনার আনন্দই আমাকে পাগল করলে, ঘরের বাহির করলে, বন্ধন-মুক্ত রিক্ত করে ছাড়লে, আর আজো সে ছুটছে আমার পিছু পিছু উল্কার মত উচ্ছলতা নিয়ে। দুঃখ আমায় ছাড়বে না, আমিও তাকে ছাড়বো না।” সে আরও লিখেছিল, “মৃগ তৃষ্ণিকার মত সুখ শুধু দূর-তৃষিত মানবাত্মার ভ্রান্তি জন্মায়, কিন্তু সুখ কোথাও নেই, সুখ বলে কোন চীজের অস্তিত্বও নেই। ওটা শুধু মানুষের কল্পনা, অতৃপ্তিকে তৃপ্তি দেবার জন্য কান্নারত ছেলেকে চাঁদ ধরে দেবার মত সুমলে রাখা। আত্মা একটু সজাগ হলেই এ প্রবঞ্চনা সহজেই ধরতে পাবে।”
এই চিঠি তার অন্তরের সত্যকথা জানিয়ে দেয়, যেখানে জীবনের কঠিন বাস্তবতাকে তিনি একপ্রকার স্বীকার করে নিতে চেয়েছিলেন, আর সুখকে একে একে অবাস্তব বলেই মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর কাছে সুখ ছিল কেবল এক অদৃশ্য মায়া, যা মানুষের মনকে বিভ্রান্ত করে, আর দুঃখই ছিল জীবনের প্রকৃত রস। তার জীবন যেন এক অবিরাম অস্থিরতার রূপ, যেখানে সুখের তৃষ্ণা যেন কখনোই পূর্ণ হতে পারে না, আর দুঃখের সাধনা এক চিরকালীন সংগ্রামের মতো।
নূরুল হুদা ও সাহসিকার চরিত্রের মাধ্যমে পরাধীনতার শৃঙ্খলিত মানবাত্মার নিঃসীম যন্ত্রণা, দ্বন্দ্ব ও ক্রন্দন যেন এক জীবন্ত চিত্র হয়ে উঠেছে। নূরুল হুদা, একজন প্রাণোচ্ছল যুবক, যার মধ্যে এক দুর্দান্ত আকর্ষণীয় শক্তি নিহিত। তার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, তার মধ্যে থাকা বিশাল ভালোবাসা, আর স্নেহের প্রতি গভীর আকাঙ্ক্ষা তাকে সবার কাছে বিশেষ করে তোলে। বাইরের জগতের কাছে সে একটি হাস্যোজ্জ্বল ও আনন্দময় যুবক, কিন্তু তার অন্তরাত্মা যেন একটি নিরব সাগর, যেখানে কেবল অশ্রু আর যন্ত্রণার ঢেউয়ের সঞ্চালন।
সে যে পৃথিবীর স্নেহের ছোট্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে চায়নি, তা তার কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়। তার হৃদয়ে এক অদ্বিতীয় আকাঙ্ক্ষা, একটি অনন্ত চাওয়ার অনুভূতি, যা তাকে জীবন ও সংসারের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে উৎসাহিত করে। নূরুল হুদা, সর্বদা একটি গভীর মানবিক চেতনায় আবদ্ধ, সেই চেতনা তাকে এক মহামানবের মহাআহ্বানে সাড়া দিতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই সে সমস্ত মমতার বাঁধন ছিন্ন করে অসীমের দিকে পা বাড়ায়, যেখানে সে খুঁজতে চায় একটি নতুন পৃথিবী, যেখানে এক মহাসত্য ও সুন্দরতার অজানা পথ তার অপেক্ষা করছে।
যুদ্ধ, কষ্ট ও বিভীষিকার মধ্য দিয়েও সে আশা হারায়নি। সে জানত, তার এই যন্ত্রণা ও সংগ্রাম তাকে কেবল একটি চিরন্তন সুন্দরতার দিকে নিয়ে যাবে। তার এই সংগ্রাম, তার এই অসীমের প্রতি আহ্বানই ছিল তার মানবধর্মের প্রকাশ—এক যে নিঃশর্ত ভালোবাসা, এক নিরলস সংগ্রাম, এক অচিরকালীন সত্যের সন্ধান।
সাহসিকা, ব্রাহ্ম পরিবারের একজন মেধাবী, সুশিক্ষিত এবং কুসংস্কারমুক্ত নারী চরিত্র। তার ব্যক্তিত্বে এক তীব্র জোর এবং সাহসিকতা ফুটে উঠেছে। তিনি শুধু শিক্ষিত নন, বরং তার দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার মধ্যে আধুনিকতার প্রতিফলন ঘটেছে। আবু হোসেন এই চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, “বলাবাহুল্য এ উপন্যাসের উজ্জ্বলতম নারী চরিত্র সাহসিকা। তিনি গত যুগের বিশিষ্ট নারী সমাজের মুক্তিদাত্রীদেরই প্রতিভূ। তার কথাবার্তা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিন্তাধারার ভিতর দিয়ে বিংশ শতাব্দীর, নারীমুক্তি আন্দোলনের সোচ্চার কণ্ঠ – একটি যথার্থ সাহসী নারীর চরিত্র ঝলমল করে উঠেছে। নজরুলের ‘নারী’ কবিতায় আমরা যে বীর্যবতী এবং স্নেহময়ী নারীর চেহারা দেখতে পাই তারই স্পষ্ট প্রতিকৃতি এই সাহসিকা। এবং বললে অন্যায় হবে না যে, নজরুলের দক্ষতা এ নারী চরিত্র সৃষ্টিতে সামান্য নয়।” (নজরুল একাডেমি পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, শরৎ, ১৩৭৬, পৃষ্ঠা ৩৪)
এটি স্পষ্ট যে, সাহসিকা চরিত্রটি নারীমুক্তির আন্দোলনের এক অগ্রদূত হিসেবে চিত্রিত। তিনি ঐ সময়ের একজন আদর্শ নারী, যিনি তার বক্তব্য, দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিন্তাধারার মাধ্যমে সমাজে নারীর অবস্থানকে আরও শক্তিশালী এবং প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তার চিন্তা এবং কর্মের মধ্যে ছিল এক মহৎ মানবিকতা, যা তাকে তার সময়ের অন্য সকল নারীর থেকে আলাদা করে তুলে।
‘‘মৃত্যুক্ষুধা’’ উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে (১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ)। এই সময় নজরুল কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তাঁর কবিতা, গদ্য, নাটক, এবং অন্যান্য সাহিত্যকর্ম তাকে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কবিতার পাশাপাশি সে সময় তিনি সমাজের বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ছিলেন। তাঁর সাহিত্যিক ভূমিকা কেবল সৃজনশীলতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তিনি সমাজের পরিবর্তন, অধিকার ও স্বাধীনতার জন্য নিজেকে নিঃস্বার্থভাবে উৎসর্গ করেছিলেন। ‘‘মৃত্যুক্ষুধা’’ তার এই সংগ্রামী চেতনারই একটি সাক্ষ্য বহন করে।
এ উপন্যাসটি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক উত্তাল সময়কালকে চিত্রিত করে। বিশেষত, এটি খিলাফত আন্দোলন এবং অসহযোগ আন্দোলনের সময়কে কেন্দ্র করে রচিত। নজরুলের সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক অবস্থান এই সময়ে যেমন ছিল তেমনই, তিনি তাঁর রচনায় সমাজের হতাশা, দুঃখ, সংগ্রাম, বেদনা, এবং নিরাশার বিষয়গুলো গভীরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ‘‘মৃত্যুক্ষুধা’’ উপন্যাসটি শুধু একটি সাহিত্যকর্ম হিসেবে নয়, বরং এটি তার সময়ে ও তার পরবর্তীকালীন সমাজের এক রূপরেখা—যে সমাজ পরাধীনতা, অত্যাচার, বৈষম্য ও নিপীড়ন থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম চালাচ্ছে।
ড. সুশীলকুমার গুপ্ত, যিনি নজরুলের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছেন, তিনি ‘‘মৃত্যুক্ষুধা’’ নিয়ে বলেছেন, “নজরুল সৎ ঔপন্যাসিকের গৌরব সঙ্গতভাবে কতকটা দাবি করতে পারেন। এই একটি গ্রন্থই সত্যকার উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। এই উপন্যাসেই নজরুল জনসাধারণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, বেদনা ও নৈরাশ্যকে সার্থক শিল্পীর মত স্পর্শ করতে পেরেছিলেন।” (নজরুল চরিত মানস, ড. সুশীলকুমার গুপ্ত)
এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, ‘‘মৃত্যুক্ষুধা’’ উপন্যাসটির মধ্যে নজরুল তার সাহিত্যিক মেধা এবং তাঁর সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। এই উপন্যাসে তিনি শুধু ঐতিহাসিক সময়কালকে চিত্রিত করেননি, বরং মানবিক সংগ্রাম, মানুষের মানসিক কষ্ট এবং আক্ষেপকেও অবলম্বন করেছেন। এটি একটি উপন্যাস হলেও এটি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সংগ্রাম নয়, জাতির বৃহত্তর সংগ্রামের এক অমলীন ছবি।
‘‘মৃত্যুক্ষুধা’’ লেখার সময় নজরুল যে গভীরভাবে সামাজিক এবং রাজনৈতিক বাস্তবতা অনুভব করেছিলেন, তা তাঁর লেখনীর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন যে মানবতা, অধিকার এবং মুক্তির সংগ্রাম কেবল একজন মানুষের ব্যক্তিগত অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ নয়, বরং একটি জাতির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সংগ্রামের সঙ্গী। নজরুলের এই উপন্যাসের মাধ্যমে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ মানুষের আত্মবিশ্বাসের জাগরণ ও মানবিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।
‘‘মৃত্যুক্ষুধা’’ উপন্যাসের মধ্যে মানবতাবাদ এক গভীর ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে প্রধান চরিত্র আনসারের মাধ্যমে। আনসার একজন দেশপ্রেমিক, সমাজকর্মী এবং বিপ্লবী। তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো শুধু সাধারণ দেশপ্রেমিক বা বিপ্লবীর চেনা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা সম্ভব নয়, বরং তা এক স্বতন্ত্র মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে। এ তিনটি দিক—দেশপ্রেম, সমাজসেবা ও বিপ্লবী চেতনা—তার ব্যক্তিত্বকে পূর্ণতা দেয়, কিন্তু এই সবকিছুর মূলে রয়েছে তার অব্যাহত মানবতাবোধ। তার আত্মার গভীরে ক্ষুধিত, বঞ্চিত এবং শোষিত মানুষের দুঃখ-বেদনা, তাঁদের অবর্ণনীয় যন্ত্রণার চিত্র অবিরত ভেসে ওঠে। ফলে, এই তীব্র মানবিক অনুভূতি তাকে সারা পৃথিবীকে এক পরিবারের মতো দেখতে শেখায়।
আনসারের মধ্যে মানবতার প্রতি এক গভীর সহানুভূতি ছিল যা তাকে নিজের সবকিছু ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। ঘরবাড়ি, বিত্তবৈভব সবই সে ত্যাগ করেছে। সেই সময়ে, যখন অধিকাংশ মানুষ শুধু নিজেদের জীবনকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখার জন্য সংগ্রাম করছিল, আনসার দেশ এবং মানবতার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিল। তিনি জানতেন, পরাধীনতার শৃঙ্খলিত মানুষের মুক্তি এককভাবে সম্ভব নয়, তার জন্য প্রয়োজন এক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, যেখানে দেশপ্রেমিক প্রতিটি নাগরিক এক হয়ে উঠবে। কিন্তু সে জানত, অহিংস আন্দোলন বা ঐতিহ্যগত পথ ধরে স্বাধীনতা আনা সম্ভব নয়। তার বিশ্বাস ছিল—সশস্ত্র সংগ্রামই হবে একমাত্র উপায়।
আনসারের রাজনৈতিক মতাদর্শও সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছিল। কংগ্রেসের পন্থী হওয়া সত্ত্বেও, তার রাজনৈতিক দর্শন পরিবর্তিত হয়, বিশেষত যখন সে জেল থেকে ফিরে আসে। তার উপলব্ধি হয় যে, ভারতের স্বাধীনতা কেবলমাত্র অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জন করা যাবে না। এই পর্যায়ে তার চিন্তা-ভাবনা থেকে, তিনি অনুভব করেন যে সশস্ত্র সংগ্রাম ও শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম না হলে দেশকে স্বাধীন করা সম্ভব নয়। ফলস্বরূপ, কৃষ্ণনগরে তার আগমন কেবল শ্রমিকদের সংগঠিত করার জন্য ছিল না, বরং দেশের প্রতি তার দায়বদ্ধতা এবং তার আদর্শিক বিশ্বাসের জন্যও ছিল।
সে বিশ্বাস করেছিল যে শুধুমাত্র শ্রমিক শ্রেণী, যাদের অধিকার সবচেয়ে বেশি লঙ্ঘিত হচ্ছে, তাদের সংগঠিত না করা হলে দেশকে স্বাধীন করা সম্ভব হবে না। সেই সময়ের অসংখ্য মজুর, কুলি, গাড়িওয়ালা, মেথর প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার পক্ষে তিনি দৃঢ়ভাবে লড়াই করেছেন। তার এই উদ্যোগ শুধু রাজনৈতিক চিন্তা বা বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গির অংশ ছিল না, বরং এর মাধ্যমে সে সমাজের নিগৃহীত শ্রেণীর মানুষের জন্য এক নতুন দিশা ও মুক্তির পথ খুলে দিতে চেয়েছিল।
এছাড়া, আনসারের চরিত্রের মাধ্যমে উপন্যাসটি মানবতার প্রতি এক নিষ্ঠাবান ও অটুট বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তার জীবন সংগ্রাম শুধু নিজের স্বার্থের জন্য ছিল না, বরং সমগ্র সমাজের উন্নতি ও মুক্তির জন্য ছিল। তিনি যে শ্রমিক শ্রেণীকে সংগঠিত করার জন্য কাজ করেছেন, তাদের মধ্যে সমতা, অধিকার এবং মর্যাদার যে বোধ তৈরির চেষ্টা করেছিলেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ছিল। আনসারের চরিত্র, তার জীবনদর্শন এবং তার বিপ্লবী কার্যকলাপের মাধ্যমে, ‘‘মৃত্যুক্ষুধা’’ উপন্যাসটি এক বৃহত্তর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্মোচন ঘটায়।
এই উপন্যাসের মাধ্যমে নজরুল একটি মহান সমাজের গঠনকল্পে দেশপ্রেম, বিদ্রোহ এবং শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার আন্দোলনের যে চিত্র তুলে ধরেছেন, তা শুধু কল্পনার ঊর্ধ্বে, বাস্তবতার দিকে মনোনিবেশ করেছে। উপন্যাসটি তার পাঠকদের কাছে শুধু একটি সাহিত্যকর্ম নয়, বরং একটি আন্দোলনের ডাক, যা মুক্তির প্রত্যাশায় সমস্ত দুঃখী মানুষের জন্য একটি নতুন জীবনসঞ্চার।
আনসার, যিনি নিজের জীবনের সমস্ত সত্ত্বা দেশমাতৃকার সেবায় নিবেদিত রেখেছেন, একদিন নিজে অনুভব করেন যে তাঁর হৃদয়ে এক গভীর দুঃখ বাসা বেঁধেছে। দেশপ্রেমের মধ্যে যে তৃপ্তি ও শান্তি পাওয়ার কথা ছিল, তা তাকে কিছুটা অবহেলিত মনে হয়। এক ক্ষণিকের জন্য, তার কাছে মনে হয়, “মানুষের শুধু পরাধীনতার দুঃখই নাই, অন্য দুঃখও আছে—যা অতি গভীর, অতলস্পর্শী। নিখিল মানবের দুঃখই কেবল মনকে পীড়িত, বিদ্রোহী করে তোলে। কিন্তু নিজের বেদনা সে যেন মানুষকে ধেয়ানী সুস্থ করে তোলে। বড় মধুর, বড় প্রিয়, সে দুঃখ।” (নজরুল রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশঃ ১১ জৈষ্ঠ্য ১৩৭৩, ২৫ মে, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা-৭৯২)
এখানে, আনসার তার জীবনের সংগ্রামের মধ্যেই উপলব্ধি করেন যে, শুধুমাত্র পরাধীনতার যন্ত্রণাই মানুষের দুঃখের একমাত্র উৎস নয়, বরং আরও একটি দুঃখ থাকে, যা অনেক গভীর, অনেক তীব্র, অনেক বিস্তৃত। দেশপ্রেম, সমাজসেবা, এমনকি বিপ্লবী কাজের মাঝেও একটি নির্দিষ্ট তৃষ্ণা, একটি অদৃশ্য অভাব থেকে যায়। সেটি হয়তো অন্যদের দুঃখের প্রতিক্রিয়া নয়, বরং নিজের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রণা থেকে উঠে আসে। কিন্তু সে অনুভব করে যে, এই বেদনা, এই কষ্ট—অসীম মহত্বের দিকে নিয়ে যেতে পারে, কারণ নিজের এই দুঃখ তাকে মানসিকভাবে পোক্ত করে এবং সে অনেক কিছুই পার করতে সক্ষম হয়। দুঃখের এই মধুরতা, এই প্রিয়তাও তাকে তার পথের প্রতি দৃঢ় থাকতে সহায়তা করে।
এমনকি আনসার নিজের বেদনার মধ্যেও এক অদ্ভুত রকমের শান্তি এবং তৃপ্তি খুঁজে পায়। সে উপলব্ধি করে, কখনও কখনও নিজের যন্ত্রণায় অন্যদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসা, এবং তাদের দুঃখ অনুভব করাই আসল মানবধর্ম। এর ফলে সে জানে যে, তার নিজস্ব দুঃখ যখন অন্যদের জন্য ব্যবহৃত হয়, তখনই তার জীবন সত্যিকারের অর্থ খুঁজে পায়।
‘‘মৃত্যুক্ষুধা’’ উপন্যাসটি রচনার সময় নজরুল কৃষ্ণনগরের চাঁদসড়কে অবস্থান করছিলেন, যেখানে বাস করতেন শ্রমজীবী মুসলিম ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের গরিব মানুষরা। এই অঞ্চলের সামাজিক বাস্তবতা এবং দরিদ্র শ্রমিকদের জীবনযাত্রা উপন্যাসটির ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। ‘‘মৃত্যুক্ষুধা’’-র মধ্যে যে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংকটের চিত্র উঠে এসেছে, তা মূলত সেই স্থানীয় পরিবেশ থেকেই অনুপ্রাণিত। নজরুলের হাতে এই উপন্যাসে যে গল্পের পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে, তা মূলত দরিদ্র মানুষের নৈরাশ্য, তাদের দুঃখ, কষ্ট, ক্ষুধা এবং অভাবী জীবনযাপনের এক অসাধারণ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে। সেই সময়ে যাঁরা কঠিন সংগ্রামে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে প্রতিনিয়ত লড়াই চালাচ্ছিলেন, তাঁদের জীবনযাত্রার গল্পেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে উপন্যাসটির গুণগত মান।
উপন্যাসের রচনা-কালে বাংলা সাহিত্যে তিরিশের ‘কল্লোল’ আন্দোলন ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছিল। তিরিশের নবীন লেখকরা সৃষ্টির আনন্দে উদ্বেলিত ছিলেন এবং আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্পর্কে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করছিলেন। কিন্তু দেশীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে নজরুল ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি শ্রমজীবী মানুষের জীবনকে এবং তাঁদের সংগ্রামী বাস্তবতাকে সাহিত্যের মূল উপজীব্য হিসেবে তুলে ধরেন। তাঁর ‘‘মৃত্যুক্ষুধা’’ উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের এক নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। যেখানে সাধারণ মানুষের দুঃখ, দারিদ্র্য, শ্রমের কষ্ট, ক্ষুধা এবং তাঁদের সাম্প্রতিক সংগ্রামকে শিল্পের একটি সার্থক রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে।
এ উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্য হলো, এতে বাঙালি সমাজের শ্রমজীবী মানুষদের জীবনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সাধারণ মানুষ, বিশেষত খেটে খাওয়া শ্রমিকরা, যাঁরা সমাজের অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণে বসবাস করছিলেন, তাদের জীবনের করুণ ছবি এখানে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাদের সংগ্রাম, যন্ত্রণা এবং জীবনের ন্যূনতম মৌলিক অধিকার অর্জনের জন্য যে সারা জীবনের লড়াই, তা উপন্যাসটির একটি মূল উপজীব্য। আর একে সার্থক শিল্পে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে নজরুল বাংলা সাহিত্যে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছিলেন।
‘‘মৃত্যুক্ষুধা’’ উপন্যাসের মাধ্যমে নজরুল বাংলা সাহিত্যে প্রথমবারের মতো এমন এক সাহিত্যধারার সূচনা করেছিলেন, যেখানে সাধারণ মানুষের সংগ্রাম এবং তাঁদের অন্তর্নিহিত দুঃখকে সাহিত্যের একটি প্রধান বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ধরনের সাহিত্যধারা পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকের গণমুখী উপন্যাসগুলির সমস্ত ধারণা এবং বৈশিষ্ট্যগুলো একেবারে ‘‘মৃত্যুক্ষুধা’’ থেকে উদ্ভূত, যা তাঁদের লেখার পেছনে অন্যতম প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।
‘‘মৃত্যুক্ষুধা’’-র মধ্যে যে শ্রমিকশ্রেণির জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে, তা পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের আরো অনেক লেখককে প্রভাবিত করেছে। এসব লেখক তাঁদের সাহিত্যকর্মে শ্রমিক শ্রেণির জীবনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন, যেটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি নতুন এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক।
এছাড়া, নজরুলের রাজনৈতিক ভাবনা এবং বিপ্লবী চেতনা তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যে প্রবাহিত ছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে কেবলমাত্র অসহযোগ আন্দোলন কিংবা রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা আসবে না, দেশকে স্বাধীন করতে হলে সমাজের প্রান্তিক জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাঁদের দুঃখ-দুর্দশার মুক্তি, সমাজে শোষণমূলক ব্যবস্থা থেকে তাঁদের মুক্তি, এই ধরনের ভাবনা ‘‘মৃত্যুক্ষুধা’’ উপন্যাসে প্রধানত ফুটে উঠেছে।
সংক্ষেপে, ‘‘মৃত্যুক্ষুধা’’ উপন্যাসটি নজরুলের সাহিত্যজীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক এবং এটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি সার্থক সৃষ্টিরূপে গণ্য।
নজরুল তাঁর সাহিত্যকর্মে মানবতাবাদ এবং সাম্যবাদের যে ভাবনা তুলে ধরেছেন, তা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র, আনসারের মাধ্যমে। আনসারের চরিত্র শুধু একজন দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবীর পরিচয় বহন করে না, বরং তা একটি উচ্চতর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণনগরের চাঁদ সড়কে আনসারের আবির্ভাব এক বিপরীতধর্মী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। সেখানে সে স্থানীয়দের কাছ থেকে এক অদ্ভুত ধরনের আগ্রহ এবং অনুসরণের পাত্র হয়ে ওঠে।
আনসারের বাহ্যিক চেহারার বর্ণনা নজরুলে দিয়েছেন একটি বিশেষ ভাষায়, যা তার চরিত্রের জটিলতাকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে। ঔপন্যাসিক নজরুল আনসারের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, “যুবকের গায়ে খেলাফতি ভলান্টিয়ারের পোশাক। কিন্তু এত ময়লা যে চিমটি কাটলে ময়লা ওঠে। খদ্দরেরই জামাকাপড় কিন্তু এত মোটা যে, বস্তা বলে ভ্রম হয়। মাথায় সৈনিকদের ‘ফেটিগ ক্যাপে’র মত টুপি, তাতে কিন্তু অর্ধচন্দ্রের বদলে পিতলের ক্ষুদ্র তরবারি-ক্রস! তরবারি-ক্রসের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনাত্মক একটা লোহার ত্রিশূল। হাতে তরবারী ধরনের অষ্টাবক্রী দীর্ঘ ষষ্ঠি। সৈনিকদের ইউনিফর্মের মত কোট-প্যান্ট। পায়ে নৌকোর মত এক জোড়া বিরাট বুট, চড়ে অনায়াসে নদী পার হওয়া যায়। পিঠে একটা বোম্বাই কিটব্যাগ। শরীরের রং যেমন ফরসা, তেমনি নাক- চোখের গড়ন। পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন মাপ করে তৈরী- গ্রীক-ভাস্কর্যের এ্যাপোলো মূর্তির মত – নিখুঁত সুন্দর। কিন্তু এমন চেহারাকে লোকটা অবহেলা করে পরিত্যক্ত প্রাসাদের মর্মর-মূর্তির মত কেমন ম্লান করে ফেলেছে। সর্বাঙ্গে ইচ্ছাকৃত অবহেলার ছাপ।” (নজরুল রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশঃ ১১ জৈষ্ঠ্য ১৩৭৩, ২৫ মে, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৫৮৮)
এখানে আনসারের বাহ্যিক চেহারা, পোশাক এবং তার সামরিক ভাবমূর্তি নির্দিষ্ট এক দার্শনিক অবস্থান এবং আত্মবিশ্বাসের প্রতীক হিসেবে প্রতীয়মান হয়। তার গায়ে পরা ময়লা পোশাক এবং এক ধরনের অবহেলার ছাপ, যেন তার নিজস্ব অবস্থান এবং সমাজের প্রতি তার ত্যাগকে স্পষ্ট করে। তা সত্ত্বেও, আনসারের বাহ্যিক সৌন্দর্য এবং শারীরিক গঠন এক অনন্য আকর্ষণের সৃষ্টি করে, যা তার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এক অভিনব সম্পর্ক তৈরি করে।
নজরুলের ভাষায়, আনসার একটি চমৎকার, একেবারে নিখুঁত মূর্তির মতো, যাকে দেখে অনায়াসে কেউ তার বাহ্যিক সৌন্দর্যে মোহিত হতে পারে। তবে সে নিজেই এই সৌন্দর্যকে পরিত্যাগ করেছে, যেন তা তার লক্ষ্য এবং আদর্শের মধ্যে কোনও বাধা সৃষ্টি না করতে পারে। সে তার সৌন্দর্যকে অবহেলা করেছে, যেন তার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে মানবিক সংগ্রাম এবং সমাজের অধিকার বঞ্চিত মানুষের জন্য এক নিরন্তর ত্যাগ।
এভাবেই, আনসারের চরিত্র একটি প্রতীক হয়ে উঠেছে মানবতার, সাম্যের এবং নিখুঁত আত্মত্যাগের। এর মাধ্যমে নজরুল তাঁর সাহিত্যকর্মে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক বার্তা প্রদান করেছেন, তা আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।
আনসার তার স্বেচ্ছাবৈরাগ্যের প্রকৃত কারণ লতিফাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিল, “দুনিয়ার সব মানুষই একই ছাঁচে ঢালা নয় রে, বুঁচি। এখানে কেউ ছোটে সুখের সন্ধানে, কেউ ছোটে দুঃখের সন্ধানে। আমি দুঃখের সন্ধানী। মনে হয় যেন আমার আত্মীয়-পরিজন কেউ নেই! আমার আত্মীয় যারা, তাদের সুখের নীড়ে আমার মন বসল না! অনাত্মীয়ের অপরিচয়ের দলের নীড়হারাদের সাথী আমি! ওদের বেদনায়, ওদের চোখের জলে আমি যেন আমাকে পরিপূর্ণ রূপে দেখতে পাই। তাই ঘুরে বেড়াই এই ঘর-ছাড়াদের মাঝে।” (নজরুল রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশঃ ১১ জৈষ্ঠ্য ১৩৭৩, ২৫ মে, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৫৯২)
এখানে আনসার তার অন্তর্গত যন্ত্রণার গভীরতা এবং তার আত্মত্যাগের নেপথ্য কারণের কথা তুলে ধরছে। সে জানায়, তার জীবনে সুখের অনুসন্ধান কখনোই ছিল না। তার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যত সুখ এবং শান্তি ছিল, তা তার মনকে কখনও প্রশান্তি দিতে পারেনি। সেই শান্তি ও সুখের ঘর তার জন্য ছিল এক অচেনা, অদৃশ্য স্থান। সেজন্যই সে অনাত্মীয়, নিঃস্ব, ঘর-ছাড়া মানুষদের মাঝে নিজের সাথী খুঁজে পায়। তাদের বেদনা, তাদের চোখের জলেই তার নিজেকে পূর্ণাঙ্গভাবে উপলব্ধি করতে পারে, যেন সেই যন্ত্রণাই তার একমাত্র প্রাপ্য। তাই সে পরিত্যক্ত, অনাথ মানুষের মাঝে নিজের পথ খুঁজে পায়।
এই কথাগুলির মধ্যে আনসারের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমাজের প্রতি তার গভীর সহানুভূতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার জীবনের লক্ষ্য একরকমের আত্মিক তৃপ্তি নয়, বরং মানবতার জন্য নিঃস্বার্থ ত্যাগ এবং সমষ্টিগত যন্ত্রণার সঙ্গে একাত্ম হওয়া।
নজরুল তার প্রতিভার মাধ্যমে আনসার চরিত্রে নিপীড়িত বিশ্বমানবতার গভীর বেদনার আর্তনাদকে অসাধারণভাবে প্রকাশ করেছেন। তার সৃষ্ট এই চরিত্রটি এক ধরনের মানবিক সংগ্রামের প্রতীক হয়ে উঠেছে, যেখানে একে অপরের দুঃখে সহমর্মিতা এবং জীবনযুদ্ধে অনমনীয় এক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। আনসারের জীবনচরিত্র যেন নিখিল মানবাত্মার করুণ সুর, যার মধ্যে ঘরছাড়া, শোষিত, নিরন্ন মানুষের জীবনের এক নিখুঁত প্রতিবিম্ব দেখা যায়। ‘‘মৃত্যুক্ষুধা’’ উপন্যাসের প্রথমদিকে কৃষ্ণনগরের চাঁদসড়কের চাঁদ-বাজার এলাকায় বসবাসরত নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবী মুসলমান এবং রোমান ক্যাথলিক ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টানদের অবস্থা চিত্রিত হয়েছে, যেখানে দুঃখ, দুর্দশা এবং জীবনযুদ্ধে অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে তাঁরা দিনযাপন করছে। গজালের মা, হিড়িম্বা, পুঁটের মা, খাতুনের মা—এদের মধ্যে তীব্র কলহ এবং পরবর্তীতে মিলনের কাহিনীগুলি উপন্যাসের অন্যতম চিত্তাকর্ষক দিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলতলায় যারা একে অপরের রক্তপিপাসু হওয়ার চেষ্টা করে, তাদের মধ্যে একজন যখন প্রসববেদনায় কাতর হয়, তখন অপরজন তার বিরোধ ভুলে ছুটে গিয়ে সাহায্য করে—এটি নজরুলের অবহেলিত সমাজের জীবন্ত চিত্রায়নের একটি অমূল্য অংশ।
গজালের মায়ের ছোট ছেলে প্যাঁকালের সঙ্গে মধু ঘরামীর মেয়ে কুর্শির প্রণয় এবং পরবর্তীতে সমাজের অত্যাচারে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণের পর তাদের বিবাহ ও মিলনের কাহিনীটি উপন্যাসে স্বতন্ত্রভাবে চিত্রিত হলেও, তা মূল কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ার কারণে উপন্যাসের রসসৃষ্টিতে কিছুটা বিঘ্ন ঘটিয়েছে। যদিও এটি এক আলাদা স্তরের কাহিনী, তবুও তার উপস্থিতি উপন্যাসের সুর ও ধারায় এক প্রকারের অমিল সৃষ্টি করে, যার ফলে কাহিনীর প্রকৃত আবেদন কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়।
মেজবৌ ‘‘মৃত্যুক্ষুধা’’ উপন্যাসের এক অতি জীবন্ত এবং সজীব চরিত্র। তার হৃদয় যেন এক অমূল্য রত্ন, যা দুঃখের কঠিন পাথরে পরীক্ষা করা সোনার মতো। দুর্ভাগ্যক্রমে, এই প্রাণপ্রিয় মেয়েটি এক অসহনীয় দারিদ্র্য ও বিধ্বস্ত পরিবারের বিধবা বউ, যার ঘরে তিনটি কর্মক্ষম পুত্রের মৃত্যু ঘটেছে। এই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিল প্যাঁকালে, যে তার মায়ের ছোট ছেলে। বিধবামুক্ত ও দারিদ্র্যের দুই কঠোর যন্ত্রণা সত্ত্বেও মেজবৌ ধৈর্য ধারণ করে নিজের ও পরিবারের সন্তানদের স্নেহে পোষণ করতে চেয়েছে। সে সমাজের নিষ্ঠুরতা ও অবজ্ঞাকে সহজেই উপেক্ষা করতে পারে। কামার্ত বৃদ্ধ বোনাই-র হাত থেকেও সে নিজের বিচক্ষণতার মাধ্যমে রক্ষা পায়। নিজের ভেতরের অসহ্য যন্ত্রণা সে হাসির আড়ালে চাপা রাখে।
মেজবৌর সৌন্দর্য ছিল এক অদৃশ্য মাধুরী, যা সকলকেই আকৃষ্ট করত, কিন্তু সে কাউকেই তার কাছে আসতে দেয়নি। সমাজের অবিচার ও দুর্ব্যবহারে সে এতটাই ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিল যে, দারিদ্র্যের অবর্ণনীয় যন্ত্রণা তার আত্মাকে নিরন্তর কষ্ট দিত। পরিশেষে, মেজবৌ স্বধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। খ্রীষ্টান মিশনের মাধ্যমে তাকে মর্যাদা ও সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, যেখানে সে লেখাপড়া শিখতে পেরেছিল এবং সেলাইয়ের কাজেও দক্ষতা অর্জন করেছিল। মিসবাবা ও পাদরীদের অশেষ স্নেহ এবং নিয়মিত খাবারের সুযোগ তাকে দেওয়া হয়েছিল। তবে মেজবৌর কাছে খ্রীষ্টধর্মের মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতার চেয়ে ক্ষুধা নিবারণ।
মেজবৌ তার নিজের সম্পর্কে আনসারকে বলেছিল, “আমি ত হঠাৎ খ্রীষ্টান হইনি। আপনারা একটু একটু করে আমাকে খ্রীষ্টান বানিয়েছেন।”
এখানে তার খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পেছনে এক গভীর মানবিক চেতনা এবং দুঃখের তীব্র প্রক্ষেপণ আছে। সে খ্রীষ্টধর্মকে গ্রহণ করেছিল তার মুক্তির প্রার্থনায়, যাতে সমাজের অমানবিকতা থেকে মুক্তি পেতে পারে, যার মধ্যে সে ক্রমশঃ বিশ্বাস হারাতে বসেছিল।
মিশনের নির্দেশে মেজবৌকে কৃষ্ণনগর থেকে বরিশাল মিশনে স্থানান্তরিত করা হয়। এই স্থানান্তরের ফলে তাকে তার সন্তানদের ছেড়ে যেতে হয়, আর সেই অপত্যস্নেহের যন্ত্রণা তাকে তীব্রভাবে আঘাত করে। মেজবৌ বরিশাল মিশনে একপ্রকার নির্লিপ্ত হয়ে পড়েন। সন্তানহীন জীবন তাকে যেন এক অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখে, তবে তার হৃদয়ে এক গভীর শূন্যতার সৃষ্টি হয়। সবচেয়ে বড় দুঃখ ছিল, নিজের সন্তানকে হারানোর বেদনা, যা তাকে প্রতিনিয়ত তাড়া করছিল।
আনসারের সাথে তার সম্পর্ক তাকে মুক্তির স্বাদ দেয়। আনসারের সংস্পর্শে এসে সে এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে দেখতে শুরু করে, তবে তার খোকাকে হারানোর শোক তাকে আবার মুসলমান ধর্মে ফিরে আসতে বাধ্য করে। মেজবৌ তখন অনুভব করেন, ক্ষুধার্ত, নিঃস্ব, অবহেলিত শিশুর মধ্যে যেন তার নিজ সন্তানকেই খুঁজে পান। সেই অনুভূতির মধ্যে যে এক গভীর মিলন, যে এক প্রেম ও ত্যাগের উন্মেষ, তা তাকে নতুন করে তার জীবনকে আবিষ্কার করতে শেখায়।
মেজবৌ একসময় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য পাঠশালা খোলার আগ্রহ প্রকাশ করেন, যা পাঠককে তার মানবিকতা ও পরোপকারিতার গভীরতা থেকে এক নতুন পরিচয় দেয়। সেবায়, স্নেহে, সৌন্দর্যে, ধৈর্য্যে, বুদ্ধি ও কর্মপ্রেরণায় মেজবৌ এক অনন্য চরিত্রে পরিণত হন। তাঁর চরিত্রে এমন এক ধরনের ঐশ্বর্য রয়েছে, যা একজন নারীকে তার নিদারুণ দুঃখ-দুর্দশা থেকেও মহত্ত্বের দিকে নিয়ে যেতে পারে। মেজবৌ, তাঁর সংকীর্ণ সমাজ থেকে মুক্ত হয়ে, এক নতুন জীবন বেছে নেন।
এমনকি যদিও মেজবৌ চরিত্রটি মূল উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তবুও তাঁর চরিত্রের ক্রমবিকাশ বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে থাকে। তাঁর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, সন্তান হারানোর বেদনা, এসবের মধ্যে মিলিত হয়ে মেজবৌ এক বহুমাত্রিক চরিত্র হয়ে উঠেছেন। তার এই অন্তর্দ্বন্দ্ব, তার মানবিক সংবেদনশীলতা, তার চূড়ান্ত ত্যাগবোধ— সব কিছু মিলিয়ে মেজবৌ, নজরুলের মানবমুখী নারীচরিত্র সৃষ্টির এক অসাধারণ উদাহরণ হয়ে উঠেছে।
প্রকৃতপক্ষে, মেজবৌ নজরুলের নারীচরিত্রের সৃষ্টিতে যে গভীর মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক চেতনা প্রকাশ পেয়েছে, তা এক অসামান্য সাহিত্যিক কীর্তি।
বিপ্লবী ও সমাজকর্মী আনসার, যিনি সংসার ও গার্হস্থ্য জীবনের চেয়ে বড়ো করে দেখেছিলেন রাজনীতির অতল মহলকে, নিজের জীবনকে একযোগভাবে দেশ ও সমাজের প্রতি নিবেদিত করেছিলেন। কৃষ্ণনগরে নাজির সাহেবের বাসায় কয়েকদিন আতিথ্য গ্রহণ করার সময়, একদিকে যেমন স্নেহ ও সহানুভূতির হাত পেতে পেয়েছিল, তেমনি তার কঠোর সংগ্রামী মনোভাবও তার নির্দিষ্ট লক্ষ্য থেকে এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্যুত হয়নি। কৃষ্ণনগরের পরিবেশে নিজেকে শুদ্ধ করতে, জীবনটাকে অঙ্গীকারের কাছে নিবেদিত করতে সে আরও একবার সজাগ হয়ে উঠেছিল। তবে, একদিন মুহূর্তের জন্য সে তার মনের সমস্ত গোপনীয়তা খুলে ফেলেছিল এবং নিজের আত্মবিশ্বাসের সহিত সে লতিফাকে বলেছিল রুবির কথা— সেই মেয়েটির কথা, যাকে সে গভীর ভালোবাসে। সঙ্গত কারণে আনসার তার বৈধব্য জীবন, জীবনের প্রতি অভিমানী দৃষ্টিভঙ্গি এবং তা থেকে উদ্ভূত জীবনের কঠিন সংগ্রামের কথাও লতিফাকে জানায়। তার অনূভূতিতে রুবির প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসার কথাও স্থান পায়। এই কথাগুলি আনসারের জীবনের অন্তর্নিহিত এক গভীর সত্য ছিল, যা সে লতিফার কাছে প্রকাশ করে।
কিন্তু এই সুখদুঃখের গল্পের চিত্র একেবারে অপরূপ ছিল না। চাঁদসড়কে তার অবস্থানকালে, আনসার কমিউনিস্ট মতবাদের প্রচারের জন্য গ্রেপ্তার হয়ে পড়ে, এবং সেসময় রুবির বাবা নদীয়ায় ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বদলি হয়ে আসেন। তার পর, লতিফা রুবির কাছে জানতে পারে, আনসারের দিনগুলো কৃষ্ণনগরে কেমন কাটছিল, তাঁর কর্মমুখর জীবনের পটভূমি সম্পর্কে নানা তথ্য রুবির কাছে পৌঁছায়, তাতে সে আরও একবার আবিষ্কার করে যে আনসার তাকে সাধ্যমতো ভালোবাসে।
কিছুদিন পর, রুবি একটি ভয়াবহ খবর শোনে। রেঙ্গুন জেলে আনসারের যক্ষ্মা হয়েছে এবং সে মুক্তি পেয়ে এক নতুন যাত্রায় ওয়ালটেয়ারে যাচ্ছিল। রুবি তখন তার প্রাণপ্রিয় আনসারকে বাঁচাতে ওয়ালটেয়ারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। যদিও সেবা ও নিজের প্রাণের উত্সর্গিত ভালোবাসা দিয়ে সে চেষ্টা করেছিল আনসারকে বাঁচানোর, তবুও দুর্ভাগ্যবশতঃ সে সফল হতে পারে না। আনসার মৃত্যুবরণ করে, আর রুবি নিজেও শরীরের ভেতরে রোগের চিহ্ন নিয়ে আক্রান্ত হয়।
গ্রন্থটি শেষ হয় রুবির হাতে লেখা একটি শেষ চিঠির মাধ্যমে, যা সে কুঁচির কাছে পাঠিয়েছিল। চিঠিটি তার অন্তরের দুর্বিষহ অনুভূতির এক গভীর প্রকাশ ছিল, যেখানে সে লিখেছিল, “আমি জানি, আমারও দিন শেষ হয়ে এল! আমিও বেলাশেষের পূরবীর কান্না শুনেছি। আমার বুকে তার বুকের মৃত্যু বীজাণু নীড় রচনা করেছে! আমার যেটুকু জীবন বাকী আছে তা খেতে তাদের আর বেশিদিন লাগবে না। তারপর চিরকালের চির মিলন— নতুন জীবনের নতুন তারায়— নতুন দেশে-নতুন প্রেমে।” (নজরুল রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশঃ ১১ জৈষ্ঠ্য ১৩৭৩, ২৫ মে, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৬৩৬)
এটি শুধু রুবির প্রতি আনসারের গভীর ভালোবাসারই প্রতিফলন নয়, বরং এক অবিনাশী চেতনারও অভিব্যক্তি, যেখানে মৃত্যুও প্রেমের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে।
তবে আনসারের চরিত্রের অন্তর্নিহিত দীপ্তি শেষ পর্যন্ত অম্লান রইল না। রুবি সমাজ সংস্কারের শৃঙ্খল অতিক্রম করে আনসারের সান্নিধ্যে এসে তার সেবার মধ্যে নিজের জীবন ও প্রেমের চরম সার্থকতা খুঁজে পেলেও, আনসারের জীবন যাপন এবং তার অপচয়িত পরিণতি পাঠককে কোনো গভীর উপলব্ধি বা নতুন কিছু বার্তা দিতে সক্ষম হয়নি। আনসারের মতো প্রাণোচ্ছল, মানবদরদী এবং বিপ্লবী চরিত্রের এমন এক শূন্যতা, এমন এক পরিণতি, পাঠক হয়তো প্রত্যাশা করেননি।
এখানেই নজরুলের উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট হয়। তিনি যে বিশেষভাবে ‘‘মৃত্যুক্ষুধা’’ উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন, তাতে একটি সামাজিক সংকট ও তার পরিণতির গভীর চিত্র তুলে ধরেছেন। ‘কী জঘন্য নোংরা পরিবেশের মধ্যেই না সমাজের একটি বৃহত্তম শক্তি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে উদ্দেশ্যহীন’ স্কুল, অপরিতৃপ্ত, অসুখী জীবনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে। সমাজের উচ্চতলার লোকেরা তাদের অবস্থাকে দেখেও কিছু ভাবার অবকাশ পায় না। তারা তাদের নিজস্ব জীবনযাত্রায় এতটাই ব্যস্ত যে, নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি তাদের নজর পড়ে না, তাদের প্রতি সহানুভূতি বা সমবেদনা ভাবনা থেকে অনেক দূরে। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে, বিশেষত ধর্মসংক্রান্ত প্রশ্নে, তারা সক্রিয় হয়ে ওঠে, যেন সেখানে তাদের কর্তব্য পালনে কোনো ফাঁকি থাকে না। নজরুল এখানে সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, শ্রেণিবৈষম্য এবং ধর্মীয় কুশাসনের বিরুদ্ধে একটি কঠোর বার্তা দিতে চেয়েছেন।
‘‘মৃত্যুক্ষুধা’’ উপন্যাসটি আসলে নজরুলের এক অপ্রতিরোধ্য প্রতিবাদ। এখানে তিনি তুলে ধরেছেন সমাজের ধর্মান্ধতা, কূপমণ্ডুকতা এবং স্বার্থপরতার চিত্র। উপন্যাসটির মাধ্যমে নজরুল তাঁর মানবতাবাদী চেতনাকে বিশাল পরিসরে প্রসারিত করেছেন। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের সকল কর্ম ও প্রচেষ্টা একমাত্র মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত। তাঁর বোধের মূল রূপ ছিল মানবতার জয়গান, যা এই উপন্যাসের প্রতিটি পাতায় প্রক্ষিপ্ত হয়ে উঠে।
তবে ‘‘কুহেলিকা’’ নজরুলের তৃতীয় এবং সর্বশেষ উপন্যাস। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালের জুলাই মাসে, এবং এর বিষয়বস্তু একেবারে সেই সময়কার পরাধীন ভারতের মুক্তিসংগ্রামের পরিবেশের মধ্যেই নিহিত। সেই সময় ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে গোপন বিপ্লবী কার্যক্রম, যার মাধ্যমে তরুণ সমাজের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল, তা থেকেই ‘‘কুহেলিকা’’ উপন্যাসটি গড়ে ওঠে। এটি একটি গোপন বিপ্লবী সংগঠনকে কেন্দ্র করে কাহিনী বাঁধে, যা সেই সময়কার প্রতিটি ঘটনা এবং চরিত্রের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বিপ্লবী চেতনাকে তুলে ধরে।
এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে রয়েছে জাহাঙ্গীর, বিপ্লবী নেতা প্রমত্ত, অধিনায়ক বজ্রপাণি, জয়তী এবং তার মেয়ে চম্পা। তাদের জীবন সংগ্রামের মধ্যে অগ্নিযুগের বিপ্লবী চেতনাকে প্রতিধ্বনিত হতে দেখা যায়। এই চরিত্রগুলি দেশের জন্য তাদের নিজস্ব সুখকে ত্যাগ করে, নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে। তাদের বাঁচার ঠিকানা ছিল একমাত্র দেশের মুক্তি, এবং তারা সেই পথে একাগ্রতার সঙ্গে এগিয়ে চলে।
‘‘কুহেলিকা’’ উপন্যাসের পটভূমি তখনকার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। যখন প্রবীণ রাজনীতিবিদরা নিজেদের আবেদন ও ভাষণে ইংরেজ শাসকের দুরূহ ব্যুহ ভেদ করতে পারছিলেন না, তখন তরুণ বিপ্লবীরা গোপনে সশস্ত্র সংগঠন গঠন করে। তারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে দিয়ে এক নতুন আক্রমণাত্মক সংগ্রামে নেমে পড়ে।
বিপ্লবীদের পক্ষে আচরণ ছিল অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত—অতর্কিত আক্রমণ, হামলা, হত্যা, এসবের মাধ্যমে তারা শাসক মহলে ভয় এবং আতঙ্ক সৃষ্টি করে। শাসকগোষ্ঠী ও বিপ্লবীদের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সংগ্রামের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কখনও কোনো প্রশাসক বিপ্লবীদের হাতে নিহত হয়, কখনও বা পুলিশ কর্মকর্তাদের উপর আক্রমণ চলে, আবার কখনো বিপ্লবীদের গোপন অস্ত্রাগার খুঁজে পাওয়া যায়। এরপর শাসক মহল শুরু করে তাদের দমনপীড়ন। বিপ্লবীরা জেলে, গঞ্জের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে এবং দ্বীপান্তরে ধাক্কা খায়, যেখানে তাদের শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার অত্যন্ত ভয়াবহ ছিল।
এই উপন্যাসে নজরুল যে চরিত্রগুলির মাধ্যমে সমাজের অবস্থা তুলে ধরেছেন, তারা শুধুমাত্র বাহ্যিক সংগ্রামের প্রতীক নয়, বরং অন্তরাত্মার, মানবতার, স্বাধীনতার এক বিশাল অঙ্গীকার। তারা যে প্রতিদিনের অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে নিজেদের অতিক্রম করে, তা অত্যন্ত স্পষ্ট। তাদের সংগ্রামের মধ্যে আমরা দেখতে পাই এক নতুন পৃথিবী, যেখানে নির্দয় শাসনের বিরুদ্ধে অসীম সাহসিকতা ও আদর্শের সংগ্রাম প্রতিধ্বনিত হয়।
নজরুলের এই উপন্যাসে, বিশেষত ‘‘কুহেলিকা’’-র মাধ্যমে, আমরা দেখতে পাই, কীভাবে প্রতিটি বিপ্লবী মানুষের জীবনে নেমে আসে একটি অমোঘ সংকল্প—স্বাধীনতা, মানবাধিকার, এবং শোষণহীন পৃথিবী প্রতিষ্ঠা। ‘‘কুহেলিকা’’ শুধু একটি ইতিহাস নয়, এটি এক অভূতপূর্ব চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গি, যা আজও আমাদের দেশপ্রেম, স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের চেতনায় গভীর প্রভাব ফেলেছে।
নজরুলের জীবনকাহিনী থেকে জানা যায় যে, প্রথমে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন। তবে এই আন্দোলনের ব্যর্থতার পর তিনি সন্ত্রাসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। তার চরিত্রের মধ্যে এই পরিবর্তন যেমন দেখা গেছে, তেমনি ‘‘কুহেলিকা’’ উপন্যাসের জাহাঙ্গীরের চরিত্রও একই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত। যখন জাহাঙ্গীর তার মাতৃভূমি ও মাতাকে শ্রদ্ধা জানাতে শিখেছিল, তখনই হঠাৎ সে জানতে পারে তার মা ফিরদৌস বেগম সাহেবা কলকাতার একজন নামী বাইজী, আর তার পিতা ফররোখ সাহেব চিরকুমার। এই খবর শুনে সে উপলব্ধি করে যে, সে পিতামাতার কামজ সন্তান।
এই উপলব্ধি তার ভিতর প্রবল আত্মগ্লানি ও ঘৃণা জন্মায়, আর তার অন্তরাত্মা যেন এক ভারী আর্তনাদে ভরে ওঠে। এসব কষ্টের মধ্যে সে ছুটে যায় বিপ্লবী প্রমত্তের কাছে। নিজের অন্তরের দুর্দশা খুলে বলার পর, আর্তকণ্ঠে জানায় যে তার জীবনের মধ্যে এক অমোঘ ঘৃণা রয়েছে, আর সেই কারণে দেশের সেবার মহান ব্রত তার জন্য সম্ভব নয়। কিন্তু তরুণ বিপ্লবী প্রমত্ত, যিনি এক সময় স্কুলশিক্ষক ছিলেন, তাকে আশ্বস্ত করে। সে জানায় যে, জন্মগতভাবে সে যে কেমনই হোক, তাতে তার পক্ষে দেশসেবার পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণ করা অসম্ভব নয়। কারণ, কোনো মানুষই তার জন্মের জন্য দায়ী নয়।
জাহাঙ্গীর, যিনি স্বভাবতই কিছুটা এলোমেলো এবং উদাসীন, মাতৃইতিহাস জানার পর সংসারের প্রতি আরো বেশি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। নিজের পৈতৃক সম্পত্তির ন্যায্য উত্তরাধিকারী হওয়া নিয়ে সে এক ধরনের অস্বস্তি অনুভব করে। তার মায়ের গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল, জাহাঙ্গীরকে বিয়ে দিয়ে সংসারী করে তোলা, কিন্তু জাহাঙ্গীরের মন অন্যদিকে সরে যায়। তার বেদনার্ত অন্তর দেশের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
হারুন ছিল জাহাঙ্গীরের কলেজ জীবনের নিবিড় বন্ধু। একত্রে মেসে থেকে তারা পড়াশোনা করত। হারুন পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বাসিন্দা, তবে তার আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। হারুনের মা, এক পুত্রসন্তানের মৃত্যুর পর, মানসিকভাবে বিকল হয়ে গিয়েছিলেন। তহমিনা, যিনি ভূণী নামেও পরিচিত, হারুনের বোন। একদিন, ছুটির দিনে, জাহাঙ্গীর হারুনের বাড়ি যায়। তার সঙ্গে ছিল কুমিল্লার ঐশ্বর্যশালী জমিদার পরিবারের উপহারসামগ্রী এবং প্রচুর খাবার।
জাহাঙ্গীরের স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ, সদয় ব্যবহার এবং উপঢৌকনগুলো হারুনের পিতামাতা ও পরিবারের সকল সদস্যকে মোহিত করে। এর মাঝেই হারুনের মা ভূণী, তার অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে, জাহাঙ্গীরকে দেখিয়ে দেয়। জাহাঙ্গীরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎেই কিছুটা অনুরাগ অনুভব করে ভূণী। তবে জাহাঙ্গীরের মনে এক ধরনের দ্বন্দ্ব চলে আসে। কারণ, বিপ্লবীদের মূল লক্ষ্য ছিল দেশমাতৃকাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দেওয়া। ভূণী মনে করে, তার মা দুর্ঘটনাক্রমে যখন তাকে জাহাঙ্গীরের হাতে তুলে দিয়েছে, তখন জাহাঙ্গীরই তার ভবিষ্যৎ স্বামী। কিন্তু জাহাঙ্গীর, ভূণীকে রেখে কলকাতায় চলে আসে।
এত বড় অপমান সহ্য করতে না পেরে, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ভূণী গভীর বেদনায় কাতর হয়ে ওঠে। হারুনকে সে জানায় যে, সে একজন বিপ্লবী। একদিন শিউড়ি স্টেশনের ওয়েটিং রুমে প্রমত্তের সঙ্গে তার দেখা হয়। প্রমত্ত তাকে বিপ্লবীদের নেতা বজ্রপাণির নির্দেশে নিয়ে যায় বিপ্লবীদের শক্তির প্রতীক, মাতৃমূর্তী জয়তীর কাছে। সেখানে চম্পার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হয়। এর পর, জাহাঙ্গীর কলকাতায় ফিরে এলে, তার জমিদারির দেওয়ানজী তাকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যায়।
হারুনের মা, পুত্রের কোনো খবর না পেয়ে কলকাতায় চলে আসে। মায়ের কাছে বক্রেশ্বরের ঘটনা শোনার পর এবং ভূণীর একটি চিঠি দেখতে পেয়ে তিনি বক্রেশ্বরে হারুনের বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। হাওড়া স্টেশনে, জাহাঙ্গীরের সঙ্গে মৌলভী ছদ্মবেশে প্রমত্তের সাক্ষাৎ হয়। মায়ের অনুরোধে, প্রমত্তকে শিউড়ি পর্যন্ত একই সেলুনে যেতে হয়।
হারুনের বাড়িতে জাহাঙ্গীরের মায়ের উপস্থিতিতে সবার মধ্যে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, হারুনের বাবা-মা এবং পরিবারের সকলেই একত্রে কলকাতায় যাবে। হারুনের বাবা-মায়ের চিকিৎসা শেষ হলে তৃণী এবং জাহাঙ্গীরের বিয়ে হবে। তবে, এই সময়ে এক মুহূর্তের দুর্বলতায় জাহাঙ্গীর ভূণীকে চরমভাবে অপমান করে ফেলে, যা তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। এই অবস্থায়, জাহাঙ্গীরের মা সবাইকে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন।
যাত্রাপথে জাহাঙ্গীর জানতে পারে যে, পুলিশ প্রমত্ত, জয়তী এবং বজ্রপাণিকে বন্দি করেছে। তার উপর একটি গুরুতর কর্তব্য নেমে আসে, তা হলো জয়তীর মেয়ে চম্পা এবং কিছু গোপন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কলকাতায় পৌঁছানো। প্রথমদিকে, চম্পা মুসলিম নারী ছদ্মবেশে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে একই সেলুনে চলতে থাকে। তবে, পুলিশ তাদের গতিবিধি বুঝতে পেরে জাহাঙ্গীর ও চম্পা বর্ধমান স্টেশনে নেমে ট্রেন ধরে রাণীগঞ্জে গিয়ে সেখান থেকে ট্যাক্সি করে কলকাতা রওনা দেয়। পথে, তারা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। চম্পা তৎক্ষণাৎ পালিয়ে যায়।
বিচারের পর, বজ্রপাণি, প্রমত্ত, জাহাঙ্গীর এবং তার দলের অনেক সদস্যের দ্বীপান্তর ঘটে। জাহাঙ্গীরের মা, ছেলের বিচারের খবর শুনে চরম শোকের মধ্যে ডুবে যান। জেলখানায় মায়ের সঙ্গে শেষ সাক্ষাতে, জাহাঙ্গীর মাকে প্রশ্ন করে, “একটু ভাবিয়া বলিল, ‘চম্পা এসেছিল তোমার কাছে?’ মাতা বলিলেন, ‘এসেছিল, কিন্তু আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।’ জাহাঙ্গীর বলিল, ‘ভুল করেছ মা, ও ঐশ্বর্যের মালিক যদি আমিই হই, তাহ’লে ঐ ঐশ্বর্যের ভার তারই হাতে ছেড়ে দিও! আমার মা’র মত শত শত মা আজ নিরন্ন, তাঁদের মুখে, তাঁদের সন্তানদের মুখে সে অন্ন দেবে। ও ঐশ্বর্য এখন আমার দেশের নির্যাতিত ভাই-বোনদের। এবার সে এলে তাকে ফিরিও না। হাঁ, ভূণীকে আমার সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ ছেড়ে দিও। ও অনেক দুঃখ পেয়েছে।’” (নজরুল রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশঃ ১১ জৈষ্ঠ্য ১৩৭৩, ২৫ মে, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৭১৮)
‘‘কুহেলিকা’’ উপন্যাসের কাহিনী গভীরভাবে অনুসরণ করলে একটি স্পষ্ট চিত্র উঠে আসে, যেখানে বিপ্লবের প্রকাশ কিছু ক্ষেত্রে ক্ষীণ হয়ে পড়েছে, যদিও প্রেম, সংশয় এবং মানসিক দ্বন্দ্বের অদ্ভুত মিশেল পরিস্ফুট হয়েছে। বিশেষত, ভূণী, জাহাঙ্গীর এবং চম্পার মধ্যে সম্পর্কের যে জটিলতা এবং দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, তা উপন্যাসের মূল সুর হয়ে ওঠে। জাহাঙ্গীরের এলোমেলো চরিত্র, তার পারিবারিক দুঃখ-বেদনা, মেসের বন্ধুদের সান্নিধ্য—এগুলো একে একে উপন্যাসের প্রেক্ষাপট তৈরী করে, যেখানে ভূণীকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিয়েও চম্পার কাছে নিজের অনুভূতিগুলো অকপটে প্রকাশ করার দৃশ্যগুলো এক অনন্য গভীরতা লাভ করে।
তবে, ‘‘কুহেলিকা’’ উপন্যাসের মূল কাহিনীর গভীরে যে বিষয়টি অবস্থান করছে তা হলো স্বদেশী আন্দোলন এবং বিপ্লবের কাঠামো। নজরুলের রাজনৈতিক চেতনাকে এখানে একটি প্রখর ধারা হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। তার বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি, যে পথে তিনি আমাদের জাতির মুক্তির চিন্তা করেছেন, তা উপন্যাসের চরিত্রগুলোর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষ করে, উপন্যাসের কাহিনীতে সশস্ত্র বিপ্লবের যে শুরুর ছায়া দেখা যায়, তা খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, এবং বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে এর বাস্তবায়ন তুলে ধরা হয়েছে। জাহাঙ্গীর, বজ্রপাণি, প্রমত্ত, জয়তী—এরা প্রত্যেকেই পরাধীন ও নির্যাতিত মানবতার প্রতি এক গভীর বেদনাবোধ অনুভব করেন, যা তাদের চরিত্রের সঞ্চালন শক্তি হিসেবে কাজ করে।
এরা সবাই একযোগে সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত, উদার মানবিকতা এবং সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজের প্রতি বিশ্বাসী। বজ্রপাণি যদিও মূলগুরু, তবে প্রমত্তই জাহাঙ্গীরের দীক্ষাগুরু। এটি সেই সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে চিত্রিত করে, যখন হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক মনোভাব জাতির মুক্তির পথে বাধা সৃষ্টি করতে চাইছিল। কিন্তু প্রমত্ত তার দীক্ষায় এসব ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে গেছেন। তিনি তার শিক্ষায় বলেন, “যে বিপ্লবাধিপ বলেন ‘আগে মুসলমান তাড়াতে হবে— তিনি ভুলে যান যে তাঁর এ অতি ক্ষমতা যদি থাকতো তাহলেও চতুর ইংরেজ প্রাণ থাকতে তা হতে দিত না। যেদিন ভারত একজাতি হবে, সেইদিন ইংরেজকেও বোঁচকা-পুঁটুলি বাঁধতে হবে। এ কথা শুধু যে ইংরেজ জানে তা নয়, রামা-শ্যামাও জানে। ‘হিন্দু, ‘মুসলমান’ এই দুটো নামের মন্ত্রৌষধিই ত ইংরেজের ভারত সাম্রাজ্য রক্ষার রক্ষা-কবচ। আমার মনে হয় কি, জানিস? ইচ্ছা করলে আমরা অনায়াসে এ দেশের মুসলমানদের জয় করতে পারি। তবে তা তরবারি দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে। অন্ততঃ একটা স্থুল রকমের শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে ওদের পরিচিত না করে তুললে, ‘কালচার’-এর সংস্পর্শে না আনলে ওদের জয় করতে পারব না। ওদের জয় করা বা স্বদেশে-প্রেঘে উদ্বুদ্ধ করা মানেই ইংরেজের হাতের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া।” (নজরুল রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশঃ ১১ জৈষ্ঠ্য ১৩৭৩, ২৫ মে, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৬৫০)
এখানে প্রমত্তের চিন্তা শুধু এক রাজনৈতিক মন্তব্য নয়, এটি একটি মানবিক বিপ্লবের ডাক। তিনি জানিয়ে দেন যে, সত্যিকারের বিপ্লবী হতে গেলে, ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বিশ্বাস করতে হবে, যার মধ্যে সকল জাতি, ধর্ম, বর্ণের মানুষ সমান অধিকারী। যেহেতু ইংরেজদের মূল শক্তি ছিল ভারতীয়দের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা, তাই এই বিভেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র—জাতিগত বিভাজন—ধ্বংস করা প্রয়োজন।
এই বিপ্লবী চিন্তা নজরুলের সাহিত্যিক চরিত্রে গভীরভাবে রচিত। তার উপন্যাসের চরিত্রগুলো নিজেদের বিপ্লবী চেতনাকে এই ধর্মীয় ও জাতিগত বিভেদ থেকে মুক্তির পথ হিসেবে দেখে এবং এভাবেই তারা ইতিহাসের এক নতুন পথে পা বাড়ায়। ‘‘কুহেলিকা’’ উপন্যাসে এসব বৈচিত্র্যময় চরিত্রের মধ্যে, তাদের সংগ্রাম এবং চিন্তা তাদের মুক্তি এবং স্বাধীনতার জন্য এক নতুন পথপ্রদর্শন করে।
মানুষের মনুষ্যত্বের বিলুপ্তি প্রমত্তকে গভীরভাবে মর্মাহত করেছে। তার বিশ্বাস ছিল, মানুষের এই মনুষ্যত্বই জাতির শক্তি এবং বিবেকের মূল। যখন মানুষ নিজের মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে, তখন জাতির ভিতর থেকে তার বিবেক এবং গৌরব নষ্ট হয়ে যায়। পরাধীনতার দুর্দশা তখন পুরো জাতির অস্থিমজ্জায় মিশে যায় এবং জাতি ক্রমাগত হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সেই হতাশার ভেতরেও জাতির প্রকৃত বিপ্লবী চেতনা তখন গড়ে ওঠে, যা মনুষ্যত্বের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠাকে লক্ষ্য করে। এই বিষয়েই প্রমত্ত তাঁর একটি উক্তিতে বলেন: “আমাদের আর্য মেরেছে, অনার্য মেরেছে, শক মেরেছে, তূণ মেরেছে। আরবী ঘোড়া মেরেছে চাট, কাবলিওয়ালা মেরেছে গুঁতো, ইরাণী মেরেছে ছুরি, ভুরানী হেনেছে তলওয়ার, মোগল-পাঠান মেরেছে জাত, পর্তুগীজ-ওলন্দাজ-দিনেমার-ফরাসী ভাতে মারতে এসে মেরেছে হাতে, আর সকলের শেষে মোক্ষম মার মেরেছে ইংরেজ। মারতে বাকী ছিল শুধু মনুষ্যত্বটুকু যার জোরে এত মারের পরও এ-জাত মরেনি— তাই মেরে দিলে ইংরেজ বাবাজী।” (নজরুল রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশঃ ১১ জৈষ্ঠ্য ১৩৭৩, ২৫ মে, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৬৪৯)
এই কথায় প্রমত্তে যে গভীর বেদনা প্রকাশিত হয়েছে তা হলো, মানুষের মনুষ্যত্বই ছিল জাতির অস্তিত্বের একমাত্র রক্ষাকারী শক্তি। বিভিন্ন শাসকরা বিভিন্ন সময় একের পর এক আঘাত এনেছে, কিন্তু মানুষ তবুও তার চেতনা হারায়নি, বরং তার শক্তি ছিল সেই মনুষ্যত্বেই। ইংরেজরা, যারা তার সমস্ত শক্তি দিয়ে ভারতের মানুষকে দমন করার জন্য চেষ্টা করেছে, অবশেষে মনুষ্যত্বকে নষ্ট করার মাধ্যমে তাদের শাসনের শেষ অস্ত্রটি ব্যবহার করেছে। প্রমত্তের এই উক্তি পরাধীনতার অবমাননার এক স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি, যা মানুষের অন্তরে প্রবাহিত অবিচলিত চেতনার কাহিনী বলে।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘চার অধ্যায়’ (১৯৩৪) এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘পথের দাবী’ (১৯২৬) উপন্যাসে পরাধীন ভারতবর্ষের সংকটগ্রস্ত মনুষ্যত্বের শোকগাথাই মূলত প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁরা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, একটি পরাধীন জাতির সবচেয়ে বড় অভিশাপ হলো তার মনুষ্যত্বের অধঃপতন, আত্মশক্তির ক্ষয় এবং মানবতার অবমাননা। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এই বিষয়ে সমান ধরনের চেতনার ধারক, যেখানে তাদের অন্তর্নিহিত ভাবনার সূচনা পরাধীনতা এবং তার কুফল থেকেই।
রবীন্দ্রনাথের ‘চার অধ্যায়’-এ বিপ্লবীরা তাদের মনুষ্যত্ব হারানোর জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করলেও, তিনি বিশ্বাস করতেন যে সহিংস বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা এবং মানবিকতার পুনঃস্থাপন সম্ভব নয়। তাঁর কাছে মানবিকতার প্রকৃত পুনর্নির্মাণ সম্ভব, একমাত্র মানুষের আত্মশক্তির বিকাশের মাধ্যমে। তিনি উদার মানবিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং সহিংসতার পথ থেকে আলাদা থাকাই মনে করতেন। অন্যদিকে, শরৎচন্দ্র কিছুটা সহানুভূতিশীল ছিলেন সহিংস বিপ্লবের প্রতি, তবে তাঁর ‘পথের দাবী’ উপন্যাসে বিপ্লবের থেকে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে নর-নারীর চিরন্তন হৃদয়বৃত্তি এবং মানবিক সম্পর্কের গভীরতা।
তবে নজরুল ইসলামের বিপ্লবী চেতনা ছিল নির্দ্বন্দ্ব এবং ভাবাবেগহীন। তিনি বিপ্লবের অন্তঃসারশূন্যতাকে কখনও অস্বীকার করেননি, কিন্তু বিপ্লবের মাঝে নর-নারীর হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্ম আলোচনায় কখনোই তেমন কোনো উচ্চকণ্ঠ হননি। তাঁর ‘‘কুহেলিকা’’ উপন্যাসে জাহাঙ্গীর, ভূণী এবং চম্পার প্রেমের সম্পর্ক যেমন উপস্থাপিত হয়েছে, তেমন ইঙ্গিতের মধ্যে এটি পাঠকের মনে তেমন দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয় না। বিপ্লবের তিক্ত বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে, যখন বজ্রপাণি, প্রমত্ত এবং বিশেষ করে জাহাঙ্গীরের দ্বীপান্তর ঘটতে থাকে, তখন পাঠক মনস্তাত্ত্বিকভাবে তার ব্যর্থ জীবনের প্রতি গভীর সহানুভূতি অনুভব করে।
সুতরাং, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র যেখানে মনুষ্যত্বের পুনরুদ্ধারের পক্ষে দৃঢ় ছিলেন এবং মানবিকতার বাণী প্রচার করেছেন, নজরুল ইসলামের কাহিনীতে বিপ্লবের অদ্বিতীয় শক্তি এবং তার ফলাফলকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যদিও মানবিক সম্পর্কের বিষয়টি সেখানে অতটা প্রাধান্য পায়নি।
‘চার অধ্যায়’-এর অন্তু, ‘পথের দাবী’-এর সব্যসাচী এবং ‘‘কুহেলিকা’’-র জাহাঙ্গীর— এই তিনটি চরিত্রে একই বিপ্লবী চেতনা এবং মানবতাবাদী ভাবনার সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। এঁরা সবাই মানুষের মুক্তির জন্য, জাতির স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ। তবে, জাহাঙ্গীরের চরিত্রটি কিছুটা ভিন্ন ধাঁচের এবং বেশি বাস্তববাদী, যা তাকে অন্তু ও সব্যসাচীর তুলনায় আলাদা করে। জাহাঙ্গীর, শুধু একজন দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবী কর্মী নয়, সে এক গভীর দেশভক্ত, যার হৃদয়ে সন্নিহিত আছে মুক্তির জাগরণ। ‘‘কুহেলিকা’’ উপন্যাসে, বক্রেশ্বরের নিসর্গ দেখে যখন জাহাঙ্গীর অভিভূত হয়ে ওঠে, তখন তার দেশের প্রতি এক অদ্বিতীয় ভালবাসা এবং দেশমাতৃকার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ফুটে ওঠে। এটি প্রমাণ করে যে, জাহাঙ্গীরের দেশভক্তি শুধুমাত্র ধারণা নয়, বরং গভীর অনুভূতির প্রকাশ।
রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে, তিনি যেহেতু উদার মানবিকতায় বিশ্বাসী, তাঁর কাছে সহিংস বিপ্লবের চেয়ে মানুষের আত্মশক্তি, মানবতার পুনরুদ্ধার এবং বিশুদ্ধ প্রেমের অধিক গুরুত্ব রয়েছে। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, সহিংস বিপ্লবের চেয়ে মানবজীবন এবং তার নৈতিক মূল্যবোধের ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। ‘চার অধ্যায়’-এ তিনি বিপ্লবী চেতনাকে মানবিক এক দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেছেন, তবে তার চেতনায় সহিংসতা ও নৃশংসতার স্থান ছিল না। তিনি মনে করতেন, মানুষের প্রকৃত মুক্তি ও উন্নতি আসে শুধু আত্মশক্তির বিকাশ এবং উদার মানবিকতার মাধ্যমে।
অপরদিকে, শরৎচন্দ্র ‘পথের দাবী’ উপন্যাসে বিপ্লবের প্রকৃতি অত্যন্ত বাস্তববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ঘাটন করেছেন। তাঁর চরিত্রগুলির মধ্যে, বিশেষ করে পারিবারিক জীবনের স্নেহ-ভালবাসা এবং নর-নারীর চিরন্তন হৃদয়বৃত্তির প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি দেখিয়েছেন যে, বিপ্লবের চেয়ে মানুষের মৌলিক সম্পর্ক এবং জীবনবোধের গুরুত্ব কীভাবে বিপ্লবী চেতনায় প্রভাব ফেলতে পারে। শরৎচন্দ্রের এই দৃষ্টিভঙ্গি বিপ্লবের মানবিক দিকটিকে আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে, যেখানে ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং নৈতিকতা নাড়া দেয়।
তবে, নজরুল ইসলামই একমাত্র এমন লেখক, যিনি বিপ্লবী চেতনা ও দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয়টিকে সম্পূর্ণ আবেগশূন্য ও বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর বিপ্লবী চেতনা অত্যন্ত জোরালো, নিরাবেগ এবং সজাগ। নজরুল ইসলামের বিপ্লবের মধ্যে রয়েছে এক অটুট সংকল্প এবং তীব্র বেদনা, যা শুধুমাত্র মানুষের পরাধীনতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো থেকে আসে। তাঁর ভাষায়, তিনি সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মভেদ এবং সকল বিভাজনকে অগ্রাহ্য করে এক মানবিক বিপ্লবের কথা বলেছেন। নজরুলের উপন্যাসে, বিপ্লবী চেতনা কখনো আবেগের আধিক্যে ডুবে না, বরং এক শক্তিশালী বাস্তবতাকে সমর্থন করে। তাঁর লেখনীর মধ্যে, কেবল মানুষের স্বাধীনতার কথাই নয়, বরং তাদের পরাধীনতায় অনুভূত বেদনারও গভীর বর্ণনা পাওয়া যায়।
এখানে নজরুল ইসলামই শুধুমাত্র মানুষকে ভালবেসে, মানুষের পরাধীনতায় তীব্র বেদনাবোধ করে, আবেগহীন জোরালো দৃষ্টিভঙ্গিতে অসাম্প্রদায়িক মননে, নিরাবেগ আলেখ্য নির্মাণে বিপ্লব চেতনাকে উপন্যাসে অভিব্যক্ত করেছেন।
নজরুলের এই অক্ষয় বিপ্লবী চেতনা এবং মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে অন্যসব বিপ্লবী লেখকদের থেকে আলাদা করে তোলে।
নজরুল ইসলামের সাহিত্যে সর্বধরনের গোঁড়ামী এবং সংকীর্ণতা উত্থাপনকারী সমস্ত ধারণার বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। তাঁর সৃজনশীলতা এবং চিন্তাভাবনা মানুষকে এমনভাবে ভালবাসতে অনুপ্রাণিত করেছে যে, সেসব বাঁধা ও সীমাবদ্ধতা, যা সামাজিক বা ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টি করে, সেগুলির প্রতি তাঁর ছিল তীব্র বিরোধিতা। মানুষ হিসেবে আমাদের প্রকৃত পরিচিতি যে তার মানবিক গুণাবলীতে, সেই ধারণা নজরুলের লেখার প্রতিটি স্তরে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। তাঁর জন্য মানুষ কখনোই তার জাতি, ধর্ম বা বর্ণের ভিত্তিতে বিচার্য নয়; মানুষের আসল মূল্য তার আত্মবিশ্বাস, তার নৈতিকতা, এবং তার মানবিকতা।
এই গভীর মানবিক অনুভূতি নজরুলের বিপ্লবী চেতনার মূলে ছিল। পরাধীন ভারতবর্ষে শৃঙ্খলিত মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় তিনি গভীরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। পরাধীনতার গ্লানি এবং মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তাঁকে আবেগে ভরিয়ে তুলেছিল। এরূপই মানবতা ও সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে ওঠার কথা তিনি বারবার বলেছেন। গোর্কির ‘মা’ উপন্যাসের মতো নজরুলের ‘‘কুহেলিকা’’-ও এমন এক বিশ্বব্যাপী নির্যাতিত মানব সমাজের কথা বলে, যারা জাতিগত, ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিভক্ত এবং অত্যাচারের শিকার। নজরুলের উপন্যাসে এই সংগ্রাম কেবল শারীরিক বা রাজনৈতিক নয়, বরং একটি গভীর মানবিক যাত্রা, যেখানে বিপ্লবী একদিন জয়ী হয়ে, জাতিকে তাদের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি দিতে সক্ষম হবে।
সমালোচকরা নজরুলের উপন্যাস নিয়ে বলেছেন, “নজরুলের সবগুলো উপন্যাস যে শিল্পসম্মত হয়েছে হয়ত তা বলা যায় না, তবু তাঁর ব্যক্তিত্বের সজীবতা, তাঁর মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনকে জানার তৃষ্ণা বাঙলা সাহিত্যের একটি বিশেষ দিককে ঔজ্জ্বল্যে প্রকটিত করেছে। ঔপন্যাসিক হিসেবে নজরুল ইসলামের যে কৃতিত্ব সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তা হল মানুষের প্রতি তাঁর সীমাহীন ভালোবাসা ও জগত জীবনের প্রতি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি।” এই মন্তব্যটি মূলত নজরুলের শিল্পীসত্তা এবং তাঁর সাহিত্যিক দক্ষতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। তাঁরা বলেন, তাঁর সাহিত্যে যে গভীর মানবিক অনুভূতি এবং রাজনৈতিক প্রতিবাদ রয়েছে, তা শুধু সময়ের প্রতি নয়, বরং মানুষের প্রতি তাঁর সীমাহীন ভালোবাসার প্রতিফলন।
মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁর আলোচনায় বলেছেন, ‘‘কুহেলিকা’’ উপন্যাসের নায়ক জাহাঙ্গীর ওরফে উলুল আর ‘‘মৃত্যুক্ষুধা’’ উপন্যাসের নায়ক আনসারকে তাই জীবনের সকল দেনা-পাওনার বাঁধন দু’হাত দিয়ে ছাড়িয়ে এক প্রলয় নেশায় মেতে উঠতে দেখি।” জাহাঙ্গীর এবং আনসার, দুই চরিত্রই নিজেদের জীবন, ভালোবাসা, এবং সামাজিক সম্পর্কের সব কিছু ত্যাগ করে এক কঠিন ব্রতের দিকে এগিয়ে চলে—এরা সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেদের জীবনকে বিপ্লবের আগুনে সমর্পণ করেছে। তবে, তাঁরা পরাজয় সত্ত্বেও কখনোই আত্মসমর্পণ করেনি, বরং তাঁদের সংগ্রাম ছিল এক মহান লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে।
নজরুল ইসলামের উপন্যাসগুলিতে বিপ্লবী চেতনার পাশাপাশি এক অদ্বিতীয় মানবতাবাদ রয়েছে, যেখানে শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা নয়, বরং মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা, এবং মৈত্রীর দিকেও আলোকপাত করা হয়েছে। তাঁর লেখায় আমরা দেখতে পাই এমন এক পৃথিবী, যেখানে বিপ্লবীরা নিজেদের জীবনের সকল দুঃখ-কষ্টকে একপাশে ফেলে দিয়ে শুধুমাত্র দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য তাদের সর্বস্ব দিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।
এভাবে নজরুল ইসলামের উপন্যাস কেবল একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিফলন নয়, বরং মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি এবং স্বতন্ত্রতা, মানবিকতার একটি গভীর ও ঐতিহাসিক পরীক্ষা, যেখানে বিপ্লব এবং মানবতা একে অপরকে পরিপূরক এবং অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত।
নজরুল ইসলামের সাহিত্যে মানবতাবাদী দর্শন এক অমলিন চেতনারূপে প্রতিফলিত হয়েছে, যা কেবল তাঁর কবিতাতেই নয়, বরং তাঁর উপন্যাসেও এক অপরিসীম উদার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রে একটি গভীর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রতিবাদী মনোভাব ফুটে উঠেছে, যা সাহিত্যের অঙ্গনে নজরুলকে একটি অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত করেছে।
‘বাঁধনহারা’ উপন্যাসের নূরুল হুদা একদিকে যেমন নিজেকে জীবনের আরাম, সুখ এবং সচ্ছলতাকে ত্যাগ করে যুদ্ধক্ষেত্রে সঁপে দিয়েছে, তেমনি ‘‘মৃত্যুক্ষুধা’’ উপন্যাসের আনসারও জীবনের আরাম-আয়েশ, বিত্তবৈভব এবং পিতা-মাতার স্নেহ-ভালোবাসা ছেড়ে বিপ্লবী জীবনকে বেছে নিয়েছে। তাঁদের প্রতিটি পদক্ষেপে এক গভীর মানবিক উপলব্ধির প্রকাশ রয়েছে, যেখানে তাঁদের স্বার্থপরতা, ব্যক্তিগত সুখ বা স্থিতিশীলতা কিছুই প্রাধান্য পায় না। বরং, তাঁদের জীবনের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় মানুষের মুক্তি, দেশের স্বাধীনতা এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা। এসব চরিত্রই কেবল নিজেদের সুখের কথা ভাবেনি, বরং তারা জানতেন যে, সমাজের শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিটি পদক্ষেপই এক মহান লড়াই।
‘‘কুহেলিকা’’ উপন্যাসের জাহাঙ্গীরও সেই একই আদর্শে বিশ্বাসী, যে আদর্শে আত্মত্যাগ ও সংগ্রামই সবচেয়ে বড় মূল্যবান। জমিদারি, মা, প্রেয়সী — এসব ত্যাগ করার পর জাহাঙ্গীরের কাছে একমাত্র লক্ষ্য ছিল দেশের স্বাধীনতা ও জনগণের মুক্তি। সে জানতো, স্বাধীনতার জন্য নিঃস্বার্থ সংগ্রাম করতেই হবে, আর তা করতে গিয়েই যে নিজের প্রিয় সবকিছু ত্যাগ করতে হবে, সেটাই ছিল তার জীবনদর্শন। তাঁর চরিত্রটি নজরুলের মানবিক চেতনার এক অত্যাশ্চর্য উদাহরণ।
এই চরিত্রগুলো সব সময় সাম্প্রদায়িকতা, হীনমন্যতা এবং পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, কেননা তাঁরা জানতেন, প্রকৃত স্বাধীনতা এবং সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হতে হলে এই সমস্ত সংকীর্ণতাকে পরাজিত করতে হবে। এরা নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করতে চেয়েছিল, কারণ তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, একমাত্র স্বাধীনতা এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে পৃথিবীকে একটি ন্যায়সঙ্গত, স্বাধীন এবং শান্তিপূর্ণ স্থানে পরিণত করা সম্ভব।
তবে, নজরুল ইসলামের উপন্যাসে আঙ্গিকগত কিছু সীমাবদ্ধতা বা কাঠামোগত দুর্বলতা থাকতে পারে। কিন্তু এর মধ্যে থেকেও তাঁর সাহিত্যের মানবিক দিকটি কখনোই ক্ষুণ্ন হয়নি। তিনি তাঁর উপন্যাসের মাধ্যমে কেবল চরিত্রগুলির সামাজিক অবস্থান বা সংগ্রাম বর্ণনা করেননি, বরং সেই সংগ্রামের পেছনে থাকা মানবিক চেতনা এবং সহানুভূতির গভীরতা অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে ফুটে উঠেছে। নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতি, মানবাধিকার এবং মানব মর্যাদার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা উপন্যাসের প্রতিটি পাতায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই মানবিকতা এবং সহানুভূতির প্রতিফলনই তাঁকে বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ মর্যাদা এনে দিয়েছে।
কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাসগুলো আঙ্গিকগত দিক থেকে কিছুটা সীমাবদ্ধ হলেও, তাঁদের অন্তর্নিহিত মানবিক ভাবনা এবং সংগ্রামী চেতনা কখনোই তাতে বিঘ্নিত হয়নি। বরং তাঁর উপন্যাসে তীব্র প্রতিবাদী মনোভাব, স্বাধীনতা সংগ্রামের অঙ্গীকার এবং নিপীড়িত মানুষের প্রতি সহানুভূতি সমগ্র সাহিত্য জগতে নজরুলের একটি অনন্য স্থান তৈরি করেছে। তাঁদের জীবনদৃষ্টি ও সংগ্রামী চরিত্রের মধ্যে, একদিকে যেমন দর্শনগত অটুট দৃঢ়তা রয়েছে, তেমনি মানবতার প্রতি যে সীমাহীন ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা রয়েছে, তা পাঠকদের গভীরভাবে আঘাত করে।
তথ্যসূত্র :
- নজরুল চরিতমানস : ড. সুশীলকুমার গুপ্ত,
- নজরুল গদ্য সমীক্ষা : মুহম্মদ মজিরউদ্দীন,
- নজরুল উপন্যাস সমীক্ষা : শাহআলম চৌধুরী
- নজরুল রচনাবলী, প্রথম প্র: ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩/ ২৫ মে ১৯৬৬,
- নজরুল একাডেমী পত্রিকা : ১ম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা, শরৎ ১৩৭৬,
- নজরুল সাহিত্য বিচারঃ শাহাবুদ্দীন আহমদ, প্র. প্র. ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬
- নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা- ঊনবিংশ সংকলন

 নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা
নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা