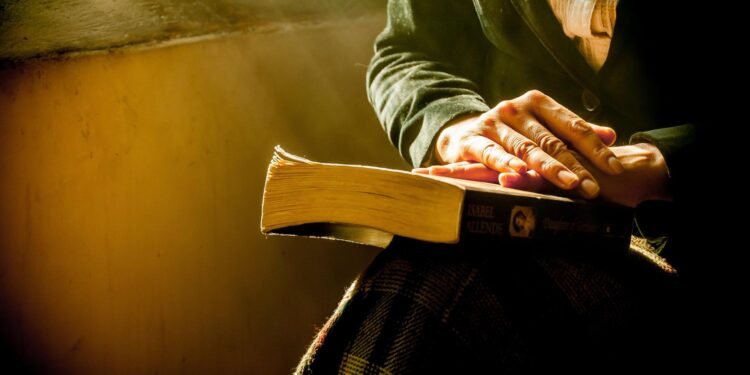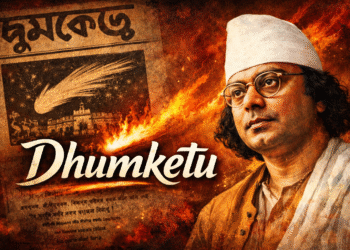লিখেছেনঃ ডঃ তাপস অধিকারী
কাশীরাম দাসের মহাভারতের অনুবাদ
মধুসূদন দত্ত কাশীরাম দাস সম্পর্কে বলেছিলেন,
“হে কাশী কবীশ দলে তুমি পূণ্যবান।”
কবি কাশীরাম দাসের জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে খুব বেশি জানা যায় না। তবে যতখানি জানা গেছে তা থেকে বােঝা যায় ইনি বর্ধমান জেলার উত্তরে ইন্দ্রানী পরগনার অন্তর্গত সিঙ্গি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রামটি ব্রাহ্মন নদীর তীরস্থ। কাশীরামের প্রপিতামহের নাম প্রিয়ঙ্কর, পিতামহের নাম সুধাকর এবং পিতার নাম কমলাকান্ত। কমলাকান্তের তিন পুত্র ছিল কৃষ্ণদাস, কাশীরাম ও গদাধর। কবিদের কৌলিক উপাধি ছিল দেব। সম্ভবত পরবর্তীকালে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহন করায় তাঁরা দাস উপাধি পান। কথিত আছে কাশীরাম মেদিনীপুরের আওসগড়ের জমিদারের আশ্রয়ে থেকে পাঠশালায় শিক্ষকতা করতেন। সেসময় রাজবাড়িতে যে সমস্ত কথক এবং পুরান পাঠকারি পণ্ডিত আসতেন, তাদের মুখ থেকে মহাভারত প্রসঙ্গ শুনে তার মহাভারতের প্রতি অনুরাগ জন্মায়। এই অনুরাগের ফলেই তিনি মহাভারতের অনুবাদ শুরু করেন। কাশীরামের লেখা মহাভারতের অনুবাদ গ্রন্থটির নাম ‘ভারত পাঁচালী”। এটি সম্ভবত তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচনা করেন।
কাশীরাম দাস মহাভারতের অনুবাদ করলেও তিনি মহাভারতের প্রথম অনুবাদক নন। তুর্কি আক্রমনাত্তর কালে উচ্চবর্ণের হিন্দু এবং নিম্ন বর্ণের হিন্দুর মধ্যে সংযােগ স্থাপনের জন্য পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন সংস্কৃতে লেখা পৌরানিক ধর্মগ্রন্থগুলির অনুবাদ শুরু হয়, মহাভারতের অনুবাদও তখনই শুরু হয়। মহাভারতের প্রথম অনুবাদক হিসাবে কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে ধরা হয়। ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে অথবা ষােড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চট্টগ্রামের সুবাদার লস্কর পরাগল খাঁর অনুরােধে মহাভারতের অনুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদের নাম ‘পরাগলি মহাভারত’। এরপর শ্রীকর নন্দী লস্কর পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর নির্দেশে মহাভারতের শুধুমাত্র অশ্বমেধ পর্বটি অনুবাদ করেন। এছাড়াও সঞ্জয়, বিজয়পণ্ডিত, নিত্যানন্দ প্রমুখের নাম মহাভারতের অনুবাদক হিসাবে পাওয়া যায়। তবে মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক হিসাবে কাশীরাম দাসই সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন।
আগেই বলেছি কাশীরাম দাস তাঁর অনুবাদটি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে করেছিলেন। এ অনুবাদটির রচনাকাল জ্ঞাপক একটি ছােট্ট শ্লোক পাওয়া গেছে। তাতে লেখা আছে—
“চন্দ্র বান পঞ্চ ঋতু শক সুনিশ্চয়।
বিরাট হইল শেষ কাশীদাস কয়।।”
এখানে ‘চন্দ্র’ অর্থে ‘১’, বান অর্থে ‘৫’, পক্ষ অর্থে ‘২’ এবং ঋতু অর্থে ‘৬’ ধরলে ১৫২৬ শকাব্দটি পাওয়া যায়। আর ১৫২৬ শকাব্দ অর্থাৎ (১৫২৬+৭৮) ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দ। সুতরাং বােঝা যাচ্ছে কাশীরাম দাস চৈতন্যোত্তর যুগে তাঁর মহাভারতের অনুবাদ কার্যটি সম্পূর্ণ করেন। তিনি নিজে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেছিলেন সেজন্য স্বাভাবিক ভাবেই তার অনুবাদে এই ধর্মের প্রেম ও মানবতাবাদেরও প্রভাব পড়েছে।

কাশীরাম দাসের মহাভারত আনুবাদ সম্পর্কে আলােচনা করতে গিয়ে অনেকেই বলেন যে, তিনি মহাভারতের সম্পূর্ণ অনুবাদ করতে পারেননি। আদি, সভা, বন ও বিরাট- এই চারটি পর্ব অনুবাদ করেন। বাকি অংশটুকু তার ভ্রাতুপুত্র নন্দরাম সমাপ্ত করেন। সমালােচকদের এই অনুমানের পিছনে একটি কারন হল কাশীরাম দাস তাঁর অনুবাদে নিজেই লিখেছেন।
“আদি, সভা, বন, বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর।।”
তবে অনেকে মনে করেন এই স্বর্গপুর আসলে বৈষ্ণবধর্মের পীঠস্থান কাশী অথবা নীলাচল। যাইহােক কাশীরাম দাস মহাভারতের সম্পূর্ণ অণুবাদ করুন আর না করুন শুধুমাত্র এই চারটি পর্বের অনুবাদ বিচার করলেও তার কবি কৃতিত্ব ছােট করা যায় না।
কাশীরাম দাস সংস্কৃত মহাভারতের হুবহু অনুবাদ করেননি, তিনি মহাভারতের ভাবানুবাদ করেছেন। তাই অনেকেই মনে করেন কাশীরাম সংস্কৃত জানতেন না, তিনি পাঁচালিকার ও কথকদের মুখ থেকে মহাভারতের যে কাহিনি শুনেছিলেন, তা-ই নিজের রচনায় লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু একথা সঠিক না। এ ব্যপারে দীনেশ চন্দ্র সেন তঁার ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ গ্রন্থে বলেছেন,
“সে সময়ের অনুবাদ মূল কাব্যের ছায়া লইয়া লিখিত হইত, কাশীরাম দাসের মহাভারত ঠিক সংস্কৃত অনুযায়ী নহে, এই জন্য কবি সংস্কৃত জানিতেন না, এইরূপ মত প্রচার করা বােধ হয় উচিত নহে।”
কাশীরামের অনুবাদটি পড়লে কখনােই মনে হয়না যে, তিনি সংস্কৃত জানতেন না। হয়তাে শ্রোতার কাছে আকর্ষণীয় করার জন্য তাঁর অনুবাদে যেমন অনেক কিছু বাদ দিয়েছেন, তেমনি আরও কিছু সংযােজন করেছেন। ফলে কাহিনিটির রসহানি হয়নি, বরং আরও আকর্ষণীয় হয়েছে। তিনি কিছু কিছু জায়গায় মহাভারতের সংস্কৃত শ্লোক যেভাবে বাংলায় রূপান্তরিত করেছেন তা লক্ষ্য করলে তাকে সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত বললেও কম বলা হয়।

আগেই বলা হয়েছে কাশীরাম দাস চৈতন্যোত্তর যুগের কবি ছিলেন এবং নিজেও বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহন করেছিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবে তাঁর রচনার ভাব ও ভাষায় চৈতন্যদেবের একটা প্রভাব পড়েছিল। তিনি তাঁর রচনায় মূল মহাভারতের রুক্ষতা, শুষ্কতা, বৈরিতা অনেকটাই কমিয়ে এনেছিলেন। বাংলার প্রকৃতির সাহচর্যে এসে তাঁর রচনায় বাঙ্গালীর মানবপ্রেম, সৌভ্রাতৃত্ব এগুলাে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। ফলে অনুবাদটি বাঙ্গালীর হৃদয়ের অনেক কাছাকাছি আসতে পেরেছে এবং ব্যপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।
কাশীরাম দাস তাঁর আনুবাদের ঘটনাবিন্যাস, নাটকীয়তা, সরস উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং হাস্যরসকে সুন্দরভাবে পরিবেশন করেছেন। ফলে তাঁর রচনা অনেকবেশি চিত্তাকর্ষী হয়ে উঠেছিল। কাশীরাম দাস ছাড়াও আর যারা মহাভারতের অনুবাদ করেছিলেন তাদের তুলনায় কাশীরামের ভাষা ছিল অনেক সহজ-সরল এবং মার্জিত। তিনি রসসাহিত্যের প্রায় সব রসকেই এই অনুবাদের উপযুক্তভাবে প্রয়ােগ করেছেন। তিনি যেন এই কাব্যের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালী সমাজের স্বার্থত্যাগের মহিমা, ভ্রাতৃপ্রীতি, মাতৃভক্তি ও স্বজন প্রীতির সত্যনিষ্ঠা, আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রভৃতিকে প্রকট করে তুলতে চেয়েছেন।
কাশীরাম দাসের মহাভারতের আলােচনা প্রসঙ্গে মধ্যযুগের আর অনুবাদক কীর্তিবাসের তুলনা এসেই পড়ে। এ প্রসঙ্গে দীনেশ চন্দ্র সেন বলেছেন,
“কীর্তিবাস যেরূপ পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে ব্যপক যশের অধিকারী হইয়া ছিলেন, কাশীদাস তাহা হইতে পাড়েন নাই।”
আবার অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দুইজনের তুলনা করে আরও বলেছেন যে,
“কীর্তিবাসী রামায়ণে বাঙ্গালী জীবন ও সমাজের এত বেশী ছাপ পড়েছে যে, রামকাহিনী বাঙ্গালীর ঘরের সামগ্রী হয়ে উঠেছে, কাশীরাম দাসের মহাভারতে ঠিক ততটা বাঙ্গালীয়ানা দেখা যায়না। তবে কাশীরামের বিণয়াবনত বৈষ্ণবমনটি রচনার মধ্যে অকৃত্রিম ভাবেই ধরা পড়েছে।। ভক্তবংশে যে তাঁর জন্ম হয়েছিল, তা তার রচনা থেকেই বুঝতে পারা যায়। এদিক থেকে উত্তর চৈতন্যযুগের ভক্তির ধারা তার হৃদয়কে গভীরভাবে প্লাবিত করেছিল।”
যাইহােক আমাদের এটা মানতেই হবে কীর্তিবাস ওঝার রামায়ণের অনুবাদে বাঙ্গালীয়ানা দেখানাের অনেক সুযােগ ছিল, কাশীরাম করেছিলেন বীররসাত্মক কাব্য মহাভারতের অনুবাদ। এখানে বাঙ্গালীয়ানার চাইতে অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে যুদ্ধ-বিগ্রহ, লড়াই-সংঘাত। তবুও কাশীরাম যে তার রচনাটি বাঙ্গালীর উপযােগী করে লিখেছিলেন এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আর হয়ত এই কারনেই আজও মহাভারতের কথা মনে পড়লে সবার আগে স্মরণে আসে কাশীরাম দাসের সেই বিখ্যাত শ্লোক
“মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পূণ্যবান।।”
আমরা দীনেশ চন্দ্র সেনের একটি মন্তব্য দিয়ে কাশীরাম দাসের আলােচনা শেষ করব। তিনি মহাভারতের আলােচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন,
“এক একখানি পত্র এক একটি চমৎকার চিত্রপটের ন্যায়, পড়িতে পড়িতে জগৎপুঞ্জ, যুদ্ধবীর ও প্রেমিকগণের মূর্তি মানসচক্ষের সমক্ষে উদ্ঘাটিত হয়; তাহাদের সরল বিবেক, দৃঢ় কামনা ও চরিত্রের সাহস কবির সচেতন লেখনির গুনে ক্ষণকালের জন্য আমাদের নিজস্ব হইয়া পড়ে। এই নিঃসম্বল, অর্ধভূক্ত, পরদোষে কটাক্ষ পান্ডুরতাপূর্ণ বাঙ্গালীজাতিও ক্ষণকালের জন্য পৃথিবীজয়ী উচ্চ আকাঙ্ক্ষাশালী অভিমানাঙ্ক্ষিত পূর্বপুরুষগণের কাহিনী পড়িয়া স্বীয় ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া গর্ব অনুভব করে।”
সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যধারা
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা হল মঙ্গলকাব্য সাহিত্যের ধারা। এই মঙ্গলকাব্য সাহিত্যের ধারার মধ্যে সর্বপ্রাচীন ধারা হল মনসামঙ্গল কাব্যধারা। সাপের দেবী মনসার পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে এই ধারা বহমান ছিল। টানা ৪০০ বছর এই ধারা বহমান থাকার ফলে মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনির ক্ষেত্রে যেমন কমবেশি নানা পরিবর্তণ লক্ষ্য করা যায়, তেমনি এই কাব্যের প্রচুর রচয়িতার নামও পাওয়া যায়৷ মনসামঙ্গলের কাহিনি সমগ্র বাংলাদেশ জুড়েই প্রচলিত ছিল। স্বাভাবিকভাবেই মনসামঙ্গলের কবিদের অস্তিত্ব সমগ্র বাংলাদেশ জুড়েই ছিল।
মনসামঙ্গলের আদিকবি হিসাবে কানাহরি দত্তের নাম পাওয়া যায়। এছাড়াও বিজয়গুপ্ত (পদ্মপুরান), বিপ্রদাস পিপলাই (মনসা বিজয়), নারায়ন দেব প্রমুখ কবি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। এরা ছিলেন প্রাকচৈতণ্য যুগের কবি এবং এরা সবাই পূর্ববঙ্গের অধিবাসী। চৈতণ্যোত্তর যুগের কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, দ্বিজ বংশীদাস, তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘােষাল, জীবন মৈত্র প্রমুখ কবিরা মনসামঙ্গল কাব্যধারার চর্চা করেন। এছাড়াও এসময় মনসার কাহিনি অবলম্বনে ২২ জন কবি ‘বাইশা’ রচনা করেন। এই কবিদের মধ্যে তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘােষাল ও জীবন মৈত্র উত্তরবঙ্গের লােক ছিলেন। এরা সপ্তদশ শতাব্দীতে মনসামঙ্গলকাব্য রচনা করে খ্যাতিলাভ করেন।
উত্তরবঙ্গের কবিদের মধ্যে তন্ত্রবিভূতি হলেন মনসামঙ্গলের নব্য আবিস্কৃত কবি। ড. আশুতােষ উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলা থেকে তন্ত্রবিভূতি রচিত মনসামঙ্গল কাব্যটি আবিস্কার করেন। পণ্ডিতরা মনে করেন তাঁর নাম ছিল বিভূতি এবং তিনি তন্ত্রসাধনা করতেন, তাই তাঁর নাম হয়েছে তন্ত্রবিভূতি৷ আবার ড. সুকুমার সেন অনুমান করেছেন,
“মনে হয় কবি জাতিতে তাঁতি ছিলেন, তাই ভণিতায় নিজেকে ‘তন্ত্রবিভূতি’ বলিয়াছেন।” (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস)।
তন্ত্রবিভূতি তাঁর কাব্যের সর্বত্র পুরাে ভণিতাই ব্যবহার করেছেন। যেমন—
“মন দিঞা সঙে মনসার গীত।
তন্ত্রবিভূতি গায়ে মনসা চরিত৷৷”
মধ্যযুগের বেশিরভাগ কবির সম্পর্কে যেমন খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায়নি, তেমনি তন্ত্রবিভূতি সম্পর্কেও বেশি কিছু জানা যায়নি। সম্ভবত তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে তার মনসামঙ্গল কাব্যটি রচনা করেন। তন্ত্রবিভূতি মনসামঙ্গল কাব্যটি দেবী মনসার পূজা প্রচারের গতানুগতিক কাহিনি অনুসারে রচিত। এর দু’টি অংশ দেবখণ্ড ও নরখণ্ড। কাব্যটি মঙ্গলকাব্যের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী দেববন্দনা দিয়ে শুরু হয়েছে। এরপর মনসার আবাহন, অনিরুদ্ধ ও উষাকে অভিশাপ প্রদান প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে। তারপর চাঁদ কর্তৃক মনসার বিরােধিতা, মনসার কোপে চাঁদের সপ্তডিঙ্গা ডুবে যাওয়া, লক্ষ্মীন্দর সহ চাঁদের সপ্তপুত্রের সর্পদংশনে মৃত্যু হওয়া, স্ত্রী সনকাসহ পুত্রবধুদের হাহাকার এবং বেহুলার প্রচেষ্টায় চাঁদের মনসা পূজায় রাজী হওয়া প্রভৃতি স্থান পেয়েছে। এ কাব্যে কোথাও কোথাও যেমন তান্ত্রিক ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব পড়েছে তেমনি চৈতণ্যোত্তর যুগে রচিত হওয়ায় বৈষ্ণবধর্মেরও প্রভাব পড়েছে।
তন্ত্রবিভূতি তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যটির ক্ষেত্রে গতানুগতিক কাহিনি গ্রহণ করলেও মাঝে মাঝে নতুন কিছু করে দেখানাের চেষ্টা করেছন। চরিত্র চিত্রণে তিনি অভিনবত্ব আনতে চেয়েছিলেন। যুদ্ধবর্ণনায়, চাঁদমনসার বিদ্বেষ বর্ণনায়, কল্পনা ও সহানুভূতির সামর্থে তিনি উচ্চস্তরের কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। হাস্যরস সৃষ্টি, রূপবর্ণনা, করুণরস সৃষ্টি প্রভৃতিতে তার বিশেষ নৈপুন্য ছিল। একারণেই ড. আশুতােষ দাস তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,
“কি কাহিনী বর্ণনে, কি চরিত্র চিত্রণে তাহার নৈপুণ্য ছিল। কবিত্ব শক্তিতে তিনি প্রায় প্রথম শ্রেণীর মনসামঙ্গল কবিদের সমগােত্র। মুকুন্দরামের ন্যায় তন্ত্রবিভূতিও দুঃখ বর্ণনায় বড়।”
অনেকেই তন্ত্রবিভূতির কাব্যে উগ্র ও অনাবৃত আদিরসের বর্ণনা দেখে তাঁর সমালােচনা করেন। কিন্তু রচনারীতি, কাহিনি বর্ণনা প্রভৃতি দিক থেকে বিচার করলে তন্ত্রবিভূতির প্রশংসাই করতে হয়। ড. আসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তার প্রশংসা করে বলেছেন,
“উত্তরবঙ্গে মনসামঙ্গলে যে নতুনত্ব পরিলক্ষিত হয়, তার প্রথম সূচনা করেন তন্ত্রবিভূতি। এইজন্য সপ্তদশ শতাব্দীর মনসামঙ্গল কাব্যের বিবর্তণের ইতিহাসে তন্ত্রবিভূতির কাব্য বিশেষভাবে উল্লেখযােগ্য।” (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত; তৃতীয় খণ্ড; প্রথম পর্ব, পৃষ্ঠা-১১১)।
তন্ত্রবিভূতি ছাড়াও উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যের আর একজন উল্লেখযােগ্য কবি হলেন জগজ্জীবন ঘােষাল। ড. আশুতােষ দাস ও সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগজ্জীবন ঘােষালের পুঁথি প্রকাশ করেন। মনেকরা হয় ইনি তন্ত্রবিভূতির পরেই মনসামঙ্গল কাব্যের চর্চা করেছিলেন। জগজ্জীবন ঘােষাল সম্পর্কে জানা গেছে যে, ইনি দিনাজপুর জেলার কুচিয়ামােড়া গ্রামে (বর্তমানে পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত) জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দিনাজপুরের রাজা প্রাণনাথের সমসাময়িক ছিলেন। কবির পিতামহের নাম জয়ানন্দ। পিতা রূপ ও মাতা রেবতী। কাব্যটি কবে রচিত হয়েছে পুঁথিতে তার কোন স্পষ্ট নির্দেশ নেই। তবে পুঁথিতে ক্ষেমানন্দের উল্লেখ থাকায় মনে করা হয় এটি ক্ষেমানন্দের পরে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচণা করা হয়েছে।
মধ্যযুগের অন্যান্য কাব্যের মত জগজ্জীবনের কাব্যটিও দেবখণ্ড ও বনিয়াখণ্ড এই দুইভাগে বিভক্ত। কাহিনিটিও গতানুগতিক এবং মাঝে মাঝে তন্ত্রবিভূতির ছাপ আছে। অনেক সময় এই ছাপ এতটাই প্রকট যে মাঝে মাঝে মনে হয় তিনি তন্ত্রবিভূতিকে নকল করে লিখেছেন। তবে গতানুগতিক কাহিনি গ্রহণ করলেও জগজ্জীবনের কাব্যে সৃষ্টিতত্বের বর্ণনা, শিব-দুর্গার গ্রাম্যকাহিনি প্রভৃতি স্থান পেয়েছে। বেহুলার কাহিনিতেও উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ বৈশিষ্ট্য পুরােপুরি রক্ষিত হয়েছে। তবে জগজ্জীবনের কাব্যের কিছু কিছু ক্ষেত্রে আদিরসের এমন বর্ণনা আছে যা আতিশয় ঘৃণ্য।

যাইহােক জগজ্জীবন ঘােষাল তাঁর কাব্যের অনেক ক্ষেত্রেই নতুনত্ব এনেছিলেন। তিনি ধর্ম, মনসা, গঙ্গা এবং শিব-দুর্গাকে নিয়ে তার কল্পজগতের নানা গল্প কথাকেও কাব্যে স্থান দিয়েছেন। তাঁর কাব্যে কিছু রুচিবিকার ও অশ্লীলতা থাকলেও তিনি চরিত্র বর্ণনায়, ভাষা-ছন্দ-অলংকার প্রভৃতিতে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বেহুলার কেশ শয্যার বর্ণনা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা যেতে পারে
“কত ভ্রমর পড়ে উড়ে উড়ে যায়।
খোপার উপর পড়ে খোপার মধু খায়।।
কনক দর্পণ লইল হস্তেতে করিয়া।
আপনার রূপ দেখে আপনি নিরখিয়া।।”
এই বর্ণনা উচ্চশ্রেনির কবিত্বের পরিচয় দেয়। হয়ত এই কারণেই ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সম্পর্কে বলেছেন,
“জগজ্জীবনের কাব্যে কলুষিত বর্ণনা থাকলেও রচনা কৌশল বিচার করলে এই কবি প্রশংসা দাবি করিতে পারেন। সংস্কৃত সাহিত্য, পুরান, অলংকার, শাস্ত্র প্রভৃতিতে তাহার বিশেষ অধিকার ছিল। ছন্দ, শব্দপ্রয়ােগ এবং উপমাদি অলংকার প্রয়ােগেও তাহার সূক্ষ দৃষ্টি, বুদ্ধি ও মনন বিশেষ প্রসংশার যােগ্য।” (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত; তৃতীয় খণ্ড; প্রথম পর্ব, পৃষ্ঠা১১৭)।
এরা দু’জন ছাড়াও মনসামঙ্গল কাব্য ধারায় উত্তরবঙ্গের আর একজন উল্লেখযােগ্য কবি হলেন- জীবন মৈত্র। তিনি ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর কাব্যটি রচণা করেছিলেন।
সুতরাং দেখা যাচ্ছে মধ্যযুগে মনসার পূজা উপলক্ষে যে মনসা মঙ্গল কাব্যগুলি রচিত হতে শুরু করে তা কোন নির্দিষ্ট গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা সমগ্র বাংলাদেশেই ছড়িয়ে পড়েছিল। এই মনসামঙ্গল কাব্যের চর্চা পূর্ববঙ্গের ও রাঢ়বঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও জনপ্রিয় হয়েছিল। আর উত্তরবঙ্গে এ কাব্যের জনপ্রিয়তার পিছনে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘােষাল, জীবন মৈত্র প্রমুখেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।
ধর্মমঙ্গল কাব্যধারা
মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যধারাগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযােগ্য কাব্যধারা হল ধর্মমঙ্গল কাব্যধারা। ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম ও তার পূজা প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে এই কাব্যধারা বিকাশ লাভ করেছিল। বর্ধমানে ও পশ্চিম এবং দক্ষিন বাংলার অনেক গ্রামে এখনও ধর্মের স্থান, মন্দির ও আস্তানা আছে। ধর্মের কোন মূর্তি নেই। তার শিলাগুলি বেদির উপর প্রতিষ্ঠিত। যদিও একেক স্থানে এই মূর্তি একেক রকম হয়। কোনটি কচ্ছপের মত, কোনটি কাঁকড়া বিছার মত, কোনটি গােলাকার, কোনটি চৌকা, আবার কোনটির কোন বিশেষ আকৃতিও নেই। তবে ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪ পরগণা জেলার দু-একটি গ্রামে ধর্মের বীরবেশি বিশাল মূর্তি আছে বলে মন্তব্য করেছেন।
এই ধর্মঠাকুরের স্বরূপ সম্পর্কে পণ্ডিতমহলে বিতর্ক আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ধর্মঠাকুর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদেবতা। সুকুমার সেন মনে করেছেন ধর্মঠাকুর একটি বিশেষ মিশ্রদেবতা। বৈদিক ধর্মাচরণ, আর্যেতর সংস্কার, ব্রাহ্ম-শৈবধর্ম, নাথ ধর্ম এবং ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির বিষ্ণু উপাসনার সঙ্গে ধর্ম উপাসনার যােগ আছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে—
‘অষ্ট্রিক জাতির পূজিত কোন আদিম দেবতা হল এই ধর্মঠাকুর। আশুতােষ ভট্টাচার্য মনে করেছেন হিন্দু ও বৌদ্ধরা এইদেশে আসার আগে ডােম সম্প্রদায়ের লােকেরা যে দেবতার পূজা করতেন সেই প্রাগার্য দেবতা সূর্যদেবতা হলেন ধর্ম। শ্বেতরশ্মি যুক্ত সূর্যকে ‘ওরম’ বলা হয়। ওর থেকে ধরম্ এবং ধর্মের উৎপত্তি। নৃতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র রায়ও ধর্মদেবতাকে দ্রাবিড় যুগের দেবতা বলে অনার্য জাতি পুজিত সূর্যদেবতা বলে মন্তব্য করেছেন। আবার কেউ কেউ ধর্মঠাকুরকে বৈদিক বরুন ও যমের সঙ্গে ডােম চঁড়াল জাতির রণদেবতা, অনার্যরে শিলাদেবতা, মুসলমানের ফকির বেশধারী দেবতার প্রভাব আছে বলে মনে করেছেন। সুতরাং বােঝা যাচ্ছে ধমের উদ্ভব বা স্বরূপ নির্ণয় করতে গেলে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্যে পৌছানাে যায়না। এর মধ্যে বৌদ্ধ, হিন্দু, পৌরানিক-লৌকিক উপাদান মিশ্রিত আছে।’
ধর্মঠাকুরের পূজা মূলতঃ রাঢ়বঙ্গেই প্রচলিত। ধর্মঠাকুরের নামে দু’টি কাহিনি আছে রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনি ও রঞ্জাবতী-লাউসেনের কাহিনি।। এর মধ্যে লাউসেনের বীরত্বের কাহিনিটি অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ধর্মঠাকুরের কৃপায় অপুত্রক রমণীরা সন্তান লাভ করে, দুরারােগ্য কুষ্ঠরােগ থেকে মানুষ মুক্তি পায়- এই বিশ্বাস থেকেই মানুষ ধর্মপূজায় মেতে ওঠেন।
যদিও ধর্মমঙ্গল কাব্যধারা অন্যন্য মঙ্গকাব্যের তুলনায় অনেক অর্বাচীন কালের সৃষ্টি, তবুও এই ধারায় অনেক কবির পরিচয় পাওয়া যায়। এই কবিদের মধ্যে ময়ূরভট্টকে ধর্মমঙ্গলের আদিকবি বলে মনে করা হয়। তিনি ছাড়াও রূপরাম চক্রবর্তী, রামদাস আদক, সীতারাম দাস, যদুনাথ বা যাদবনাথ, শ্যামপন্ডিত প্রমুখরাও ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। এদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন রূপরাম চক্রবর্তী। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীতে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। তাঁর সম্পর্কে ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,
“চরিত্র চিত্রণ, বর্ণনাভঙ্গীমা, আত্মকথা প্রসঙ্গে বাস্তত চিত্র অঙ্কণের প্রবনতা, ভাষাও রচনারীতি বিচার করলে তাকে প্রশংসা করতেই হবে, ধর্মমঙ্গলের সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি ঘনরাম রচনাচাতুর্যে অধিকতর খ্যাতিলাভ করলেও সৃষ্টিশক্তিতে রূপরামের প্রচেষ্টা অনেকবেশি আত্মিক।।”
রূপরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল কাব্যে কৃতিত্ব দেখালেও এই কাব্যধারার সর্বশ্রেষ্ঠ কবির স্বীকৃতি দেওয়া হয় ঘনরাম চক্রবর্তীকে।
ধর্মমঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি ঘনরাম চক্রবর্তী অষ্টাদশ শতাব্দীর লােক ছিলেন। তার কাব্য প্রথম মূদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করে এবং ব্যপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কাব্যের ভণিতা থেকে ঘনরাম সম্পর্কে জানা গেছে যে তিনি বর্ধমান জেলার দামােদর নদীর তীরে কুকুরা কৃষ্ণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গৌরিকান্ত ও মাতার নাম সীতা। কবির চারপুত্র ছিল। তিনি অত্যন্ত রামভক্ত ছিলেন বলে পুত্রদের নামও রামের নামে দিয়েছিলেন। যথা- রামরাম, রামগােপাল, রামগােবিন্দ ও রামকৃষ্ণ। তাঁর কাব্যে যে সন তারিখের উল্লেখ আছে তাতে মনে করা হয়, তিনি ১৬৩৩ শকাব্দ অর্থাৎ (১৬৩৩+৭৮) ১৭১১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর কাব্যটি সমাপ্ত করেন।
ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যটি ২৪টি পালায় বিভক্ত। তিনি কাব্যের নামের ক্ষেত্রে অনাদিমঙ্গল। শ্রীধর্মসঙ্গীত, মধুরভারতী প্রভৃতি নামও ব্যবহার করেছেন। তিনি কবিত্বের দিক দিয়ে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে ড. সুকুমার সেন বলেছেন,
“ধর্মমঙ্গল রচয়িতাদের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিত ও দক্ষ ছিলেন ঘনরাম চক্রবর্তী। তিনি সুলেখক ছিলেন। তাহার রচনা সর্বাধিক পরিচিত ধর্মমঙ্গল কাব্য।”
এই শক্তিশালী কবি তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনি বর্ণনায়, ঘটনা সংস্থাপনে, ভাষারীতির ব্যবহারে, ছন্দ-অলংকার প্রয়ােগে যথেষ্ট নিপুনতা দেখিয়েছেন। তাঁর কাব্যটি যেন রাঢ় অঞ্চলের মানুষের জীবন্ত দলিল হয়ে উঠেছে। এই কাব্যে বীরত্ব, মনুষ্যত্ব ও নারীধর্মের যে উচ্চআদর্শ প্রচারিত হয়েছে তা বিশেষ প্রশংসার যােগ্য। ঘনরামের চরিত্রগুলি বিশেষত লাউসেন, রঞ্জাবতী, মহামদ প্রমুখেরা আপন স্বাতন্ত্রে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। লাউসেনের মধ্যে বীরত্ব ও পুরুষত্বের যথার্থ সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। রঞ্জাবতী বাঙালী নারীর আদর্শে গঠিত হলেও তার মধ্যে বীরত্বের ভাব আছে। আবার মহামদের মাধ্যমে ঘনরাম মহাভারতের শকুনিকেই যেন ফুটিয়ে তুলেছেন। খলচরিত্র হিসাবে এই মহামদ অপূর্ব সৃষ্টি। এছাড়াও কালুডােম, লখাই প্রমুখ অপ্রধাণ ছােট চরিত্রগুলিতেও ঘনরাম কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।
ঘনরামের কাব্যটিতে হাস্যরস বা কৌতুকরসের সৃষ্টেতেও উচ্চাঙ্গের রুচিবােধের পরিচয় আছে। অনুপ্রাসসহ সব ধরণের অলংকার প্রয়ােগে তিনি সাবলীল ছিলেন। যুদ্ধ বর্ণনায় ঘনরাম আশ্চর্য কল্পনার পেরিচয় দিয়েছেন
‘টনটান ঘনঘান চলেচলে চনচন
ঝনঝান ঘরণ।।
দেখিতে বিপরীত চৌদিকে চমকিত
যা যুগভাবে পরমাদ।।”
সংস্কৃত ঘেঁষা শব্দ প্রয়ােগেও ঘনরাম যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। হয়তঃ এই সকল কারণে ড. আশুতােষ ভট্ট চার্য ঘনরাম সম্পর্কে বলেছেন,
“চন্ডীমঙ্গল কাব্যের ঐশ্বর্য্য যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি যেমন মুকুন্দরাম, ঘনরাম তেমনি ধর্মমঙ্গল কাব্যের ঐশ্বর্য্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।”
ধর্মমঙ্গল কাব্যে রাঢ় অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা ফুটে উঠেছে এবং এই কাব্যটি রাঢ় অঞ্চলেই সর্বাধিক প্রচলিত আছে জন্য আনেকেই ধর্মমঙ্গলকে রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য বলতে চান। আমরা জাতীয় মহাকাব্য সেই কাব্যকে বলি যেখানে একটি জাতির ইতিহাস, জীবনযাপন প্রণালী, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, রীতিনীতি প্রভৃতির প্রতিফলন ঘটে অর্থাৎ কাব্যটির মধ্য দিয়ে সেই জাতিকে সম্পূর্ণভাবে চিনে নেওয়া যায়। ধর্মমঙ্গল কাব্যটি বীরভূম, বর্ধমান ও বাঁকুড়ার জনজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা। এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে যে অন্ত্যজ শ্রেনির মানুষের বাস তাদেরই ইতিহাস, জীবনযাপন প্রণালী, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, রীতিনীতির প্রকাশ ঘটেছে। পাশাপাশি মহাকাব্যের শর্তপুরণ করে কাব্যটিতে অষ্টাধিক সর্গ অর্থাৎ ২৪টি সর্গ আছে। কাব্যটি বীররস প্রধাণ, এতে যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনাও আছে। এখানে নানা অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ঘটানাে হয়েছে, যা মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্যকে স্মরণ করায়। যদিও অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেছেন ধর্মমঙ্গল কাব্যে শুধুমাত্র রাঢ়ের অন্ত্যজ শ্রেনির মানুষদের পরিচয় আছে সামগ্রিক জীবনকে ফুটিয়ে তােলা হয়নি, কিন্তু তার এই মত মেনে নেওয়া যায়না। কারণ অন্ত্যজ শ্রেনিদের নিয়ে ধর্মমঙ্গল কাব্যের সূচনা হলেও এই কাব্যে সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ, নদ-নদি, স্থান প্রভৃতি সবই উঠে এসেছে। তাই কাব্যটি সমগ্র রাঢ় অঞ্চলে ব্যপক জনপ্রিয়তা লাভ করে সেখানকার জাতীয় কাব্য হতে পেরেছে।
আরাকান রাজসভার সাহিত্যচর্চা
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল বাংলার মূল ভূখন্ডের বাইরে চট্ট গ্রামের অদূরে আরাকানে (বর্তমানে ব্রহ্মদেশ বা মায়ানমারের অন্তর্গত) বৌদ্ধরাজাদের পৃষ্টপােষকতায় কিছু মুসলিম কবিদের দ্বারা বাংলা সাহিত্যের চর্চা। আরাকান যা দীর্ঘদিন বাঙ্গালীদের কাছে ‘মগের মুলুক’ নামে পরিচিত ছিল সেখানে সপ্তদশ শতাব্দীতে মুসলিম কবিরা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিকতা ত্যাগ করে দেবদেবী নির্ভর সাহিত্য রচনা না করে রােমান্টিক প্রণয় কাব্য রচনা করেন। এই কবিরা মুসলিম হলেও ধর্ম নিরপেক্ষ সাহিত্য রচনার দিকেই বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। যা মধ্যযুগের পরিপ্রেক্ষিতে বিস্ময়কর ঘটনা।
আরাকানে দীর্ঘদিন মগজাতীয় বৌদ্ধ রাজারা রাজত্ব করতেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এ রাজাদের সঙ্গে গৌড়াধিপতির বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। এই ঘনিষ্ঠতার কারণে বাংলার মূল ভূখণ্ড থেকে অনেক মুসলিম সম্প্রদায়ের লােকেরা আরাকানে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ নিজ প্রতিভার গুনে আরাকান রাজের মন্ত্রী ও সেনাপতির মত পদে রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। এই লােকগুলি যেহেতু দীর্ঘদিন বাংলার মূল ভূখন্ডে বসবাস করছিলেন তাই বাংলার শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি তাদের যথেষ্ট আকর্ষণ ছিল। হয়ত এই কারনেই আরাকান রাজের শীর্ষপদে অধিষ্ঠিত এই মুসলিম রাজপুরুষেরা সেখানে শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা শুরু করেন। মুলতঃ এদের প্রচেষ্টায় ও পৃষ্ঠপােষকতায় সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্যের বিকাশ সম্ভব হয়। আরাকান রাজসভায় সাহিত্য চর্চা করেছেন এইরকম বেশ কয়েকজন মুসলিম কবির নাম পাওয়া যায়। তবে এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভাধর দু’জন কবি হলেন- দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল।
দৌলত কাজী
দৌলত কাজী আরাকান রাজসভার সবচেয়ে প্রতিভাধর ও সংবর্ধিত কবি। তাঁর সম্পর্কে জানা গেছে যে, তিনি চট্টগ্রামের অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামে এক সুফী মতাবলম্বী মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আনুমানিক জন্মকাল ষােড়শ শতাব্দীর শেষভাগ। ইনি আরাকান রাজ থিরি-সু-ধম্মা অর্থাৎ শ্রী সুধর্মার রাজ সভার কবি ছিলেন। এই রাজার সমর সচীব ছিলেন আশরফ খান। দৌলত কাজী আশরফ খানের অনুগ্রহে, পৃষ্টপােষকতায় ও নির্দেশে তার একমাত্র কাব্য ‘লােরচন্দ্রানি’ বা ‘সতী ময়না’ রচনায় হাত দেন। তবে এটি দৌলত কাজীর মৌলিক রচনা ছিলনা। এটি হিন্দি কবি মিয়াসাধনের ঠেট গােহারি ভাষায় রচিত ‘ময়নাকো সতু’ কাব্য অবলম্বনে রচিত। দৌলত কাজী কাব্যটি সমাপ্তও করতে পারেন নি। এর দুই-তৃতীয়াংশ লিখে মারা যান। তবে অসম্পূর্ণ কাব্যটি থেকে দৌলত কাজীর কবি প্রতিভার নানা দিক ধরা পড়েছে। দৌলত কাজীর তাঁর কাব্যটি রচনা করেন আনুমানিক ১৬২ ১- ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে।
দৌলত কাজীর ‘লােরচন্দ্রানি’ বা ‘সতীময়না’ কাব্যের বিষয়বস্তু লাের ও চন্দ্রানীর প্রেমের আখ্যানকে নিয়েই গড়ে উঠেছে। এর কাহিনিতে দেখা যায় গােহারী দেশের রাজকন্যা চন্দ্রানির ভাগ্যদোষে এক নপুংসক বামনের সাথে বিয়ে হয়। শিকারে এসে রাজা লাের চন্দ্রানিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তার সাথে মিলিত হয়। কিন্তু তাদের এই মিলনের প্রধান বাধা ছিল চন্দ্রানির স্বামী বামন। ফলে বামনের সাথে লােরের যুদ্ধ বাধে এবং সেই যুদ্ধে বামন পরাজিত ও নিহত হয়। এরপর লাের চন্দ্রানিকে বিয়ে করে গােহারি দেশেই থেকে যায়। কিন্তু চন্দ্রানির সাথে সাক্ষাতের পুর্বে লাের বিবাহিত ছিল, বাড়িতে তার সতী সাধ্বী স্ত্রী ছিল, যার নাম ময়না। দীর্ঘদিন লাের ফিরে না এলে ময়না স্বামী বিরহে কাতর হয়ে পড়ে। এসময় এক লম্পট রাজপুত্র ময়নাকে প্রলােভন দেখালেও ময়নার প্রবল সতীত্বের কারনে কাছে ভীড়তে পারেনি৷ যখন ময়নার এরকম মানসিক অবস্থা তখন ময়নার দুঃখ ও বিরহের যন্ত্রনা দূর করার জন্য তার এক সখী তাকে রাজা উপেন্দ্রদেব ও তার গর্ভবতী স্ত্রী রতনকলিকার এক উপকাহিনি শােনান। সেখানে দীর্ঘ বিরহের পর স্বামী-স্ত্রীর মিলন হয়। ‘লােরচন্দ্রানি’ কাব্য এই পর্যন্ত দৌলত কাজী রচনা করেছিলেন। বাকি অংশটির রচয়িতা আরাকানের অপর কবি সৈয়দ আলাওল। এই অংশে দেখা যায় সখীর কাছে শােনার পর ময়না লােরের কাছে দূত পাঠায়। লােরের সব কিছু মনে পড়ে এবং সে চন্দ্রানিকে নিয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে গিয়ে সুখে দিন কাটায়। সৈয়দ আলাওল রচিত এই অংশটি দৌলত কাজীর তুলনায় অত্যন্ত দুর্বল রচনা।
দৌলত কাজী একটা কাব্যের মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ রচনা করলেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তার রচনাটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তিনি হিন্দি কাব্যের আনুবাদ করলেও কাহিনি বর্ণনায় ও উপস্থাপনে নতুনত্ব এনেছেন। অনেক ক্ষেত্রেই বাঙ্গালীর উপযােগী ঘটনা ও দৃশ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। দৌলত কাজীর চরিত্রগুলিও জীবন্তভাবে এই কাব্যে ফুটে উঠেছে। তার ময়নামতী চরিত্রটি সতীত্বের আদর্শ প্রতিমূর্তি। চন্দ্রানীর রুপ বর্ণনায় তিনি অসামান্য কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। রাজা লােরও তাঁর কাব্যে নায়কের সমস্তগুন নিয়ে হাজির। নপুংসক বমনের বীরত্ব ও লােরের সাথে তার যুদ্ধ এই কাব্যের সম্পদ।
দৌলত কাজী সুফী মতাবলম্বী মুসলীম ছিলেন জন্য সুফী মতবাদের প্রভাবও তাঁর কাব্যে যথেষ্ট পরিমানে আছে। তিনি নিজে মুসলীম হলেও কাব্যের যত্রতত্র হিন্দু বিষয়ের আমদানি ঘটিয়ে তার উদার ধর্মবােধেরই ছাপ রেখেছেন, যা তৎকালে প্রায় অসম্ভব ছিল। কাব্যের ভাষা, ছন্দ, অলংকার প্রয়ােগেও দৌলত কাজী অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর রচনার প্রশংসা করে ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,
“দৌলত কাজী সতীময়নার যেটুকু লিখেছেন তার কাহিনী খুব সংযত ও পরিছন্ন। ময়নার সতীত্ব, প্রলভনের সামনে অবিচল নিষ্ঠা, পলাতক স্বামীর প্রতি আপরিসীম শ্রদ্ধা প্রভৃতি বিষয় সমূহ কবি চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। * * * কিন্তু সৈয়দ আলাওল যে শেষাংশ সম্পূর্ণ করেন তার কাহিনী, চরিত্র, রচনারীতি কিছুই দৌলত কাজীর সমতুল্য হয় নি।”
সৈয়দ আলাওল
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিদের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত কবি হলেন সৈয়দ আলাওল। ইনি অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত ফতেয়াবাদ বা ফরিদপুরে অন্তর্গত জালালপুর গ্রামে ষােড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মজলিস কুতুবের মন্ত্রী ছিলেন। বাল্যকালে জলদস্যুদের সঙ্গে সংঘর্ষে আলাওলের পিতা মারা যান। পিতৃহীন অবস্থায় কবির বাল্যজীবন দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়েই কাটে। পরবর্তীকালে তিনি আরাকানের সেনাবাহিনিতে যােগ দেন। এইসময় তিনি আরাকানরাজের সমরসচিব মাগনঠাকুরের পৃষ্ঠপােষকতা পান। মুলতঃ এই মাগনঠাকুরের কারনেই আরাকান রাজসভায় তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ে এবং রাজ আনুকূল্যেই তিনি সাহিত্য সেবায় মন দেন। যদিও একবার তাঁকে রাজরােষে পড়ে কারাবরণও করতে হয়।
সৈয়দ আলাওলের লেখা বেশ কয়েকটি গ্রন্থের নাম যানা যায়। এইগুলি হল—১) সয়ফুলমুলুকবদিউজ্জামাল, ২) হপ্তাপয়কর, ৩) তােহফা, ৪) সেকেন্দার নামা, ৫) পদ্মাবতী। এছাড়াও তিনি দৌলত কাজীর ‘লােরচন্দ্রানি’ কাব্যটি সমাপ্ত করেন এবং আরও কিছু সাহিত্য রচনা করেন। তবে ‘পদ্মাবতী’ কাব্যটির জন্যই তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আজও স্মরণীয়। সৈয়দ আলাওল বৃদ্ধবয়সে ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে পরলােক গমন করেন।
সৈয়দ আলাওলের ‘পদ্মাবতী’ কোন মৌলিক রচনা নয়; এটি প্রসিদ্ধ হিন্দি কবি মালিক মহম্মদ জায়সীর ‘পদুমাবৎ’ কাব্যের কাহিনি অবলম্বনে রচিত। এই কাব্যটি ইতিহাসে আলাউদ্দিন খলজীর চিতাের আক্রমণের কাহিনি অবলম্বনে রচিত। তবে কাব্যের খাতিরে এখানে ইতিহাসকে হুবহু অনুসরণ না করে অনেক কাল্পনিক ঘটনাকে নিয়ে আসা হয়েছে। এর কাহিনিতে দেখা যায় চিতাের রাজ রত্নসেনের সাথে সিংহল রাজকন্যা পদ্মাবতীর বিবাহ হয়। কিন্তু দিল্লির সম্রাট আলাউদ্দিন খলজী পদ্মাবতীর রূপ-সৌন্দর্যের কথা শুনে তাকে লাভ করার জন্য চিতাের আক্রমণ করেন। ফলে চিতাের রাজ রত্নসেনের সাথে তার যুদ্ধ বাঁধে এবং বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেও শেষ পর্যন্ত চিতাের রাজ রত্নসেন আলাউদ্দিনের কাছে পরাজিত ও নিহত হন। এদিকে রানী পদ্মাবতী আপন সতীত্ব রক্ষার জন্য ‘জহরব্রত পালন করে আত্মবিসর্জন করেন।
সৈয়দ আলাওল হিন্দি কাব্যের অনুসরণে কাব্যটি রচনা করলেও কাব্যটিতে নানাদিক থেকে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কাব্যটি তিনি হুবহু অনুবাদ করেননি, মাঝে মাঝে মৌলিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন যা কাব্যটির পক্ষে আকর্ষণীয় হয়েছে। চরিত্র চিত্রণে তিনি আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর রানী পদ্মাবতী সতীত্বের প্রতিমূর্তী হিসাবে আজও উজ্জ্বল। রাণা রত্নসেনের মধ্যে তিনি পুরুষত্ব ও বীরত্বের আদর্শ সহাবস্থান ঘটিয়েছেন। তাঁর কাব্যের ভাষা, বর্ণনারীতি প্রভৃতি সবক্ষেত্রেই স্বচ্ছন্দতা আছে। ছন্দ, অলংকার এর ক্ষেত্রেও কবি আলাওল যথেষ্ট কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। পাশাপাশি মুসলিম সম্রাট আলাউদ্দিনের সাথে রত্নসেনের বিবাদে আলাওল ধর্মনিরপেক্ষতার ছাপ রেখেছেন। কবি নিজে মুসলিম ধর্মাবলম্বী হলেও হিন্দু সংস্কৃতি সম্পর্কে তার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল তাও লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্ত কারনে ‘পদ্মাবতী’ আজও আলাওলকে কবিত্বের উচ্চ শিখরে ধরে রেখেছে।
দৌলত কাজী ও আলাওল ছাড়াও আরাকান রাজসভায় আরও কিছু মুসলমান কবি বাংলা সাহিত্যের চর্চা করেছিলেন। এরা হলেন সৈয়দ সুলতান, মহম্মদ খান, হাজি মহম্মদ প্রমুখ। তবে কবিত্বশক্তিতে এরা উপরের দু’জনের সমতুল্য ছিলেন না। যাইহােক মধ্যযুগের এই মুসলীম কবিরা নানা কারনে বাংলা সাহিত্যে নিজেদের স্বতন্ত্র সথান করে নিয়েছেন। এই কারনগুলি হল—
প্রথমত:
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের চর্চা মূলতঃ বাংলার মূল ভূখন্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু বাংলার বাইরে সুদুর আরাকানে বাংলা সাহিত্যের চর্চা হওয়ার কারনে বাংলা সাহিত্যের ভৌগােলিক সীমা বৃদ্ধি পেয়েছে।
দ্বিতীয়তঃ
সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় এ যুগে শুধুমাত্র হিন্দুরাই বাংলা সাহিত্যের চর্চা করেছেন। কিন্তু আরাকানে যে সাহিত্য রচিত হয়েছিল তার রচয়িতারা ছিলেন মুসলিম। সুতরাং মধ্যযুগের সাহিত্য যে শুধুমাত্র হিন্দুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তাতে মুসলিমরাও অংশ গ্রহণ করেছিল তার প্রমান এই আরাকান রাজসভার সাহিত্য।
তৃতীয়ত:
আরকান রাজসভার সাহিত্য বাদে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পুরােটাই দেবদেবী নির্ভর। আরাকানেই প্রথম বাংলা সাহিত্যকে দেব নির্ভরতা কাটিয়ে মানব নির্ভর করা হয়।
চতুর্থত:
আরাকান রাজসভার মুসলমান কবিরা হিন্দুদের বিষয়বস্তু নিয়ে সাহিত্য চর্চা করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এই সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির একটা সমন্বয় গড়ে উঠেছিল। যা মধ্যযুগের নিরিখে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।
পঞ্চমত:
আরাকান রাজসভার কবিরা যে মানব নির্ভর কাব্যগুলি রচনা করেছিলেন সেগুলি ছিল রােমান্টিক প্রণয়কাব্য। এইরকম প্রণয়কাব্য মধ্যযুগের আর কোন সাহিত্যিকের রচনায় দেখা যায়নি।
সর্বোপরি, আরাকান রাজসভার কবিরা মৌলক কাব্য রচনা না করে অনুবাদ কাব্য লিখেছিলেন। এদের পূর্বেও বাংলায় অনেকগুলাে অনুবাদ কাব্য রচিত হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি ছিল কোন না কোন সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ। আরাকানের কবিরাই প্রথম সংস্কৃত ছাড়া অন্য ভাষা থেকে অনুবাদ শুরু করেন। ফলে বাংলা সাহিত্যে অনুবাদের পরিধির বিস্তার ঘটে। এ সব কারনে আরাকান রাজসভা ও সেখানকার কবিগণ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয়।
নাথ সাহিত্য
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য মূলত বিভিন্ন ধর্ম ও উপধর্ম সম্প্রদায় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। শাক্ত, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব প্রভৃতি প্রধান ধর্ম সম্প্রদায়ের পাশাপাশি এ যুগে নানা উপধর্ম সম্প্রদায়ও গড়ে উঠেছিল। এই ধর্ম ও উপধর্ম সম্প্রদায়গুলির উদ্ভব মূলতঃ আর্য সংস্কৃতি থেকে হয়েছিল। কিন্তু আর্যদের পূর্বে ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন কাল থেকেই অনার্য সংস্কৃতির বিস্তারলাভ ঘটেছিল। এই আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির মিশ্রচেতনা থেকেই ভারতবর্ষে শৈব নাথধর্ম গড়ে ওঠে। এই নাথ ধর্মের আদর্শগত বৈশিষ্ট্য নিয়েই বাংলা সাহিত্যে নাথ সাহিত্যের চর্চা শুরু হয়।
খ্রিস্টিয় দশম শতাব্দীতে সমগ্র উত্তরভারতে গােরক্ষপন্থী নাথ সম্প্রদায় বর্তমান ছিল। পশ্চিমভারতেও এদের কমবেশি প্রভাব ছিল। বাংলাদেশেও অধিক প্রাচীনকাল থেকেই নাথ সম্প্রদায়ের লােকেরা নিজেদের সাধন-ভজন করে আসছিল। এই সম্প্রদায়ের লােকেরা নিজেদের ধর্ম, কর্ম, আচার-আচরণকে কেন্দ্র করে বহু। ছড়া, পাঁচালী, লােকগীতি ও আখ্যণ কাব্য রচনা করেছেন। এগুলি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ রচনাগুলিতে সুকঠোর তপশ্চর্যা, সংযম, ইন্দ্রীয়দক্ষতা ও দৈহিক হঠযােগ সাধনার দ্বারা কিভাবে আশ্চর্য, অনৈসর্গিক শক্তি অর্জন করা যায় তার বর্ণনা আছে। নাথপন্থীদের এই সাধনা ও গুরু পরম্পরার কাহিনি নিয়ে বহু পুস্তক-পুস্তিকা রচিত হয়েছে। তাদের গুরু পরম্পরায় আদিগুরু হলেন শিব। শিব ও গােরক্ষনাথকে ধরে এই সম্প্রদায়ে প্রায় ৯জন গুরুর কথা জানা যায়। নাথসাহিত্যে এই গুরুদের কার্যকলাপ বর্ণিত হয়েছে।
সমগ্র নাথসাহিত্যকে দু’টি বৃত্তে ভাগ করা হয়- ১) গােরক্ষনাথের মহিমাবিষয়ক ‘গােরক্ষনাথ বৃত্ত’ বা ‘মীনচেতন’ এবং ২) রানী ময়নামতী ও তার পুত্র গােপীচন্দ্রকে নিয়ে ‘ময়নামতী-গােপীচন্দ্র বৃত্ত’।
গােরক্ষনাথ বৃত্তে গােরক্ষনাথের মহিমার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে দেখানাে হয়েছে ধর্মঠাকুর নিরঞ্জনের শরীরের নানা অঙ্গ থেকে এক একজন যােগীর উদ্ভব হলে জটা থেকে গােরক্ষনাথ এবং সমগ্রদেহ থেকে গৌরির উদ্ভব হয়। নিরঞ্জনের নির্দেশে শিব গৌরিকে বিবাহ করেন। এরপর গৌরি শিবের সব শিষ্যদের পরীক্ষা নিতে চাইলে একমাত্র গােরক্ষনাথ ছাড়া সবাই গৌরির রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং গৌরি তাদের অভিশাপ দেন৷ অভিশাপ পেয়ে গােরক্ষনাথের গুরু মীননাথ কদলীদেশে গিয়ে সাধন-ভজন সব ভুলে ষােলশত রমণীর সাথে কাম-ক্লেদ রসে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। গােরক্ষনাথ গুরুকে উদ্ধারের জন্য নর্তকের বেশে সেখানে প্রবেশ করেন এবং সেখানে অনেক কঠোর পরিশ্রম করে শেষ পর্যন্ত গুরুকে পূর্বচেতনায় ফিরিয়ে আনেন। যেহেতু এই বৃত্তে মীননাথের চেতনা ফিরিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে, তাই এর আর এক নাম ‘মীনচেতন’।

গােরক্ষনাথ বৃত্তের বেশ কয়েকজন কবির নাম জানা যায়। বর্তমানে গােরক্ষমহিমা বিষয়ক তিনখানি পুঁথি ছাপা হয়েছে। যথা- ১) ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত কবি শ্যামদাস সেনের ‘মীনচেতন’। ২) মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত শেখ ফয়জুল্লার ‘গােরক্ষবিজয়’ এবং ৩) ড. পঞ্চানন মন্ডল সম্পাদিত ভীমসেনের ‘গােখবিজয়।
এই কাব্যগুলির মধ্যে কোনটি প্রাচীন তা নিয়ে পন্ডিতমহলে বিতর্ক আছে। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত মােলটি পুঁথির মধ্যে চোদ্দটিতে শেখ ফয়জুল্লার ভণিতা দেখা যায় যার মধ্যে নয়টিতে শুধু তারই ভণিতা আছে। এই রচণায় আরবী, ফার্সী, মুসলমানি বাংলা শব্দের ব্যবহার দেখে মনে করা হয় তা মুলতঃ শেখ ফয়জুল্লার রচনা। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে এটি রচিত হয়েছে। ড. আশুতােষ ভট্টাচার্য এই কাব্যটির মানবিক আবেদনে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। কালিদাস রায় লিখেছেন যে গােরক্ষবিজয়ের মূল বক্তব্য হল—
“গুরু নিজে সম্পূর্ণ সিদ্ধ না হইয়াও যদি অনন্য সাধারন শিষ্য লাভ করেন, তবে তার দীক্ষামন্ত্রে শিষ্যও গুরুর গুরু হইয়া উঠিতে পারেন।”
শেখ ফয়জুল্লার কাব্যটির প্রধান সম্পদ গােরক্ষনাথের চরিত্র। গােরক্ষনাথ বিপথগামী গুরুকে উদ্ধারের জন্য ছদ্মবেশে কদলীরাজ্যে প্রবেশ করে গুরু মীননাথকে তিরস্কার করতেও ছাড়েন নি।
“বােঝাইলে না বােঝ তুমি পশুর লক্ষন।
অমৃত ছাড়িয়া করাে গরল ভক্ষণ৷৷”
এ রচনা থেকে অনেক সময় রচয়িতাকে নারী বিদ্বেষী বলে মনে হলেও কদলী রাজ্যের বর্ণনায় তিনি শান্ত সুন্দর চিত্র অঙ্কন করেছেন। শেখ ফয়জুল্লা তাঁর রচনায় নানা ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপমার সাহায্যে ব্যঞ্জণার সৃষ্টি করেছেন। যেমন এক জায়গায় বলেছেন,
“আমার বচনে গুরু তােমার নাহি মন।
অশ্বথের গাছে যেমন কহি এ স্বপন।।”
আবার আর এক জায়গায় বলেছেন
“মূখের অক্ষর দেখাইলে নাই ফল।
তেনাে মতে কহি আমি তােমাকে নিস্ফল।।”
নাথসাহিত্যের অপরবৃত্ত ময়নামতী-গােপীচন্দ্র বৃত্তে অভিশাপগ্রস্থ হয়ে জলন্ধরি পাদ বা হাড়িপা মেহেরকুলের রানী ময়নামতীর রাজ্যে নীচ হাড়ির কর্ম করতে শুরু করেন। এদিকে যােগসিদ্ধা রানী ময়নামতী আপন মহাজ্ঞান শক্তি দ্বারা জানতে পারেন যে, যদি তার স্বামী তার কাছে থেকে মহাজ্ঞান না নেন তাহলে তার মৃত্যু আসন্ন। পৌরুষত্বে ঘা লাগবে এই কারনে তার স্বামী স্ত্রীর কাছে থেকে মহাজ্ঞান নেন না এবং অকালেই মারা যান। স্বামীর মৃত্যুর পর ময়নামতীর গােপীচন্দ্র নামে এন পুত্র জন্মায়। বয়স হলে রানী তাকে অদুনা ও পদুনা নামে দুই বােনের সাথে বিয়ে দেন। কিন্তু রানী এর ক্ষেত্রেও মহাজ্ঞান দ্বারা জানতে পারেন গােপীচন্দ্র যদি হাড়িপার কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে কিছুকাল সন্ন্যাস জীবন না কাটান তাহলে তারও মৃত্যু আসন্ন। এদিকে নব বিবাহিতা আদুনা-পদুনা কিছুতেই স্বামীকে সন্ন্যাসী হতে দিতে রাজী হয়না। ফলে সে স্ত্রীদের প্ররােচনায় নিজের মার নামে হড়িপাকে জড়িয়ে কলঙ্ক রটায় এবং ময়নামতীকে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়। শেষ পর্যন্ত গােপীচন্দ্র মার প্রস্তাব মেনে নিয়ে হড়িপার কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে ১২ বছর সন্ন্যাস জীবন কাটিয়ে ফিরে এসে স্ত্রীদের নিয়ে সুখে সংসার জীবন কাটান।
গােপীচন্দ্র বৃত্তে বেশ কয়েকজন কবির নাম জানা যায়। এদের মধ্যে কয়েকজন উল্লেখযােগ্য হলেন দুর্লভ মল্লিক, ভবানী দাস, সুকুর মহম্মদ প্রমূখ। তবে শ্রেষ্ট কবি হিসাবে দুর্লভ মল্লিককে ধরা হয়। দুর্লভ মল্লিক রাঢ় অঞ্চলের মানুষ ছিলেন জন্য তাঁর রচনা অনেকটাই প্রাঞ্জল। কাব্যের নায়ক গােপীচন্দ্র চরিত্রটি অনেকটাই স্বাভাবিক ও অন্তর্দন্দ্বে সমৃদ্ধ। সন্ন্যাস গ্রহণের প্রস্তাবে সে মা ময়নামতীকে বলেছিল,
‘করিবে আমারে যােগী যদি ছিল মনে।
অদুনা-পদুনা তবে বিভা দিলা কেনে।।
মায়ের অগ্নিপরীক্ষা দেওয়ার সময় তার অন্তরে দ্বন্দ্ব ও অপরাধবােধ দেখা দিলে সে বলেছে—
“তােমারে পােড়াব মাতা অপযশ লােকে।
কুকর্ম করে আমি মরিব নরকে।।”
গােপীচন্দ্রের দুই স্ত্রী চরিত্রে স্বামী প্রেম বড়াে হয়ে উঠেছে। তারা স্বামীকে বলেছিল—
“তােমারে লইতে যম আসিবে যখন।
তােমার বদলে মােরা যাব একজন।।”
দুর্লভ মল্লিক তার কাব্যের অনেক ক্ষেত্রে দার্শনিক তত্ত্বের আভাস দিয়েছেন। এই বৃত্তের অপর কবি ভবানী দাসের ভাষা অত্যন্ত গ্রাম্য। তাঁর রচনায় যেমন বৈষ্ণব পদাবলীর কিছুটা প্রভাব আছে তেমনি অনেক ক্ষেত্রে হাস্যরসের অবতারণা আছে। ভবানী দাস তাঁর কাব্যে একস্থানে চৈতন্যদেব-এর উল্লেখ করেছেন,
“কেশব ভারতী গুরু কোথা হইতে আইল।।
কিবা মন্ত্র দিয়া নিমাই সন্ন্যাস ছাড়িল৷৷”
এই ধারার অপর কবি সুকুর মহম্মদও স্বাভাবিক চরিত্রের সৃষ্টি করে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। শৈবনাথ ধর্ম বহু প্রচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করেছে। আজও কোথাও কোথাও এর অস্তিত্ব আছে। মধ্যযুগে এদের নিয়ে বাংলা সাহিত্য রচিত হয়েছিল। তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শৈবনাথ ধর্মকে নিয়ে লেখা নাথসাহিত্যগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শেষ শক্তিধর কবি হলেন রায়গুনাকর ভারতচন্দ্র। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর অবক্ষয়ের যুগে জন্মগ্রহণ করে প্রাচীণ ও নবীনের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে সাহিত্য চর্চা করেছিলেন। ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক ধারায় সাহিত্য চর্চা করলেও তার মধ্য দিয়ে নতুনের দিকেই দিক নির্দেশ করেছেন। একদিকে প্রাচীনের দৈববাদ, অপরদিকে আধুনিকের যুক্তিবাদ ভারতচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভাকবি ছিলেন। রাজসভায় থেকে সাহিত্য চর্চা করতে গিয়ে তিনি নাগরিক সমাজকে তাঁর রচনায় ফুটিয়ে তুলেছেন।
মধ্যযুগের অন্যান্য কবিদের সম্পর্কে খুব বেশি জানা না গেলেও ভারতচন্দ্রের নিজস্ব আত্মপরিচয় এবং ঈশ্বরগুপ্ত কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাবলী থেকে ভারতচন্দ্র সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা যায়। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে হাওড়া-হুগলি জেলার ভুরসুট পরগনার পোড়াে গ্রামে এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর পিতা বর্ধমানরাজের রােষাণলে পড়লে ছােট থেকেই ভারতচন্দ্রের জীবন দুঃখময় হয়ে ওঠে। ভারতচন্দ্র মাতুলালয়ে মানুষ হন এবং সেখানেই অতি উত্তমরূপে সংস্কৃত শেখেন। কিন্তু তার সময়ে সংস্কৃত ভাষার তেমন কদর ছিলনা। এই সময় তিনি পরিবারে তিরস্কৃত হয়ে ফার্সিভাষা শিখতে বাধ্য হন। তিনি পরিবারের অসম্মতিতে নিজ মনােনীত পাত্রীকে বিয়ে করলে পরিবারের বিরাগভাজন হন। পরে সম্পদ উদ্ধারের আশায় বর্ধমান রাজ দরবারে গিয়ে বন্দী হন এবং সেখান থেকে কোন ক্রমে পালিয়ে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে নীলাচলে যাত্রা করেন। এ সময় তার শ্বশুর বাড়ির একজন সন্ন্যাসীবেশী ভারতচন্দ্রকে চিনতে পেরে পরিবারে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। শেষে সংস্কৃত ও ফার্সি ভাষায় পন্ডিত ভারতচন্দ্রকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সভাকবি হিসাবে নিযুক্ত করেন এবং মূলাজোড় গ্রামে বাস করার আনুমতি দেন। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ভারতচন্দ্র সেখানেই দেহত্যাগ করেন।
ভারতচন্দ্রের জীবৎকাল খুব বেশি নাহলেও তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর অস্থিরতার যুগে বেশ কয়েকটি কাব্য রচনা করে সাহিত্যের ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছেন। ভারতচন্দ্র প্রথম জীবনে সত্যপীরের ব্রতকথা অবলম্বনে ‘সত্যপীরের পাঁচালী’ নামক একটি কাব্য রচনা করেন। এছাড়াও ‘রসমঞ্জরী’ ও ‘নাগাষ্টক’ নামক দু’টি গ্রন্থও রচনা করেন। তিনি কয়েকটি ভাষার মিশ্রণে ‘চন্ডীনাটক’ নামে একটি নাটক রচনার পরিকল্পনা করেন। তবে এগুলি ভারতচন্দ্রকে খুব বেশি খ্যাতি দেয়নি। তাঁর খ্যাতি মূলতঃ ‘অন্নদামঙ্গল কাব্যটির জন্য। ‘অন্নদামঙ্গল কাব্যটি পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত তিনটি খন্ডে বিভক্ত। এই খন্ডগুলি হল— ১) অন্নদামঙ্গল, ২) কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর এবং ৩) অন্নপূর্ণা মঙ্গল বা মানসিংহ। ভারতচন্দ্র ১৭৫২-৫৩ খ্রিস্টাব্দে কাব্যটি রচনা করেছেন বলে মনে করা হয়।
‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যের প্রথম খন্ডটিতে নবাব আলিবর্দি কতৃক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বন্দী হওয়া এবং দেবী আন্নপূর্নার কৃপায় উদ্ধারের কথা আছে। ভারতচন্দ্র যে কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায় কাব্যটি লিখছেন তা নিজে স্বীকারও করে নিয়েছেন। এই কাব্যের প্রথমে শিব-দুর্গার ঘর-গৃহস্থালীর কাহিনি ও অভাবের বর্ণনা আছে। এই অভাব দুর করার জন্য শিব ঘরণী পার্বতী অন্নপূর্ণা রূপে তার পূজা প্রচারের আশা ব্যক্ত করেছেন। এরপর গতানুগতিক মঙ্গল কাব্যের কহিনির মতই অভিশাপগ্রস্ত হয়ে কোন দেবতা স্বর্গভ্রষ্ট হয়েছেন এবং মর্তে এসে দেবী অন্নপূর্নার পূজা প্রচার করেছেন। এই মূল কাহিনির পাশাপাশি ভারতচন্দ্র শিব-দুর্গা এবং ব্যাসদেবকে নিয়ে কাশী নির্মাণের এক উপকাহিনিও সংযােজন করেছেন। এই খন্ডের একটি ছােট ও ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ঈশ্বরী পাটনী।
‘অন্নদামঙ্গল’-এর দ্বিতীয় খন্ড অর্থাৎ ‘বিদ্যাসুন্দর’ বা ‘কালিকামঙ্গল’-এ রাজকুমারি বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয় কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে। সুন্দর কিভাবে বিদ্যার গােপন কক্ষে প্রবেশ করে ধরা পড়ে যায় এবং বিচারে শিরােচ্ছেদের দন্ডাদেশ পায় তার বর্ণনা আছে। কবি দেখিয়েছেন সুন্দরকে বাচাতে দেবী অন্নদা কালিকার রূপ ধরে মশানে গিয়ে হাজির হন। এ কাব্যের অনেক যায়গায় আদিরসের বাড়াবাড়ি আছে জন্য অনেকে একে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট বলেছেন।
‘অন্নদামঙ্গল’-এর তৃতীয় খন্ডটি সবচেয়ে নিকৃষ্টতম। এখন্ডে ভারতচন্দ্র দেবী অন্নদার পূজা প্রচারের সঙ্গে ইতিহাসের যােগ দেখানাের চেষ্টা করেছেন। তবে এখানে ইতিহাসের ঘটনার চাইতে অনৈতিহাসিক ঘটনা এবং কল্পনাই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।
যাইহােক ভারতচন্দ্রের কবি কৃতিত্ব মূলতঃ এই ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যটির জন্যই। এই কাব্যের নানা ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের গতানুগতিক ধারায় মঙ্গলকাব্য রচনা করলেও তাঁর কাব্যটিকে বারবার ‘নতুনমঙ্গল’ বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন
‘নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়।”
ভারতচন্দ্রের কাব্যের এই নতুনত্ব ধরা পড়েছে তার কাহিনি পরিকল্পনায়, বর্ণনারীতিতে, চরিত্রচিত্রণে ও ভাষা-ছন্দ-অলংকার এবং প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহারের মাধ্যমে।
ভারতচন্দ্র তাঁর ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যটি দেবী অন্নদার পূজা প্রচারের জন্য রচনা করলেও তার মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে খুশী করা। কাব্যটিতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নাম বারবার ব্যবহার দেখেই তা বােঝা যায়। স্বাভাবিকভাবেই কাব্যের কাহিনি পরিকল্পনাতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে খুশি করার একটা ব্যপার ছিল। এজন্য বর্ণনারীতিতে ভারতচন্দ্র অনেক সময় স্বাধীনভাবে এগােতে পারেননি। তবে এই কাব্যে দৈব ঘটনার চেয়ে মানবিক ঘটনাই অনেক বেশি প্রধান্য পেয়েছে। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যখন বাংলায় স্বাধীন নবাবীর সূচনা হয় তখন সাধারন বাঙালীদের দুরবস্থা কোথায় পৌছেছিল তা ভারতচন্দ্রের কাব্যটি পড়লেই বােঝা যায়।
ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’-এর চরিত্রগুলিও যথেষ্ট উন্নতমানের সৃষ্টি। শিব, পার্বতী প্রমুখ দেবচরিত্রকে তিনি একাব্যে সাধারনের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন। তাই দেখা যায় শিবের ঘরে নিত্য অভাব এবং এই অভাব নিয়ে শিব-পার্বতী সাধারণ মানবুষের মতই কোন্দল করে। ভারতচন্দ্রের ব্যাসদেব আধুনিক উপন্যাসের খল চরিত্রের পূর্বাভাস। হরিহর ও তার মার দারিদ্র এই কাব্যে বাস্তব সম্মতভাবে চিত্রিত। আর ঈশ্বরী পাটনী ক্ষুদ্র হলেও ভারতচন্দ্রের কাব্যের সম্পদ। তাঁর উক্তি,
‘‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।”
তাকে বাংলা সাহিত্যে অমর করে রেখেছে। ঈশ্বরী পাটণির এই উক্তি থেকেই বাংলা সাহিত্য দৈব মূখীনতা কাটিয়ে মানব মূখীন হয়ে উঠেছে। ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে ভাষা ব্যবহারে ভারতচন্দ্র অভিনবত্ব এনেছেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন,
“পড়িয়াছি যেইমত কহিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লােকে বুঝিবারে নারি।
না রবে প্রসাদগুন, না হবে রসাল।
রচিয়াছি কবি ভাষা যাবনী মিশাল।।”
ভারতচন্দ্রের এই যাবনী মিশাল ভষায় তৎসম, অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি সব ভাষার শব্দই স্থান পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি শিষ্ট শব্দের পাশাপাশি অশিষ্ট (Slang) শব্দের প্রয়ােগ করেছেন।
ছন্দ-অলংকার প্রয়ােগে ভারতচন্দ্র যথেষ্ট স্বচ্ছন্দ ছিলেন। প্রচলিত পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী ছন্দের পাশাপাশি বাংলা লৌকিক ও সংস্কৃত (ভূজঙ্গ প্রয়াস, তৃনক) ছন্দেরও সুন্দর প্রয়ােগ ঘটিয়েছেন। আবার অলংকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি শব্দালংকার, অর্থালংকারের সবগুলিকেই সার্থকভাবে প্রয়ােগ করেছেন। যেমন—
১) ‘‘ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুনে।” (যমক)
২)‘‘অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুন।
কোনগুন নাই তার কপালে আগুন৷৷ (ব্যজস্তুতি)।
ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে এমন কিছু কথা বলেছেন যা এখনও বাংলায় প্রবাদরূপে প্রচলিত। যেমন,
১) “বড় পীরিতি বালির বাঁধ।
ক্ষণেকে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ।।”
২) “মন্ত্রের সাধন, কিংবা শরীর পাতন।”
৩) “নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।”
৪) “সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।”
৫) “খুন হয়েছিনু বাছা নুন চেয়ে চেয়ে।।”
ভারতচন্দ্র ছিলেন মধ্যযুগের শেষ শক্তিধর কবি। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর (১৭৬০) পর আর কোন কবি জন্মান নি, যিনি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিক ধারাটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে গদ্যের আবির্ভাব ঘটে। আর গদ্যের আবির্ভাবের সাথে সাথে বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূচনা হয়। মধ্যযুগের সাহিত্য ছিল মূলতঃ দৈব নির্ভর, তাই এই যুগকে বলে ভক্তির যুগ। আর আধুনিক যুগ মানব নির্ভর, তাই এই যুগকে বলে যুক্তির যুগ। ভারতচন্দ্র ভক্তিরযুগে দাঁড়িয়ে তাঁর কাব্যে মানবতার কথা বলেছিলেন জন্য তাঁর কাব্যে আধুনিকতার অনেক লক্ষন প্রকটিত হয়েছে। এজন্য অনেকে তাঁকে মধ্যযুগ বা আধুনিক যুগ কোন যুগেরই কবি বলে চিহ্নিত না করে যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলে অভিহিত করেছেন। যেহেতু তিনি দু’টো যুগের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সাহিত্য চর্চা করেছিলেন এবং তাঁর কাব্যে মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগ দু’টি যুগেরই প্রভাব পড়েছিল, তাই তাঁকে আমরা যুগ সন্ধিক্ষণের কবি বলতেই পারি। তবে ভারতচন্দ্রের মত প্রতিভাধর কবিদের কোন যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা ঠিক নয়। হয়ত এই কারনেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন,
“রাজসভার কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল গান রাজকন্ঠ্যের মনিমালার মত। যেমন তাহার উজ্জ্বলতা, তেমন তাহার কারুকার্য।”
[লেখক সহকারী অধ্যাপক, ইসলামপুর কলেজ]
‘নবজাগরণ’ অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপ্লিকেশনটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।
![]()
‘নবজাগরণ’ এর টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।
‘নবজাগরণ’ এর ফেসবুক পেজে লাইক করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

 নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা
নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা