আমাদের স্বাধীনতা লাভের নেপথ্যে রয়েছে ভারতীয় জনগণের আপসহীন ধারাবাহিক সংগ্রাম। ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সেই ধারাবাহিক সংগ্রামেরই অন্যতম দিক। ১৭৫৭-র পলাশী যুদ্ধের পরই এই বিদ্রোহ বঙ্গদেশের ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সবচেয়ে বড় আঘাত দেয়। ব্রিটিশ বিরােধী এই বিদ্রোহ ৩৭ বছর (১৭৬৩-১৮০০) স্থায়ী হয়। কৃষক, কারিগর, ইংরেজ শাসনে সামন্ত রাজা ও জমিদারদের ছত্রভঙ্গ বেকার সৈন্য, লাঠিয়াল, পাইক, বরকন্দাজ আর ফকির-সন্ন্যাসীদের সম্মিলিত উদ্যোগে ১৮শতকের শেষ চার দশক এই বিদ্রোহ খুবই সক্রিয় ছিল।
১৭৭০ সালে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের (১১৭৬ সন) সময় থেকে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে যুক্ত হয় কোম্পানির নির্মম শােষণ, অত্যাচার। আঠারাে শতকের ছয়ের দশকে ঢাকার মসলিন শিল্পের কারিগরদের উপর অত্যাচার শুরু হয়, বৃদ্ধাঙ্গুলি কেটে দিয়ে কারিগরদের পঙ্গু করে ফেলার চেষ্টা চলে। দেশের মানুষের দুর্দশার সীমা ছিল না। ফলে সাধারণ মানুষ দলে দলে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহে যােগ দিয়ে কোম্পানির শাসন প্রায় বিকল করে দেয়। ১৭৭২ সালের মধ্যে বিদ্রোহ রংপুর থেকে অতি দ্রুত ঢাকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহীদের প্রবল আক্রমণের মুখে ইংরেজ রাজশক্তি প্রায় কর্তৃত্বহীন হয়ে পড়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে এই বিদ্রোহ ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় গণশক্তির প্রথম গৌরবময় সশস্ত্র অভূত্থান। বিদ্রোহ মূলত ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। মুসলিমদের মাদারিয়া সম্প্রদায়ের ফকিররা ছিলেন ফকির বিদ্রোহের হােতা। আর হিন্দুদের শৈব সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা ছিলেন সন্ন্যাসী বিদ্রোহের হােতা। উভয় সম্প্রদায়ের এই মিলিত সংগ্রামকে ব্রিটিশরা ‘হিন্দুস্থানের যাযাবর’দের সংগ্রাম বলে অভিহিত করেছেন। এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পত্তনের শুরুতে সন্ন্যাসী ও ফকিররা ব্রিটিশ শক্তিকে ও ব্রিটিশ আশ্রিত দেশীয় জমিদার, মহাজন ও বেনিয়াদের বিব্রত করে রেখেছিলেন। এই সন্ন্যাসী ফকিরদের সঙ্গে যােগ দিয়েছিলেন মুঘল নৃপতি ও নবাবদের কর্মচ্যুত সিপাই সৈন্যরা। এর ফলে এই ফকিরসন্ন্যাসীদের শক্তি অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছিল। আর সি মজুমদার সন্ন্যাসী-ফকিরদের সামরিক সামর্থ্য প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লিখেছেন, “…their fighting qualities were not negligible…they threatened to sweep away the English power completely”.১
সেদিনের ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অবিসংবাদী নেতা ছিলেন মজনু শাহ ওরফে বাকের আলি। মজনু শাহ সত্যিই ফকির ছিলেন না ওই ছদ্মনামে আসলে কোনও প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, প্রতিপত্তিশালী জনৈক জনপ্রিয় মুসলমান ব্যক্তিই এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। খান চৌধুরী আমানতুল্লা আহমদের ‘কোচবিহারের ইতিহাসে’ এবং নগেন্দ্রনাথ বসুর ‘বিশ্বকোষে’ উল্লেখিত বকেয়া মহম্মদ বা বাকের আলি নামে রংপুরের জনৈক ভূস্বামীই মজনু শাহ ছদ্মনামে ব্রিটিশ বিরােধী গণশক্তিকে চালনা করতেন, অথচ প্রকাশ্যে চলাফেরা করতেন ব্রিটিশদের চোখের সামনেই। বাকের ছিলেন মুঘল বংশােদ্ভূত এবং তার এক কন্যার সঙ্গে দিল্লীর দ্বিতীয় আকবর বাদশাহের বিবাহ হয়। সেকালের মুঘল পরিচয় ছিল উত্তর ভারতীয় ঐক্যের প্রতীক এবং মজনুর মুঘল পরিচয় প্রচারিত হলে বাংলার জনযুদ্ধ সমগ্র উত্তর ভারতেই বিস্তৃত হয়ে পড়তে পারে, এই আশঙ্কা থেকেও ইংরেজরা মজনু শাহের প্রকৃত পরিচয় গােপনে যত্নপর হয়েছিল বলে মনে হয়।

মজনু শাহ ১৭৩৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার বিদ্রোহী জীবনে উত্তরণের পশ্চাতে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তা হল: যৌবনে ফকির বা দরবেশ হওয়ার তার সাধ জাগে, তাই সাধনাও শুরু হয়। উপযুক্ত আধ্যাত্মিক পীরের সন্ধানে তিনি নানা স্থান ঘুরেছিলেন। এ উদ্দেশ্যে পাটনা থেকে তিনি গিয়েছিলেন গৌড়ে হযরত নুর কুতুব-উল-আলমের সমাধিক্ষেত্রে। সেখান থেকে স্বপ্নযােগে তিনি নির্দেশ পান হয়রতনুর কুতুব-এর পীর বীরভূমের রাজনগরে সমাধিস্থ দরবেশ শাহ হামিদউদ্দীনের সঙ্গে তিনি যেন সাক্ষাৎ করেন। আধ্যাত্মিক পথের সন্ধানী মজনু শাহ ছুটে চললেন বীরভূমের রাজধানী রাজনগর শহরে। এ সময় চলছিল সারা দেশ জুড়ে সর্বনাশা দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তরের বিভীষিকা। রাজনগর-সাধক হামিদউদ্দীনের সমাধির খাদেম মজনু শাহকে দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষের সেবায় আত্মনিয়ােগ করতে ও দেশের শত্রু প্রজা-শােষক ব্রিটিশকে দেশ থেকে তাড়াতে অনুপ্রাণিত করেন।
উত্তর ভারতের কানপুরের কাছে ‘মীরখানপুর’ বা মাখনপুর বা মকানপুরে মজনু শাহ বাস করতেন। এখান থেকে বিহার ও উত্তর বাংলায় তার অভিযান তৎপরতা চলত। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের বগুড়া জেলায় ‘মহাস্থানগড় বা মস্তানগড়ে তিনি একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর সামরিক তৎপরতার এটি প্রধান কেন্দ্র ছিল বাংলাদেশ। বগুড়া থেকে বারাে মাইল দক্ষিণে মাদারগঞ্জে তিনি আর একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে মজনু শাহের অভ্যুদয়ের পরেই তাঁর প্রথম কর্তব্য ছিল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ফকিরদের সংঘবদ্ধ করা। তার দলে বহু হিন্দু সন্ন্যাসীও যােগ দিয়েছিলেন। প্রায় দেড় দশক পর্যন্ত তিনি বিহার ও বাংলার ব্রিটিশ প্রশাসকদের ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিলেন। শাহ মজনুর আশঙ্কায় ইংরাজ কর্মচারী ও কুঠিয়ালরা যে সন্ত্রস্ত ছিলেন তার প্রমাণ তাঁদের তদানীন্তন লেখা চিঠিপত্রে পাওয়া যায়।২
মজনু শাহ বুরহানা তরিকার শায়খ ছিলেন। এজন্য তিনি মজনু শাহ বুরহানা নামেও খ্যাত ছিলেন। বুরহানা তরিকার প্রবর্তক বুরহানউদ্দীন বুরহানা মূলত জালালিয়া তরিকার শায়খ ছিলেন। জালালিয়া তরিকা সােহরাওয়ার্দীয়া তরিকার শাখা বিশেষ।৩ Letters from Charles Grant to Augustus Clevand and Gilbert Irouside 6th & 8th March, 1783, Revenue Dept. Consultation No.14, dated 08.04.1783 and Public Dept. original Consultations No.13 &15, dated 15.03.1783. অনুসারে মজনু শাহ্ প্রাথমিক অবস্থায় মাদারিয়া তরিকাভুক্ত ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি বুরহানিয়া তরিকাভুক্ত হন।৪
শাহ সুজা (১৬৩৯-১৬৬০) প্রদত্ত ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দের এক ফরমানে শাহ সুলতান হাসান মুরিয়া বুরহানার উল্লেখ পাওয়া যায়।৫ তিনি দিনাজপুর জেলা সদর থেকে ২৬ মাইল দূরবর্তী হেমতাবাদ থানাধীন বালিয়াদীঘিকে কেন্দ্র করে ইসলাম প্রচার করতেন। সম্রাট শাহ সুজা সুফী নেতা শাহ সুলতান মুরিয়া বুরহানাকে সনদে বিশেষ অধিকার প্রদান করেছিলেন।৬ তিনিও বুরহানিয়া তরিকার শায়খ ছিলেন। শাহ সুজা কর্তৃক প্রদত্ত ফরমানে উল্লেখ করা হয়েছে : “Whenever you wish to go out for the guidence of the people or for travel into the cities, countries divisions and all sorts of places where you like to go according to your free will & inclinations you may take all the articles of the Jueus e.g. bannars, standerds, flags, poles, stuffs, band, mahi and muratibs etc.
You will be entitled within the countries of Bengal, Bihar and Orissah to consficats as you like properties to which there is no heir or pirpal or rent free tenures. When you pass through any tract or the country the landlords and trenants will supply you with provisions.
You will also be able for the good of mankind & the faith of Islam to be guided by the learned people. No cess contribution of any kind will be levied.’৭
১৭৮২ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী ভারতের গভর্ণর জেনারেলের নিকট লিখিত এক সরকারী পত্রে মজনু শাহ সম্পর্কে লেখা হয় : “A famous leader of the Sannyasies or badithi.’ ওই তারিখের অপর এক পত্রে — leader of the begger-banditi’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে তার নেতৃত্বের বিষয়টি প্রমাণিত হয়।৮
Edward Thompson & G.. T. Garratt gå afoglista Pelagis your loss বলেন, বিদ্রোহীদের প্রকৃত পরিচয় যাই হােক না কেন তাদের বিদ্রোহ হেস্টিংসের সময়ে সর্বাপেক্ষা রহস্যময় ঘটনা। হেস্টিংস তাদেরকে হিন্দুস্থানের যাযাবর নামে অভিহিত করেছেন। তিনি যে কয়েকটি মিথ্যা ধারণার সৃষ্টি করে গেছেন এটি তার মধ্যে অন্যতম। …বিদ্রোহীদের অভ্যুত্থান আজও রহস্যাবৃত এবং ভারতবাসীদের দিক থেকে এ রহস্য উদঘাটন করে এর নির্ভুল ব্যাখ্যা করা প্রয়ােজন।৯
১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মজনু শাহ ও তাঁর খলিফাগণ বৃটিশ বিরােধী অসংখ্য অভিযান পরিচালনা করেন। তারমধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযান ও অপারেশন সম্বন্ধে আলােকপাত করে তার জীবন-বৃত্তান্তের সম্পূর্ণতা প্রদানের চেষ্টা করা হল :
ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রথম অভিযান পরিচালিত হয় ১৭৬৩ খিস্টাব্দে ঢাকায় ইংরেজ কুঠির উপর। এ আকস্মিক আক্রমণে কুঠির ইংরেজ বণিকগণ ভয়ে এমন সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে যে, আক্রমণকারীদের কোনরূপ বাধা দেওয়ার চেষ্টা না করে তারা নিজেদের প্রাণ বাঁচানাের জন্য সমস্ত ধন-সম্পদ ফেলে কুঠির পিছন দরজা দিয়ে অন্ধকারে নৌকাযােগে পলায়ন করে। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহীরা আবার রামপুর-বােয়ালিয়ার কুঠি আক্রমণ করে ইংরেজ বণিক ও স্থানীয় জমিদারদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করে। এ দুটি বিদ্রোহের নেতৃত্বে কে ছিলেন তা পুরােপুরি জানা যায় না। সম্ভবত কোন সন্ন্যাসী বা ফকির নেতা বিদ্রোহীদের সংগঠিত করে এ আক্রমণ পরিচালিত করেছিলেন।
মজনু শাহের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী ফকিরদের আক্রমণ পরিচালিত হয় ১৭৬৬ থেকে। ১৭৬৬ খিস্টাব্দে উত্তরবঙ্গ ও নেপালের সীমান্তে ইংরেজ বণিকদের প্রতিনিধি মার্টেল বহু লােকজনসহ কাঠ কাটতে গেলে মজনু শাহের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহীরা তাদের সকলকে বন্দী করে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এ ঘটনার পর রংপুরে মােতায়েনকৃত ক্যাপ্টেন ম্যাকেঞ্জির নেতৃত্বাধীন এক বিশাল সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহীদের দমনের জন্য আগমন করেন। মজনু শাহের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী বাহিনী শত্রু পক্ষের শক্তি দেখে গভীর জঙ্গলে পলায়ন করে। সেনাপতি ম্যাকেঞ্জি সুবিধা করতে না পেরে ফিরে যান এবং ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে আরাে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে পুনরায় এ অঞ্চলে ফিরে এলে বিদ্রোহীরা যুদ্ধ এড়িয়ে উত্তরে চলে যায়। শীতের প্রারম্ভে বিদ্রোহীরা ইংরেজ বাহিনীর উপর আক্রমণ আরম্ভ করে। বিদ্রোহীরা রংপুর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। অপর দিকে ইংরেজ বাহিনীকে আরাে শক্তিশালী করার জন্য লেফট্যান্যান্ট কিথ বহু সৈন্য সামন্তসহ ম্যাকেঞ্জির বাহিনীর সাথে যােগদান করেন। শত্রুর শক্তি দেখে বিদ্রোহীরা আবার পশ্চাদপদসরণ করে ইংরেজ বাহিনীকে আরাে গভীর জঙ্গলের ভিতর টেনে নিয়ে যায়। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নেপালের সীমান্তে মােরঙ্গ অঞ্চলে বিদ্রোহীরা তাদের সমস্ত শক্তি সংহত করে ইংরেজ বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ অতর্কিত আক্রমণে ইংরেজ বাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। সেনাপতি কিথ বহু সৈন্যসহ এ যুদ্ধে নিহত হয়।১০
১৭৬৯-এ যুদ্ধে পরাজয়ের পর শাসকগােষ্ঠীর মধ্যে ভীষণ ত্রাসের সৃষ্টি হয়। বিদ্রোহীদের বিদ্রোহ দমনের জন্য ইংরেজ সরকার দেশের বিভিন্ন জেলায় ও অঞ্চলে সুপারভাইজার নামক একদল কর্মচারী নিয়ােগ করে, তাদের মাধ্যমে বিদ্রোহীদের গােপন সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করে। কিন্তু এতেও কোন ফল হয়নি বরং নতুন নতুন অঞ্চলে বিদ্রোহীরা ছড়িয়ে পড়ে।
১৭৬৯ খিস্টাব্দের বিদ্রোহের পর বিদ্রোহীরা উত্তরবঙ্গে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য দিনাজপুর, বগুড়া, জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন স্থানে মাটির প্রাচীর ঘেরা দুর্গ নির্মাণ করে। এদের মধ্যে প্রাচীন শহর মহাস্থানগড় ও পৌণ্ড্রবর্ধনের দুর্গ বিশেষভাবে উল্লেখযােগ্য। মহাস্থানগড়ের দুর্গটি চারদিকে খাড়া পাহাড়ে ঘেরা। বিদ্রোহীরা এই প্রাকৃতিক দুর্গটিকে আরাে সুরক্ষিত করে তােলে।১১ ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে মজনু শাহের পরিচালনাধীন আড়াই হাজার বিদ্রোহী সৈন্যের সাথে লেক্ট্যান্যান্ট টেলর ও লেট্যান্যান্ট ফেণ্টহাম পরিচালিত এক বিরাট ইংরেজ বাহিনীর সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মজনু শাহ মহাস্থানগড়ের সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এরপর তিনি বিদ্রোহের প্রয়ােজনে বিহার গমন করেন।
বিহার গমনের কয়েক মাস পর মজনু শাহ পুনরায় সক্রিয় হয়ে ওঠেন। এ সময় তিনি দেশের সকল শ্রেণী, এমনকি জমিদারগণও যাতে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয় সে প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। তাঁর এ প্রচেষ্টায় ইংরেজ সরকারের বহু কর্মচারী বিদ্রোহীদের সাহায্য করতে অগ্রসর হয়। অনেকে চাকরী ছেড়ে দিয়ে বিদ্রোহে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। এ পর্যায়ে মজনু শাহ বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দেশের ধনী ও জমিদারগণ যাতে জনগণের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয় তার জন্য চেষ্টা চালান।
১৭৭২-এর জানুয়ারি মাস হতে নাটোর অঞ্চলে মজনু শাহের নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা বিশেষ সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারা এ অঞ্চলের জমিদার এবং ইংরেজ শাসকদের অনুচরদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করত এবং তাদের বেঁধে নিয়ে গিয়ে কৃষকদের উপর অত্যাচারের প্রতিশােধ নিত।
১৭৭২-এর ২২শে জানুয়ারি রাজশাহীর সুপাভাইজার এক সরকারী পত্রে লিখেছেন, “বুরহানা ফকির মজনু শাহ বহু সংখ্যক লােকজন নিয়ে পরগণায় প্রবেশ করে একজন প্রধান ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে বন্দী (জিম্মী) করে রেখেছেন। এ বাহিনীতে বহু সংখ্যক ফকির রয়েছে, তাদেরকে প্রতিহত বা মােকাবিলা করা কঠিন।”১২
১৭৭৩-এর ডিসেম্বর মাসে মজনু শাহ ৭০০ লােকের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে দিনাজপুরের মেসিদা নামক স্থানে আস্তানা গড়ে তােলে। তিনি সেখানকার জমিদারদের নিকট পাওনা অথবা রাজস্ব বাবদ ১৫০০/- দাবি করেন এবং জমিদারদের গ্রেফতার করে ধরে আনার জন্য দুইশত ফকিরকে প্রেরণ করেন। কিন্তু জমিদারের পলায়নের খবর পেয়ে এই ফকির দল প্রায় ৩০ মাইল দূরবর্তী লেম্ববাড়িয়া পর্যন্ত উক্ত জমিদারকে ধাওয়া করে। ফকির বাহিনী ঐ পরিমাণ অর্থ উক্ত জমিদারের কাচারি থেকে আদায় করে। এই সময় থেকে ফকির বাহিনী সেখানকার সরকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ফলে বিদ্রোহের আঘাতে সরকারী শাসনব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। বিদ্রোহীরা বহু স্থানে ইংরেজ সরকারের সংগৃহীত রাজস্ব লুণ্ঠন করার ফলে রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে যায় এবং বিহার ও বঙ্গদেশেইংরেজদের সামরিক মর্যাদা হ্রাস পেতে থাকে। ফলে শাসকগণ বাধ্য হয়ে সকল শক্তি নিয়ােগ করে বিদ্রোহের মূলােচ্ছেদ করার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে।
বিদ্রোহ দমনের জন্য শাসকশ্রেণী গ্রামাঞ্চলে ও শহরে নতুন নতুন আইন প্রবর্তন করে বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করে। বিদ্রোহীদের গােপন সংগঠন, গােপন যােগাযােগ ব্যবস্থা ও চলাচল সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহের জন্য জমিদারদের, এমনকি কৃষকদেরও আইনের দ্বারা বাধ্য করা হয়েছিল। গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ঘােষণা করলেন, যে গ্রামের কৃষকগণ ইংরেজ শাসকদের নিকট বিদ্রোহীদের সংবাদ দিতে অস্বীকার করবে এবং বিদ্রোহীদের সাহায্য করবে তাদের দাস হিসাবে বিক্রয় করা হবে। এ ঘােষণা অনুসারে কয়েক সহস্র কৃষককে ক্রীতদাসে পরিণত করা হল। বিভিন্ন গ্রামের বহু কৃষককেঅবাধ্যতার অভিযােগে অভিযুক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিস্বরূপ গ্রামের মধ্যস্থলে ফঁসীকাষ্ঠে হত্যা করে গ্রামবাসীদের ভয় দেখানাের জন্য মৃতদেহগুলাে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। বিদ্রোহী বা তাদের সাথে সম্পর্ক আছে এরূপ সন্দেহ হলে যে কোন লােককে বিনা প্রমাণে ফাসী দেবার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। যাদের ফাসী দেওয়া হত তাদের পরিবারের সমস্ত লােককে চিরকালের জন্য ক্রীতদাসে পরিণত করা হত।১৩ শাসকবর্গের এমন পদক্ষেপের ফলে বিদ্রোহ সাময়িকভাবে স্তমিত হয়ে পড়ে। ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছােটখাট কয়েকটি আক্রমণ ছাড়া বিদ্রোহীদের তেমন কোন তৎপরতা আর দেখা যায়নি।
১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগ হতে পুনরায় বিদ্রোহ শুরু হয়। এ সময় মজনু শাহ উত্তরবঙ্গে ফিরে এসে বিদ্রোহীদের আবার সঙ্গবদ্ধ করার ও নতুন লােক সংগ্রহের চেষ্টা করেন। দিনাজপুর জেলায় মজনু শাহের উপস্থিতির সংবাদে শাসকবর্গ এতই ভীত হয়েছিল যে, অবিলম্বে জেলার সকল স্থান হতে রাজস্বের সংগৃহীত অর্থ দিনাজপুর শহরের সুরক্ষিত ঘাটিতে স্থানান্তরিত করে রাজকোষের রক্ষী বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু মজনু শাহ আপাতত কিছুই করলেন না। সুতরাং ভীত-সন্ত্রস্ত শাসনকর্তারা মজনুর প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে তার নিকট একটি পত্র প্রেরণ করে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য জানার চেষ্টা করে এবং তার সৈন্যদল ভেঙ্গে দেয়ার অনুরােধ করেন। অপরদিকে বগুড়া হতে তাঁর বিরুদ্ধে একটি বিশাল ইংরেজ বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে মজনু শাহ আপাতত যুদ্ধ এড়াবার জন্য করতােয়া নদী ও ময়মনসিংহ জেলার সীমান্ত পার হয়ে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে ঘাঁটি স্থাপন করেন।
১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ নভেম্বর একটি ইংরেজ সৈন্যদলের সাথে মজনুর বাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ১৪ নভেম্বর একটি ইংরেজ সৈন্যদলের সাথে মজনুর বাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ১৪ নভেম্বর তারিখে এক পত্রে লেফট্যান্যান্ট রবার্টসন জানান, “গত রাত নটায় নিজের ক্যাম্প হতে রওয়ানা হয়ে প্রায় নয় ক্রোশ পথ অতিক্রম করার পর আজ সকালে সূর্যোদয়ের পূর্বেই আমরা ফকীর মজনুর শিবিরের নিকট উপস্থিত হলাম। আমাদের আগমন সম্পর্কে তাদের কাছে ছিল না কোন পূর্বাভাস। এ জন্যই তারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দিকে বৃত্তাকারে অবস্থান করছিল। সংখ্যায় ফকীর সন্ন্যাসীরা তিন শতাধিক হলেও তাদের নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা এতই শিথিল ছিল যে তাদের বিশ গজের মধ্যেও আমাদের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে নি। আমাদের দেখা মাত্রই তারা অস্ত্রহাতে আদের আক্রমণে উদ্যত হল এবং এ সময়ই আমাদের সৈন্যদের গুলি বর্ষণের নির্দেশ দিই। ফকীর সন্ন্যাসী দল পেছনের জঙ্গলে আশ্রয় নিল এবং আমাদের প্রতি পাল্টা গুলি বর্ষণ শুরু করল। এ গুলি বর্ষণে আমাদের কয়েকজন সৈন্য আহত হয় এবং আমার পায়েও একটা গুলি লাগে। আমরা ভাবতে পারিনি যে অপ্রস্তুত ফকির সন্ন্যাসীরা এরূপ অতর্কিত আক্রমণের পরও আমাদের রুখে দাঁড়াতে পারবে। প্রায় আধ ঘণ্টা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর এ ফকির দল স্থান ত্যাগ করে। তাদের নেতা মজনু শাহও অশ্বপৃষ্ঠে পলায়নে সমর্থ হয়।”১৪
১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে মজনু শাহের নেতৃত্বে ফকির বাহিনীর আবার রংপুরে আগমনের কথা জানা যায়। ১৭৮২-এ ময়মনসিংহের আলাপসিংহ পরগণায় ফকিরদের তৎপরতা তীব্র আকার ধারণ করে। এ সময় পুখরিয়া নামক স্থানে মজনুর সাথে কোম্পানী সরকারের সৈন্যদলের এক সংঘর্ষ হয় এবং মজনু শাহ শেষ পর্যন্ত তার অনুসারীদের নিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যান।১৫
১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মজনু শাহ এক হাজার সশস্ত্র অনুচরসহ ময়মনসিংহ জেলার মধ্য অঞ্চলে উপস্থিত হলে জেলার রেসিডেন্ট মজনর নিকট একটি পত্র লিখে কোনরূপ উৎপীড়ন ও যুদ্ধবিগ্রহ না করে অবিলম্বে জেলা ত্যাগ করার জন্য তাকে অনুরােধ করেন। কিন্তু মজনু শাহ এ অঞ্চলে যুদ্ধ করতে আসেননি, তিনি এসেছিলেন এ জেলার বিভিন্ন বিদ্রোহী দলের মধ্যে সংযােগ স্থাপন করে আবার পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ চালাবার ব্যবস্থা করতে। তাই দেখা যায়, সঙ্গে একটি বিরাট সৈন্যদল থাকলেও তিনি শত্রুদের সাথে যুদ্ধ এড়িয়ে চলেছেন, এমনকি মধুপুরের অতি দুর্গম পথ পাড়ি দিয়েছেন। এভাবে ঘুরে ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চল দিয়ে মজনু উত্তরবঙ্গে ফিরে যান।
১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে পুনরায় ময়মনসিং জেলায় মজনু শাহর উপস্থিতির সংবাদে গভর্ণর জেনারেল হেস্টিংস ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁরা সেনাপতিদের উদ্দেশ্য করে লিখেন, “আমরা আবার জাফর শাহী পরগণায় (ময়মনসিংহ) মজনুর উপস্থিতির সংবাদ পাইতেছি। আমরা প্রতি বছর এ লােকটার উৎপাত সহ্য করতে পারি না। আমরা শুনে এসেছি এ লােকটা নাকি ব্রহ্মপুত্র নদের উপরেই বহাল তবিয়তে বাস করে, আর প্রতি বছর আমাদের কোম্পানির জেলাগুলি জ্বালিয়ে মারে, সে সকল স্থান হতে ইচ্ছামত টাকা আদায় করে, অথচ কেহ তাকে বাধা দিতে পারে না।”১৬ তারপর মজনু শাহকে ধরার জন্য কোম্পানী সরকার কয়েকটি প্রধান সৈন্যদল ময়মনসিংহের দিকে প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা আসার আগেই মজনু মালদহে প্রবেশ করেন। মালদহ জেলায় ঘুরে ঘুরে এবার তিনি ইংরেজ কুঠি ও জমিদারদের উপর আক্রমণ করে তাদের সঞ্চিত অর্থ লুণ্ঠন করতে থাকেন। এ সময় রক্ষী বাহিনী হতে বহু বরকন্দাজ মজনুর সাথে যােগদান করে। মজনুকে ধরার জন্য মালদহেও কয়েকটি ইংরেজ সৈন্যদলর ছুটে আসে। কিন্তু দেখা গেল এ সকল সৈন্যদল মালদহে পৌঁছাবার বহু পূর্বেই মজনু এ জেলা ত্যাগ করে বহুদূর চলে গেছেন।
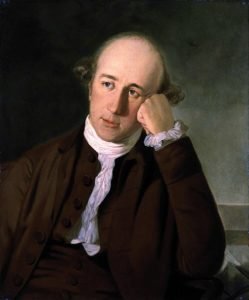
মজনু শাহকে ধরে বিদ্রোহীদের আক্রমণ বন্ধ করার শত চেষ্টা করেও গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ব্যর্থ হন। এর ফলে গভর্ণর জেনারেল ও রেভিনিউ বাের্ড বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েন। সকল সেনাপতি ও কালেক্টরদের ব্যর্থতার কৈফিয়ত বিশ্লেষণ করে তারা এর একটা কারণ খুঁজে বের করেন। তারা এ সিদ্ধান্তে পৌছলেন যে, পূর্বে কয়েকবার মজনুকে সাফল্যের সাথে বাধা দেওয়া ও তাকে আক্রমণ করা সম্ভব হয়েছে বটে, কিন্তু তার উৎপাতের জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি। জমিদাররাও তার চলাচল সম্পর্কে সংবাদ দিতে ভয় পায়। সে তার অনুচরদের এমনভাবে শিক্ষা দিয়েছে যে, পশ্চাদ্ধাবন করলেই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং এমন একটা স্থানে আবার মিলিত হয় যে স্থানে তাদের উপস্থিতি কল্পনাও করা যায় না।১৭
মজনু ও তাঁর অনুচরদের আক্রমণে বাধা দেবার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সেনাপতিগণ নতুনভাবে সামরিক আয়ােজন আরম্ভ করে। উপযুক্ত রাস্তাঘাট না থাকায় সুবৃহৎ সৈন্যবাহিনী দ্রুত চলাচলে অসুবিধা দেখে তারা বৃহৎ বাহিনীগুলােকে ভেঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ করেন। এভাবে পুনর্গঠিত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্যদল নানাবিধ উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সমগ্র উত্তরবঙ্গ এবং ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলায় বিদ্রোহীদের সন্ধানে ঘুরতে থাকে।
দেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তােলাই ছিল মজনুর উদ্দেশ্য। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলে যাতে সাধারণ শত্ৰু, শােষক ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতে পারে সে জন্য তিনি প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন ও সকলের কাছে সাহায্যের আবেদন করছিলেন। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গােয়েন্দাচক্র সক্রিয় ছিল। মজনু শাহকে ময়মনসিংহ জেলা ছেড়ে যাওয়ার আদেশ এল। ওদিকে জেলা কর্তৃপক্ষ জরুরী তলব পাঠালেন, মজনু শাহকে জীবন্ত অথবা মৃত ধরে দেওয়া চাই। কোম্পানীর সেনা ও পুলিশ বিভাগ সক্রিয় হয়ে উঠল, কিন্তু ইতােমধ্যে মজনু শাহ ময়মনসিংহ ছেড়ে মালদা জেলায়, তারপর সেখান থেকে কোনও অজ্ঞাত স্থানে পাড়ি দেন।
১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে কোম্পানীর সেনাপতি ক্রোর সাথে মজনু শাহের ফকির বাহিনীর এক সংঘর্ষ ঘটে মহাস্থানগড় থেকে ৬মাইল দূরে। মজনুর বাহিনীতে ছিলেন চারশাে সশস্ত্র ফকির এবং দুশাে তলােয়ার ও বর্শাধারী সেনা। ১৭৮৬ তে ফকিররা দুটি স্বতন্ত্র দলে বিভক্ত হয়ে উত্তরবঙ্গে হানা দেন। একটি দলের নেতৃত্বে থাকেন মজনু স্বয়ং, অন্য দলটির নেতৃত্ব দেন মুসা শাহ। ১৭৮৬-র ১৭ আগস্ট মজনু শাহকে লেফটেনান্ট আঁশলীর সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হতে হয়। ২৯ শে সেপ্টেম্বর লেফটেনান্ট ব্রেনানের বাহিনীর সঙ্গে ‘কালেশ্বর নামক স্থানে মজনুর সংঘর্ষ হয়। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের কিছু লােক হতাহত হয়, মজনু শাহ স্বয়ং আহত হন। মজনু শাহের অনুচররা আহত নেতাকে বহন করে তাঁর প্রধান কর্মস্থান মাখনপুরে নিয়ে যান। সেখানে মজনু শাহ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। কেউ কেউ বলেন ১৭৮৬ সালের মার্চ বা মে মাসে মজনুর প্রয়াণ ঘটে।১৮
মজনু শাহর মৃত্যুর পর সশস্ত্র সংগ্রামীদের নেতা হন তার অনুসারী মুসা শাহ। মুসা শাহর নেতৃত্বে প্রতিরােধ সংগ্রামীরা ১৭৮৭ সালে বর্ধমানের বিভিন্ন স্থানে হামলা করে। ১৭৮৮ সালের মার্চে রাজশাহীতে রানী ভবানীর আগ্রাসী বরকন্দাজ বাহিনীর সাথে এক সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে ফকিররা। সে বছর জুনে জাহাঙ্গীরপুর পরগণার চামপুরে লেফটেনান্ট ক্রিষ্টির সাথে এক যুদ্ধে হেরে পিছু হটে যান মুসা শাহ ও তার বাহিনী। ১৭৯২ সালে ফকির নেতা পরাগ আলীর সাথে এক আকিস্মক দ্বন্দ্ব যুদ্ধে নিহত হন প্রবীণ সংগ্রামী নেতা মূসা শাহ।
এর পর ১৭৯৪ সালে ফকির নেতা চেরাগআলী রংপুরের কাউনিয়ায় ছাউনি ফেলেছিলেন বলে জানা যায়। এ সময় মতিগিরি নামক এক সন্ন্যাসী নেতা এক রাতে গুপ্ত হামলা চালিয়ে চেরাগ আলীকে হত্যা করে। চেরাগ আলীর হত্যাকাণ্ডের পর করিম শাহ ও সােবহান শাহ কিছুদিন লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু এর পূর্বেই কোনাে কারণে সন্ন্যাসীরা নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে, অস্ত্র ত্যাগ করেছে সাধারণ প্রজারাও। এরপর মজনুর বাহিনীর আর কোনাে বড় রকম তৎপরতার খবর পাওয়া যায়নি। তবে মজনু শাহ যে তীব্র প্রতিরােধ লড়াইয়ের সূচনা করেন তার প্রভাব পড়ে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে। মজনু শাহ ও তার অনুসারীদের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হন অন্যান্য স্থানের ফকিরগণও। কুমিল্লার হাজীগঞ্জের হুলি ফকির ১৭৮৬-৮৭ সালের দিকে দেবী সিংহের এক ক্রীতদাসকে আশ্রয় দেন এবং তার পরিবারকে মুক্ত করে দেওয়ার জন্য দেবী সিংহকে চিঠি লেখেন। দেবী সিংহ কর্ণপাত না করায় হুলি ফকির স্থানীয় অনুসারীদের সংগঠিত করে আশপাশের ইংরেজ কেন্দ্রগুলােয় লুটপাট চালান এবং খাজনা আদায়ে বাধা দেন, কিন্তু উপনিবেশিক সেনাবাহিনী এগিয়ে এলে যুদ্ধ না করে আত্মগােপন করেন হুলি ফকির।১৯
বরিশালে অত্যাচারিত প্রজাদের অনুরােধে ওখানকার সাধক পীর বলাকী শাহ ১৭৯১র ডিসেম্বরের শেষ দিকে তার নিজের এলাকায় স্বাধীনতা ঘােষণা করেন। তিনি ছিলেন বাকেরগঞ্জ জেলার সলিমাবাদ পরগণার ঘাঘরী গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা ও আবাসিক ফকির। তিনি প্রজাদের সংগঠিত করে পুরনাে কামান মেরামত করেন এবং দুর্গ গড়ে তুলেন। বলাকী শাহকে দমন করতে আসা আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজ দখলদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধে বহু মুক্তিযােদ্ধা শহীদ হন। উপনিবেশিক আইনে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন বলাকী শাহ।২০ ১৭৯৯ সালে সিলেটে পীর আগা মােহাম্মদ রেজা ইংরেজের বিরুদ্ধে তার সংগ্রামের সূচনা করেন। রাজনৈতিক চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে বানিয়াচঙ্গের জমিদার দেওয়ান আদম রেজার নিকট পত্র লিখে ইংরেজ-বিরােধী সংগ্রামে সাহায্য কামনা করেন তিনি। স্থানীয় প্রজা ও অনুসারীদের সংগঠিত করে প্রায় পাঁচ হাজার যােদ্ধা নিয়ে জুলাইয়ে সিলেট আক্রমণের জন্য অগ্রসর হন রেজা শাহ। কিন্তু সম্মুখ যুদ্ধে টিকতে না পেরে পিছু হটে আসেন। এবং আগষ্টের প্রথম সপ্তাহে ত্রিপুরায় পালিয়ে যাওয়ার পথে বন্দী হন। বিচারের প্রহসনে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় তার।
মজনু শাহর মৃত্যুর পর পর মুসা শাহ নিহত হওয়ায় উত্তরবঙ্গে ফকির-সন্ন্যাসীদের সংগ্রাম খুব একটা অগ্রসর হয়নি। সন্ন্যাসীদের ভূমিকার পরিবর্তনও ব্যর্থতার একটি কারণ। ফকির যােদ্ধারা কিছুকাল কোচবিহার রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরে উত্তরবঙ্গে ফিরে এলেও আর কোনাে সুসংগঠিত তৎপরতার খবর পাওয়া যায় না।
মজনু শাহ-র সন্তানদের মধ্যে পরাগল শাহ ও শিষ্য চেরাগ আলী আন্দোলনের শিখাকে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। মজনু শাহের পর সবচেয়ে উল্লেখযােগ্য ফকীর নেতা ছিলেন সােবহান শাহ। বাংলা ও বিহারের বিস্তীর্ণ এলাকা তার আন্দোলনের ক্ষেত্র ছিল। সােবহান শাহের অনুচর জহুর আলী ও মতিউল্লাহ ইংরেজ সেনাদের দ্বারা গ্রেপ্তার হন ও তাঁদের কয়েক বছরের কারাদন্ড হয়। ফকির নেতাদের বিচার চলার সময় মালদা জেলার কোনও এক জঙ্গলে ফকিরদের এক গােপন অস্ত্রাগারের সন্ধান পাওয়া যায়। আঠারাে শতাব্দীর শেষের দিকে নওয়াজ শাহ, বুন্ধু শাহ প্রভৃতি ফকির নেতারা আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন, যদিও ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি আন্দোলনের শিখা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। মজনু শাহের সমকালে এবং পরবর্তীকালে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন রেখেছিলেন ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানী প্রমুখ সন্ন্যাসী নেতারা। জলপথে যুদ্ধ ছিল এদের প্রধান কাজ।
“১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাস হইতে বাংলার বিখ্যাত বিদ্রোহী নায়ক ভবানী পাঠক ও বিদ্রোহী নায়িকা দেবী চৌধুরানীর উল্লেখ দেখা যায়। এই সময় কয়েকজন ব্যবসায়ী ঢাকার সরকারী কাস্টমস-এর সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট অভিযােগ করে যে, ভবানী পাঠক নামে এক দুঃসাহসী ব্যক্তি পথে তাহাদের নৌকা লুণ্ঠন করিয়াছে। ভবানী পাঠককে সদল-বলে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সুপারিন্টেন্ডেন্ট উক্ত ব্যবসায়ীগণের সহিত গ্রেপ্তারী পরােয়ানা সহ একদল বরকন্দাজ প্রেরণা করেন। ভবানী পাঠক এই গ্রেপ্তারী পরােয়ানা ও ইংরেজদের দেশের শাসক বলিয়া মানিতে অস্বীকার করেন এবং দেবী চৌধুরানীর সহযােগিতায় একদল বিদ্রোহী সৈন্য লইয়াইংরেজ ও দেশীয় বণিকদের বহু পণ্যবাহী নৌকা লুণ্ঠন করেন। তাঁহাদের নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণে ময়মনসিংহ ও বগুড়া জেলার একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা অচল হইবার উপক্রম হয়। অবশেষে লেঃ ব্রেনানের নেতৃত্বে একটি ইংরেজ সৈন্যবাহিনী ভবানী পাঠক ও তাঁহার সহযােগিনী দেবী চৌধুরানীর বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। একদিন ভবানী পাঠক তাহার অল্প সংখ্যক অনুচরসহ ইংরেজ বাহিনীর বেষ্টনের মধ্যে পড়িয়া যান। এক ভীষণ জলযুদ্ধে পাঠকের দল পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে স্বয়ং ভবানী পাঠক ও তাহার প্রধান সহকারী বলিয়া কথিত একজন পাঠান ও অপর দুইজন সহকারী নিহত হন এবং আটজন সৈন্য গুরুতররূপে আহত ও বিয়াল্লিশ জন সৈন্য বন্দী হয়। ইহা ব্যতীত বিদ্রোহীদের ‘অস্ত্রশস্ত্রে পূর্ণ সাতখানি নৌকা (ছিপ) ইংরেজদের হস্তগত হয়। সম্ভবত এই জলযুদ্ধের সময় দেবী চৌধুরানী ভবানী পাঠকের সঙ্গে ছিলেন না। ইংরেজ কর্মচারীদের পত্র ও বিবরণ হইতে জানা যায় যে, পাঠকের মৃত্যুর পরেও দেবী চৌধুরানীর আক্রমণে শাসকগণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন।”২১ বিদ্রোহের অন্যান্য নেতারা ছিলেন কৃপানাথ, রমজান শাহ, আমুদি শাহ, ইমাম শাহ, মহম্মদ, পীতাম্বর, মাদারবক্স, মনজু, শিবচন্দ্র রায়, হনুমান গিরি, মােহন গিরি, গণেশ গিরি, বাবুই গিরি, উমরাও গিরি, ভবানী গিরি, রামকিষান মােহান্ত, করিম শাহ, রওসন শাহ প্রমুখ।
মূলত ফকির এবং সন্ন্যাসীরা একত্রিত হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন। ফকির মজনু শাহের সঙ্গে ভবানী পাঠক এবং দেবী চৌধুরানীর ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।২২ নেতৃত্বের প্রশ্নে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে। প্রথমত, বিদ্রোহের প্রাথমিক পর্বে নেতৃত্বের প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। সন্ন্যাসী ও ফকিররা যারা যেখানে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী ছিল, তারা সেখানে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিল। তারা কখনও একক ভাবে, কখনও যৌথভাবে কোনাে নেতা ছাড়াই বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল। অবশ্যই এইসব ক্ষেত্রে জনগণের সক্রিয় সহযােগিতা ছিল প্রয়ােজনীয়। এই সহযােগিতার অভাব হয়নি। কারণ ইংরেজ আমলে সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ ছিল। রতনলাল চক্রবর্তীর মতে কতিপয় জমিদারসহ ফকির-সন্ন্যাসীগণ স্থানীয় জনগণের সাহায্য ও সহযােগিতা লাভ করেন।২৩ গ্রামের সাধারণ মানুষ সন্ন্যাসীদের হয়ে গুপ্তচরের কাজ করত। একথা ঠিক যে, উঠতি জমিদারগণ ও কান্তবাবু, দেবী সিংহ, গােবিন্দ সিংহ, রামকান্ত রায়, দুলাল রায়, জয়নারায়ণ ঘােষাল প্রভৃতি বেনিয়া ও মুৎসুদ্দি এই বিদ্রোহের বিরােধিতা করেছিলেন। কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল কম। বস্তুত, জনগণের সহায়তা ছাড়া এই বিদ্রোহ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়ত, বিদ্রোহের পরবর্তী পর্যায়ে যখন ব্যক্তিগত নেতৃত্বের প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন নেতারা অনেক সময় যৌথভাবে কাজ করতেন। ১৭৯০ সালের জানুয়ারি মাসে ময়মনসিং-এর কালেক্টরের ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, চেরাগ আলি ও অন্যান্য ফকির, মােহন গিরি ও অন্যান্য সন্ন্যাসীর সঙ্গে একত্রে বিদ্রোহ পরিচালনা করেছিল। সন্ন্যাসীরা ফকিরদের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করতে আপত্তি করেনি। তবে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্বে এই ঐক্যবােধের অভাব ও মতভেদ দেখা গিয়েছিল। তৃতীয়ত, এই সন্ন্যাসী ও ফকিররা এই বিদ্রোহে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকায় এই বিদ্রোহে ধর্মের একটি ভূমিকা ছিল। হাচিনসন মন্তব্য করেছেন যে, সন্ন্যাসীরা কৃষকের অর্থনৈতিক বিদ্রোহের সঙ্গে ধর্মের প্রেরণা যুক্ত করে। তবে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কৃষক ও কারিগর কতটা নিজ নিজ ধর্মের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, তা বলা কঠিন। আসলে সাধারণ মানুষ ইংরেজ শাসনে নানা কারণে ক্ষুব্ধ ছিল। কিন্তু তারা সেই ক্ষোভকে সংগঠিত পথে প্রতিবাদের ভাষায় রূপান্তরিত করতে পারছিল না। ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ তাদের সেই সুযােগ এনে দেয়। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব ছিল ধর্মীয় নেতাদের হাতে। এর বাইরে এই বিদ্রোহের সঙ্গে ধর্মের কোনাে সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয় না। তবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এক আদর্শগত ঐক্য এই বিদ্রোহে এক নতুন মাত্রা দিয়েছিল। তাছাড়া সন্ন্যাসী ও ফকিররা নিজেদের সংকীর্ণ কোনাে ধর্মীয় পরিমন্ডলের মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি।
মুসলমান ফকির ও হিন্দু সন্ন্যাসীদের সংগঠন আলাদা হলেও এবং কখনও কখনও তাদের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হলেও তারা মিলিতভাবে ব্রিটিশদের আক্রমণ করত। রাজশাহীর কালেক্টর এক রিপাের্টে লেখেন, “ফকিরেরা নিকটে অবস্থিত সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যােগ দিয়েছে।”২৪ ফকির ও সন্ন্যাসীদের কাজের মধ্যে এতই মিল যে, কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাদের মধ্যে সব সময়ে পার্থক্য প্রদর্শন করা প্রয়ােজন বােধ করত না। তাই তারা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে এই ধরনের আক্রমণকারী মাত্রকেই ‘সন্ন্যাসী’ এই সাধারণ নামে অভিহিত করত। সন্ন্যাসীরা স্থানীয় জমিদার ও বণিকদের উপর মাঝে মাঝে হামলা করলেও তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল কোম্পানী-রাজ।
ফকিরদের বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে স্বয়ং মজনু শাহই রাজশাহীর নাটোরের রাণী ভবানীর কাছে এক পত্রে (১৭৭২-র প্রথম ভাগে) আবেদন জানিয়েছিল: “আমরা বহুদিন থেকে বাংলাদেশে ভিক্ষা করে বেড়াই এবং জনগণও আমাদেরকে ভিক্ষা দিয়ে থাকেন। আমরা বহুকাল ধরে বিভিন্ন ধর্মস্থানে ও দরগায় আল্লার উদ্দেশ্যে নামাজ আদায় করে আসছি। আমরা কখনাে কারাে বিরুদ্ধে নিন্দা জ্ঞাপন করিনি। এমনকি কারাের উপর অত্যাচারও করিনি। তবুও গত বছর আমাদের ১৫০ জন ফকীরকে বিনা অপরাধে খুন করা হয়েছে। …ইংরেজরা আমাদের দলগতভাবে ধর্মস্থান ও অন্যান্য দরগায় যেতে বাধা প্রধান করে থাকে। ইংরেজদের এই কাজ সম্পূর্ণ অন্যায়। আপনি দেশের শাসক। আমরা ফকীর। আমরা সব সময় আপনার মঙ্গল কামনা করি। আমরা আপনার সাহায্যপ্রার্থী।”২৫
এই আবেদনেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ফকিরদের ব্রিটিশ বিরােধী বিদ্রোহের মূল কারণ। দ্ব্যর্থক হলেও চিঠিটির অর্থ স্পষ্ট : ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে জনগণের এ বিদ্রোহে যােগদানের জন্য রানী ভবানীর নিকট আবেদন। কিন্তু রানী ভবানী বােধহয় এতে সাড়া দেননি, কারণ নাটোর অঞ্চলে শীঘ্রই মজনু শাহর নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা তৎপর হয়ে ওঠে। বিদ্রোহীরা অত্যাচারী ধনিক ও জমিদারদের এবং ইংরেজদের অনুচরবৃন্দের ধনসম্পদ লুট করে এবং কৃষকদের ওপর অত্যাচারের প্রতিশােধ গ্রহণ করে। বিদ্রোহীরা এ সময় স্থানীয় কামারশালায় তৈরি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করত। কিন্তু বিদ্রোহী সৈন্যগণ যাতে সাধারণ মানুষকে কোন অত্যাচার না করে তার জন্য কঠোর নির্দেশ দেওয়া থাকত মজনু শাহের। নাটোরের সুপারভাইজার রেভেনিউ কাউন্সিলে প্রদত্ত তার এক পত্রে লেখেন, “আমার হরকরা সংবাদ নিয়ে এল, গতকাল ফকিরদের এক বিরাট দল সিলবেরির (বগুড়া জেলার) একটি গ্রামে এসে সমবেত হয়েছে। তাদের নায়ক মজনু তার অনুচরদের কঠোর নির্দেশ দিয়েছে যে, তারা যেন জনসাধারণের ওপর কোনরূপ অত্যাচার বা বলপ্রয়ােগ না করে এবং জনসাধারণের স্বেচ্ছায় দান ব্যতীত কোনকিছুই গ্রহণ না-করে।” এই পত্রপ্রেরক সুপারভাইজারই আর এক পত্রে জানিয়েছিলেন যে, গ্রামবাসী নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে বিদ্রোহীদের আহারের ব্যবস্থা করেছে এবং বিদ্রোহীরা গ্রামবাসীদের ওপর কোন অত্যাচার করেনি। এ ছাড়া বহু কৃষক বিদ্রোহীদের দলে যােগ দিয়েছে এবং কৃষকগণ ইংরেজ সরকারকে কর দেওয়া বন্ধ করে সেই কর বিদ্রোহীদের হাতে দিয়েছে।
১৭৭৩-এ পূর্নিয়া জেলা থেকে কয়েকটি বিদ্রোহীদল রংপুরের বিদ্রোহী কৃষকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে গ্রামাঞ্চল থেকে ইংরেজ কর্মচারী ও অত্যাচারী জমিদারদের তাড়িয়ে দেয় এবং ইংরেজ বাণিজ্য-কুঠিগুলাে লুট করে। ইংরেজগণ এক বিরাট বাহিনী তাদের দমনের জন্য নিয়ে আসে। এ অঞ্চলের সকল গ্রামের কৃষক-জনগণ তীরধনুক, বল্লম, লাঠি, সড়কি নিয়ে বিদ্রোহী দলে যােগদান করে ইংরেজদের ঘিরে ফেলে! ইংরেজরা তাদের অধীন দেশীয় সিপাহীদের পাল্টা আক্রমণের আদেশ দিলে তারা স্বদেশের কৃষকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে। ফলে ইংরেজ বাহিনী সম্পূর্ণ পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে রংপুর জেলার সুপারভাইজার পার্লং-এর চিঠিতে আছে, ‘কৃষকরা আমাদের সাহায্য তাে করেই নি, বরং তারা লাঠি প্রভৃতি নিয়ে সন্ন্যাসীদের পক্ষে যুদ্ধ করেছে। যে সব ইংরেজ সৈন্য জঙ্গলের লম্বা ঘাসের মধ্যে লুকিয়েছিল তাদের তারা খুঁজে বের করে হত্যা করেছে। কোন ইংরেজ সৈন্য গ্রামে ঢুকলে কৃষকরা তাদের হত্যা করে বন্দুকগুলাে ছিনিয়ে নিয়েছে।
সে-সময়ে ফকির এবং সন্ন্যাসী বিদ্রোহে যারা সমর্থন দিয়েছিলেন, তারা ছিলেন অধিকাংশই গ্রামের সাধারণ মানুষ। জনগণ তাদের গতিবিধি এবং গােপন কার্যক্রম কখনও কারও কাছে প্রকাশ করত না। তবে দেশের মধ্যে যারা জনগণের স্বার্থ বিরােধী কার্যকলাপে জড়িত ছিল, সেই সব অবস্থাপন্ন জমিদাররা সব সময় আতঙ্কিত থাকতেন সন্ন্যাসীদের ভয়ে। তারা সন্ন্যাসীদেরকে অভিহিত করতেন ডাকাত এবং দস্যু বলে। ওয়ারেন হেস্টিংস নিজেও মন্তব্য করেছেন:তারা দস্যুগিরি করে ভিক্ষাবৃত্তি করতেন। কোনও কোনও জমিদার সন্ন্যাসী এবং ফকিরদের নানাভাবে সাহায্য ও সহযােগিতা করতেন। পুর্ণিয়ার রামকুঠি আক্রমণকালে সেখানকার স্থানীয় জমিদার বিদ্রোহী ফকিরদের সাহায্য করেছিলেন। উক্ত জমিদার ইংরেজ সেপাইদের বিন্দুমাত্র সাহায্য করেননি।২৬
ইংরেজরা এ দেশীয় জমিদারদের সব সময় সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। বগুড়া জেলার সিলবারিস পরগণায় লেঃ টেলর সন্দেহের বশবর্তী হয়ে সেখানকার কয়েকজন জমিদারকে গ্রেফতার করেন। বিদ্রোহী ফকির এবং সন্ন্যাসীদের মধ্যে একটা সৈনিকসুলভ শৃঙ্খলা গড়ে উঠেছিল। দলের নেতৃবৃন্দকে তারা ডাকত হাকিম বলে।২৭ সাধারণ জনগণের সঙ্গে ফকির এবং সন্ন্যাসীদের একটা সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। যে সকল স্থানে ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে ফকির এবং সন্ন্যাসীদের লড়াই সংঘটিত হয়েছিল সেই সকল স্থানের অধিবাসীরা কখনও ইংরেজদেরকে সাহায্য করেনি। বরং ফকির এবং সন্ন্যাসীদের পক্ষাবলম্বন করে দেশীয় অধিবাসীরা অস্ত্রশস্ত্র এবং লাঠি দিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অস্ত্র কেড়ে নিয়েছিল। দিনাজপুর জেলায় মুসা শাহের নেতৃত্বে ফকিররা যে সমস্ত অভিযান ইংরেজদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করেছিল, ওই সকল অভিযানে কোম্পানী কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের কাছে সাহায্য চেয়েও তারা কোনও সাহায্য পায়নি। এ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদনে আক্ষেপ করে লেখা হয়েছিল: “স্থানীয় গ্রামবাসীরা সাহায্য করলে মুসা শাহকে গ্রেফতার করা সম্ভব হতাে কিন্তু তারা সাহায্য করা তাে দূরের কথা বরং লুটপাট করার কাজে অংশ নিয়েছে।”২৮
কোম্পানীর স্বেচ্ছাচারী আচরণ এবং নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের কারণে উত্তর বাংলার জনগণের মধ্যে ব্যাপক একটা বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছিল। সেই বিক্ষোভকেই ফকির এবং সন্ন্যাসীরা কাজে লাগিয়ে বিদ্রোহে পরিণত করেছিল। মজনু শাহের সাংগঠনিক দক্ষতা ও ইংরেজ বিরােধী নেতৃত্ব এবং ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানীর মেধা ও কর্মতৎপরতা শক্তির সম্মেলনে পরিণত করে তুলেছিল। অথাৎ এটা ছিল ফরাসী প্রজাতন্ত্রেরই মতাে একটা সুশৃঙ্খলাবদ্ধ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন।
ফকির এবং সন্ন্যাসীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার কোনও চিহ্ন ছিল না। তাদের কাজের মধ্যেও ছিল না কোনও পার্থক্য। চলনে-বলনে পােশাক পরিচ্ছদে এতই মিল ছিল যে কে হিন্দু কে মুসলমান তা একটুও বােঝার উপায় ছিল না। ১৭৮৬ সালের ২রা মার্চ তারিখে লিখিত বগুড়ার কালেক্টর মিঃ চ্যাম্পিয়নের এক পত্রে জানা যায়, সমকালে একদল হিন্দু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মুসলমান ফকিরদের এক ভয়ানক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়। দাঙ্গায় মজনুর দলের অনেকে নিহত হয়।২৯ এই দাঙ্গা ১৯৭৭ সালের কোন এক সময়ে বগুড়া জেলার চাম্পাপুকুরের কাটাখালের পার্শ্বে অনুষ্ঠিত হয়। বগুড়ার ইতিহাস-লেখক প্রভাসচন্দ্র সেন এ-ঘটনার উল্লেখ করেছেন।৩০ মিঃ সেন এই বৃত্তান্ত কোথা থেকে পেয়েছেন, তার কোন উল্লেখ করেন নি। কিন্তু চাম্পাপুকুরের দাঙ্গায় যে মজনু ফকিরের মৃত্যু হয়নি, মিঃ চ্যাম্পিয়নের উপরিউক্ত বিবৃতি থেকেই জানা যাচ্ছে।
মিঃ চ্যাম্পিয়ন আরও উল্লেখ করেছেন যে, এটি তাদের পূর্ববর্তী কোন কলহের পরিণাম। বলাবাহুল্য, ফকির সন্ন্যাসীদের মধ্যে ইতিপূর্বেও এমন কি পরেও একাধিকবার এই ধরনের দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এবং যতদূর মনে হয়, এটি সাম্প্রদায়িক মনােভাবের ফল নয়।
উদাহরণ স্বরূপ, বলা যেতে পারে, ১৭৮২ সালে ময়মনসিংহের শেরপুরে এক সন্ন্যাসীদলের সঙ্গে মজনু দলের এক দাঙ্গা হয়। দাঙ্গায় ৩০ অথবা ৪০ জন সন্ন্যাসী নিহত হয়। এই সন্ন্যাসীরা ‘রামাইয়্যাত’ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। মজনুর সঙ্গে প্রায় দেড় হাজার ফকির ছিল। তারা আশঙ্কা করেছিল যে, শেরপুরের নিকট দিয়ে প্রায় ৬০০ সন্ন্যাসীদের যে দলটি ইতিপূর্বে অতিক্রম করেছিল, তারা ফেরার পথে তাদের বন্ধুদের এ-হত্যার প্রতিশােধ নেবে। ঘটনাটির উল্লেখকালে মিঃ লজ, ময়মনসিংহের নিকটবর্তী বেগুনবাড়ির তত্ত্বাবধায়ক বলেন যে, তার ধারণা, সন্ন্যাসীরা এর প্রতিশােধ নেবে কি, তারাই বরং ফকিরদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এখানে লুটতরাজে অংশ নেবে। কেননা, তাদের উভয়েরই লক্ষ্য যে এক, মানে, লুটপাট করা। মিঃ লজের ধারণা সত্য হয়েছিল।
পরবর্তী ১০ ডিসেম্বর তারিখে রঙপুরের কালেক্টর গুডল্যান্ড সাহেব রেভিনিউ বাের্ডে এই মর্মে এক চিঠি পাঠান যে, প্রায় ৭০০ লােকের একদল হিন্দু-সন্ন্যাসী ভিতরবন্দ পরগনাতে মুসলমান ফকিরদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তারা ঢাকা থেকে এসে দেওয়ানগঞ্জের কাছে ব্রহ্মপুত্র পার হয়েছে। এদেরকে দমন করবার জন্য লেফটেনন্যান্ট ম্যাকডােনাল্ডকে নিয়ােগ করা হয়। ১৮০ জন কোম্পানি সৈন্যসহ মিঃ ম্যাকডােনাল্ড যাত্রা করেন।
জানা যায়, এই যাত্রায় ফকির নেতা মুসাশাহ ও সন্ন্যাসী নেতা মােহন গিরি ধৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ যে, রেভিনিউ কমিটি এ-ব্যাপারে গুডল্যান্ড সাহেবকে এমন নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, বিচার যেন পুঙ্খানুপুঙ্খ হয় এবং এমন সাক্ষ্য প্রমাণ যেন হাজির করা হয় যার দ্বারা তাদের দোষ যথার্থভাবে প্রমাণিত হয়। এমনকি ক্যাপ্টেন ম্যাকডােনাল্ডকে আক্রমণের পূর্বে তাদের কি লেনদেন হয় এবং আত্মরক্ষার জন্য তারা কেমন দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করেছিল, তারও যথাযথ বিবরণ যেন উঘটিত হয়। এই সঙ্গে আরও বলা হয় যে, বিচারে যদি কারও মৃত্যুদন্ড বা অনুরূপ কোন শান্তির ব্যবস্থা না হয়, তাহলে বন্দীগণকে যেন সম্মানিত বাের্ডের অনুমতি লাভের পূর্বে মুক্তি দেওয়া না হয়।৩১ এ থেকে এ-কথা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, ফকিরসন্ন্যাসীদের মধ্যে আর যাই থাক, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছিল না। আর ব্রিটিশ-বিরােধী মনােভাব বা কোম্পানী-বিদ্বেষ তাদের সহজাত ছিল বলা যেতে পারে।
আসলে তখনকার সেই ঐতিহাসিক পর্বে যখন বাংলার মানুষ যুদ্ধ বিগ্রহ, রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্যের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখত না, কেবল বিদ্যাদান থেকে জলদান পর্যন্ত কাজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখত এবং রক্ষা করত নিজেদের সমাজ ধর্ম—যে সমাজ-ধর্ম শতাব্দীর পর শতাব্দী কোনও শাসকই নষ্ট করতে পারেনি, এমনকি সমাজ বিনষ্ট করে কাউকে লক্ষ্মীছাড়া করে দিতে পারেনি, নিশ্চয়ই সেই সমাজ-ধর্মের ওপর কোম্পান শাসকরা এমন কিছু অত্যাচার ও অবিচার চালিয়েছিল, যার ফলে ফকির এবং সন্ন্যাসীরা হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিল অস্ত্র।
উপনিবেশিক নথিকারের কাছে ফকির-সন্ন্যাসীরা ছিল লুটেরা, ডাকাত, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী; যেহেতু তারা উপনিবেশায়নে প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করে। এই রকম উপনিবেশী দৃষ্টির শাসনে তৈরি নথিতে ফকির-সন্ন্যাসীরা অতর্কিতে হামলা চালিয়ে গ্রামকে গ্রাম তছনছ করে ফেলে, গৃহস্থদের সর্বস্ব লুটে নিয়ে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, হেলাফেলায় নিরীহ মানুষ খুন করে। এগুলাে ইংরেজের প্রচারণায় লাভ করে ‘সত্য’-এর মর্যাদা। পরে দেশীয় লেখকরা এ জাতীয় নথির ওপর নির্ভর করে ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে প্রায় ডাকাত দলের ঘটনায় পরিণত করেন। যেহেতু এর বিপরীতে অন্য কোনাে বয়ান কোনাে সত্য উপস্থিত করতে পারেনি তাই এই দৃষ্টিই টিকে যায় এবং প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধারের প্রচেষ্টায় প্রধান বাধা হয়ে থাকে। এখন এই কথিত ‘সত্য’-বর্ণনার উৎস খুঁজে দেখা যাক।
ইংরেজ-বিরােধী সশস্ত্র ফকির-সন্ন্যাসীদের ওপর দস্যুবৃত্তির অপবাদ আরােপ ও দীর্ঘকাল তা টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয় বিশেষ কয়েকটি কারণে। প্রথমত, ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী অবস্থান ও মিথ্যাচার প্রস্তুত করে ইতিহাস বিকৃতির মূল ভিত্তি। ফকির সন্ন্যাসীদের সাথে ইংরেজদের সরাসরি সংঘাতের মধ্যে ১৭৬৩ সালে বাকেরগঞ্জের ইংরেজ কেন্দ্র আক্রমণ, সে বছরই সন্ন্যাসীদের দ্বারা রাজশাহীর কুঠি লুট এবং আরেকদল ফকির কর্তৃক ঢাকার ফ্যাক্টরি দখল ইংরেজদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে। ফলে নিয়মিত সেনাবাহিনীর দ্বারা ফকির সন্ন্যাসীদের দমনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। তখন থেকেই স্থানীয় প্রশাসকদের রিপাের্টে ফকির ও সন্ন্যাসীদেরকে ভবঘুরে, ডাকাত, অত্যাচারী, ইত্যাদি বলে উল্লেখ করা হত। পরে সিদ্ধান্তমূলক মন্তব্যসহ ফকির-সন্ন্যাসীদেরকে সম্প্রদায়গতভাবে ডাকাত হিসেবে অভিহিত করা হয়। সংগ্রামী ফকির সন্ন্যাসীদেরকে লুটেরা-ডাকাত অভিহিত করে লেখা হয় যে, এরা আদতে ফকিরই নয়, তীর্থ পর্যটনের ভান করে বাংলার সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় আর চুরি ডাকাতি করে।
১৭৬৩ সাল থেকে ফকিররা সংগঠিতভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই শুরু করার পরই তাদেরকে ডাকাত অভিহিত করে অপপ্রচারণা চালানাে হয়। এর আগে কখনাে ফকিরদেরকে ডাকাত বলা হয়নি। তাছাড়া ইংরেজের নথিপত্র নির্দিষ্ট কোনাে গ্রামে ফকিরদের নির্দিষ্ট কোনাে ডাকাতির ঘটনাও উল্লেখ করতে পারেনি। ইংরেজদের ট্রেজারী লুট ডাকাতি নয়। ইংরেজরা যে আইন ভেঙ্গে এদেশে আধিপত্য বিস্তার করে, সে আইন ফকিররা মেনে চলবে কেন? এসব কারণে ফকিরদের বৃটিশ-বিরােধী লড়াইয়ের ওপর আরােপিত বিকৃত ইতিহাসকে বিবেচনা করতে হবে সাম্রাজ্যবাদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের একটি নির্মিত প্রকল্প হিসেবে।
দ্বিতীয়ত, দেশীয়দের মধ্যে মজনু ও তার অনুসারীদের ডাকাত কল্পমূর্তি নির্মাণে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে কয়েকটি বিশেষ ধরনের রচনা। এ প্রসঙ্গে প্রথমে উত্তরবঙ্গের একটি লােককবিতা উল্লেখযােগ্য। কবিতাটি পঞ্চানন দাস নামের এক কবির রচনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়, ১৩১৭ সালে।৩২ কবিতাটির ভাষ্য :মজনু ফকির ও তার অনুসারীরা বাংলা ধ্বংস করার জন্য এদেশে এসে সাধারণ মানুষের বাড়িঘর লুটপাট করতাে, গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিতাে, যুবতী মেয়েদেরকে ধর্ষণ করতাে; মজনু এতটাই নির্দয় তস্কর যে, সারা দেশের লােক তার মৃত্যু কামনা করতাে। সব মিলিয়ে এক লােমহর্ষক কাহিনী।
কবি রতিরাম দাস কর্তৃক রচিত আরেকটি লােককবিতা প্রকাশিত হয় এর কিছুদিন পূর্বে একই পত্রিকায়। ঐ কবিতাটিতে রংপুর প্রজাবিদ্রোহে (১৭৮২-৮৩) দেবী চৌধুরাণী ও রাজা শিবচন্দ্রের অসীম বীরত্বের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।
ইংরেজরাও মজনু শাহর উপর নারী-ধর্ষণ ও গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়ার অপবাদ আরােপ করেনি। রতিরাম দাস ও পঞ্চানন দাসের নামে প্রকাশিত কবিতা দুটি ভাষায়, ছন্দে, শব্দ ব্যবহারে খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ। পঞ্চানন দাসের কবিতাটি সমকালীন অন্যান্য উৎসের তথ্যের বিরােধী এবং সাম্প্রদায়িকতা মনােভাবাপন্ন, অথচ এর রচয়িতা সম্পর্কে সামান্যতম পরিচয়ও পাওয়া যায়নি। এ কারণে কবিতাটি ঐতিহাসিক আলােচনায় সম্পৃক্ত করার সুযােগ নেই। অসিতনাথ চন্দ্র মনে করেন, পঞ্চানন দাসের মজনুর কবিতাটিতে মজনুর উপর মিথ্যা অপবাদ আরােপ করা হয়েছে।৩৩
বঙ্কিমচন্দ্রর উপর ইংরেজ কাহিনিকার স্কটের প্রভাব তর্কাতীত। স্কটের সৃষ্টি আইভানহাে বঙ্কিমচন্দ্রকে সারা জীবন নেশাগ্রস্ত করে রেখেছিল। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই দেবী চৌধুরাণী ও আনন্দমঠ-এর ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করেছেন। তবু হিন্দু পুনর্জাগরণেরকালে আনন্দমঠ উপন্যাসে সন্ন্যাসীদের যে রূপ নির্মাণ করা হয়, তাতে ফকির-সন্ন্যাসীদের নামের ওপর ডাকাত পরিচয় আরাে আঁটো হয়ে বসে।

পূর্বে উল্লেখিত যামিনীমােহন ঘােষের সন্ন্যাসী অ্যান্ডফকির রেডারস ইন বেঙ্গল’উত্তরবঙ্গের ফকির-সন্ন্যাসীদের বৃটিশ-বিরােধী সংগ্রাম নিয়ে লিখিত প্রথম (১৯৩০) পূণাঙ্গ গ্রন্থ। যামিনীমােহন বিশ শতকের তিরিশের দশকে, স্বাধীনতা আন্দোলনের পরম পর্বে। তিনি রায় বাহাদুর’ খেতাব অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। এ জন্য অন্তত ইংরেজদের মনতুষ্টির প্রয়ােজন ছিল। গ্রন্থের ভূমিকায় যামিনীমােহন লিখেছেন যে, প্রধানত বৃটিশদের নথিপত্র থেকেই লেখার মাল-মশলা সংগৃহীত হয়েছে এবং এ ব্যাপারে প্রয়ােজনীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়েছেন রেকর্ড বিভাগের কর্মকর্তা এ ক্যাসল।
এভাবে আমরা দেখব, ফকির-সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে কোম্পানির কর্মচারীদের অপপ্রচারণা ইংরেজ পণ্ডিতবর্গ, বঙ্কিমচন্দ্র, যামিনীমােহন বাবুদের বুদ্ধি ও মননে পরিপুষ্ট হয়ে যুগযুগ ধরে আচ্ছন্ন করে রেখেছে আমাদের চৈতন্য। তাই ফকির সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম যে মত প্রকাশ করেন একটি নিবন্ধে তাও কোম্পানির কাউন্সিল ও যামিনীবাবুদের চিন্তা কাঠামােতেই আবর্তিত হয়। সিরাজুল ইসলাম তার চুড়ান্ত মতের সপক্ষে সূত্র-প্রমাণ উল্লেখ করতে গিয়ে কেবল উপনিবেশবাদী জ্ঞানভাণ্ডারের কথাই নির্দেশ করেন। এর চেয়েও বিস্ময়কর যে, তিনি এ সম্পর্কে অন্য একজনের রচনাকে ছােটো করার জন্য সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে তাতে সাম্প্রদায়িক রঙ লাগানােরও চেষ্টা করেন।৩৪
তৃতীয়ত, ফকির ও সন্ন্যাসীদের পূর্ব-ইতিহাস এক করে দেখার কারণেও বৃটিশ বিরােধী লড়াইয়ের ওপর দস্যুবৃত্তির অপবাদ আরােপ সহজ হয়। মুসলমানরা শাসন ক্ষমতা হারানােয় মুসলিম ফকিরদের মনে বিশেষ ক্ষোভ সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষের উপর বিদেশী দখলদারদের অমানবিক শােষণ-নির্যাতনও তাদেরকে আবেগাক্রান্ত করে। অন্যদিকে, ইংরেজ কর্মচারীরা উস্কানিমূলকভাবে ফকির-সন্ন্যাসীদের তীর্থযাত্রায় বাধা সৃষ্টি করে। বৃটিশ ধর্মকেও শােষণের ক্ষেত্ররূপে কল্পনা করে ট্যাক্স বসায় তীর্থযাত্রার ওপর। সম্পদের সাথে সংস্রবহীন ফকিরদের পক্ষে এসব ট্যাক্স পরিশােধ করা সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া অত্যন্ত অপমানজনক এ রকম ট্যাক্স আরােপ করায় ইংরেজদের প্রতি তাদের ক্রুদ্ধ হওয়ারই কথা। এ সকল কারণে ফকিররা বৃটিশদের উৎখাত করার জন্য সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করে। সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর বৃটিশরা উপলব্ধি করে যে তারা একটি দীর্ঘ গণবিপ্লবের গােড়ায় দাঁড়িয়ে। বিচক্ষণ হেস্টিংসের মতাে মানুষেরা তাই প্রথম দফায় পাইকারী হারে সবাইকে ডাকাত-লুটেরা বলে গণ-বিদ্রোহকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমরা দেখি: “…from the available records, it is proved without a shadow of doubt that these were not ‘plundering activities’ nor ‘depredation’ carried out by a band of ‘nomadic medicants’ but a revolution, a rebillion against British by the rural population of the country with the sannyasis and the Fakirs as their leaders against foreign rulers, against the oppression of the British, their traders and Zaminders. All the landless peasant joined the Sannaysis and Fakirs wherever they went and helped them with all their might.”৩৫
ইংরেজের দাস শ্ৰেণীটি অর্থাৎ জমিদার, ইজারাদার, নায়েব-গােমস্তা, বণিক-মহাজনরা নিজেরাই চুরি-ডাকাতি, লুটপাট করত।৩৬ আবার ফকিরদের নেতৃত্বে সাধারণ প্রজাদের একটি অংশই সে অর্থ ছিনিয়ে নিত জমিদার-ইজারাদার বা ইংরেজ কর্মচারীদের নিকট থেকে। ফকিরদের বিরুদ্ধে এমন কোনাে প্রমাণ নেই যে, তারা সাধারণ কৃষক বা দরিদ্র প্রজাদের নিকট থেকে কখনাে কিছু ছিনিয়ে নিয়েছে। বরং বিপরীত তথ্য রয়েছে সাম্রাজ্যের নথিতেই। নাটোরের সুপারভাইজার কর্তৃক ফকির মজনু শাহ ও তার অনুগত যােদ্ধাদের সম্পর্কে লেখা চিঠিতে জানা যায়, “এরা কখনাে স্থানীয় কৃষকদের উপর উৎপীড়ন বা তাদের সম্পত্তি লুঠ করেনি। বরং বিদ্রোহীদের প্রতি নেতাদের কঠোর নির্দেশ ছিলাে যাতে তারা সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি বা ধনসম্পদ লুঠ না করে।”৩৭
ফকির ও সন্ন্যাসীদের বৃটিশ-বিরােধী যুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির দ্বিতীয় অভিযােগটি আমাদের ঐতিহাসিক-পণ্ডিতদের সৃষ্টি। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম তার পূর্বোক্ত নিবন্ধে পরিষ্কার করেই বলেছেন যে, এ বিদ্রোহে রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক রতনলাল চক্রবর্তী ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। কিছু নতুন তথ্যও উদ্ধার করেছেন তিনি। রতনলাল ফকির সন্ন্যাসীদেরকে ঢালাওভাবে ডাকাত বলার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। একইভাবে তাদেরকে বিপ্লবী, স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রভৃতি আখ্যায় সম্মানিতও করতে চান না। কারণ তিনি মনে করেন, ফকির ও সন্ন্যাসীরা ইংরেজ উচ্ছেদের জন্য যুদ্ধ করলেও দেশ-পরিচালনার ব্যাপারে তাদের সুস্পষ্ট রাজনৈতিক নীতিমালা ও লক্ষ্য ছিল না।৩৮
ফকির ও সন্ন্যাসীদের প্রতিরােধ সংগ্রামের মূল্যায়নে রতনলালের ব্যবহৃত দৃষ্টিকোণ গ্রহণযােগ্য নয়। তিনি মনে করেন যেহেতু ফকির সন্ন্যাসীদের আন্দোলন সংগঠিত ও সুশৃঙ্খল ছিল না এবং শাসন-পরিচালনার ব্যাপারে নির্দিষ্ট নীতিমালা ছিল না, তাই তাকে স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা যাবে না। বােঝা যায় তিনি রাষ্ট্র এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের ধারণার অনিবার্যতার প্রতি ইঙ্গিত করেন; আধুনিক মানব সমাজে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ কর্তৃক বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষকে শােষণের জন্য ব্যবহৃত ওই দুটো মূল যন্ত্রের প্রতি পক্ষপাতিত্ব তার। তবে তার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেও ফকিরদের রাজনৈতিক চেতনা ও লক্ষ্য চিহ্নিত করা সম্ভব।
এ সংগ্রাম সংগঠিত ও পরিচালিত হয়েছে সুফী ফকির ও সাধক সন্ন্যাসীদের দ্বারা। সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল বৃটিশ কর্তৃত্বের অবসান। এবং অবশ্যই রাষ্ট্র কাঠামাের মধ্যেই। এ ধরনের স্বাধীনতা স্পৃহায় ব্যক্তির রাজনৈতিক ইচ্ছার সুস্পষ্ট প্রকাশ রয়েছে। সমাজের পদ্ধতির মধ্যে ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশের প্রশ্নটি রাজনীতির মৌলিক বিষয়। ফকির যােদ্ধারা ইংরেজদের উপনিবেশিক শাসন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। বিদেশী সমর্থনপুষ্ট বিশ্বাসঘাতক একনায়কদের ফরমানের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষেরা অনাস্থা জানিয়েছিলেন তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্য লড়াই করে ইংরেজদের হটিয়ে দিয়ে পূর্ববর্তী ব্যবস্থাতেই থিতু হতে চেয়েছিলেন তারা। ১৭৭১ সালের মার্চের শুরুতে ঘােড়াঘাটায় শতাধিক ফকির বিনা অপরাধে নিহত হওয়ার পর বিপর্যস্ত মজনু রানী ভবানীর নিকট আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন, “আপনি দেশের শাসক। আমরা সর্বদা আপনার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি। আমরা আপনার সাহায্যপ্রার্থী।” স্পষ্টত তিনি তার সংগ্রামে শরিক করতে চেয়েছিলেন স্থানীয় শক্তিশালী সামন্তদের। মজনুর আহ্বান সফল হলে হয়ত বাংলার ইতিহাস ভিন্ন হত।
১৭৭৬ সালে বগুড়ায় অবস্থানকালে মজনু শাহর সাথে যথেষ্ট সংখ্যক রাজপুত যােদ্ধা ছিল। তিনি তখন মহাস্থানগড়ে একটি দূর্গ নির্মাণের চেষ্টা করছেন। এ রিপাের্ট করেন বগুড়ার ইংরেজ কর্মকর্তা গ্ল্যাডউইন। বগুড়ার প্রাদেশিক কাউন্সিলকে গ্ল্যাডউইন এই রিপাের্টে কড়া ভাষায় বলেন, “ভদ্র মহােদয়গণ! আপনারা ভাবছেন, আমি মজনু শাহ সম্পর্কে বড় বেশি ভাবছি, কিন্তু আপনারা ঠিক বুঝতে পারছেন না, ব্যাপারটি সত্যি সত্যিই বড় উদ্বেগজনক। এ যদি শুধু আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথা হত, আমি নিশ্চয়ই সাহায্যের জন্য কোন আবেদন করতাম না। কিন্তু প্রজাগণ বড় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে, তাই কর্তব্যবােধে আমি আপনাদের সাহায্যের জন্য আবেদন করতে বাধ্য হয়েছি।
সে এবার শুধুমাত্র কয়েকজন উদ্ধৃঙ্খল বাঙালি সাথে নিয়ে আসেনি, রীতিমত সশস্ত্র রাজপুত বাহিনীর নায়ক হিসেবে এসেছে। সে এখানে একটি সেনানিবাসও গড়ে তুলতে শুরু করেছে এবং প্রকাশ্যেই ঘােষণা করেছে যে, এবার সারা বর্ষাকাল সে এখানে থাকবে। সেজন্য খাদ্যদ্রব্যাদিও সংগ্রহ করছে। দিনাজপুর থেকে তার বিরুদ্ধে একদল সেনাবাহিনী পাঠানাে হচ্ছে শুনে সে অনেক কষ্টে করতােয়া পাড়ি দিয়ে সােজা ব্রহ্মপুত্রের দিকে চলে গেছে। পথে কোথাও বিশ্রাম করেনি।
তার আসার দুই বা তিনদিন পরে তার কাছে একজন কাজী পাঠিয়ে তার অভিপ্রায় জানতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে জানিয়েছে তার কিছু বন্ধকী দেনা-পাওনা আছে। শান্তিতে মস্তানগড়ে থাকতে দিলে সে সেগুলি আদায় করে নিয়ে যাবে। আর যদি বাধা দেওয়া হয়, সে ভয় পায় না, বরং বিরােধিতার জন্য সে প্রস্তুত।”৩৯
এ রকম বিশাল যােদ্ধা বাহিনী গড়ে তােলা এবং দুর্গ নির্মাণের প্রয়াস তার রাজনৈতিক আকাঙ্খর কথা জানায় এবং পূর্ণ সামরিক প্রস্তুতির পরিচয় দেয়। মজনু শাহর পরবর্তী ফকির নেতারা আরাে বেশি রাজনীতি সচেতন ছিলেন, ছিলেন আরাে সংগঠিত ও লক্ষ্যমুখী।
পূর্বোক্ত দেশীয় পণ্ডিতদের কেউ কেউ সশস্ত্র ফকিরদের পেছনে গণসমর্থনেরও অভাব দেখেন। আমরা ইংরেজদের রিপাের্ট বিশ্লেষণ করেও দেখাতে পারি যে, ফকির-সন্ন্যাসীদের পেছনে জনগণের ব্যাপক সমর্থন ছিল। ইংরেজ উৎখাতের লড়াই সূচিত ও পরিচালিত হয়েছে ফকির-সন্ন্যাসী নেতাদের দ্বারা। কিন্তু কেবল ফকির সন্ন্যাসীরাই যুদ্ধ করেনি, বিপুল সংখ্যক অত্যাচারিত কৃষক, সম্পত্তিচ্যুত জোতদার-জমিদার ও চাকুরীচ্যুত-বিক্ষুব্ধ বেকার সৈন্য এতে অংশগ্রহণ। এক সময় যােদ্ধার সংখ্যা দাঁড়ায় পঞ্চাশ হাজারে। ইংরেজদের নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং ধরে নেওয়া উচিত যে, এসব ঘটনায় জনগণ ফকিরদের পক্ষাবলম্বন করে এবং ওদেরকে নিরাপদে লুকিয়ে রাখে।৪০ একবার অসুস্থ পরাগ আলী রাজশাহীর পরশায় কিনু দেওয়ানের বাড়িতে আশ্রয় পেয়ে প্রাণ বাঁচাতে সমর্থ হন।৪১ প্রকৃতপক্ষে, ফকির-সন্ন্যাসীরা যেখানেই গেছে সেখানেই তাদের প্রতি সহযােগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে প্রজারা। পরবর্তীকালে পশ্চিমের কোনাে কোনাে ঐতিহাসিকও বিদ্রোহে ব্যাপক সংখ্যক জনগণের অংশগ্রহণের কথা পরােক্ষে হলেও স্বীকার করেছেন। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর জীবনীকার প্যাট্রিক টার্নবুল লিখেছেন, “…but holy men proved far more troublesome, playing as they did on local superstition and fears. For a time in 1773, it almost as if a state of civil war existed as groups of sepoys combed the countryside, and both Sannyasis and Fakirs gave ample proof that they were prepared to fight back. On several occassions isolated army units were ambushed, their officer killed.”৪২
তাছাড়া একদল ডাকাতের জন্য সারা দেশের প্রশাসন ভেঙ্গে পড়ার কথা নয়। মূলত সূচনাপর্বের সশস্ত্র ফকির-সন্ন্যাসীদের সাথে হাজার হাজার সর্বহারা প্রজা, নিঃস্ব প্রাক্তনসৈনিক, নির্যাতিত মানুষেরা যােগ দেয়। এ ছিল গণবিদ্রোহের উঁচু তরঙ্গগুলাের একটি। এতে সাময়িকভাবে বেসামাল হয়ে পড়ে দখলদার বাহিনী। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ, সহায়তা প্রদান ও নৈতিক সমর্থন ছিল বলেই ফকির ও সন্ন্যাসীদের লড়াই প্রায় চল্লিশ বছর অব্যাহত থাকে। ইংরেজের অত্যাচার, জমিদারদের অধিক হারে খাজনা আদায়, তালুকদার, ইজারাদার, নায়েব-গােমস্তাদের দাপটে অস্তিত্বের সংকটের মুখােমুখি হাজার হাজার প্রজা ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের মধ্যে মুক্তির স্বপ্ন না দেখলে স্বেচ্ছাপ্রণােদিত হয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত না। কোম্পানী কর্তৃপক্ষের মজনু-ভীতি যে কিরূপ প্রবল ছিল এবং সর্বশক্তি নিয়ােগ করেও যে তারাও তার আন্দোলন দমন করতে কিরূপ বিপুলভাবে ব্যর্থ হয়েছেন রেভিনিউ কমিটি থেকে প্রচারিত নিম্নলিখিত ইংরেজী বিবৃতিটি থেকে তার সুস্পষ্ট পরিচয় মিলছে। বলাবাহুল্য, এতে মজনুর বীরত্ব, তাঁর সাংগঠনিক নৈপুণ্য ও দূরদর্শিতার খুব প্রশংসা করা হয়েছে : “Although Majinoo has been overtaken and attacked with success in some former occasions, it has been found difficult in general to punish him for his depredations. The Zaminders are apprehensive of giving information respecting his motions and his followers are taught to disperse when pressed and unite again at appointed stations, it seldom happens that they can be apprehended.”৪৩
মূলত ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছিল বৃটিশদের বিরুদ্ধে সীমিত আকারের গণযুদ্ধ, যাতে অংশগ্রহণ করে জনগণের একটি দল, অন্যরা সমর্থন করে। হেস্টিংস নিজেও এদেরকে সম্প্রদায় হিসেবে স্বীকার করে তাদের তৎপরতাকে সরকারের বিপক্ষে যুদ্ধ অভিহিত করে লিখেন: “সম্প্রদায় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত বাংলার ডাকাতগণ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত।”৪৪
উপমহাদেশীয় গবেষকদের মধ্যে অসিতনাথ চন্দ্র যথাযথ প্রেক্ষিত থেকে এ বিদ্রোহের অন্তর্গত শক্তি ও প্রাণাবেগ চিহ্নিত করেছেন: “The Sannyasis and the Fakirs might have been working for lofty ideals – patriotism, religion, liberty – but the time was not ripe enough to reap rich harvest. Accepting that some of the incursion were acuated by these ideals these may, at best, be termed the forrunner of the first effort to free the country from the British yoke a hundred years later – but it was too late then.’৪৫
এই সমস্ত আলােচনার প্রেক্ষিতে ফকির-সন্ন্যাসীদের বৃটিশ বিরােধী লড়াই সম্পর্কে যে বিষয়গুলি মূলত উঠে আসে তা হল :
ক) লড়াইয়ের লক্ষ্য ছিল ইংরেজদের উৎখাত, জমিদার-ইজারাদার-গােমস্তা শ্ৰেণীটির ক্ষমতা ক্ষুন্ন করে সাধারণ প্রজাদের ওপর চেপে বসা কর ও নির্যাতনের বােঝা লাঘব।
খ) শ্রেণী-স্বার্থ রক্ষার প্রয়ােজনে এ লড়াইয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় স্থানীয় জমিদার, ইজারাদার, গােমস্তা, বণিক-মহাজনের।
গ) ফকির ও সন্ন্যাসীদের সশস্ত্র সংগ্রামের অনেক আগে থেকে সন্ন্যাসীদের বিভিন্ন গােষ্ঠী প্রথমে মারাঠা বাহিনীর সাথে, পরে স্বাধীনভাবে বাংলায় ডাকাতি, লুটতরাজ করতাে।
ঘ) ফকির ও সন্ন্যাসীরা ভিন্ন ভিন্ন কারণে বৃটিশ-বিরােধী লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে, যদিও উভয়ের লক্ষ্য ছিল এক। পরবর্তী পর্যায়ে লড়াই থেকে সরে দাঁড়ায় সন্ন্যাসীরা। এটি প্রথম বৃটিশ-বিরােধী সশস্ত্র লড়াই ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম একটি কারণ।
আমাদের প্রয়ােজন এই প্রেক্ষিতটুকু মনে রেখে ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ইতিহাস পুনর্গঠনে অগ্রসর হওয়া, যাতে অতি আবেগে সত্য চাপা না পড়ে। তেমনি প্রতিটি দলের স্বস্ব অবস্থান, গতি-প্রকৃতি ও অবদান সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। গােটা ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে ফকির ও সন্ন্যাসী যােদ্ধাদের আত্মত্যাগের আখ্যানের স্থান নির্দিষ্ট করতে গিয়ে অসিতনাথ চন্দ্র মজনু শাহ সম্পর্কে লিখেছেন, ‘The Majnu’s operations, unfruitful though it was at the time, might be seriously considered as precursor to the freedom movement that took place later in time … It would not be far from the truth to say that we see history in the making from his activities.’ ৪৬
অথচ স্বাধীনতা যুদ্ধের শত শত পৃষ্ঠার ইতিহাসে ফকির-সন্ন্যাসীদের সংগ্রামের নামমাত্র উল্লেখ থাকে; কখনাে এক বা দু’প্যারা, বড়জোর দু’এক পৃষ্ঠার সাম্রাজ্যবাদী বিবরণ। ইংরেজ দখলদারিত্বের সুচনাপর্বের কঠিন সময়ে যখন শাসক শ্রেণীর একটি অংশ ইংরেজের বশীভূত, সামন্তশ্রেণী দখলদারদের একান্ত অনুগত রাজস্ব-সংগ্রাহক কর্মচারী মাত্র, তখন সাধারণ প্রজাদের সমর্থন ও কখনাে কখনাে সক্রিয় অংশগ্রহণে ফকির-সন্ন্যাসীরা মজনু শাহের নেতৃত্বে যে তীব্র প্রতিরােধ গড়ে তােলেন তার মূল্য ও প্রভাব অপরিসীম। নিজেদের যথাযথভাবে চেনার জন্য, স্বাধীনতার লক্ষ্যে পূর্ব-পুরুষের আত্মত্যাগের গৌরব গাঁথায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য সেই আত্মত্যাগের বয়ান উদ্ধার করা অত্যন্ত জরুরী।
আঠারাে শতকের শেষার্ধে এ দেশে ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে যাঁদের সংঘর্ষ হয়েছে তা প্রধানত এদেশীয় নবাব ও রাজন্যবর্গের সঙ্গে। সেখানে জনসাধারণের, সাধারণ কৃষক শ্রমিকের ভূমিকা প্রায় নিষ্ক্রিয় ছিল বললেই চলে। কিন্তু ফকির সন্ন্যাসীরা তাঁদের আন্দোলনের সমর্থনে দেশের সাধারণ কৃষক কারিগরদের অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন, এটা তাঁদের পক্ষে কৃতিত্বের বিষয়। প্রথম গেরিলা যুদ্ধের রণকৌশল তারাই দেখান। তাদের কোনও কোনও অস্ত্র বিপক্ষীয়দের ত্রাসের কারণ হয়েছিল। মজনু শাহের হাতে ‘ভেলা’ নামে এমন এক আগ্নেয়াস্ত্র থাকত যার থেকে অনেক দূর পর্যন্ত অগ্নি নিক্ষেপ সম্ভব হত।
“..ইংরেজ শাসনের পূর্বে পাঠান এবং মােগল শাসনকালেও কৃষকের সশস্ত্র সংগ্রামের অসংখ্য কাহিনী ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়াইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সেই সকল সংগ্রাম ছিল একান্তভাবেই স্থানীয় গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের মধ্য দিয়াই সর্বপ্রথম ভারতের কৃষক বিশাল অঞ্চল (সমগ্র পূর্ব-ভারত) ব্যাপিয়া একটা বিদ্রোহের আকারে শাসকগােষ্ঠীর সহিত শক্তির দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়াছিল…।”৪৭
এই বিদ্রোহ কোম্পানির পক্ষে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার কারণ হলেও এর ফলে কোম্পানির ঔপনিবেশিক চরিত্র ও কৃষকবিরােধী নীতির কোনাে পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু এই বিদ্রোহ ছিল কোম্পানির অপশাসন ও জনবিরােধী নীতির বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ এবং বাংলার জনগণ যে তাদের ঔপনিবেশিক শাসকদের চরিত্র বুঝতে ভুল করেনি, এই বিদ্রোহে তা প্রমাণিত হয়েছিল। ড. অতীশ দাশগুপ্ত লিখেছেন, “Though the insurgents could not turn the tide, they did not fail….to identify their main enemy and consequently, they hardly made any major compromise with the colonial rulers.”৪৮
ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ প্রমাণ করেছিল যে, অপশাসন ও অর্থনৈতিক শােষণের বিরুদ্ধে হিন্দু ও মুসলমানের যৌথ আন্দোলন সম্ভব। এটা ঠিক, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও বােঝাপড়া বিদ্রোহের শেষ পর্বে অক্ষুন্ন ছিল না এবং মতভেদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তবু সামগ্রিকভাবে এক আদর্শগত ঐক্য উভয় সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ করেছিল। সর্বোপরি এর প্রভাব দীর্ঘকাল ধরে ভারতের, বিশেষত বাংলার জনসাধারণকে বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রেরণা দান করেছে। এর “একশত বৎসর পরে বাংলাদেশে যে সন্ত্রাসবাদী সংগ্রাম দেখা দিয়াছিল, বহু দিক হইতে এই সন্ন্যাসী-বিদ্রোহই ছিল তাহার এক অগ্রদূত।”৪৯
তথ্যসূত্র :
১. R C Majumder, History of Freedom Movement in India, Vol-1, Farma K L M, Kol., 1971, P-68-70.
২. চৌধুরী শামসুর রহমান, বাংলার ফকীর বিদ্রোহ, ইসলামি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ৯-১০।
৩. দেওয়ান নূরুল আনােয়ার হােসেন চৌধুরী, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্মৃত ইতিহাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ.৫।
৪. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৬শ খন্ড, ২য় ভাগ, ১৯৯৬, পৃ. ১০৮।
৫. Mohammad Enamul Hoque, A History of Sufism in Ben| gal, Dacca, 1975, P. 152. ।
৬. সৈয়দ আনােয়ার হােসেন ও মুনতাসির মামুন সম্পাদিত, বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরােধ আন্দোলন, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সােসাইটি, ১৯৮৬, পৃ.১৮।
৭. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৬শ খন্ড, ২য় ভাগ, ১৯৯৬, পৃ. ১০৮।
৮. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৬শ খন্ড, ২য় ভাগ, ১৯৯৬, পৃ. ১০৮।
৯. Edward Thompson & G.T. Garratt, Rise and Fulfilment of British rule in India, Central Book Dep.Allahabad, 1973, P. 70.
১০. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, বুক ওয়ার্ল্ড, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ২৭।
১১. Capt. Rennel’s letter to the collector 30th October, 1766, Long’s Selection, সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, বুক ওয়ার্ল্ড, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ২৭।
১২. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৬শ খন্ড, ২য় ভাগ, ১৯৯৬, পৃ. ১০৯।
১৩. নােয়াখালি ডিস্ট্রিক্ট গেজেট, পৃ. ২১।
১৪. অসিতনাথ চন্দ্র, দ্য সন্ন্যাসী রিবেলিয়ন, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ৮৯-৯০।
১৫. সৈয়দ আনােয়ার হােসেন ও মুনতাসির মামুন সম্পাদিত, বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরােধ আন্দোলন, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সােসাইটি, ১৯৮৬, পৃ.২৭।
১৬. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, বুক ওয়ার্ল্ড, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৩১।
১৭. Maulavi Abdul Wali, Notes on the Fakirs of Baliya Dighi in Dinajpur, Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1903, P. 62-63.
১৮. মুহম্মদ আবু তালিব, ফকীর নেতা মজনু শাহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ. ৭।
১৯. ওয়াকিল আহমেদ, বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৮৫, পৃ. ৮৬।
২০. দেওয়ান নূরুল আনােয়ার হােসেন চৌধুরী, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্মৃত ইতিহাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৫২-৫৩।
২১. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, বুক ওয়ার্ল্ড, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ.৪৬-৪৭।
২২. জে এম ঘােষ, সন্ন্যাসী অ্যান্ড ফকীর রেডার্স ইন বেঙ্গল, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপাে, কলকাতা, ১৯৩০, পৃ. ১০৯।
২৩. রতনলাল চক্রবর্তী, ফকীর সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ১৭৬৩-১৮০০; সৈয়দ আনােয়ার হােসেন ও মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত, বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরােধ আন্দোলন, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সােসাইটি, ১৯৮৬।
২৪. জে এম ঘােষ, সন্ন্যাসী অ্যান্ড ফকীর রেডার্স ইন বেঙ্গল, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপাে, কলকাতা, ১৯৩০, পৃ. ৬২।
২৫. জে এম ঘােষ, সন্ন্যাসী অ্যান্ড ফকীর রেডার্স ইন বেঙ্গল, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপাে, কলকাতা, ১৯৩০, পৃ. ৪৭।
২৬. জে এম ঘােষ, সন্ন্যাসী অ্যান্ড ফকীর রেডার্স ইন বেঙ্গল, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপাে, কলকাতা, ১৯৩০, পৃ. ১২৪।
২৭. জে এম ঘােষ, সন্ন্যাসী অ্যান্ড ফকীর রেডার্স ইন বেঙ্গল, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপাে, কলকাতা, ১৯৩০, পৃ. ১০।
২৮. জে এম ঘােষ, সন্ন্যাসী অ্যান্ড ফকীর রেডার্স ইন বেঙ্গল, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপাে, কলকাতা, ১৯৩০, পৃ.১০২।
২৯. জে এম ঘােষ, সন্ন্যাসী অ্যান্ড ফকীর রেডার্স ইন বেঙ্গল, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপাে, কলকাতা, ১৯৩০, পৃঃ ৯৪।
৩০. প্রভাসচন্দ্র সেন, বগুড়ার ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, বগুড়া, ৩৩৬, পৃঃ ১৩৮-৩৯।
৩১. জে এম ঘােষ, সন্ন্যাসী অ্যান্ড ফকীর রেডার্স ইন বেঙ্গল, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপাে, কলকাতা, ১৯৩০, পৃঃ ৮৪-৮৫।
৩২. হায়দার আলী চৌধুরী, পলাশী যুদ্ধোত্তর আজাদী সংগ্রামের পাদপীঠ, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭, পৃ.১২।
৩৩. অসিতনাথ চন্দ্র, দ্য সন্ন্যাসী রিবেলিয়ন, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ.১০৬।
৩৪. সিরাজুল ইসলাম, ফকির ও সন্ন্যাসী আন্দোলন প্রসঙ্গে’, দৈনিক বাংলা, ১৭ নভেম্বর, ১৯৭২, ঢাকা।
৩৫. অসিতনাথ চন্দ্র, দ্য সন্ন্যাসী রিবেলিয়ন, কলকাতা, ১৯৭৭,পৃ. ১৫২-৫৩।
৩৬. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম,বুক ওয়ার্ল্ড, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ.২২।
৩৭. মেসবাহুল হক,পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীলবিদ্রোহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৮২ পৃ. ৮৬।
৩৮.রতনলাল চক্রবর্তী, ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ১৭৬৩-১৮০০; সৈয়দ আনােয়ার হােসেন ও মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত, বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরােধ আন্দোলন, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সােসাইটি, ১৯৮৬।
৩৯. জে এম ঘােষ, সন্ন্যাসী অ্যান্ড ফকীর রেডার্স ইন বেঙ্গল, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপাে, কলকাতা, ১৯৩০, পৃ. ৭২-৭৩; মুহম্মদ আবু তালিব, ফকীর নেতা মজনু শাহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮,পৃ. ৬৬-৬৭।
৪০. দেওয়ান নূরুল আনােয়ার হােসেন চৌধুরী, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্মৃত ইতিহাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২২৪।
৪১. মুহম্মদ আবু তালিব, ফকীর নেতা মজনু শাহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮,পৃ. ৮৯।
৪২. প্যাট্রিক টার্নবুল, ওয়ারেন হেস্টিংস, লন্ডন, ১৯৭৫,পৃ.৬৪।
৪৩. জে এম ঘােষ, সন্ন্যাসী অ্যান্ড ফকীর রেডার্স ইন বেঙ্গল, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপাে, কলকাতা, পৃঃ ৯১।
৪৪. রতনলাল চক্রবর্তী, ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ১৭৬৩-১৮০০; সৈয়দ আনােয়ার হােসেন ও মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত, বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরােধ আন্দোলন, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সােসাইটি, ১৯৮৬।
৪৫. অসিতনাথ চন্দ্র, দ্যা সন্ন্যাসী রিবেলিয়ন, কলকাতা, ১৯৭৭,পৃ.৬৪।
৪৬. অসিতনাথ চন্দ্র, দ্যা সন্ন্যাসী রিবেলিয়ন, কলকাতা, ১৯৭৭,পৃ.১০১-১০৫।
৪৭. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, বুক ওয়ার্ল্ড, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৫৬।
৪৮. অতীশ দাশগুপ্ত, দ্য ফকির অ্যান্ড সন্ন্যাসী আপরাইজিংস, কলকাতা, পৃ. ৫০।
৪৯. এল হাচিনসান, এম্পায়ার অফ দ্য নবাবস, কলকাতা, পৃ. ৯২।

 নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা
নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা




