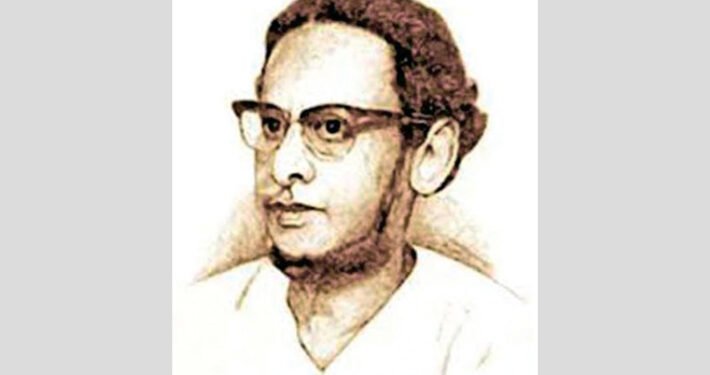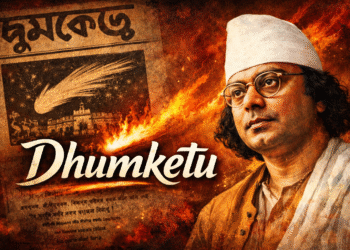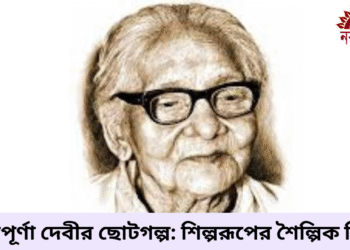উনিশ শতকের প্রথমার্ধে শুরু হলেও এ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বাংলার রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সঙ্গে বাঙালি মুসলমানের জাগরণ সংযুক্ত হয়। অর্থ ও তাৎপর্যে এ জাগরণ চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে বিশ শতকের তৃতীয় দশকে। এ পর্যায়ে অন্যতম কর্ণধার ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। এরপর অর্থাৎ চল্লিশের দশকে ফররুখ আহমদের (১৯১৮-৭৪) উত্থান। প্রারম্ভে তিনি পরিষ্কারভাবে কোনাে দল বা মতাদর্শ গ্রহণ না করলেও তখন তিনি বাম ঘেঁষা ছিলেন। কবিতায় তিনি নির্যাতিতদের পক্ষে লড়াই করেছেন। তখন শােষণ নিপীড়ন সামাজিক বন্ধ্যাত্ব ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অনেক যশস্বী কবিকণ্ঠই সােচ্চার ছিলেন। তাদের বেশিরভাগের ভাব ও ভাষায়, চিন্তা ও আদর্শের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই স্ববিরােধিতার ছাপ পরিলৰিত হয়েছে। কিন্তু কবি ফররুখ আহমদ একাধারে পৌরুষ দীপ্ত ছন্দের স্রষ্টা, সামাজিক অনগ্রসরতা ও শােষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিরামহীন কণ্ঠ এবং আদর্শের প্রতি প্রণাতীত অটল। ঐতিহ্যপ্রিয় কবি হিসেবে চিহ্নিত হয়েও এজন্যেই তিনি সার্বজনীন কবি এবং মানব-প্রেমিক ব্যক্তিত্ব।
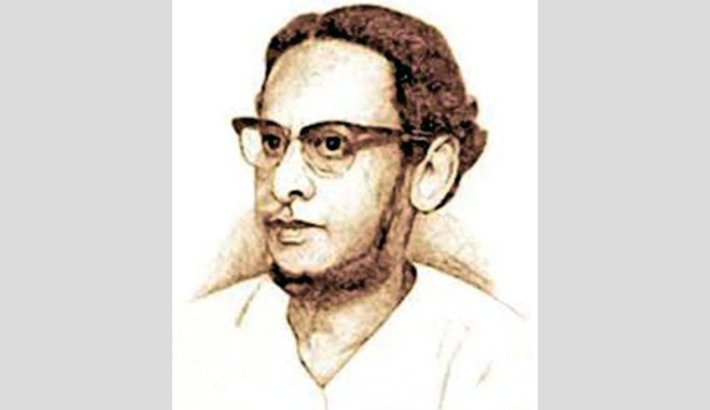
১৯১৮ সালের ১০ জুন যশােহর ও ফরিদপুর জেলার সীমান্ত মাঝআইল গ্রামে ফররুখ আহমদের জন্ম। তার লেখাপড়া শুরু হয় গ্রামের পাঠশালায়। ঘরে তিনি আরবি-ফারসিও শেখেন। পিতা সৈয়দ হাতেম আলি, মাতা রওসন আখতার। পিতা ছিলেন পুলিশ ইন্সপেক্টর। পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত করে ফররুখ কলকাতার মডেল এম.ই. স্কুলে ভর্তি হন। কলকাতার তালতলা এলাকায় ইউরােপীয়ান এসাইলাম লেনে স্কুলটি অবস্থিত ছিল। এরপর তিনি ভর্তি হন বালিগঞ্জ হাইস্কুলে। এ স্কুলে তখন প্রধান শিক্ষক ছিলেন খ্যাতনামা কবি ও সুবিখ্যাত ‘বিধানবী’ গ্রন্থের রচয়িতা গােলাম মােস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪)। এরপর তিনি খুলনা জেলা স্কুলে ভর্তি হয়ে সেখান থেকে ১৯৩৭ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। খুলনা জেলা স্কুলে তার শিক্ষক ছিলেন কবি আবুল হাশেম (১৮৯৮-১৯৮৫)। খুলনা জেলা স্কুলের ম্যাগাজিনেই ফররুখের প্রথম কবিতা ছাপা হয়। তার ফলেই তার শিক্ষক আবুল হাশেম তার মধ্যে প্রতিভার স্বাক্ষর লক্ষ্য করেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবুল ফজলও (১৯০৩-৮৩) এ সময় তার শিক্ষক ছিলেন। ১৯৩৯ সালে তিনি কলকাতা রিপন কলেজ থেকে আই.এ. পাশ করেন। এরপর তিনি প্রথমে দর্শন ও পরে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে প্রথমে কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ ও পরে সিটি কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু নানা কারণে তিনি আর পড়াশােনা চালাতে পারেননি।
ফররুখ আহমদের কলেজ জীবনে শিক্ষক ছিলেন প্রখ্যাত কবি ও সমালােচক বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) ও সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-১৯৮৫)। মেধাবী ছাত্র ও প্রতিভাবান কবি হিসেবে তিনি এঁদের প্রিয় পাত্রে পরিণত হন। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হিসেবে ফররুখ আহমদকে সে সময় অনেকেই ‘দ্বিতীয় আশুতােষ’ নামে আখ্যায়িত করতেন। তার সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় (১৯২১-৯২), ফতেহ লােহানী (১৯২৬-৭৫), শিল্পী কামরুল হাসান, কবি সুভাষ মুখােপাধ্যায় (১৯২০-২০০৩) প্রমুখ। প্রমথনাথ বিশী তার কবিপ্রতিভায় চমৎকৃত হয়ে তাঁকে ‘তরুণ সেক্সপীয়র’ নামে অভিহিত করেন। বুদ্ধদেব বসু তার বিখ্যাত কবিতা পত্রিকায় ফররুখ আহমদের কয়েকটি কবিতা ছাপেন, তখন সবেমাত্র তিনি কলেজের ছাত্র। কবিতা পত্রিকায় সেকালে কবিতা ছাপা হওয়া ছিল দুর্লভ সৌভাগ্যের ব্যাপার। কলেজে পড়াকালেই ফররুখ এ বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী হন। এভাবে অতি অল্প বয়সে আমরা বাংলা সাহিত্যের এক কালজয়ী অমর প্রতিভার বর্ণাঢ্য আবির্ভাব লক্ষ্য করলাম। অবশ্য পারিবারিকভাবেই তিনি সাহিত্য চর্চার পরিবেশ পেয়েছিলেন। তার কাকা কাশেম আলি সাহিত্য চর্চা করতেন, বড়ভাই সিদ্দিক আহমদ গান বাঁধতে পারতেন। আর ছােটো ভাইয়ের আকর্ষণ ছিল চিত্র অঙ্কনের দিকে।
(১)
প্রথম মুদ্রিত কবিতা ‘রাত্রি’ (১৩৪৪) নামক সনেটটি লেখার মাধ্যমে ফররুখ আহমদ কবি হিসেবে কাব্য অঙ্গনে প্রবেশ করেন। এ সময় তাঁর কবিতার ছন্দ ও বলিষ্ঠতা সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম দিকের কাব্য রচনায় তিনি মূলত রােমান্টিক মানসিকতার পরিচয় দেন। তাঁর রূপকল্প ও উপমা উপস্থাপনা শব্দচয়ন ও ভাবের সংস্কৃতি ক্রমশ মৌলিকতায় সমৃদ্ধ হতে থাকে। সৃজনশীল কবিত্ব শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শের অপ্রতিরােধ্য রূপরেখায় তিনি আবদ্ধ হয়ে পড়েন। সে যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বলয়ের মধ্যে অবস্থান করে এই প্রভাবের অনুকূলে বিচরণ করাই স্বাভাবিক ছিল। মুসলিম জাতীয়তাবাদের ঐতিহাসিক বিকাশ লগ্নে দায়িত্ববান কবি তাই নবজাগরণের বাণী শুনিয়েছেন। দৃপ্ত কণ্ঠে গেয়েছেন মানবতার কালজয়ী সঙ্গীত। ১৯৪৭ সালের আগে কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে ফররুখ আহমদ সম্পর্কে আলােচনা কথিকা প্রচার করা হয়। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, তিনি তৎকালে বাংলা কাব্যের জগতে কতখানি আলােড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। তার আগে নবীন মুসলমান কবিদের মধ্যে এক কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) সম্পর্কে কলকাতা বেতারে আলােচনা শ্রুত হয়েছিল।
খুলনা জেলা স্কুল ম্যাগাজিনে ১৯৩৭ সালে ফররুখের প্রথম কবিতা ছাপা হবার পর একই বছরে ‘বুলবুল’ ও ‘মাসিক মােহাম্মদী’তে তাঁর কবিতা ছাপা হয়। এছাড়াও ‘আজাদ’, ‘সওগাত’, ‘দিগন্ত’, ‘মৃত্তিকা’, ‘অরণি’, ‘পরিচয়’ প্রভৃতি পত্রিকায় একের পর এক তার বহু কবিতা ছাপা হয়। তাঁর প্রকাশিত রচনাবলী—কবিতা সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪), আজাদ করাে পাকিস্তান (১৯৪৬), সিরাজাম মুনীরা (১৯৫২), মুহূর্তের কবিতা (১৯৬৩), কাফেলা (রচনাকাল ১৯৪৩-৫৮, প্রকাশকাল ১৯৮০), হে বন্য স্বপ্নেরা (১৯৭৬), দিল(বা (১৯৯৪), হাবেদা মরুর কাহিনী (১৯৮১), নির্বাচিত কবিতা (১৯৯২)। মহাকাব্য হাতেম তায়ী (১৯৬৬)। গীতিনাট্য নৌফেল ও হাতেম (১৯৬১)। ব্যঙ্গ কবিতা অনুস্বার (১৯৪৪-৪৬), বিসর্গ (১৯৪৬৪৮), ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক কাব্য (১৯৯১), হালকা লেখা, তসবির নামা, রসরঙ্গ, ধােলাই কাব্য। গান রক্ত গােলাব, মাহফিল (হামদ ও নাত), কাব্য-গীতি। নাটক রাজ-রাজড়া (গদ্য ব্যঙ্গ নাটিকা)। শিশু সাহিত্য পাখির বাসা (১৯৬৫), হরফের ছড়া (১৯৬৮), নতুন লেখা (১৯৬৯), ছড়ার আসর-১ (১৯৭০), ছড়ার আসর-২, ছড়ার আসর-৩, চিড়িয়াখানা, ফুলের জলসা, কিসসা কাহিনী, সাঁঝ সকালের কিত্সা, আলােক লতা, খুশীর ছড়া, মজার ছড়া, পাখীর ছড়া, রংমশাল, জোড় হরফের খেলা, পােকামাকড়। গল্প ফররুখ আহমদের গল্প (১৯৯০)। পাঠ্যবই নয়া জামাত-প্রথম ভাগ (১৯৫০), নয়া জামাত-দ্বিতীয় ভাগ (১৯৯০), নয়া জামাত-তৃতীয় ভাগ (১৯৫০), নয়া জামাত-চতুর্থ ভাগ (১৯৫০)। অনুবাদ কাব্য কুরআন মঞ্জুষা, ২. ইকবালের নির্বাচিত কবিতা।
এছাড়া ফররুখ আহমদের কিছু প্রবন্ধ রয়েছে যা আজও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। তাঁর রচিত বই-এর তালিকাও সম্পূর্ণ নয়, এখনাে তার নতুন নতুন বইয়ের পান্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। ফররুখ আহমদের রচিত একটি অসমাপ্ত উপন্যাসের পান্ডুলিপিও পাওয়া গেছে।
শুরুতেই বলা হয়েছে, ফররুখ আহমদ তাঁর সাহিত্য চর্চার প্রথম পর্যায়ে (১৯৩৫-১৯৪১) আকৃষ্ট হয়েছিলেন সমকালীন বামপন্থী রাজনীতির প্রতি। এ ক্ষেত্রে তিনি এম এন রায়ের সমাজতান্ত্রিক মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হন। কবিতা, পরিচয়, অরণি, নবযুগ, নবশক্তি প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তার সাম্যবাদী অনুভবজাত এ কালের কবিতা। অগ্রন্থিত এসব কবিতার কয়েকটি সংকলিত হয়েছে কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত ‘হে বন্য স্বপ্নেরা’ (১৯৭৬) গ্রন্থে। ভূমিকায় সম্পাদক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী লিখেছেন,
“এসব কবিতার নিবিড় নিপুণ ধ্বনি ও ছন্দের আনন্দ মনে করিয়ে দেয় আরেকজন বামপন্থী কবির কথা— যিনি ফররুখেরই সমবয়সী—সুভাষ মুখােপাধ্যায়।”
এরপর কবির চেতনালােকে পরিবর্তন ঘটে। “টেইলর হােস্টেলের সুপারিনটেনডেন্ট বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ও ফুরফুরার পীর সাহেবের খলিফা আবদুল খালেকের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপের পর ফররুখ আহমদ ইসলামী আদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়েন।” এ সময়ে রাজনীতির অঙ্গনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি ক্রমে বৃদ্ধি পায়। কলকাতায় ১৯৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সােসাইটি, কবি এর সঙ্গে যুক্ত হন। পশ্চাৎপদ নির্যাতিত বাঙালি তথা ভারতীয় মুসলমানদের স্বাধীন স্বদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নরূপে ‘পাকিস্তান’ তাকে আকর্ষণ করে। কবি তালিম হােসেন ‘ফররুখ আহমদ ও আমি’ শীর্ষক প্রবন্ধে ফররুখ প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন, সেটা খুবই গুরুত্ববহ “আমাদের আজকের তরুণ বংশধররা জানে না বা তাদের জানাবার কোনাে ব্যবস্থা হয়নি যে, এদেশে ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন পাকিস্তানী আন্দোলনের ফলশ্রুতি নয় বরং তার ঠিক উল্টোটাই ঐতিহাসিক সত্য।” (উষালােকে, ফররুখ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮৯, ঢাকা)। ফররুখ ও শেষ-বিচারে পাকিস্তান আন্দোলনের কবি নন। তাঁর সমগ্র কবিতাবলি সেই সাক্ষই দিচ্ছে।
শব্দ, ছন্দ, কাব্যভাষা ও বিষয়-সব মিলিয়ে ফররুখ আহমদের কবিতাগুচ্ছ ও গ্রন্থসমূহ এত অনুপম যে, যার তুলনা করা যায় ফররুখের পূর্বসূরী শ্রেষ্ঠ ক’জন কবির আলােড়ক কবিতাগ্রন্থের সঙ্গে। জীবনানন্দ দাশের ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘প্রথম’, বিষ্ণু দে-র ‘উর্বশী ও আর্টেমিস’, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অর্কেস্ট্রা’, অমিয় চক্রবর্তীর ‘খসড়া’, অজিত দত্তের ‘কুসুমের মাস’, বুদ্ধদেব বসুর ‘বন্দীর বন্দনা প্রভৃতির সঙ্গে। ফররুখ আহমদের প্রথম কবিতা গ্রন্থ ‘সাত সাগরের মাঝি’র দিকে একটু গভীরভাবে নজর দিলেই বুঝা যাবে—তাতে কবি কেবল নিজস্ব কাব্য বিষয়ই খুঁজে পাননি, তার প্রকাশের উপযুক্ত কাব্য ভাষাও আবিষ্কার করেছেন। সেখানে নজরুল ইসলাম, মােহিতলাল মজুমদার (১৮৮২-১৯৫২), জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-৮৮), অজিত দত্ত (১৯০৮-৭৯), বিষ্ণু দে-র (১৯০৯-৮২) দূর রণন নেই। যদিও যে কোনাে প্রকৃত কবির মত পূর্বজদের শিক্ষা তিনি পুরাে কাজে লাগিয়েছেন। তাই জীবনানন্দ আর প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমুদ্রচারণা থেকে ফররুখের সমুদ্র সফর স্বতন্ত্র হয়ে গেছে। নজরুলের ইসলামী পুনরুজ্জীবন থেকে ফররুখের ইসলামি পুনরুজ্জীবনের স্বর-স্বাদ আলাদা। বিষ্ণু দে-র ইতিহাস
পুরাণের প্রয়ােগ থেকে ফররুখের ইতিহাস-পুরাণ ব্যবহার ভিন্ন রকম। সবমিলিয়ে, ‘সাত সাগরের মাঝি’ এমন এক কাব্যগ্রন্থ, যাকে আমাদের বিবেচনায় ফররুখ আহমদও অতিক্রম করতে পারেননি।
১৯৪৩-৪৪ সালে রচিত এবং প্রধানত সওগাত’ ও ‘মােহাম্মদী’তে প্রকাশিত এই চেতনাজাত ১৯টি কবিতা নিয়ে ১৯৪৪ সালে কলকাতায় প্রকাশিত হয় ফররুখ আহমদের কাব্যগ্রন্থ ‘সাত সাগরের মাঝি’—আধুনিক বাংলা কাব্যে এক অতি বিশিষ্ট সংযােজন। সামগ্রিক বিচারে একটি উত্তম শিল্পকর্ম। আরব্য উপন্যাসের সিন্দাবাদকে তিনি অপরাজেয় উচ্ছল জীবনের প্রতীকরূপে ব্যবহার করে যে কাব্য সৃষ্টি করেছেন, নিঃসন্দেহে তরুণ সমাজের জন্যে তা নতুন সমাজ-জীবন নির্মাণের আহবান। সবল আশাবাদ কাব্যটির মূল কথা। কাব্যটির আরম্ভ চমৎকার—
“কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ, শুনছি আবার নােনা দরিয়ার ডাক, ভাসে জোওয়ার মওজের শিরে সফেদ চাদির তাজ, পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ বয়ে আনে নােনা দরিয়ার ডাক।”
এ কাব্যের বিশ্লেষণে সুনীলকুমার মুখােপাধ্যায় বলেন, “সাত সাগরের মাঝি কাব্যের অধিকাংশ কবিতায়ই কবির ঐতিহ্যপ্রীতি ও ইসলামী ধর্মাদর্শের মহত্ত্বে অকুণ্ঠ বিশ্বাস ও অনুরাগের পরিচয় পরিস্ফুট। এ ঐতিহ্য ও ধর্মাদর্শের আলােতে তিনি আধুনিক মুসলমানদের জীবন-সমস্যা সমাধানের পথ যেমন খুঁজেছেন, তেমনি প্রাণের একটি অপরূপ সৌন্দর্য ও ঐধর্য পিপাসা নিবৃত্ত করার চেষ্টা পেয়েছেন।”
আধুনিক মানসের সাথে ঐতিহ্যবােধের দ্বন্দ্ব অনেক ক্ষেত্রে কবিতার আবেদনকে ক্ষণস্থায়ী করে তােলে। কিন্তু ফররুখ আহমদের কবিতায় ঐতিহ্যলালিত মূল্যবােধ এবং কালিক যন্ত্রণার মধ্যকার দ্বন্দ্ব মুখ্য হয়ে ওঠেনি তাঁর পরিণত জীবনবােধের কারণেই। সবকিছু মিলেমিশে এমন একাকার হয়ে গেছে যে, শিল্প নির্মাণের অসাধারণ ক্ষমতা না থাকলে তা কখনােই সম্ভব হতাে না।
তিরিশােত্তর বাংলা কবিতায় যে অস্থিরতার উন্মাদনা সিদ্ধান্তহীন জীবন-জিজ্ঞাসায় প্রতিনিয়ত কাতর হয়ে উঠেছিল, সেই পাশ্চাত্যশাসিত অবক্ষয়বােধের আবেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসা যে-কোনাে কবির পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফররুখ আহমদ এই পরিপ্রেক্ষিতের অধিবাসী হয়েও নিজের জন্য একটা নতুন মানসপটভূমি নির্মাণ করেছিলেন। আদর্শবােধের ইঙ্গিত মাঝেমধ্যে প্রধান হয়ে উঠলেও কবিতার প্রতীক এবং বিষয়বস্তুকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গ্রহণ করেছিলেন প্রাক-ইসলামি রূপকথা থেকে। রূপকথার রহস্যময় ভাবাবহের মধ্যে জৈবনিক সত্য আরােপ করায় বিষয়ভাবনায় যেমন নতুনত্ব এসেছে, তেমনি বাংলা কবিতার শৈল্পিক উৎকর্ষের ক্ষেত্রে এসেছে অভাবনীয় সাফল্য। মানুষের প্রতি অপরিসীম মমত্ববােধ এবং ঐতিহ্য ভাবনার নতুনত্বে তিনি কবিতার অসাড় ভাবাকাশে নতুন স্পন্দন সঞ্চারিত করেছেন। আরবি-ফারসি শব্দ বাংলা কবিতায় যথার্থ আসন লাভ করে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮২-১৯২২) হাতে। মােহিতলাল মজুমদার (১৮৮২-১৯৫২) এবং নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) হাতে তার সম্মান বৃদ্ধি পায় বহুগুণে। কিন্তু নজরুলের পূর্বে প্রকৃতপক্ষে শব্দের অন্তর্নিহিত শক্তি অর্জিত হয়নি। তিরিশােত্তর কবিতায় এই অনিবার্য ধারাকে অতিক্রম করতে চাইলেন কবিরা। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) তৎসম শব্দের প্রয়ােগবাহুল্যকে নিজস্ব কাব্যচিন্তার যথার্থ বাহন হিসেবে গ্রহণ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে এর স্থবিরতা কবিদের কাছে আর গ্রহণযােগ্য মনে হয়নি। এই আপাত-পরিত্যাজ্য শব্দসম্পদ নিয়েই ফররুখ আহমদ তার ‘সাত সাগরের মাঝি’ কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। শব্দের অন্তর্গত যে শক্তি প্রয়ােগের চাতুর্যে অসামান্য উদ্দীপনায় ঝলসে ওঠে তরবারির মতাে, ফররুখ আহমদ সেই শক্তি স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিষয় নির্বাচনের সাথে শব্দচয়নের আশ্চর্য সমন্বয় তাঁর কবিতাকে নতুন দিগন্তের বার্তাবহ করে তুলেছে। প্রয়ােগের এই পরীক্ষা। তার কবিতাকে যেমন দান করেছে নিজস্বতা, তেমনি শব্দ-অতিরেকে ব্যঞ্জনায় তার স্বপ্নচারিতার রহস্যময় পটভূমি সবকিছুকে অতিক্রম করে হয়ে উঠেছে আনন্দময় শিল্পের অনুষঙ্গ।
‘সাত সাগরের মাঝি’ কাব্যগ্রন্থটি ফররুখ আহমদ উৎসর্গ করেন দার্শনিক মহাকবি আল্লামা ইকবালের অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে “নতুন পথের মােহে তৃপ্তিহীন তােমার অন্বেষা পাড়ি দেয় মরু, মাঠ, বন, / অর্থই দরিয়া তীর। হে বিজয়ী! তবু অনুক্ষণ / ধান করাে কোন পথ, কোন রাত্রি অজানা তােমার, / এক সমুদ্রের শেষে জাগে অন্য সমুদ্র স্বনন! / যেথা ক্ষীয়মান মৃত পাহাড়ের ঘুমন্ত শিখরে / জীবনের ক্ষীণসত্তা মূছাতুর, অসাঢ়, নিশ্চল(—/ সে নির্জিত তমিস্রা সাগরে / দিনের দুর্জয় ঝড় আনিয়াছ, হে স্বর্ণ ঈগল।।”
‘সিন্দাবাদ’, ‘দরিয়ায় শেষ রাত্রি’, ‘আকাশ নাবিক’, ‘পাঞ্জেরি’, ‘স্বর্ণ ঈগল’, ‘সাত সাগরের মাঝি’ প্রভৃতি কবিতায়ও এই বক্তব্যই কবি প্রতীকে, উপমায় ও প্রত্যক্ষ উচ্চারণে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। তাছাড়া ‘সাত সাগরের মাঝি’ গ্রন্থের স্মরণীয় কবিতা ‘ডাহুক’ ও ‘লাশ’। ডাহুকের ডাকের প্রতীকে জিকিরের (আল্লাহর স্মরণ) তন্ময়তা ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। এই কবিতায় চিত্রকল্পসমূহে ও বর্ণনায় এবং ছন্দ-নিয়ন্ত্রণে তিনি অসাধারণ দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। কবিতায় সর্বত্র আমরা সবল ও মুক্ত জীবনের জয়গান লক্ষ্য করে কবি বলছেন—
“চাঁদের দুয়ারে
যে সুরার তীব্র ভেসে চলাে উত্তাল পাথারে,
প্রান্তরে তারার ঝড়ে
সেই সুরে ঝরে পড়ে
বিবর্ণ পালক।”
অন্যদিকে ‘লাশ’ তেরশ পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিতে একটি অসাধারণ কবিতা। মানুষের সৃষ্ট এই দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে ওই সময়ে অনেকেই কবিতা, কথাসাহিত্য ও নাটক লিখেছেন। সেসবের মধ্যে যে স্বল্পসংখ্যক সৃষ্টি চিরায়ত মর্যাদা লাভ করেছে। ‘লাশ’ কবিতা নিঃসন্দেহে তার মধ্যে একটি বিশিষ্ট রচনা। ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের চিত্র সমাজ সচেতন কবি ফররুখের কবিতায় ফুটে উঠেছে। কবি এ পাশবিকতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘােষণা করেছেন। কবি দেখেছেন—
“যেখানে প্রশস্ত পথ ঘুরে গেল মােড়, কালাে পিচ-ঢালা রঙে লাগে নাই ধূলির আঁচড়। সেখানে পথের পাশে মুখ গুজে পড়ে আছে জমিনের পর সন্ধ্যার জনতা জানি কোনদিন রাখে না সে মৃতের খবর।” (লাশ) ওই মৃত মানুষটির দিকে তাকিয়ে কবি ফররুখের মনে হয়েছে—
“পড়ে আছে মৃত মানবতা।
তারি সাথে পথে মুখ গুঁজে!”
কবির কণ্ঠ এর বিরুদ্ধে উচ্চকিত। অভিশাপে মুখর—“তুমি ধ্বংস হও।”
‘সাত সাগরের মাঝি’ গ্রন্থ ফররুখের নিরন্তর যাত্রার ইতিহাস। অধিকাংশ কবিতাতেই যাত্রার প্রসঙ্গ সরাসরি এসেছেসিন্দাবাদ, বার দরিয়ায়, দরিয়ায় শেষ রাত্রি, আকাশ-নাবিক, বন্দরে সন্ধ্যা, পাঞ্জেরী, তুফান, সাত সাগরের মাঝি। এই যাত্রার লক্ষ্য কাফুরের মত নতুন জীবন, এই যাত্রার প্রতিকূলতা ‘আবলুস ঘন আঁধার। এই যাত্রায় নির্ভীক কবি চিত্তের ঘােষণা ‘মােরা মুসলিম দরিয়ার মাঝি মওতের নাহি ভয়…, (‘দরিয়ার শেষ রাত্রি’)। এখানেই কবি ফররুখ আহমদ স্পষ্ট করে বলতে চাইছেন, ‘মােরা মুসলিম’, অর্থাৎ তিনি মুসলমানদের কবি। খুব স্বাভাবিক ব্যাপার এটি, যেহেতু শিক্ষাদীক্ষা ও কলাবিদ্যার নানা শাখায় তখন মুসলমানেরা অনেক পিছিয়ে। কাজেই মুসলমানদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে, কিন্তু রাষ্ট্র তথা জাতীয় জীবনের প্রাণস্পন্দনকে অনুভব ও প্রকাশ করার মত লােকের দেখা মিলবে না, এ কী করে সম্ভব? ফররুখ আহমদ কাজেই তার সমস্ত সামর্থ্য দিয়ে এই দায়িত্ব কাঁধে নিলেন। কিন্তু উপরে উদ্ধার করা পংক্তি দুটির সূত্রে প্রর্ণ একটি ওঠানাে যায় সঙ্গত কারণেই। কবি সম্মুখগামীদের মৃত্যুনির্ভীক চিত্তের কথা বলেন। প্রশ্ন হচ্ছে—তিনি যে বলছেন, ‘মওতের নাহি ভয়’, তার পেছনে যুক্তি কী—‘মােরা মুসলিম বলে, নাকি ‘দরিয়ার মাঝি’ বলে? অনুমান, প্রথমােক্তটাই এখানে প্রধান, দ্বিতীয়টি সহযােগ এনে দিয়েছে।
এই ‘সাত সাগরের মাঝি’তেই কবি সমকাল ও বাস্তব জীবন সম্পর্কে ইঙ্গিত রেখে যান। কাব্যিক পর্যটনের সূত্রে তিনি মারােয়ার পাহাড়তলীতে চলে যান। যে ঝড় তিনি প্রত্যক্ষ করেন তাতে এলাচের দানা উড়ে যায়, দারুচিনি শাখা ভেঙে পড়ে বনান্তরে। এই সবের ভিতরে কোথাও দূর বনে শােনা যায় ডাহুকের ডাক। স্বপ্নবিভাের কবিকে বাস্তব সম্পর্কে সজাগ করে দিচ্ছে। ডাহুকের ডাক। কবির চোখে স্বপ্ন, কিন্তু বুকের ভিতরে কথা জমাট হয়ে আছে অপ্রকাশের ভারে। অন্যদিকে ডাহুকের চোখে কোনাে স্বপ্ন না থাকলেও হৃদয় নিংড়ে সে প্রাণের কথা প্রকাশ করছে। অতঃপর আরব্য রজনীর অন্ধকার কাটে। দিনের আলােতে চোখে পড়ে সাড়ে তিন হাত হাড় রচিতেছে মানুষের অন্তিম কবর।—(‘লাশ’)। যে পরিবেশে কবি জাহাজের নােঙর তুলে দিচ্ছেন নতুন বন্দরের দিকে, যে আবহাওয়ায় কবি সিন্দাবাদ, শাহরিয়ার, স্বর্ণ-ঈগলের উপস্থাপন করছেন সেই প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অতঃপর কবি স্পষ্ট স্বরে জানাচ্ছেন ‘আমি দেখি পথের দু’ধারে ক্ষুধিত শিশুর শব, / আমি দেখি পাশে পাশে উপচিয়া পড়ে যায় / ধনিকের গর্বিত আসব, / আমি দেখি কৃষাণের দুয়ারে দুর্ভি( বিভীষিকা / আমি দেখি লাঞ্ছিতের ললাটে জ্বলিছে শুধু অপমান টীকা, গর্বিতের পরিহাসে মানুষ হয়েছে দাস, / নারী হল লুণ্ঠিতা গণিকা। (“আউলাদ’)। উৎসাহের সঙ্গে আরাে লক্ষ্য করতে হয়, সমাজসংশ্লিষ্ট ও ‘বর্তমান’ বিষয়বস্তু নিয়ে যে কবিতাগুলাে রচিত সেখানে ফররুখের আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার কমে গেছে। ‘ডাহুক’, ‘লাশ’ ও ‘আউলাদ’ এই তিনটি উল্লেখযােগ্য কবিতায় বিদেশী শব্দের ব্যবহার অবিৰ্বাস্যভাবে স্বল্প। কাজেই ফররুখ আহমদের কবিতায় আরবি-ফারসি শব্দ এসেছে বিষয়ানুগ হয়ে। যত্রতত্র উদ্দেশ্যহীনভাবে নয়। স্বপ্নচারী কবি আশায় উজ্জীবিত হয়ে মুসলমানদের সুবর্ণ যুগ ও গৌরবময় ইতিহাসের আশ্রয়ে ফিরে গেছেন। কিন্তু কর্তব্য সম্পর্কে বিস্মরণ তাকে গ্রাস করতে পারেনি। যে জন্যে তিনি স্বপ্নচারী হয়েও বলতে ভােলেন না—ধিত মাটিতে সে নয় তাজমহল, মানুষের মাঠে বিরান মাটিতে এবার ফলাবে তাজা ফসল…’ (নিশান’)।
(২)
মধ্যবিত্ত সমাজ পরিমণ্ডলে ফররুখ আহমদ লালিত হয়েছিলেন, কিন্তু তার কবি মানস জীবন শাসিত নয়। আধুনিক বাংলা কবিতায় যখন নগর সভ্যতার কোলাহল প্রবল, সেই সময়ে ফররুখ আহমদ নতুন প্রতীক উপমা ও উৎপ্রেক্ষার এক স্বতন্ত্র কাব্য আবহ রচনায় সমর্থ হয়েছিলেন। তার এ সাফল্যের মূলে ছিল ভিন্নতর ঐতিহ্যের প্রেরণা ও অবলম্বন। উত্তর তিরিশের বাংলা কবিতায় যে ক্ষয় ও যন্ত্রণার চিহ্ন উৎকীর্ণ, ফররুখ তার অংশীদার নন। খুব সম্ভব এ পথে তিনি কাব্যের মুক্তি প্রত্যক্ষ করেননি। অন্যদিকে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত শব্দাবলীও তার অনুমােদন লাভে ব্যর্থ হয়। প্রায় বিস্মৃত দো-ভাষী পুঁথির জগৎ থেকে অপরিচিত শব্দাবলী তিনি পুন(দ্ধার করেছেন। তাদের কাব্য সম্ভাবনাকে দক্ষ কারিগরের মতাে যাচাই করেছেন এবং নতুন ব্যঞ্জনায় সেই শব্দরাজিকে পরে কবিতায় ব্যবহার করেছেন। আরব্য উপন্যাসের কাহিনির নির্বাচিত অংশকে পুনরুজ্জীবিত করে ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর কবিতার অবয়বে। তাঁর কবিতা পড়লে চোখে ভেসে উঠে এক অবধারিত নীল সমুদ্র, আলিফ লায়লার রাত, জাফরান জেসমিনের দীপ্ত পাপড়ি, জাহাজ-মাস্তুল-নাবিক। মােটকথা মধ্যবিত্ত জীবনের নােঙর মুক্ত এক নায়কের মতাে ফররুখ আহমদ বাংলা কবিতাকে বহিঃসমুদ্রে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন এবং দিয়েছিলেনও।
রবীন্দ্রনাথের ‘বর্ষশেষ’ এবং ফররুখের ‘বৈশাখ’ কবিতা দুটো পাঠ করলে পার্থক্য স্পষ্ট হয়। ‘বৈশাখ’ কবিতার একটি স্তবক,
“চৈত্রের বিশীর্ণ পাতা রেখে গেছে শেষ চিহ্ন সালতামামীর,
ফাল্গুনের ফুলদান (কো কাফের পরী যেন) আজ শুধু কাহিনী স্মৃতির
খররৌদ্রে অবসন্ন রাহি মুসাফির যত পথপ্রান্তে নিঃসাড়, নিশ্চল
আতশের শিখা হানে সূর্য রমি লেলিহান ঝিমায় মুমূর্ষ পৃথ্বিতল,
রােজ হাশরের দগ্ধ তপ্ত তা মাঠ, বন, মৃত্যুমুখী নিস্তব্ধ, নির্বাক,
সুরে ইস্রাফিলকণ্ঠে পদ্মা মেঘনার তীরে
এসাে তুমি হে দৃপ্ত বৈশাখ।”
(বৈশাখ)
এই কবিতায় স্তবক বিন্যাস রবীন্দ্রনাথের ‘বর্ষশেষ’ কবিতার প্রতিধ্বনির মতাে হলেও এখানে ল(ণীয় যে, শব্দ ও চিত্রকল্প রচনায় ফররুখ আহমদ আদৌ রাবীন্দ্রিক নন। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেমন ‘রাহি মুসাফির’, ‘আতশের শিখা’, ‘রমি লেলিহান’, ‘রােজ হাশরের দগ্ধ তপ্ত তা মাঠ’, ‘সুরে ইস্রাফিল কণ্ঠে’ ইত্যাদি তার নিজকৃত অবিষ্কার। খুব সম্ভব রবীন্দ্রনাথের ‘বর্ষশেষ’ কবিতার বলিষ্ঠতা তাকে আকৃষ্ট করেছিল, কিন্তু একজনের ক্ষেত্রে যখন উপনিষদ ও হিন্দু পুরাণ প্রাণনার প্রধান উৎস, অন্যের চৈতন্যে তখন ইসলাম ও মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস পরম নির্ভর। সুতরাং উভয়ের কবিতার স্বাদ গন্ধ ও শব্দবিন্যাস ভিন্ন হতে বাধ্য। তারপরও বলি, মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) ‘মেঘনাদবধ’ কাব্যের প্রায় পদে পদে পৌরাণিক উপমার আশ্রয় নিয়েছেন। ফররুখ আহমদ মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নিজস্ব ভাড়ার থেকে তার উপমা সম্ভার সংগ্রহ করেছেন। যেমন,
“তামাম আলমে দেখি বেশুমার রহমত খােদার
যে রহমত পেয়ে বাঁচে জ্বিন ও ইনসান আশরাফুল
মাখলুকাত দু’জাহানে অথবা পরো প্রাণীকুল
শূন্যস্তরে ভাসমান যে রহমে দিশা পায় খুঁজে
মাটির মানুষ চলে সে রহমে পূর্ণতার পথে।”
ফররুখ আহমদ মুসলিম ঐতিহ্যে ছায়াঘেরা ছিলেন বলেই তার পথে মুসলিম ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির শেকড় সন্ধান সম্ভব হয়েছিল।
গতানুগতিক ট্রাডিশনের শৃঙ্খল ভেঙে তিনি এক নতুন আঙ্গিকে বাংলা সাহিত্য ও কাব্যের প্রাণ সঞ্চার করলেন। ইসলামিক বি-বী চিন্তা-চেতনার মৌলিক ধারণা থেকে এতটুকুও নড়লেন না বরং তিনি তাঁর কাব্যে সাহিত্যের মাধ্যমে ইসলামি চেতনায় সাম্প্রদায়িক হীনমন্যতার ক্ষুদ্রতার উত্তরণ ঘটিয়ে বিমানবতার সঙ্গীতে মানুষের মন দিলেন ভরিয়ে। তার শক্তিশালী লেখনীর শাণিত উচ্চারণে তিনি বিধের নিপীড়িতদের পথে, সর্বহারাদের পথে অবিচারী অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে ঘােষণা করলেন নিরাপােস প্রচণ্ড বিদ্রোহ। অতঃপর বাংলা সাহিত্যে নবতর উত্তরণ ঘটে গেল ত্রিশের কবিদের হাতে যাঁরা আধুনিকতার একটা নতুন রূপ দিলেন বাংলা সাহিত্যের কাব্যে। এই নতুনদের পুরােধা ছিলেন বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) এবং তাঁর সমসাময়িকগণ তথা প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬) এবং পরবর্তী কবিগণ হলেন মনীশ ঘটক (১৯০২-১৯৭৯), বিমলচন্দ্র ঘােষ (১৯১০-১৯৮২), অরুণ মিত্র (১৯০৯-২০০২), সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭) এবং সুভাষ মুখােপাধ্যায় (১৯২০-২০০৩)। আধুনিক বাংলা কাব্যে সাহিত্যের এই ধারাবাহিক আন্দোলনের ফল্প প্রবাহে এলেন ফররুখ আহমদ। এই সময়েই কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের (১৯২৬-১৯৪৭) আবির্ভাব। এঁরা সকলেই নজরুলের যুগ-প্রবর্তনার আবহে অবগাহিত। বিবের এক প্রত্যক্ষ এবং সূক্ষ্ম চেতনায় এঁরা সকলেই যেন মাতাল।
(৩)
এই সময়ের কবিরা শ্রেণি চেতনায় উদ্দীপ্ত, শ্রেণি সংগ্রামের ডাক আসছে তখন সােভিয়েত ইউনিয়নের কম্যুনিস্ট আন্দোলনের জোয়ারে। সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক বেনিয়া শাসনের বিরুদ্ধে সমগ্র পৃথিবীতে তখন প্রবল প্রচণ্ড ক্ষোভ, বিদ্রোহ, বিল্পব। একদিকে বিদেশী শাসনের শৃঙ্খল মুক্তির পণ, অন্যদিকে নৈতিক আদর্শের দ্বন্দ্ব, সাম্প্রদায়িক হানাহানির বিষাক্ত হাওয়া, অজ্ঞজনে ধর্মীয় সংকীর্ণতা উসকে দেওয়া, নিরন্ন সর্বহারার জাতপাতহীন বেদনার আহারাজি, কোথাও জয়মা-ভবানী, কোথাও জয়হিন্দ আবার কোথাও লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান—এইসব মিশ্র অনুভূতির আড়ালে ন্যস্ত স্বার্থবাদীদের পৈশাচিক লােভ-লালসা সমগ্র পরাধীন ভারতবর্ষকে তখন করে তুলেছিল প্রায় বলগাহীন। সেইসব দিনের বিদ্রোহের বিপুল আওয়াজে ফররুখ দেখালেন নতুন অভিযাত্রার স্বপ্ন। সাত সাগরের মাঝি’ কবিতা প্রচণ্ড আলােড়ন তুলেছে ১৯৪৪ সালের কলকাতার প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকার পাতায়। ফররুখের স্বপ্নে তখন আপন ঐতিহ্যের স্রোত প্রবহমান। মহাকবি ইকবালের প্রেরণায় ফররুখ মাতােয়ারা। দেখলেন তিনি মানব-মুক্তি ইসলামে। আর সেই ধ্যান-ধারণায় মগ্ন হলেন তাঁর কাব্য ভাবনার অবাধ অবারিত অন্তরঙ্গতায়—যেখানে গাওয়া যায় মজলুমের গান, মানুষের গান, তার পূর্বসূরী ইকবাল, নজরুল যেসব গান গেয়েছেন তা তাকে আকৃষ্ট না করে পারেনি।
তখন সমগ্র ভারতবর্ষে উত্তাল মানুষের ঢল মিছিলে মিছিলে, ব্রিটিশ বিরােধী আন্দোলনে-ভারত ছাড়াে শ্লোগানে মুখরিত তখন ভারতবর্ষের আকাশ বাতাস। আবার অন্যদিকে নিপীড়িত নির্যাতিত অবহেলিত মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস ত্যাগ করে কায়েদে আজম জিন্নাহ সাহেব এগিয়ে চলেছেন পাকিস্তান আন্দোলনের পতাকা নিয়ে। সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশবাদী শক্তি ব্রিটিশ শাসনের অবসান তখন প্রায় অত্যাসন্ন। এ সময় ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির মুষ্টিমেয় লােকবল ১৯১৭ সালের রাশিয়ায় বলশেভিক বিবের ক্যুমুনিস্ট অভ্যুত্থানে সােভিয়েত রাশিয়ার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছে। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য এই দলেরই মুখ্য শ্লোগানধর্মী কবিতা দিয়ে যখন শােষিত-নিপীড়িত জনগােষ্ঠীকে প্রেরণা দিয়ে চলেছেন, তখন ফররুখ আহমদ আপন ঐতিহ্যের অর্থাৎ ইসলামি সাম্যবাদী দিশায় একই জনগােষ্ঠীর পক্ষে তাঁর কাব্যের ফল্গুধারায় অনুপ্রাণিত করছেন সমগ্র দেশবাসীকে। তিনি জাগিয়ে দিতে চান ঘুমন্ত মানুষকে, অভিযাত্রী হওয়ার জন্যে তাদের আহ্বান জানান। এ ছিল সাত সাগর পাড়ি জমানাের নাবিকদের সঙ্গে সামিল হয়ে দুনিয়ার সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান। কিশাের কবি সুকান্ত যখন নিপীড়িত বির্ণের মুক্তিদাতা হিসেবে লেনিনের নেতৃত্বকে সম্বল করে ভাবলেন, এই বলে,
“লেনিন ভেঙেছে রুশে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ,
অন্যায়ের মুখােমুখি লেনিন প্রথম প্রতিবাদ…
আজকেও অযুত লেনিন।
ক্রমশ সংক্ষিপ্ত করে বিব্যাপী পরীক্ষিত দিন,
বিপর্যস্ত ধনতন্ত্র, কণ্ঠরুদ্ধ বুকে আর্তনাদ,
আসে শত্রু জয়ের সংবাদ।।
এবং শেষাবধি সুকান্ত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে ওঠেন, ‘বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন। অন্যদিকে ফররুখ আহমদ ইসলামি সমাজতন্ত্রের নবীকে স্মরণ করে লিখলেন,
“…কে আমি’ জানালে তুমিই প্রথম।
উন্মী নবী দীপ্ত সূর্য আলাের আরশিতে ধরিয়াছে কাল
আমারই ছবি। সে এলাে, সে এলাে, রাজার মত সে এ
গলিতে তবু দীনের মত, পুষ্প কোমল তার অন্তর হলাে
বিক্ষত কাটায় ক্ষত, তবু সে জাগালাে মেশকের বাস,
জাগালাে মরুতে জল আনার
ইব্রাহিমের পরশে যেমন ফুল হয়ে ফোটে
ক্ষুব্ধ নার।”
নজরুলের সূক্ষ্ম প্রভাব সুকান্ত এবং ফররুখের মধ্যে একান্তভাবেই লীন হয়ে গিয়েছিল। ভাবের বিশাল সাম্রাজ্যে এ দুয়ের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকলেও উভয়েই সমাজরাষ্ট্রকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটাতে উদ্দীপ্ত ছিলেন। দৃষ্টিভঙ্গির সমান্তরালে মূলত মানব মুক্তির সর্বলােক সন্ধানে ইসলাম প্রকৃতপক্ষে সমাজতন্ত্রে অভীষ্ট। ‘সিরাজাম মুনীরা’ কাব্যগ্রন্থে ফররুখ আহমদ খােলাফায়ে রাশেদীনের (মহান চার খলিফার) দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমরকে (রা.) নিয়ে ‘ওমর দরাজদীল’ কবিতার ছত্রে ছত্রে দেখিয়েছেন। হযরত ওমর (রা.) কেমন প্রক্রিয়ায় ইসলামের সমাজতন্ত্রী সাম্যবাদের ব্যবহারিক গুণে রাষ্ট্রকে কেমনভাবে সমৃদ্ধ করেছিলেন, যেখানে ব্যক্তিকে ভােগ কখনােই অতিক্রম করতে পারেনি। তিনিই ইসলামের সেই খলিফা যিনি প্রকৃতপক্ষে ইসলামি সমাজতন্ত্রের ব্যবহারিক রূপ যে কি তা প্রত্যক্ষ দেখিয়েছিলেন সমগ্র বিশ্বকে। ফররুখ আহমদ তাঁর কবিতায় সেই সমাজতন্ত্রকে বাক-প্রতিমায় ভাস্বর করে গেছেন। আধুনিক বাংলা কবিতায় সমাজনীতি এবং রাজনীতি ধর্মের বিশ্বাসের প্রতীক হয়ে এত উজ্জ্বল রূপ ধারণ করতে পারে তারই স্বাক্ষর বহন করে ফররুখ আহমদের কাব্যকৃতি।
‘সিরাজাম মুনীরা’ কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতায় উপজীব্য হযরত মােহাম্মদ ও তার অনুসারীদের সত্যসন্ধানী, মানবমুখী ও সংগ্রামী জীবনের পুণ্যকাহিনি। এসব কবিতায় কবি মহজীবনাদর্শের আলােকে মানব-পথিকের পথ নির্দেশের প্রয়াস পেয়েছেন। অপরদিকে ইসলামী জীবনাদর্শ, ঐতিহ্য ও ধর্মাদর্শের প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধা ও আস্থা প্রকাশ পেয়েছে বেশ ক’টি কবিতায়। রােমান্টিক আত্মভাবনা ও বিশুদ্ধ হৃদয়ানুভূতির প্রকাশ লক্ষ করা যায় ‘মন’, ‘প্রেমপন্থী’, ‘অশ্রুবিন্দু’এই তিনটি কবিতায়। অর্থাৎ এ কাব্যে একদিকে ইসলাম ধর্মসাধক মহাপুরুষদের জীবনের মধ্যে ব্যক্তিজীবনের তথা জাতীয় জীবনের সে আদর্শ রূপায়ণের প্রয়ােজনীয়তা সম্পর্কে নিজের বিধাস, সে আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা ও তার জন্যে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম ও সাধনা চালিয়ে যাবার সংকল্প প্রকাশ করেছেন। বস্তুত ‘সাত সাগরের’ ‘অভিযাত্রী’ কবি ‘সিরাজাম মুনীরা’য় সমাজের কর্তব্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আদর্শপন্থানুসরণে মুসলিম পুনর্জাগরণের আকাঙ্খটিকে রূপায়ণের চেষ্টা পেয়েছেন। আসলে পচনশীল সমাজের অনাচার-অবিচারে ক্ষুব্ধ চিত্র কবি সাত সাগরের মাঝি’তে যে অভিযান শুরু করেছিলেন মনে হয় অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের রচনা ‘সিরাজাম মুনীরা’য় তার লক্ষস্থলের সন্ধান পেয়েছেন। সুনীলকুমার মুখােপাধ্যায়ের মন্তব্য, ‘সিরাজুম মুনীরা’কে ‘সাত সাগরের মাঝি’র স্বপ্ন-ভাবনার একটি যথার্থ আদর্শ বাস্তব উপসংহার বলা চলে।”
এ কাব্যে অতীত জীবন-ঐথর্যের দূরায়ত কোনাে স্বপ্ন নয়, মুসলিম অভ্যুত্থান যুগের ব্যক্তিত্ব ও ভাবধারার ঐতিহ্যই কাব্যরূপ লাভ করেছে। কবি এখানে সাত সাগরের অপরূপ ঐধর্যের জগতের স্বপ্নটি সামনে রেখে মুসলিম-অভ্যুত্থান যুগের ব্যক্তিত্ব ও ভাবধারার আলােকে আধুনিক মুসলিম জীবনের পুনর্গঠন আকাঙ্খায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।
সমকালীন মুসলিম জাগরণকামী কবিদের প্রায় সকলে হযরত মােহাম্মদের (সঃ) প্রশস্তিমূলক কবিতা লিখেছেন এবং তার জীবনাদর্শে বাংলার মুসলিমের জীবনবােধ ও জীবনাচরণকে উদ্ভাসিত করতে চেয়েছেন। সেই সঙ্গে হযরত মােহাম্মদের (সঃ) সময়কালে পরিব্যপ্ত সমাজ বাস্তবতা ও সংগ্রামকে বর্তমান কালের সাথেও তুলনা করেছেন। ফররুখ আহমদও সেই প্রবহমান ধারাকে অধিকতর প্রাণবন্ত করেছেন। ‘সিরাজাম মুনীরা’ কাব্যগ্রন্থে সেই সুর অনুরণিত হয়েছে—
“তব বিদ্যুৎ কণা-স্ফুলিঙ্গে লুকানাে রয়েছে লক্ষ দিন,
তােমার আলােয় জাগে সিদ্দিক, জিনুরাইন, আলী নবীন,
ঘুম ভেঙে যায় আল ফারুকের—হেরি ও প্রভাত জ্যোতিষ্মন।
মুক্ত উদার আলােকে তােমার অগণন শিখা পায় যে প্রাণ।”
ফররুখ আহমদ বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেন যে, যে আলাের প্রভায় হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা.), হযরত ওমর (রা.), হযরত ওসমান জিন্নরাইন (রা.), হযরত আলি (রা.) সহ উষর মরুভূমি উদ্ভাসিত—তা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও বাংলার মুসলমান কেন অন্ধ, আর কেনই বা তন্দ্রাচ্ছন্ন?
“তবু ভাঙলােকি, ঘুম ভাঙলােকি, ঘুম ভাঙলাে এ অন্ধদের
আজ বিস্মৃতি তােলে যে আড়াল তােমার দিনের এই দিনের!”
ফররুখ আহমদ খােলাফায়ে রাশেদীনের স্বর্ণযুগকে তাঁর কবিতায় উপজীব্য করেছেন। ‘ওমর দরাজদীল’ ছাড়াও ‘আবুবকর সিদ্দিক’, ‘ওসমান গণী’, ‘আলী হায়দার’ শিরােনামে কবিতা লিখে খােলাফায়ে রাশেদীনের বর্ণাঢ্য জীবনধারাকে (যেমন হযরত আবুবকরের কষ্ট সহিষ্ণুতা, হযরত ওমরের প্রজাহিতৈষণা, হযরত ওসমানের দানবীরতা ও হযরত আলির নির্ভীক চিত্ততাচারিত্রক দৃঢ়তাকে) একমাত্র অনুসৃত জীবনধারা হিসেবে বাংলার মুসলমানের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মীর মশাররফ হােসেন (১৮৪৭-১৯১২), ইসমাঈল হােসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) প্রমুখের মতাে তিনিও মােহাররমের শােকাবহ ঘটনাকে কেন্দ্র করে লিখেছেন শহীদে কারবালা’। পৃথিবীর খ্যাতনামা আউলিয়াদের জীবন কাহিনিকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে ‘গাওসূল আজম’, ‘সুলতানুল হিন্দ’, ‘খাজা নকশবন্দ’, ‘মুজাদ্দিদ আলফেসানী’ প্রভৃতি কবিতা। মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০) সহ আরও অনেক লেখক মহান ধর্ম সংস্কারকদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করেছেন। ইসলাম প্রচারে এ সকল সংস্কারকদের কর্ম প্রচেষ্টা, শত বাধা বিঘ্নকে পরাক্রমের সাথে অতিক্রমণ ও আত্মত্যাগকে মহীয়ান করে উপস্থাপন করেছেন। যাতে সম্বিতহারা বাংলার মুসলমান তাদেরই মহান পূর্বপুরুষদের বিপুল, মহান আলেখ্য ও সংগ্রামী জীবন দ্বারা উজ্জীবিত হতে পারে। নয়া জামানার বা নবযুগের শুভ উদ্বোধন ঘটাতে পারে। ফররুখ আহমদের ভাষায়,
“প্রতি পাপড়ির পূর্ণ বিকাশে জাগুক মুক্ত গুলে আনার,
প্রতি পাথরের সম্মেলনের প্রকাশে দাঁড়াক তুর পাহাড়,
নামুক সেখানে তওরাত ধারা, নামুক নূরানী আল্ কোরান
পূর্ণ মুমিন জমায়েত হেথা আনুক আবার নুতন বান,
হেরার সূর্য ঝলকে আবার আসুক মুক্ত চির নূতন,
মুজাহিদ সেনা করুক আবার নয়া জামানার উদ্বোধন।”
ফাররুখ এ সকল মহান ব্যক্তিদের জীবনীকে তাঁর কাব্যে উপজীব্য করে একজন ধর্ম প্রচারকের কর্ম সম্পাদন করেছেন।
(৪)
একটু আগেই বলা হয়েছে, আল্লামা ইকবালের জাগরণের বাণী ফাররুখকে উদ্বেলিত করে। তিনি ইকবালের অসংখ্য কবিতা বাংলায় অনুবাদ করে ইকবাল দর্শন ও জাগরণের বাণীকে বাংলার মুসলমানের হৃদয়ে সঞ্চারিত করতে প্রয়াসী হন। ইকবালের প্রতি তার এই উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ বর্ণিত হয়েছে তাঁর ‘ইকবাল-প্রসঙ্গ’ প্রবন্ধে, যা ফররুখ মানস অনুধাবনে সহায়তা করে। ফররুখ আহমদ লিখেছেন, “ইকবালের কবিতার ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে—পৃথিবীর কাব্যভাণ্ডারে ইকবাল যে বিশিষ্ট জাগরণের বাণী বয়ে এনেছেন তা সকল দেশ ও সকল কালের উপযােগী হলেও আদর্শচ্যুত, পরাধীন মুসলমান সমাজের জন্যই তার প্রয়ােজনীয়তা সবচাইতে বেশি। একথা অনস্বীকার্য যে, ইকবালের বি-বী-চিন্তার অগ্নিস্ফুলিঙ্গেই ভারতীয় মুসলমানের মনে আজাদীর স্বপ্ন-বহ্নি মেঘের মতাে পক্ষে বিস্তার করেছে। আমাদের রাজনৈতিক ঝাণ্ডাবাহীর দল প্রয়ােজনমত ভুলে গেলেও লেখক সম্প্রদায়কে মনে রাখতে হবে একথা।…আত্মপ্রকাশের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার মতবাদ ইকবাল গ্রহণ করেছিলেন মূল কোরান থেকে, ইরানী কবিদের বিশিষ্ট ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন তিনি সেই মতবাদ।”
আল্লামা ইকবালের মতাে পাকিস্তানকে তিনি কল্পনা করেছেন ইসলামি আদর্শ প্রতিষ্ঠা, রক্ষা ও প্রসারের উজ্জ্বল ক্ষেত্ররূপে। সমকালীন মুসলমান সাহিত্যিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক নেতা কর্মীদের অনেকেই এ ভাবাদর্শে উজ্জীবিত ও উচ্চকিত হন। ফররুখ আহমদের ‘আজাদ করাে পাকিস্তান’ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলােয় এ সুর পরিস্ফুট। বিভাগ পূর্বকালে রচিত মােট ১০টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত এ কাব্যে কবি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আদর্শ, স্বপ্ন, আকাঙ্খ ব্যক্ত করেছেন। মুসলিম লীগ কর্তৃক গৃহীত পাকিস্তান প্রস্তাবে মুসলমানদের জন্যে যে আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল কবি তাতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে এই কবিতাগুলাে লেখেন। পাকিস্তান বলতে তিনি শুধুমাত্র একখণ্ড ভূমিকেই বােঝেননি, বরং পাকিস্তানকে তিনি অনুভব করেছেন স্বপ্ন ও আদর্শের লালনাগার হিসেবে। কাব্যের পরিচিতমূলক বক্তব্যেও তিনি পাকিস্তান দাবি সম্পর্কে তার মতামত রেখেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, “স্বাধীন হয়ে বাঁচবার অধিকার মানুষ মাত্রেরই। নিজের চরবার মাঠে নিজের সম্পূর্ণ অধিকার দাবি অযৌক্তিক নয়। এদিক দিয়ে পাকিস্তান দাবি খাদ্যাখাদ্যের মতাে বিবেচিত হলেও তা গ্রহণযােগ্য। খাদ্যাখাদ্যের বিচার জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের, পশুর নয় এবং মানুষ যখন বাঁচে স্বাধীন হয়েই বাঁচে।”
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা থাকবে না। অত্যাচার জুলুম থাকবে না, অর্থাৎ একটা আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান গড়ে উঠবে বলে কবি বিশ্বাস করতেন। বর্তমান শােষক-শাসকরা হটে গিয়ে স্বাধীন পাকিস্তানে নিরন্ন মানুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে বলে কবি যে মনােভাব পােষণ করতেন তারই প্রতিফলন ঘটেছে এ কাব্যের বিভিন্ন কবিতায়। এখানে তার শাণিত বৰ্ত্তব্য।
“ওড়াও ঝান্ডা খুনেরা লাল
ওড়াও আকাশে আল-হেলাল
খঞ্জরে ভাঙো জিঞ্জির ভীতি।
কাপুক দুনিয়া টালমাটাল।।”
এসকল কবিতায় কবি নিঃসাড়, নিস্পন্দ বাংলার মুসলমানকে প্রাণদ উন্মাদনায়, ধূমকেতু বেগে জাগরণের আহ্বান জানিয়েছেন—
“জাগাে জনতার আত্মা! ওঠো, কথা কও, কতােকাল আর তুমি ঘুমাবে নিসাড় নিস্পন্দ, আকাশ ছেয়ে চলেছে যখন নতুন জ্যোতিষ্ক-সৃষ্টি তখনাে তােমার স্থবির নিশ্চল বুকে নাই কোন প্রাণদ-ইংগিত নাই অগ্নিকণা নাই ধুমকেতু বেগ!”
সমকালীন মুসলমানের দুরবস্থার বর্ণনা ও তা হতে উত্তরণের পথ-নির্দেশ আছে তার কবিতায়। তিনি প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের প্রতি বৈরী মনােভাবাপন্ন ছিলেন না। তবে, মুসলমানের স্বাতন্ত্র চেতনাকে জোরদার করতে চেয়েছেন। গৌরবময় ঐতিহ্যিক ধারায় মুসলমানের পুণর্জাগরণকে কামনা করেছেন। তার কাব্য মানসলােক সম্পর্কে জ্ঞাত কবি সাহিত্যিক সমালােচকদের প্রায় সকলেই তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত স্বাতন্ত্রবাদী চেতনা ও মুসলিম জাগরণ আকাঙ্খর বিষয়ে ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন। তারমধ্যে সৈয়দ এমদাদ আলী, নাজমুল আবদ,বসুধা চক্রবর্তী প্রমুখের মন্তব্য প্রণিধানযােগ্য। জয়নুল আবেদীন বলেন “জাগরণের স্বপ্নে কবি বিভাের। তিনি মুসলিম জাতির উত্থানকে বাস্তবে রূপায়িত দেখতে চান।…‘সিন্দাবাদ’ ‘বার দরিয়ায়’ ‘দরিয়ার শেষ রাত্রি’ ‘পাঞ্জেরি’…প্রভৃতি কবিতায় ফুটে উঠেছে তার প্রাণের জাতীয় বেদনাবােধ। বর্তমান অবনতির কলংক কালিমা, জাতির মুক্তির সাধনা বিধময় তার স্বাধীনতার তীব্র আকুতি, বর্তমান মানব সমাজের পংকিল অবস্থার বিশ্লেষণ…। সিন্দাবাদ’, ‘বার দরিয়ায়’…প্রভৃতি কবিতায় আছে জাতীয় জাগরণের জন্য প্রাণের আকুল আহ্বান, আর ‘হে নিশান-বাহী’ ‘নিশান’…প্রভৃতিতে আছে জাতীয় উত্থানের গতি ও লথের নির্দেশ।”
আশাবাদী কবি যাত্রাপথের সমূহ বিপদ-আপদ উত্তীর্ণ হয়ে গন্তব্যের চরম সীমায় উপনীত হতে দৃঢ়সংকল্প। একে রূপক হিসেবে গ্রহণ করলে বলতে হয় যে, জীবনের অবশ্যম্ভাবী সাফল্যের মাধ্যমে কবি মুসলিম জাতীয় জাগরণের সাফল্য নিরীক্ষণ করেছেন। কবির স্বপ্নাতুর মানসচেতনায় এ ভাবটাই শিল্পমণ্ডিত হয়ে ধরা পড়েছে। তাই কবি পূর্ণ বিধাসে আশার বাণী ব্যক্ত করেছেন এভাবে—
“পাল তুলে দাও, ঝাণ্ডা উড়াও, সিন্দাবাদ।
এল দুস্তর তরঙ্গ বাধা তিমিরময়ী।
কী হবে ব্যর্থ ক্লান্ত রাতের প্রহর গুণে?
নতুন সফরে হবে এ কিন্তী দিগ্বিজয়ী।
তরঙ্গমুখে জাগে কত ভয়কে জানে আজ?
দ্বিধা সংশয় কত জমা হয়—কে মানে আজ?
এ ঝড়-তুফানে জাগাে দুর্বার দুঃসাহসী
নতুন সফরে হবে এ কিন্তী দিগ্বিজয়ী।”
(‘নতুন সফর’)
(৫)
মুসলিমগণ এক সময় শৌর্য, বীর্য, শিং, সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে অতুলনীয় ছিল, কিন্তু কালের বিবর্তনে উদ্যমের অভাবে তারা অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। ফলে সমস্ত ঐধর্য হারিয়ে হৃত সর্বস্ব জাতিরূপে তারা আজ বিধবাসীর কাছে অবহেলিত ও উপেক্ষিত। কবি মুসলিম জাতির হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য সাতসাগরের মাঝির প্রতীক আরব্য উপন্যাসের নায়ক সিন্দাবাদ জাহাজীকে বিপদসঙ্কুল অভিযানের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষরূপে কল্পনা করে উৎসাহিত করেছেন। তাই তিনি বলেন,
“ছিড়ে ফেলাে আজ আয়েশী রাতের মখমল অবসাদ নতুন পানিতে হাল খুলে দাও, হে মাঝি সিন্দাবাদ!”
(সিন্দাবাদ’) ‘সাত সাগরের মাঝি’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘পাঞ্জেরি’ একটি প্রতিনিধিত্বশীল রূপক কবিতা। এটি ফররুখ আহমদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। ‘পাঞ্জেরি’ আরবি শব্দ। এর অর্থ জাহাজের মাস্তুলে রতি আলােকবর্তিকা। কবি এ কবিতায় পাঞ্জেরিকে জাহাজের পথনির্দেশক বাতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আর রূপক অর্থে মুসলিম জাতির পথপ্রদর্শক নেতা হিসেবে কল্পনা করেছেন। তাই এর নামকরণ যেমন অর্থবহ, তেমনি ইঙ্গিতধর্মী। ঐতিহ্যময় মুসলিম জাতি আজ তাদের গৌরব ও ঐতিহ্যকে ভুলে দিগভ্রান্ত হয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত। তাদের পথ দেখাবে যারা, তারা আজ হতাশাগ্রস্ত ও নিস্ক্রিয়। তারা জেগে না উঠলে জাতির জেগে ওঠা সম্ভব নয়। সুতরাং পাঞ্জেরির মত দায়িত্ব নিয়ে তাদের অগ্রসর হতে হবে। তাই স্বজাতির করুণ দুঃখ-দুর্দশায় ব্যথিত হয়ে মানবদরদী কবি ইসলাম-রূপ জাহাজকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে জাতির পুনর্জাগরণ কামনা করেছেন। ‘পাঞ্জেরি’ কবিতায় কবির সেই আকুল অহ্বান—
“জাগাে বন্দরে কৈফিয়তের তীব্র ভ্রুকুটি হেরি,
জাগাে অগণন ক্ষুধিত মুখের নীরব ভ্রুকুটি হেরি
দেখ চেয়ে দেখ সূর্য ওঠার কত দেরি, কত দেরি।”
বস্তুত সমগ্র কবিতাটিতে ফররুখ আহমদ ইসলামি ঐতিহ্যের রূপায়ণ ঘটাতে দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের রূপক, উপমা, প্রতীক ও শব্দ প্রয়ােগে চমৎকার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তার ঐতিহ্য-প্রীতির চমৎকার অভিব্যক্তি ঘটেছে ‘নিশান’ কবিতায়। এখানে কবির ঐতিহ্য-প্রীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে ব্যথিত, অত্যাচারিত, উপেক্ষিত এবং ধিতের প্রতি প্রবল সহানুভূতি ও গভীর মমত্ববােধ। যথা—
“ক্ষুধা বিশীর্ণ অশ্রুজল,
এবার তােমার যাত্রা সে পথে
যেথা উমরের পায়ের ছাপ,
জং ধরে যেথা পড়ে আছে হায়
আলীর হাতের জুলফিকার
পিঠে বেঝা নিয়ে ক্ষুধিতের দ্বারে
চলে একটানা পথ তােমার
দেখাে সিরাজম মুনীরা জ্বলছে।
মুছে দিতে সব ফঁাকা প্রলাপ।”
পঞ্চাশের দশকের গােড়ার দিকে বাঙালি মুসলমান কবি সাহিত্যিকদের একাংশ পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে তাদের লেখনী পরিচালনা করেছেন। ভারতে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক আচরণের কারণে বৃটিশ শাসন অবসানের পর মুসলমান স্বীয় ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে স্বাধীনভাবে রক্ষা করতে পারবে কি না এ বিষয়ে তারা সংশয়াকূল হয়ে ওঠেন। ফলশ্রুতিতে তারা রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন পরিচালনার পাশাপাশি সাহিত্যিক আন্দোলনও শুরু করেন। মুসলমানের জাগরণের জন্য পাকিস্তান নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করবে বলে তারা মনে করেন। সমকালীন মােহাম্মদী’ পত্রিকায় পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও এর নেতা কায়েদে আজমের স্বপক্ষে অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়। মােফাখখারুল ইসলামের ‘তারানা-ই-পাকিস্তান’, মােহাম্মদ রওশন ইয়াজদানীর কায়েদে আজম’, গােলাম মােস্তফার ‘পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত’, তালিম হােসেনের ‘গান’ প্রভৃতি এ জাতীয় রচনা।
বৃটিশ রাজত্বে যখন অগণিত মানব সন্তান দুর্ভিক্ষ মৃত, বৃটিশ নির্যাতন-নিপীড়নে মুসলমান রক্তারক্তি তখন ইসলামি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তান অর্জনকে ফররুখ শ্রেয়তর জ্ঞান করেছেন। কুরআনের রাজ ও খােলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শকে কায়েম করার জন্য তিনি বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তাঁর ভাষায়,
“নব চেতনার বিষাণ বাজায়ে ডাকিছে তােমারে পাক কোরান,
ডাকে খােলাফায়ে রাশেদীন যেথা গণতন্ত্রের মাঠ বিরাণ!
সে বিরাণ মাঠ আজিকে ভরাতে, কোরানের জ্যোতি নিয়ে এসাে সাথে।
আনাে সাথে করি, বিজয়ী দামামা, আনাে মােজাহেদী ঝড় তুফান।”
নতুন রাষ্ট্রে মুসলিম জাতি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ফররুখ আহমদ ঠিকই দেখেছিলেন, কিন্তু আজ সংগ্রাম নিজের সঙ্গে বলে সমস্যাকে অনেকটা এড়িয়ে গেছেন। কারণ এই সমকালেই বহু ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে যায়। বাঙালি তার আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামে প্রতিপথের মুখােমুখি। সে সবের কোনাে ছাপ ফররুখ আহমদের কবিতায় নেই। যে ফররুখ আহমদ একদিন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করবার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন, লিখেছিলেন ‘উর্দু বনাম বাংলা’ নামের ব্যঙ্গ কবিতা, তিনি বায়ান্নোর ভাষা-আন্দোলনের মত এত বড় ঘটনায় সাড়া দেন না। সে কী ফররুখ কথিত সেই মুসলিম জাতীয়তাবাদের আদর্শের ভিত্তি কমজোরি হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায়? সাতচল্লিশে হাতে ধরিয়ে দেওয়া ছদ্ম-স্বাধীনতায় অতৃপ্ত মুসলমান যখন ক্রমশ বাঙালি হচ্ছিল তখন প্রতিভাবান হওয়া সত্ত্বেও কবি ফররুখ আহমদ মানসিকতার দিক থেকে পেছনে পড়ে থাকেন। তিনিই বন্দরে নতুন দিনের স্বপ্ন দেখেছিলেন—সেই তিনিই সমকালীন ইত্যাকার ঘটনাপ্রবাহকে নতুন দিনের হাতছানি বলে মেনে নিতে পারেননি।
‘সিরাজাম মুনীরা’র কবিতাবলী ভাষা-আন্দোলনের পূর্বেকার রচনা বলে ছাড় দেওয়া গেলেও আশা করা গিয়েছিল পরবর্তী মুহূর্তের কবিতা’য় প্রত্যাশা পূরণ হবে। কিন্তু সেখানে রয়েছে বাংলা ভাষার প্রতি নামের সাদামাঠা কবিতা একটি। যে জোয়ার এবং স্পন্দন সমাজের অনেক গভীরে প্রবিষ্ট হয়ে নাড়িয়ে দিয়েছিল তার কোনাে নমুনা ফররুখে নেই। মুহূর্তের কবিতায় কবির প্রথম কৃতিত্ব এর সনেট-সাফল্যে। বিষয়বৈচিত্র্যে এই গ্রন্থ তার সীমানাকে পূর্বের চেয়ে বাড়িয়েছে। সনেটের আঙ্গিক শাসন সত্ত্বেও ফররুখ আহমদের কাব্যপ্রতিভার বিকাশ এতে অসাধারণত্ব অর্জন করে। পুঁথি, ধর্ম, ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগের নিদর্শন হয়ে রচিত হয় কিছু কিছু কবিতা। কখনাে কখনাে পুনরুক্তিতে আত্রান্ত হয়েছে কয়েকটি কবিতা। হাতেমতায়ীকে নিয়ে লেখা ‘নৌফেল ও হাতেম’ কাব্যনাট্য এবং ‘হাতেমতায়ী’ কাহিনি-কাব্যের সঙ্গে আবার তিনি লিখছেন হাতেমতায়ী’—তবে এবার সনেটে। বােঝা যায় একদা অর্জিত পুঁথিসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তার কাটছেই না। ফলে এই বিষয়ে একে একে এসেছে। শাহ গরীবুল্লাহর অসমাপ্ত পুঁথি প্রসঙ্গে, ‘পুঁথির আসর’ ‘পুঁথি-পড়া’ ‘মুহারাম মাসে, শহীদে কারবালা’, ‘তাজকেরাতুল আউলিয়া, কাসাসুল আম্বিয়া, শাহনামা’, ‘আলিফ-লায়লা’, ‘চাহার দরবেশ’ কবিতাসমূহে। এছাড়া প্রকৃতি-সন্দর্শন, সৌন্দর্যচেতনা ও সমাজ-ভাবনার কবিতায় কবি স্বতঃস্ফুর্ত কবিত্বে স্ফুরিত।
‘মুহূর্তের কবিতা’র একশটি সনেটে সামগ্রিকভাবে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার সঙ্গত কারণেই হ্রাস পেয়েছে। ধর্মঐতিহ্যনির্ভর কবিতাসমূহে যা কিছু বিদেশী শব্দের ব্যবহার লক্ষ্ণণীয়। কবিতার বিষয়ের দাবিতেই এটা হয়েছে। নিসর্গ, সমাজ, স্বদেশ বিষয়ক কবিতায় প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার বিরােধাভাসের সৃষ্টি করতে পারে বলেই হয়ত ফররুখ সে-পথে যাননি।
‘মুহূর্তের কবিতা’-র সনেটগুচ্ছ ক্ষণিকের ভাবনায় উচ্চকিত হলেও এতে ফররুখ আহমদের পরিণত শিল্পমনের স্বাক্ষর বিদ্যমান। বিমর্ষ বেদনার আবাহনে জেগে ওঠে যে আকাঙ্খ, তার স্বীকৃতি এবং কবি প্রাণের বিচিত্র জৈবনিক ও হৃদয়গত অনুভূতির শিল্পিত বিন্যাস ঘটেছে এ গ্রন্থের কবিতায়। যেমন ‘আর এক রাত্রি যদি পাই আমি পথে জিন্দেগীর / শেষ করে যাবাে তবে জীবনের যত স্বপ্ন আছে।” অথবা “মুশতারী তার মতাে হয় যদি সুদীর্ঘ জীবন / তা হলে থাকে না আর অতৃপ্ত আশার ফরিয়াদ (‘রাত্রির ঘটনা’ ‘মুহুর্তের কবিতা’)। এখানে কবির যে সূক্ষ্ম জীবনবােধ সক্রিয় তা ঐতিহ্যচেতনার হাত ধরে এক নতুন প্রত্যয়ের আলােকে উজ্জ্বল।
মুহূর্তের কবিতায় ফররুখ আহমদ একেবারে প্রথম দিককার ‘হে বন্য স্বপ্নেরা’র উত্তরাধিকার বহন করে আনেন। (স্মর্তব্য, ‘হে বন্য স্বপ্নেরা’ প্রকাশিত হয় কবির মৃত্যুর পরে)। আধুনিক কবি যে-সকল উপজীব্যে কাব্যভাষা নির্মাণ করেন তার পরিচয় ‘হে বন্য স্বপ্নেরা’তে আছে। এই গ্রন্থের কবিতায় উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা ও দর্শনের ঋজুতা নেই, কিন্তু সূক্ষ্মানুভূতি সম্পন্ন এক কবি আত্মা আছে। চারপাশের জরা ও ব্যাধিগ্রস্ত সময়, অমানবিকতায় কবি ক্ষুব্ধ। এই বিক্ষোভে তীব্রতা হয়তাে নেই, ফর্মুর মত একটি মিহি সোঁত শুধু থাকে—ম্লান চঁাদ কৃষ্ণপক্ষ রাতে’ কবির চোখে জাগে কঁচরাপাড়ায় নারী আর স্বপ্নের ইঙ্গিত। নগরের অবসাদঘন রাত্রি, প্রেত-জনতার কালাে মিছিল, পদ্মার ভাঙন-বন্যা, মানুষের অপমৃত্যু, শূন্য মাঠ, মরা ঘাস, যন্ত্রের গর্জন, ধ্বংস-দুর্ভিক্ষ, শকুনের পাখসাট এই সব ছাড়িয়ে দুর্ভেদ্য তিমির ঘন রাত্রির তােরণ হতে ভেসে আসে দোয়েলের শিস। এই সুতীব্র ঝাঝালাে ডাক ডাহুকের নয় ‘ঘুম পাড়ানাের সুরে এ তাে শুধু ঘুম ভাঙানাের তিক্ত মাদকতা। বন্দরের রশি ছিড়ে কবির নতুন যাত্রার শুরু এখান থেকেই। সাত সাগরের মাঝি’তে যাত্রা, রাত্রি ও দিনের যে বিশাল পটভূমি রচিত হয় তার বীজ লুকানাে ‘হে বন্য স্বপ্নেরা’য়। আবার ‘হে বন্য স্বপ্নেরা’র ঐতিহ্যানুসন্ধান সাত সাগরের মাঝি’র পরিপ্রেক্ষিত নির্মাণে সহায়ক হয়েছে।
(৬)
চল্লিশের দশকে সমস্ত পৃথিবীসহ ভারতবর্ষ ছিল উত্তাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশবিভাগ এসবের ঢেউ একের পর এক আছড়ে পড়েছিল। তার সঙ্গে ছিল নিপীড়িত মানুষের উত্থান। বাঙালি-মুসলমানের উত্থান—এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্য উত্তেজনা-উন্মাদনা। এইসব চল্লিশের কবিদের সমাজমুখী ও আত্মচেতন করেছিল। এসবের বাইরেও এই দশকের কবিদের কবিতায় নারীপ্রসঙ্গ নানা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উপস্থিত। কবি আহসান হাবীব ‘তােমাতে অমর আমি’ কবিতায় নারীর তিনটি সত্তা জননী, প্রেয়সী আর প্রকৃতি—এই ত্রিশক্তির এক চমৎকার ঐক্যের ভিত্তি রচনা করেছেন। এই কবিতায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যেও কবি নারীকে পুষের ‘অনিন্দ্যপ্রাণের সঙ্গী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যা নারী-পুরুযের সামাজিক-সম্পর্ক বা জেন্ডারসমতায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।
নারী জননী, সেই জননীর শৌখিন মনন ও মেজাজ-এর পরিচয় তুলে ধরেছেন কবি আবুল হােসেন তার মা ছিলেন’ কবিতায়। কবিতার ভাষাকে সরল করার সংকল্পে কবি সংসার-অনুরত্তা নারীর চমৎকার উপস্থাপন করেছেন এ কবিতায়। উত্তমপুরুষের বর্ণনায় কবি বাঙালি মধ্যবিত্ত মায়ের যৌক্তিক চরিত্র চিত্রণ করেন এভাবে “আমাদের মা ছিল বেজায় শৌখিন / কখনাে দেখিনি তাকে একটু মােটা অথবা ময়লা / কাপড়ও পরতে। বিছানায় অথবা ঘরের কোনাে / কোণে যদি ধূলাে জমলাে তার আর্ত চিৎকারে / তটস্থ সমস্ত বাড়ী। কাজের ছেলেটা কি বুড়ী ঝি / ছেলে মেয়ে এমনকি স্বামী কারুর রেহাই নেই।” (‘মা ছিলেন’)।
যেহেতু বাঙালি মুসলমানের পুনর্জাগরণকে ফররুখ আহমদ তার কবিতায় ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। যে কারণে আরব্য উপন্যাসের নায়িকারা সেকালে হয়ে উঠেছিল তার কবিতার চরিত্র। বাঙালি নারীর আদল ভেঙে ফররুখ আহমদের নারীরা তাই অনেকাংশেই হয়ে ওঠে আরব-আদর্শের নারী। সে নারীর কাছে তিনি জীবনের সুর খুঁজে বেড়ান
“চাদির তখতে চাঁদ ডুবে যায়।
পাহাড় পেতেছে জানু,
নতুন আকাশে জীবনের সুর
জাগাও হাসিন বানু।”
(শাহরিয়ার)
ফররুখ আহমদ তাঁর কবিতায় নারীকে পাখি প্রতীকের মাঝে উপস্থাপন করেন। এই পাখি প্রতীকে নারীকে রূপায়িত করার মধ্যে অবশ্য এক ধরনের পুরুষতান্ত্রিক মনােভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। দৃষ্টান্ত,
“হে পাখী শুভ্রতনু,
সফেদ পলকে চমকে বিজুরী, চমকে বর্ণধনু,
সােনালি, রূপালি, রত্তিম রংগিন।
————————————-
ইরান বাগের বেদনা ওড়ায়ে এনেছাে পক্ষপুটে
স্বপ্ন দেখেছে দূর আকাশের সেতারা তােমার সুরে,
সহসা-প্রকাশ আনারকলির পাপড়ি উঠেছে ফুটে,
লাজ-রক্তিম আনন্দ তার সকল বন্ধ টুটে,
দূর দিগন্ত পাড়ি দিয়ে তারে জাগাও তােমার সুরে
আখরােট বনে।
বাদাম, খুবানি বনে।”
ইরান-তুরান-আরব আখরােট, বাদাম, খুবানি—এইসব শব্দের অনুষঙ্গে কবি কবিতায় যে পরিবেশ রচনা করেন, সেখানে তার চিত্রিত নারীদের কোনােমতেই বাঙালি নারী মনে হয় না। এছাড়া কবি ফররুখ আহমদ তাঁর কবিতায় নারীকে বিষয়ীগত নন্দনতত্ত্বের আলােকে মূল্যায়ন করেন। যেখানে নারী স্বকীয়ভাবে সুন্দর নয়। পুরুষতন্ত্রের কারণে পুরুষের প্রেম ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সুন্দর। নারীকে তিনি ছলনাময়ী হিসেবেই চিহ্নিত করেন—
“হে প্রিয়া শাহেরজাদী। তুমি আজ কী অজ্ঞাত প্রেমে
জেগে ওঠো শঙ্কায়, লজ্জায়?
তােমার সকল প্রেম আবার লুকাতে চায়
নেকাব-প্রচ্ছায়?
বৃথা বাজে রিনিঝিনি
হীরার জেওর!
হে ছলনাময়ী! অন্ধপুষের, পৌরুষের কেড়ে নাও
শ্রান্ত ঘুমখাের,
ছড়াও পরাগ রক্তধরা
জাফরানের মধু-গন্ধ ভরা।
তােমাকে সুন্দর করে সে আমার প্রেম
অন্তরের ঘ্রাণ, ..”
(ঝরােকা)
(৭)
ফররুখ আহমদের কাব্যে ইসলামি অনুসঙ্গের প্রসঙ্গটি নিয়ে অনেক সাহিত্য সমালােচক কটা( করেছেন। এটা ঠিক যে, তার কবিতার প্রধান সুর ইসলামি সেন্টিমেন্ট বা ধর্মীয় অনুভূতি। কবি পি বি শেলী তার ‘এ ডিফেন্স অফ পােয়েট্রি’তে কবিতায় ধর্মীয় অনুভূতিকে স্বীকার করেছেন। আর ধর্মীয় বিষয় যে কবিতায় থাকতে বাধা নেই, অমীয় চক্রবর্তীর ইকবাল ভাবনায় তা আছে। অমীয় চক্রবর্তী, আহসান হাবিব, সৈয়দ আলী আহসান, আবুল হােসেন ইকবালের কবিতা অনুবাদ করেছেন, ফররুখ আহমদও করেছেন। ফররুখ আহমদ জিন্নাকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন, সুকান্ত ভট্টাচার্যও ‘জিন্না’কে নিয়ে কবিতা লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জিন্নাহর জনসভায় ভাষণ লিখে পাঠিয়েছেন, ফররুখ আহমদ জিন্নাহর আজাদ করাে ‘পাকিস্তান’ লিখেছেন। আমরা ১৯৪৭-এর পূর্বের অনুভূতিকে ১৯৭১-এর অনুভূতি দিয়ে বিচার করে ফররুখ আহমদের প্রতি সুবিচার করিনি, তাতে ক্ষতি হয়েছে বাংলা সাহিত্যের, ফররুখ আহমদের নয়। আর ফররুখ আহমদের কবিতায় ধর্মীয় অনুভূতি? বাংলা কবিতার প্রাচীন যুগে। বৌদ্ধদের ধর্মীয় অনুভূতি, মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতি এবং বাংলা কবিতার আধুনিক যুগের ‘আদি আধুনিক’ মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভারতীয় ধর্মীয় অনুভূতি, সবকিছুতে ধর্মীয় উৎস কাজ করেছে। তাছাড়া আধুনিক বাংলা কবিতার তিরিশের দশকের প্রধান কবিরা যেমন জীবনানন্দ দাশ, অমীয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু তারা তাদের কবিতায় ধর্মীয় অনুভূতি (ধর্মীয় অনুভূতি অর্থে হিন্দু পুরাণ, কারাে কারাে ক্ষেত্রে মুসলিম শাস্ত্র) থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখতে পারেননি।
টি এস এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫) যখন তঁার ‘দ্য ওয়াস্ট ল্যান্ড’-এ উপনিষদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন, তখন তিনি খ্রিস্টান জীবনকে গ্রহণ করেন না—তার কাব্য ভাবনায় কাজ করে হিন্দুদের উপনিষদ। রবিনসন জেফার্স (১৮৮৭-১৯৬২) হিন্দুদের শিবকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন, তাই বলে তিনি হিন্দু হয়ে যাননি, আমেরিকান খ্রিস্টানই ছিলেন। কাজেই কোনাে কবিকে ধর্মীয় বেড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা উচিৎ নয় বা মূল্যায়ন করা যায় না।
কবি ফররুখ ‘নৌফেল ও হাতেম’ ও ‘হাতেম তায়ী’ শীর্ষক রচনা দুটিতে রূপকের শরণাপন্ন হয়েছেন। বহুল প্রচলিত হাতেম তায়ী পুঁথির কাহিনি অবলম্বনে রচিত তাঁর এ-দুটি কাব্যে তিনি রক্তপাত ও যুদ্ধ বিগ্রহ বর্জন করেও মহৎ মানবতা যে জয়ী হতে পারে তাই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন বলে মনে হয়। টলস্টয়ী মানবতাবােধ থেকে এ মানবতাবােধ পৃথক বলে মনে হয় না। স্মরণযােগ্য যে, টলস্টয়ও তার আদর্শ এবং খৃষ্টধর্মের মধ্যে কোনাে বিরােধ খুঁজে পাননি। টলস্টয়ের মতাে টি এস এলিয়টও ভালাে খৃষ্টান হয়েও ভালাে কবি।
ফররুখ আহমদ আধুনিক বাংলা কবিতায় ইসলামি ঐতিহ্যের নব-রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। এই ঐতিহ্য সংক্রান্তি বিষয়ে অনেকের রয়েছে উন্নাসিকতা। অথচ তারা ভুলে যান, ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে কোনাে সাহিত্যই দাঁড়াতে পারে না, ঐতিহ্যই হল তার ভিত্তিভূমি। দার্শনিক চিন্তা-চেতনায় থাকতে পারে মতপার্থক্য, সেই দর্শনের আলােকেই ঘটে নব-রূপায়ণ। ফররুখ আহমদ আধুনিক কবিতায় ঐতিহ্যের নতুন মাত্রা দিয়েছেন তার দর্শনিক চেতনায়। ঐতিহ্যের অনুগমন করেই তিনি স্বপ্ন দেখেছেন ‘গড়ে তােল সেই ডেরাপৃথিবী নুতন/প্রশান্তি, সুষমাময়, পরিপূর্ণ প্রেম ও সেবায়।
ফররুখ কখনই স্বদেশ ও স্ব-কালকে এড়িয়ে যাননি। বরং তিনি স্বদেশের ঘটনাপ্রবাহে ও স্ব-কালের স্রোতধারায় আলােড়িত হয়েছেন। তার কবিতায় বার বার এসেছে দেশের চিত্র, কালের প্রতিচ্ছবি। স্বদেশ ও স্ব-কালে ঐতিহ্যের সংযােগ তার কবিতাকে কাল ও ভূখণ্ড উত্তীর্ণ করে ধ্রুপদ করে তুলেছে।
ফররুখ আহমদ কবির ধর্মে আস্থাশীল ছিলেন। মুসলিম জীবন ও ঐতিহ্যকে তিনি কবির দৃষ্টিতে বিচার করেছেন। আর তা অন্যায় নয়, যেমন অন্যায় নয় উল্লেখিত ভিন দেশীয় কবিদের হিন্দু-মুসলিম প্রসঙ্গ নিয়ে কবিতা লেখা। আমরা ফররুখ আহমদের ‘হাতেম তায়ী’-এর শেষের দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাব, সেখানে ইসলাম বা অন্য কোনও ধর্মের কেউ বড় হয়নি—বড় হয়েছে। ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে মানুষ-
“সন্ততিরা,—আসে নাই যারা আজও পৃথিবীর বুকে
(অস্পষ্ট আলাের মত দেখি আমি নিশানা যাদের
দূর নীহারিকা লােকে), মুক্তি যেন পায় সে আউলাদ
সকল বিভ্রান্তি, পাপ, অত্যাচার অবিচার থেকে।
বহু খণ্ডে বিখণ্ডিত মানুষের বিচ্ছিন্ন সমাজে
সকল বিভেদ মুছে করে যেন শান্তির আবাদ
সকল বিশ্বাসী প্রাণ-ইনসানে কামিল। আর যারা
পড়ে আছে লুণ্ঠিত ধূলায়, নির্যাতিত সেইসব
মজলুমান পায় যেন বাঁচার অকুণ্ঠ অধিকার
সব মানুষের সাথে জীবনের পূর্ণতার পথে
চলে যেন সে মিছিল কেবলি সম্মুখে।”
অথবা
“আদমের আউলাদ, এক খান্দানের গােত্রভুক্ত
নারী-নর, দেশে দেশে দূরান্তরে রয়েছে ছড়িয়ে
বহু বর্ণ, অসংখ্য জবান কিন্তু রক্তধারা এক।
এক অনুভূতি হৃদয়ের। হাসি ও কান্নার অশ্রু
বয়ে যায় একভাবে নীড় বাঁধা জীবনে, অথবা
মরুচারী বেদুইন যাযাবর জীবনের স্রোতে।
আল্লাহর রহমত, রেজা ঘিরে আছে একভাবে এই
দুনিয়া জাহান। মুক্ত আলাে বায়ু নামে একভাবে
জনপদে, এক স্নেহচ্ছায়া ঘিরে আছে এ পৃথিবী
আল্লার সংসার। তবু কেন এ বিভেদ ইবলিসের
কি দুরাশা ধ্বংস করে মানুষের ঘর? কেড়ে নেয়
শিশুর মুখের হাসি মুছে ফেলে শক্ত তরুণের,
স্তব্ধ করে বলদর্পী কি আশায় জ্ঞানীর জবান?
রক্ত শােষণের পালা চলেনি কি অব্যাহত আজও
এই পৃথিবীতে? ..”
ফররুখ আহমদের এই অনুভূতি সার্বজনীন, এই উপলব্ধি বিং মানবতাবাদকে সমর্থন করে। এ উক্ত যে শুধু হাতেম তায়ীর তা নয়, ফররুখ আহমদেরও। আসলে ধর্মীয় কবিতা লিখতে গিয়ে তিনি সমাজকে ভােলেননি। সমাজের মানুষকেও এড়িয়ে যাননি। ধর্মান্ধতাকে তিনি কখনও বড় করে দেখেননি। হিন্দুর ধর্ম, মুসলমানের ধর্ম, খ্রীষ্টানের ধর্ম আলাদা হতে পারে কিন্তু মানুষের ধর্ম এক। ওখানেই মানুষের এক জাতিত্ব ও আসল স্বরূপের প্রকাশ।
বলা বাহুল্য হাতেমের পূর্ণ সাফল্য ও বিজয়ের মৌল রহস্য কি? সে হল আল্লাহর প্রতি অবিচল বিধাস আর মানুষের প্রতি অবিমিশ্র প্রেম এবং তা সম্পূর্ণভাবে নিষ্কলুষ প্রেম। এই প্রেম মানুষের জন্য সর্বত্যাগীর, সর্বস্বত্যাগীর। দুসরা সওয়াল-এর ‘পরীর প্রেম’ পরিচ্ছেদে কবি প্রেমের শক্তির সেই ব্যাখ্যা এইভাবে দিয়েছেন—
“পারেনি যেখানে যেতে কোন প্রাণী শক্তিমান
কি করে সেখানে যাবে ঐ পরী নাজুক প্রাণ!
প্রেমের শক্তি কাটবে কি তবে এ শর্বরী ?
হাতেম তায়ীকে চিনেছিল শুধু হাসনা পরী।
অস্ফুট স্বরে পরী-রাণী তবে এ কথা বলেঃ
প্রেমের পন্থা মানেনি তাে বাধা জগদ্দলে,
মাশুকের পথ চেয়েছে জাহানে আশেক যদি
পারেনি কখন বাধা দিতে তারে পাহাড়, নদী
পারেনি কখন থামাতে সে গতি গিরি ও দরি!
হাতেম তায়ীকে চিনেছিল শুধু হাসনা পরী।”
এই মনুষ্যত্ব ও মানবতাবােধ হাতেম তায়ীতে পরিশুদ্ধ পরিণতিতে পৌঁছেছিল কিন্তু তার আরম্ভ হয়েছিল ফররুখের কাব্যজীবনের শুরুতে। কবির প্রথম জীবনের কবিতা ‘রাত্রির অগাধ বনে’, ‘স্বপ্ন শেষ’, শকুনেরা’ অথবা ‘লক্ষ্য ধ্বংস্তুপ’, ‘দুর্ভিক্ষের সন্তান’, ‘প্রেরণ’, ‘পরিপ্রেক্ষিত’, ‘এই সংগ্রাম’, ‘আজ সংগ্রাম’, এবং কিছু পরিণত যৌবনে রচিত তার লাশ’ প্রভৃতিতে আমরা যে কবিকে দেখি তিনি মানবতার লাঞ্ছনায় ব্যথিত ও বিদ্রোহী। এই বেদনা ফররুখ কে একটি সমাধানকারী আদর্শের দিকে আকর্ষণ করেছে। তাঁর সমসাময়িক কালে সুভাষ, সুকান্ত প্রমুখ কবিদের কবিতাতেও ওই ব্যথিত মানবতার জন্য হাহাকারের সুর তীব্র হয়ে বেজেছিল এবং তারাও একটি বিশেষ আদর্শের সংগ্রামে নিপীড়িত মানুষের দুঃখের সমাধান খুঁজেছিলেন কিন্তু সে সমাধানের পথে ফররুখ স্বস্তি না পেয়ে অন্য পথ অবলম্বন করেন। এতে বাংলা কাব্যে কেবল বৈচিত্র বৃদ্ধি হল না, ফররুখ নিজেও মুক্তি পেলেন এবং এক নিজস্ব ধারার সৃষ্টি করতে সমর্থ হলেন।
ফররুখ ‘কাফেলা’ কাব্যগ্রন্থে ‘শিকল’ নামক কবিতার মাধ্যমে শােষিত-বঞ্চিত-অত্যাচারিত জনতার পথে মুক্তির মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। যেমন—
“শিকল যদিও শিথিল হয়েছে বণিক রাজার
পুঁজিবাদ তবু শতমুখে তার বিষ ছড়ায়,
বর্গীরা লােটে দুই হাতে ধান, শূন্য খামার
বিরান বাগের বুলবুল হ’ল শকুনি হায়,
মজলুমানের রক্তে এখনাে পৃথ্বি লাল
কোথায় ওড়াবাে শান্তি প্রতীক আল-হেলাল?
কোথায় ওড়াবাে হেলাল? সামনে মৃত্যু-প্রাকার!
কোথায় আমার মুক্তির দিশা-পথ রঙিন ?
হানে বিশ্বাসে ইবলিস্ তার খঞ্জর ধার,
হায় পলাতক এখনাে তােমার আসেনি দিন,
খােলেনি অন্ধ আজো কবন্ধ রাতের খিল
আধারের চেয়ে আরাে বিষাক্ত, ক্রুর জটিল।
হে নকীব! জাগাে, জাগাও সুপ্ত দিগন্ত নীল,
সব বন্ধন মুক্তির সুর বাজাও আজ,
ইস্রাফিলের ‘সুরে’ পৃথিবীকে জাগাও আজ!
চির পলাতক শিকার সে হােক দৃপ্ত আজ
মানবতা হােক নির্যাতিতের মাধার তাজ।।”
কবি ফররুখ আহমদ পুঁজিবাদ-ধনতন্ত্রের ঘাের বিরােধী ছিলেন। আর গরীব দুখী-অসহায়ের পক্ষে লড়াই করেছেন—তার কবিতায় তার প্রমাণ। তিনি তার ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক ‘কাব্যে’র এক স্থানে বলেছেন,
“গরীবের হাড়ে তৈরী হয়েছে তখন ইমারত,
শাহী বালাখানা আর বেশুমার হেরেমের পথ।।
কওমের অগ্রগতি হয়েছে তখন চক্রগতি,
অভিনব অর্থ নিয়ে জেগেছে বিকৃতি শরাফতি!
ধর্ম ব্যবসায়ী, পাপী কিংবা ধর্ম বহির্ভূত মন
জামাতের পুরােভাগে ইমামতি করেছে তখন
অথবা বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে ঢের ধূর্ত সুচতুর
প্রচুর মুনাফা লুটে ধর্মকেই করেছে ফতুর!
কৌশলী শিকারী যত খেলােয়াড়ী চালে অপরূপ
সিঁদকাঠি না নিয়েও করে গেছে তবিল তসরূপ।
নিতান্ত বেহুশ বলে জাতি আর পায়নি সম্বিৎ!
এভাবে কোথায় থাকে চিরস্থায়ী আজাদীর ভিত?”
তিনি তার ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্যে’-র অন্য এক স্থানে বলেন,
“চোরাগােপ্তা পথ যিনি নেন বেছে হাটে ও বাজারে
সন্ধ্যায় তাকেই দেখি সুফীবেশে পীরের মাজারে!
শ্রমসাধ্য কাজে যিনি বারবার দিয়ে যান ফাকি
পীরের খলিফা সেজে গ্রামে তিনি করেন মােল্লাকি
বিবিধ কুকাণ্ড করে বহু বা বক্তৃতা মফিলে
সর্বদা দারাজ দস্ত নেন কিছু নিজস্ব তবিলে।
অকর্মা সুবাদে সৎ দুনিয়ার অপদার্থ যত
বিব্রত বা ব্যতিব্যস্ত প্রশংসা কুড়াতে অন্তত,
যদ্যপি এ দুনিয়ায় নাই কারাে কানাকড়ি দাম।
সর্বদা খোঁজেন তারা কর্মহীন ‘ভালাে’র ঈনাম!
কঠিন কর্তব্য যত এডিয়ে সহজে সবিনয়ে।
চাতুর্য দেখাতে ফের অংশ কেউ নেয় অভিনয়ে
দেখাতে কৃষ্টির খেল অনাসৃষ্টি ঘটিয়ে পাপের
নবােদ্যমে টানে জের নওরােজ, মীনা বাজারের!
মীরজাফরের যুগে ভাবেনি যা কেউ কোন দিন
এ যুগে বাচ্চা বুড়া সে পথেও হয় যে রঙিন!”
মানবিকতার এ ধারা ফররুখ শেষাব্দি প্রবহমান রেখেছিলেন।
মাইকেল মধুসূদন দত্ত কারবালার কাহিনি নিয়ে মহাকাব্য লেখার ইচ্ছা পােষণ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও দুঃখ প্রকাশ করে আবুল ফজলকে লিখেছিলেন—
“চাদের এক পৃষ্ঠায় আলাে পড়ে না সে আমাদের অগােচর, তেমনি দুর্দৈবক্রমে বাংলাদেশের আধখানায় সাহিত্যের আলাে যদি না পড়ে তাহলে আমরা বাংলাদেশকে চিনতে পারব না, না পারলে তার সঙ্গে ব্যবহারের ভুল ঘটতে থাকবে।”
ফররুখ আহমদ আরবের কাহিনি কিংবা কারবালার কাহিনি নিয়ে মহাকাব্য রচনা করেননি, তবে কারবালার কাহিনিকে কবিতায় রূপ দিয়েছেন এবং আরবের লােককাহিনি হাতেম তায়ী’কে নিয়ে মহাকাব্য লেখার চেষ্টা করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভকে প্রশমনের চেষ্টা করেছেন ফররুখ আহমদ, তাঁর কবিতায় মুসলিম জীবনের চিত্র অঙ্কন করে।
(৮)
মধুসুদনের সঙ্গে ফররুখ কে আমরা তুলনা করেছি। মধুসূদনের ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’ কবির শক্তি, সামর্থ ও ঊর্ধগামিতার যে ঝলসানাে রূপের ধারক, তার সর্বশেষ সৃষ্টি ‘মায়াকানন’ তার দেউলিয়াত্বের দর্পণ রূপে তার ফতুর দশার অভিজ্ঞান রূপে উত্থান ও পতন নির্দেশ করছে। কিন্তু ফররুখের ক্ষেত্রে এই সাদৃশ্য টানার প্রস্তাব আমরা করি না। কারণ, ‘হাবেদা মরুর কাহিনী’ ‘মায়া কানন’-এর মত ফতুর নয় কিংবা হালকাও নয়। ‘হাবেদা মরুর কাহিনী’ একটি নিরাভরণ সার্থক রূপক কাব্য। আগাগােড়া এক সীটিয়ে বসে দারুণ ঔৎসুক্যে এটি পড়তে হয়। আমাদের স্বকাল এতে এমনি রূপে অঙ্কিত যা রূপকে-প্রতীকেও হুবহু তাই। এটি একটি গদ্য পৃথিবীর রূপকাশ্রয়, একটি সরল রেখায় খচিত, মাত্র একটি ভূষণে ভূষিত। ফররুখ যেহেতু যথাযথ কালচেতনায় প্রাজ্ঞ তাই তিনি তা পারেন না। এখানে কবির প্রতিভার ফতুরত্ব আবিষ্কার নিরর্থক। যেমন নুন-পানি, তেমনি কাম জানি’ এই হচ্ছে দক্ষ রাঁধুনির বচন। যেমন কাল তেমনি তার রূপাঙ্কন দক্ষ কবিরই কাজ। যথা উত্তুঙ্গ ‘বলাকা’ রচয়িতার রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছেন ‘পুনশ্চ’ কাব্য সাদামাটা গদ্যে কালের সঙ্গে তাল ঠুকে। তেমনি ‘সাত সাগরের মাঝি’র কবিও স্বকালের সঙ্গে ঘরােয়া গদ্যের মিতালি পেতেছেন হাবেদা ‘মরুর কাহিনী’তে মাত্র একটি কারণে —
“যেন বঞ্চিত বনি আদমের দীর্ঘশ্বাস
রূপ নিতে পারে শান্তির প্রশ্বাসে
যেন এই তৃষাতপ্ত হাবেদার মরু মাঠ।
আবার হতে পরে
সুন্দর শান্তিময় মাটির জান্নাত
দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য।
দুনিয়ার সকল মানবীর জন্য।”
(উনপঞ্চাশ হাবেদা মরুর কাহিনী)
এই গ্রন্থের শেষ কবিতার একেবারে শেষাংশ হতে উপরের উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে। কবির অশেষ শুভ কামনা বলিষ্ঠ আশাবাদ, মানবমুক্তির দূর্জয় স্বপ্নসাধের সকল উপকরণই এখানে আছে। এশিয়ার কুড়ি কোটি জনতা অধ্যুষিত একটি সভ্যমণ্ডলের মুখ্য কবিকণ্ঠরূপে তার এই উচ্চারণ খুব সহজেই বলে দেয় যে, ইনি ‘ফররুখ আহমদ’। আমরা তাই কবির মরণােত্তর পর্বের এ কাব্যগ্রন্থকে ফররুখের একটি উল্লেখযােগ্য সৃষ্টি এবং আমাদের সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ রূপক কাব্য রূপেই গণ্য করতে চাই।
শেষে বলা যায় যে, কবি ফররুখ আহমদ বাংলার কবিতাঙ্গনে একজন বলিষ্ঠ কবিপুরুষ। কল্যাণময় বিধগড়ার স্বপ্নই তিনি দেখে গেছেন এবং সেই স্বপ্নের আশ্লেষ তিনি তার সাহিত্যের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছেন আমাদের মনে। তিনি আমাদের জাগর স্বপ্নের কবি। তাঁর কবি-ভাষায় আমাদের জীবনের কথা, স্বপ্ন-কল্পনার কথা সমুচ্চারিত হয়েছে। তাঁর কাব্যের আবেদন তাই অনিঃশেষ। পাদপ্রদীপের সামনে না দাঁড়ান, ঢক্কা-নিনাদ না থাক— মাস মিডিয়ার সুবিধার বেদীতে তিনি নাই বা দাঁড়ালেন—তাঁর কবিতা কালের নিক্তিতে ও কষ্টিপাথরে ওজন-যাচাইয়ে খাঁটি সােনা বলেই প্রতিভাত হবে। সুনীলকুমার মুখােপাধ্যায় লিখেছেন,
“ফররুখ আহমদ সম্পর্কে যে কয়েকটি কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় তা হচ্ছে এই যে, তিনি আধুনিক বাংলা কাব্যের এক শক্তিমান শিল্পী। সীমিত ভাবনার পরিমণ্ডলেও তিনি বিরল-দৃষ্ট শিল্প সামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা কাব্যের ভাষা, ছন্দ ও আঙ্গিকের উৎকর্ষ বিধানে তাঁর প্রযত্নের অন্ত ছিল না।”
তথ্যসূত্রঃ
- ১. ফররুখ আহমদ রাত্রি, বুলবুল, শ্রাবণ ১৩৪৪।
- ২. ফররুখ আহমদ পাপ জন্ম, মাসিক মােহাম্মদী, শ্রাবণ ১৩৪৪।
- ৩. সাইয়েদা ইয়াসমিন বানু, আব্বাকে যেমন দেখেছি, দেখুন-শাহাবুদ্দিন আহমদ সম্পাদিত, ফররুখ আহমদ ব্যাক্তি ও কবি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ২৮৪।
- ৪. জিল্লুর রহমান সম্পাদিত, হে বন্য স্বপ্নেরা, ঢাকা, ১৯৭৬, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
- ৫. সুনীলকুমার মুখােপাধ্যায়, কবি ফররুখ আহমদ, নওরােজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৯, পৃ. ৬৩।
- ৬. ফররুখ আহমদ সাত সাগরের মাঝি, দেখুন-মােহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ও আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, ফররুখ রচনাবলী, খণ্ড-১, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৭৯, উৎসর্গ অংশ দ্রষ্টব্য।
- ৭. মাসিক মােহাম্মদী, বিভিন্ন সংখ্যা।
- ৮. সওগাত, বৈশাখ ১৩৫২।
- ৯. ফররুখ আহমদ, মুহূর্তের কবিতা, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকি সম্পাদিত, পরিমার্জিত দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, ১৯৭৮।
- সাহিত্য সমালােচক মােহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ‘মুহূর্তের কবিতা সম্পর্কে বলেন, “এই সনেট-সংকলনের মাধ্যমে পাকবাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য নির্মাণ ও নির্দেশের চেষ্টা হয়েছে। মুহূর্তের কবিতা পাঠে স্বাভাবিকভাবেই যে অনুভূতিটি আমাদের স্পর্শ করে তা হল এই, আদর্শানুগত্য এবং ঐতিহ্যলগ্ন হয়ে থেকে ফররুখ আহমদ যে কবি-মানসটিকে গড়ে তুলেছেন। মুহূর্তের জন্যে তা চরিত্রভ্রষ্ট হয়নি।… ঐতিহ্য বােধের যে বিকাশ ফররুখ আহমদের সাত সাগরের মাঝিতে লক্ষ্যণীয়, মুহূর্তের কবিতায় তা ব্যাপকতায় সমৃদ্ধমান।” (দেখুন- মােহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, ‘পঁচিশ বছরের কবিতা’, উত্তরাধিকার, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ১৯৩)।
- ১০. ফররুখ আহমদ, নৌফেল ও হাতেম, পাকিস্তান লেখক সংঘ, ১৯৬১, ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা,
- ১১. ফররুখ আহমদ, হাতেম তায়ী, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৩৭৩।
- ১২. সুনীল কুমার মুখােপাধ্যায়, কবি ফররুখ আহমদ, দেখুন-বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সােসাইটি লিঃ সংকলিত, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৭।
‘নবজাগরণ’ অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপ্লিকেশনটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।
![]()
‘নবজাগরণ’ এর টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।
‘নবজাগরণ’ এর ফেসবুক পেজে লাইক করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

 নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা
নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা