উনিশ শতকের প্রবুদ্ধ বঙ্গসমাজের পুরােধাদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০১৮৯১) ছিলেন নিঃসন্দেহে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। যখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর জন্ম হয়, তখন বাংলার ধর্ম ও সমাজ জীবন এক চরম ক্রান্তিকালের মুখােমুখি। একদিকে যেমন খৃষ্টান মিশনারীদের অত্যধিক উৎসাহ ও আগ্রহে হিন্দুধর্মের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি রাধাকান্ত দেবের (১৭৮৪-১৮৬৭) নেতৃত্বে রক্ষণশীলদের প্রবল বাধায় হিন্দুধর্ম ও সমাজ সংস্কারের অত্যন্ত প্রয়ােজনীয় কাজ ব্যাহত হচ্ছিল। খৃষ্টান মিশনারীদের হাত থেকে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করার ব্রত যদি রামমােহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) গ্রহণ না করতেন, তাহলে সনাতন হিন্দুধর্মের পরিণতি যে কি হতাে তা অনুমেয়। খৃষ্টান মিশনারীদের তখন একমাত্র লক্ষ্য ছিল যেনতেন প্রকারে ভারতে খৃষ্টধর্মের প্রচার করা। খৃষ্টান মিশনারীদের মনের ভাব আলেকজান্ডার. ডাফ খােলাখুলিভাবেই প্রকাশ করে বলেছিলেন এভাবে: ‘The Prevalent idea seemed to be, that by fair means or foul-by bribery or magical influence by denunciation or corporeal restraint we were determined to force the youngmen to become christians.’ কিন্তু রামমোহনের কঠোর যুক্তিবাদ ও উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং সর্বোপরি তার একেশ্বরবাদী প্রচেষ্টা হিন্দুদের মনঃপুত হয়নি। ফলে রামমােহনকে হিন্দুরাই পছন্দ করেনি। তাঁর প্রগতিশীল সমাজ সংস্কারে রাধাকান্ত দেব ও তার অনুগামী রক্ষণশীলরা বাধা দিয়ে ১৮৩০ সালে ধর্মসভার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; তাদের লক্ষ্য ছিল এই সব সংস্কারের প্রচেষ্টা ভেঙে দেওয়া। অথচ হিন্দুধর্ম ও সমাজের কুপ্রথা-কুসংস্কার দূর করতে না পারলে হিন্দুধর্মের পক্ষে খৃষ্টান মিশনারীদের আক্রমণ ঠেকানাে সম্ভব ছিল না। কিন্তু শুধু খৃষ্টান মিশনারীরাই নয়, বেপরােয়া ডিরােজিওর অনুগামী ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যগণও হিন্দুধর্মের অস্তিত্ব বিলােপ করতে চাইছিল। সুতরাং বিদ্যাসাগর যখন সমাজ সংস্কারে ব্রতী হন, তখন কোনাে দিক থেকেই পরিস্থিতি তার অনুকূল ছিল না।

কোনও বাধা বিপত্তির সামনে মাথা নােয়ানাের মানুষ বিদ্যাসাগর ছিলেন না। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ভাষায়: “এই দেশে এই জাতির মধ্যে সহসা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর মত একটা কঠোর কঙ্কালবিশিষ্ট মনুষ্যের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়।…তাহার বঙ্গদেশে আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে সন্দেহ নাই।” প্রায় একই কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ: “আমাদের এই অবমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর মতাে এমন অখন্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, আমরা বলতে পারি না। কাকের বাসায় কোকিল ডিম পাড়িয়া যায়—মানব ইতিহাসের বিধাতা সেইরূপ গােপনে কৌশলে বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন।”
(১)
রামমােহনের পর বিদ্যাসাগরই বাংলাকে মানুষ করার ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু রামমােহনের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর অনেক বিষয়েই মিল ছিল না। ইউরােপীয় ভাবাদর্শ ও চিন্তা বিদ্যাসাগরকে রামমােহনের মত গভীরভাবে প্রভাবিত করেনি। রামমােহনের মত প্রসারিত আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি তার ছিল না। বিদ্যাসাগর ছিলেন একান্তভাবেই বাংলার ঘরের মানুষ। সাজে পােষাকে, আচার ব্যবহারে তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালি ব্রাহ্মণ। অথচ রাধাকান্ত দেবের মত গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতা থেকে তিনি ছিলেন মুক্ত। রামমােহন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আদর্শ সম্পর্কে এতই মােহমুগ্ধ ছিলেন যে, সংস্কৃত ও দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ বা উৎসাহ ছিল না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মধ্যে এই ধরণের মনােভাব ছিল না। তিনি সংস্কৃত পন্ডিত হলেও, ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়ােজনীয়তা সম্পর্কে সব সময়েই সচেতন ছিলেন। রামমােহনের মত শিক্ষা বিস্তারে তারও যথেষ্ট আগ্রহ ছিল ও তিনি মনে করতেন শিক্ষার আলােতেই অজ্ঞতার অন্ধকার দূর হয়ে যাবে।
লক্ষ্য করার বিষয়, শিক্ষা বিস্তারে রামমােহনের প্রচন্ড উৎসাহ ও আগ্রহ থাকলেও স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে তিনি তেমন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেননি। অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে অগ্রনায়ক ছিলেন এবং বেথুনকে তাঁর বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের কাজে সর্বতােভাবে সাহায্য করেন। অবশ্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ও বিচ্ছিন্নভাবে এবং উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতবিহীনভাবে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার কিছু প্রচেষ্টা ইতােপূর্বেই শুরু হয়েছিল। এর সূত্রপাত হয় খৃস্টান মিশনারীদের দ্বারা। চুঁচুড়াতে মিঃ রবার্ট মে কর্তৃক ১৮১৮ সালে নারীদের জন্য প্রথম মিশনারী স্কুল প্রতিষ্ঠার পর স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে প্রথম একটা সংগঠিত উদ্যোগ দেখা যায় ১৮১৯ সালে ‘ক্যালকাটা ফিমেল জুভেনাইল সােসাইটি’ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। সরকারী রিপাের্টে জানা যায় যে এই সােসাইটি কলকাতা ও তার পাশ্ববর্তী অঞ্চলে তিনটি বিদ্যালয় পরিচালনা করত যেখানে ২০০ জন বালিকা বানান, ভূগােল ইত্যাদি শিক্ষা লাভ করত।১ বাঙালিদের মধ্যে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন প্যারীচাঁদ সরকার, ১৮৪৭ সালে বারাসাতে। তারপর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর প্রচেষ্টা বঙ্গদেশে বাস্তবিকপক্ষে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ঘটায়।
ইতিমধ্যেই ডিরােজিয়ানদের এবং আগে কয়েকজনের উদ্যোগে স্ত্রীশিক্ষার কিছু প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। বাংলার পত্র-পত্রিকাগুলিতেও স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে কিছু আলােচনা প্রকাশিত হয়েছিল। রাজা রাধাকান্ত দেব, যিনি বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রচেষ্টার ঘােরতর বিরােধী ছিলেন, তিনিও স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে আগ্রহী ছিলেন। বিশেষ করে ১৮৪৮ সালে বেথুন সপারিষদ গভর্ণর জেনারেলের আইন সদস্য এবং শিক্ষা পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হবার পর স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে একটা নতুন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়। তারপর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং সে প্রচেষ্টায় বেথুনের সহযােগিতা স্ত্রীশিক্ষায় একটা প্রাণ সঞ্চার হয়। স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের এই প্রচেষ্টায় অনেকেই তার সহযােগী হয়েছিলেন। বেথুন স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর তার সম্পাদকের দায়িত্ব বিদ্যাসাগরের উপরই অর্পণ করেন।২ এই বেথুন স্কুল শুধু নয়, বিভিন্ন স্থানে স্কুল স্থাপন এবং এই বিষয় নিয়ে উচ্চতর সরকারী অধিকর্তার সঙ্গে তার মতবিরােধ এবং মাসিক ৫০০ টাকা মাহিনার চাকুরি অনায়াসে ত্যাগ, নিজ ব্যয়ে বিদ্যালয় পরিচালনা ইত্যাদি ঘটনা শিক্ষা বিস্তার এবং বিশেষ করে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের দৃঢ়তারই সাক্ষ্য বহন করে। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : “মতভেদ নিবন্ধন, বিশেষতঃ তাহার স্বদেশীয় বন্ধুদের কাহারও কাহারও অত্যধিক উৎপীড়নে, শেষে বিরক্ত হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বেথুন স্কুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংশ্রব ত্যাগ করেন, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার সুপ্রচার সাধনকল্পে যে সকল অনুষ্ঠান আয়ােজন হইত, তাহাতে তাহার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত হৃদয়ের পূর্ণ যােগ ছিল। কোথাও ঐরূপ কার্যের অনুষ্ঠান হইলে, তাহাতে সাহায্য করিতে কখনও বিরত থাকিতেন না। পুরনারীগণের শিক্ষা দিবার জন্য বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় যে সকল স্ত্রীশিক্ষা-বিধায়িনী সম্মিলনী স্থাপিত হইয়া স্ত্রীশিক্ষার সপ্রচার সাধন করিতেছে, সে সকলের প্রতি তাহার বিশেষ স্নেহদৃষ্টি ছিল। উত্তরপাড়া হিতকারী, শ্রীহট্ট ও মৈমনসিংহ সম্মিলনী, ফরিদপুর সুহৃদ সভা, বাখরগঞ্জ হিতসাধিনী, বিক্রমপুর সম্মিলনী, মধ্য বাঙ্গালা সম্মিলনী প্রভৃতির কার্যবিবরণী শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। আমরা কোন সম্মিলনীর পারিতােষিক বিতরণ উপলক্ষে তাহার নিকট পুস্তকাদি সাহায্য প্রার্থনার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া যাইতাম। সে সময় প্রসঙ্গক্রমে এইসকল সম্মিলনীর বিষয় অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। ঐরূপ কোন সম্মিলনীর দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার সহায়তা হইতেছে শুনিলে, গভীর আনন্দ প্রকাশ করিতেন।”৩
এই বিবরণের মধ্য দিয়ে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর অকৃত্রিম আগ্রহ ও আন্তরিক প্রয়াস অত্যন্ত নিখুঁতভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। তারপর শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রী হিসাবে প্রথম এম.এ. পাশ করলে বিদ্যাসাগর আনন্দে কেমন অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন তাঁর সাক্ষ্য পাওয়া যায় চন্দ্রমুখীকে এক প্রস্থ শেকসপীয়ার রচনাবলী উপহার এবং সেই গ্রন্থে উষ্ণ অভিনন্দনমূলক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে।৪
গুণগত মানে নয়, উদ্দেশ্যগত ব্যাপ্তিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি ছিল মহত্তর। ১৮৫৩ সালে বীরসিংহ গ্রামে অবৈতনিক ও আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত ৩৭ বছর ধরে তিনি একটি নর্মাল স্কুলসহ ২০টি মডেল স্কুল, ৩৫টি (৪৩) বালিকা বিদ্যালয় ও একটি কলেজ স্থাপন করেছিলেন। এর মধ্যে বীরসিংহের আবাসিক বিদ্যালয়টি চলত বিদ্যাসাগরের অর্থে। তার প্রতিষ্ঠিত সব স্কলই ছিল গ্রামে। বিত্তার্জনের লক্ষ্যে নয়, শিক্ষাবিস্তারের লক্ষ্যেই তার এসব বিদ্যালয় স্থাপন। বালিকা বিদ্যালয়গুলাে সরকারি অনুমােদন থেকে বঞ্চিত হলে তিনি যেভাবে এগুলাে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন তা ইতিহাস হয়ে আছে। এজন্য কত টাকা যে তাকে খেসারত দিতে হয়েছিল তার ঠিক-ঠিকানা নেই। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আলাদা করে কোনাে চিন্তাভাবনা ইতালির মানবতাবাদীরা করেননি। গাঁটের পয়সা খরচ করে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনের তাে কথাই ওঠে না। জুন-জুলাই মাসের প্রখর রৌদ্রে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে সরকারি আশ্বাস ও স্থানীয় মানুষজনের উদ্যোগকে এক সূত্রে বেঁধে তিনি যেভাবে বিদ্যালয় স্থাপন করে বেড়িয়েছিলেন, ইতালির রেনেসাঁসম্যানরা বাস্তবে এ নিয়ে ভেবেছিলেন—তার প্রমাণ পাওয়া ভার। মিস মেরি কার্পেন্টারের সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের কাজে বেড়িয়ে ঘােড়ার গাড়ি উল্টে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর মারাত্মক জখম হওয়ার ঘটনা সকলেরই জানা। বুকের পাঁজর দিয়ে দেশের মানুষের জন্য শিক্ষা বিস্তারের এই সংগ্রামের কাহিনি ইতালিতে নেই।
(২)
পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টিও উত্থাপিত হতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নীতিগত দিক থেকে বাঞ্ছনীয় মনে করলেও তার জন্যে তার বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছিল না। তাহলে তিনি সরকার কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে জমিদারদের ওপর রেট ধার্যের প্রস্তাব অন্তত সমর্থন করতে পারতেন। তাতে সমগ্র জনগণের শিক্ষা হলেও জনগণের নিম্নশ্রেণিভুক্ত একটা অংশের শিক্ষা নিশ্চয়ই কিছু অংশে সম্প্রসারিত হতাে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূল্যায়নে তার এই ধরণের মতামত ও কার্যকলাপকে উপেক্ষা করা চলে না। এসব বিষয়ে তাঁর সুনির্দিষ্ট কতকগুলি মতামতের সঙ্গে তাঁর কতকগুলি ব্যক্তিগত কার্যকলাপকে জড়িয়ে ফেলে অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন।
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বভাবত অত্যন্ত উদারচেতা ও হৃদয়বান মানুষ ছিলেন। এরকম অনেক উদাহরণ হয়তাে পাওয়া যাবে যেখানে তিনি কোনাে নিম্নশ্রেণিভুক্ত ছাত্রের বা বিশেষ কোনাে এক এলাকার কিছু সংখ্যক দরিদ্র মানুষের শিক্ষার জন্যে ব্যক্তিগতভাবে অকাতরে অর্থ ব্যয় করেছেন। কিন্তু সেই ধরণের ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং অর্থব্যয়ের দ্বারা কেউ যদি মনে করেন যে, বিদ্যাসাগর জনশিক্ষা অথবা দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণির জনগণের শিক্ষাবিকাশের ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে উদ্যোগী ছিলেন, তাহলে ভুল হবে। সে উদ্যোগ তাঁর ছিল না। কেন ছিল না সে সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন এবং যেভাবে বলেছেন তার মধ্যেই তার শ্রেণি-আনুগত্যের এবং শ্রেণি-চেতনার যে সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় তাঁকে অস্বীকার করতে চেষ্টা করা তাত্ত্বিক বিড়ম্বনার নামান্তর মাত্র।
এ প্রসঙ্গে মুসলমান সমাজের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিলে বিদ্যাসাগরের প্রগতিশীল ভূমিকা স্পষ্টতর হবে এবং তাঁর শিক্ষানীতির মৌলিক প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহের যথার্থতাও প্রমাণিত হবে। হাজী মহম্মদ মহসীন (১৭১০-১৮১২) ১৮০৬ সালে তাঁর বিখ্যাত উইলে নিজের যথাসর্বস্ব মুসলমান সম্প্রদায়ের উপকার এবং সাধারণভাবে জনশিক্ষার জন্য আল্লাহর নামে উৎসর্গ করেন। এই উইলটিতে মহম্মদ মহসীন যে উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেন সেটা উনিশ শতকের হিন্দু-মুসলমান উচ্চ ও মধ্যশ্রেণির কারও মধ্যে দেখা যায়নি। কারণ জনশিক্ষা বলতে এই উইলে তিনি বিশেষভাবে মুসলিম শিক্ষা অর্থাৎ নিজের সম্প্রদায়ের শিক্ষা বােঝাননি। এ ব্যাপারে তাঁর উইলে হিন্দু-মুসলিম ইত্যাদি কোনও সম্প্রদায়ের উল্লেখই ছিল না।৫

সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ব্যাপার হলেও তার ভিত্তিভূমি প্রথমার্ধেই রচিত হয়েছিল এবং সেই পরিবেশেও হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত উচ্চশ্রেণির সমাজনেতারা কেবলমাত্র নিজ নিজ সম্প্রদায়ের শিক্ষা-দীক্ষা এবং উন্নতির চিন্তাই করতেন। অন্য সম্প্রদায়ের কথা তাদের মাথায় ছিল না। এ জন্যে ইংরেজি বাংলাচর্চার ক্ষেত্রে, পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে, হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত নেতারা যে উদ্যোগ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির মাধ্যমে নিয়েছিলেন সেগুলি বিশেষভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রদের শিক্ষার জন্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে মুসলমানদের কোনও প্রবেশাধিকারের কথা কেউ চিন্তা করেননি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও এদিক দিয়ে কোনও ব্যতিক্রম ছিলেন না। হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সকল বর্ণের ছাত্রদের সংস্কৃত কলেজে ভর্তির প্রশ্ন যখন ওঠে তখন রক্ষণশীলরা ভয়ানকভাবে সেই প্রস্তাবের বিরােধিতা করে। এই বিরােধিতা এতাে প্রবল ছিল যে, ইচ্ছে সত্ত্বেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত করার প্রস্তাব কর্তৃপক্ষের কাছে দিতে পারেননি। যে প্রস্তাব তিনি দিয়েছিলেন তাতে কায়স্থ পর্যন্ত ভর্তির কথা ছিল, নিম্নশ্রেণির হিন্দু বা মুসলমানদের ভর্তির কথা তাে দূর অস্ত! শিক্ষা-সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর নিজের চিন্তা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। সে দিক দিয়ে বিচার করলে, শ্রেণি-ধর্ম নির্বিশেষে সাধারণভাবে জনশিক্ষার জন্য হাজী মহম্মদ মহসীনের বিরাট দান (যার বাৎসরিক আয় ১৮৩০ এর পর দাঁড়ায় ৫১,০০০ টাকায়) একটা উল্লেখযােগ্য ব্যাপার।
বাঙালির রেনেসাঁস ছিল মুখ্যত ‘হিন্দু রেনেসাঁস’। মুসলমান স্বেচ্ছাচারের ধারণা তার সঙ্গে যেন ওতপ্রােতভাবে জড়িয়ে আছে। কেননা সেই স্বেচ্ছাচারের কথা তুলে ব্রিটিশ শাসনকে সমর্থন করা সহজ হল—‘মুসলমানরূপ পিশাচেরা এই ভাগ্যহীন ভারতবর্ষকে ৯১৯ শকে আক্রমণ করিয়া বিবিধ অত্যাচার দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড এবং মুমূর্ষ করিল, তার ফলে দেশে বিদ্যা ও ধর্ম ধ্বংস হল। এই তথ্য পরিবেশনের পর এল সেই অমােঘ সিদ্ধান্ত : ইংল্যান্ডের প্রার্দুভাবে এদেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, প্রায় ৮০০ বছর পর্যন্ত যে দুঃখ এদেশে সঞ্চিত হইয়াছে তাহা ক্রমে দূরীকৃত হইতেছে। পরবর্তীকালে, পরাধীনতার যন্ত্রণা যাঁকে অতিষ্ঠ করেছে সেই বঙ্কিমচন্দ্রও বলেছেন; যাহারা সাত শত বৎসর পরের জুতা মাথায় বহিতেছে, তাহারা আবার পুরুষ! বলিতে লজ্জা করে না’?৬
(৩)
মুসলমানদের সম্পর্কে কোনাে বিজাতীয় ভাবনা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর ছিল না। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অকুণ্ঠিতভাবে তিনি দাঁড়িয়েছেন তাদের দুঃখ-যন্ত্রণার লাঘব ঘটাতে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের আর্তসেবায় জাত বা সম্প্রদায়গত বিবেচনার কোনাে চিহ্ন ছিল না। তবু পুনরুক্তি হলেও বলি যে, এই মানুষটিও নিজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমানদের প্রবেশাধিকার দেননি। বিদ্যাসাগরের একান্ত গুণগ্রাহী হয়েও অন্নদাশঙ্কর রায় দুঃখের সঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন: “সিউড়িতে আগে কলেজ ছিল না। যুদ্ধকালে বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপকরা কলকাতা থেকে এসে শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। একদিন আমার আদালতের একজন মুসলমান কর্মচারী আমাকে বলেন যে তার ছেলেকে কলেজে পড়াতে চান, কিন্তু মুসলমান বলেই ওকে ভর্তি করা হচ্ছে না। সে কী কথা। আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পাই যে কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজেও মুসলমান ছাত্রদের ভর্তি করা হয় না! সেই বিদ্যাসাগর কলেজেও মুসলমান ছাত্রদের ভর্তি করা হয় না। সেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আমল থেকেই কলেজের নিয়মাবলীতে ধর্ম নিয়ে বাছবিচার আছে। হিন্দু কলেজেও ছাত্রদের বেলায় বাছবিচার করা হতাে। সেই কারণেই প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয় ও তাতে খ্রীষ্টান মুসলমান অ্যাংলাে-ইণ্ডিয়ানদেরও ভর্তি হতে দেওয়া হয়। মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার সুযােগ থাকলে তারা হিন্দুদের চেয়ে পেছিয়ে থাকতাে না। পেছিয়ে না থাকলে বিশেষ সুবিধা দাবি করতাে না। এতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমদর্শিতার অভাব সূচিত হয়।”৭
মুসলমানদের সম্পর্কে হিন্দু উচ্চবর্ণের এলার্জি ছিল। ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর তা ছিল না। কিন্তু উচ্চবর্ণের মানসিকতার ওপর সামাজিক কর্মকাণ্ডের জগতে আঘাতের মাত্রা তিনি উচ্চগ্রামে তােলেননি। সমাজ বিচ্ছিন্ন ডিরােজিয়ানদের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি হয়তাে শিক্ষা নিয়েছিলেন। সমাজ সংস্কারক হিসেবে তাকে বুঝতে হয়েছে সমাজের অবস্থাটা, সমাজের প্রভাবশালী অংশের কথা মনে রাখতে হয়েছে। শুধু বাস্তববাদী নন, তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল। গােপাল হালদারের এই মন্তব্যে৮ সায় না দিয়ে উপায় নেই। বাংলার মানুষ বলতে উনিশ শতকের মনীষীরা বুঝতেন মুখ্যত ও মুলত হিন্দু বাঙালিকে, বা আরও ঠিকমতাে বললে বর্ণহিন্দুকে। সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রও ছিল সেইটুকুই।”৯ বিদ্যাসাগরও এই সীমান্ত লংঘন করতে পারেননি।
তবে এটাও বাস্তব যে, ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যেমন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি পাশ্চাত্য আদর্শ ও আধুনিকতার গুরুত্ব সম্পর্কে একইভাবে সচেতন ছিলেন। বিদ্যাসাগরের মধ্যে এই অতীত ঐতিহ্য ও আধুনিকতার অপূর্ব সংমিশ্রণ হয়েছে বলেই অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁকে ‘Traditional moderniser’ আখ্যা দিয়েছেন। রামমােহনের মত তিনিও রক্ষণশীল হিন্দুদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন এবং বিধবা বিবাহ আন্দোলনের জন্য তাঁর জীবন সংশয় হয়েছিল। উগ্র পাশ্চাত্যপন্থী ইয়ং বেঙ্গলের সঙ্গেও তাঁর মতের অমিল ছিল। কিন্তু রামমােহনের মত তিনি বিতর্কিত ও পুরােপুরি মিত্রহীন হয়ে পড়েননি। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল। তিনি দেবেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববােধিনী সভার সদস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন। অন্যদিকে ডিরােজিওপন্থী ইয়ং বেঙ্গলের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ভাল ছিল। শিক্ষা বিস্তারের কাজে ও বিধবা বিবাহ আন্দোলনে তিনি তাদের সক্রিয় সাহায্য ও সহযােগিতা পেয়েছিলেন। কিন্তু সমাজ সংস্কার করতে গিয়ে তিনি নিজে ব্রাহ্ম সমাজ বা ডিরােজিও গােষ্ঠী কোনাে দিকে ঝুঁকে পড়েননি। নিজের লক্ষ্য ও পথ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবিচল ছিলেন। তাঁর চরিত্র, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, সংগ্রামী মনােভাব ও তেজস্বিতা যেমন আমাদের মুগ্ধ করে, তেমনি তার মানবতাবােধ, পতিতের প্রতি করুণা ও দয়া এবং মানবজীবনের মহত্ত্বজ্ঞান’ আমাদের প্রশংসা কেড়ে নেয়। বাঙালি মায়ের মমত্ববােধ ছিল বলেই বিধবাদের দুঃখে তার চোখে জল এসে যেত। সমস্ত সামাজিক কুপ্রথাকে তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সমাজের সত্যটুকু লক্ষ্য করেছিলেন। বিনয় ঘােষের ভাষায়: “রামমােহনের মতাে প্রধানত আইডিয়ালিস্ট বা কৃষ্ণমােহনের মত এক্সট্রিমিস্ট কোনটাই তিনি (বিদ্যাসাগর) হতে পারেননি। তাঁর সমকালীন সমাজ কর্মীদের মধ্যে তিনি ছিলেন আদর্শবাদের সঙ্গে বাস্তববাদের সমন্বয় তার চরিত্রে যেমন ঘটেছিল, এমন আর কারাে চরিত্রে বােধ হয় ঘটেনি। এই সমন্বয়ই বিদ্যাসাগর চরিত্রের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য।”১০
রামমােহনকে কেন্দ্র করে যত তর্ক-বিতর্ক ও উত্তপ্ত আলােচনা হয়েছে, বিদ্যাসাগরকে নিয়ে তা হয়নি। সমকালীন যুগে রামমােহনকে গোঁড়া হিন্দু, অত্যুৎসাহী খৃষ্টান মিশনারী ও হিন্দুধর্মের কঠোর সমালােচক চরম আদর্শে বিশ্বাসী ইয়ংবেঙ্গল কেউই নিজের লােক বলে মনে করেনি। তাঁর ধর্ম চিন্তা ও সমাজ সংস্কারের পরিকল্পনা অনেকেরই মনঃপুত হয়নি। এটা ঠিক যে, বিধবা বিবাহের ব্যাপারে বিদ্যাসাগরকেও প্রচন্ড বিরােধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তার জীবন বিনাশের আশঙ্কাও ছিল। কিন্তু যেহেতু তার ধর্ম ও ঈশ্বর চেতনা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল, যেহেতু তিনি ধর্মসংস্কারের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেননি, সেহেতু তিনি ধর্ম সংক্রান্ত কোন বিতর্কে জড়িয়ে পড়েননি। ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে তাঁর ভাল সম্পর্ক ছিল। ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ ও কর্মসূচীও তাঁর অপছন্দ হয়নি; কিন্তু তিনি ব্রাহ্ম সমাজে যােগদান করেননি। এক অর্থে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সারা জীবন নিঃসঙ্গ ছিলেন। কোন দল বা গােষ্ঠীর মধ্যে থাকা তার ধাতে পােষাত না। তার কারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব ও ন্যায়নীতিপরায়ণতা। বিদ্যাসাগর চরিত্রের এই দিকটি উল্লেখ করে একদা শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছিলেন: “বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃতি তাে জানাই আছে, তাঁহার কাছে স্বর্গ ও নরক ভিন্ন মাঝামাঝি একটা স্থান নাই।” রবীন্দ্রনাথও প্রায় একই কথা বলেছেন: “বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁহার স্বজাতি সােদর কেহ ছিল না। এদেশে তিনি তাহার সমযােগ্য সহযােগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নিবার্সন ভােগ করিয়াছেন।” ভদ্ৰশ্রেণির মানুষের আচরণে তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন এবং তাদের প্রতি তাঁর আস্থা চলে গিয়েছিল। শেষজীবনে কার্মাটারে সহজ সরল সাঁওতালদের সাহচর্য তাঁকে আনন্দ দিয়েছিল।
(৪)
সমকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খুব একটা বিতর্কিত পুরুষ না হলেও ঊনবিংশ শতকের সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তাঁর অবদান সম্পর্কে পন্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মত বৈষম্য আছে। অনেকে যাঁরা তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্ত, তাঁর প্রশংসায় এতই পঞ্চমুখ যে, তার দোষ, ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে কোন ভাবনা চিন্তা করেননি। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, বিদ্যাসাগর বাঙালি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিভূ এবং ঔপনিবেশিক যুগের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পারেন নি। রামমােহনের মত তিনিও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ঈশ্বরপ্রেরিত বিধান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ইংরেজদের বিচারবােধ ও উদারনীতির উপর তার অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস ছিল। তিনি পুরােপুরিভাবে রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন বলে ইংরেজ সরকার তাঁর উপর কোন কুধারণা রাখতেন না। একবার ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি স্যার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে কংগ্রেসে যােগদান করার জন্য স্বয়ং আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তিনি উত্তরে বলেছিলেন: “আমাকে বাদ দিয়েই তােমরা কাজে এগােও।১১
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সরকারি চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করার পর শাসক ইংরেজের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ কেমন ছিল সে সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: “বিদ্যাসাগর এখন আর সরকারী বেতনভােগী কর্মচারী নন। না হইলেও বে-সরকারী পরামর্শদাতা হিসাবে তিনি সরকারের উপকার সাধন করিতে লাগিলেন। পরপর বহু ছােটলাটই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। …অবসর গ্রহণের বিশ বৎসর পরে ১৮৯০ সালে নববর্ষের প্রথম দিনে ভারত গভর্ণমেন্ট তাঁহাকে সি আই ই উপাধিতে ভূষিত করেন।” এই সি আই ই বলতে বােঝায় ‘কম্পেনিয়ন অফ দ্য ইন্ডিয়ান এম্পায়ার’ যার বাংলা অর্থ—‘ভারত সাম্রাজ্যের সহযােগী’।
‘বাঙ্গালার ইতিহাস’-এর দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে বাক্য রচনা করেছেন তার প্রতি চোখ বুলালে ইংরেজদের প্রতি তাঁর ভক্তি ও আনুগত্যের পরিচয়ই পাওয়া যায়: “বাঙ্গালার ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ, শ্ৰীযুক্ত মার্শম্যান সাহেবের রচিত ঈঙ্গরেজী গ্রন্থের শেষ নয় অধ্যায় অবলম্বন পূর্বক সংকলিত…এই পুস্তকে অতি দুরাচার নবাব সিরাজউদৌলার সিংহাসনারােহণ অবধি, চিরস্মরণীয় লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক মহােদয়ের অধিকার সমাপ্তি পর্যন্ত বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।”১২

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর ‘বাঙ্গালার ইতিহাস প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন: “বিদ্যাসাগর প্রায় মার্শম্যানের অবিকল অনুবাদ করিয়াছেন। মার্শম্যানের সাম্রাজ্যবাদী ও ইসলামবিদ্বেষী দৃষ্টিভঙ্গিমাও তিনি হুবহু স্বীকার করিয়া লইয়া অনুবাদ করিয়াছেন।১৩ এ প্রসঙ্গে আর একটি মূল্যবান উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি: “বলা বাহুল্য, মার্শম্যানের নকলে লেখা ইতিহাসের মাধ্যমে সুকুমার-মতি বালক-বালিকাদের জন্য বিদ্যাসাগর ইংরাজ সরকারের যে ভাবমূর্তি উপস্থিত করেছেন তা না করলেই ভাল হত।”১৪
১৮৫৭-র বিপ্লবের মুহূর্তে তার প্রধান কাজ ছিল বহু বিবাহ বন্ধের ব্যবস্থা করা। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর ভাষাতেই লিখেছেন, “কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময় রাজ বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। রাজপুরুষেরা বিদ্রোহের নিবারণ বিষয়ে সম্পূর্ণ ব্যাপৃত হইলেন; বহু বিবাহের নিবারণ বিষয়ে আর তাহাদের মনােযােগ দিবার অবকাশ রহিল না।”১৫
উল্লেখ্য ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ এবং ১৮৫৯-৬১ সালে বাংলায় নীলবিদ্রোহ এবং অন্যান্য কৃষক বিদ্রোহ ঔপনিবেশিক শাসনকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। ১৭৯৩ সালে কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভারতের ভূমি ব্যবস্থায় সামন্তবাদী শােষণকে পাকাপােক্ত করে দেয়। এই ক্ষেত্রে যেমন রামমােহন, তেমনি বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। দীনবন্ধু মিত্র এবং ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’-এর সম্পাদক হরিশচন্দ্র যেভাবে নির্যাতিত কৃষকদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র তা কোনােদিন চিন্তাও করেননি। হিন্দু বিধবাদের দুরবস্থার কথা চিন্তা করে তাঁর হৃদয় বিচলিত হলেও দরিদ্র কৃষকদের ওপর নীলকরদের নির্যাতন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের হাজারাে অত্যাচার তাঁর মনকে বিন্দুমাত্র আলােড়িত করেনি। তাই বিধবা বিবাহের সংস্কার আন্দোলনে তিনি প্রচুর অর্থ ও শক্তি ব্যয় করলেও নিজের কথা, লেখা ও কর্মের মাধ্যমে বৃহত্তর কৃষকসমাজের সুখ-দুঃখের প্রতি তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন।
রামমােহন অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলাের অভিযানে বৃটিশ শাসনকে আশীর্বাদ স্বরূপ দেখেছিলেন। বৃটিশ শাসন সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর অনুরূপ কোন মনােভাব প্রকাশ পায়নি। কিন্তু তিনি শিক্ষাবিস্তার ইত্যাদি প্রশ্নে শাসকদের সঙ্গে প্রকাশ্য বিবাদে লিপ্ত হলেও এবং তাদের নিকট সর্বদা মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেও এবং আত্মমর্যাদা ও ভারতীয়দের প্রগতি তার ধ্যান-জ্ঞান হলেও, প্রকাশ্যে বৃটিশ শাসন-বিরােধী কোন মতামতও তিনি ব্যক্ত করেননি। এমনকি তার জীবদ্দশায় ‘মহাবিদ্রোহ’ ‘নীল বিদ্রোহ’ ইত্যাদি সংঘটিত হলেও, হরিশচন্দ্র মুখােপাধ্যায় প্রমুখরা নীল বিদ্রোহের সরাসরি এবং প্রকাশ্য সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও এইসব বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মৌনীভাব বিস্ময়ের উদ্রেক করে। অর্থাৎ ভারতীয় সমাজকে সেই সময় যে জরুরী সমস্যাগুলি আলােড়িত করছিল এবং সমাধানের দাবি করছিল—ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি এবং সামন্তবাদী শােষণের অবসান—সেই সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর কোন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়নি।
কুখ্যাত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলেছেন: “এই দশশালা বন্দোবস্ত ইহাই নিদ্ধারিত হইল, এ পর্যন্ত যে সকল জমিদার কেবল রাজস্ব সংগ্রহ করিতেছেন; অতঃপর তাঁহারাই ভূমির স্বামী হইবেন; প্রজারা তাঁহাদের সহিত রাজস্বের বন্দোবস্ত করিবেক।…চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়াতে বাঙ্গলাদেশের যে সবিশেষ উপকার দর্শিয়াছে ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।”
বিপ্লবী ও বিরােধীদের ইংরেজ-বিরুদ্ধ গতি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি বলেছেন, “বাবুরা কংগ্রেস করিতেছেন, আন্দোলন করিতেছেন, আস্ফালন করিতেছেন, বক্তৃতা করিতেছেন, ভারত উদ্ধার করিতেছেন। দেশের সহস্র সহস্র লােক অনাহারে প্রতিদিন মরিতেছেন তাহার দিকে কেহই দেখিতেছেন না। রাজনীতি লইয়া কি হইবে?”১৬ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ১৮৫৭-র সিপাহি বিদ্রোহ তথা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামকেও তিনি সমর্থন করেননি। তাছাড়া বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজে সিপাহী বিদ্রোহ দমনকারী ব্রিটিশ সেনাবাহিনীদের থাকতে দেওয়া হয়েছিল। এদিক থেকে দেখলে বিদ্যাসাগরের পক্ষে জাতীয়তাবাদী হওয়া কঠিন।১৭ যদিও ব্যক্তি ইংরেজের ঔদ্ধত্যের সমুচিত জবাব দিতে তিনি কোনাে কৃপণতা করেননি। কিন্তু ইংরেজদের সমষ্টিগত শাসনের প্রতি তার কোনাে বিরাগ ছিল না। বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর ‘বাঙ্গালার ইতিহাস’ (২য় ভাগ) বইটিতে ইংরেজ শাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রকাশ রয়েছে, সেখানে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে তিনি বড় মাপের দুবৃত্ত বলেই উল্লেখ করেছেন, যেন নৈতিক অপরাধের জন্যই তার পতন ঘটেছে, চক্রান্তের কারণে নয়। ব্যক্তি চরিত্র দিয়ে রাজনৈতিক ঘটনার ব্যাখ্যা করার এই প্রবণতা ধার্মি কদের পক্ষেই শােভনীয় হতে পারে, ধর্মনিরপেক্ষদের নয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর ভাষ্য অনুসরণ করলে বলা যায়, চক্রান্তের শিকার যিনি তিনিই পরিণত হন দুবৃত্তে। অশােক সেন মনে করেন ঔপনিবেশিক শাসনের আওতায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর সমস্ত প্রগতিশীল ও আধুনিক সংস্কারের প্রচেষ্টা মায়া মরীচিকার মত মিলিয়ে যেতে বাধ্য ছিল। তিনি লিখছেন: ‘Vidyasagar had no sufficient means to link up tradition an modernity in any meaningful sense of that convergence… Vidyasagar was a victim of the illusions which he shared with his stage of history, about the prospects of modernization under colonial rule.’১৮
এই সব পরস্পর বিরােধী মতামত সত্বেও কিন্তু কেউ ঊনবিংশ শতকে বাংলার ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর অসাধারণ ভূমিকা ও গুরুত্ব অস্বীকার করেননি। শিক্ষাবিস্তারে তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা বিশেষত স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে তার আগ্রহ, বাংলা গদ্যের জনক হিসাবে তাঁর অবদান, সামাজিক সংস্কারে তার অসাধারণ নিষ্ঠা ও সর্বোপরি মানুষের প্রতি অকৃত্রিম মমত্ববােধ নিয়ে কোন বিতর্ক থাকতে পারে না। সবচেয়ে বড় কথা তিনি তার সমস্ত আন্দোলনে সাধারণ মানুষকে সামিল করতে চেয়েছিলেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের উপর গুরুত্ব আরােপ করে তিনি অপামর জনগণের মধ্যে শিক্ষার আলাে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার এই আন্তরিক সংযােগই তাকে রামমােহনের থেকে কিছুটা পৃথক করে রেখেছে। সাধারণ মানুষের কাছে রামমােহন ছিলেন দূরের মানুষ, ধরাছোঁয়ার অনেক বাইরে; কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন তাঁদের ঘরের মানুষ, যেন একান্ত আপনজন। তাছাড়া বিদ্যাসাগরের শিক্ষা সংস্কারের একটি প্রধান দিক বাংলা ভাষায় আধুনিক স্কুলপাঠ্য বই লেখা ও প্রকাশ। এইসব বইয়ের মতাদর্শগত তাৎপর্য ও প্রভাব নিয়ে কোন মৌলিক আলােচনা কিন্তু চোখে পড়ে না। এমনকি বাংলা ভাষার ‘প্রথম যথার্থ শিল্পী’ হিসাবে তিনি বাংলা গদ্যকে যে পথে পরিচালিত করেছিলেন। তাঁর শ্রেণি তাৎপর্য নিয়েও তেমন আলােচনা হয়নি। অথচ বিষয়গুলির সামাজিক তাৎপর্য যে যথেষ্ট সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। চেম্বার্স বায়ােগ্রাফীর’অনুসরণে লেখা ‘জীবন চরিত’, মার্শম্যানের বইয়ের ভাবানুবাদ ‘বাঙ্গলার ইতিহাস’, ‘বােধােদয়’ ও ‘বর্ণপরিচয়’ (আজও বাংলা ভাষায় হাতেখড়ি হয় এই ‘বপরিচয় দিয়েই) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর কয়েকটি প্রধান শিশুপাঠ্য বই। এই বইগুলির অন্তর্নিহিত বার্তা নিঃসন্দেহে স্থিতাবস্থার সহায়ক।১৯ বাঙালি ভদ্রলােকের মূল্যবােধ গড়ে উঠেছিল এইসব বইয়ের প্রভাবে। তার লিখিত ‘উপক্রমণিকা’ ও ‘ব্যাকরণ কৌমুদী’ আজও সংস্কৃত শিক্ষানবিশদের কাছে অবশ্য পাঠ্য। তাছাড়া তার বেতাল পঞ্চবিংশতি’, ‘সীতার বনবাস’, ‘কথামালা’ প্রভৃতি গদ্য রচনার মাধ্যমে বাংলা ভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যাসাগরের হাতেই বাংলা ভাষা সহজ ও প্রাঞ্জল হল। কমা সেমিকোলন ইত্যাদি যতি চিহ্নের বহুল ব্যবহার প্রচলন করে তিনি বাংলা ভাষায় যে গতিশীলতা সৃষ্টি করেন তার ফলেই ভাষা হিসেবে বাংলা সমস্ত রচনার উপযােগী হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগরের ভাষা সংস্কৃত-প্রভাবিত হলেও গদ্যের ছেদ চিহ্নের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের মধ্যে বৈচিত্র্য তৈরী করে ভাষার রূপ এভাবে তিনিই এনে দিয়েছিলেন। আসলে সংস্কৃত ভাষায় মহাপণ্ডিত হলেও তিনি ছাত্র ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য যা কিছু লিখেছেন সবই মাতৃভাষায়। সংস্কৃত শিক্ষার ওপর তিনি যতটুকু গুরুত্ব দিয়েছিলেন সবই মাতৃভাষায় শিক্ষার পথকে সুদৃঢ় ও সমৃদ্ধ করার জন্য। মাতৃভাষায় সংস্কৃত-ব্যাকরণ লিখে তিনি একটা বৈপ্লবিক কাণ্ড করেন। হাজার হাজার বছরের সংস্কৃত-শিক্ষার ইতিহাসে ঐ জিনিস প্রথম ঘটল।
রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: “বাংলা ভাষাকে পূর্ব প্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বরভার হইতে মুক্ত করিয়া তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযােজনার সুনিময় স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাঙলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহারযােগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে; তিনি তাহাকে শােভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে ধ্বনি সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাঙলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযােগী আর্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্বে বাঙলা গদ্যের যে অবস্থা ছিল, তাহা আলােচনা করিয়া দেখিলে এই ভাষাগঠনে বিদ্যাসাগরের শিল্প প্রতিভা ও সৃষ্টিক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।”২০ বাংলা ভাষাকে আধুনিক রূপদানের ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদানকে উপরােল্লিখিত ভাষায় বর্ণনা করে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগরকে আধুনিক বাংলা গদ্যের জনক রূপেই অভিহিত করেছেন। বিদ্যাসাগরের ভাষা-বিষয়ক কীর্তি সম্পর্কে এই মূল্যায়ন খুবই যথার্থ।
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর লেখায় কত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করতেন, সেটা বড় কথা নয়। আসল কথা হল, তিনি সংস্কৃত রচনা পদ্ধতিকে পরিবর্তন করে বাংলা ভাষায় এক নতুন শব্দ-বিন্যাস রীতি প্রচলন করেছিলেন। এই রীতির ওপর ভিত্তি করেই মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, কেশবচন্দ্র সেন, মশাররফ হােসেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখেরা বিভিন্ন ধরণের রচনা উনিশ শতকে প্রকাশ করেছিলেন, শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞানের ভাষারূপে বাংলা ভাষার অনেকখানি উৎকর্ষ সাধন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এর ফলে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার বাংলা ভাষায় ঐতিহাসিক নিয়মে এবং স্বাভাবিকভাবেই কমে এসেছিল, ইউরােপে যেমন কমে এসেছিল জাতীয় ভাষাগুলির মধ্যে লাতিন শব্দের ব্যবহার।
শিক্ষার ক্ষেত্রে সেকুলারিজম, মনে হয়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর একটি বড় কৃতিত্ব। শুধু বাংলা শিশুপাঠ্য বই-এ নয়, সংস্কৃত শেখার প্রাথমিক বই, ঋজুপাঠ-এও কোনাে ধর্মগ্রন্থ থেকে কোনাে বাণী বা শ্লোক নেওয়া হয়নি। গীতা-র মতাে ধর্মগ্রন্থ থেকেও কোনাে উক্তি সেখানে উদ্ধৃত হয়নি। মৃত্যুর আগে তিনি একটি উদ্ভট শ্লোকমালা সঙ্কলন করেন। তার সমালােচনা প্রসঙ্গে ‘এডুকেশন গেজেট’ পত্রিকায় তির্যক ভঙ্গিতে লেখা হয়েছিল: “বিদ্যাসাগর মহাশয় বাল্যকালে পূজ্যপাদ গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ভট্টাচাৰ্য মহাশয়ের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তদীয় কণ্ঠবিনির্গত সরস কবিতাবলী এই প্রাচীন বয়স পর্যন্ত স্মৃতিপথে রাখিয়া প্রকাশ করিলেন।…বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই সংগ্রহের মধ্যে দেববিষয়ক বা পরমার্থ বিষয়ক কবিতা নাই বলিলেই হয়। হয় তাহার গুরুদেব সে সকল শিষ্যকে বলেন নাই, অথবা শিষ্যের স্মরণ নাই।”২১
এখানেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর সঙ্গে বিবেকানন্দ-র তফাত। প্রিয়নাথ সিংহকে বিবেকানন্দ একবার বললেন, ‘দেশের মহা দুর্গতি হয়েছে, কিছু কর রে। ছােটছেলেদের পড়বার উপযুক্ত একখানাও কেতাব নেই।’ প্রিয়নাথ স্বভাবতই বললেন, ‘বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তাে অনেকগুলি বই আছে।’ অবজ্ঞাভরে চড়াগলায় হেসে বিবেকানন্দ বললেন, ‘ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ, গােপাল অতি সুবােধ বালক—ওতে কোনাে কাজ হবে না। ওতে বই ভালাে হবে না। রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ থেকে ছােট ছােট গল্প নিয়ে অতি সােজা ভাষায় কতকগুলি বাংলাতে কতকগুলি ইংরেজিতে কেতাব চাই। সেইগুলি ছােট ছেলেদের পড়াতে হবে।’২২

যদি পরধর্ম সহিষ্ণুতার কথা বলেন, তবে বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহে ইসলাম বা খ্রিস্টধর্মের বিরােধী ছিলেন না। কিন্তু সেকুলারও ছিলেন না। তাই শিক্ষার শুরুতেই তিনি হিন্দু ধর্মগ্রন্থের আশ্রয় নেওয়ার পক্ষপাতী। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমও আদতে ধর্মভিত্তিক। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের যুগেও কিন্তু ধর্ম ছাড়া নীতিশিক্ষার কথা ভাবা হয়নি।
এসবের অনেক আগেও ইয়ং বেঙ্গল-এর মুখপত্র, জ্ঞানান্বেষণ-এ ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছিল: হিন্দু কলেজে কেন ন্যাচারাল থিওলজি ও মর্যাল ফিলােসফি পড়ানাে হয় না!২৩ কেশবচন্দ্র সেনও চেয়েছিলেন, কোনাে সাম্প্রদায়িক ধর্ম না…শেখালেও, অসাম্প্রদায়িক ‘প্রাকৃতিক ধৰ্ম্ম বিজ্ঞান’ (অর্থাৎ ন্যাচারাল থিওলজি) শেখানাে হােক।২৪ পরবর্তীকালে ধর্মশিক্ষার দাবি ক্রমেই জোরদার হতে থাকে। বিরক্ত হয়ে প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখেছিলেন: “আমরা এখন ‘জাতীয় শিক্ষা চাই। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা কি? জাতীয় শিক্ষা অর্থে কি বটতলার বই পড়া? আৰ্য সমাজের লােকে জাতীয় শিক্ষার অর্থ করছেন বেদ পাঠ করা; কেন না তাদের মতে বেদ অভ্রান্ত। বিবেকানন্দের ভক্ত ববেন— বেদান্ত পাঠ কর—দ্বৈত, অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বিচার কর। আবার কেহ বা বলবেন— রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ পাঠ কর। কিন্তু হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি নানা ধর্মাবলম্বী ভারতবাসীগণ সকলে এই ব্যবস্থায় সমমত হবেন কি? মুসলমান ‘জাতীয়’ অর্থে বললেন—কোরান পড। খৃষ্টান বলবেন—বাইবেল পড। এত মতের অনৈক্য হলে আসল কাজে যে বাধা পড়বেই। পরম ধার্মিক হিন্দু রাজার রাজত্বকালে শূদ্র তপস্যা করছে বলে তার শিরচ্ছেদনের ব্যবস্থা হল; মনুমহাশয় ব্যবস্থা করেন যে শূদ্রের কর্ণে বেদোচ্চারণ শব্দ প্রবেশ করলে উত্তপ্ত সীসক সেই কর্ণে ঢেলে দিতে হয়। এই মনুস্মৃতি নিয়ে জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা হয় কি? বেদ, বেদান্ত পাঠ্য হলে বাংলার শতকরা ৫২ জন মুসলমান কি করবে? দয়ানন্দ বা বিবেকানন্দ—কোন্ পন্থী হলে মুসলমান ভ্রাতাদের টেনে নেওয়া যেতে পারে? আমরা হিন্দু মুসলমান এক বলে আহ্লাদে নৃত্য করছি, কিন্তু মুসলমান আমাদের জল ছুঁলেই সর্বনাশ।”২৫
আখ্যানমঞ্জরী, চরিতাবলী বা ওই জাতীয় শিশুশিক্ষার বইতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোনাে ধর্মনেতাকে ঠাই দেননি। ফলে বিহারীলাল সরকার তার মধ্যেও ‘কুশিক্ষার বীজ দেখতে পান।২৬ একজন হিন্দুও জীবনচরিত-এ আদর্শ চরিত্র হিসেবে আসেননি—এতে তার খুবই আপত্তি ছিল। কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের জীবনী পড়ে হিন্দু সন্তানের কোনাে উপকার হবে না—এই ছিল তার মত। বিহারীলাল লিখেছেন, “সংস্কৃত ভাষা-পারদর্শী ও বহুশাস্ত্রজ্ঞ বিদ্যাসাগর মহাশয় যে এইরূপ চরিত্র সংগ্রহে সমর্থ ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাহা হয় নাই; শুদ্ধ দেশের দুরদৃষ্ট দোষে। শিক্ষার স্রোত তখন বিপথে ধাবিত হইয়াছিল।”২৭
(৫)
শিক্ষাসংস্কারই হােক আর সমাজ সংস্কারই হােক, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সতর্কতার সঙ্গে পা ফেলেছেন। অথচ এই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ই শাস্ত্র ও বেদ-বেদান্ত সম্পর্কে দুঃসাহসিক মন্তব্য করছেন, সংস্কৃত কলেজের সিলেবাসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটানাের উদ্যোগ নিয়েছেন। বৈপ্লবিক, কেননা কনটেন্টের বিচারে সেই শিক্ষা সেকুলার। বাঙালি সমাজের মানসিক পশ্চাৎপদতা ও কুসংস্কার দূর করার জন্যে ইউরােপীয় ধর্মনিরপেক্ষ দর্শন-বিজ্ঞান তিনি পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। তিনি বুঝেছিলেন সমাজের জড়তার মূলে আছে মানুষের যুক্তিবাদ-বিমুখ প্রত্যয়। নির্বিচার বিশ্বাসের জগতে মনুষ্যত্ব প্রতিদিন লাঞ্ছিত হচ্ছে। বিদ্যাসাগর প্রতিকার চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—নতুন মানুষের চাষ করতে পারলে তবে এদেশের ভালাে হবে। সেই চাষের জায়গা হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন শিক্ষার ক্ষেত্রকে।
পুরনাে হিন্দু-দর্শনের তিনি ছিলেন কঠোর সমালােচক। শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক ডঃ মৌয়াটকে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা-সংস্কার সংক্রান্ত প্রস্তাব তিনি দিয়েছিলেন (১৬ ডিসেম্বর, ১৮৫০)। তাতে তিনি লেখেন, হিন্দু দর্শনের বেশিরভাগটাই আধুনিক ধ্যানধারণার সঙ্গে মেলে না। ওসব ছাত্ররা পড়ুক, পড়তে তাদের হবেও। কিন্তু সেই সঙ্গে পড়ুক ইউরােপের আধুনিক দর্শন। তখন আধুনিক জীবনবােধের আলােকে তারা বিচার করে নিতে পারবে আমাদের সনাতন শাস্ত্র সাহিত্যের নিরর্থকতা। পরস্পর-বিরােধী মতামতের সেই অনাধুনিক জঙ্গলে পাশ্চাত্য বা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান হবে তাদের পথপ্রদর্শক (His knowledge of European Philosophy shall be to him an invaluable guide to the understanding of the merits of the different systems.’)
যে-কোনও পাশ্চাত্য দর্শনের পঠন-পাঠন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর অভীষ্ট ছিল না। তাই ভালানটাইনের প্রস্তাবের বিপক্ষে তিনি গিয়েছিলেন। ভালানটাইন সুপারিশ করেছিলেন। কলকাতার সংস্কৃত কলেজে সাংখ্য-বেদান্তের সঙ্গে বিশপ বার্কলের দর্শন-গ্রন্থও পড়ানাে হােক। বিদ্যাসাগর বললেন, বার্কলের নয়, জন স্টুয়ার্ট মিলের বই অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত। সাংখ্য-বেদান্ত অবিসংবাদিতভাবেই ভ্রান্ত দর্শন। কিন্তু সংস্কৃত কলেজে তা পড়াতেই হচ্ছে। অতএব দরকার প্রতিষেধক পাশ্চাত্য দর্শন। বার্কলে সে প্রয়ােজন সিদ্ধ করবে। উল্টে সনাতন সংস্কারকেই বদ্ধমূল করবে। বিদ্যাসাগরের যুদ্ধ ঐ-সব সংস্কারের বিরুদ্ধেই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মনে করেন, হিন্দু-দর্শনের অনেকখানি অংশই অন্তঃসারশূন্য (…there are many passages in Hindu Philosophy which cannot be rendered into English with ease and sufficient intelligibility only because there is nothing substantial in them.) তাই ইউরােপীয় বিজ্ঞানচেতনার সঙ্গে প্রাচীন শাস্ত্রবােধের সমন্বয় ঘটানাে প্রায় অসম্ভব। আমাদের প্রাচীন ধারার পণ্ডিতমণ্ডলী দৃঢ়মূল সংস্কারে অটল। প্রসঙ্গত, ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের (রাঃ) উদাহরণ দিয়েছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত লাইব্রেরির গতি কী হবে?—এই প্রশ্নের উত্তরে খলিফা সেনাপতিকে বলে পাঠালেন, ‘ও-সব বইয়ের বিষয়বস্তুর সঙ্গে হয় কোরান-বিদ্যার মিল আছে, অথবা নেই। যদি মিল থাকে তাহলে বইগুলাের দরকার নেই, যদি মিল না থাকে তাহলে বইগুলাে সাংঘাতিক খারাপ’, সুতরাং লাইব্রেরি ধ্বংসে কালবিলম্ব কর্তব্য নয়। বিদ্যাসাগর বলতে চান, হিন্দু পণ্ডিত আর মুসলমান মৌলানা—গোঁড়ামিতে দু পক্ষই সমান।২৮ বিদ্যাসাগর তাই লিখেছেন, ‘যদি কেহ আমাকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভাবে, তাহাতে আমার যৎপরােনাস্তি অপমান বােধ হয়’।
এত করেও বিদ্যাসাগর অবশ্য সফল হননি। তিনি বেঁচে থাকতে প্রথমে নববিধান ব্রাহ্ম, তারপরে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ধর্ম নিয়েই আলােড়ন তুলল; ১৮৮০ সালের দশকে এল হিন্দু পুনরুজ্জীবনের পালা। ঈশ্বর সাকার না নিরাকার—এই নিয়ে তর্ক বাঁধল ছাত্র-যুবদের মধ্যে।২৯ ১৮৯০-এর দশক থেকে দেখা দিল এক পালাবদলের সূচনা, সমাজসংস্কারের জায়গা নিল রাজনীতি।৩০ সে রাজনীতি গােড়া থেকেই হিন্দুগামী। সমাজ সংস্কারের কর্মসূচী পরিত্যক্ত হল। আর সেই সঙ্গে পরিত্যক্ত হল বিদ্যাসাগরের সেকুলার শিক্ষাদর্শ।
কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর শিক্ষা সংস্কারে অনলস প্রচেষ্টার কথা স্বীকার করে নিয়েও বলতে হয় অনেক সময় তার কাজে ও কথায় সংগতি ছিল না। তার মধ্যে এক ধরণের অন্তর্বিরােধ বা স্ববিরােধ ছিল। পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল বিরল দৃষ্টান্ত। পিতা ঠাকুরদাসের সম্মতি না পেলে তিনি বিধবা বিবাহে আগ্রহী হতেন কিনা সন্দেহ আছে। অর্থাৎ পিতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার জন্য তিনি তাঁর আদর্শ ও লক্ষ্য বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু মাতৃভক্তির কথা বলতে যে দামােদর নদী সারানাের প্রসঙ্গ তােলা হয় তা সত্য নয়। মজার কথা, যে বিদ্যাসাগর স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য জীবন পণ করেছিলেন, তিনি কিন্তু তার নিজের মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে কোন আগ্রহ প্রকাশ করেননি। এমনকি তার স্ত্রীও নিরক্ষর ছিলেন। এর সম্ভাব্য কারণ স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারে ঠাকুরদাসের বিরােধিতা। বিধবা বিবাহের প্রশ্নেও তার ভাবনাচিন্তার মধ্যে অসংগতি ছিল। বিধবা বিবাহকে আইনসঙ্গত রূপ দেবার জন্য তিনি যতটা উদ্যম ও আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, হিন্দু বিবাহের গলদগুলি দূর করার বা সংশােধন করার ব্যাপারে তা দেখাননি। হিন্দু বিবাহের অনুষ্ঠানের মধ্যে তিনি আমূল পরিবর্তন আনার কোন চেষ্টা করেননি। অথচ তা না করলে যে বিধবা বিবাহ আন্দোলনই অনেকটা অর্থহীন হয়ে পড়ে, তা নিয়ে তিনি কোন ভাবনা চিন্তা করেননি। এ বিষয়ে তার সঙ্গে ডিরােজিও শিষ্যদের গুরুতর মত পার্থক্য ছিল। ফলে বিধবা বিবাহ আইন সিদ্ধ হবার পরও তাকে অনেক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আসলে প্রচলিত লােকাচারের বিরুদ্ধে কোন কিছু করার ইচ্ছা তার ছিল, বা দেশাচারকে পুরােপুরি অস্বীকার করার সাধ্য তার ছিল না। বিদ্যাসাগরের আর একটি সীমাবদ্ধতা হল তিনি অনেক প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা করলেও ধৈর্য ধরে তার পূণাঙ্গ রূপ দিতে পারেননি। বিদ্যাসাগরের অধিকাংশই প্রচেষ্টাই তাই সফল হয়নি।
(৬)
যে যুগে ও পরিবেশের মধ্যে থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর সংস্কার কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন, তাতে তার ব্যর্থতা হয়তাে পুরােপুরি অস্বাভাবিক নয়। বরং এই সীমিত সুযােগের মধ্যে তিনি যতটুকু করতে পেরেছেন, তাই যথেষ্ট প্রশংসা দাবী করে। উল্লেখ, উনিশ শতকের চতুর্থ দশক থেকেই বিধবা বিবাহের প্রশ্নটি বাঙালি হিন্দু সমাজে রীতিমতাে আলােচনার বিষয়বস্তু। শিক্ষিত বাঙালি সমাজ ইতিমধ্যে সতী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মূলত ধর্মীয় কারণে ত্রিধা-বিভক্ত। সতীপ্রথাকেন্দ্রিক বাদানুবাদ সীমাবদ্ধ ছিল মুখ্যত মধ্যপন্থী ও রক্ষণশীলদের মধ্যে। বিধবাবিবাহের ব্যাপারে এই বাদানুবাদ চরমপন্থী ইয়ংবেঙ্গল (অবশ্য উনিশ শতকের চতুর্থ দশক থেকে ইয়ংবেঙ্গলের মনােভাব ধীরে ধীরে নমনীয় ও আপসপন্থী হয়ে উঠতে থাকে) ও ধর্মসভাপন্থী রক্ষণশীলদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। মধ্যপন্থীরা এ বিষয়ে সুযােগ-সুবিধামতাে মতামত প্রকাশ করতেন। রক্ষণশীল ব্রাহ্ম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজনারায়ণ বসুর দুই ভাইয়ের বিধবা বিবাহ করার সংবাদ পেয়ে তাকে লিখেছিলেন, এই বিধবা বিবাহ হইতে যে গরল উত্থিত হইবে তাহা তােমার কোমল মনকে অস্থির করিয়া ফেলিবে; কিন্তু সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়।৩১
প্যারীচাঁদ সরকার প্রসন্নকুমার ঠাকুরের কাছে বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের পর চাঁদা চাইতে গেলে তিনি তা দিতে অস্বীকার করে প্যারীচাঁদকে এরকম ‘ধর্মবিরােধী অনুষ্ঠানে’ যােগ দেওয়ায় ভৎর্সনা করেন।
মধ্যপন্থীরা যাই করুন, বাংলার নব্যযুবকরা কিন্তু সােৎসাহে বিভিন্ন স্থানে মিলিত হয়ে এ-বিষয়ক আলােচনায় অংশগ্রহণ করতে থাকেন। ১৮৫৩-র গােড়ার দিকে এ সম্পর্কে তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটিতে ৮০ জনের মতাে ও দ্বিতীয়টিতে ১০০ জনের মতাে লােক হয়েছিল। শেষটিতে এত লােক হয়েছিল যে সকলের বসার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। সমবেত সকলে বিধবাদের শােচনীয় অবস্থার বর্ণনা করে বিধবাবিবাহের প্রতি তাদের সমর্থন জানান।৩২
এর কিছুদিন পরে ১৮৫৫ খিস্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর তারকনাথ দত্ত মেডিকেল কলেজ থিয়েটারে অনুষ্ঠিত বেথুন সােসাইটির একটি সভায় হিন্দু বিধবাবিবাহ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি বলেন, শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়, সামাজিক দিক থেকেও তিনি বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের পক্ষপাতী। সভায় তার বক্তব্যকে সমর্থন জানান হরদেব চট্টোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ ও কালীকুমার দাস।৩৩ দেখা যাচ্ছে, ঊনিশ শতকের মধ্যভাগেই বিধবাবিবাহের প্রশ্নটি নিয়ে বাঙালি হিন্দুসমাজ বাদানুবাদে লিপ্ত। এই বাদানুবাদকে আধুনিক যুগ-নির্দেশিত পথে এগিয়ে নিয়ে গেলেন প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান সংস্কৃত কলেজের ছাত্র এবং পরে অধ্যক্ষ ‘অভিনব পণ্ডিত’ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ।
বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব তিনি সমস্ত বিচ্ছিন্ন প্রয়াসকে সংহত করে এমন একটি আন্দোলন গড়ে তােলেন, যা জনমনকে আলােড়িত এবং সমাজকে বিচলিত করে তােলে। ইয়ংবেঙ্গল যেখানে নারীর মানসমুক্তির জন্য বিধবাবিবাহে আগ্রহী, বিদ্যাসাগর সেখানে ‘বাঙালি মায়ের মতাে হৃদয় দিয়ে বিধবা মেয়েদের দুরবস্থা উপলব্ধি করে সমাজ রক্ষাকল্পে বিধবাবিবাহ আন্দোলনে অবতীর্ণ। ইয়ংবেঙ্গলের আবেদন যেখানে প্রধানত যুক্তিগ্রাহ্য, বিদ্যাসাগরের আবেদন সেখানে যুক্তিগ্রাহ্য হয়েও প্রধানত মানবিক।
বিধবা বিবাহের বিপক্ষে কথাবার্তার মধ্যে ১৮৫৫ খিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হল বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব। যতদূর জানা যায়, এটাই বিধবা বিবাহের সমর্থনে বাংলায় লেখা প্রথম পুস্তিকা। পুস্তিকাটিতে সংক্ষেপে তিনি দেখালেন, কলিযুগে বিধবা বিবাহ অশাস্ত্রীয় নয়। বিশেষকরে ‘পরাশর সংহিতা’ থেকে উদ্ধৃতি তুলে তিনি স্পষ্টায়িত করলেন যে হিন্দুশাস্ত্রে বিধবা বিবাহের অনুমােদন আছে।৩৪ বিধবা বিবাহ প্রচলিত হলে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা ব্যাভিচারদোষ ও দ্রুণহত্যাপাপের নিবারণ ও তিনকূলের কলঙ্ক রােধ হতে পারে। এসব দেখিয়ে তিনি শেষে আবেদন জানালেন, এর শাস্ত্রীয়তা বিষয়ে যা লেখা হল, তা আলােচনা করে সকলে দেখুন, বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা?
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর পুস্তিকাটির পরিচয় দিতে গিয়ে ‘সংবাদ প্রভাকর’ তার লিখিত প্রমাণাদিকে একপ্রকার অকাট্য বলে ঘােষণা করে লিখল, ‘ঐ পুস্তক পাঠ করা হিন্দুমাত্রেরই পক্ষে অতি প্রয়ােজনীয়।”৩৫ ‘তত্ত্ববােধিনী পত্রিকা’ ১৭৭৬ শকের ফাল্গুন সংখ্যায় বিদ্যাসাগরের ‘বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা’ সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করে। পুস্তিকাটির পরিচয়দান প্রসঙ্গে সাহেবি কাগজ ‘সিটিজেন’ লেখে: The author with his wanted perspecuity of language, soundness of argument, based on texts deduced from accredited Hindoo Scriptures most clearly and rationally proves that the marriage of Hindoo widows is not only desireable but is in no way antagonistic with the dogmas of the Hindoo Shaster. The interesting brochure in question is very neatly got up… and reflex credit on the learned author in having boldly taken the lead in unhesitatingly advocating the cause of Hindoo Widow Marriage being himself a brahmin and a Pandit of the first order of the present time.৩৬ বিদ্যাসাগরের পুস্তিকা প্রকাশের পর বিধবা বিবাহ নিয়ে আলােচনার ধুম পড়ে গেল। নামী-অনামী অনেকেই ছােট-বড় পুস্তিকা প্রকাশ করে বিদ্যাসাগরের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানালেন।
(৭)
মােটামুটিভাবে প্রতিবাদ-পুস্তিকাগুলির প্রধান বক্তব্য তিনটি: বিধবা বিবাহ অশাস্ত্রীয়, বিধবাবিবাহ এদেশীয় প্রথা ও আচার বিরুদ্ধ, বিধবা হওয়া পূর্বজন্মের পাপ—এর সঙ্গে অন্যান্য হরেকরকম বক্তব্য তাে ছিলই। এইসব বক্তব্যকে খণ্ডন করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫৫র অক্টোবর মাসে প্রকাশ করলেন বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব’ (২য় পুস্তক)। আগরপাড়ার মহেশচন্দ্র চূড়ামণি, কোন্নগরের দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, আড়িয়াদহের শ্রীরাম তর্কালঙ্কার, পুটিয়ার ঈশানচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, সয়দাবাদের গােবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ, কৃষ্ণমােহন ন্যায়পঞ্চানন, রামগােপাল তর্কালঙ্কার, মাধবরাম ন্যায়রত্ন, রাধাকান্ত তর্কালঙ্কার, জনাই-এর জগদীশ্বর বিদ্যারত্ন, আন্দুল রাজসভার সভাপণ্ডিত, রামদাস তর্কসিদ্ধান্ত, ভবানীপুরের প্রসন্নকুমার মুখােপাধ্যায়, নন্দকুমার কবিরত্ন, আনন্দচন্দ্র শিরােমণি, গঙ্গানারায়ণ ন্যায়বাচস্পতি, হারাধন কবিরাজ, সর্বানন্দ ন্যায়বাগীশ, ভাটপাড়ার রামদয়াল তর্করত্ন, কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের সভাসদগণ, কাষ্ঠশালীর শিবনাথ রায়, বারাণসীর ঠাকুরদাস শর্মা, পীতাম্বর সেন কবিরত্ন, শ্রীরামপুরের কালিদাস মৈত্র, কৃষ্ণকিশাের নিয়ােগী, মুর্শিদাবাদের রামনিধি বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি পণ্ডিতদের মত তিনি তাঁর দ্বিতীয় পুস্তকে খণ্ডন করলেন।৩৭
১৭৭৭ শকের অগ্রহায়ণ সংখ্যা তত্ত্ববােধিনী’তে বিধবাবিবাহ দ্বিতীয় ভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে গ্রন্থটির উপক্ৰম ভাগ উদ্ধৃত করে সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়, “বিধবা স্ত্রীদিগের পুনৰ্ব্বার বিবাহ নিরাবলম্ব যুক্তি অনুসারে সর্বতােভাবেই কৰ্ত্তব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রানুসারে সম্পূর্ণ বিধেয় বলিয়া অবধারিত হইল। অতএব এক্ষণে উহা প্রচলিত করিয়া তাহাদিগের অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা ও ঘােরতর পাতকরাশি নিবারণ করিতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করা উচিত নহে।”৩৮
ঈশ্বরগুপ্ত, বিধবা বিবাহ আইনের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় অর্পিত আবেদনে৩৯ সই করেছেন, প্রথম বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছেন, ‘সংবাদ প্রভাকর’-এ বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ গ্রন্থ সম্পর্কে একবার নয়, বারবার সশ্রদ্ধ উক্তি৪০ করেছেন, এ ধরনের পুস্তক প্রকাশ করে সাধারণের উৎসাহ বৃদ্ধি করা অতি আবশ্যক বলে মত প্রকাশে কুণ্ঠিত হননি। ‘অহং যথার্থবাদী’ স্বাক্ষরে ‘বন্ধু হইতে প্রাপ্ত’-তে বিধবাবিবাহ চালু না থাকার ফল আলােচনা করে, বিদ্যাসাগরের গ্রন্থের প্রতি ‘ধর্মানুরঞ্জিকা’-সম্পাদক। যেভাবে কটুক্তি নিক্ষেপ করে শিষ্টাচারের বিধি লঙ্ঘন করেছেন, তার জন্য ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর ক্ষোভ প্রকাশ না করে পারেনি।৪১ পুত্রবতী বিধবার বিবাহ সমর্থন না করলেও বালবিধবার বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ, যুক্তিসিদ্ধ ঐহিক নিয়মসিদ্ধ সৰ্ব্বতােভাবেই প্রসিদ্ধ কোনােমতেই অসিদ্ধ নহে’—একথা লিখতে দ্বিধা করেননি। বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত অথবা নয় তা নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মাথা ঘামাননি। প্রশ্নটিকে যুক্তির সাহায্যে বিচার করে তার মনে হয়েছে বালিকা বিধবার বিবাহ দেওয়া অবশ্যকর্তব্য। তার এই মনােভাবের পরিচয় মেলে ‘সংবাদ প্রভাকর’-এ প্রকাশিত একটি কবিতায়। এতে তিনি পরিষ্কার জানিয়েছেন—
‘বালিকা অক্ষতযােনি, পতিহীনা যত
তাহার বিবাহ দিতে আমি দিন মত।
-
- •• ••• ••• •••
তাদের বিবাহ যাঁরা না করেন দান
নিদয় হৃদয় তারা পাষাণসমান।৪২
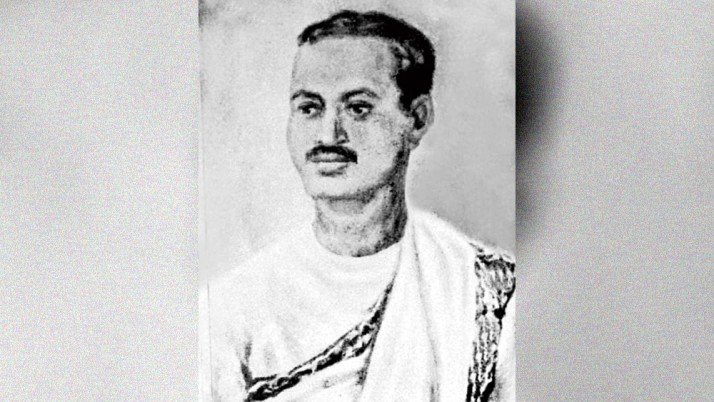
যাইহােক, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর বিধবা বিবাহ আন্দোলন সমাজকে আলােড়িত করেছিল, ঝড় তুলেছিল বাঙালি সমাজে কিন্তু সমাজে তা স্বীকৃতি পায়নি। লক্ষ লক্ষ বিধবার মধ্যে গােটা ঊনিশ শতকে একশােটিও বিধবা বিবাহ হয়েছিল কিনা সন্দেহ। বিদ্যাসাগরজীবনীকার জানিয়েছেন “আইন পাশ হইবার পর ৬০/৭০ টি মাত্র বিধবা বিবাহ হইয়াছে। বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া হিন্দু সমাজে স্বীকৃত হয় নাই।”৪৩ উনিশ শতকে যত বিধবা বিবাহ হয়েছিল, তার চেয়ে বেশি না হলেও প্রায় সমসংখ্যক পুস্তক-পুস্তিকা এই আন্দোলনের পক্ষে-বিপক্ষে রচিত হয়েছিল। অর্থাৎ যদিও বিদ্যাসাগরের আন্দোলন ছিল মূলত মানবিক, কিন্তু তার আন্দোলনের সাফল্য আইন প্রণয়নেই সীমাবদ্ধ।
আসলে বিধবা বিবাহ আন্দোলন একান্তভাবে সীমাবদ্ধ আন্দোলন, মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণের হিন্দু বাল বিধবা সংক্রান্ত, সতী আন্দোলনের মতাে এর সঙ্গে জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িত ছিল না। এবং এর বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছিল যুগসঞ্চিত সংস্কার।
(৮)
উনিশ শতকে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার বিঘ্নস্বরূপ বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবা বিবাহ নিষেধ—এই তিনটি সমস্যা সম্পর্কেই সচেতন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সবচেয়ে গুরুত্ব আরােপ করেছিলেন বিধবা বিবাহের ওপর। বিধবা বিবাহ নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আদৌ সহায়ক হবে কিনা এ সম্পর্কে কোনাে সংশয় তার মনে দেখা দেয়নি। এই সামাজিক প্রথা অবশ্য সতীদাহের মতােই নিম্নশ্রেণির হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। এই প্রথাই ছিল উচ্চশ্রেণির অর্থাৎ বিত্তবান বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের। মুসলমানদের শাস্ত্রে বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে কিছু নেই, এবং তা সর্বতােভাবে শাস্ত্রসম্মত। হজরত মােহাম্মদের (সঃ) প্রথম বিবাহই (৫৯৫খৃঃ) ছিল বিধবা-বিবাহ। সেই হিসেবে বিধবা বিবাহের প্রশ্ন মুসলমান সম্প্রদায়ের সমস্যা না হলেও উচ্চশ্রেণির মুসলমানদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ উনিশ শতকের বাংলাদেশে তেমন প্রচলিত ছিল না। হিন্দু উচ্চশ্রেণি যেমন মুসলমান উচ্চশ্রেণির মধ্যে প্রচলিত অবরােধ প্রথার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল তেমনি মুসলমান উচ্চশ্রেণিও এক্ষেত্রে হিন্দু উচ্চশ্রেণির বিধবাদের চিরবৈধব্যের আদর্শের দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর সংস্কার আন্দোলন অবশ্য মুসলমান উচ্চশ্রেণির বিধবাদের ক্ষেত্রে প্রযােজ্য ছিল না। সেদিক দিয়ে তার সামাজিক আন্দোলনের যেমন একটা শ্রেণিচরিত্র ছিল তেমনি তার একটা জাতিগত’ চরিত্রও ছিল। উচ্চশ্রেণির হিন্দু বিধবা নারীদের ওপর যে নিপীড়ন ‘চিরবৈধব্যে’র আদর্শের মাধ্যমে প্রচলিত ছিল, সেই নিপীড়নের বিরুদ্ধেই নিয়ােজিত হয়েছিল বিদ্যাসাগরের মূল সংস্কার প্রচেষ্টা।
উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ শুধুমাত্র বিধবা বিবাহ শিক্ষার আলােক বঞ্চিত, মানসিক জড়তাগ্রস্থ নারীদের মুক্তির পথ দেখাতে পারত কিনা সন্দেহ। বাল্য বিবাহ এবং বহুবিবাহ রােধ এবং বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হলে বালবিধবাদের সমস্যা যে অনেকটা নিবারিত হবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তা জানতেন। বিধবা বিবাহের মতাে এ দুটি সম্পর্কে সাধারণের সংস্কারও এত প্রবল ছিল না। এসব সত্ত্বেও তিনি প্রথমেই বিধবা বিবাহ প্রচলনে আগ্রহী হন। কিন্তু কেন?
বিদ্যাসাগরের চোখের সামনে বাঙালি সমাজে বালবিধবার দুরবস্থা তাকে বিচলিত করেছিল। “বীরসিংহ গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যাসাগরের খেলার সাথী ছিল। বালিকাটি বালবিধবা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাকে খুব পছন্দ করতেন এবং মনে হয় বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের মধ্যে অনুরাগের সঞ্চার হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন জানতে পারলেন যে সে বিধবা এবং শাস্ত্রের নির্দেশে সেই বালিকা আজীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করতে না পেরে সে আত্মহত্যা করে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন সেই অসহায় বিধবার শােচনীয় পরিণামের কথা জানতে পারলেন তখন তিনি শপথ করলেন যে তিনি হিন্দু বিধবাদের পূনর্বিবাহের অধিকার সমাজে প্রচলিত করে সরকারকে দিয়ে তা বিধিবদ্ধ করাবেন।”৪৪ বিনয় ঘােষের এই তথ্য সঠিক ও যুক্তিযুক্ত। কারণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করা পছন্দ করতেন না।
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জানতেন যে, আইনগত ব্যবস্থা না থাকলে শুধু বাচনিক বিজয় যথেষ্ট নয়। তাই তিনি হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের জন্য আইন প্রণয়নের অনুরােধ জানিয়ে সরকারের কাছে এক আবেদন পেশ করেন (৪ অক্টোবর ১৮৫৫)। এতে তার নিজেরসহ ৯৮৮ জনের স্বাক্ষর ছিল। অচিরেই একটি বিধবা বিবাহ বিল তৈরি হলাে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে আলােচনার জন্য। এ বিলের বিরুদ্ধে অনেকগুলি আবেদন পড়ল। আবেদনকারীদের প্রধান যুক্তি ছিল এই যে, বিধবা বিবাহ হিন্দু আইন, প্রথা ও ধর্মের পরিপন্থী এবং এর সমর্থনে আইন পাস করলে তা ব্যাপক সামাজিক, আইনগত ও অর্থনৈতিক সমস্যার জন্ম দেবে। কোনাে কোনাে আবেদনে গুরুতর রাজনৈতিক পরিণতির আভাসও দেওয়া হয়েছিল। আবার বিলটিকে সমর্থন করেও কতিপয় আবেদন পেশ করা হয়েছিল, যার মধ্যে ছিল ৩৭৫টি স্বাক্ষর সম্বলিত ডিরােজিওপন্থীদের একটি আবেদন। এতে সম্পূর্ণ অযাজকীয় বিবাহের ব্যবস্থাসহ আরও আমূল পরিবর্তনসূচক আইন পাসের আহ্বান জানানাে হয়। অবশেষে ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে বিলটি কোনাে পরিবর্তন ছাড়াই আইনে (১৮৫৬ সালের ১৫নং আইন) পরিণত হলে হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের আইনগত বাধা দূর হয়।
বিদ্যাসাগরের চরিত্রের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল যে তিনি যা বিশ্বাস করতেন বা প্রচার করতেন তা নিজের ক্ষেত্রেও বাস্তবিকভাবে প্রয়ােগ করতেন। তাই তার ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্র এক বাল-বিধবাকে বিবাহ (১৮৭০) করে পিতার আদর্শের সার্থক রূপায়ণ করেছিলেন। কিন্তু এই বিবাহে আত্মীয়-স্বজন আপত্তি জানালে ও অসন্তুষ্ট হলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার ভাই শম্ভুচন্দ্রকে লেখেন : “…আমি বিধবা বিবাহের প্রবর্তক। আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি এমনস্থলে আমার পুত্র বিধবা বিবাহ না করিয়া কুমারী বিবাহ করিলে আমি লােকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম। ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম…বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সকর্ম। এ জন্মে যে ইহা অপেক্ষা আর কোন সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরান্মুখ নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ব বিচ্ছেদ অতি সামান্য কথা।…আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি। নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বােধ হইবে, তাহা করিব, লােকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।”৪৫
এই পত্রের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে যে দৃঢ়তা ও আদর্শনিষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে তা বিদ্যাসাগর চরিত্রের এক অনবদ্য দিক। আবার এই পুত্রই যখন পরবর্তীকালে তার বিবাহিত স্ত্রীকে ত্যাগ করতে চাইল, ন্যায়নিষ্ঠ বিদ্যাসাগর তাতে প্রবল আপত্তি জানালেন এবং তার উইলে পুত্রবধূকেই তার নিজ সম্পত্তির অধিকার দিলেন, তার নিজ পুত্রকে নয়। আদর্শ ও কর্তব্যনিষ্ঠা এবং দরদী হৃদয়ের এর থেকে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কি থাকতে পারে?
বিধবা বিবাহ আইন কিন্তু দীর্ঘদিনের সংস্কারের মূলােচ্ছেদ করতে পারেনি। যে কারণে আইন পাশের বছর তিনেক পরে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়’৪৬মন্তব্য করে, এদেশের কি ভদ্র কি অভদ্র সকলেই বিধবা বিবাহ দূষ্য ও শাস্ত্র নিষিদ্ধ এবং ব্যবহারবিরুদ্ধ বলিয়া জানেন। এই মনােভাবের জন্য দু’চারজন ছাড়া অধিকাংশই বিয়ে করত টাকার লােভে বা রমণীভােগের প্রলােভনে। কালীপ্রসন্ন সিংহ ‘সম্বাদ ভাস্কর’-এ ঘােষণা করেছিলেন ‘সম্বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক বিধবা বিবাহকারীকে তিনি হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন— কার্যকালে অবশ্য সর্বত্র তিনি তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি। হরি চক্রবর্তী নামে এক অর্থলােভী ‘বিধবা বিবাহকারক’ এই প্রতিশ্রুতির অর্থ না পেয়ে ভাস্কর সম্পাদকের কাছে প্রেরিত এক পত্রে দুঃখপ্রকাশ করেন।৪৭
বাস্তবিকই বিধবা বিবাহ উপলক্ষে বিদ্যাসাগর সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। তিনি নিজেই এক জায়গায় লিখে গেছেন, ৬০টি বিধবা বিবাহের জন্য তার ৮২ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছিল।৪৮ যাই হােক জীবনের শেষ দিকে তার ব্যর্থতার জন্য তিনি অনেক আক্ষেপ করেছেন এবং তিনি কিছুটা হতাশ হয়ে সংগ্রামবিমুখ হয়ে পড়েছিলেন। স্বদেশবাসীর, বিশেষত শিক্ষিত ও শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিরােধিতায় তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন। বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে দুঃখ করে একট চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: “আমাদের দেশের লােক এত অসার অপদার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে আমি কখনই বিধবা বিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না।”৪৯
উনিশ শতকের শেষ দিকে হিন্দু উচ্চ ও মধ্যশ্রেণির রক্ষণশীলতার উত্থান, ওই শ্রেণিরই একজন হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মধ্যে যে হতাশার সৃষ্টি করেছিল, তার সব থেকে বড় প্রমাণ সহবাস সম্মতি আইন সম্পর্কে ১৮৯১ সালের ফেব্রুয়ারিতে অর্থাৎ মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস পূর্বে, তার অভিমত। এ প্রসঙ্গে বাল্যবিবাহ প্রথা আইনের দ্বারা রহিত করার দাবি না জানিয়ে তিনি সরকারকে লিখেছিলেন, “…I should feel like the measure to be so framed as to give something like an adequate protection to child-wives, without in any way conflicting with any religious usage.I would propose that it should be an offence for a man to consummate marriage before his wife has had her first menses …such a law would not only serve the interests of humanity…but would, so far from interfering with religious usage, enforce a rule laid down in the Sastras.”৫০
যে ব্যক্তি ১৮৭০ সালে পুত্রের বিবাহ এক বালবিধবার সঙ্গে আত্মীয়দের বিরােধিতা সত্ত্বেও বিবাহ দিয়েছিলেন তিনিই বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে পূর্বে লেখনী ধারণ ও আন্দোলন করা সত্ত্বেও ১৮৯১ সালে ধর্মীয় আচার লঙঘন না করে শাস্ত্রসম্মত আইন প্রণয়নের জন্যে সরকারের কাছে প্রস্তাব করলেন। এই পরাজয় শুধু বিদ্যাসাগরের পরাজয় ছিল। এ পরাজয় ছিল উনিশ শতকের সমাজের উচ্চ ও মধ্যশ্রেণির অগ্রণী অংশের। শুধু হিন্দু সমাজেরও নয়, সমগ্র বাঙালি সমাজের। যে কারণে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি বণিক পরিবারগুলি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাণিজ্যের পাট চুকিয়ে জমিদারির মধ্যে নিজেদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার সন্ধান করেছিল, ঠিক সেই কারণেই উনিশ শতকের পাঁচের দশক পর্যন্ত বাঙালি সমাজের উচ্চ ও মধ্যশ্রেণির যেটুকু অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল, সে অগ্রগতিও প্রতিক্রিয়ার আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়ে অনেকাংশে বিলুপ্ত হয়েছিল।৫১
(৯)
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪) এই দু’জন মনীষীর পরস্পর বিরােধিতা। তাঁরা যদি একযােগে কাজ করতেন তাহলে উনিশ শতকের জাগরণের সফলতা আরও বেশি হত। এজন্য বিদ্যাসাগর ততটা দায়ী নন, যতটা বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের শক্তিশালী লেখনীর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের নিরলস প্রয়াস যুক্ত হলে দেশের চেহারা বদলে যেত।
বিদ্যাসাগর রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলােকে স্বধর্মে থেকেও মানবতাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন। আর বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট হলেও তিনি ছিলেন হিন্দু ঐতিহ্যমুখী জাতীয়তাবাদের জনক। ঊনিশ শতকের গাড়িকে একজন চাইছেন সামনের দিকে এগিয়ে দিতে, আর একজন চাইছেন পিছনদিকে ঠেলে দিতে৷ বিদ্যাসাগরের যাবতীয় কাজের বিরােধিতা করাই বঙ্কিমচন্দ্রের বাতিক ছিল। সেদিন সামাজিক সংস্কারের যে কাজ বিদ্যাসাগর শুরু করেছিলেন এবং শিক্ষার যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তা সমর্থন করেননি। বরং স্বধর্মে দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত থেকে সংস্কারের কথা বলেছেন—যা সামগ্রিকভাবে বাঙালিজাতি হিন্দু-মুসলমানের পক্ষে কল্যাণকর হয়নি। বিদ্যাসাগর মুসলমান সমাজের জন্য কিছু করেননি, কারণ তিনি মুসলমান সমাজকে জানতেন না, যে সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা নেই, সে সম্পর্কে কিছু বলা তাঁর স্বভাব ছিল না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান সমাজ সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানতেন না। যেটুকু জানতেন সেটুকু ইংরেজ লিখিত ইতিহাস পড়ে। মুসলমান সমাজের সঙ্গে তিনি যে মিশেছিলেন এমন তথ্য আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।
বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রবর্তন এবং বহুবিবাহ রহিত করার জন্য আন্দোলন করেছিলেন (যেটা পূর্বেই বলা হয়েছে)। বহুবিবাহকে তিনি সমাজের কলঙ্ক বলে মনে করেছিলেন বলেই দুর্নীতি, ব্যভিচারকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। নারীকে খেলার সামগ্রীতে পরিণত হতে দেননি। এক একজন কুলিনের ৫০/৬০ জন করে স্ত্রী থাকত, এই কুপ্রথা উচ্ছেদ করার জন্য তিনি এগিয়ে এলেন। এই আন্দোলনের তিনি প্রথম হােতা নন। রামমােহন রায় ও ইয়ং বেঙ্গলরা এই কুলিন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। ১৮৫৪ সালে রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৬৬) কুলীনকুলসর্বস্ব’ নাটকে এবং প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে ‘আলালের ঘরের দুলাল’-এ (১৮৫৮) কুলীন জামাইদের চিত্র তুলে ধরেন। বিদ্যাসাগর যখন বিধবা বিবাহ ও বহুবিবাহ রহিত আন্দোলন শুরু করলেন বাধা এল শুধু সমাজ থেকে নয় সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর কাছ থেকেও। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বিরােধিতা করেছিলেন। ১২৮০ আষাঢ় সংখ্যা ‘বঙ্গদর্শন’-এ বহুবিবাহ রহিত করার বিপক্ষে তিনি অশালীন ও কটু মন্তব্য করেছিলেন, “যদি ধর্মশাস্ত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশ্বাস ও ভক্তি থাকে এবং যদি বহুবিবাহ সেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস থাকে, তবে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে অধিকারী বটে, এবং তাঁহার পুস্তক একজন সদানুষ্ঠতার সদানুষ্ঠানে প্রবৃত্তির প্রমাণস্বরূপ সকলের নিকট আদরণীয়। আর যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্ত্রে বিশ্বাস ও ভক্তি না থাকে, তবে সেই শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া কপটতা মাত্র।…যে ব্যক্তি আত্মরক্ষার্থে কপটতা করে, তাহার অপেক্ষা যে নিষ্প্রয়ােজনে কপটতা করে, সেই অধিকতর নিন্দনীয়। যিনি এই পাপপূর্ণ, মিথ্যাপরায়ণ মনুষ্যজাতিকে এমত শিক্ষা দেন যে, সদনুষ্ঠানের জন্য প্রতারণা এবং কপটাচারও অবলম্বনীয়, তাঁহাকে আমরা মনুষ্যজাতির পরম শত্রু বিবেচনা করি। তিনি কুশিক্ষার পরমগুরু।”

বিধবা বিবাহ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের সমর্থন ছিল না। প্রকাশ্যে বিরােধিতা করেছেন, উপন্যাসেও কটাক্ষ করেছেন। ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসে সূর্যমুখীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, “ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে নাকি বড় পন্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবা বিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার ব্যবস্থা করে সে যদি পন্ডিত হয় তবে মূখ কে?” “বঙ্গদর্শন’ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭ সংখ্যায় তিনি লিখেছিলেন, “বিধবাদের দুঃখ যে অসহ্য এমত আমাদের বােধ হয় না। যদি বাস্তবিক অসহ্য হয় অথচ তাহাতে সমাজের উপকার থাকে, তবে তাহা মােচন করিবার আবশ্যক কি? …যদি পাঁচজন বিধবার দুঃখ মােচন না করিলে নিষ্ঠুরতা হয় তবে বিধবা বিবাহ চালাইয়া সমাজের সহস্র ব্যক্তির অপকার করা চন্ডালতা—গােরু মেরে জুতা দান ধর্ম নহে। বিধবার যদি দুশ্চরিত্রা হইবার আশঙ্কা থাকে, বিবাহ দিলেও সে আশঙ্কা একেবারে নির্মূল হয় না। অনেক সধবাও দুশ্চরিত্রা হয়।”
অনেকেই ‘সাম্য’ গ্রন্থের পঞ্চম পরিচ্ছেদ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি উদ্ধৃত করে দেখাতে চান যে, বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহকে বঙ্কিমচন্দ্র সমর্থন করেন। সেই পংক্তিগুলি হল— “পন্ডিত শ্ৰীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্ম সম্প্রদায় অনেক যত্ন করিয়াছেন— তাঁহাদিগের যশ অক্ষয় হউক।” প্রথমত এই উক্তিটি বিধবাবিবাহের সমর্থনসূচক নয় এই কারণে যে, তৎকালীন নারীসমাজের শােচনীয় অবস্থা দেখে বঙ্কিমচন্দ্র নারীশিক্ষার প্রয়ােজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। নারীশিক্ষা প্রচার ও প্রসারে বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত প্রয়াস ও ব্রাহ্ম সমাজের পৃষ্ঠপােষকতা দেখেই উপরােক্ত কথাগুলি বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন। দ্বিতীয়ত বঙ্কিমচন্দ্র ‘সাম্য’ গ্রন্থ বাজার থেকে তুলে নিয়েছিলেন। যে গ্রন্থের প্রচার তিনি বন্ধ করেছিলেন সেই গ্রন্থের বক্তব্যের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের আস্থা ছিল না বলেই মনে হয়।

বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্বকে বঙ্কিমচন্দ্র চিরকাল খাটো করে দেখেছেন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের (১৮৪০-১৯৩২) সঙ্গে মৌখিক আলাপে বঙ্কিমচন্দ্র ‘সীতার বনবাস’কে কান্নার জোলাপ বলেছেন। লিখিত সমালােচনায় বলেছিলেন, “তিনি স্বপ্রণীত গ্রন্থে আরও কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাহা পাঠকালে রামের কান্না পড়িয়া আমাদিগের মনে হইয়াছিল যে, বাঙ্গালীর মেয়েরা স্বামী বা পুত্রকে বিদেশে চাকরি করিতে পাঠাইয়া এইরূপ করিয়া কাঁদে বটে।” রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩১-১৮৯৪) একথার প্রতিবাদ করেছেন, “বিদ্যাসাগর রচিত সীতার বনবাসকে অনেকে কান্নার জোলাপ কহে। ঐ পুস্তকের প্রথমাংশ ভবভূতি প্রণীত উত্তরচরিতের প্রায় অবিকল অনুবাদ, কিন্তু অপর সমুদয় ভাগ কেবল নূতন রূপ রচনাই নহে, উহাতে যে কি মধুর, কি চমৎকারজনক ও কি অলৌকিক কান্ড সম্পাদিত হইয়াছে তাহা বর্ণনীয় নহে। বােধ হয় উহাতে এমত পৃষ্ঠাও নাই, যাহা পাঠ করিতে পাষাণেরও হৃদয় দ্রব না হয়। করুণ রসের উদ্দীপনে বিদ্যাসাগরের যে কি অদ্ভুত শক্তি আছে, তাহা এক সীতার বনবাসেই পর্যাপ্তরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।”৫২ শুধু সাহিত্য কেন বিদ্যাসাগরের যাবতীয় কীর্তিকে বঙ্কিমচন্দ্র নস্যাৎ করেছেন। কিছুটা অসূয়াবশত কিছুটা দম্ভবশত। ‘ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব’ (১৮৮৫) প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র রামমােহনের পরে দেশপ্রেমিক নেতা হিসেবে বিদ্যাসাগরের নাম না করে রামগােপাল ঘােষ (১৮১৫-১৮৬৮) ও হরিশচন্দ্র মুখােপাধ্যায়ের (১৮২৪১৮৬১) নাম করেছিলেন।
(১০)
শেষে বলি, বিদ্যাসাগরের তত্ত্বে ও কর্মে নবজাগরণের প্রায় সব উপাদানের উল্লেখযােগ্য উপস্থিতি সত্ত্বেও কয়েকটি কারণে ভারতের নবজাগরণে তার অবদান সীমিত এবং অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। প্রথমত, নারীমুক্তিতে, বিশেষত বিধবা বিবাহে তার তৎপরতায় সমাজপতিরা খড়গহস্ত হয়ে ওঠায় তিনি ভারতের এক প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের নিরস্ত করতে পেরেছিলেন। এই পদ্ধতি নবজাগরণের পরিপূরক। কিন্তু এই পদ্ধতিকে আরও বিস্তৃত করে, এবং ধর্মশাস্ত্রের আগেকার আরও যুক্তিবাদী এবং বস্তুবাদী প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যকে নবরূপে উপস্থাপিত করলে এই পদ্ধতির প্রয়ােগ আরও সর্বজনীন হত, আর নবজাগরণের বৌদ্ধিক-সাংস্কৃতিক প্রবাহ আরও সমৃদ্ধ হত। তাছাড়া লােকায়ত বা চার্বাক দর্শনের বলিষ্ঠ বস্তুবাদ, নাস্তিকতা, এবং জগৎ ও জীবনমুখিতা সম্বন্ধেও তিনি অবশ্যই অবহিত ছিলেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতের এই বিশেষ বৌদ্ধিকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্যটিকে পুনরুজ্জীবিত করে নবজাগরণে গতি সঞ্চার করতে তিনি তৎপর হননি।
অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের কোনও উল্লেখযােগ্য বক্তব্য বা কার্যক্রম ছিল না। মূলত ইংরেজ সরকারের সহায়তায়ই তিনি শিক্ষা বিস্তার এবং সমাজ সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন। তার জীবিতকালেই বাংলার তথা ভারতের রাজনৈতিক পরিবেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে তার মনে কোনও চঞ্চলতা থাকলেও বাইরে তা প্রকাশ পায়নি। সমকালীন ইউরােপ ও আমেরিকায় বৈপ্লবিক রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং শ্রমিক আন্দোলনের জোয়ার নিশ্চয়ই তার অজানা ছিল। কিন্তু এমনকি শুধুমাত্র তাত্ত্বিক স্তরে রাজনৈতিক চিন্তাও তিনি প্রকাশ করেননি। প্রকৃতপক্ষে দারিদ্রের মধ্যে বেড়ে উঠেও বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন আধুনিক কিন্তু মধ্যপন্থী সংস্কারক। কোনও বৈপ্লবিক সমাজতত্ত্ব বা সংগঠন গড়ে তুলতে তিনি আগ্রহী ছিলেন না। আর এ কারণেই তার সমাজ সংস্কারের কার্যক্রম নবজাগরণের সম্ভাবনাকে আরও বিকশিত করে তুলতে পারেনি। সম্ভবত তাই শেষ জীবনে তিনি নিরাশ ও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন।
তাছাড়া যে বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রচলন এবং বহু বিবাহ ও বাল্যবিবাহ বন্ধ করার সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলনে চারিত্রিক ঋজুতার পরিচয় দিয়েছিলেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন, শিক্ষার প্রসারে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন, পাঠ্যসূচীর প্রশ্নে সাংখ্য-বেদান্ত প্রভৃতি ভারতীয় দর্শনকে ভ্রান্ত বলে ঘােষণা করে এগুলির প্রভাব দূর করার জন্য আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং ঈশ্বর, ধর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে দিয়েছিলেন নির্মোহ অবস্থানের পরিচয়—তিনিই আবার জনশিক্ষার প্রসার বলতে শিক্ষাকে শুধুমাত্র উচ্চশ্রেণীর (মধ্যশ্রেণীসহ) মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সর্বশ্রেণির মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে মূলত কোনও উৎসাহ দেখাননি।
সংস্কারমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও জাতিভেদের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর কোনও আন্দোলন পরিচালনার উৎসাহ পাননি। একমাত্র তার তৎপরতায়ই সংস্কৃত কলেজে সর্বপ্রথম অব্রাহ্মণ ছাত্রদেরও ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়ে তার আর কোনও তাত্ত্বিক অবদান বা কর্মপ্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়নি। অথচ বিধবা বিবাহের চেয়ে এ বিষয়টি যে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। হয়তাে তিনি ভারতের আর্থসামাজিক কাঠামাের মধ্যে জাতিবর্ণভেদের গভীর শেকড়, এর দুরুচ্ছেদ্যতা, আর সমাজপতিদের সম্ভাব্য প্রবল প্রতিরােধের সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেই এ ব্যাপারে অগ্রণী হননি। কিন্তু এহেন পশ্চাদপসারণের ফলেই আমাদের নবজাগরণ অসম্পূর্ণ ও অসমাপ্ত থেকে গেছে। পাশাপাশি লােকাচারের দোহাই দিয়েও তিনি মহিলা শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের বিরােধিতা করেছিলেন, বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য
প্রস্তাবিত আইনের প্রশ্নে ধর্মীয় আচার লঙঘন না করার জন্য সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন; সিপাহী বিদ্রোহ দমনকারী ব্রিটিশ বাহিনীর থাকবার জন্য তার পরিচালনাধীন সংস্কৃত কলেজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। নীলবিদ্রোহ বা সিপাহী বিদ্রোহের প্রতি সামান্যতম সমর্থন নিয়েও এগিয়ে তিনি আসতে পারেননি।
সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব ও মহত্ত্বকে অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক বাংলার নির্মাণকর্তা হিসাবে তাঁর অবদান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ণ উদ্ধৃত করে আমাদের বক্তব্যে ইতি টানছি : “তার (বিদ্যাসাগর) দেশের লােক যে যুগে বদ্ধ হয়ে আছেন, বিদ্যাগর সেই যুগকে ছাড়িয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ সেই বড় যুগে তার জন্ম, যার মধ্যে আধুনিক কালেরও স্থান আছে, যা ভাবীকালকে প্রত্যাখ্যান করে। যে গঙ্গা মরে গেছে তার মধ্যে স্রোত নেই, কিন্তু ডােবা আছে। বহমান গঙ্গা তার থেকে সরে এসেছে, সমুদ্রের সঙ্গে তার যােগ। এই গঙ্গাকেই বলি আধুনিক। বহমানকাল গঙ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবন ধারার মিল ছিল, এই জন্য বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক। যারা অতীতের বড় বাধা লঙ্ঘন করে দেশের চিত্তকে ভবিষ্যতের পরম সার্থকতার দিকে বহন করে নিয়ে যাবার সারথিস্বরূপ, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই মহারথিগণের একজন অগ্রগণ্য ছিলেন, আমার মনে এই সত্যিটিই সবচেয়ে বড় হয়ে লেগেছে।” বিদ্যাসাগর সম্পর্কে এর চেয়ে বড় শ্রদ্ধাঞ্জলি আর হতে পারে না।
তথ্যসূত্রঃ
১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ব্রিটিশ প্যারামাউন্টসি অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান রেনেসাঁস, পার্ট-২, ভারতীয় বিদ্যাভবন, বম্বে, ১৯৬৫, পৃ. ২৮৫।
২. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্ত্রীশিক্ষায় বিদ্যাসাগর; দেখুন-বিমান বসু সম্পাদিত, প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৫১।
৩. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।
৪. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।
৫. মােহাম্মদ আজিজুল হক, বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা, প্রথম প্রকাশ, ১৯১৭; অনুবাদ-মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ২৭ ২৮।
৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ‘প্রাচীনা ও নবীনা’, বিবিধ প্রবন্ধ, কলকাতা, ১৯৯৬।
৭. অন্নদাশংকর রায়, স্বাধীনতার পূর্বাভাষ, কলকাতা, ১৩৮৬, পৃ.১৩১।
৮. গােপাল হালদার, প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৫।
৯. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, বাঙালির নতুন আত্মপরিচয়: সূচনার সূচনা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পত্রিকা, সংখ্যা-৪, ১৯৯২, কলকাতা।
১০. বিনয় ঘােষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ৩৯৩।
১১. ইন্দুভূষণ দাস, রামমােহন বিদ্যাসাগর মাইকেল, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৫৪।
১২. বিদ্যাসাগর রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ১০৫।
১৩. বিদ্যাসাগর রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১।
১৪. কনক মুখােপাধ্যায়, উনবিংশ শতাব্দীর নারী প্রগতি ও রামমােহন বিদ্যাসাগর, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ.৭৪।
১৫. কনক মুখােপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫।
১৬. কনক মুখােপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৬-৭৭।
১৭. সিপাহী বিদ্রোহ দমনকারী সরকারি সৈন্যবাহিনীকে কেন সংস্কৃত কলেজে থাকতে দেওয়া হয়েছিল-কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে এই অভিযােগ করা হয়। কিন্তু জানবার চেষ্টা করা হয়নি এ নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের কি ধরণের চিঠি চালাচালি হয়েছিল, বা সরকার চালিত একটি প্রতিষ্ঠানের বাড়িঘর সরকার কোনাে কারণে অধিগ্রহণ করতে চাইলে অধ্যক্ষের কতটুকু কি করার থাকে? এখন তাে দেখি কলেজ-বাড়ি অধিগ্রহণের ব্যাপারে এস.ডি.ও. বা বি.ডি.ও-র মতাে সরকারি আমলার একটি দু-লাইনের নির্দেশের কাছে বাঘা বাঘা অধ্যক্ষরা কিরকম অসহায় হয়ে যান। এরকম যুক্তি কেউ কেউ (যেমন-শক্তিসাধন মুখােপাধ্যায়) দেন। বিনয় ঘােষও লিখেছেন, “১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় থেকে দেখা যায়, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সরকারী শিক্ষা বিভাগের মত বিরােধের আবার সূত্রপাত হতে থাকে।…ক্রমে তা এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে বিদ্যাসাগর শেষ পর্যন্ত তার অধ্যক্ষতার সরকারী চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।” (বিনয় ঘােষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪)। শুধুমাত্র মতবিরােধ এবং চাকরি ত্যাগের সময় নির্ধারণ করার জন্যই এখানে সিপাহীবিদ্রোহের প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে ব্যাপারটা এমন নয়, চাকরি ত্যাগের কারণ নির্ধারণ করাটাও এর একটা লক্ষ্য। কোনাে পাঠকের চোখই তা এড়িয়ে যেতে পারে না। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় সংস্কৃত কলেজকে বৃটিশ সেনাবাহিনীর হাসপাতালে পরিণত করা হয়েছিল। বলা হয়, ঈশ্বরচন্দ্র নাকি তার তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। অনেকের আলােচনাতেই তার প্রতিবাদ পত্রের উল্লেখ আছে কিন্তু তার কোনাে অংশও উদ্ধৃত হয়েছে এমনটি বর্তমান লেখকের চোখে পড়েনি (এটা তার ঘাটতি ও হতে পারে)। তবে হীরেন বােস তার ইংরেজিতে লেখা ‘রেনেসাঁনায়ক’ শীর্ষক প্রবন্ধে যে আলােচনা করেছেন তাতে ঐ পত্রের কিছুটা আঁচ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, “তার কাছে নিজের চাকরির চেয়েও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির পবিত্রতার প্রশ্নটি অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বৃটিশের দেওয়া মাইনের চাকুরে হয়েও নিজের পরিণতির কথা না ভেবে তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরােধিতা করেছিলেন। সে সময়ের উত্তাল বছরগুলির পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে নিজের আদর্শের সপক্ষে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের এই অবস্থান ছিল অসাধারণ।” (বিনয় ঘােষ, প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৬৬)। এ থেকে বােঝা গেল, তিনি নিজের আদর্শ রক্ষা করার জন্য প্রতিবাদ করেছিলেন। কী সেই আদর্শ? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা রক্ষা করা। রােম’যখন দাবানলে দগ্ধ হয়, তখন ‘বেহালা’ রক্ষা করাটাই হয় ‘নীরাে’দের প্রধান কাজ। সমগ্র ভারতবর্ষ যখন ঔপনিবেশিক শক্তির বর্বরতায় রক্তের প্লাবনে ভাসছে, কৃষক আর তাদেরই সন্তান সিপাহীদের রক্তে সারা ভারতবর্ষের মাটি যখন লাল, ইংরেজ রাজ-শক্তি যখন ভারতবর্ষের জাতীয় স্বাধীনতার আত্মার টুটি টিপে ধরে সমগ্র ভারত ভূমিকেই ‘অপবিত্র করে তুলেছে তখন সংস্কৃত কলেজের ‘পবিত্রতা রক্ষার আওয়াজ তােলাটা যদি ‘মহান আদর্শরূপে গৌরবান্বিত হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় সেই আদর্শ ভীরু কাপুরুষের আদর্শ, বীরের আদর্শ নয়; সেই আদর্শহীন স্বার্থান্বেষীর আদর্শ জাতির স্বার্থে সর্বস্বত্যাগীর আদর্শ নয়; এই আদর্শের সাথে জাতির কোন সম্পর্ক নেই, এই আদর্শে জাতির কোন প্রয়ােজন নেই কারণ, জাতি বীর প্রসবিনী, সিধু-কানু-চঁাদ-ভৈরব-শের আলিমঙ্গল পাঁড়ের উত্তরাধিকারী অসংখ্য বীরের জননী যন্ত্রণায় কাতর, রক্তাক্ত। সেই রক্তের বন্যায় কয়েক লক্ষ সংস্কৃত কলেজ ভেসে গেলে জাতিই কলঙ্কমুক্ত হতে পারতাে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা রক্ষার প্রশ্ন তুলে শুধুমাত্র একটা চিঠি দেওয়াটাকেই যারা এক মহান আদর্শরূপে গৌরবান্বিত করছেন, তাদের আদর্শবােধ নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই, বােঝা যায় ঔপনিবেশিক শিক্ষার এক বিকৃত আদর্শবােধে তারা আচ্ছন্ন, জাতির গৌরবকে ধারণ করার ক্ষমতা তাদের নেই। আরও কথা আছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিবাদ করেছিলেন। কী ধরনে প্রতিবাদ ? এই প্রতিবাদ’কেও বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি কতদূর দৌড়েছিলেন? ইতিহাস বলছে, এক পা-ও নয়। সরকারী নির্দেশে সংস্কৃত কলেজের বাড়ি ছেড়ে, অন্যত্র ঘর ভাড়া নিয়ে (সরকারী খরচে) তিনি দিব্বি কলেজ চালিয়েছেন। আর কী করেছিলেন? ১৮৫৭সালের নভেম্বর থেকে ১৮৫৮ সালের মে পর্যন্ত মাত্র ছ’মাসের মধ্যে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় দক্ষিণ বাংলার বিভিন্ন জেলায় ৩৫টিবালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, অবশ্যই তা ছিল সরকারী পরিকল্পনা। তার চাকরিতে ইস্তফা দেওয়ার সাথে সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কিত কোনাে কারণই ছিল না। বরং যা ছিল অথাৎ তৎকালীন প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের সাথে তার চিঠিপত্রের বয়ান থেকে যা উদ্ধার হয় তা হলাে মূলত দক্ষিণবঙ্গের স্কুল পরিদর্শকের পদে তাকে নিয়ােগ না করার (এই পদে নিযুক্ত হবার কোনাে দেশীয় লােকই যােগ্য বিবেচিত হতাে না) অভিমান। সেই অভিমানেই তাঁর সরকারী চাকরিতে পদত্যাগ। (ইন্দ্র মিত্র, করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, আনন্দ পাব., কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ২০৮১০)। সত্য যখন এই, তাহলে বুদ্ধিজীবীবৃন্দ কেন এই ঘটনাটিকে এমনভাবে হাজির করছেন যাতে মনে হয় যেন জাতির মান মর্যাদা রক্ষার মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি এই চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন? আসলে দায়, ঈশ্বরচন্দ্রকে জাতীয় জাগরণের কাণ্ডারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার দায়। কিন্তু ঔপনিবেশিক শিক্ষা কি এটুকু বােঝার বােধ-বুদ্ধিও যােগায় না? সম্ভবত এটাই সত্যি। তা না হলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্বদেশ প্রীতির স্তম্ভ হিসেবে তারা মেট্রোপলিটন স্কুলকে তুলে ধরেন কেন? এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : “আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষাকে স্বাধীনভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল। যিনি দরিদ্র ছিলেন তিনি দেশের প্রধান দাতা হইলেন…।” (রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড-১১, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ. ১৮১)।বিনয় ঘােষের বক্তব্য, “তিনি যে আপন বিদ্যালয়ে (অর্থাৎ মেট্রোপলিটান স্কুলে) ইংরেজ শিক্ষক বা অধ্যাপক নিযুক্ত না করিয়া এ দেশীয় শিক্ষক বা অধ্যাপক নিযুক্ত করিতেন, তাহাই তাঁহার স্বদেশিপােষকতা-প্রবৃত্তির পরিচয়। এদেশী শিক্ষক লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দিগ্বিজয়ী।” (বিনয় ঘােষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১)। ঔপনিবেশিক শিক্ষার কী অভাবনীয় পারদর্শিতা! মেট্রোপলিটান স্কুলের প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ যে আহ্লাদ প্রকাশ করেছেন, এর কী ব্যাখ্যা হতে পারে? ইংরেজরা যে এখানে এই ‘স্বাধীন চিন্তা’টারই জন্ম দিতে চেয়েছিল, অপেক্ষায় ছিল একজন ঈশ্বরচন্দ্রের ‘আর্বিভাব’-এর এটা বােঝাও কি তার পক্ষে কঠিন ছিল? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সাটক্লিফ যখন মন্তব্য করে ‘দ্য পণ্ডিত হ্যাজ ডান ওয়ান্ডার্স’ তখনও কি এটা বুঝতে বাকী থাকে যে এরকমই একটা দারুণ কিছুর জন্য তারা অপেক্ষা করছিল? এতে তারাও রীতিমতাে উল্লসিত। বিনয় ঘােষও উল্লাস প্রকাশ করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র ‘প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দিগ্বিজয়ী হয়েছেন বলে। মেট্রোপলিটান স্কুলের প্রতিষ্ঠা এবং এর ‘গৌরবজনক’ ফল যদি ইংরেজদের পরাজয় হিসাবে পরিগণিত হয়, তাহলে এটা বলতে পারি এ ধরনের একের পর এক পরাজয়ের মালা পাবার জন্য ইংরেজ উপনিবেশবাদীরা সেদিন রীতিমতাে আগ্রহী ছিল। কোনাে চোর যদি দেখে গেরস্ত তার সাথে দৌড়ের প্রতিযােগিতা শুরু করেছে এবং তাতে তাকে হারিয়ে দিয়ে ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে তাতে সেই চোরের চেয়ে আনন্দিত আর কে হবে? কারণ সে জানে এখানে পরাজয়টাই তার জয়, আর গেরস্তের জয়টাই তার পরাজয়। বৃটিশ রাজপ্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত এদেশের বুদ্ধিজীবীরা যদি জয়-পরাজয়ের যথার্থ বােধই অর্জন করতে পারবেন তবে তাে ঔপনিবেশিক শক্তি হিসাবে বৃটিশদের মূখ বলতে হয়। না, ওরা এত মূর্খ ছিল না। বিনয় ঘােষ বলেছেন, মেট্রোপলিটান স্কুলে কোনাে ইংরেজ শিক্ষক নিয়ােগ না করে দেশীয় শিক্ষক নিয়ােগ করাটা ঈশ্বরচন্দ্রের স্বদেশিপােষকতা। আগের কথাটাই আবার বলি—ইংরেজ অধ্যাপক ছাড়াই যােগ্যতার সাথে কোনাে ইংরেজি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান চালানােটা যদি স্বাদেশিকতা হয়, তাহলে এই স্বাদেশিকতাকে পুষ্ট করার জন্যই সেদিনকার ইংরেজরা এখানে প্রাণান্ত চেষ্টা চালাচ্ছিল। কারণ, এই ‘স্বাদেশিকতা’ তাদের উপনিবেশিকতাকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে তাকে আরও পুষ্ট করে তুলবে এ ব্যাপারে তাদের কোনাে সন্দেহ ছিল না। গােপাল হালদার আমাদের বুঝিয়েছিলেন, “পাশ্চাত্য সভ্যতার রূপ হ্যাট-কোটেনয়। এ কথাকে মেনে নিয়েও কী অন্য আরেকটা কথা বলা যায় না যে, চটি চাদর পরাটাই স্বাদেশিকতা নয় ? আকৃতি কখনই প্রকৃতির নির্ধারক নয়, আবার কখনােই আধেয়কে নিশ্চিতভাবে প্রকাশ করে না। কমণ্ডলুর পানীয় কখনােই এ নিশ্চয়তা দেয় না যে, তা জলই, মাদক নয়। তাই বিনয় বাবুরা যখন এধরনের উক্তি করেন, তখন কখনাে কখনাে সংশয় জাগে সত্যি সত্যিই এই ভদ্রলােকেরা স্বাদেশিকতার অর্থ বােঝেন না, না, আমাদের ভুল বােঝান? কোনাে শিক্ষার মর্ম চেতনা কী কে শেখালাে তার উপর নির্ভর করে ? না কি, কী শেখালাে তার ওপর ? এর জবাব সবারই জানা, বিনয় বাবুদেরও জানা। চটি-চাদর পরা ঈশ্বরচন্দ্রের পরিচালিত মেট্রোপলিটান স্কুলের স্বদেশী শিক্ষকরা কি ‘বর্ণপরিচয়’, ‘নীতিবােধ’, বােধেদয়’ বা ‘বাঙ্গালার ইতিহাসএর ‘পাঠ’ ভুলে শিক্ষকতা করতেন? ‘ইংরেজ-রাজাদের আমাদের পূজা করা কর্তব্য’—এই শিক্ষা কি মেট্রোপলিটান স্কুলে দেওয়া হতাে না? এরপরেও যদি মেট্রোপলিটান স্কুলকে ইংরেজি শিক্ষার স্বাধীন স্বদেশী প্রতিষ্ঠান বলে জাহির করার চেষ্টা হয়, তাহলে সেই চেষ্টা যে ঔপনিবেশিক শিক্ষাকেই জেনে বুঝে চক্রান্তমূলকভাবেস্বাধীন ও স্বদেশী শিক্ষা বলে প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয় একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।
১৮. Asok Sen, Vidyasagar and his illusive milestones, | Kolkata, Calcutta, 1987, P. 150, 154.
১৯. আন্দ্রে জি ফ্রাঙ্ক, অন ক্যাপিটালিস্ট আণ্ডার ডেভেলপমেন্ট, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, দিল্লি, ১৯৭৫।
২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর চরিত; দেখুন-বদরুদ্দীন উমর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ, চিরায়ত, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৩৪।
২১. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পত্রিকা, সংখ্যা-৬, মে ১৯৯৪, পৃ.১৯১।
২২. উৎস মানুষ, জুলাই ১৯৯০, পৃ.১৮৮-১৮৯; স্বামী বিবেকানন্দ বাণী ও রচনা, খন্ড-৯, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা; ইন্দ্র মিত্র, প্রাগুক্ত,পৃ.৭২০; শঙ্করীপ্রসাদ বস, রসসাগর বিদ্যাসাগর, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৪০।
২৩. জ্ঞানান্বেষণ, ২৫ আগস্ট ১৮৩৮; দেখুন-এস সি মৈত্র, সিলেকসনস ফ্রম জ্ঞানান্বেষণ, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃ. ১০১; অলােক রায়, আলেকজান্ডার ডাফ ও অনুগামী কয়েকজন, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ১৫।
২৪. গৌরগােবিন্দ রায়, আচাৰ্য কেশবচন্দ্র, খণ্ড-২, এলাহাবাদ, ১৯৩৮, পৃ. ৯৩৬।
২৫. প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী, চক্রবর্তী অ্যান্ড চ্যাটার্জি, কলকাতা, ১৯৭২, পৃ. ১৬৮-১৬৯।
২৬. বিহারীলাল সরকার, বিদ্যাসাগর, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ১৪০।
২৭. বিহারীলাল সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০।
২৮. সাংস্কৃতিক নষ্টামির উদাহরণ দিতে গিয়ে দেশ-বিদেশের বহু বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিত ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা মহামান্য হজরত ওমরের (৬৩৪-৪৪) উপর তৎকালীন মিশরের রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থাগার ধ্বংসের (৬৪২) অভিযােগ উত্থাপন করেন। এমনকি ১৯৫৩ সালে ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ ভ্যালেন্টাইনের শিক্ষানীতির আলােচনা প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে বক্তব্য দিয়েছিলেন তাতেও এই ধ্বংসের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। এটা ছিল একটা অপপ্রচার মাত্র। প্রচলিত যে, খলিফা হজরত ওমরের নির্দেশ মেনে তার সেনাপতি আমর ইবনুল আস (বিদ্যাসাগর যাঁকে অমরু বলে উল্লেখ করেছেন) নাকি ৬ মাস ধরে আলেকজান্দ্রিয়ার অসংখ্য স্নানাগারের অগ্নিকুন্ডে গ্রন্থাগারের মূল্যবান বই সব ফেলে ধ্বংস করেছিলেন। ইতিহাসের বিচারে এই কাহিনি সঠিক নয়। রােমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার খৃষ্টপূর্ব ৪৮ অব্দে আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার পুড়িয়ে দেন। ঐতিহাসিক আর এস ম্যাকেনসেন বলেন, সিজারের অগ্নিকান্ডের পরও গ্রন্থাগারে কিছু সংগ্রহ থাকায় পণ্ডিত ব্যক্তিরা এখানে যাতায়াত করতেন। কিন্তু ২১৬ সালে রােমান সম্রাট কারাকাল (১৮৬-২১৭) এটি বন্ধ করে দেন। পরে ২৭৩ সালে রােম সম্রাট অরােলিয়াম (২২২২৭৫) গ্রন্থাগারটি পুরােপুরি ধ্বংস করে দেন। (ব্যাকগ্রাউণ্ড অফ দ্য হিস্টরি অফ মুসলিম লাইব্রেরিজ, আমেরিকান জার্নাল অফ সেমিটিক ল্যাঙ্গুয়েজ, ১৯৩৫, পৃ. ১১৯)। । পরে আবার এখানে ‘দুহিতা লাইব্রেরী’ নামে একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। ৩৮৯ সালে রােম সম্রাট থিওডােসিয়াসের ইন্ধনে এই গ্রন্থাগারও ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এরপর আরবীয়রা যখন ৬৪২-এ আলেকজান্দ্রিয়া দখল করেন সেখানে তখন কোনও গ্রন্থাগার ছিলই না। সমকালীন কোনও লেখক কিন্তু আমর কিংবা হজরত ওমরের বিরুদ্ধে গ্রন্থাগার ধ্বংসের অভিযােগ তােলেননি। প্রায় ৬০০ বছর পর আল বাগদাদীই (মৃত্যু ১২৩১) সম্ভবত আজগুবি কাহিনি রটান। (আল বাগদাদী, আল ইফাদা ওয়াল ইতিবার, সম্পাদনা ও ল্যাটিন অনুবাদ, জে হােয়াইট, অক্সফোর্ড, ১৮০০, পৃ.১১৪)। অবশ্য কেন তিনি এমন প্রচার করেন তা জানা যায়নি। তবে তাঁর বক্তব্য পরবর্তীকালে লেখকরা অতিরঞ্জিত করেছেন। (পি কে হিট্টি, হিস্টরি অফ দ্য আরবস, বাংলা অনুবাদ, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১৮৪)। পি কে হিট্টি বলেন, আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ধ্বংসের গল্পটি কাহিনি হিসেবে চমৎকার, তবে এর ঐতিহাসিক মূল্য কিছুই নাই। (হিট্টি, দ্য আরবস: এ শর্ট হিস্টরি, বাংলা অনুবাদ, অবসর, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৩৬)। উইলিয়াম মূরও তার ‘দ্য খালিফেট’ গ্রন্থে (এডিনবার্গ, ১৯২৪) এই কাহিনিকে কাল্পনিক বলে অভিহিত করেছেন। মুসলমানগণ কর্তৃক আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার পােড়ানাে যে ভ্রান্ত এবং খ্রিস্টানরাই যে এই কাজ করেছিল, বিশ্ব ইতিহাসের দ্রষ্টা হিসেবে স্বামী বিবেকানন্দ অবহিত ছিলেন। তিনি বলেছিলেন: “এই মিশরেই সে আলেকজান্দ্রিয়া নগর, সেখানকার বিদ্যালয়, পুস্তকাগার, বিদ্বজ্জন জগৎ প্রসিদ্ধ হয়েছিল। সে আলেকজান্দ্রিয়া মূখ গোঁড়া-ইতর ক্রিশ্চানদের হাতে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেল, পুস্তকালয় ভস্মরাশি হল, বিদ্যার সর্বনাশ হল।” (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, খণ্ড-৬, পৃ. ৯৭)।
২৯. বাসন্তী চক্রবর্তী সম্পাদিত, কৃষ্ণকুমার মিত্র : আত্মচরিত, কলকাতা, ১৯৩৭, পৃ. ৬৮।
৩০. চারণ, বর্ষ-১, অক্টোবর ১৯৯৪, পৃ. ৭১-৮৬।
৩১. রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৫২, পৃ.
৩২. দ্য সিটিজেন, ২ মে ১৮৫৩।
৩৩. দ্য সিটিজেন, ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৫৫।
৩৪. নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।/পঞ্চস্বপৎসু নারীণাং পতির নৌ বিধীয়তে।। (পরাশর সংহিতা, ৪: ৩০) অর্থাৎ স্বামী নিরুদ্দেশ হলে কিংবা মারা গেলে অথবা সন্ন্যাস গ্রহণ করলে অথবা পুরুষত্বহীন হলে কিংবা সমাজচ্যুত হলে— এই পাঁচ প্রকার বিপত্তিতে স্ত্রীদের অন্য পতিগ্রহণ বিধিসম্মত)।
৩৫. সংবাদ প্রভাকর, ৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৫৫।
৩৬. দ্য সিটিজেন, ৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৫৫।
৩৭. স্বপন বসু, বাংলার নবচেতনার ইতিহাস,পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০০, পৃ.২৬০।
৩৮. তত্ত্ববােধিনী, অগ্রহায়ণ ১৭৭৭ শক, পৃ. ১০৪।
৩৯. চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, কলকাতা, ১৩৭৬, পৃ.২১৬।
৪০. সংবাদ প্রভাকর, ৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৫৫ ও ৯ ফেব্রুয়ারী ১৮৫৫।
৪১. সংবাদ প্রভাকর, ৭মার্চ ১৮৫৫।
৪২. সংবাদ প্রভাকর, ১ ভাদ্র ১২৬৩।
৪৩. বিহারীলাল সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩।
৪৪. বিনয় ঘােষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।
৪৫. বিনয় ঘােষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০।
৪৬. সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ১০ মে ১৮৫৯।
৪৭. বিনয় ঘােষ, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, তৃতীয় খন্ড, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৯৬৪, পৃ. ৩৭৭।।
৪৮. হারানচন্দ্র রক্ষিত, ভিক্টোরীয় যুগে বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃ.২১৩।
৪৯. চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, কলকাতা, ১৩৭৬, পৃ. ২৪৫।
৫০. উদ্ধৃত-বদরুদ্দীন উমর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ, চিরায়ত, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৬৪।
৫১. বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।
৫২. রামগতি ন্যায়রত্ন, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, কলকাতা, ১৯৫৬, পৃ. ২০৪।

 নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা
নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা




