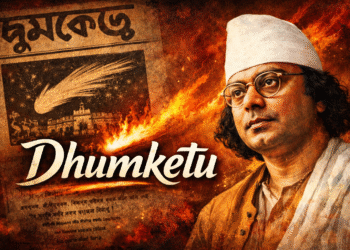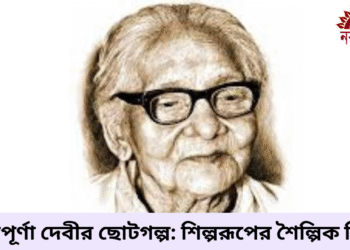লিখেছেনঃ কুন্তল চট্টোপাধ্যায়
‘পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন’, অধিকাংশ কবিতাপ্রেমী বাঙালির প্রেম ও কবিতার প্রথম পাঠ শুরু হয় জীবনানন্দ দাশ-এর প্রবাদ-প্রতিম এই লাইনটি দিয়ে। জীবনানন্দের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘বনলতা সেন’ (১৯৪২)-এর নাম-কবিতার রহস্যময়ী নিসর্গ-নারীর উত্তোলিত দৃষ্টির এই গভীর রোমান্টিক উপমা রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা প্রেমের কবিতার এক স্মরণীয় স্বাক্ষর-পংক্তি। প্রাচীন বিদিশা নগরীর রাত্রির মতো অপার কৃষ্ণকেশদাম আর শ্রাবস্তীর কারুকার্যমণ্ডিত মুখশ্রী নিয়ে প্রকৃতির শান্ত সৌন্দর্যের এক অপূর্ব লাবণ্য সঞ্চার করেছিলো নাটোর-দুহিতা বনলতা। ইতিহাসের দূরবিস্তারী পটপ্রেক্ষায় আভাসিত হয়েছিলো এক আশ্চর্য নারীপ্রতিমা, স্থান-কালের বস্তুসীমা অতিক্রম করে যে নারী বহন করে এনেছিলো দূরাভিসারী রোমান্টিক মর্মময়তা, যে নারী লৌকিক প্রাত্যহিকতা পেরিয়ে হয়ে উঠেছিলো প্রেম ও প্রকৃতি, শ্রেয় আশ্রয় ও প্রেয় অন্বিষ্টের প্রতীক। কিন্তু এসব কথা বলার পরেও দা ভিঞ্চির মোনালিসা ও তার দুয়ে হাসির মতো জীবনানন্দের বনলতা ও তাকে নিয়ে লেখা কবিতা বিষয়ে অনেক জিজ্ঞাসাই হয়তো অমীমাংসিত থেকে যাবে।

প্রতিটি ছ’লাইনের তিনটি স্তবকে বিভক্ত মোট আঠারো লাইনের এই কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো বুদ্ধদেব বসুর ‘কবিতা’ পত্রিকায়, ১৯৩৫-এর ডিসেম্বর মাসে। এর সাত বছর বাদে জীবনানন্দের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতা হিসাবে এটি সংকলিত হয়। জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায় যে কবিতাটির সম্ভাব্য রচনাকাল ১৯৩৪ যখন কবি তাঁর বিবাহোত্তর জীবনে কলকাতাবাসী, কর্মচ্যুত। তবে ‘বনলতা সেন’ নামটি এসেছিলো তারও দু’বছর আগে লেখা আত্মজৈবনিক আখ্যান ‘কারুবাসনায়, যদিও সে-কাহিনি আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয়েছিলো অর্ধ-শতাব্দীকাল পেরিয়ে, কবির মৃত্যুরও অনেক বছর পরে। নামটি ফিরে এসেছিলো তাঁর অন্য আরও তিনটি কবিতায়। মনে করা যেতে পারে যে বনলতা সেন নাম্নী নারীর স্মৃতি ও তার নারীসত্তার প্রতি কবির আকুতির কোনো এক ধারাবাহিকতা ও পুনরাবৃত্তি আছে। আবার অন্যসূত্রে এও জানা যায় একবার জীবনানন্দ অশোক মিত্রকে বলেছিলেন যে ‘বনলতা সেন’ নামে রাজশাহীর জেলে আটক এক রাজবন্দীর খবর পত্রিকায় পড়ে নামটির ব্যাপারে তিনি আগ্রহী হয়েছিলেন (সূত্র বনলতা সেন : গণিকা, প্ৰেমিকা নাকি এক অচেনা নারী? / ছয়শো একর, chhoyshoacre.com/Blog/Article/5e85eb19f- c7be2c66d1d1854)। এতদসত্ত্বেও পুংনাম হিসাবে কবিতায় ‘বনলতা সেন’ নামটির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায় এবং ‘বনলতা সেন’ পুরুষ বলে গৃহীত হলে সমলৈঙ্গিক প্রেমসম্পর্কের প্রেক্ষিতে এ-কবিতার এক ভিন্নতর পাঠের প্রস্তুতি নিতে হয় পাঠককে।
যুগ যুগান্ত পার হয়ে সহস্রাব্দের পথযাত্রী কবি কবিতার প্রথম লাইনেই উত্তম পুরুষ মুখচ্ছদ ‘আমি’তে নিজেকে চিহ্নিত করেন অতীতচারী দূরগামীতায়, যেন সময়-যানে চড়ে বসা স্মৃতিতাড়িত এক পথিকের ভূমিকায়—’হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে।’ শুরু থেকেই এ যেন এক জাতিয়ার কথকের বয়ান যার ভাষায় গায়ে লেগে থাকে গুরুচণ্ডালির ধুলো। ‘হাজার বছর’ যেন অসীমের দিকে এক ক্রম সম্প্রসারণশীল ঘটমানতার সূচক, আবার এক অনাদি অতীতের অঙ্কুর প্রহরে ফিরে দেখার সংকেতও বটে। সৃষ্টির শুরুর পুরাঘটিত অতীত থেকে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে নিরন্তর ও সদা-জায়মান পথ চলার এই দ্বিমাত্রিক ঘটমান বর্তমানকে ইঙ্গিত করতেই কি ‘পরে’ ও ‘হাঁটিতেছি’-র গুরুচণ্ডালি? ঘটমান বর্তমান ক্রিয়াপদের সাধুরীতির প্রাচীনত্ব ও ‘পথ’ শব্দটির পুনঃপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে হাজার বছরব্যাপী যাত্রার ইতিহাস-ভূমি যেন আভাসিত হয় — সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে / অনেক ঘুরেছি আমি।’ এছাড়াও কবিতার কথক পরিক্রমা করেছিলো মগধরাজ বিম্বিসার ও মৌর্যসম্রাট অশোকের ধূসর জগতে’। বিম্বিসার ও অশোকের জগৎ কি কালের নিয়মে ম্লান ও মৃত বলে ‘ধূসর’? নাকি এ-দুই প্রতাপশালী নৃপতির জগৎ যুদ্ধ-হিংসা- রিরংসার কারণে স্খলন-পতন-রিপুবাসনায় তাদের আমলেও ‘ধুসর ছিলো বলা যায় ? এমনকি আরও দূরবর্তী বিদর্ভ নগরের অন্ধকারে ছিলো এ কবিতার কথকের উপস্থিতি। ‘ধূসর’ থেকে আরও বেশি কালো হলে ‘অন্ধকার’, কিন্তু মহাভারতে উল্লেখিত বিদর্ভ নগরী কি অর্থে আরও কালিমালিপ্ত ? অসামান্য রূপসী দময়ন্তী ছিলো বিদর্ভরাজ ভীমের কন্যা। দময়ন্তী বরমাল্য দিয়েছিলো নলের গলায়। কামাতুর দেবতা কলি দময়ন্তীর সংসার ধ্বংস করেছিলো আর বিদর্ভ তাই পাপের স্মৃতি-বিজড়িত এবং সে-কারণে ‘অন্ধকার’।
সাগর থেকে সাগরে, এক নগরীর ম্লানিমা থেকে আর এক নগরীর কৃষ্ণপক্ষে, রাত্রির অন্ধকারে, যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর শান্তির দুনিয়ায় দীর্ঘ ও পরিব্যাপ্ত ভ্রমণ এ-কবিতার কথককে দিয়েছিলো ক্লান্তি; আর উত্তাল জীবন-সমুদ্রের সেই ক্লান্তিময়, বিপদসংকুল অস্তিত্বে তাকে ‘দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন’। কবিতার ‘আমি’-র সঙ্গে কবি জীবনানন্দের অভেদ কল্পনা যেমন সঠিক নয়, তেমনি বনলতাও জীবনানন্দের ব্যক্তিগত পরিচয়ের সম্পর্কে ধৃত কোনো নারী (বা পুরুষ) নিশ্চয়ই নন। অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত রাজশাহী বিভাগের জেলাশহর নাটোরে কি গিয়েছিলেন কবি জীবনানন্দ? আর নাটোরই বা কেন? নাটোরে কি কোনো অভিজাত সেন পরিবারের অস্তিত্ব ছিলো? এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের অধ্যাপক-গবেষক আকবর আলি খানের বক্তব্য সঠিক হলে জীবনানন্দ তাঁর জীবদ্দশায় নাটোরে যান নি। সরকারী নথিপত্র থেকে অধ্যাপক খান জেনেছিলেন যে নাটোরে উত্তর বাংলার রূপজীবী নারীদের একটি বড়ো কেন্দ্র ছিলো। তাঁর অনুমান যে জীবনানন্দ নিছক কাকতালীয়ভাবে ‘নাটোরের বনলতা সেন’ লেখেন নি — ‘তিনি রূপজীবী হিসেবে বনলতার পরিচয় তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।’ তাঁর এও মনে হয় যে নাটোরের ঐ রূপজীবী নারীকে কবি হয়তো দেখেছিলেন কলকাতায় বা অন্যত্র (সূত্র, আন্তর্জাল পত্রিকা ‘সাপ্তাহিক’, বৰ্ষ ৮, সংখ্যা It 19, www.saptahik.com)
কবিতার এই ‘আমি’ আবহমান কাল ধরে চলতে থাকা ভ্রাম্যমান ও ভ্রমণক্লান্ত মানুষের এক উত্তমপুরুষ কণ্ঠ। পৃথিবীর নানা স্থান-কালে, ইতিহাসের স্তর-স্তরান্তরে, অস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বান্তরে চলমান মানুষের আর্কিটাইপ। অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায় যথার্থই বলেছেন, ‘এরকম করে মানুষের অস্তিত্বের ধারণা জীবনানন্দের আগে পৃথিবীর অন্য কোনও কবির মুখে শোনা যায় নি।’ অধুনা স্বাধীন দ্বীপ-রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত শ্রীলঙ্কা প্রাচীন কালের সিংহল দ্বীপ, যার ইতিহাস আনুমানিক আড়াই হাজার বছরের পুরনো। কবিতার নির্বিশেষ আবহমান ‘আমি’র ভ্রাম্যমানতার মানচিত্রে সেই ‘সিংহল সমুদ্র’-র কথা আছে। কিন্তু ‘মালয় সাগর’বলতে কোন্ সমুদ্র বুঝিয়েছেন কবি? এই নামে তো পৃথিবীর ভৌগোলিক পরিধিতে কোনো সাগর নেই। সিংহল দ্বীপের সমুদ্র থেকে কোন্ দিকে চলেছিলেন জীবনানন্দের কবিতা ‘আমি’? কবি কি তবে এখানে মালয় উপদ্বীপ সংলগ্ন সমুদ্রাংশের কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন? বিশিষ্ট জীবনানন্দ-বিশেষজ্ঞ ক্লিনটন বি সিলীর সিদ্ধান্ত এই যে এখানে কবি দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূল অর্থেই ‘মালয় সাগর’ লিখেছিলেন। তবে প্রাচীন সিংহল থেকে অতি-ভৌগোলিক ‘মালয় সাগর’ তথা মালাবার উপকূল পর্যন্ত উত্তমপুরুষ কথকের অভিযাত্রায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ’নিশীথের অন্ধকারে’। এই যাত্রা কি ছিলো নিছক ব্যবস্থাপনাগতভাবে রাত্রিকালীন ? সাধু ক্রিয়াপদ ও আবহমান ভ্রাম্যমানতার প্রাচীনত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবেই কি অতি-প্রচল সিনট্যাগম্যাটিক ‘রাত্রি’র পরিবর্তে ঈষৎ আর্কাইক এবং তুলনায় কিঞ্চিৎ রহস্যমণ্ডিত ও দূরস্থিত প্যারডিগম্যাটিক বিকল্প ‘নিশীথ’ বেছে নিয়েছিলেন জীবনানন্দ? কবিতার ভ্রমণক্লান্ত কথক উপস্থিত ছিলো ‘বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে’। লক্ষ্যণীয় যে সিংহল তথা শ্রীলঙ্কা যেমন মূলতঃ বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের দেশ, তেমনি ষষ্ঠ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মগধরাজ বিম্বিসার ছিলেন প্রাচীন বৌদ্ধ নৃপতি, তদকালীন উত্তর ভারতে যাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিলো। তৃতীয় মৌর্য সম্রাট অশোক ও চণ্ডাশোক থেকে ধর্মাশোকে রূপান্তরিত হয়েছিলেন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। তিনিও ছিলেন প্রাচীন ভারত তথা এশিয়ার অন্যত্র বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ও প্রচারক। তাই এটা বলা বোধহয় অসঙ্গত হবে না যে জীবনানন্দের উত্তমপুরুষ কথকের পরিভ্রমণের মানচিত্রটি ছিলো প্রাচীন ভারতীয় / এশিয় বৌদ্ধধর্ম-প্রধান ভূখণ্ড জুড়ে। আর এই চলমানতার খণ্ড-কাহিনিগুলি যেন জন্মজন্মান্তরের কাহিনি, অনেকটা ভগবান বুদ্ধের জাতকের গল্পমালার মতো । কিন্তু বিম্বিসার ও অশোক নামগুলি কি অন্যতর কোনো তাৎপর্য বহন করে? যদি বনলতা কোনো রূপজীবী নারীকে বোঝায়, তাহলে এটাও আমাদের মনে রাখা দরকার যে বিম্বিসার বিবাহ করেছিলেন তেমনি এক নারী, গণিকা ও নর্তকী আম্রপালিকে। আর তাদের পুত্র অজাতশত্রু ছিলেন বৌদ্ধধর্মবিদ্বেষী। অজাতশত্রুর হাতে গৃহবন্দী অবস্থায় ক্ষমতাচ্যুত বিম্বিসারের অনাহারে মৃত্যু হয়েছিলো বলে প্রকাশ। অন্যদিকে মৌর্য নৃপতি অশোক তাঁর প্রথম জীবনে ছিলেন নিষ্ঠুর যুদ্ধবাজ, কলিঙ্গ যুদ্ধে বহু মানুষের মৃত্যুতে তাঁর হৃদয়-পরিবর্তন ঘটে; তিনি প্রণত হন যুদ্ধ থেকে বুদ্ধে। ইতিহাসের এসব বিষয় জীবনানন্দ অবশ্যই জানতেন। সেক্ষেত্রে ‘ধূসর জগত’ কেবল কাল-ধূসরিত অতীতকে বোঝাচ্ছে না; অন্য এক কৌণিকতায় আরও বোঝাতে চাইছে ধর্ম-অধর্ম, সুনীতি-স্বেচ্ছাচার, বিশ্বাস-বিশ্বাসভঙ্গের মধ্যবর্তী এক অস্বচ্ছ ‘গ্রে ওয়ার্ল্ড’কে।
আরও দূরবর্তী অন্ধকার বিদর্ভ নগরে হাজার বছর ধরে পথচলা ‘আমি’র উপস্থিতিও যে বিশেষ অর্থবহ সে-কথা আগে বলেছি। অন্ধকারের পথযাত্রীর আ-সৃষ্টি চলমানতার এই মগ্ন-চেতন অধিবাস্তব নস্টালজিয়া কেবল ইতিহাস-ভূগোলের খেয়াল-খেলা হতে পারে না। মেধা-মনন-স্মৃতি-সত্তার এক ব্যতিক্রমী অভিপ্সার বয়ান লেখক জীবনানন্দের ক্ষেত্রে তো নয়ই। আর এই স্মৃতিকথনে স্থান ও কালের মায়াবী বয়ানে অন্ধকারের পৌনঃপুনিকতার কারিগরি আমাদের যার-পর-নাই তাড়িত করে—’সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে’, ‘বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে’, ‘আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে’। পৌরাণিক বিদর্ভ নগরের খ্যাতি নল-দময়ন্তীর প্রণয় ও বিবাহের আখ্যানের সূত্রে। এখানে বিদর্ভের দূরবর্তীতা হতে পারে তার পৌরাণিকতার কারণে, কিন্তু তার ‘অন্ধকার’ কেমন ও কী কারণে? এক্ষেত্রেও আকবর আলি খান তাঁর ব্যাখ্যা দিয়েছেন—’বিদর্ভ নগর হলো নলদময়ন্তীর কাহিনীর, দময়ন্তীর পিতৃভূমি। সেই বিদর্ভ নগরীর মধ্যে নলকে পছন্দ করে দময়ন্তী যখন বিয়ে করতে গেল, দেবতারা বলল যে, আমরা দময়ন্তীকে বিয়ে করব। তখন স্বয়ংবর সভায় নল আসল। এখন নলকে যাতে চিনতে না পারে অন্যান্য দেবতারা নলের মতো চেহারা নিয়ে বিয়ের আসরে বসে যায়। দেবতাদের চোখে পলক পড়ে না। মানুষের চোখে পড়ে। ওটা দেখে দময়ন্তী ঠিকই নলকে বের করল। সব দেবতারা খুশি হয়ে চলে গেল কিন্তু কলি অসন্তুষ্ট থাকল। সে বলল যে, এ বিয়ে আমি মানি না। তাদের জীবন দুর্বিষহ করার চেষ্টা করল। এই যে অন্ধকার বিদর্ভ নগর সেটার মানে কী? সেটা হলো দেবতারা যেখানে মানুষের জীবন দুর্বিষহ করছে। সেই অন্ধকারের কথা বলছেন।

সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরের দীর্ঘ পরিভ্রমণে সেই অভিযাত্রী ছিলেন ক্লান্ত এবং চারপাশের জীবনকে তিনি দেখেছিলেন আবেগার্ত অনুভবে, বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের এক অনুপ্রাস-নির্ভর দৃশ্য চিত্রকল্পে—’আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন।’ সেই ক্লান্তি ও জীবন তাড়নার উত্তাল প্রক্ষোভে তার দেখা হয়েছিলো বনলতার সঙ্গে এবং তার স্বীকারোক্তি—’আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।’ কেমন ছিলো সেই শান্তি? কেন সেই শাস্তি দীর্ঘমেয়াদী ছিলো না, ছিলো কেবল দু-দণ্ডের? বনলতা রূপজীবী নারী বলেই কি শান্তি ছিলো স্বল্পস্থায়ী? কিন্তু কোনো রূপজীবী নারীর স্বল্পমেয়াদী সাক্ষাতে কি ‘শান্তি’ পাওয়া সম্ভব? ‘শান্তি’ তো এক সুস্থিত মানসিক অবস্থা, দৈহিক সুখভোগের বিষয় তো নয়। তাহলে কিভাবে নাটোরের রূপজীবী বনলতায় প্রেয়সীর সান্নিধ্যের শান্তি খুঁজে পেয়েছিলেন জন্ম জন্মান্তরের ক্লান্ত পথযাত্রী? বনলতা সেন সম্পর্কে আকবর আলি খানের বক্তব্য নিয়ে তাই কিছু প্রশ্নচিহ্ন উঁকি দিচ্ছে।
নাটোর-দুহিতা বনলতার কালো চুল আর মুখশ্রীর সৌন্দর্য রহস্য পথযাত্রীর স্মৃতিলিখনে উচ্চারিত হয় কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের শুরুতে—’চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, / মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য।’ যে অন্ধকার প্রথম স্তবকে ঘুরে-ফিরে এসেছে, দ্বিতীয় স্তবকে বনলতার চুলে সেই অন্ধকার, প্রাচীন বিদিশা নগরীর রাত্রির অন্ধকার। আপাতগ্রাহ্যভাবে এ এক দৃশ্য চিত্রকল্প যাতে বলা হয়েছে যে বনলতার চুল রাতের অন্ধকারের মতো কালো এবং সে রাত কোনো এক সুপ্রাচীন নগর-রাত্রি। কিন্তু আকবর আলি খান মনে করেন যে জীবনানন্দ এই উপমায় কালিদাসের ‘মেঘদূত’কে নিয়ে এসেছেন। যক্ষ তার প্রেমিকার কাছে বাণী পাঠাতে গিয়ে মেঘকে বলছে যে, সে যাওয়ার সময় এই নগরীর ওপর দিয়ে, ঐ শহরের ওপর দিয়ে, নদীর ওপর দিয়ে যাবে— ইত্যাদি। বিদিশার ওপর দিয়ে যখন যাবে তখন দেখ বে সেখানে কিছু শিলাগৃহ আছে যেখানে রাত্রিবেলা গণিকারা বিভিন্ন পুরুষের দেহ মর্দন করে এবং তার গন্ধে রাত্রির বিদিশা অন্যরকম হয়ে যায়। কালিদাসের ‘বিদিশার নিশা’ হলে অবশ্যই এই উপমায় রঙের নয়, গন্ধের কথা বলেছেন জীবনানন্দ, বনলতার চুলের গন্ধ। একালের মধ্যপ্রদেশের বিদিশা জেলাশহরের কথা জীবনানন্দ বলেন নি; বলেছেন সেই কবেকার’ বিদিশার কথা, যে প্রাচীন নগরীর নৈচাগিরি উপত্যকার পরিত্যক্ত বৌদ্ধ বিহারে পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে গুহাগুলিতে রূপজীবী নারীরা অন্ধকার রাত্রিতে কামক্রীড়ায় লিপ্ত হতো পুরুষদের সঙ্গে, সুবাসিত চন্দনে চর্চিত করতো পুরুষদের দেহ। বনলতার চুলের উপমাকে যদি এভাবে ঘ্রাণের চিত্রকল্প রূপে দেখা হয় সুপ্রাচীন বিদিশার রূপজীবী নারীদের কামকলার প্রসঙ্গসূত্রে, তাহলে নাটোরের রূপজীবী নারী হিসেবে বনলতাকে তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মনে হতে পারে।
বনলতার মুখমণ্ডলে ‘শ্রাবস্তীর কারুকার্য’ দেখেছিলো কবিতার উত্তম-পুরুষ কথক। বিদিশার মতো শ্রাবস্তীও এক প্রাচীন নগরী, বুদ্ধ তথা বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। তবে কেবল প্রাচীনতার ব্যঞ্জনা অনতে কবি বোধ হয় ‘বিদিশার নিশা’ ও ‘শ্রাবস্তীর কারুকার্য লেখেন নি। এক আকর্ষক নারী-সৌন্দর্য ও নারী-মুখশ্রীর রহস্যময়তার ইঙ্গিত বহন করছে জীবনানন্দের ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ নির্দেশিত উপমা। দূর ইতিহাসের কালিকা প্রাচীনত্ব তার অন্যতম অনুষঙ্গ হলেও বুদ্ধের জীবন ও সাধনার সঙ্গে শ্রাবস্তীর দীর্ঘ ও নিবিড় সম্পর্ক এই উপমার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা এবং অবশ্যই এই কারুকার্য প্রাচীন বৌদ্ধ নগরীর দেয়াল, সৌধ, মন্দির-গাত্রে নারীমুখ সৌন্দর্যের কারুকার্য। বৌদ্ধ শিল্পকলায় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে দু’ধরনের নারীমূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। এক হলো ‘মার’ নামক এক অসুরের তিন কন্যা যারা বুদ্ধকে প্রলুব্ধ ও বিচ্যুত করতে চেয়েছিলো তাঁর বোধি অর্জনের সাধনা থেকে। আর আছে অপ্সরাদের মূর্তি যারা একইভাবে প্রেরিত হয়েছিলো বুদ্ধকে তাঁর সাধনমার্গ থেকে ভ্রষ্ট করতে। বনলতার মুখেও তাহলে কি ছিলো ‘মার’-এর কন্যা ও অপ্সরাদের মতো প্রলুব্ধকারী নারীর ছল-চাতুরি, যেমনটা থাকতে পারতো নাটোরের রূপজীবী নারীর মুখে? ‘কারুকার্য’ শব্দটিতে স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষ ছাড়াও কি রূপজীবী নারীর অতি-প্রসাধিত মুখের কোনো ব্যঞ্জনার্থ থাকতে পারে?
রূপজীবী নারী হোক বা প্রেয়সী, ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত পথযাত্রীর কাছে বনলতা সেন যেন এক দূরবর্তী আশ্রয়—’অতিদূর সমুদ্রের পর / হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা / সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর, / তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে।’ মালয় সাগরে রাত্রির অন্ধকার ছিলো; বিম্বিসার-অশোকের জগতে ছিলো অন্য এক আবছায়া, ধূসরতা; আর এক অন্ধকার ছিলো প্রাচীন বিদর্ভে; অন্ধকার ছিলো প্রাচীন বিদিশাতেও। বনলতাকেও এ পথযাত্রী দেখেছিলো অন্ধকারে, যেভাবে কোনো হালভাঙা জাহাজের দিশাহারা নাবিক দূর থেকে দেখতে পায় দারুচিনি দ্বীপের সবুজ তৃণভূমি । কেমন ও কতটা কালো ছিলো সেই অন্ধকার যাতে বনলতার রাত্রির মতো কালো চুল দেখতে পাওয়া গিয়েছিলো? দেখা গিয়েছিলো প্রাচীন শ্রাবস্তীর নারী মূর্তির মতো তার মুখের কারুকাজ ? অন্ধকারে বনলতার কণ্ঠস্বর শুনেছিলো পথযাত্রী, গোটা কবিতার ভাষ্যে মাত্র একবারই, “বলেছে সে, ‘এতদিন কোথায় ছিলেন ?” তবে কি পথযাত্রী বনলতার পূর্বপরিচিত ছিলো ? তার জন্য কি প্রতীক্ষায় ছিলো বনলতা? আকস্মিক প্রথম সাক্ষাতে কোনো অপরিচিতা তো এমন কথা বলে না । কবিতার দ্বিতীয় স্তবকটি শেষ হয় বাংলা কবিতার অন্যতম সর্বাধিক উদ্ধৃত একটি উপমা দিয়ে—’পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।’ পাখি তো অনেক রকম; তাদের নীড়ের আকৃতি ও গঠনেও রয়েছে ভিন্নতা। সব পাখির নীড় দৃষ্টিনন্দন নয়; কোনো পাখির নীড়ই ঠিক মানুষের চোখের মতো নয়। তবে পাখি যেমন দিনান্তে তার নীড়ে ফেরে বিশ্রাম ও আশ্রয়ের খোঁজে, তেমনই ক্লান্ত পথযাত্রী বনলতার চোখের দৃষ্টিতে যেন শান্ত এক আশ্রয় খুঁজে পায়। নাটোরের বনলতা যদি রূপজীবী নারীও হয়, তার দৃষ্টি নীড়ের নিরাপত্তায় যেন এক শান্ত সাহচর্যের আশ্বাস ফুটে ওঠে।
রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের কবিতাকে বলেছিলেন ‘চিত্ররূপময়’। তাঁর পাঠক মাত্রেই স্বীকার করবেন যেন ইন্দ্রিয়ময়তা, বিশেষ করে দৃষ্টি-ঘ্রাণ-স্পর্শের সংবেদনের চমকপ্রদ শব্দচিত্র জীবনানন্দের কবিতার অন্যতম কুল-লক্ষণ। আলোচ্য কবিতায় তৃতীয় তথা শেষ স্তবকের শুরুতে সেই ইন্দ্রিয়ময়তার জাদু আসন্ন সন্ধ্যার এক আচ্ছন্নতা এনে দেয় ইন্দ্রিয়ান্তরকরণ বা synaesthesia -র বাকপ্রতিমায়—’সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন (দৃষ্টি শ্রুতি) / সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল (দৃষ্টি-ঘ্রাণ-স্পর্শ)।’ পাখির নীড়ের উপমায় সন্ধ্যার আগমনী তো ছিলোই; এখন সেই সন্ধ্যার অনুভব আরও ইন্দ্রিয়ঘন হয়ে ওঠে। আসন্ন সন্ধ্যার দৃশ্যমানতা শ্রুতিগোচর হয় একটি সাইনেসথেটিক অলংকরণে ‘শিশিরের শব্দের মতন’ এই তুলনায়। আর পরপর দুটি সাইনেসথেসিয়ার প্রয়োগে দৃষ্টির অভিজ্ঞতা যেন ঘ্রাণ ও স্পর্শের ক্রম-সম্প্রসারিত সংবেদনে মর্মময় হয়ে ওঠে ‘ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল’ চিত্ররূপে। দিনের শেষে তার ডানা থেকে রোদের গন্ধ মুছে ফেলা চিলটি যেন এক অবসানের চিহ্নায়ক হয়ে ওঠে। সেই অবসানের স্বর বাচনিক উৎক্রমের কুহকে আরও রহস্য নিবিড় হয়ে ওঠে পরবর্তী দুই পংক্তিতে—’পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন / তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল।’ একদিকে দিনান্তে পৃথিবীর সব রঙ নিভে গিয়ে যেন এক চির-অন্ধকারের আবহ, আবার অন্যদিকে জোনাকির রঙে ঝিলমিল সেই অন্ধকারে জীবন-কাহিনির খসড়ার আশ্চর্য উন্মীলন যেন এক রাহসিক পুনরারম্ভ। সুদূর অতীতের অন্ধকার থেকে চলতে চলতে, স্থান থেকে স্থানান্তরে এক অন্ধকার থেকে অন্য অন্ধকারে চলতে চলতে মানুষের ঘরে ফেরা, নীড়ে ফেরা পাখিদের মতো, সাগর-সঙ্গমে ফিরে আসা নদীদের মতো, যদি অবসিত যাত্রার অন্তিম অন্ধকারে তার জন্য অপেক্ষায় থাকে এক একান্ত আপন আশ্রয়—’সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী – ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন; / থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।’ পূর্ববর্তী দুটি স্তবকেরই শেষে ‘নাটোরের বনলতা সেন’-এর উল্লেখ ছিলো। এখন কিন্তু কবিতার শেষে বনলতার নাটোরের পরিচয় আর নেই। বনলতা এখন তার নামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে এক প্রকৃতি-নারী, ক্লান্ত অস্তিত্বযাত্রী আশ্রয়-প্রতিমা। জীবনের সব দেনা-পাওনার হিসেব ফুরিয়ে গেলে নাটোরের রূপজীবী পণ্য-নারী হয়ে ওঠে বাণিজ্য-অতিক্রমী চিরসঙ্গিনী।
ছয় পংক্তির তিনটি স্তবকে ‘বনলতা সেন’ কবিতাটি নিয়মিত ও সুষম নির্মিতির দৃষ্টান্ত বলেই গণ্য হবে। প্রতিটি স্তবকের প্রথম চার পংক্তি নিয়ে একটি চৌপদী বা quatrain, যার ১ম ও ৩য় এবং ২য় ও ৪র্থ পংক্তি পরস্পরের সঙ্গে মিলযুক্ত, আর প্রতিটি স্তবক শেষ হয়েছে একটি সমিল দ্বিপদী বা rhymed couplet -এ। প্রতিটি স্তবকের চৌপদী অংশে উত্তম পুরুষ কথকের অভিযাত্রার অভিজ্ঞতা-অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে, আর সমিল দ্বিপদীতে এসেছে বনলতার স্মৃতি। অর্থাৎ ভাববস্তুর চলনের সঙ্গে কারিগরি বিন্যাসের সুশৃঙ্খল বোঝাপড়া রয়েছে। ব্যঞ্জনা-অনুযঙ্গ-প্রসঙ্গ জীবনদৃষ্টির নানা বহুমাত্রিকতা সত্ত্বেও ‘বনলতা সেন’ প্রেমেরই কবিতা, যেমনটি সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে। প্রতিটি স্তবকের শেষে এবং কবিতার অন্তিম দ্বিপদীতে রয়েছে বনলতার প্রতি প্রেমকাতরতা। কিন্তু পাশাপাশি এটাও ঠিক যে জীবনানন্দ সেই কাতরতা অতিক্রম করেছেন। তাঁর বোধিতে প্রোথিত সময় তথা ইতিহাস চেতনার গাঢ় সংশ্লেষে ‘বনলতা সেন’হয়ে উঠেছে আবহমান মানুষের ক্লান্তিকর অস্তিত্বের প্রশ্ন নিয়ে রচিত এক আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসা। ‘কবিতার কথা’ প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, ‘কবির হৃদয়ে থাকবে কল্পনা এবং কল্পনার অভ্যন্তরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা’। কোনো এক রূপসী বনলতা সেন-এর স্মৃতি তাঁকে তাড়িত করলেও এ-কবিতায় কবির পার্সোনা—উত্তম পুরুষ কথক—জীবন ও জীবিকার অন্বেষায় ক্লান্ত নিরুদ্দেশ অস্তিত্বের মধ্যে কল্পনা করেছে মানুষের গভীর আর্তি, আত্মস্থ করতে চেয়েছে আদি মানবের অনুভব।
১৮৩১-এ তাঁর কাব্যসংকলনে প্রকাশিত এডগার অ্যালান পো’র কবিতা ‘টু হেলেন’-এর সঙ্গে জীবনানন্দের কবিতার সাদৃশ্যের কথা বলা হয়ে থাকে। দুটি কবিতারই কেন্দ্রে কোনো এক নারী এবং তাকে নিয়ে কবির কল্পনা হয়তো সেই সাদৃশ্য ইঙ্গিত করে। তবে ট্রয়ের হেলেন যেমন বিশ্ববন্দিত কিংবদন্তী নারী, নাটোরের বনলতা তেমন নয়। এছাড়া পো’র কবিতায় হেলেনের অপার সৌন্দর্য এবং সেই সৌন্দর্যের স্তুতি যেমন কবিতার একমাত্র বিষয়, জীবনানন্দের কবিতায় তেমন নয়; জীবনানন্দের কবিতায় সুপ্রাচীন কাল থেকে মানুষের অর্থহীন অস্তিত্বযাপনের ক্লান্তি ও উদ্বেগের ইতিহাসে বনলতা এক ক্ষণিকলভ্য দূরস্থিত মায়াবী উল্লেখ হয়ে পথযাত্রীকে শান্তি ও আশ্রয়ের সান্ত্বনা দেয় ৷
- [লেখক পরিচিতি : সহযোগী অধ্যাপক, নরসিংহ দত্ত কলজে। অতিথি অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রকাশিত গ্রন্থ : সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ’ প্রভৃতি।]
‘নবজাগরণ’ এর টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।
‘নবজাগরণ’ এর ফেসবুক পেজে লাইক করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

 নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা
নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা