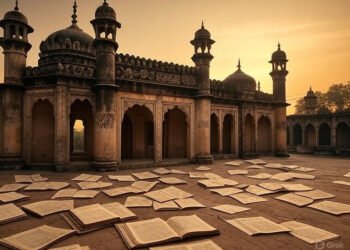আধুনিককালের প্রগতি ভাবনা সম্পর্কে আমাদের সবারই কমবেশি ধারণা রয়েছে। কাজেই বিস্তারিত আলােচনার প্রয়ােজন নেই। রাজা রামমােহন রায়ই (১৭৭৪-১৮৩৩) উনিশ শতকের গােড়ায় গােটা ভারতে নতুন যুগের প্রবর্তক, প্রথম প্রগতিবাদী মানুষ। তার ব্যক্তিত্ত্ব ও বৈষয়িক জীবনে নানা অসংগতি থাকলেও বিদ্যায়-বিত্তে-জ্ঞানে-প্রজ্ঞায় তিনি তাঁর সমকালের প্রথম সারির যে কোনাে প্রাগ্রসর চিন্তাসম্পন্ন ইউরােপীয় নাগরিকের সমকক্ষ ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে নবযুগের উদ্গাতা, দূরদর্শী ও বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাবিদ। প্রগতিশীল যুক্তিবাদের আরও প্রসার ঘটে লুই ভিভিয়ান ডিরােজিওর (১৮০৯-১৮৩১) প্রভাবে ও প্রচারে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে। শাস্ত্রিক সামাজিক লৌকিক বিধাসসংস্কার থেকে মুক্তি ছিল তাদের জীবনে নবলব্ধ যুক্তিবাদের অবদান। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯) প্রগতিশীলতা আমরা খুব একটা স্বীকার করি না বটে, কিন্তু তিনিই প্রথম বুঝেছিলেন যে, সাহিত্য বিনােদনের বস্তু নয়, জাতীয় জীবনবিকাশের ভিত্তি ও অবলম্বনও। এরপর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) যুক্তিনির্ভর জ্ঞানমনস্কতা, যা তাঁর প্রগতিশীলতার এবং পাশ্চাত্য প্রভাবিত প্রাগ্রসর চিন্তাভাবনারই উজ্জ্বল নিদর্শন। বিদ্যাসাগরেরই সমবয়সী অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) ছিলেন আর একজন জিজ্ঞাসুদ্রোহী। ২০১১ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্ম সার্ধশতবর্ষে চাপা পড়ে গিয়েছিল প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সার্ধশতবার্ষিকী। এই ধারাবাহিকতাতেই আবার নিঃশব্দে এসে গেল ২০২০ সাল। চিরবরণীয় ঈশ্বরচন্দ্রকে স্মরণ করতে গিয়ে আমরা যেন বিস্মৃত হলাম অক্ষয়কুমারকে। ১৫ জুলাই তার জন্মের দুইশত বছর অতিক্রান্ত। পরিতাপের বিষয়, কোথাও তিনি তেমনভাবে আলােচিত হলেন না! বহু লিটলম্যাগ-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নিয়ে ঢাউস সব সংখ্যা করলেন, সেখানে অক্ষয়কুমার দত্ত যেন ব্রাত্যই থেকে গেলেন। ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত অবশ্য কিছু রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আশীষ লাহিড়ী (‘অক্ষয়কুমার দত্ত আঁধার রাতে একলা পথিক’) ও ডা. শঙ্করকুমার নাথ (অক্ষয়কুমার দত্ত বিজ্ঞান ভাবনার পথিকৃৎ) অবশ্য গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু এই সামান্য আলােচনা বুঝি তার প্রাপ্য ছিল? শুধু মননচর্চার ভারবাহী বাংলা ভাষার গদ্যশিল্পী নন তিনি, উনিশ শতকের জ্ঞানবিচার প্রবাহে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের আধুনিক পুনর্মূল্যায়নে তিনি সম্ভবত সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন। তার যুক্তিনিষ্ঠা, বিজ্ঞানচেতনা ও ধর্ম-নিরপেক্ষ ভাবনা তাকে উনিশ শতকের একজন বিশিষ্ট চিন্তকরূপে চিহ্নিত রেখেছে, যদিও তার নাম আজকাল কমই উচ্চারিত হয়। বাংলা গদ্যের উৎকর্ষ সাধনে তার দান বিদ্যাসাগরের চেয়ে কম নয়, কিন্তু তিনি সে খ্যাতি থেকে বঞ্চিতপ্রায়। তিনি ইংরেজি, সংস্কৃত ছাড়াও জানতেন গ্রিক, ল্যাটিন, হিব্রু। মধুসূদন ও অক্ষয়কুমার দত্তই ছিলেন সেকালের প্রখ্যাত বহুভাষাবিদ। অক্ষয়কুমারের উপর কোতে, মিল ও স্পেনসারের দার্শনিক মতবাদের প্রভাব ছিল। যুক্তি ও তথ্য-নিষ্ঠা অক্ষয়কুমারকে তার স্বকালে প্রগতি ও আধুনিক চিন্তার প্রতিভু করে তুলেছিল। এমন এক অগ্রগামী চিন্তার পােষককে ভুলে থাকা বুঝি বঙ্গীয় সমাজের বিস্মৃতিপরায়ণতাকেই প্রমাণ করে।

শৈশবে অক্ষয়কুমার দত্ত গ্রামের পাঠশালায় গুরুচরণ সরকারের কাছে চার বছর লেখাপড়া শিখেছিলেন। ফারসি শিখতেন মুন্সি আমিরুদ্দিনের কাছে, সংস্কৃত পড়তেন গােপীনাথ তর্কালঙ্কারের টোলে। দশ বছর বয়সে পিতা পীতাম্বর দত্ত তাকে উচ্চশিক্ষার জন্য বর্ধমানের চুপীগ্রাম থেকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। প্রথমে অক্ষয়কুমার মিঃ জে নামধারী এক ব্যক্তির কাছে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু তার পড়ানাের ধরন পছন্দ না হওয়ায় পরে মিশনারী পাদ্রিদের কাছে যান। মিশনারীদের প্রভাব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পিতা তাঁকে খিদিরপুরের (পিতার কর্মস্থল) ওরিয়েন্টাল সেমিনারী স্কুলে ভর্তি করেন। তখন ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর অধ্যক্ষ ছিলেন মিঃ হার্ডম্যান জেফরয়। এই স্কুলে বছর তিনেক পড়বার পর পিতা পীতাম্বর দত্তের মৃত্যু ও দারিদ্র্যবশত (১৮-১৯ বছর বয়সে) তিনি প্রথাগত শিক্ষা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু তার জ্ঞানার্জনের চেষ্টা সারাজীবনই অব্যাহত ছিল।
জ্ঞানচর্চার স্বরূপ
অক্ষয়কুমার দত্ত ছাত্রজীবনেই ভূগােল, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণােমিতি, কনিক সেকশন, ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব এবং নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে গভীরজ্ঞান আহরণ করেন। ১৯৪০ সালে ‘সংবাদ প্রভাকর’-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে এবং দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ‘তত্ত্ববােধিনী-সভা’র (১৮৩৯) সদস্য হন। অক্ষয়কুমার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে নানা আলােচনায় অংশগ্রহণ করতে থাকেন। একদা ‘তত্ত্ববােধিনী’ পাঠশালায় অক্ষয়কুমার শিক্ষক নিযুক্ত হন। পদার্থবিজ্ঞান ও ভূগােল পড়াতেন। এই পাঠশালার পাঠ্যরূপে তাঁর ‘বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার’ নির্বাচিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ পৃষ্ঠপােষিত ‘তত্ত্ববােধিনী পত্রিকা’ (১৮৪৩) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয়কুমারের প্রতিভা নিজের স্বতন্ত্র পথ খুঁজে নেয়। তার প্রতিভার বিকাশও ঘটে এ পত্রিকার মারফৎ। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের পাশাপাশি এখানে বিজ্ঞান, সমাজ, দর্শন, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও অন্যান্য বিষয়ে নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বরে তিনি উক্ত পত্রিকার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। পাঁচজন সদস্য নিয়ে এই পত্রিকা পরিচালনা করার জন্য একটি সমিতি গঠন করা হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত এঁদের একজন ছিলেন। এই সূত্রে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ তৎকালীন বিখ্যাত মনীষীদের সংস্পর্শে আসেন। দীর্ঘ বারাে বছর সেই পত্রিকা সম্পাদনা করে একটি ধর্মীয় গােষ্ঠীগত মুখপত্রকে প্রায় একক উদ্যোগে অক্ষয়কুমার করে তুললেন সেকালের এক বিশিষ্ট সাময়িকপত্রে। সেখানে নাগরিক মানুষের কাছে সম্পাদকীয় স্তম্ভে তিনি অবগত করলেন পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থার কথা (১৮৫০)। পরে কর্তৃপথের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেন। নকুড়চন্দ্র বিধাস লিখেছেন “পীড়া ও অন্য কোন কারণবশত অক্ষয়বাবু তখন তত্ত্ববােধিনী পত্রিকা ও ব্রাহ্মসমাজের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণেচ্ছু হন।”১ এই অন্য কোনাে কারণটি কী তা অনুমান করতে খুব কষ্ট হয় না। তবু, অক্ষয়কুমার চলে গেলেন, না তাকে তাড়ানাে হল, সে বিতর্কে না ঢুকে এটুকু অন্তত আমরা বলতে পারি, অক্ষয়কুমারের বিজ্ঞানচেতনার সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মবােধের যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, সেটি ছিল অত্যন্ত প্রবল। ওইরকম দ্বন্দ্ব নিয়ে কোনাে প্রতিষ্ঠানে কারও পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়, বিশেষত যেখানে এক পক্ষ হলেন মালিক, অন্যপক্ষ বেতনভুক্ত কর্মচারী। অতএব অক্ষয়কুমার ১৮৫৫ সালে উক্ত পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব থেকে সরে আসেন।

অক্ষয়কুমারের জ্ঞানস্পৃহা ছিল অদম্য। কঠিন শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হয়েও বিজ্ঞান বিষয়ক পড়াশােনা অব্যাহত রাখলেন আর বিদেশি ভাষায় শিক্ষার্জন করে দেশিয় ভাষায় তা প্রকাশ করলেন প্রথম থেকেই। অক্ষয়কুমার রচিত গ্রন্থগুলিতে একদিকে যেমন ঘটেছে তার বহুমুখী পাণ্ডিত্যের প্রকাশ, অন্যদিকে তেমনি প্রকাশ পেয়েছে তার মূলত জ্ঞানবিচারী চিন্তাভাবনা। তার রচিত বিদগ্ধ রচনাগুলি যেমন- ‘ভূগােল’ (১৮৪১), ‘বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার’ (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫১ ও ১৮৫৩), ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়’ (দুই খণ্ড ১৮৭০ ও ১৮৮৩), পদার্থবিদ্যা (১৮৫৬), ধৰ্ম্মনীতি’ (১৮৫৪), ‘চণ্ডিপাঠ’ (১-৩ ভাগ ১৮৫৩-১৮৫৯), ‘প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার’ (১৯০১) ইত্যাদি সমালােচকদের প্রশংসা অর্জন করে।
১৮৪১ সালটি হল বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সাহিত্য রচনার একটি মাইলফলক। কেননা, এই বছরেই প্রকাশিত হল অক্ষয়কুমার দত্তের লেখা বই ‘ভূগােল’। বাংলা ভাষায় এই প্রথম একটি বিজ্ঞান সংক্রান্ত বই লেখা হল, যা সাধারণ মানুষের কাছে বেশ সহজবােধ্য হল। অক্ষয়কুমারের আগে যাঁরা লিখেছিলেন, সেগুলির সবই প্রায় ভাষার জটিলতাদোষে দুষ্ট ছিল, খানিকটা দুর্বোধ্য ছিল এবং অযথা তথ্যে ঠাসা ছিল, যার অধিকাংশই কৃত্রিমতায় পর্যবসিত ছিল। অক্ষয়কুমারই প্রথম, যিনি ইয়ােরােপীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে আমাদের মতাে করে বাংলা ভাষায় সাজিয়ে গুছিয়ে পরিবেশন করলেন তার ‘ভূগােল’ গ্রন্থের মাধ্যমে। ইংল্যাণ্ড থেকে প্রকাশিত বেশ কিছু ইংরেজিতে লেখা ভূগােল সংক্রান্ত গ্রন্থ থেকেই অক্ষয়কুমার তাঁর রসদ সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর কৃতিত্ব এই যে, তিনি বিজ্ঞান সংক্রান্ত যত লেখা লিখেছিলেন তা কিন্তু অনুবাদ নয়, অনুকরণও নয়, অনুসরণ করেছেন মাত্র, নিজের ভাবনা-চিন্তা, অধিগতবিদ্যা, মেধা দিয়ে লেখাগুলি আমাদের উপহার দিয়েছেন।
‘পদার্থবিদ্যা’ এই শিরােনামে পদার্থবিজ্ঞানের আলােচনা শুরু করলেন অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববােধিনী পত্রিকায় ১৭৬৯ শকের আষাঢ় সংখ্যা (৫৪ সংখ্যা) থেকে ধারাবাহিকভাবে। প্রথম পর্বে ‘জ্যোতিষ’ শিরােনামে শুরু হয়েছে এই ধারাবাহিক। শুরুর দিকে অক্ষয়কুমার একটি পাদটীকায় লিখেছেন,
“ইহা বলাবাহুল্য যে ইংরাজি গ্রন্থ হইতে এই যৎকিঞ্চিৎ পদার্থবিদ্যা সংগ্রহ করা যাইতেছে। যদিও পূর্বকালে এদেশে জ্যোতি আদিয় বাহুল্য আলােচনা ছিল, কিন্তু ধর্মশাস্ত্রের ন্যায় অন্য অন্য শাস্ত্রকেও অখণ্ডরূপে প্রামাণ্য করিয়া তাহার চর্চা পরিত্যাগ করাতে এইক্ষণে তাহা লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। সংস্কৃত গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে তাহাই সত্য, মনুষ্যের দ্বারা তাহার আর উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই, এ সংস্কার এদেশীয় লােকের অতি অল্পকাল জন্মিয়াছে। জ্যোতিৰ্বেৰ্তা ভাস্করাচাৰ্য্য যিনি ৭০০ বৎসর মাত্ৰ পূৰ্ব্বে বর্তমান ছিলেন, তঁাহার কৃত গােলাধ্যায়ের বাসনাভাষ্যে লিখিয়াছেন যে জ্যোতি আদি বিদ্যা বিষয়ে কোন শাস্ত্রবাক্য অভ্রান্ত রূপে মানা হয় না, ইহা সিদ্ধান্ত অপেক্ষা করে, এবং মনুষ্যের দ্বারা চিরকাল শােষিত ও উন্নত হইতে পারে।”
এরপর একে একে এল জড় ও জড়ের গুণ’, ‘চৌম্বকাকর্ষণ’, ‘বাষ্পীভবন’, ‘ঘনীভবন’, ‘কাঠিন্য’, ‘স্থিতিস্থাপকতা, ‘ঘাতসহত্ব’, ‘ভঙ্গপ্রবণতা’, ‘ভিদাবরােধকতা’, ‘ভাসুরতাপাদন’, ‘তান্তবতা’, ‘সান্তরতা’, ‘বিস্তাৰ্য্যতা’, ‘সঙ্কোচ্যতা’, ‘গতির নিয়ম’, ‘বিবৃদ্ধগতি’, ‘মাধ্যাকর্ষণ’, ‘ভারকেন্দ্র’, ‘পেণ্ডুলাম’ ইত্যাদি নানান বিষয়। সত্যি বলতে কি বাংলা ভাষায় এমনভাবে বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্বগুলিকে আলােচনা করা হয়েছে, যা আগে দেখা যায়নি। ফলে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা শক্তিশালী হল অক্ষয়কুমারের স্পর্শে। এইসব লেখাই সংশােধিত আকারে ‘পদার্থবিদ্যা’ নামে ১৮৫৬ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল। বাংলায় লেখা পদার্থবিজ্ঞানের এই বইটির (১৫৪ পৃষ্ঠার বই) ভূমিকায় অক্ষয়কুমার লিখেছেন,
“এই পুস্তক মুদ্রিত হইবার সময়ে শ্ৰীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অমৃতলাল মিত্র মহাশয়েরা অনুগ্রহ পূর্বক দেখিয়া দিয়াছেন।”
‘বাহ্যবস্তু’ ও ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়’ জর্জ কম্ব এবং উইলসন-এর রচনার অনুবাদ। কিন্তু শেষােক্ত গ্রন্থটিতে অক্ষয়কুমার অনেক নতুন মূল্যবান তথ্য ও পরিসংখ্যাণ যােগ করেছিলেন। বাংলায় বিজ্ঞানভিত্তিক রচনার উপযােগী নতুন পরিভাষা সৃষ্টি করে তিনি বাংলা ভাষায় নিজের অবদান রেখেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,
“বাংলা গদ্য-সাহিত্যের প্রথম যুগে যে দুই জন শিল্পীর সাধনায় বাংলা ভাষা সাহিত্যরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহাদের একজন ঈর্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অন্যজন অক্ষয়কুমার দত্ত। ঈর্বরচন্দ্র সংস্কৃত, হিন্দী ও ইংরেজী সাহিত্য-পুস্তককে আদর্শ করিয়া যে কার্য করিয়াছিলেন, অক্ষয়কুমার ইংরেজী বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থের আদর্শে ঠিক সেই কাৰ্যই সাধিত করিয়া গিয়াছেন। ..যতদিন বাংলা ভাষা জীবিত থাকিবে ততদিন ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমারকে স্মরণ রাখিতে হইবে।”
এই বিশ্লেষণের মধ্যে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের ভূমিকায় নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিখুঁতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অক্ষয়কুমারের গদ্যের সবচেয়ে বড় গুণ হল বক্তব্যের স্পষ্টতা ও যুক্তিবাদিতা। ওই গুণে তাঁর গদ্য এখনাে আদরণীয়। উদাহরণ স্বরূপ ‘বাহ্যবস্তু’র (১ম ভাগ) ‘বিজ্ঞাপন’ অর্থাৎ ভূমিকা থেকে আংশিক উদ্ধার করা যেতে পারে,
“এতদ্দেশীয় লােকে সংস্কৃত বচন শুনিলেই তাহাতে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করেন, এবং তদ্বিদ্ধ বাক্য প্রত্যয়সিদ্ধ হইলেও অবিাস করিয়া থাকেন। আমাদিগের এই বিষম কুসংস্কার মহানর্থের মূল হইয়াছে। তাহা পরিত্যাগ না করিলে কোনােত্খমেই আমাদের মঙ্গল নাই। পূৰ্ব্বে যেমন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা স্ব স্ব বুদ্ধি পরিচালন পূৰ্ব্বক জ্যোতিষাদি কয়েকটি বিদ্যার সৃষ্টি করিয়া সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ যবনাদি অন্যান্য জাতীয় পণ্ডিতেরাও স্ব স্ব ভাষায় বিবিধ বিদ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণকার ইউরােপীয় পণ্ডিতেরা আপনাদিগের অসাধারণ বুদ্ধিবলে ঐ সকল বিদ্যার যেরূপ উন্নতি করিয়াছেন, তাহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, সংস্কৃত জ্যোতিষদিকে অতি সামান্য বােধ হয়।”
অক্ষয়কুমার দত্তের এই গদ্যকে সাধু থেকে চলিতে অনুবাদ করে নিলেই স্পষ্ট হয়ে যায়, এর কাঠামাে কত মজবুত। বিশিষ্ট সমালােচক নবেন্দু সেন বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, অক্ষয়কুমারের গদ্য কীভাবে বাংলা স্বাভাবিক কথাছন্দকে অনুসরণ করেছিল।২ সুকুমার সেনের বক্তব্য “অক্ষয়কুমারই প্রথম ভারতীয় ব্যক্তি যিনি বিজ্ঞান চর্চায় ও গবেষণায় মন দিয়েছিলেন… অক্ষয়কুমার দত্তের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পূর্ণমাত্রায় বৈজ্ঞানিক এবং তার ঋজু ও পরিমিত বাক্রীতি সেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপজাত। তাঁর রচনারীতিতে লাবণ্য নাই কিন্তু দৃঢ়তা, ঋজুতা ও ব্যবহারযােগ্যতা আছে। বৈজ্ঞানিকের উপযুক্ত ভাষা অক্ষয়কুমারই বাংলায় প্রথম দেখিয়ে গেছেন।৩ সাধারণভাবে যুক্তিগ্রাহ্য গদ্য ভাষায় লিখলেও প্রয়ােজনবােধে তিনি সাহিত্যিক ভাষাও ব্যবহার করেছেন। তাঁর রচিত মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থগুলি বাংলা সাহিত্যে এক নতুন দিগন্ত উন্মােচন করে।
‘তত্ত্ববােধিনী’ পত্রিকায় নিয়মিত সচিত্র বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখে অক্ষয়কুমার বাঙালিদের বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহিত করতে থাকেন। সেইসব লেখাকেই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার সার্থক সূচনা বলা যেতে পারে। পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, মানব শরীরবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে একের পর এক তাঁর সেই রচনাগুলিতে যেমন ছিল বিষয়ের বৈচিত্র্য, তেমনই সহজ ছিল তার উপস্থাপনা। তার সেই লেখাগুলিই ক্রমশ সংকলিত হল ‘চাণ্ডিপাঠ’ নামের শিশু-কিশােরপাঠ্য বিখ্যাত পাঠ্যপুস্তকে। এই পাঠ্যপুস্তকই শৈশবে পড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।
‘তত্ত্ববােধিনী’ পত্রিকায় বিজ্ঞানের প্রায় সমস্ত বিষয়েই কিছু না কিছু আলােচনা করেছেন অক্ষয়কুমার দত্ত। এই পত্রিকায় ভূগােল বিষয়ে লেখাগুলিও যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি করে, সন্দেহ নেই। যেমন, ছবিসহ ‘বিসুবিয়স নামক আগ্নেয়গিরি’ (বৈশাখ, ১৭৭৪ শক), ‘জলপ্রপাত’ (আষাঢ়, ১৭৭৪ শক), ‘উষ্ণপ্রস্রবণ’ (আশ্বিন, ১৭৭৪ শক) ইত্যাদি লেখাগুলি এক কথায় অনবদ্য। তাঁর ভূগােল বিষয়ক লেখাগুলি আলােচনা করতে গিয়ে ডক্টর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তার ‘বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান’ গ্রন্থে লিখেছেন,
“কোনাে কোনাে রচনায় কবিত্বের পরিচয় রয়েছে। যেমন, ১৭৭৫ শকাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত জলস্তম্ভ সম্পর্কে প্রবন্ধটি। জলস্তম্ভের শােভা বর্ণনায় লেখক অক্ষয়কুমার দত্তের কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। রচনার নিদর্শন জলস্তম্ভ দেখিতে অতি আশ্চর্য্য। নভেমণ্ডলস্থ/মেঘাবলি যেন বির্বাধিপতির পৃথ্বীরূপ/প্রাসাদের পরম রমণীয় ছাদ স্বরূপ প্রতীয়মান/হয় এবং জলস্তম্ভ যেন প্রকৃত স্তম্ভ হইয়া/তাহা ধারণ করিয়া থাকে। এই যুগের তত্ত্ববােধিনীতে প্রকাশিত অন্যান্য প্রবন্ধগুলােও সুলিখিত। এই প্রসঙ্গে ১৭৭৫ শকাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত ‘জোয়ার ভাটা’ এবং ১৭৭৫ শকাব্দের আধিন সংখ্যায় প্রকাশিত হিমশিলা সম্পর্কে আলােচনা উল্লেখযােগ্য। ভূগােল বিষয়ক অধিকাংশ রচনাই পরে ‘চণ্ডিপাঠে’ সংকলিত হয়েছিল।”
‘চণ্ডিপাঠ’ ছাড়াও উনিশ শতকের মাঝামাঝি অক্ষয়কুমারের আরও দুটি প্রধান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রথমটি ‘বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার’ ও দ্বিতীয়টি ধৰ্ম্মনীতি। অনেকেই গ্রন্থ দুটিকে একই সূত্রে গ্রথিত হিসেবে দেখেছেন এবং লেখক নিজেও ‘ধৰ্ম্মনীতি’র নানা পৃষ্ঠায় তার বক্তব্যের তত্ত্বভিত্তি হিসেবে ‘বাহ্যবস্তু’র উল্লেখ করেছেন। কিন্তু গ্রন্থ দুটি পাঠ ও অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, ‘ধৰ্ম্মনীতি’ গ্রন্থে ঈর্থরের উপস্থিতি আকস্মিক সিদ্ধান্ত মাত্র, তার যুক্তিবিন্যাসে ও সিদ্ধান্তে ঈধরের অস্তিত্ব অপ্রমাণিত। সেই কারণে ‘বাহ্যবস্তু’ গ্রন্থে তার ঈর বিাসের ঘােষণায় যে দৃঢ় প্রতীতির পরিচয় পাওয়া যায় ‘ধৰ্ম্মনীতি’ গ্রন্থে তা পাওয়া যায় না।
‘বাহ্যবস্তু’র বিষয়বস্তুতে নীতিগত বিষয়ও প্রাধান্য লাভ করেছে। যেমন বিধাতার নিয়ম পালনে ব্যর্থ হলে মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কারণ ঘটে, পক্ষান্তরে তার নিয়ম পালন মানুষের মনে শান্তির কারণ হয়। কি কি নিয়ম পালনে সুখ এবং কোন্ কোন্ নিয়মের লঙ্ঘনে দুঃখ, অক্ষয়কুমার তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলােচনা করেছেন। বাহ্যবস্তুর দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপন বা ভূমিকায় অক্ষয়কুমার বলেন,
“..যে সমস্ত কাৰ্য্য আমাদের পরমপিতা পরমেশ্বরের প্রীতিকর, প্রাণ পর্যন্ত করিয়াও তাহা সাধন করা কর্তব্য। কিন্তু কোন্ কোন্ কাৰ্য্য তাহার প্রীতিকর, তাহা না জানিলে, তৎসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভাবিত নহে। বিপতি যে সকল শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিরাজ্য পালন করিতেছেন, তদনুযায়ী কাৰ্য্য করাই তাহার প্রিয় কাৰ্য্য, তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশপূৰ্ব্বক তৎসমুদয় সম্পাদন করাই আমাদের ধর্ম।”
এই তত্ত্বভিত্তির উপরে বাহ্যবস্তু প্রতিষ্ঠিত। তাই ওই বিজ্ঞাপনেই ‘একমাত্র ধর্ম’ কী তা উল্লেখ করে অক্ষয়কুমার দত্ত আরও বলেন,
“এ পর্যন্ত কত প্রকার নিয়ম অবধারিত হইয়াছে এবং কিরূপেই বা সে সকল নিয়ম শিক্ষা করিতে সমর্থ হওয়া যায় তাহা এই পুস্তকে যথাসাধ্য প্রদর্শিত হইল।”
সুতরাং এই গ্রন্থে অক্ষয়কুমার দত্ত মনে করেছেন যে, প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী কাজ করাই ধর্ম এবং এইসব নিয়ম স্বয়ং ঈশ্বর তৈরি করেছেন বলে প্রকৃতির নিয়ম মেনে চললে তবেই মানুষ সাক্ষাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী স্বকীয় কর্তব্য করতে পারবে। বিদ্যাপতির সৃষ্ট এইসব নিয়ম যে সবই মানুষের পক্ষে ‘শুভকর’ এ বিষয়ে তিনি নিঃসংশয়।
‘বাহ্যবস্তু’র তত্ত্বভিত্তির প্রসঙ্গে বলা যায় যে, সপ্তদশ শতকে নিউটনের সৌরজগৎ ও তার নিয়মাবলীর বিষয়ে আবিষ্কারের ভিত্তিতে অষ্টাদশ শতকের ইয়ােরােপে বিধসৃষ্টি ও তার সঙ্গে স্রষ্টার সম্পর্ক বিষয়ক যে মতবাদ গড়ে ওঠে, অথচ যার সঙ্গে স্বয়ং নিউটনের কোনােই সম্পর্ক ছিল না, ‘ডেইজম’ নামে প্রচলিত সেই মতাদর্শই ‘বাহ্যবস্তু’র ভাবভিত্তি। এই মত অনুযায়ী ঈধর কোনাে এক সময়ে একটি নিখুঁত ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায় এই বিজগতকে সৃষ্টি করেন, যার প্রত্যেকটি অংশ অন্য প্রত্যেক অংশের সঙ্গে সুন্দরভাবে সংযুক্ত, সমগ্র যন্ত্রটি এবং তার প্রত্যেক অংশ নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন, এবং সর্বত্র যা প্রত্যক্ষ তা হল নিয়মের শাসন। অতএব অক্ষয়কুমার দত্তের ভাষায় ‘বিরূপ অভ্রান্ত গ্রন্থই’ সাক্ষাৎ ‘ঈশ্বর প্রণীত শাস্ত্র’ যার কার্যকারণ সূত্র বা ‘নিয়ম’ সমুদায়ই মানুষের চর্চা ও অনুধ্যানের বিষয় হওয়া উচিত। অবশ্য অ(য়কুমার তার এসব রচনায় যতখানি যুক্তিবাদের পরিচয় দিয়েছেন, ততখানি সরসতা সঞ্চার করতে পারেননি।
অক্ষয়কুমার দত্তের ‘ধৰ্ম্মনীতি’ (১৮৫৬) ‘বাহ্যবস্তু’র পরিপূরক। ‘ধৰ্ম্মনীতি’ গ্রন্থে মত-বিধাসের ঘােষণার চেয়েও সমাজ-সম্পর্ক ও সমাজবদ্ধ মানুষের সামাজিক আদর্শ কি ধরনের হওয়া উচিত সে বিষয়ে জীবন-ঘনিষ্ঠ আলােচনাই প্রাধান্য পেয়েছে। স্পষ্টতই ‘ধৰ্ম্মনীতি’র মূল বিষয় কর্তব্যাকর্তব্য ও ধর্মাধর্ম থেকে দাম্পত্য জীবনের নানা প্রসঙ্গ, সন্তানপালন, ভাইবােনের পারস্পরিক সম্পর্ক, দাসদাসীর সঙ্গে আচরণ ইত্যাদি গার্হস্থ্যজীবনের যাবতীয় বিষয়। এ গ্রন্থে অক্ষয়কুমারের নীতিধর্ম ব্যাখ্যায় মানবধর্মকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এসব নীতি প্রচারে পারমার্থিক বিষয়ের আলােচনা প্রাধান্য লাভ করতে পারেনি বলেই তাঁর এই গ্রন্থে যুগধর্মের পরিচয় পরিস্ফুট। ‘ধৰ্ম্মনীতি’ পুস্তকের বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রচলিত দেশাচারের বিরুদ্ধে লেখকের যে মনােভাব প্রকাশ পেয়েছে তাতে তাঁর নির্ভীক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংস্কার-নীতির একটা মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায়। যেমন বিবাহ প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমারের বক্তব্য উনিশ শতকের শিথিত হিন্দু সমাজের একটি ক্রমবর্ধমান সঙ্কটের উপর আলােকপাত করে। উনিশ শতকে উচ্চবর্ণের হিন্দু বাঙালি সমাজে পুত্র সন্তানকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে, প্রধানত সরকারি প্রশাসনে ভারতীয়দের পক্ষে পাওয়া সম্ভব এমন উচ্চপদ প্রাপ্তির যােগ্য করে তােলার একটা চেষ্টা উত্তরােত্তর প্রবল হতে থাকে। কন্যাসন্তানকে তুলনীয় উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রয়ােজন সেকালের সমাজে ছিল না—এমনকি ঘরের বাইরে বিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত করার চেষ্টাও কার্যত অনুপস্থিত ছিল। পুত্র সন্তানরা উত্তরােত্তর কলেজী শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকলে, তাদের বিবাহের বয়স ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে, কিন্তু শিক্ষাহীন মেয়েদের বিবাহের বয়স নয়/দশ বছরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এর ফলে শিক্ষা ও বয়সের পার্থক্যহেতু দম্পতির মানসিক মিলন শুরু থেকেই ব্যাহত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা চিরস্থায়ী রূপ নেয়। উনিশ-বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে এর বহুল পরিচয় পাওয়া যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই অক্ষয়কুমারের এই খেদোতক্তির তাৎপর্য বােঝা যায় “বিদ্যাবান উদার-স্বভাব মহাশয় পুরুষের সহিত বিদ্যাহীনা, কলহপ্রিয়া দ্রোশয়া রমণীয় পাণিগ্রহণ হওয়া অশেষ ক্লেশের বিষয়। ..এতদ্দেশীয় অনেক বিদ্যার্থী ব্যক্তিই এ বিষয়ের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল।” বলা বাহুল্য এই পরিস্থিতি তৎকালীন সমাজেই সৃষ্ট। সে সময়ে মেয়েদের শিক্ষা না দিয়ে গৃহবন্দী করে রেখে, নিজ নিজ শিক্ষিত তুলনায় বয়স্ক স্বামীর সঙ্গে তাদের মানসিক সাযুজ্য অসম্ভব করে তােলা হয়। এই পরিস্থিতিতে হীনমন্যতায় পীড়িত স্ত্রীদের পক্ষে কলহ ব্যতীত আত্মপ্রতিষ্ঠার ও স্বামীর সঙ্গে সংযােগ স্থাপনের বিশেষ কোনাে পথ থাকে না। অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীরা এ সত্য ভালােভাবেই অবগত ছিলেন এবং সেই কারণেই “স্ত্রী ও স্বামী উভয়ের মনের গতি, কার্য্যের রীতি ও ধর্মবিষয়ক মত এক প্রকার হওয়া আবশ্যক।” বিবেচনা করে তারা স্ত্রী শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কারণ তারা জানতেন যে, মানসিক ঐক্য না হলে, “কেবল তাহারাই অসুখী থাকেন এমত নহে, তাহাদের সন্তানেরাও দূষিতপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া অনেক প্রকার ক্লেশ ভােগ করে।”
গুরুগম্ভীর বিষয়কে উপস্থাপন করার কৃতিত্ব ছাড়াও অক্ষয়কুমার যখন তার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বিষয়কে প্রবন্ধে রূপদান করেন, তখন তার উপস্থাপনায় যে সাহিত্যিক তার প্রকাশ ঘটে, তার সঙ্গে তার অনুভূতির গভীরতার যেন একটা চমৎকার সৌহার্দ পাতানাে সম্ভব হয়। খানিকটা নিদর্শন,
“হায়! যাহারা কেবল দণ্ডভয়ে আপনার অনভিমত কাৰ্য্যে এইরূপ নিয়ােজিত থাকে—গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রৌদ্র ও বর্ষা ঋতুর অজস্র বারিবর্ষণ সহ্য করে, তাহাদিগের কি বিজাতীয় যন্ত্রণা! তাহারা দণ্ডায়মান হইয়া হল চালনা কক্ষক, হস্তদ্বারা নীলভূমির তৃণ উৎপাটন কক্ষক, নীলপত্রচ্ছেদন কক্ষক, তৎপূর্ণ নৌকাই বা বাহন কক্ষক, তাহাদের অন্তঃকরণ কদাপি সে স্থানেও সে কার্য্যে নিবিষ্ট থাকে না। যখন কৃষকেরা নীলকরের নীলক্ষেত্র কর্ষণ করে, তখন তাহারা আপনার ভূমি ও আপনার শস্য স্মরণ করিয়া উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হয়! স্বসস্তানবৎ স্নেহাস্পদ শস্য বৃক্ষ গুলি স্বচক্ষে দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হয়। সে সময়ে তাহাদের স্বীয় ভূমি কর্ষণপূৰ্ব্বক সম্বৎসরের অন্ন সংস্থান করা আবশ্যক, যে সময়ে তাহারা স্বকীয় কাৰ্য্য সমাধা করিতেই সাবকাশ পায় না, সেই সময় তাহাদিগকে অযথােচিত বেতন স্বীকার পূর্বক অন্যের কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া শরীর ক্ষয় হয়।”
‘চণ্ডিপাঠ’ নিয়ে আরও কিছু বলা দরকার। তথ্যনিষ্ঠ বিষয়বস্তু অবলম্বনে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচার এ গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। বেশ অভিনব ছিল এই ‘চাণ্ডিপাঠ’ বইটি। বইয়ের মাথায় লেখা থাকত ‘এন্টারটেইনিং লেসনস ইন সায়েন্স অ্যান্ড লিটারেচর’। সেখানে অক্ষয়কুমার ‘কীটাণু বিষয়ে যেমন অবহিত করছেন নবীন পাঠককে, তেমনই লিখছেন ‘ব্রহ্মাণ্ড কী প্রকাণ্ড ব্যাপার। মাঝখানে রয়েছে উল্কাপিণ্ড’, ‘সূর্য’ আর চন্দ্রের ‘গ্রহণ’, ‘মেঘ ও বৃষ্টি’ এবং ‘তড়িৎ, বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত’ বিষয়ক বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ আবার ‘বিহঙ্গম-দেহ’ নিয়েও আলােচনা। ‘চণ্ডিপাঠ’-এর প্রথম ভাগেই আবার ছিল ‘আগ্নেয়গিরি’, ‘উষ্ণপ্রস্রবণ’, ‘জলপ্রপাত’ বা ‘পৃথিবীর গতি’ বিষয়ক ভৌগােলিক বিষয় থেকে সিন্ধুঘােটক, ‘বনমানুষ’-এর মতাে জীববিদ্যার বিষয়। এই বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনার পাশেই রয়েছে কখনও ‘মিত্রতা’ বা ‘আত্মগ্লানি’ নিয়ে তার ভাবনাচিন্তা, আবার ‘শারীরিক স্বাস্থ্য-বিধান’, ‘বায়ু-সেবন’ ও ‘গৃহ-পরিমার্জন’ আর ‘স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন’ বিষয়ক নিবন্ধও। লক্ষণীয় যে, বিজ্ঞানের সঙ্গে মানবচরিত্র সাধন, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে স্বাস্থ্য-বিধান থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আর সবচেয়ে বড়াে কথা স্বদেশগঠন—উনিশ শতকীয় শিশু-কিশােরের বেড়ে ওঠার জন্য এক অসামান্য পাঠ্যক্রমের প্রকল্প তিনি যেন তৈরি করে নেন তার ‘চণ্ডিপাঠ’-এর তিন খণ্ড জুড়ে। এর মধ্যেই লক্ষণীয় পাঁচটি বিষয়। প্রথমত, উনিশ শতকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রকৃতিকে বােঝাবার চেষ্টা, দ্বিতীয়ত, বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানচিন্তার সঙ্গেই যে একটা মূল্যবােধেরও সংযােগ আছে, সেই বিধাসটিকে নবীন পাঠকের মধ্যে যুক্ত করে দেওয়া, তৃতীয়ত, অক্ষয়কুমারের এই লেখাগুলি বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাদি প্রকাশের বহু আগের ঘটনা চতুর্থত, প্রায় প্রতিটি বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাই ছিল সচিত্র। বৈজ্ঞানিক রেখাচিত্র সম্বলিত বইয়ের সূচনাপর্বেও তিনি অন্যতম পথিকৃৎ। পঞ্চমত, এই ধরনের বইতে প্রয়ােজনীয় পরিভাষা ব্যবহারের কূটপ্রশ্ন তুলে কাজটিকে ব্যাহত করেননি তিনি।
নিজেই একের পর এক অসামান্য সব পরিভাষা উপহার দিয়ে গিয়েছেন ভবিষ্যতের বাংলার জন্য। তার সবই পরবর্তীকালে গৃহীত হয়েছে এমন নয়, তবে তার তৈরি পরিভাষার একটা বড়াে অংশই আধুনিক বিজ্ঞানচর্চায় গৃহীত। অন্য সব কাজ বাদ দিলেও, এই পরিভাষা-প্রণয়নের পথিকৃৎ হিসেবেই তাকে ভােলা আমাদের অনুচিত। যেমন, ‘স্টমাক’, ‘মাসল’, ‘ব্রেন’-কে ‘পাকস্থলী’, মাংসপেশি’, ‘মস্তিষ্ক’ ইত্যাদি। কেমিস্ট্রি’কে ‘রসায়ন’, হটস্প্রিং ’কে ‘উষ্ণপ্রস্রবণ’, ‘এমব্রায়াে’কে ‘ভ্রূণ’, ‘বােটানি’কে ‘উদ্ভিদবিদ্যা’, ‘ওয়েসিস’কে ‘মরুদ্যান’, কার্বন’কে ‘অঙ্গার’—এমন কত উদাহরণ। কাণ্ডজ্ঞান আর সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে বিজ্ঞানের সত্যকে মিশিয়ে যে কত সুন্দর সহজ পরিভাষা তৈরি করা যায়, তিনি সেই পথ-নির্দেশক। তাই পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ‘চাণ্ডিপাঠে’র কদর বেশি। ‘চণ্ডিপাঠে’ অক্ষয়কুমার তথ্যনিষ্ঠ বিষয়বস্তুর মাধ্যমে তার সেই সনাতন নীতিধর্ম প্রচারের প্রবণতা দেখালেও তার কল্পনার ঐধর্যের পথ এতে রুদ্ধ হয়নি। তৃতীয় ভাগে ‘স্বপ্নদর্শনে’র প্রবন্ধ তিনটিতে এই কল্পনাবিকাশের ছাপ বিদ্যমান। একজন ইংরেজ লেখকের রচনা অবলম্বনে তার সেই তিনটি প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন। মূল রচনাটি যােসেফ অ্যাডিশন-এর ‘ভিশন অফ মির্জা’ নামক বিখ্যাত কাহিনি।
পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ‘চণ্ডিপাঠ’ তাে কয়েক পুরুষ ধরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। রামগতি ন্যায়রত্ন লিখেছেন তাহার রচনা যেমন সরল, তেমনই মধুর, তেমনই বিশুদ্ধ ও তেমনই জ্ঞানপ্রদ। বিশেষ করে ‘চণ্ডিপাঠ’ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড সম্বন্ধে তার মন্তব্য,
“ইহার পূর্বে বির্ণের নিয়ম ও বাস্তব পদার্থসংক্রান্ত এরূপ মনােহর ও জ্ঞানপ্রদ বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক রচিত হয় নাই। এই পুস্তক দুইখানি ঐ বিষয়ে যেমন সৰ্ব্বপ্রথম, তেমনই সর্বোৎকৃষ্ট। এই দুই পুস্তক পাঠ করিলে যে কত নতুন বিষয়ের জ্ঞানলাভ হয়, তাহা বলিয়া শেষ করিয়া যায় না।”৪
জীবনীকার নকুড়চন্দ্র বিশ্বাসের কথায়,
“আমাদিগের দেশে এরূপ বিদ্যালয় অতি বিরল, যাহাতে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ চণ্ডিপাঠ না অধীত হয় তৃতীয় ভাগ অপেক্ষাকৃত দুরূহ ও উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ। ইহা রচয়িতার ভাব-গাম্ভীর্যের পরিচায়ক। যখন বি এ ক্লাসে পরীক্ষায় বাঙ্গালা সাহিত্য সন্নিবিষ্ট ছিল, তখন ইহা পাঠ্য ছিল।”৫
অক্ষয়কুমারের শ্রেষ্ঠ গবেষণামূলক রচনা ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়’। আধুনিক শিক্ষার পরিভাষায় বহুল ব্যবহৃত ফিল্ড-স্টাডি বিষয়টি যে সমাজবিজ্ঞান চর্চায় কতদূর পৌঁছােতে পারে এই অক্ষয় গ্রন্থের দুই খণ্ড তার অনুপম দৃষ্টান্ত। তত্ত্ববােধিনী পত্রিকায় এ গ্রন্থের রচনা প্রথম প্রকাশিত হতে থাকে। কঠিন শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হয়ে অক্ষয়কুমার যখন রােগযন্ত্রণায় কাতর তখন এ গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত হয়। এদিক থেকে গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমারের গভীর মনােবল ও নিষ্ঠার কোনাে গ্রন্থকেই অক্ষয়কুমার বাংলায় হুবহু অনুবাদ করেননি, আশ্রয় করেছেন মাত্র। তিনি ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের প্রথম ভাগের উপক্রমণিকায় ভাষাতাত্ত্বিক আলােচনা করেছেন। তার আলােচনার বিষয় হল ইন্দো-ইউরােপীয়, ইন্দো-ইরানীয় এবং ভারতীয় আর্যভাষা। দ্বিতীয় ভাগের উপক্রমণিকায় স্থান পেয়েছে প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক এবং পুরাণাশ্রিত ধর্ম ও দর্শন সাহিত্যের আলােচনা। ফলে এ গ্রন্থের বিষয়গুলাে গভীর জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। তিনি জ্ঞানের দুরূহ তত্ত্বকে গভীর মনােযােগের সঙ্গে যুক্তিনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির মাধ্যমে আলােচনা করেছেন।
‘ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়’ গ্রন্থের বিশেষ মূল্য শুধু তার ধর্মতত্ত্ব ও হিন্দুধর্মের বিকাশ-এর বিষয়ে যে আলােচনা রয়েছে তার জন্যেই নয়, যদিও সম্পূর্ণ যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে বৈদিক ও পরবর্তী সাংস্কৃতিক এবং প্রাচীন ইরাণীতে ইংরেজি ও ফারসি ভাষায় ভারততত্ত্বের সে-কালীন গবেষণার নির্দেশ সহ এরকম আলােচনা বাংলা ভাষায় আগে বা পরে আর দেখা যায়নি। তবু গ্রন্থটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে তার সমসাময়িক সমাজ ও স্বদেশ ভাবনার জন্য। এ বিষয়ে তিনি যে চিন্তা ও ভাবের প্রকাশ করেছেন তা তৎকালীন ভাবনা-চিন্তাকে স্পর্শ করেও তার সীমা বহুদূর উত্তীর্ণ হয়ে যায়।
অক্ষয়কুমারের প্রবলতম ক্ষোভ ও দুঃখের কারণ ভারতের পরাধীনতা। বৈদিক সাহিত্যের আলােচনা প্রসঙ্গে অকস্মাৎ তিনি দুঃখে, ক্ষোভে ফেটে পড়েন। বলে ওঠেন,
“সেই হিন্দু কি এই হিন্দু! এককালের সিংহ-শার্দুল-প্রসবিনী ভারতভূমি এখন শশ-মূষিক প্রসবিনী হইয়া কতই লাঞ্ছিত হইতেছেন। তদীয় পূর্ব-প্রতাপের চিতাগ্নি হইতে কি সুদীর্ঘ ও ঘনীভূত ধূমাবলী উত্থিত হইতেছে। তাহার বর্তমান অবস্থা অগ্নিময়, ভবিষ্যৎ গাঢ়তর ধূমে আচ্ছন্ন।”
সত্যিই তাে ভারতবর্ষের ক্ষমতা পেয়ে ইংল্যাণ্ড ‘উজ্জ্বল ও উন্নত হয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষের দশা কি হয়েছে? অক্ষয়কুমার ইংল্যাণ্ডকে উদ্দেশ্য করে বলেন
“তােমার রাজমুকুটই (এর)…হীরকখণ্ড…গাঢ়তর কলুষ কলিমায় প্রকৃত অঙ্গারখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে…।”
দর্শন ও বিজ্ঞানচিন্তা
অক্ষয়কুমার দত্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইউরােপীয় দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সেই দার্শনিক চিন্তাধারা প্রকৃতিবাদ হিসেবে পরিচিত। ডিমােক্রিটাস, লুক্রিটিয়াস, স্পিনােজা প্রমুখ দার্শনিক প্রকৃতিবাদকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু প্রকৃতিবাদ সম্পর্কে তাদের মতবাদের মধ্যে ঐক্য আছে। প্রকৃতিবাদীদের মতে, বিধ এক সুশৃঙ্খল, সুনিয়ন্ত্রিত নিয়মের অধীন। বস্তুর উদ্ভব, বিকাশ, গঠন এবং বস্তু সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় নিয়মের অধীন। তবে বস্তুজগৎ কোনাে অতীন্দ্রিয় বা অতিপ্রাকৃত সত্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। বস্তুময় বিপ্রকৃতির গতিপথ সুনিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের অধীন এ জগৎ একটি বাঁধাধরা নিয়ম মেনেই চলছে। বহু ও বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য, পরিবর্তনের ভেতর স্থায়িত্ব এবং বহুমুখী ও বিস্ময়কর নিসর্গের ভিতর বুদ্ধির গােচরাধীন দৃঢ় এক বস্তুসত্তা বিরাজমান। সেই সত্তার পাশ্চাতে কোনাে অলৌকিক বা ঐশ অভিপ্রায় নেই।৬
বস্তু অণু-পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। বস্তুর সত্তার প্রকৃতি নিরপেক্ষ ও সমন্বিত। বস্তুর গতিপথ নিয়মিত ও অনিয়ন্ত্রিত। বিজগতের ঘটনাপ্রবাহ এক গতিশীল যান্ত্রিক নিয়মে আবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যেও সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা বর্তমান। প্রকৃতিবাদীরা প্রকৃতির নিয়মের অন্তরালে কোনাে অতীন্দ্রিয় ও পরম সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। প্রাচীন গ্রিসের প্রকৃতিবাদ বস্তুবাদের সরল রূপ পরিগ্রহ করে। প্রকৃতিবাদের ছাঁচে বস্তুবাদ রূপায়িত হয়েছিল বটে, কিন্তু সকল প্রকৃতিবাদীকে বস্তুবাদী বলা যায় না।৭ প্রকৃতিবাদীরা নীতিবিদ্যাকে পরিবেশের অনুসারী বলে মনে করতেন। প্রকৃতিবাদের প্রধান লক্ষণ হল নিরীৰ্থরবাদ কিংবা অজ্ঞেয়বাদ। অক্ষয়কুমার দত্ত অজ্ঞেয়বাদী হিসেবে পরিচিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে নাস্তিক বলে মনে করতেন। রাজনারায়ণ বসু অক্ষয়কুমারকে অজ্ঞেয়বাদী বলে অভিহিত করেছেন।
অক্ষয়কুমার দত্তের মতে, এই বিজগৎ প্রকৃতির নিয়মের অধীন। বিজগৎ কোনাে বিধাতীত ঈর্থরের নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত নয়। তার কাছে প্রাকৃতিক নিয়মই ঈথরের নিয়ম। প্রার্থনার পরিবর্তে প্রাকৃতিক নিয়ম পালন করলেই মানুষ সুখী হতে পারে। “মানবকুলের হিতসাধন করাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসনা…” এই ছিল তাঁর মত।৮ অক্ষয়কুমার মনে করতেন, বিজ্ঞানই সব জ্ঞানের আকার। বিজ্ঞানভিত্তিক প্রাকৃতিক নিয়মের মাধ্যমেই মানুষের জীবন ও সমাজের নীতি নির্ধারিত হওয়া উচিত। তার এই প্রকৃতিবাদী চিন্তাকে তিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে সংগতি বজায় রেখে নিজের আত্মীয়বর্গ, সমাজ ও দেশের, তথা সমগ্র মানবকুলের প্রতি কর্তব্য পালন— এই হল শ্রেষ্ঠ ধর্ম ও উপাসনা। এ সম্পর্কে অক্ষয়কুমার বলেন “বিপতি যে সকল শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিরাজ্য পালন করিতেছেন, তদানুযায়ী কাৰ্য্যই তাঁহার প্রিয় কাৰ্য্য এবং তাহার প্রতি প্রীতিপ্রকাশ পূর্বক তৎসমুদায় সম্পাদন করাই আমাদের একমাত্র ধর্ম।”৯
অক্ষয়কুমার দত্ত মনে প্রাণে বিধাস করতেন যে, শরীর, বুদ্ধি ও ধর্ম প্রকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এবং এসবের উন্নতির অনুশীলন করাই প্রকৃত ধর্ম। তিনি ব্রাহ্মসমাজের আদর্শরূপে এই নীতিকেই গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, প্রকৃতির নিয়মানুসারে কর্তব্য সম্পাদন করাই ধর্ম, আর তা না করাই অধর্ম। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,
“সমাজ হইতে বেদের আধিপত্য উঠাইয়া দিয়া, স্বভাবকে ধৰ্ম্ম পুস্তকরূপে প্রতিপন্ন করত তিনিই ব্রাহ্ম ধৰ্ম্মকে স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম বলিয়া প্রথম প্রচার করেন। কিন্তু তাহার ধর্মের পত্তনভূমি বুদ্ধি ও যুক্তি। বুদ্ধিকে নেতা করিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্মকে অতি কঠোর বৌদ্ধধর্মের আকারে প্রচার করিয়াছিলেন।”
অক্ষয়কুমার প্রাকৃতিক নিয়মের অপরিহার্যতায় সম্পূর্ণরূপে বিধাস করতেন। তিনি অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিধাস করতেন এরকম পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি প্রাকৃতিক নিয়মের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই মানুষ ও সমাজকে বিচার করেছেন। তাকে বস্তুবাদী দার্শনিক বলে অভিহিত করা যায়। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে একটা সম্পর্ক খুঁজে বের করার চেষ্টা আধুনিককালে এদেশে তিনিই প্রথম করেন। এ সম্পর্কে অক্ষয়কুমার বলেন,
“পূর্বে আমাদিগের দেশে যত দর্শনশাস্ত্র প্রকাশ হইয়াছে, এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা তাহার তাৎপৰ্য্য ছিল না। আপনারদিগের শারীরিক ও মানসিক স্বভাব ও বাহ্যবস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ বিবেচনা করিবার প্রয়ােজন তকালের লােকের সম্যক বােধগম্য হয় নাই।”১০
উনিশ শতকে উপযােগবাদী বা হিতবাদী চিন্তা ইংল্যাণ্ডে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। বাংলায়ও হিতবাদী চিন্তার প্রভাব পড়ে। অক্ষয়কুমার দত্ত হিতবাদী চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। হিতবাদীদের মতে, ‘সর্বাধিক লােকের সর্বাধিক সুখ’ মানুষের নৈতিক আদর্শ। সুখের মানদণ্ডেই মানুষের জীবনের সার্থকতা ও সফলতা নির্ধারিত হয়। প্রকৃতির নিয়মেই মানুষ সুখ অনুসন্ধান করে। বাংলায় হিতবাদী চিন্তার প্রভাব সম্পর্কে কেশবচন্দ্র সেন বলেন,
“The Politics of the age is Benthamism, its ethics Utilitarianism, its religion Rationalism, its philosophy Positivism.”১১
বেন্থামের হিতবাদী ও যুক্তিবাদী চিন্তার প্রভাব অক্ষয়কুমারের মধ্যে স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। এর পরবর্তীকালে বঙ্কিচন্দ্রের ওপরও হিতবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে। অক্ষয়কুমার ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়ই হিতবাদী চিন্তাধারার বিকাশ সাধন করেন। তবে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য ছিল। অক্ষয়কুমার হিতবাদকে দেখতেন ব্যক্তি মানুষের বিকাশের দিক থেকে। আর বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের সমষ্টিগত উন্নতির দিক থেকে হিতবাদকে দেখতেন।
অক্ষয়কুমার দত্তের মতে, প্রাকৃতিক নিয়মে সুখ অর্জন সম্ভব। তিনি সুখ অর্জনকে তিন পর্যায়ে বিন্যস্ত করেন। ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক। জড় জগতের রূপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষিত হয়েছে ভৌতিক পর্যায়ে। মানুষের জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যুর প্রতিক্রিয়ার দৈহিক নিয়মের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় শারীরিক পর্যায়ে। জৈব চেতনার বিশ্লেষণ এবং মানুষ ও পশুর ভিন্ন স্তরে নিহিত চেতনার কথা আলােচিত হয়েছে মানসিক পর্যায়ে। বাহ্য বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষের জৈব প্রবণতাকে অক্ষয়কুমার বুদ্ধি, ধর্ম ও নিকৃষ্ট বৃত্তিতে বিন্যাস করেছেন। তাঁর এই বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিতে অতীন্দ্রিয় চেতনার কোনাে অস্তিত্ব নেই। মানবিক প্রবণতা প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার অর্জনস্পৃহা, লােকানুরাগ, সাবধানতা ইত্যাদির সঙ্গে ভক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন— কিন্তু সে ভক্তি ঈশ্বরের পরিবর্তে মানুষের প্রতি প্রদর্শন করতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শনেও ভর্তির বিশেষ স্থানে আছে এবং তা তিনি মহৎ আদর্শের ক্ষেত্রে প্রয়ােগ করতে চেয়েছেন। প্রকৃতিকে বিজ্ঞান নির্ভর দৃষ্টিতে জেনে কিভাবে সেই জ্ঞান থেকে সুখ অর্জন করা যায় সে সম্পর্কে অ(য়কুমার তিনটি সূত্র নির্দেশ করেছেন। যেমন,
- ১. শরীর ও মনের যথােচিত সঞ্চালন,
- ২. সমুদয় মনােবৃত্তির সামঞ্জস্য বিধান এবং
- ৩. বাহ্যবস্তু সম্পর্কিত নিয়মের সঙ্গে সুসমঞ্জস্য মনােবৃত্তির সংগতি সাধন এবং সঠিক, সৎ ও শুভপথে পদক্ষেপের পন্থা নিরূপণ।
এখানেও পাশ্চাত্য হিতবাদী চিন্তা ও বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের বেশ মিল দেখা যায়। দেহমনের শক্তি বিকাশের কথা বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধী, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ উপলব্ধি করেছেন। তবে তাদের সকলের লক্ষ্য ছিল ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল সমাজ, আর অক্ষয়কুমারের লক্ষ্য ছিল মানুষ। তবে অক্ষয়কুমার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ ও জীবন দর্শনকে বিশ্লেষণ করেননি। তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসারি জীবন ও সমাজের সুসামঞ্জস্য বিধি ব্যবস্থাই চেয়েছিলেন। তাঁর এই বিজ্ঞান নির্ভর মানবতন্ত্রী মনােভাব উত্তরসূরিদের মধ্যে মানবেন্দ্রনাথের দর্শনেই লক্ষ্য করা যায়।

অক্ষয়কুমার নির্বিচারে কিছুই গ্রহণ করেননি। প্রকৃতিকে তিনি যথার্থ জ্ঞান ও ধর্মের উৎস বলে মনে করতেন। প্রকৃতি থেকেই সম্যক জ্ঞানের উপলব্ধি করা যায়। প্রকৃতির নিয়মের মধ্যেই ধর্ম, ন্যায়পরায়ণতা, ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় নিহিত রয়েছে। প্রকৃতির নিয়মকে উদ্ঘাটিত করতে হলে এবং তা থেকে মানুষ ও সমাজের পালনীয় অন্যান্য নিয়মে পৌঁছাতে হলে যুক্তিবাদী, মনননির্ভর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা থাকা দরকার। অক্ষয়কুমার তাঁর দর্শনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকেই গ্রহণ করেছেন। এদিক থেকে তিনি একজন প্রকৃতিবাদী ও বাস্তববাদী। তাছাড়া ভারতীয় দর্শনে যে প্রকৃত অর্থে কোনাে বিজ্ঞান-দর্শন নেই, অথবা ছিল না, সেটাও অক্ষয়কুমারের অন্যতম প্রতিপাদ্য। এবং ‘সমসাময়িক’ ইউরােপের যেসব বিজ্ঞান-দর্শন তার কাছে বিজ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়েছে, সেগুলি নিয়েই তিনি চর্চা করেছেন ও তার সৃজনশীল প্রয়ােগও ঘটিয়েছেন। বেকন, কোতে, মিল প্রভৃতির ভাবধারাকে আশ্রয় করে অক্ষয়কুমার দত্ত সেই ঘাটতি-পূরণের কাজটিরই সূত্রপাত করে যান ১৮৭০ থেকে ১৮৮৩-এর মধ্যে। সেই কারণে আধুনিক ভারতে বিজ্ঞানদর্শন চর্চার পথিকৃৎ তিনিই। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বা ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের বিজ্ঞান-দর্শনচর্চার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন তিনিই।
ভারতীয় বিজ্ঞানভাবনা ও গ্রীক, ইরান ও আরব দেশ মারফত তার বিভ্রমণ, তার লেনদেনের প্রত্রিয়া নিয়েও অক্ষয়কুমার আলােচনা করেছেন। সব মিলিয়ে তার প্রতিপাদ্য এই যে ভারতীয় সভ্যতা নানা মতের, নানা ভাবধারার বিচিত্রমুখী সংঘাতের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে। আধ্যাত্মিকতা সে সভ্যতার একটি দিক নিশ্চয়ই, কিন্তু একমাত্র দিক তাে নয়ই, এমনকি প্রধান দিকও নয়। যুক্তিশীলতা ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সে সভ্যতার এক মস্ত দিক। ষােলাে শতকের পর থেকে ইউরােপে যে বিজ্ঞান বিকাশ লাভ করে তাকে নিরিখ ধরে নিয়ে তিনি দেখান যে, প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারায় কতকগুলি বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার অতি অসামান্য উদ্ভব ঘটেছিল, কিন্তু সেইসব ভাবনার সূত্রকে পরিণতির পথে নিয়ে যাবার মতাে উপযুক্ত পদ্ধতিতন্ত্র গড়ে ওঠেনি। ফলে সেইসব ভাবনার বীজ ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়। এই চিন্তাধারাকেই পরে প্রফুল্লচন্দ্র রায় আরও বিকশিত করে তােলেন।
আসলে অক্ষয়কুমার আমাদের ভাবতে শিখিয়েছেন বিজ্ঞানের অ-আ-ক-খ, জীবন এবং প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি, তার নিগুঢ় তত্ত্বগুলি। তার জীবনী এবং রচনা সংগ্রহের সংকলক এবং ‘অক্ষয়-সুধা’ (১৯২৪) নামের পুস্তকের রচয়িতা শিবরতন মিত্র যা বলেছেন, বােধহয় সেটাই অক্ষয়কুমার সম্পর্কে এবং তার বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসু মানসিকতা সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা। তিনি উপরােক্ত পুস্তকের ‘অক্ষয়কুমার দত্ত ও বঙ্গসাহিত্য’ শিরােনামে লিখেছেন,
“অক্ষয়কুমার প্রধানত বৈজ্ঞানিক। আজ ইংরেজ জাতি, জৰ্ম্মাণ জাতি, ফরাসী ও মার্কিণ জাতি বৈজ্ঞানিকতায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকতার প্রতিভা একদিনে হয় নাই। বৈজ্ঞানিকী বুদ্ধির অনুশীলনে, ইংরাজ জাতিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য মনীষী বেকন হইতে জন স্টুয়ার্ট মিল পর্যন্ত মনীষীগণ কি কঠোর তপস্যা এবং কি ভীষণ সংগ্রাম করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বেকনের সময়ে ভদ্রলােকেরা নীতিশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি সূক্ষ্ম ও উন্নত বিষয়ের আলােচনাকে ভদ্রলােকের উপযুক্ত কাৰ্য্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। আরিষ্টটল প্রভৃতি প্রাচীন যুগের বড় বড় পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত লইয়া আলােচনা করা সমাজে সম্মানজনক কাৰ্য্য ছিল। এই মানুষকে প্রত্যক্ষ্য স্কুল ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ব্যাপার সমূহ পর্যবেক্ষণ করাইয়া অধ্যবসায় সহকারে সেই সমুদায় বিষয়ের শ্রেণীবিভাগ করিবার সহিষ্ণুতায় দীক্ষিত করিতে বেকনকে অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। আজ ইংরাজ যে গৌরবান্বিত, তাহার কারণ এই বৈজ্ঞানিকতা। অক্ষয়কুমার আমাদের দেশে এই বৈজ্ঞানিকতার প্রতিষ্ঠার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন এবং সেই কঠোর তপস্যায় আত্মবিসৰ্জন করিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিকের যাবতীয় লক্ষণ অক্ষয়কুমারের চরিত্রে পরিদৃষ্ট হয়।”
‘ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়’ গ্রন্থের দীর্ঘ দার্শনিক ও ঐতিহাসিক পরিক্রমার অন্তে আমরা জানতে পারি “ষড়দর্শনের অধিকাংশটাই অনীরবাদী অথবা সংশয়ী মতবাদে পূর্ণ। অন্যান্য গৌণ দর্শনও ‘এক একরূপ নাস্তিকবাদ’ ছাড়া আর কিছুই নয়। আর চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি প্রধান অ-বৈদিক দর্শনগুলির ঈর্থর-অস্বীকৃতি তাে সুপ্রসিদ্ধ।” অক্ষয়কুমারের প্রশ্ন “তা যদি হয়, তাহলে কেন আমরা মিথ্যে এবং অনৈতিহাসিক আধ্যাত্মিকতার তকমা গায়ে এঁটে দেশের ও বিদেশের কিছু স্বার্থসন্ধানী লােকের হাতের পুতুল হয়ে ঘুরে বেড়াব? কেন বলব যে ভারতের সবকিছুই ঈরবাদী ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট? কেন আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষেরা প্রায় সকলেই এই আধ্যাত্মিক ও মননগত প্রবঞ্চনাকে মেনে নিয়েছেন ?” এই প্রবঞ্চনা সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক দিক থেকে কীভাবে আমাদের সর্বনাশ করে চলেছে, তা নিয়ে অমর্ত্য সেন অনবদ্য আলােচনা করেছেন তার ‘দ্য আর্গুমেনটেটিভ ইণ্ডিয়ান’ বইতে— যদিও কেন জানি না, তিনি অক্ষয়কুমারের প্রসঙ্গ একবারও তােলেননি।
রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য তার ‘কামারের এক ঘা’ (২০০৩) গ্রন্থের ১৬৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,
“খাঁটি বৈজ্ঞানিক মেজাজ নিয়েই তিনি দেখেছেন যাবতীয় আস্তিক দর্শনকে আর সেই সঙ্গে বেদ-বাদী ও বেদ-বাহা …উপাসক সম্প্রদায়কে। তার আগেও এই একই বিষয় নিয়ে আলােচনা করেছিলেন এইচ এইচ উইলসন, পরেও করেছেন আরও অনেক গবেষক (এঁদের মধ্যে আরও একজন ধ্রুববাদীর নামও স্মরণ করা উচিত যােগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য)। কিন্তু অক্ষয়কুমারের আগে বা পরে কেউই আস্তিক দর্শন ও ধর্মমতকে ‘মানসিক রােগ’ বলে ঘােষণা করেননি (যদিও তেমনই মনে করে থাকতে পারেন)। তাদের মনােভাব ছিল একান্তই অ্যাকাডেমিক রােগের মূলােচ্ছেদ করার উদ্দেশ্য তাদের ছিল না।”
যে উপলক্ষে রামকৃষ্ণবাবু এই কথা বলেছেন সেটি বিশেষ অনুধানযােগ্য। অক্ষয়কুমার সব্যসাচীর মতাে এক হাতে সমাজকে বিজ্ঞানমনস্ক করেছেন এবং অন্য হাতে সমাজের কুসংস্কারগুলিকে আঘাত করেছেন এবং তা যথাসম্ভব দূর করার চেষ্টা করেছেন। যেভাবে তিনি সামাজিক ও ধর্মীয় অনাচারের বিরুদ্ধে কলম শানিয়েছেন, সেখানে তিনি তার যুগে অন্যদের চেয়েও অনেকটা এগিয়ে ছিলেন। তিনি ভয় পাওয়ার মানুষ ছিলেন না। ন্যায়, সত্য ও আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যতটা লড়াই করা যায়, ততটাই করবার চেষ্টা করেছেন। তাই তিনি তাঁর ‘প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার’ (১৯০১) নামক গ্রন্থে বলতে পেরেছিলেন, “কেবল কতকগুলি ভারতীয় শাস্ত্রকার যে স্বার্থপর কপটাচারী ছিলেন, তাহা নহে পূর্বর্তন ইয়ুরােপীয় আচার্য্যেরাও ঐরূপ প্রকৃতির লােক ছিলেন। তাঁহাদের ধর্মবিধাস একরূপ, কিন্তু দেখাইতেন অন্যরূপ। আমাদের দেশে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দেবপূজার ব্যবস্থা ও তদীয় আদেশ ও দৈববাণীর বিষয় প্রচলিত আছে, ধূৰ্ত্ত পাশ্চাত্য পুরােহিতেরাও সেই প্রকার জুপিটার, মিনার্ভা, হরকুলিশ, নেপচুন ইত্যাদি দেবদেবীর অর্চনা এবং লােকবঞ্চক দৈববাণী ও দেবদেশ প্রচার করিয়া সরলহৃদয় জনসাধারণকে ভ্রান্তি ও কুসংস্কারময় তিমিরে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশী ধর্মব্যবসায়ীরা স্বকপােল-কল্পিত ধর্মকর্মে সাধারণকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য আপনারাও তাহার অনুষ্ঠান করিতেন। আবশ্যকমত স্বপ্রাধান্য-বর্ধক যদৃচ্ছা ধৰ্ম্মশাস্ত্র কল্পনা ও তদনুযায়ী উপদেশ প্রদান করিতেন। যাহা সত্য বলিয়া তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহা প্রচার না করিয়া, যে সমস্ত ভ্রান্তিময় ও কুসংস্কারপূর্ণ ধৰ্মকৰ্ম্ম, আচার ব্যবহার ও অমূলক বিাসের উচ্ছেদ সাধন তাহাদের একান্ত কর্তব্য, স্বার্থের জন্য তাহাই দেশমধ্যে প্রচলন করিতে সমধিক্যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন।
যাহাতে অবাস্তব ধর্মকর্মে লােকের প্রবৃত্তি হয়, তজ্জন্য আচার্য্যেরা নানা প্রকার আড়ম্বর আয়ােজন করিতে বিশেষরূপ উদ্যোগী ছিলেন। আপনাদিগের ভােগলালসা তৃপ্ত করিবার জন্য বিবিধ প্রকার সুভােগ্য সামগ্রী দেব-সমক্ষে উৎসর্গ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। শাস্ত্রোক্ত এইসকল বিষয়ের উপর সাধারণের দৃঢ়বিধাস উৎপাদনের নিমিত্ত উহা শিবদুর্গাদি দেবদেবীর উক্তি বলিয়া স্বরচিত শাস্ত্রমধ্যে মিথ্যা কথার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন। যে সকল দেবপ্রতিমা কল্পিত মূর্তি বলিয়া তাঁহারা আন্তরিক অবিৰ্বাস ও অমান্য করিতেন, তাহারই উপাসনায় সাধারণকে প্রবর্তিত করিবার জন্য সর্বসমক্ষ ঐ সকল প্রতিমার নিকট আপনাদিগের সংস্কৃত মস্তক অবনত করিয়া প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি দৰ্শাইতেন। এবং দেবতুষ্টি (অর্থাৎ নিজতুষ্টি) সাধনার্থ দধি দুগ্ধ (ক্ষীর মিষ্টান্নাদি অত্যুৎকৃষ্ট চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় নৈবেদ্য সজ্জা ও উত্তমােত্তম পরিধেয় রেশমী পশমী সূত্র ও পট্টবস্ত্র প্রতিমা সন্নিধানে অৰ্পণ করিতেন। কিন্তু আদানপ্রদান সর্ব্বৈব মিথ্যা, গঙ্গার জল গঙ্গায় থাকিত, অথচ পিতৃপুরুষের উদ্ধার সাধন হইত। ইহাত হইল খাওয়া-পরার ব্যবস্থা, কিন্তু ধনেরও তাে আবশ্যক তজ্জন্য স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা রত্নাদি যথাসাধ্য দক্ষিণা দিবারও বিধি পরিত্যক্ত হইল না। এবং শুভ অশুভ ঘটনা সম্বন্ধেও এইরূপে নিজ ব্যবসায়টি সৰ্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিলেন। আপনাদিগের জাতীয় পবিত্রতা ও স্পর্ধা স্বকৃত শাস্ত্রমধ্যে এতদূর বর্ধিত করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণবিশেষ জগদীর্থরের বক্ষে ও পদাঘাত করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণনা করিতেও লজ্জাবােধ করেন নাই বা কুণ্ঠিত হন নাই। অধঃপতিত ভারতে সকলই শােভা পায়। এমন অবাস্তবিক বিষয় জগতে কিছুই নাই যাহা কপট সূত্রবাহিরা নিজ স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত শাস্ত্রে সন্নিবেশিত না করিতে পারেন।”
[দ্বিতীয় পর্বটি পড়তে এখানে ক্লিক করুন]
তথ্যসূত্রঃ
- ১. নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, অক্ষয়রিত, আদি ব্রাহ্মসমাজ, কলকাতা, ১৯৮৭ ( এক্ষণ, পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৭৮ সনে
- পুনর্মুদ্রিত, পৃ. ৬০।
- ২. নবেন্দু সেন, গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭১, পৃ. ৪১।
- ৩. সুকুমার সেন, বাংলার সাহিত্য-ইতিহাস, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, ১৯৯৩, পৃ. ১৬৭।
- ৪. বিনয় ঘােষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃ. ৩২৫।
- ৫. নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, এক্ষণ, পৃ. ৫৬।
- ৬. অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, কলকাতা, ১৯০৭, ‘ভূমিকা’ দ্রষ্টব্য।
- ৭. E.R.A. Seligman ed., Encyclopedia of the Social Sciences, 1959, Vol. 11-12, P. 302-305; উদ্ধৃতি-সৌরেন্দ্রমােহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, ১ম খণ্ড, জি এই পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৬৪।
- ৮. অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, প্রাগুক্ত, উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৪০।
- ৯. অক্ষয়কুমার দত্ত, বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, ২য় ভাগ, কলকাতা, ১৮৫৩, বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।
- ১০. অয়কুমার দত্ত, বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, প্রাগুক্ত, উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য।
- ১১. P.S. Basu. Life and Works of Brahmananda Keshub Chandra Sen, Calcutta, 1972, P. 106.
‘নবজাগরণ’ অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপ্লিকেশনটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।
![]()

 নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা
নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা