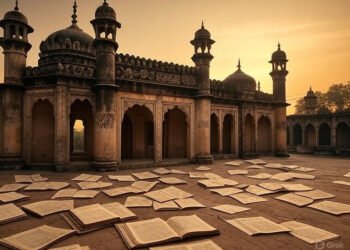লিখেছেনঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
বঙ্গভঙ্গবিরােধী আন্দোলন তখনকার বাংলাদেশে প্রবল ও অভূতপূর্ব এক আলােড়ন সৃষ্টি করেছিল। স্বর্ণযুগ বলাটা অতিশয়ােক্তি অবশ্যই, কিন্তু বান যে এসেছিল সেটা ঠিক। যেন এক নবজারগরণ। এর আগে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে, আরাে একটি জাগরণের সংবাদ আমরা শুনি, যাকে বঙ্গীয় রেনেসাঁ বলে অভিহিত করার রেওয়াজ রয়েছে। রেনেসাঁন্সের কথা বিশেষভাবে বলতেন রামমােহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪) এবং বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২), কিন্তু সেই বহুঘঘাষিত রেনেসাঁন্সের তুলনায় বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নের এই নতুন আলােড়নটি ছিল একাধিক দিক দিয়ে ভিন্ন রকমের ও অগ্রসরমাত্রার। যেমন এ ছিল স্পষ্টরূপে সাম্রাজ্যবাদবিরােধী; ঊনিবিংশ শতাব্দীর জাগরণে যে উপাদানটির অভাব ছিল প্রকট। তখনকার তৎপরতার প্রধান পুরুষ রামমােহন সাম্রাজ্যবাদের অবসান চান নি, বরঞ্চ ইংরেজরা ভারতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করলে তিনি খুশীই হতেন এবং ইংরেজশাসনকে বিধাতার আশীর্বাদ বলেই তার মনে হয়েছে।

অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র স্বাধীনতাকামী ছিলেন ঠিকই, কিন্তু ইংরেজশাসনের অবসান শীঘ্র। ঘটবে বলে মােটেই ভরসা করতেন না, তাই অবনত অবস্থায় আত্মােন্নতির চেষ্টাই ছিল তার সুচিন্তিত পরামর্শ; এবং রামমােহনের মতাে তিনিও ইংরেজ শাসনের সুফল’সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, যে-সুফল তিনি বিশেষভাবে দেখতে পাচ্ছিলেন শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে দ্বিতীয়ত,এঁদের কাজটাজনগণের বিপুল যে অংশ তাকে স্পর্শ করেনি। রামমােহন ইংল্যাণ্ডে গেছেন, সেখানেই তিনি দেহত্যাগ করেন। লেখা ও বক্তৃতায় বিপিন পাল কিছুটা চরমপন্থী ছিলেন বলা যায়, কিন্তু ইংরেজরা সহজে চলে যাচ্ছে এমনটা তিনিও দেখতে পান নি। বিপিন পালও একাধিকবার ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা গেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র মা যাবার কথা ভাবেনও নি, ইংরেজীতে উপন্যাস লেখার উদ্যোগ নিয়েছিলেন একে শুরুতে, তারপরে ওই পথে দ্বিতীয় কোনাে পদক্ষেপ ঘটে নি এই ঔপন্যাসিকের; তাঁর সময়ও সাধনার সবটাই নিয়ােজিত ছিল মাতৃভাষার চর্চাতে; কিন্তু তার আবেদনও সীমি ছিল শহরের শিক্ষিত মানুষদের মধ্যেই।
তৃতীয় ব্যাপরটা ছিল এই যে, তথাকথিত রেনেসাঁন্সের স্থপতিরা ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন । তাঁরা ইহজাগতিকতার চর্চা করেছেন অবশ্যই, কিন্তু ধর্ম তাদের চিন্তাজগতের ওপর শান্তভাবে হলেও দৃঢ়তার সঙ্গেই কর্তৃত্ব করতাে। রামমােহনের একটি বড় কাজ সতীদাহ নিবারণ; সে-ব্যাপারে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাকে কঠিন দ্বন্দ্বে নিয়ােজিত হতে হয়েছিল। ছিলেন তিনি মূর্তিপূজা-বিরােধী; হিন্দু ধর্মের আধুনিকায়নে তার ভূমিকা অগ্রনায়কের; কিন্তু ধর্মের বাইরে যে গেছেন তা নয়, ভেতরেই ছিলেন। সংস্কারকের ভূমিকা নিয়ে তিনি ব্রাহ্মমতবাদের প্রবর্তন করেন। সূচনাতে সে-মতবাদ শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে সুন্দরভাবে আকর্ষণ করেছিল, কিন্তু সমাজের সর্বত্র যে তা যাবে সেটা সম্ভব ছিল না, এবং তেমনটা ঘটেও নি। পরিবারের সঙ্গে বিরােধিতায় লিপ্ত হয়ে এমনকি ত্যাজ্য বলে ঘােষিত হওয়ার বিপদ মাথায় নিয়েও কেউ কেউ এই নতুন ধারায় দীক্ষা নিয়েছেন; এঁদের মধ্যে সুদূর সিলেটের বিপিন পাল ছিলেন একজন। কিন্তু ব্রাহ্মরা যে তাই বলে অহিন্দু হয়ে গেছেন তা নয়; এবং শেষ পর্যন্ত এই মতবাদ হিন্দু ধর্মেরই একটি নির্বিরােধ শাখা হিসাবেই স্থিতি লাভ করেছে।
বঙ্গভঙ্গ-বিরােধী আন্দোলন যে জাগরণও আলােড়ন সৃষ্টিকরলাে তা ছিল স্পষ্টরূপে সাম্রাজ্যবাদ-বিরােধী, সেটি ছড়িয়ে গেছিল সারা দেশে, এবং তার হবার কথা ছিল ইহজাগতিক তথা ধর্মনিরপেক্ষ। ঔপনিবেশিক শাসকরা তখন আর মিত্র নেই, পরিষ্কার রূপে শত্রুতে পরিণত হয়েছে। ‘আমরা পরাধীন জাতি অনেক কাল পরাধীন থাকিব’, ‘ইংরেজ আমাদের পরমােপকারী’ এ ধরনের যে-সব মন্তব্য একদা বঙ্কিমচন্দ্র করেছেন। স্বদেশী যুগের তরুণরা সেগুলাে মানতে নারাজ ছিল, যদিও তাদের কেউ কেউ অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে বঙ্কিমচন্দ্রকেতাদের পথপ্রদর্শক ঋষি বলে গণ্য করেছেন। স্বদেশ আন্দোলনকারীদের পক্ষে রাজা ভিন্ন-জাতীয় হলেই রাজ্য ‘পরতন্ত্র বা পরাধীন’ হবে না, বঙ্কিমের এই ধারণায় অংশীদার হওয়াও কঠিন ছিল; কেননা জাতি’রমনে তখন স্বাধীনতার যে স্পৃহা জেগে উঠেছিল তা বিদেশী শাসনকে সহ্য করতে অসম্মত হয়ে পড়েছি বিশেষ করে এই কারণে যে-শাসকতখন অতিপ্রকাশ্যে নিপীড়নকারীতে পরিণত হয়েছে।
আমাদের এই আলােচনাতে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বারবার আসাটা অবধারিত, দুই কারণে। এক, নিজে তিনি অত্যন্ত শক্তিশালীও প্রভাববিস্তারকারী লেখক ছিলেন। লেখক হিসাবে তার কালে তিনিই ছিলেন সর্বপ্রধান, যে জন্য অনুরাগীরা তাঁকে ‘সাহিত্যসম্রাট’ বলেন। দুই, তিনি তখনকার এবং পরবর্তী সময়েরও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, যারা ছিল প্রধানত হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্য, তাদের মনােভাব, জগদৃষ্টি ও আকাঙ্ক্ষাকে তার লেখার মধ্য দিয়ে। মূর্ত করেছেন তাে বটেই, কোনাে কোনাে দিক দিয়ে সুগঠিতও করেছেন। এমনটা অন্য কেউ পারেন নি।তার কালজয়ী উপন্যাস আনন্দমঠ সাহিত্যবিচারে যতটা মূল্যবান, সামাজিক দলীল ও সমাজের মুখপাত্র হিসেবে তার চাইতে অনেক বেশী প্রভাবশালী রচনাবটে। ওই উপন্যাসের সমাপ্তিতে বিদ্রোহী সন্ন্যাসীদের প্রধান নেতা মহাপুরুষ চিকিৎসক তার শিষ্য সত্যানন্দ ঠাকুরকে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করা থেকে নিবৃত হয়ে অস্ত্রসম্বরণ করতে বলছেন। তার কারণ ইংরেজ তখন আর শত্রু নয়, বাণিজ্য ছেড়ে শাসনভার অর্থাৎ প্রজাপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করে সে মিত্র হয়ে উঠেছে। মহাপুরুষ বলছেন যে, ‘ইংরেজ রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে – নিষ্কন্টকে ধর্মাচরণ করিবে’, এবং বহির্জগৎ সম্পর্কে অতিপ্রয়ােজনীয় জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবে। একটি ছােট, প্রায়-নিম্নকণ্ঠ, কিন্তু সুবিচারপ্রসূত মন্তব্যও আছে শিষ্যের প্রতি গুরুর; সেটি এইরকমের, ‘আর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষে জয়ী হয়, এমন শক্তি কাহারও নাই।’ পরামর্শটা তাই এই রকমের যে, বৃথা রক্তপাত ঘটাতে যেয়াে না, যুদ্ধে পারবে না, তার চেয়ে বরঞ্চ সহযােগিতা করাে, ধর্মাচরণ ও জ্ঞানান্বেষণের যে সুযােগ পেয়েছে তাকেই স্বাধীনতা জ্ঞান করে উপকৃত ও উন্নত হও। তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এটাও যে, আনন্দমঠ যখন বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন কেবল মুসলমান নয়, ইংরেজ এবং মুসলমান উভয়কেই শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল; কিন্তু পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় (১৮৮২) ছবিটা বদলে যায়, শত্রু ইংরেজ নয়, শুধু মুসলমানই পরিণত হয় শত্রুতে, সেখানে ‘মার মার মুসলমান মার’ ধ্বনি শােনা যেতে থাকে।
আনন্দমঠ-এর সর্বত্র প্রবল জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রবাহিত। কিন্তু সে-জাতীয়তাবাদ হিন্দু জাতীয়তাবাদ বৈ নয়। উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে সন্তানসৈন্যরা। নিজেদের মধ্যে যে আলাপ-আলােচনা করছে তা এরকমের :
কেহ বলে – “ভাই এমন দিন কি হইবে, তুচ্ছ বাঙ্গালী হইয়া রণক্ষেত্রে এ শরীরপাত করিব?” কেহ বলে, “ভাই, এমন দিন কি হইবে মসজিদ ভাঙ্গিয়া রাধামাধবের মন্দির গড়িব?”
কথাগুলাে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের নয়, উপন্যাসের মানুষের; কিন্তু ওই যে বাঙ্গালী বলতে কেবল হিন্দুকে মনে করা এই ঘটনা স্বদেশী আন্দোলনের ভেতরেই ঢুকে গিয়েছিল, যেপ্রসঙ্গে আবার আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে। উপন্যাসে একটি ঐতিহাসিক ভ্রান্তিও অবশ্য ঘটেছে। ফকির-সন্ন্যাসীদের যে আন্দোলনকে ভিত্তি করে বঙ্কিমচন্দ্র তার উপন্যাস লিখেছেন সে-লড়াইটা ছিল ইংরেজবিরােধী, তাকে সাম্প্রদায়িক চেহারা দেওয়া অনৈতিহাসিক কাজ। এবং ক্ষতিকরও বটে, পরে যা প্রমাণিত হয়েছে।
বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে তখনকার বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক প্রতিরােধ-আন্দোলন শুরু হয় তেমনটি এর আগে কখনাে দেখা যায় নি। খুব বড় একটা ঘটনা অবশ্য ঘটেছিল ১৮৫৭ সালে, যাকে সঙ্গতভাবেই বলা হয়েছে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে বাঙালী যে ছিল না তা নয়, কিন্তু সেটা বাংলার যুদ্ধ ছিল না, ছিল সর্বভারতের; তার চেয়েও বড় সত্য ছিল এটা যে, ওই ঘটনায় যে-বাঙালীরা যুক্ত ছিলেন তারা ছিলেন সাধারণ সিপাহী, শ্রেণীগতভাবে মধ্যবিত্ত বাঙালী তাতে অংশ নেওয়া তাে দূরের কথা। বরঞ্চ বিরােধিতাই করেছে। বিশেষ করে লেখার মধ্য দিয়ে। বাঙালী মধ্যবিত্ত তখন জোরেশােরে সংবাদপত্রে লেখালেখি করছে, তাদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন খাঁটি বাঙালী কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় সিপাহী অভ্যুত্থানের যােদ্ধাদের নিয়ে যে ধরনের রঙ্গরস করা হয়েছে তার ভেতর সম্প্রদায়গত বিভেদ সৃষ্টি ক্ষতিকর উপদান ছিল। যে-যুদ্ধটি ছিল সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক কবি তাকে নির্দয়ভাবে যবনের কাজ বলে পরিহাস করেছেন। ব্রিটিশের শাসনকে ‘রামরাজ্য’ বলে অভিহিত করে তিনি লিখেছেন,
“যবনের যত বংশ
একেবারে হবে ধ্বংস
সাজিয়াছে কোম্পানির সেনা
গরু জরু লবে কেড়ে চাপদেড়ে যত নেড়ে
এই বেলা সামাল সামাল।”
চাপদেড়ে নেড়েদেরকে সাবধান করে দিচ্ছেন বটে, কিন্তু তাদের আশু বিপদ দেখে যে উল্লসিত হয়েছেন সেটাও মােটেই লুকানাে থাকেনি। সেইসঙ্গে আপন লােকদের জন্য কবির সৎপরামর্শও রয়েছে,
“ভারতের প্রিয় পুত্র হিন্দু সমুদয়
মুক্ত মুখে বলাে সবে ব্রিটিশের জয়।”
এরকমের লেখা পড়লে ইংরেজরা কতটা উৎফুল্ল হতাে সে-বিষয়ে নিশ্চিত না হওয়া গেলেও, মুসলমান পাঠকদের পক্ষে যে মােটেই আহ্লাদিত হবার কথা নয়, সেটা তাে নিশ্চিত।

সেই ইংরেজভক্ত, ইংরেজের সাফল্যে উল্লসিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এই প্রথমবার শ্রেণীগত (নিছক ব্যক্তিগত নয়) ভাবে একটা অবস্থান নিল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে। ‘জয় ব্রিটিশের জয়’ বলে জয়ধ্বনি দেবে কি, ইংরেজরা দেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুক এটাই জোরেশােরে চাইলাে। অপরদিকে ইংরেজ যে অনড়, অবিচল, অপ্রতিরােধ্য, সে যে চিরকাল না হলেও অনেককাল ধরে থাকবে পূর্ববর্তী এই বিশ্বাসেও চিড় ধরলাে। বিশেষ করে আন্দোলনের মুখে ছয় বছর পরে শাসক ইংরেজ যখন রণে ভঙ্গ দিয়ে বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হলাে, যাকে সেটেল্ড ফ্যাক্ট বলে দম্ভ করেছিল তাকে আনসেটলড় করতে সম্মত হলাে, তখন তাে বােঝাই গেলাে যে ইংরেজ তেমন অপরাজেয় নয়, যেমনটা তাকে মনে করা হতাে।
আন্দোলনটা যে কেবল বঙ্গভঙ্গ রদকরবার জন্য ছিল তা তাে নয়, ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরােধীই, আসলে। স্বদেশী প্রতিরােধ বাংলার সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি,প্রবেশ করেছে সর্বভারতীয় রাজনীতিতেও। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের কথা যখন প্রকাশ পায় তখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সঙ্গে সঙ্গে তাদের বার্ষিক সম্মেলন থেকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে; ১৯০৩-এ জানিয়েছে, ১৯০৪-এ জানিয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই কংগ্রেসে নরমপন্থীদের পাশাপাশি চরমপন্থীদের কাজ শুরু হয়ে গেছে। চরমপন্থীর অনুসারীরা কেবল যে পথে ও পার্কে বন্দেমাতরম ধ্বনি দিয়েছেন তা নয়, বােমা তৈরি করেছেন, এবং বােমা নিক্ষেপ করে নিজে প্রাণ দিয়ে ইংরেজ প্রশাসকদেরকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছেন।
বঙ্গদেশে স্বদেশী আন্দোলন কলকাতা শহর ছাপিয়ে ছাড়িয়ে মফস্বল অঞ্চলেও চলে গেছে। মফস্বলেই বরঞ্চ বেশী প্রবলতা দেখা গেছে, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে। পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত হিন্দু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল যে তারা কলকাতাকে হারাবে, অর্থাৎ রাজধানী ও বন্দরের সবরকমের সুযােগ তাদের কাছ থেকে আরাে দূরে সরে যাবে, আগেই তাদের বাঙ্গাল বলা হতাে, এখন তা বলা হবে আরাে তীক্ষ্ণরূপে গলা ফুলিয়ে। আর নতুন রাজধানী ঢাকাতেও যে তারা বিশেষ সুবিধা করতে পারবে এমন ভরসা মােটেই করা যাচ্ছিল না, ছােট লাট ব্যামফিল্ড ফুলার তাে বটেই অন্য আমলারাও মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাত দেখানােকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে বলে ধারণা করবার কারণ ঘটছিল। বিশেষ করে চাকরিতে নিয়ােগের ক্ষেত্রে মুসলমানরা অগ্রাধিকার পাবে বলে প্রকাশ্যেই বলা হচ্ছিল।
পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গেই বাঙালী হিন্দুমধ্যবিত্তের পক্ষে বিপন্ন বােধ করবার একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কারণও কার্যকর ছিল। প্রথম কথা, তাদেরকে দুইভাগে ভাগ করে ফেলা হচ্ছিল যার অর্থ দুর্বল করে দেওয়া। দ্বিতীয় কথা, তারা খেয়াল করলাে যে উভয় বঙ্গেই তাদেরকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিহার ও ওড়িষ্যার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার দরুণ পশ্চিমবঙ্গে অবাংলাভাষীরা হবে সংখ্যাগুরু, বাংলাভাষীরা হবে সংখ্যালঘু। আর পূর্ববঙ্গে যেহেতুমুসলমানদের সংখ্যা অধিকতাই এখানেও তারা কোণঠাসা হয়ে পড়বে। পশ্চিমে সহ্য করতে হবে অবাঙালীদের আধিপত্য, আর পূর্বে মেনে নিতে হবে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য। বিপদ দুই দিক থেকেই এবং দুই বঙ্গেই।
পেশা, চাকরি, জমিদারী, ব্যবসা-বাণিজ্য, যােগাযােগ, সংস্কৃতি এসব তাে বটেই খােদ অস্তিত্বের ওপরই আক্রমণ আসছে মনে করে বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত রুখে দাঁড়িয়েছে। তার জন্য পিছু সরবার কোনাে জায়গা ছিল না। ফলে অভূতপূর্ব দেশপ্রেম দেখা দিয়েছে। মায়ের ডাকে সন্তানেরা একত্র হয়েছে। উদ্যোগ, উৎসাহ, উৎকণ্ঠা সবকিছু মিলিয়ে আয়ােজনটা ছিল মহাকাব্যিক। কিন্তু হায়, মহাকাব্য শেষ পর্যন্ত রচিত হয় নি। যা পাওয়া গেলাে তা একটি বিয়ােগান্ত নাটক, একটি মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি, যার নাম সাতচল্লিশের দেশভাগ। উনিশ শ’ পাঁচেরটি ছিল প্রদেশভাগ, ঊনিশশ’ সাতল্লিশের ঘটনা ঘটলাে দেশকে দুটুকরাে করার। সমস্ত ব্যপারটা ছিল অবিশ্বাস্য, অস্বাভাবিক ও ক্ষতিকর। কেউ বিশ্বাস করেনি ভারত ওইভাবে দুভাগ হবে, যেভাবে হয়েছে। ব্যাপরটা প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কোনাে দিক দিয়েই স্বাভাবিক ছিল না। আর ক্ষতি যা হয়েছে সেটা তাে কিছুতেই পূরণ হবার নয়। অর্থনীতি, প্রকৃতি, নদী, পাহাড়-পর্বত, যাতায়াতের ব্যবস্থা, যােগাযােগ সবকিছুই বিপদগ্রস্ত হয়েছে।সব চেয়ে বড়ক্ষতি হয়েছে মানুষের। সাতচল্লিশের তথাকথিত স্বাধীনতার আগে এবং পরে সারা ভারত জুড়ে যেসব দাঙ্গা ঘটেছে আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে তা হলাে সবচেয়ে কলঙ্কজনক অধ্যায়। ছেচল্লিশের ১৬ই আগস্ট কলকাতা শহরে একদিনের দাঙ্গাতেই পাঁচ হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়। তখনকার বড় লাট পরিহাস করে বলেছেন, অত মানুষ পলাশীর যুদ্ধেও প্রাণ হারায় নি। তা পরিহাসের সুযােগ ছিল বৈকি। পলাশীর ঔপনিবেশিক যুদ্ধের চেয়ে অনেক বেশী রক্তাক্ত ছিল ষোেলই আগস্টের গৃহযুদ্ধ। কেবল সেদিন নয়, তারপরেও দাঙ্গা হয়েছে, নােয়াখালীতে, বিহারে, উত্তর ভারতে, পাঞ্জাবে। স্বাধীনতার পরেও দাঙ্গা থামেনি। আগস্ট মাসের শেষে কলকাতায় যে দাঙ্গা বেধেছিল সেটা থামত না, গান্ধী না থাকলে। দিল্লীর দাঙ্গাও গান্ধীই থামিয়েছেন। পরিণামে ‘মুসলমান-তােষণকারী’ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে উগ্র হিন্দুপন্থীদের হাতে তাকে প্রাণ দিতে হয়েছে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির ছয় মাস পেরুবার আগেই, ১৯৪৮ সালের জানুয়ারীর ৩০ তারিখে।
সাতচল্লিশের চৌদ্দই-পনেরই আগস্টের আগেও দাঙ্গা চলছিল। ব্রিটিশ আমলারা নিজেদের মধ্যে চিঠি চালাচালি করে হাস্যরসের সঙ্গে বলেছে যে, হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে আক্রমণ করতে এতই ব্যস্ত যে তারা ব্রিটিশকে আক্রমণের সুযােগ পাচ্ছে না। স্থানীয় রাজনীতিকদের কেউ কেউ আশা করেছিলেন ভারতবিভাগ সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করবে। তেমনটা মােটেই ঘটেনি। জিন্নাহ ভারত ছেড়ে চলে গেলেন পাকিস্তানে, ভারতীয় মুসলমানদের বলে গেলেন ভারতের নাগরিক হিসাবে বসবাস করতে। কিন্তু তাদেরকে তাে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল স্বাধীন ‘আবাসভূমি’র। পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের তিনি পরামর্শ দিলেন পাকিস্তানী হয়ে যেতে, অর্থাৎ দ্বিজাতি তত্ত্ব ভুলে যেতে। যে-ভিত্তির ওপর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তাকেই তিনি নাকচ করে দিলেন অমন অনায়াসে। নতুন দুই রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের কি হবে, মনে হলাে তিনি তা ভাবেনই নি। অন্যদিকে ভারতভাগের জন্য একজাতি তত্ত্বে বিশ্বাসী কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার যে নেতারা শেষ পর্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছিলেন তারাও যে সংখ্যালঘুদের সম্ভাব্য পরিণতি নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেল না। প্রাণ হারালেন অসংখ্য নিরীহ মানুষ, ভিটেমাটি এবং জীবন ও জীবিকা থেকে উচ্ছেদ হলেন যে কতজন তার হিসাব কখনাে জানা যাবে না। বাঙালীদের জন্য দুঃসহ সত্য যেটা তা হলাে এই যে, ভারতবিভাগের বীজের বপনটা ঘটেছিল বঙ্গভঙ্গ রােধ করবার আন্দোলনের ভেতর দিয়েই। ইতিবাচক। ঘটনার এমন নেতিবাচক পরিণতি ইতিহাসের এক নিষ্ঠুর পরিহাস বৈকি।
তবে এই পরিণতির ব্যাখ্যা করা মােটেই কষ্টের কাজ নয়। আর সেটা করলে দেখা যাবে যা ঘটেছে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে তা ঘটাই ছিল স্বাভাবিক। এক কথায় বলতে গেলে ব্যর্থতাটা হলাে নেতৃত্বের।
বঙ্গভঙ্গের আশঙ্কাও ঘটনা দেশপ্রেমের যে জোয়ার এনেছিল, তা ছিল আশার ব্যাপার এবং ভরসার স্থল। এবং অচিরেই এই দেশপ্রেম রূপ নিলাে জাতীয়তাবাদের। আর বিপদটা শুরু হলাে ওই রূপান্তর থেকেই। দেশ আসলে জাতির চেয়ে বড় — অনেক ক্ষেত্রেই ভৌগােলিকভাবে, এবং সকল সময়েই তাত্ত্বিকভাবে। দেশ বলতে কেবল স্থান বােঝায় না, বােঝায় মূলত দেশের মানুষ। দেশপ্রেম হলাে দেশের মানুষের প্রতি ভালােবাসা। সকল দেশবাসীর ভালােবাসা প্রত্যেকের জন্য, এবং প্রত্যেক দেশবাসীর ভালােবাসা সকলের জন্য। জাতি বলতেও ভালােবাসাই বােঝায়, জাতির মানুষদের ভালােবাসা, মানুষদের জন্য। দু’য়ের ভেতর তফাৎটা এইখানে যে, একটি দেশে একাধিক জাতি থাকতে পারে, অনেক সময়ে থাকে। যেমন বর্তমান বাংলাদেশে আছে। বাংলাদেশ একটি আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; এখানে অধিকাংশ মানুষই বাঙালী, কিন্তু তাই বলে সব মানুষই যে বাঙালী তা নয়, অন্যান্য জাতিসত্তাও রয়েছে, তা লােকগণনায় তাদের সংখ্যা যতই অল্প হােক না কেন। দেশপ্রেমের পরিধির ভেতর বাংলাদেশের সব মানুষই আসবে, কিন্তু একক জাতীয়তাবাদ দেশের সকল অধিবাসীকে ধারণ করতে ব্যর্থ হবে, স্বভাবতই।
বঙ্গভঙ্গ-বিরােধী আবেগ ও অনুভূতি যখন বিশুদ্ধ দেশপ্রেমিক চরিত্রের ছিল তখন তাতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই স্থান সঙ্কুলান হবার কথা ছিল, কিন্তু যখন তা রূপ নিলাে জাতীয়তাবাদের তখন তার সাথে মিশ্রণ ঘটে গেলাে ধর্মের; এবং সেই মিশ্রণের ফাঁক দিয়ে সেই অঙ্কর ব্যাধি উৎসাহ পেলাে বিকশিত হবার ব্যাপারে, যার নাম সাম্প্রদায়িকতা। দেশপ্রেম তখন দু’ভাগে ভাগ হয়ে গিয়ে পরিণত হলাে হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম জাতীয়তাবাদে। বিভাজনটি যে ওইখানেই স্থির থাকবে সেটা সম্ভব ছিল না, স্বাভাবিকও ছিল না। সেটা এগিয়েছে। দুইপক্ষ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে, অনিবার্য হয়ে পড়েছে সংঘর্ষ, এবং ঘটনা অগ্রসর হয়েছে বিয়ােগান্ত পরিণতির দিকে, অর্থাৎ দেশবিভাগের দিকে।
অন্নদাশঙ্কর রায়ের সেই ছড়াটিতে হাল্কাভাবে যে-কথাটি বলা হয়েছে সেটি অত্যন্ত মর্মান্তিক সত্য। ছােট্ট খুকুটি তেলের শিশি ভাঙ্গলে পরে ধমক খায়, কিন্তু বুড়াে খােকারা ভারত ভেঙ্গে ভাগ করে প্রাতঃস্মরণীয় নেতা হন। কেউ কেউ অবশ্য ছিলেন নিরুপায়, কিন্তু অধিকাংশই ভাবেন নি কি ঘটছে ঘটতে যাচ্ছে, চেষ্টা করেন নি প্রতিহত করার। অনেকেই টের পান নি তাদের তৎপরতার পরিণতিটি কি হতে পারে। স্বদেশী আন্দোলনের প্রাথমদিকে এক সময়ের শ্রমিক নেতা এবং পরবর্তীতে গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী র্যামজে ম্যাকডােনাল্ড সেই সময়ে ভারতে এসেছিলেন, বাংলায় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে, এবং তার মনে হয়েছে এঁরা খুবই ভালাে বক্তা এবং অত্যন্ত সরব লেখক, কিন্তু যথার্থ নেতা নন, কেননা মানুষকে কোন দিকে নিয়ে যাবেন সেটা তারা জানেন না। কিন্তু তিনি এটা পরিষ্কার টের পেয়েছেন যে, স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলা সারা ভারতকে আদর্শায়িত করে তুলছে, এবং জাতীয়তাবাদকে রূপান্তরিত করছে ধর্মে, গানে ও কবিতায়, চিত্রকলায় ও সাহিত্যে। দেখেছেন যে, বঙ্গভূমি থেকে,
“ধর্মের অসংখ্য স্রোতস্বিনী সবেগে প্রবাহিত হচ্ছে যারা সবাই জাতীয়তাবাদী চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত ও প্রাণবন্ত করে তুলছে।” তিনি যে অতিরঞ্জন করেছেন এমন বলা যাবে না।”
জাতীয়তাবাদে ধর্মের প্রবেশ ঘটার এই ব্যাপরটাকেও কিন্তু স্বাভাবিকই বলতে হবে। নেতৃত্ব যাদের হাতে ছিল তাদের অধিকাংশই ধর্মের প্রভাব ও প্রয়ােজনীয়তাকে মানতেন। কারণ ছিল একাধিক। প্রথমত, ধর্ম ছিল তাদের সংস্কৃতি, অভ্যাস ও অনুভূতির অংশ। আমাদের এই অঞ্চলের মানুষের পক্ষে সামাজিক, সংস্কৃতিকভাবে তাে বটেই, ব্যক্তিগতভাবেও ধর্মের বাইরে যাওয়া কঠিন, যে জন্য ইহজাগতিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা এখানে খুবই দ্বিধাগ্রস্ত। যেমন ধরা যাক, বাংলাদেশের কথা। এর প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে; কিন্তু সেখানে তাকে স্থির রাখা যায় নি। ধর্ম যে কেবল হৃদয়ের ব্যাপার তা নয়, বিশ্বাসের বস্তুও, এমনকি বললে অন্যায় হবে না, অনেক ক্ষেত্রেই তা স্নায়বিক ব্যবস্থারও অন্তর্গত হয়ে রয়েছে।

১৯০৫ সালের দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ধর্মের ব্যবহার তাই কিছুটা যে নেতৃত্বের ব্যক্তিগত প্রবণতার কারণে ঘটেছে সেটা সত্য। দ্বিতীয়ত, ধর্ম হচ্ছে মানুষের জন্য আশ্রয়। রাজনৈতিক আন্দোলনে ধর্মকে ব্যবহার করলে আন্দোলনকারীরা ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা, ভরসা, সাহস ইত্যাদি পান। মনে করবার সুযােগ ঘটে যে সরকারের বিরুদ্ধে। তাদের লড়াইয়ের পেছনে অদৃশ্য শক্তির সমর্থন আছে, যে জন্য সরকার যতই পীড়ন করুক না কেন পীড়নকারীর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তৃতীয় একটি কারণও গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হচ্ছে এই যে, ধর্মের ভাষায় কথা বললে সেটা মানুষের কাছে সহজে গিয়ে পৌঁছায়, দ্রুত আবেদন সৃষ্টি করে, মানুষ অনুপ্রাণিত হয়, তারা সাড়া দেয়, কাছে আসে, ঐক্য গড়ে তােলে। লৌকিক ভাষার তুলনায় ধর্মীয় ভাষা সব সময়েই সরল ও সহজবােধ্য; সে-ভাষা শিক্ষিত মানুষ যেমন বােঝে, অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষেরও তেমনি বােধগম্য হয়। ধর্মীয় উপমা, রূপক, কাহিনী, বক্তব্যকে একাধারে সহজ, পরিচিত ও আবেগত-সমৃদ্ধ করে তােলে।
স্বদেশী আন্দোলনের নেতারা ছিলেন উচ্চশিক্ষিত মানুষ, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বাংলায় লিখতে ও বলতে অভ্যস্ত পর্যন্ত ছিলেন না, ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করতেন; অন্যরাও যে ধরনের বাংলা ভাষা ব্যবহার করতেন সাধারণ মানুষের জন্য তা যে অত্যন্ত সহজবােধ্য হবে এ বিষয়ে তারা নিশ্চিত হতে পারতেন না। অন্যদিকে ধর্মের ভাষায় কথা বলার সময় তারা নিজেরা যেমন অনুপ্রাণিত বােধ করতেন, শ্রোতাদেরকেও তেমনি উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন। ব্যাপার আরাে একটি ছিল। সেটা এই যে, ধর্ম তাদেরকে আত্মপরিচয় লাভে সাহায্য করতাে। শাসক ইংরেজ কেবল বিদেশী নয়, সে বিধর্মীও, এই বােধটা জাতীয়তাবাদের জন্য যে উদ্দীপক শক্তি ছিল তাতে কোনাে সন্দেহ নেই। ইংরেজী ভাষার ব্যবহার করা না-করা দিয়ে দুই পক্ষের ব্যবধানকে স্পষ্ট করার অসুবিধা ছিল; কারণ ইংরেজী ভাষা কেবল শাসক শ্রেণী নয়, আন্দোলনকারীরাও ব্যবহার করতেন। কিন্তু ধর্মের দিক দিয়ে দুই পক্ষ ছিল একেবারেই দুই জগতের, এক পক্ষ খ্রিস্টান, বিপরীত পক্ষ হিন্দু, দুইয়ের ভেতর মিলনের কোনাে ক্ষেত্র নেই।
এসব কারণে দেশপ্রেমিক আন্দোলনের পরিচ্ছন্ন স্রোতের ভেতর সাম্প্রদায়িকতার বিপজ্জনক আবিলতা চলে এলাে। ধর্ম পরিচয়ের চিহ্ন হিসাবে থাকা এক কথা, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। ধার্মিক মানুষ মৌলবাদী হতে পারেন, মৌলবাদের ভেতর সাম্প্রদায়িকতা উপাদান থাকে নিশ্চয়ই, কিন্তু ধর্মীয় মৌলবাদ আর সাম্প্রদায়িকতা তাে এক বস্তু তা নয়, দুয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা জিনিসটা মৌলবাদের তুলনাতে অধিক পরিমাণে রাজনৈতিক। এর সঙ্গে ক্ষমতা ও সম্পত্তির প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গীজড়িত। দুই ধর্মের দুই মৌলবাদী পাশাপাশি বসবাস করতে পারেন, তাঁদের মধ্যে সম্প্রীতি থাকাও অসম্ভব নয়, ভূদেবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-৯৪) তার লেখাতে এ ধরনের সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কিন্তু দু’জন যদি দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন, বিশেষ করে একপক্ষ যদি অপর পক্ষের সম্পত্তি (সেটা স্থাবর অস্থাবর যে ধরনেরই হােক) দখল করতে উদ্যত হয়, এবং সেই উদ্যোগকে শক্তিশালী করবার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করে তখন সাম্প্রদায়িকতা দেখা দেয়।
এদেশে ধর্মবিশ্বাস প্রাচীন ব্যাপার; হিন্দু মুসলমান এখানে যুগ যুগ ধরে প্রতিবেশী হিসাবে বসবাস করেছে। তারা একই আকাশের রােদ-বৃষ্টি-জ্যোৎস্না ভােগ-উপভােগ করেছে, চাষ করেছে মিলেমিশে, একই বাজারহাটে কেনাবেচা করতে তাদের অসুবিধা হয়নি। শোকে-দুঃখে পরস্পরকে সাহায্য করেছে, পরস্পরের উৎসবে, এমনকি ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও অনায়াসে যােগ দিয়েছে, মন্দিরের ঘণ্টা মিশে গেছে আযানের ধ্বনির সাথে, কোনাে গােলযোেগ বাধে নি। কিন্তু বিপদ ঘটলােতখনই যখন ধর্ম চলে এলাে রাজনীতিতে, অর্থাৎ যুক্ত হয়ে গেলাে ক্ষমতার জন্য রাজনৈতিক প্রতিযােগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দ্বন্দ্বইত্যাদির সঙ্গে। যে-লড়াইটা হবার কথা ছিল বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের সঙ্গে ঔপনিবেশিক ইংরেজের, সে-লড়াইয়ের ভেতরে প্রবেশ করলাে ভ্রাতৃঘাতী হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ। মহাকাব্যের সম্ভাবনা মােড় ঘুরে এগুতে থাকলাে ট্র্যাজেডির অভিমুখে।
১৮১৭ সালে যখন হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সে-কলেজে মুসলমানের যে প্রবেশাধিকার থাকবেনা এটা ধরেই নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা নিয়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের কোনাে মাথা ব্যথা ছিল না। কেননা ওই সম্প্রদায়ের ছেলেরা তখনাে পড়তে আসবার মতাে সামর্থ্য অর্জন করে নি। কিন্তু পরে ১৮৫৪ সালে হিন্দুকলেজ যখন সরকারী কলেজ হয়েছে, নাম নিয়েছে প্রেসিডেন্সি কলেজের তখন সেই কলেজে যদি মুসলমান ছাত্রদের জন্য নিষিদ্ধ থাকতাে তাহলে সমস্যার সৃষ্টি হতাে, কেননা ততদিনে মুসলমান ছাত্ররা কলকাতায় আনাগােনা শুরু করে দিয়েছে।
বাংলায় মুসলমানরা যে সংখ্যায় অধিক এ সত্যও প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু কেবল সংখ্যায় অধিক হবার ব্যাপার নয়, তারা যে শিক্ষিত এবং আত্মসচেতন হয়ে উঠতে থাকলাে তাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত মধ্যবিত্ত এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের উঠতি মধ্যবিত্তের দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হবে এমনটা বােঝা গেলাে। আশঙ্কা করা গেলাে যে, হিন্দু ও মুসলমান এই নাম বিশেষ্য থাকবে না, পরিণত হবে বিশেষণে; দুই সম্প্রদায়ই নিজ নিজ গুণ অর্থাৎ ক্ষমতা প্রকাশে আগ্রহী ও তৎপর হয়ে উঠবে। ১৯০৫ এর পরে সেই দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। তাতে শাসক ইংরেজ তার নিজের স্বার্থেই উস্কানি দিয়েছে, সােৎসাহে।
স্বদেশী আন্দোলনের সাফল্য যদি বলি বঙ্গভঙ্গ রদ করায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এটাও মানতে হবে যে, ওই আন্দোলনের ব্যর্থতা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার অগ্রযাত্রার পথকে প্রশস্ত করে দেওয়ায়। আমরা ১৯০৫ সালের কথা ভাবছি। স্মরণ করা বােধকরি অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ওই বছরই রাশিয়াতে লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের চেষ্টা হয়েছে, যে-চেষ্টাকে বলা হয় ১৯১৭ সালের বিপ্লবের চূড়ান্ত মহড়া। সেই বিপ্লবী প্রচেষ্টার ঢেউ পরের কথা, তেমন একটা খবরও স্বদেশী আন্দোলনের লােকদের কাছে পরিষ্কারভাবে এসেছিল কিনা সন্দেহ। ভারতে তখন বরঞ্চ এই তথ্য নিয়ে এক ধরনের সন্তুষ্টি ছিল যে ওই বছরই যুদ্ধে জাপানের কাছে রুশ বাহিনীর পরাজয় ঘটেছে।
রুশদের পরাজয়কে ভারতীয়দের কেউ কেউ প্রাচ্যের কাছে পশ্চিমের পরাজয় হিসাবে দেখেছেন।রুশ দেশের সঙ্গে ভারতীয় পরিস্থিতির অবশ্য মৌলিক পার্থক্য ছিল। এক, রুশ দেশ ছিল স্বাধীন, ভারত পরাধীন। দুই. রুশদের কাঁধে জারতন্ত্র স্বৈরাচারী ছিল ঠিকই কিন্তু ওই শাসক ভারতীয় শাসকদের মতাে শক্ত ও সুকৌশলী ছিল না। আর সবচেয়ে বড় সত্য যেটা সেটা হলাে রুশ বিপ্লবীদের সামনে ছিল শ্রেণীর প্রশ্ন, ভারতীয়দের সামনে প্রধান হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতার প্রশ্ন। স্বাধীনতার প্রশ্নের মীমাংসা না করে অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শাসকদেরকে না হটিয়ে শ্রেণী সংগ্রামকে অর্থাৎ সামাজিক বিপ্লবের বিষয়টিকে সামনে আনা সম্ভব ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ঘটনা এই যে, ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম।
করার ক্ষেত্রেই ভারতীয়দের জন্য সাম্প্রদায়িক বিভাজনটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল মস্ত বড় এক অন্তরায়। স্বদেশী আন্দোলনের মতাে সাম্প্রদায়িকতাও বাংলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, ছড়িয়ে পড়েছে সারা ভারতে, ইতি এবং নেতি ভ্রমণ করেছে এক সঙ্গেই।
জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা দেবাে কিভাবে? জাতীয়তাবাদ একটি অনুভূতির ব্যাপার, যার ভেতর স্বপ্ন থাকে, আকাঙ্ক্ষা থাকে, কাজ করে স্মৃতি। তবে জাতীয়তাবাদের একটা বস্তুগত ভিতও তাে চাই। সেই ভিতটি একাধিক উপাদান দিয়ে তৈরি যাদের মধ্যে রয়েছে ভাষার, ধর্মের ও অর্থনৈতিক জীবনের ঐক্য। কিন্তু এই তিনের মধ্যে প্রধা উপাদান কোনটি? প্রধান হলাে ভাষা। ভাষার জোরটা যে বেশী সেটা বােঝা যায় মােটাদাগের এই সত্যটা থেকেই যে, ধর্মান্তরিত হওয়ার তুলনায় ভাষান্তরিত হওয়া অনেক কঠিন। তাছাড়া একটি জনগােষ্ঠীর ভাষা সেখানকার ধর্ম ও শ্রেণীবিভাজনকে অতিক্রম করবার শক্তি রাখে। জাতীয়তাবাদের সংগঠনে ভাষার পরে আসে অর্থনৈতিক জীবনের ঐক্য, তারপরে ধর্ম।
জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বাঙালী সামাজে অন্তত চারটি ধারণার প্রচলন আমরা লক্ষ্য করবাে। এই চারটি ধারণাই প্রতিনিধিত্বমূলক। একটির কথা বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন তার ধর্মতত্ত্ব নিবন্ধে। সেখানে গুরু জানাচ্ছেন তার শিষ্যকে —
“পৃথিবীতে যত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণদিগের মত প্রভাবশালী, ক্ষমতাশালী ও ধার্মিক কোনাে জাতি নহে।”
ধারণাটি শুধু ধর্মীয় নয়, সরাসরি বর্ণবাদীও বটে।
ওই সময়েই মীর মশাররফ হােসেন (১৮৪৭-১৯২২) তাঁর ‘গােকুল নির্মূল আশঙ্কা : প্রস্তাব এক’-এ বলছেন আরেক ধরনের জাতির কথা –
“এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই প্রধান। পরস্পর এমন সম্বন্ধ যে, ধৰ্ম্মে ভিন্ন কিন্তু মর্মেও কর্মে এক — সংসার কাৰ্যে ভাই না বলিয়া থাকিতে পারি না।”
এখানে জাতির ভিত্তি বর্ণ নয়, ভাষাও নয়, ভিত্তি হচ্ছে ধর্ম। মশাররফের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনাে সাম্প্রদায়িকতা নেই। তিনি যা বলছেন সে ধরনের মত স্যার সৈয়দ আহমদ খানও (১৮১৭-৯৮) ব্যক্ত করেছেন। তিনিও বলেছেন যে ভারতের দেহ এক, কিন্তু তার চোখ দু’টি, হিন্দু ও মুসলমান। এই মতে সাম্প্রদায়িকতা নেই বটে, কিন্তু এতে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিটা রয়েছে। দুই জাতির অস্তিত্ব-বিষয়ক ধারণা ভিন্ন ভিন্নভাবে দয়ানন্দ সরস্বতী, বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়, বীর সাভারকার, জিন্নাহ, প্যাটেল, শ্যামাপ্রসাদ মুখােপাধ্যায়দের মধ্যে এমনকি বাংলাকে অখণ্ড ও স্বাধীন রাখতে আগ্রহী আবুল হাশিমের চিন্তাধারার মধ্যেও দেখতে পাবাে।
তৃতীয় একটি মত পাওয়া যাচ্ছে, সেটি এই রকমের –
বঙ্গবাসীকে বাঙ্গালী বলে, এই বাঙ্গালী এখন হিন্দু মুলমান দুই শাখায় বিভক্ত। … বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত না হইলে কাহারও উন্নতি লাভের আশা নাই।২
এই মতটি দ্বিজাতি তত্ত্বে বিশ্বাসী নয়। এতে বলা হচ্ছে যে হিন্দু মুসলমান একই জাতি, তবে তারা দুটি শাখা। লেখকের মতে জাতীয়তার ভিত্তি বর্ণ বা ধর্ম নয়,ভাষাও নয়, ভিত্তি হচ্ছে বাসস্থান। বঙ্গভূমিতে যারা বাস করে তারাই বাঙালী। চতুর্থ মতটি কিছুটা আবেগের সঙ্গেই প্রকাশিত, যে-আবেগ সঙ্গত বটে –
পুরুষানুক্রমে যুগ যুগান্তর ধরে বাঙ্গালী দেশের গণ্ডীর মধ্যে বাস করে, আর এই বাঙ্গালা ভাষাতেই সর্বক্ষণ মনের ভাব ব্যক্ত করেও যদি বাঙ্গালী না হয়ে আমরা অপর কোন একটা জাতি সেজে বেঁচে থাকতে চাই, তাহলে আমাদের তাে আর কখনও উত্থান নাই-ই, অধিকন্তু চিরতমসাচ্ছন্ন গহ্বরে পতনই অবশ্যম্ভাবী।৩

প্রতিনিধিত্বমূলক এই চারটি মতের দিকে ফিরে তাকানাে যাক। বাসভূমির পরিচয় দিয়ে জাতীয়তার পরিচয় হবে, অর্থাৎ যারা বাংলায় বাস করে তারা সবাই বাঙালী বা কেবল মাত্র তারাই বাঙালী, প্রবাসীরা নয়, এই ধারণা সত্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণবাদী ধারণা বলছেব্রাহ্মণতথা আর্যরা একটি জাতি; এই ধারণাটি অবশ্যই অগ্রহণযােগ্য এবং বিপজ্জনক। হিন্দু ও মুসলমান এরা দুই জাত এটা হচ্ছে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী ধারণা, যার কথামীর মশাররফের উক্তিতে পাওয়া গেলাে। এটাই ব্যাপক গ্রহণযােগ্যতা পেয়েছে এবং কার্যকর হয়েছে। কিন্তু ওটিকে মীর মশাররফ যেভাবে দেখেছেন পরবর্তীতে সেভাবে দেখা যায় নি, এবং বিভাজনটি ভাই ভাই-এর মৈত্রী না হয়ে ভাই ভাই ঠাই ঠাইতে পরিণত হয়েছে। সেই বিরােধ পরিণামে ভারতকে দু’টুকরাে না-করে ক্ষান্ত হয় নি।
সবচেয়ে যৌক্তিক ও কল্যাণকর যে-ধারণা সেটি হলাে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের, যার উল্লেখ ওপরের চতুর্থ উদ্ধৃতিটিতে পাচ্ছি। লেখিকা একজন মহিলা, তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি যে সত্যটির দেখা পেয়েছেন সেটি হচ্ছে এই যে, আমরা যেহেতু বাংলাভাষাতেই সর্বক্ষণ নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করি তাই আমরা বাঙালী, আমাদের পক্ষে অন্য কোনাে জাতি’ সেজে বেঁচে থাকার চেষ্টা কোনাে প্রকার উত্থান তাে আনবেই না, বরঞ্চ পতনকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলবে। ভাষা-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের এই ধারণা কেবল একথা বলে না যে, বাঙালী এক জাতি, সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যটিকেও প্রকাশ করে যে, ভারত একজাতির দেশ নয়; দুইজাতির (হিন্দুও মুসলমানের) দেশও নয়, ভারত হচ্ছে বহুজাতির দেশ। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে ১৮টি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, এই ভাষাভাষীরা প্রত্যেকেই একেকটি স্বতন্ত্র জাতি।
ভারতবর্ষকে এক করার চেষ্টা সব সময়েই ছিল একটা সাম্রাজ্যবাদী উদ্যোগ। এই উদ্যোগ মৌর্যরা নিয়েছে, মােগলরা নিয়েছে, ইংরেজরা নিয়েছে। যে ঐক্য তারা গড়ে তুলেছে সেটা জাতীয় নয়, মূলত প্রশাসনিক বটে। ব্রিটিশের অধীনে ভারতবর্ষ একটি কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছিল, এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম স্বভাবতই একটি সর্বভারতীয় রূপ নিয়েছিল, সে-হিসাবে তাকে জাতীয় সংগ্রাম বলা হয়েছে; কিন্তু ওই সংগ্রাম ভারতীয়দেরকে এক জাতিতে পরিণত করে নি।কংগ্রেস বলেছেভারত এক জাতির দেশ; লীগ বলেছে দুই জাতির, কিন্তু আসল সত্যটা দু’পক্ষের কেউই স্বীকার করে নি। সেটা হলাে এই যে, এক তাে নয়ই দুইও নয়, ভারত বহু জাতির দেশ।
স্বাধীন ভারতে এখন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে, যার মূল কারণটি হচ্ছে জাতিগত বিভেদ এবং জাতিগত পার্থক্যের ভিত্তি হচ্ছে ভাষাগত পার্থক্য। ধর্ম দিয়ে ভারতকে এক রাখা যাবে এ ধারণা একেবারেই অবাস্তব। অনুরূপভাবে ছােট আয়তনের হলেও পাকিস্তানের জন্যও সেই একই সমস্যা। বাঙালীরা পাকিস্তান থেকে বের হয়ে এসেছে, নিজেদের ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী অস্তিত্বকে রক্ষা করবার প্রয়ােজনে; খণ্ডিত পাকিস্তানে এখন জাতিগত পার্থক্য রয়েছে, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, পাঠান এবং মােহাজের — এরা এক জাতি নয়, ধর্মের ঐক্য থাকলেও ভাষার ঐক্য নেই, এবং ওই রাষ্ট্রে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন যে এখনাে প্রবল হচ্ছে না তার কারণ একটাই; পাঞ্জাবী আধিপত্য ও সামরিক বাহিনীর শাসন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযােগ্য যে, অবিভক্ত ভারতের পক্ষে রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানের যথার্থ উপায় ছিল ভারত-পাকিস্তান বিভাজন নয়, ভারতে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী স্বাধীন রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠা, যে-রাষ্ট্রগুলাে স্বেচ্ছায় এবং বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার সংরক্ষিত রেখে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারতাে, যেমনটি বর্তমানে ইউরােপের স্বাধীন রাষ্ট্রগুলাে গড়বার চেষ্টা করছে, ইউরােপীয় ইউনিয়ন স্থাপনের মধ্য দিয়ে।
এই রকম একটি প্রস্তাব ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি দিয়েছিল। কিন্তু সেটা এসেছিল অনেক বিলম্বে। ততদিনে দেশভাগের বন্দোবস্ত কংগ্রেস, লীগ, ব্রিটিশ সরকার এই তিন পক্ষ মিলে পাকাপাকি করে ফেলেছে। তাছাড়া পার্টি নিজেও জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে একধরনের বিভ্রান্তির শিকার হয়েছিল, যে জন্য তারা ভারতের বিভিন্ন জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীতুলেছিল ঠিকই, কিন্তু অল্পদিনের জন্য হলেও ধর্মকে জাতীয়তার প্রধান উপাদান বলে ধারণা করেছিল। যে-বিবেচনায় ভারতের মুসলমানদেরকে তারা একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে ধরে নিয়েছিল, এবং ধরে নিয়ে মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়ােজনে স্বতন্ত্র বাসভূমির অর্থাৎ পাকিস্তানের দাবীকে এক ধরনের সমর্থন দিয়েছিল। তাদের এই ভ্রান্ত নীতি ১৯৪২ থেকে কার্যকর ছিল; ১৯৪৬ এর শুরুতে পার্টি এই ভুল সংশােধন করে।১৯৪৭-এর মে মাসেকমিউনিস্ট পার্টিরবঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি বাংলাকে ভাগ করার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই সময়ে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক পি সি যােশী ও পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক ভবানী সেন একটি যুক্তবিবৃতিতে বাংলায় হিন্দু-মুসমানের ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে শরৎ বসু ও আবুল হাশিম যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তার প্রতি সমর্থন জানান।৪
এই বিরােধিতায় অবশ্য ‘জাতীয়তাবাদী’ ইতিহাসবিদরা বিরক্তই হয়েছেন; রমেশচন্দ্র মজুমদার তাে মন্তব্যই করেছেন যে, কমিউনিষ্টরা ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ক্ষতি করেই সন্তুষ্ট ছিল না, তারা ভারতের ঐক্যকেও ধ্বস করতে চেয়েছিল।৫ সােভিয়েট ইউনিয়নের সংবিধানে ১১টি ভাষাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল, এবং সকল জাতিসত্তাকেই অধিকার দেওয়া হয়েছিল প্রয়ােজনবােধে বিচ্ছিন্ন হবার। এই ব্যবস্থা ছিল পরিপূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক, কমিউনিস্ট পার্টি তেমন ব্যবস্থাকে সমর্থন করে যেসঠিক কাজই করার উদ্যোগ নিয়েছিল সেটা তখন পরিষ্কারভাবে বােঝার উপায় ছিল না ঠিকই, কেননা তখন মানুষ দ্বি-জাতিতত্ত্বের পক্ষে-বিপক্ষে উত্তেজিত, কিন্তু এখন যখন ভারতে (এবং পাকিস্তানেও) বিভিন্ন জাতিসত্তা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার চাইছেতখন ওই বহুজাতিক ব্যবস্থার বাস্তবতাউপযােগিতা ধরা পড়ছে বৈকি।
বিভ্রান্তিটা মােটেই অস্বাভাবিকছিলনা। দ্বি-জাতিতত্ত্বের ব্যাপারে অনমনীয় যে মােহম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮) তিনিও প্রথমে মনে করতেন ভারতে দুটি সম্প্রদায় আছে ঠিকই, কিন্তু তাই বলে তারা যে দু’টি স্বতন্ত্র জাতি তা নয়। এমনকি ১৯৪৪ সালে যখন পাকিস্তানের জন্য তিনি তীব্র আন্দোলন করছেন, তখনও ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অল্প কিছুদিন আগে বিলেতের নিউজ ক্রনিকল’কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তাকে বলতে শুনি,
“এত বিশাল এই দেশকে যেখানে ২০টি বিভিন্ন জাতি এবং ২০টি বিভিন্ন ভাষা রয়েছে তাকে একটি সংহত ও স্থায়ী সাম্রাজ্যের মধ্যে গ্রথিত সন্নিবদ্ধ করা যায় এসব কথা যে ব্যক্তির সামান্যতম সাধারণ বুদ্ধি আছে সে কি বিশ্বাস করতে পারে?”৬
ভারতকে এক রাখা সম্ভব নয় এটা তিনি বলছেন, এ-কথা অন্যরাও মানতেন; এর একটা সমাধান হতে পারতাে প্রদেশগুলােকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন, যে-প্রস্তাব কিন্তু জিন্নাহ করেছিলেনও, ১৯২৮ সালে, তার সুপিরিচিত ১৪ দফায়, যা কংগ্রেস তখন মােটেই গ্রহণযােগ্য মনে করে নি। ১৯৪৪ সালের জিন্নাহর বক্তব্যটিতে যা তাৎপর্যপূর্ণ তা হলাে, এই স্বীকৃতি যে ভারত এক বা দু’জাতির দেশ নয়, এখানে প্রায় ২০টি জাতি আছে এবং এই জাতিগুলাের ভিত্তি ধর্ম নয়, ভাষা। . বিভ্রান্তি প্রসঙ্গে আবার আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ফেরত যাবাে। ভাষার ব্যাপারে বঙ্কিম অত্যন্ত সচেতন ছিলেন, তার পক্ষে বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হওয়া খুবই সঙ্গত ছিল। কিন্তু সেটা তিনি হতে পারলেন না। তার কারণ হচ্ছে তার পক্ষে ধর্ম তথা ব্রাহ্মণ্য বর্ণবাদকে পরিত্যাগ করতে না-পারা। এদিক থেকে তিনি যে কেবল উদাহরণ তাই নন, মতাদর্শগতভাবে প্রভাবকও বটেন। ‘বন্দেমাতরম’ রণধ্বনি তাঁরই রচনা। ওই গান তিনি আনন্দমঠ উপন্যাস লেখার আগেই লিখেছিলেন; এবং গানটিতে তিনি যেমাতৃভূমির বন্দনা করেছেন, সেই সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা ভূমি, তার শুভ্র-জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনী, ফুল্লকুসুমিত মদলশােভিত সুহাসিনী সুমধুরভাষিণী সুখদায়িনী মূর্তি, সেটি মােটেই সারা ভারতের নয়, অতিঅবশ্যি বাংলাদেশের; আর যে সপ্তকোটী কণ্ঠ এবং হদ্বিসপ্তকোটী বাহুর উল্লেখ করেছেন সেই সাত কোটি তখন বাংলাদেশের জনসংখ্যা বটে, যার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর অন্তত সমান সমান। কিন্তু তবু তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বাংলার কথা বলতে পারলেন না, বললেন কেবল হিন্দুর কথাই, মুসলমান পাঠক তাকে সাম্প্রদায়িক বলে বিবেচনা করতে বাধ্য হলাে। এই ঘটনার জন্য তিনি ব্যক্তিগত ভাবে যতটা না দায়ী তার চেয়ে বেশী দায়ী হচ্ছে তার সময় ও শ্রেণী। সময় ও শ্রেণীর প্রভাব তিনি গ্রহণ করেছেন, এমনকি ওই দুয়ের মুখপাত্রই হয়ে উঠেছেন। ব্যাপারটা বাঙালীকে ভাষার ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদ গড়ে তােলার জন্য সাহায্য তাে করলােই না, বরঞ্চ সেই সম্ভাবনাকে বিঘ্নিত করলাে।
বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে গঠিত হতে দেখেছেন, কিন্তু কংগ্রেসের রাজনীতিতে তার আস্থা ছিল না, না-থাকার কারণ বােঝা শক্ত নয়। প্রথম কংগ্রেস জনগণের প্রতিষ্ঠান ছিল না, দ্বিতীয়ত কংগ্রেসের রাজনীতি ছিল আবেদন-নিবেদন-প্রতিবেদনের; বঙ্কিম জনগণের কথা ভাবতেন এবং তার সমর্থন ছিল আনন্দমঠের সন্ন্যাসীরা যে-ধরনের সশস্ত্র অভ্যুত্থান করেছে তার প্রতি। কিন্তু সে-সমর্থনের কথা বলার সুযােগ ছিল না। সিপাহী অভ্যুত্থানের সময়কার সেই অসামান্য নারী, আঁসীর রানীর উল্লেখ করে তিনি এমন কথা বলেছেন, আমার ইচ্ছা হয় একবার সে চরিত্র চিত্র করি কিন্তু এক আনন্দমঠেই সাহেবরা চটিয়াছে তাহলে আর রক্ষে থাকবে না।৭
চটেছিল এটা ঠিক, আনন্দমঠকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হতে পারে এমনও শােনা গিয়েছিল; সরকারী চাকরিতে তিনি প্রত্যাশিত পদোন্নতি লাভ করেন নি এটাও সত্য। তাছাড়া শ্রেণীগত বিবেচনায় ইংরেজকে যে উপকারী মনে করেছেন সেটাও ঠিক। স্বাধীনতার স্পৃহা বঙ্কিমের ভেতর খুবই প্রবল ছিল, প্রকৃত শত্রু যে ইংরেজ তাও যে জানতেন না তা নয়, কিন্তু তাকেশত্রু বলে চিহ্নিতকরা সম্ভব ছিলনা, বিপদ ছিল একাধিক দিয়ে। আনন্দমঠ-এ তাই মুসলমানই শত্রু হয়ে দাঁড়ল। তার চির দুঃখী কৃষক পরাণ মণ্ডল ও হাসিম শেখকে তিনি একত্র দাঁড়াতে সাহায্য করতে পারলেন না। শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্তের পক্ষে ওই উপন্যাসকে যেমন উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি, তেমনি তাকে সহজ ভাবে গ্রহণ করারও উপায় ঘটেনি। উপন্যাসের শেষখণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে আছে,
“সকলে বলিল, মুসলমান পরাভূত হইয়াছে, দেশ আবার হিন্দুর হইয়াছে। সকলে একবার মুক্তকণ্ঠে হরি হরি বল। গ্রাম্য লােকেরা মুসলমান দেখিলেই তাড়াইয়া মারিতে যায়। কেহ কেহ সেই রাত্রে দলবদ্ধ হইয়া মুসলমানদিগের পাড়ায় গিয়া তাহাদের ঘরে আগুন দিয়া সর্বস্ব লুটিয়া লইতে লাগিল। অনেক যবন নিহত হইল, অনেক মুসলমান দাড়ি ফেলিয়া গায়ে মৃত্তিকা মাখিয়া হরিনাম করিতে আরম্ভ করিল। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে লাগিল, ‘মুই হেঁদু’।”
ছবিটা দাঙ্গার বটে। অনেকটা একালে গুজরাতে যেমনটা ঘটেছে তার পুরগামী চিত্র যেন। এর একটু পরেই আবার ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় জানা যাচ্ছে,
“মুসলমানেরা বলিতে লাগিল, ‘আল্লা আকবর! এতনা রােজের পর কোরানশরিফ বেবাকিঝুঁটো হলাে; মােরা যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ করি, তা এই তেলককাটা হেঁদুর দল ফতে করতে নারলাম। দুনিয়া সব ফাকি।”
এ সব বর্ণনায় যে-হাস্যরস আছে তা সিপাহী যােদ্ধাদেরকে নিয়ে ঈশ্বরগুপ্তের ব্যঙ্গবিদ্রুপের চেয়েও তীব্র, এবং মুসলমান পাঠকদের সদ্যজাত স্পর্শকাতর আত্মসচেতনতার জন্য পীড়াদায়ক। আনন্দমঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, একাধিক ভারতীয় ভাষায়-এর অনুবাদ করা হয়েছে। তবে এই জনপ্রিয়তার ব্যাখ্যা কেবল সাহিত্যমূল্য দিয়ে কর যাবে না, ব্যাখ্যার জন্য বক্তব্যমূল্যকেও বিবেচনা করতে হবে। আর যে-কারণে এই গ্রন্থহিন্দু পাঠকের কাছেঅত প্রিয় ঠিক সেই কারণ তাে বটেই তার সঙ্গে উল্টো মুসলমানকে উপহাস্য করে তুলবার অতিরিক্ত ঘটনার দরুনও মুসলমান পাঠক এর প্রতিবিরূপ হয়েছে; বাংলার নানা জায়গায় একে পােড়ানােও হয়েছে, কোথাও কোথাও ‘বদ্যুৎসব’ও ঘটেছে।
বন্দেমাতরম গান যে মুসলমানের কাছে গ্রহণযােগ্য হবে না তার একটা কারণ আনন্দমঠেরসঙ্গে এর সংলগ্নতা; দ্বিতীয় (এবং সেটাই প্রধান) কারণহলাে গানেমাতৃভূমিকে যেভাবে দেবী হিসাবে বন্দনা করা হয়েছে তার ‘পৌত্তলিকতা’। বন্দেমাতরম তাই মুসলমানকে আকৃষ্ট তাে করেইনি, বরঞ্চউল্টো ‘আল্লা হাে আকবর’ ধ্বনি দিয়ে বিপরীত অবস্থান নিতে উদ্বুদ্ধ করেছে।
বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙালীত্ব বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। তিনি ইংরেজী ভাষার পেছনে মােটেই ছােটেন নি, আগাগােড়া মাতৃভাষার চর্চা করেছেন। সাহিত্যের ইতিহাসবিদরা লক্ষ্য করেছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম স্বদেশকে মাতৃভূমি এবং স্বভাষাকে মাতৃভাষারূপে আখ্যায়িত করেন। এর আগে বাঙালীরাই বাংলাকে বলত ভাষা, লৌকিক ভাষা, দেশী ভাষা, বঙ্গীয় ভাষা, গৌড়ীয় ভাষা ইত্যাদি। সন্দেহ নেই যে বাংলা সাহিত্যে তার স্থানও অবদান রবীন্দ্রনাথের পরেই; কিন্তু তবুদুর্ভাগ্য এই শেষপর্যন্ত হিন্দুত্ব ঘােচানাের অপারগতার দরুন তিনি অত্যন্ত আধুনিক হয়েও পরিপূর্ণরূপে বাঙালী হতে পারলেন না; অন্ততপক্ষে অংশত হিন্দুই রয়ে গেলেন। পেছনে ছিল আর্যত্বের অভিমান, ভেতরে ছিল স্বাধীনতার প্রবল স্পৃহা ও সেই সঙ্গে সাম্যের ব্যাপারে গভীর ভীতি, ছিল আত্মপরিচয় নিয়ে দোদুল্যমানতা, এবং ধর্মের কাছ থেকে সেই আশ্রয় ও গৌরব প্রাপ্তির আগ্রহ, ধর্ম যা বিশ্বাসীদেরকে আনায়াসে সরবরাহ করে থাকে।
বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই নিজেদেরকে একই সঙ্গে বাঙালী ও ভারতীয় হিসাবে দেখতে চেয়েছেন, যদিও বাংলার কথাই অবশ্য তারা অনেক বেশী ভেবেছেন ভারতের চেয়ে, এবং অনেক সময়েই বাংলাকে বিবেচনা করেছেন ভারতের অংশ হিসাবে। কিন্তু তবু তাদের বাঙালীত্ব ও ভারতীয়ত্বের মধ্যে একটি অনিবার্য বিরােধ ছিল বৈকি; বিরােধটা এই যে ভারতীয়ত্বের মূল বন্ধনই হলাে ধর্মের, যেখানে বাঙালীত্বের ভিত্তি হচ্ছে ভাষা। আবারাে স্মরণ করা দরকার যে, সমস্যাটি কেবল ব্যক্তির ছিল না, ছিল সমসাময়িক ইতিহাসের এবং শ্রেণীরও। বাঙালীর ইতিহাস ও উৎপত্তি অনুসন্ধানের বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। ‘বাঙালীর উৎপত্তি’ নামের নিবন্ধের সপ্তম পরিচ্ছেদে ‘স্থূলকথা’ নাম দিয়ে তিনি লিখছেন –
“বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা যাহা পাইয়াছি। সে তাহার পুনরুক্তি করিতেছি। ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ভারতীয় এবং ইউরােপীয় ও প্রধান জাতিসকল এক প্রাচীন আৰ্য্যবংশ হইতে উৎপন্ন। যাহার ভাষা আৰ্যভাষা, কি সেই আৰ্য্যবংশীয় বাঙ্গালীর ভাষা আৰ্য্যভাষা, এজন্য বাঙ্গালী আৰ্য্যবংশীয় জাতি।”
কিন্তু তাই বলে সবাই যে আৰ্য্য এমন তাে বলবার উপায় নেই, কেননা বাস্তব দৃশ্য সরবে তেমন ধারণার বিরােধিতা করে। তাই তিনি মানছেন –
“মা কিন্তু বাঙ্গালী অমিশ্রিত বা বিশুদ্ধ আৰ্য্য নহে। ব্রাহ্মণ অমিশ্রিত এবং বিশুদ্ধ আৰ্য্য সন্দেহ নাই, কেননা, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ হইতেই উৎপত্তি সম্ভাবনা, সঙ্করত্ব ঘটিলে ব্রাহ্মণত্ব যায়।”
চোখের সামনে ইংরেজরা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ রূপে এবং ব্যক্তি হিসাবে নয় কেবল জাতি হিসাবেই বিদ্যমান ছিল তাই ইংরেজের জাতিগঠন এবং বাঙালীর জাতিগঠনের মধ্যে তুলনায় বিষয়টি এসেছে। এবং সেখানে তিনি দুটি বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন—
“টিউটন হউক বা নৰ্মান হউক যতগুলি জাতির সংমিশ্রণে ইংরেজ জাতি প্রস্তুত কি হইয়াছে, সকলগুলিই আৰ্য্যবংশীয়। বাঙ্গালী যে কয়েকটি জাতিতে গঠিত হইয়াছে, তাহার কেহ আৰ্য, কেহ অনাৰ্য। দ্বিতীয় প্রভেদ এই যে,ইংলন্ডে টিউটন ও ডেন ও নৰ্মান, এই তিন জাতির রক্ত একত্রে মিশিয়াছে। পরস্পরের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধের দ্বারা মিলিত হইয়া তাহাদিগের পার্থক্য লুপ্ত হইয়াছে। তিনে এক জাতি দাঁড়াইয়াছে; বাছিয়া তিনটি পৃথক করিবার উপায় নেই। মােটের উপর এক ইংরেজ জাতি কেবল পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতীয় আর্য্যদিগের বর্ণধৰ্মিত্ব হেতু বাঙ্গালায় তিনটি পৃথক স্রোত মিশিয়া একটি প্রবল প্রবাহে পরিণত হয় নাই; আৰ্যসম্ভুত অন্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক রহিয়াছেন।…(তাই) ইংরেজএকজাতি, বাঙ্গালীরা বহুজাতি।”
জাতীয়তা নির্ধারণে ভাষার প্রশ্নটি আসছে, কিন্তু ভাষার চেয়ে বড় হয়ে উঠছে বর্ণ, এবং ভাষাও আবার বর্ণের অর্থাৎ রক্তের পরিচয়কেই উদ্যাটিত করছে। ধরা পড়ছে এই সত্য যে, ভারতীয় এবং ইউরােপীয় প্রধান জাতিসকল এক প্রাচীন আৰ্য্যবংশ হইতে উৎপন্ন। অর্থাৎ ইংরেজদের সাথে ভারতীয় (এবং বাঙ্গালী) ব্রাহ্মণের বর্ণগত পার্থক্য নেই, পার্থক্য যা তা অবস্থানগত, ঘটনাক্রমে ইংরেজ এখন শাসক, ব্রাহ্মণ শাসিত। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মরণরাই ছিল ইংরেজ, তারা সরাসরি শাসক না হােক, আমলা তাে ছিল বটেই।বঙ্কিমচন্দ্র এমনকি আর্যরক্তের কথাও বলছেন, রক্ত দিয়ে জাতি নির্ধারণের তত্ত্বকে সমর্থন করেছেন, পরবর্তীকালে যে তত্ত্ব জার্মান বর্ণবাদীদের হাতে পড়ে প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিয়েছে। ওই নিবন্ধেরই আরেক জায়গায় বলা আছে। (প্রথম পরিচ্ছেদের শেষ বাক্য।)
“যে রক্তের তেজে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিসকল শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, বাঙ্গালীর শরীরেও সেই রক্ত বহিতেছে।”
এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে, ইংরেজ জাতি যে এক সেটা কিন্তু রক্তের পরিচয়ে নয়, ভাষার পরিচয়ে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা এ্যালান হিউম রক্তের পরিচয়ে স্কটিশ ছিলেন, কিন্তু ভাষার কারণে তাকে ইংরেজই মনে করা হতাে; হিউম ক্যাথলিক, প্রটেস্টান্ট নাকি অ্যাঙ্গলিকান ছিলেন এ নিয়ে কোনাে প্রশ্নই ওঠেনি।
কিন্তু সকল বাঙালী যে আৰ্য্য রক্তপ্রবাহ লাভে সৌভাগ্যবান নয় সেটাও তাে সত্য, যে জন্য অনিচ্ছুক বঙ্কিমকে মানতেই হচ্ছে যে,
“তা বাস্তবিক এক্ষণে যাহাদিগকে আমরা বাঙ্গালী বলি, তাহাদিগের মধ্যে চারি প্রকার বাঙ্গালী পাই। এক আৰ্য, দ্বিতীয় আনাৰ্য্য হিন্দু, তৃতীয় আৰ্য্যানাৰ্য্য হিন্দু, আর তিনের বার এক চতুর্থ জাতি বাঙ্গালী মুসলমান; উপরের স্তরে প্রায় কেবলই আৰ্য। এই জন্য দূর হইতে দেখিতে বাঙ্গালী জাতি অমিশ্ৰিত আৰ্যজাতি বলিয়াই বােধ হয় এবং বাঙ্গালার ইতিহাস এক আৰ্য্যবংশীয় জাতির ইতিহাস বলিয়া লিখিত হয়।”
দূর থেকে দেখলে মনে হবে সবাই আর্য, কিন্তু কাছে গেলে টের পাওয়া যাবে না যে ঘটনা অন্যরকম। তুলনায় আর্যের সংখ্যাই কম, অনেকেই অনার্য, কেউ কেউ আর্য ও অনার্যের মিশ্রণ, অর্থাৎ আৰ্যানার্য। কিন্তু একটা খাড়াকাড়ি ভাগ রয়েছে, সেটা হিন্দু ও মুসলমানের, ‘তিনের বার এক চতুর্থ জাতি বাঙ্গালী মুসলমান।’ তাহলে হিন্দু মুসলমান এক জাতি হবে কি করে, কোন উপায়ে? তারা তাে পরস্পর থেকে বর্ণ ও ধর্ম উভয়েই দ্বারাই বিভক্ত। বােঝা যাচ্ছে বঙ্কিম বাঙালীকে এক ও অবিভাজ্য মনে করেন নি।
‘ভারত-কলঙ্ক’ নামে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট করেই বলেছেন, আত্মপরিচয়ের কথাটা –
“আমি হিন্দু, তুমি হিন্দু, রাম হিন্দু, যদু হিন্দু, আরও লক্ষ লক্ষ হিন্দু আছে। এই লক্ষ লক্ষ হিন্দুমাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল, তাহাতেই আমার মঙ্গল। যাহাতে তাহাদের মঙ্গল নাই, আমারও তাহাতে মঙ্গলনাই। অতএব সকল হিন্দুর যাহাতেমঙ্গল হয় তাহাই আমার কর্তব্য।…এই জ্ঞান জাতিপ্রতিষ্ঠার প্রথম ভাগ; অর্ধাংশ মাত্র।”
এটা তাে গেল জাতিপ্রতিষ্ঠার প্রথম ভাগ, অর্ধাংশ মাত্র। বাকি অর্ধেক অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাগ রীতিমত ভয়ঙ্কর –
“হিন্দুজাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গলমাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাতে না হয় আমরা তাহাই করিব।”
উগ্রজাতীয়তাবাদী তাে বটেই, এ বক্তব্যকে ফ্যাসিবাদের পূর্বসুরী বললে আপত্তি করবার পক্ষে যুক্তি পাওয়া কঠিন হবে। পরবর্তীকালে হিন্দু মহাসভা ও ভারতীয় জনতা পার্টি এ ধরনের মতবাদ নিয়েই রাজনীতি করেছে। বঙ্কিম নিজে অবশ্য রাজনীতিক নন, কিন্তু তার বক্তব্য বর্ণবাদী ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে সাহায্য করেছে বৈকি।
বর্ণবাদের ত্রুটি কোথায়, তা কি এই অসামান্য দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষটি, যাকে বলা হয়েছে ‘শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ’, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রজুয়েটদের যিনি একজন, জন স্টুয়ার্ট মিলের মৃত্যুতে বঙ্গদর্শনে যিনি লিখেছিলেন, “আমাদিগের মনে হইতেছে যেন আমাদিগের কোন পরম আত্মীয়ের সহিত চিরবিচ্ছেদ হইয়াছে”, কোতের পজিটিভিজম সম্পর্কে যিনি অবহিত ছিলেন, তিনি জানতেন না? জানতেন না এমন মনে করবার কারণ দেখি না। ‘সাম্য’ নামের সেই বিখ্যাত নিবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্র তাে পরিষ্কার বলেছেন –
“পৃথিবীতে যত প্রকার সামাজিক বৈষম্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ভারতবর্ষের এ পূৰ্ব্বকালিক বর্ণবৈষম্যের ন্যায় গুরুতর বৈষম্য কখন কোন সমাজে প্রচলিত হয় নাই। কিন্তু ইনি হচ্ছেন আগের বঙ্কিমচন্দ্র, যখন তিনি সাম্যে আগ্রহী, ‘সাম্যাবতার’ রুশােকে বুদ্ধদেবও যিশুখ্রিস্টের সমান মনে করেছেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন কিনা সন্দেহ, এবং যখন তিনি বঙ্গদেশের কৃষকের দুর্দশায় গভীরভাবে পীড়িত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এই বঙ্কিমচন্দ্র পরে বদলে গেছেন, পরে তিনি ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদী হয়ে উঠেছেন, তাঁর রচনায় বর্ণবাদিতা প্রশ্রয় ও প্রকাশ পেয়েছে। পরিবর্তিত বঙ্কিম ‘সাম্য’ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, ‘সাম্যটা ভুল, খুব বিক্রি হয় বটে, কিন্তু আর ছাপব না।”৯ ওই সিদ্ধান্তে তিনি অটল ছিলেন, তাঁর জীবনকালে ওই বই আর ছাপা হয় নি।”
এই পরিবর্তিত বঙ্কিমচন্দ্র অনেকের কাছেই ‘ঋষি’ বলে বিশেষভাবে গণ্য ও শ্রদ্ধেয় হয়েছেন। স্বদেশী আন্দোলনের জাতীয়তাবাদী অনুপ্রেরণার ওপর তিনি গভীর প্রভাব ফেলেছেন, এবং যে বর্ণবাদী ও সাম্প্রদায়িকতা হিন্দু মুসলমানকে একই জাতির অন্তর্গত প্রতিবেশী দুই সম্প্রদায় হিসাবে না-দেখে পরস্পরবিরােধী দুটি জাতি হিসাবে দেখতে চেয়েছেন সেই চিন্তাধারা তাঁর লেখায় সমর্থন খুঁজে পেয়েছে। আর দেশভাগ ও ভারতবিভাগের জন্য ওই সাম্প্রদায়িকতাই যে দায়ী সেটা তাে আমরা দেখতেই পেয়েছি। দুই সম্প্রদায়কে দুই জাতি মনে করার ধারাটি দেশভাগের পরে যে শেষ হয়ে গেছে তা নয়, পূর্ববঙ্গে অবশ্য ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কিন্তু এমনকি আধুনিক ইতিহাসবিদদের মধ্যেও এখনাে অনেকে আছেন যাঁরা মনে করেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের যে ধারণা ছিল সেই ধারণা মিথ্যা ছিল না, এবং হিন্দু-মুসলমান সত্যি সত্যি বর্ণদ্বারা বিভক্ত। যেমন, ‘নিম্নবর্গের নতুন ধারার ইতিহাসবিদদের মধ্যে একজন, দীপেশ চক্রবর্তী, তার হ্যাবিটেশনস অব মডানিটি, এসেজ ইন দি ওয়েক অব সাবঅলটার্ন স্টাডিজ (শিকাগাে, ২০০২) বইতে বাংলার হিন্দু-মুসলমান বিভাজনকে ‘পলিটিক্স অব এথনিসিটি’ বলেই চিহ্নিত করেছেন।
‘ভারত-কলঙ্ক’ প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন যে, ইংরেজ বাঙালীকে অনেক নতুন কথা শিখিয়েছে। “সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য।” যে-সকল অমূল্য শিক্ষা ইংরেজের চিত্তভাণ্ডার থেকে পাওয়া গেছে তার মধ্যে একটি হলাে স্বাতন্ত্র-প্রিয়তা অপরটি ‘জাতিপ্রতিষ্ঠা’। পাদটীকায় তিনি বলছেন ‘জাতি শব্দে Nationality বা Nation বুঝিতে হইবে।’ তাঁর প্রবন্ধটি পড়ে এটা মনে হয় যে ‘স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা’ বলতে তিনি বােঝাচ্ছেন আত্মসচেতনতা বা আত্মজ্ঞানকে। বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন যে, ইংরেজ আসার আগে এই দুটি বিষয় সম্পর্কে ‘হিন্দু’রা কিছুই জানতাে না। তিনি বাঙালীর কথা বলেন নি, আবারাে হিন্দুর কথাই বলেছেন। বস্তুত এই যে নবজাগ্রত আত্মসচেতনতা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠায় আগ্রহ ওই বােধ দুটিই বাঙালী হিন্দুকে বাঙালী হওয়ার পরিবর্তে হিন্দু হওয়ার দিকে পরিচালিত করলাে। এবং সেই যাওয়াটা ত্বরান্বিত হলাে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনের ভেতর দিয়ে।
অরবিন্দ ঘােষের ভূমিকাকে বিবেচনার মধ্যে আনলে কেবল যে বঙ্গভঙ্গ-বিরােধী আন্দোলনের আলােচনা অসম্পূর্ণ থাকবে তা-ই নয়, দেশপ্রেমিকের সঙ্গে ধর্ম কিভাবেও কি পরিমাণে যুক্ত হলাে সেটাও পুরােপুরি বােঝা যাবে না। অরবিন্দ ঘােষের এবং তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রনাথ ঘােষের (১৮৮০-১৯৫৯) চিন্তায় স্বাধীনতার জন্য আকাঙ্ক্ষা ছিল অত্যন্ত তীব্র। পরবর্তীকালে সুভাষ বসু যা করেছিলেন, অরবিন্দও তেমন কাজ দিয়েই রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন, তিনি আইসিএস হবার সম্ভাবনাকে নাকচ করে দয়ে বিলাত থেকে ভারতে চলে আসেন এবং বঙ্গভঙ্গবিরােধী আন্দোলনে যােগ দেন। কিন্তু দু’জনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একেবারেই পৃথক। অরবিন্দ রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের সংমিশ্রণে আগ্রহী ছিলেন, সুভাষের অবস্থান ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত প্রান্তে।

অরবিন্দ চরমপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর চিন্তায় আপােসের কোনাে জায়গা ছিল না। ১৯০৭ সালে অরবিন্দ বলেছেন,
“প্রথমে এবং সবার আগে চাই রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে লক্ষ্যবস্তু হিসাবে গ্রহণ করা; তা না করে জাতির (race) সামাজিক সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার, শিল্পে প্রসার ও নৈতিক উন্নতির চেষ্টা করাটা চরম অজ্ঞতা ও অর্থহীনতা ভিন্ন অন্যকিছু নয়।”
লক্ষ্য করবার বিষয় জাতি বলতে তিনিও race-এর কথা বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ধারণাগত এই মিলটা নিতান্তই যে কাকতালীয় তা কিন্তু নয়। অরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্র দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। স্বদেশী যুগে যে দৈনিক পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করতেন তার নাম বন্দেমাতরম। বঙ্কিমকে তিনি ঋষি হিসাবে দেখতেন, এবং সেভাবে দেখার দরুন শিল্পী বঙ্কিমের চেয়ে ধর্মতাত্ত্বিক বঙ্কিমকে অনেক উচ্চ স্থান দিতেন। অরবিন্দ আবেদন-নিবেদন-প্রতিবেদনের রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন না। তার দুই ভাই যুক্ত ছিলেন গােপন বিপ্লবী দলের সঙ্গে। প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারত থেকে সাম্রাজ্যবাদীদেরকে বিতাড়িত করা। তিনি সর্বহারার কথা বলেছেন, তার চিন্তায় সমাজতন্ত্রও ছিল, কিন্তু সে-সমাজতন্ত্র বৈজ্ঞানিক নয়, সেটি ভারতীয়, অর্থাৎ ধর্মভিত্তিক। যে-সমাজতন্ত্রের পক্ষে প্রথম পদক্ষেপইহজগতিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা সেটাকে তারা মানতেন না। তার সংগ্রামটা তাই ছিল ধর্মকে ভিত্তি করে গড়ে-ওঠা জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম।
ভেতরের ব্যাপারটা সুস্পষ্টভাবেই বের হয়ে এলােতখন যখন তিনি বিপ্লবীতৎপরতার অভিযােগে কারারুদ্ধ হলেন। বিচারাধীন আসামী হিসাবে প্রেসিডেন্সি জেলে বছর খানেক ছিলেন। সেখানে তার অন্তর্গত আধ্যাত্মিকতা বিপ্লবী আগুনকে ছাপিয়ে প্রবল হয়ে উঠলাে, কারাগার থেকে জানালা দিয়ে তাকিয়ে তিনি গাছের ডালে ডালে শ্রীকৃষ্ণকে দোদুল্যমান দেখতে পেলেন এবং নিজে পুরােপুরি ধার্মিক হয়ে উঠলেন। কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে অরবিন্দ দেখেন বাইরে তেমন আন্দোলন নেই, সবটা কেমন চুপচাপ। এর মধ্যে আবার শােনা গেলাে তাকে পুনরায় গ্রেফতার করা হতে পারে। গ্রেফতার এড়ানাের জন্য বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে অরবিন্দু ব্রিটশ-শাসিত ভারতেই আর থাকলেন না, প্রথমে গেলেন ফরাসী শাসিত চন্দননগরে, সেখান থেকে পণ্ডিচেরীতে। পণ্ডিচেরীতে তার কাজটা দাঁড়ালাে পুরােপুরি অরাজনৈতিক, এবং ‘সর্বাত্মকরূপে আধ্যাত্মিক’ ভারতের স্বাধীনতার জন্য তিনি প্রার্থনা, যােগসাধনা, গ্রন্থরচনা ইত্যাদি কাজে মগ্ন হলেন।তার রাজনৈতিক জীবন অকালেই শেষ হয়ে গেলাে।এবং তিনি ঋষি হয়ে উঠলেন। আনন্দমঠেরমহাপুরুষ আশ্রম গড়েছিলেন হিমালয়-শিখরে, অরবিন্দ গড়লেন সমুদ্রের তীরে।
এর আগে, কারামুক্তি উপলক্ষে কলকাতায় আয়ােজিত এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে অরবিন্দ তাঁর নতুন অবস্থানটি বেশ পরিষ্কার ভাবেই তুলে ধরেছিলেন,
“আমি তাে আগেই বলেছিলাম যে এই আন্দোলন কোনাে রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, বলেছিলাম যে জাতীয়তাবাদ জিনিসটা রাজনীতি নয়, এ হচ্ছে একটি ধর্ম, একটি জীবনদর্শন, একটি বিশ্বাস। কথাটা আমি আবারাে বলছি, যদিও অন্যভাবে। এখন আমি আর বলি না যে জাতীয়তাবাদ হচ্ছে একটি জীবনদর্শন, একটি ধর্ম, একটি বিশ্বাস; আমি বলি যে আমাদের জন্য সনাতন ধর্মই হচ্ছে জাতীয়তাবাদ।১২ জাতীয়তাবাদ তাে সব সময়েই রাজনীতির ব্যাপার, কিন্তু অরবিন্দ ঘােষদের কাছে সেটা আর রাজনীতি রইলাে না, পরিণত হলাে ধর্মে। এই ধর্মও আবার সনাতন হিন্দু ধর্ম, যাতে বঙ্কিমচন্দ্র আস্থা রাখতেন, এবং যার চর্চা ছাড়া জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয় বলে তারা মনে করতেন।”
দেশপ্রেমের সঙ্গে ধর্মকে মিশিয়ে ফেলার ব্যাপারটা অরবিন্দের একার ক্ষেত্রে ঘটে নি। তখনকার বিপ্লবী আন্দোলনের ভেতরেই তা ছিল। আন্দোলনকারীরা আনন্দমঠের সন্ন্যাসীদের দৃষ্টান্ত থেকে অনুপ্রেরণা পেতেন; তারা মন্দিরে গিয়ে কালী মূর্তিকে সাক্ষী রেখে বিপ্লবে দীক্ষা নিতেন। – মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তার রাজনৈতিক আত্মজীবনীতে স্মরণ করেছেন যে, যুবক বয়সে কলকাতায় তিনি বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন এবং অরবিন্দের সঙ্গে একাধিকবার তার সাক্ষাত হয়। ফল দাঁড়িয়েছিল এই যে, তিনি ওই আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং একটি দলে যােগ দেন। তিনি দেখেছেন যে বিপ্লবীরা সকলেই হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লােক, এবং টের পেয়েছেন সেকটি দলই সক্রিয়ভাবে মুসলিম বিদ্বেষী।৩ তাঁর অভিজ্ঞতা যে ব্যতিক্রমধর্মী ছিল না, সেটা না-বললেও চলে।
আধুনিক যুগে বিপ্লবী আন্দোলনের আলােচনায় ভেডিমার ইলিচ লেনিন (১৮৭-১৯২৪) অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। অরবিন্দের মতাে লেনিনও ছিলেন গভীরভাবে দেশপ্রেমিক এবং বিপ্লবী। দু’জন প্রায় সমবয়স্ক, অরবিন্দের জন্ম ১৮৭২-তে, লেনিনের ১৮৭০ এ। কিন্তু দু’জনের পথ কেবল যে ভিন্ন তা নয়, ছিল পরস্পর বিরুদ্ধ। লেনিনের বড় ভাই শাসা উলিয়ানভ গােপন বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন। তখনকার রুশ বিপ্লবীরা ভয়ঙ্কর রকমের উৎপীড়ক জারতন্ত্রের উচ্ছেদ চাইছিলেন; কিন্তু তারা সঠিক পথের সন্ধান খুঁজে পান নি। তরুণ বিপ্লবীদের কেউ কেউ জারকে হত্যা করার উদ্যোগ নিয়েছেন। ভেবেছেন ওটাই পথ। লেনিনের বড় ভাই ওই রকমের একটি উদ্যোগে অংশ নেওয়ার অপরাধে চারজন সহপাঠীর সঙ্গে গ্রেফতার হয়ে ফঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দেন। এই ঘটনা লেনিনকে একই সঙ্গে অত্যন্ত ব্যথিত ও গভীরভাবে চিন্তিত করে। ভাইয়ের মতােই তিনিও মনেপ্রাণে জারতন্ত্রের উচ্ছেদ চাইছিলেন, কিন্তু লেনিন ভেবে দেখলেন জার তৃতীয় আলেকজান্ডারের আগে যিনি সম্রাট ছিলেন তাঁকেও বিপ্লবীরা হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু ওই জার চলে যাওয়ায় জনগণের ভাগ্যে যে কোনাে পরিবর্তন ঘটেছে তা নয়, দ্বিতীয় আলেকজান্ডারে জায়গায় তৃতীয় আলেকজান্ডার এসেছেন, এবং সমানে অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছেন। এঁকে যদি সরানাে যায় তবে তার জায়গায় আরেকজন এসে যাবেন, কিন্তু বিদ্যমান ব্যবস্থায় কোনাে পরিবর্তন ঘটবে না। ব্যবস্থা কি করে বদলানাে, সমাজে কি করে বিপ্লব ঘটানাে যায়, সে-সম্পর্কে যখন গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন তখনই তিনি মার্কস-এঙ্গেলসের রচনার সঙ্গে বিশেষ করে কমিউনিস্ট ইস্তেহার ও পুঁজিগ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হন।বুঝতে পারেন পথ ওইটাই।
অরবিন্দরা তেমন কোনাে পথের সন্ধান পাননি। ধর্মীয় পুনর্জাগরণের যে বর্ণবাদী পথ ধরে তারা এগুলেন সেটা কোনাে পথ নয়, অন্ধকার গলি বটে। ওই অন্ধকার পথ ধরে এগুতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন পণ্ডিচেরীর আধ্যাত্মিক আশ্রমে। তাই দেখি লেনিন যখন রুশবিপ্লব ঘটানাের জন্য ধারাবাহিক কাজে নিযুক্ত, অরবিন্দ তখন যােগাভ্যাসে নিমগ্ন। সামনে এগুবেন কি, পিছন দিকে হেটে গেছেন,এবং যে আন্দোলনের হবার কথা ছিল পুরােপুরি ইহজাগতিক ও ধর্মনিরপেক্ষ, ধর্মকে যুক্ত করার ফলে তা হয়ে গেলাে বিভক্ত, বিপথগামী এবং পরিণামে দেশভাগকে অনিবার্য করে তুলবার জন্য বেশভালােভাবেই দায়ী।
অরবিন্দদের করুণ ব্যর্থতার দ্বিতীয় কারণটিও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। স্বদেশীচরমপন্থীদের ভেতর বীরত্বের কোনাে অভাব ছিল না। ক্ষুদিরাম বসু প্রফুল্ল চাকী থেকে শুরু করে বহু তরুণ-তরুণী ব্রিটিশ-বিরােধী সমস্ত কার্যক্রমে অংশ নিয়ে প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু চরমপন্থীদের সঙ্গে জনগণের কোনাে যােগ ছিল না। অত্যন্ত বিপজ্জনক সমস্ত দায়িত্ব, কাজগুলাে হয়ে দাঁড়িয়েছিল ব্যক্তিগত আত্মত্যাগের কাজ। সংগঠন যা গড়ে উঠেছে তা ছিল স্বাভাবিক কারণেই গুপ্ত; জনগণ এদের কাজের খবর পেতাে ঘটনার পরে।
বিপ্লবী লেনিনদের পার্টিও নিরাপত্তার প্রয়ােজনে গােপনেই কাজ করতাে, কিন্তু সে-পার্টির শক্ত ভিত্তি ছিল শ্রমজীবী মানুষ, ছাত্র, যুবক ও পেশাজীবী বিপ্লবীদের মধ্যে। পার্টিও ছিল অত্যন্ত সুগঠিত। তাদের পত্রিকা ছিল, প্রকাশনা ছিল। অরবিন্দ যেমন প্রেসিডেন্সি জেল থেকে বের হয়ে জনসমর্থনের অভাব এবং ব্রিটিশ সরকারের শক্তি দেখে হতাশ হলেন এবং রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে ধর্মের কাছে পুরােপুরি আত্মসমর্পণ করলেন। তেমন ঘটনা রুশ বিপ্লবীদের জীবনে ঘটে নি; কেননা একদিকে তাদের অঙ্গীকার যেমন ছিল অনমনীয় তেমনি জনসমর্থন ও সংগঠন ছিল দৃঢ় ও ক্রমবর্ধমান।…
জাতীয়তাবাদী বঙ্কিম স্বাধীনতার কথা ভাবতেন, কিন্তু সে-স্বাধীনতা শীঘ্র আসছে। এমনটা কল্পনা করবার মতাে ভরসা পেতেন না। তার ছয় দশক আগে সেই অনেক বড়মাপের দেশপ্রেমিক বাঙালী, রামমােহন রায়, যিনি স্বাধীনতা একবারেই নয়, বড় জোর ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে কোনাে একসময়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে এতটা ভাবতে পেরেছেন, তার জন্য দুঃখের বিশেষ কারণ ছিল নিজের সমাজের অর্থাৎ হিন্দু সমাজের অনৈক্য নিয়ে। স্মরণীয় যে রামমােহন ইংরেজদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এই ভেবে যে, ঈশ্বরপ্রেরিত হয়ে তারা মুসলমানদের দুঃশাসন থেকে বাংলার অধিবাসীকে। উদ্ধার করেছে। বাঙালী বলতে যিনি নিজেদের হিন্দু সম্প্রদায়কেই বুঝতেন। রামানন্দ। চট্টোপাধ্যায় ১৯০৫ সালে যা বলেছেন রামমােহন রায় সেটাকে ১৮২১ সালে অধিকতর স্পষ্ট সত্য বলেই জানতেন।
১৮২৮ সালের একটি চিঠিতে হিন্দু সমাজের দুর্বলতার কথা বলতে গিয়ে রামমােহন মন্তব্য করেছেন,
“The distinctions of castes, introducing innumerable divisions and subdivisions among them, has entirely deprived them of partriotic feeling”১৪
যাকে তিনি বর্ণ (caste) বলছেন, আসলে তা হচ্ছে শ্ৰেণী। তবে এটাও ঠিক যে তার সমাজে শ্রেণী ও বর্ণ এক হয়ে গিয়েছিল, শ্রেণীবিভাজনকে স্থায়ীরূপ দেওয়া হয়েছিল ধর্মভিত্তিক বর্ণবাদের সাহায্য নিয়ে। শ্ৰেণীকে ধর্মীয় রূপ দেওয়ার এই কৌশলটি ভারতীয় ব্রাহ্মণদের মৌলিক কৌশল এবং স্বভাবতঃই অর্থনৈতিক বা আইনী বিভাজনের তুলনায় অধিক কার্যকর। যে-ব্যক্তি ব্রাহ্মণ সে জন্মসূত্রেইব্রাহ্মণ, আর শূদ্র যে সেও জন্মের কারণেই শূদ্র —এই ধর্মীয় বিধান লঙ্ঘন করার সাধ্য কার, ঈশ্বর ভিন্ন? আর ঈশ্বর নিজেই যেহেতু এটি চালু রেখেছেন তাই এই স্থায়িত্বে বিঘ্ন ঘটায় কে? – ওই চিঠিতেই রামমােহন বলছেন যে, সংস্কার খুবই প্রয়ােজন,
“it is necessary that some change should take place in their religion, atleast for the sake of political advantage and social comfort.১৫
রামমােহন ধর্মবিশ্বাসী কিন্তু সেই সঙ্গে আবার ইহজাগতিকও, এখনকার পরিভাষায় তাকে বলা চলে রাজনৈতিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ; কেননা রাষ্ট্র ও ধর্মকে তিনি একাকার করে ফেলতে চান না; এবং নিজের সম্প্রদায়ের জন্য যা তার কাম্য তা আধ্যাত্মিক সুখ নয়, কাম্য হচ্ছে political advantage ও social comfort. রাজনৈতিক সুবিধা ও সামাজিক সুখই হচ্ছে বিবেচ্য, তাদের অধীনেই তিনি ধর্মকে রাখবেন, ধর্ম যে জীবনের ওপর কর্তৃত্ব। করবে এমনটা নয়। কিন্তু যে শ্রেণীতে তার অবস্থান সেটি তার জন্য একটি পরিষ্কার গণ্ডি টেনে দিয়েছে, যাকে লঙ্ঘন করা তাঁর মতাে অসাধারণ পুরুষের পক্ষেও সম্ভব হয় নি।
রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্য রাজনৈতিক সংগ্রামের এবং সামাজিক সুখের জন্য সামাজিক পরিবর্তন চাওয়াটাই ছিল যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু তার পক্ষে তেমন আকাঙ্ক্ষার কথা বলা ছিল অসম্ভব। কেননা রাজনৈতিক সংগ্রামের পথে যেতে হলে ব্রিটিশ-বিরােধিতায় লিপ্ত হতে হতাে, সেটা ছিল অবাস্তব। আর সমাজে পরিবর্তন আনতে চাওয়াটা হতাে বিপজ্জনক, কেননা নাড়া দিলে কে জানে হয়তাে সমাজবিপ্লবই দেখা দিতাে। সমাজ-সংস্কারে রামমােহনের অঙ্গীকার সর্বজনবিদিত; সতীদাহ নিবারণে তার ভূমিকা অনন্যসাধারণ। কিন্তু সমাজ সংস্কার আর সমাজবিপ্লব সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু; রামমােহনের সময় সামাজিক বিপ্লবের কথা ওঠে নি, বঙ্কিমের সময় দেশে না উঠুক বাইরে বিস্তর উঠেছে, এবং সে ঢেউ যে দেশে আসবে না তার কোনাে নিশ্চয়তা পাওয়া যায় নি। বিবেচনার আরাে বিষয় এই যে, তাঁর সময়ে নানা স্থানে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে, সে-বিদ্রোহে বিপ্লবের দূরবর্তী পদধ্বনি শুনতে পাবেন না এমন বধির আর যে-ই হােন বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন না।
রামমােহন ধর্মসংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন; ব্রাহ্মধর্ম মূলত তার চেষ্টাতেই প্রচলিত। হয়েছিল। এটি ছিল আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ। বােঝা যায় পেছনে উদ্দেশ্যটা ছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক। দেশপ্রেমের কথা রামমােহন ভেবেছেন, সামাজিক ঐক্যস্থাপন তার লক্ষ্যের ভেতর ছিল; কিন্তু দেশ ছিল হিন্দু সম্প্রদায় দ্বারা গঠিত, সমাজ বলতে ছিল নবােদ্ভিন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী। জাতিগঠনের উদ্যোগের দরুন জাতি নয়, গঠিত হচ্ছিল শ্রেণী। শ্রেণীর স্বার্থ প্রতিষ্ঠা পাচ্ছিল জাতির সমষ্টিগত স্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগের ভেতর দিয়ে। ওই শ্ৰেণীই পরে বঙ্গভঙ্গবিরােধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে। এগিয়েছে, কিন্তু সঠিক পথের সন্ধান পায় নি। সাম্রাজ্যবাদ বিরােধিতা টা অবশ্যই সঠিক ছিল; কিন্তু শ্ৰেণীস্বার্থকে সংহতকরণটা ছিল একেবারেই বেঠিক। তদুপরি তিনি ধর্মসংস্কারে ও শাস্ত্রীয় গ্রন্থ অনুবাদে যেভাবে নিয়ােজিত ছিলেন তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, যথার্থরূপে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি তা হনও নি।
সাম্রাজ্যবাদবিরােধী ওই আন্দোলনের নােঙর ছিল দু’টি, একটি হচ্ছে মাতৃভূমি অপরটি মাতৃভাষা। দুটি বােধ যে আলাদা ভাবে ছিল তাও নয়। মিশে গিয়েছিল। অত্যন্ত কার্যকর ভাবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষার প্রতি ভালােবাসাকে, বলা যায় ধারণা দুটিকেই, তিনি তার লেখার মধ্য দিয়ে শক্তিশালী করে তুলেছিলেন।রবীন্দ্রনাথ এসে ভালােবাসা ও ধারণা উভয়কেই আরাে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।
বঙ্গভঙ্গবিরােধী আন্দোলনের একেবারে সূচনাতে, রাখীবন্ধনের উৎসব উপক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে-গানটি লিখেছেন সেটি আমাদের অনেকেরই পরিচিত; কিন্তু তবু ফিরে দেখার জন্য স্মরণযােগ্য। গানটি শুরু এহরকমের,
বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল।
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান
বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান।
এ পর্যন্ত আছে বাংলার প্রকৃতির বর্ণনা, যে-প্রকৃতি সকল বাঙালীরই মমতার বস্তু। তারপরেই প্রকৃতিকে পেছনে রেখে মানুষ চলে আসছে, বলা হচ্ছে বাঙালীর কথা কেবল যেমধ্যবিত্ত বাঙালী, রামানন্দের সেই হিন্দু বাঙালী তা নয়, সকল বাঙালীই এখানে উপস্থিত,
বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক সত্য হউক ,
সত্য হউক হে ভগবান
আর আসছে ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা-
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বােন,
এক হউক এক হউক,
এক হউক হে ভগবান
ভগবানের কথা এসেছে, কিন্তু এই ভগবানের তেমন কোনাে সাম্প্রদায়িক অনুষঙ্গ নেই, এটি অনেকটা বাংলা ভাষার ভেতর থেকেই বের হয়ে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের এই গান জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দেমাতরম’-এর তুলনায় সে-জনপ্রিয়তা অকিঞ্চিতকর। বঙ্কিম তার গানটি লেখেন ১৮৭৬ সালে, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের গানের ২৯ বছর আগে। ‘বন্দেমাতরম’ প্রচার পায় ছয় বছর পরে, ১৮৮৩ তে, যখন সেটি আনন্দমঠ উপন্যাসের অংশ হয়ে যায়। একেবারে অনিবার্য অংশ।
বঙ্কিমচন্দ্র অল্পসল্প কবিতা লিখেছেন, তাঁর গদ্য অনেকক্ষেত্রেই ছন্দবিহীন কবিতার মতােই, তার ভেতরে যে একজন রােমান্টিক কবি ছিলেন তাঁর অতিশয় উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে এই গানটির ভেতর। এটি একটি অসাধারণ সৃষ্টি। কবিতা হিসাবে এটি স্মরণীয় হতে পারতাে, সে যােগ্যতা এর রয়েছে। কিন্তু কেবল নান্দনিক আকর্ষণের দরুননয় তার সঙ্গে রাজনৈতিক আবেদন যুক্ত হওয়ায়, এবং সেই কারণে প্রভাবশালী হওয়ার ফলে রচনাটি অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। বাংলার ইতিহাসে অপর কোনাে গান এতটা রাজনৈতিক তাৎপর্যমণ্ডিত হয় নি। বলাবাহুল্য ওই তাৎপর্যের মধ্যে প্রচণ্ড বিতর্কও অন্তর্ভুক্ত। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এই গান প্রবল উদ্দীপনা তৈরি করেছে; মুসলমানরা এই গানের প্রতি আগাগােড়া বিরূপ ছিল; শাসক ইংরেজ এর ধ্বনি শুনলে ক্ষিপ্ত হতাে। এই তিন ধরনের প্রতিক্রিয়ার উপাদান ওই গানে পরিপূর্ণরূপে উপস্থিত ছিল।
একটি ঘটনা বেশ কৌতূহলােদ্দীপক, কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। সেটা হলাে স্বদেশী আন্দোলনে ‘জয় বাংলা’ ধ্বনির ব্যবহার। আন্দোলনের সময়ে ‘সােনার বাঙ্গালা’ নামে কয়েকটি গােপনইস্তেহারের প্রকাশ ও প্রচার ঘটেছিল,এবং তাদের একটিতে হিন্দুমুসলমান সবাইকে ডাক দেওয়া হয়েছিল ঐক্য গড়ে তুলবার।১৬ এটি ১৯০৬ সালের ঘটনা, কয়েক যুগ পরে দেশবিভাগের ভয়ঙ্কর কাণ্ডকারখানা এবং পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন আন্দোলন পার হয়ে ১৯৭০ এ ইহজাগতিক ও ধর্মনিরপেক্ষ ‘জয় বাংলা’ ধ্বনি আবার উঠেছে, একাত্তরে তা রণধ্বনিতে পরিণত হয়েছে; কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের কালে আন্দোলনের ভেতর থেকেই বের হয়ে এসেও ‘জয় বাংলা’ ধ্বনি টিকতে পারে নি, অন্যদুটি ধ্বনির নিচে চাপা পড়ে গেছে, যাদের একটি হলাে ‘বন্দেমাতরম’ অন্যটি ‘আল্লাহু আকবর’। অল্প সময়ের ভেতরই দুটি ধ্বনি পরস্পরের শত্রুপক্ষে পরিণত হয়েছে।
এখানে স্মরণ করা প্রাসঙ্গিক যে বন্দেমারমকে নিয়ে সমস্যার ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র। অবহিত ও সচেতন ছিলেন, যে জন্য আজাদ হিন্দু ফৌজ-এর মার্চ সঙ্গীত হিসাবে তিনি ওই সঙ্গীতকে ব্যবহার করতে সম্মত হন নি, ‘কদম কদমবাড়ায়ে যা’ (অনেকটা নজরুলের চল্ চল্ চল্-এর মতাে) নামে নতুন একটি গান তৈরি করিয়ে নিয়েছেন। হিন্দু, মুসলমান ও শিখদের ভিন্ন সম্ভাষণরীতির কোনােটিকেই গ্রহণ না করে তিনি ‘জয় হিন্দ’ সম্ভাষণ চালু করেছিলেন। জয় হিন্দের ওই হিন্দু, কেবল হিন্দুর নয়, সকল ভারতবাসীর, সেই অর্থে যে অর্থেদার্শনিক হেগেল, কার্ল মার্কসসহ ইউরােপীয়রা ভারতকে বলেছেন হিন্দুস্থান। গ্রীকরা হিন্দু বলতে সিন্ধুনদী এলাকার বাসিন্দাদের বােঝাতে, বিশেষ কোনাে সম্প্রদায়কে নয়।
মাতৃভক্তি বাংলা সংস্কৃতিতে গভীরভাবে প্রােথিত। দেশকে মাতা হিসাবে দেখাও। প্রতিষ্ঠিত অভ্যাস। কিন্তু অসুবিধা ঘটে তখনই মাতা যখন প্রতিমায় পরিণত হন। বঙ্গভঙ্গবিরােধী আন্দোলনের সময় একটি ছবি বিশেষভাবে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই ছবি স্বদেশী পতাকাতে ব্যবহৃত হতাে। ‘বঙ্গমাতা’ নাম দিয়ে ছবিটি এঁকেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯০২ সালে; ১৯০৫ এ এটির নাম দাঁড়ায় ভারতমাতা। এই ছবিতে মাতৃভূমিকে বাঙালী নারী হিসাবে আঁকা হয়েছে, কিন্তু এই নারী এখানে নারী থাকে নি, দেবীর রূপ নিয়েছে, যে-দেবীর চারটি হাত, যার চার হাতে ধরা রয়েছে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও ধর্ম।১৭ বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই ছবি মুসলিম মধ্যবিত্তকে প্রীত করে নি। এ দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদের সাম্প্রদায়িক রূপগ্রহণের পেছনকার কারণ হচ্ছে শ্রেণী। হিন্দু মধ্যবিত্ত জাতি বলতে নিজেদের সম্প্রদায়কেই বােঝাতে শুরু করেছিল, সেখানে মুসলমানের জন্য স্থানসংকুলান হবে এমন সম্ভাবনা দেখা যায় নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই জাতীয়তাবাদী চেতনা আত্মপ্রকাশ করা শুরু হয়েছে, বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় হলাে সমিতি ও মেলার প্রতিষ্ঠা। এই ব্যাপারে নবগােপাল মিত্র (১৮৪০-৯৪) এতােটাই নিবেদিত প্রাণ ছিলেন যে, তাকে বলা হতাে ন্যাশনাল মিত্র। তিনি প্রথমে চৈত্র মেলার প্রবর্তন করেন, পরে তা জাতীয় মেলার নাম নেয়; ওই দুই নামে যে উদারতা ছিল তা স্বভাবতই নষ্ট হয়ে যায় জাতীয় মেলার তৃতীয় বছরে, ১৮৬৭ সালে মেলা যখন পরিণত হয় হিন্দু মেলাতে। নবগােপাল মিত্রের অনুপ্রেরণাদানকারীদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-৯৯)। রাজনারায়ণের প্রভাব ছিল বিস্তৃত ও গভীর। অনেকদিন তিনি শিক্ষকতা করেছেন; তিনি লিখতেন, বক্তৃতা করতেন, সংগঠন গড়েছেন, বহুজনকে উদ্দীপ্ত করেছেন দেশপ্রেমিক কাজে। তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ওপরও তার প্রভাব পড়েছিল বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতাে রাজনারায়ণকেও ঋষি আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।
রাজনারায়ণ অনেক দিক দিয়েই উদার ছিলেন; ছাত্রজীবনে তিনি ইয়ং বেঙ্গলের ইহজাগতিক চিন্তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, পরে ব্রাহ্ম ধর্মগ্রহণ করেছেন, নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্যবিদ্যালয় খুলেছেন, বয়স্ক কৃষক-শ্রমিকদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করার প্রয়ােজনীয়তাকে বিবেচনায় রেখে নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন, বাঙালীর বিলেত যাওয়া বিষয়ে তার আপত্তি ছিল না। সমাজ থেকে অশিক্ষা-কুশিক্ষা দূর করবার ব্যাপারে তার আগ্রহ ও ব্যস্ততার কোনাে অভাব ছিল না। সেকালে সুরাপান একটি বড়রকমের ব্যাধি ছিল, রাজনারায়ণ তাই সুরাপান নিবারণী সভা গড়েছেন। তৎপরতার দিক থেকে তার উদ্যেগে গড়ে-ওঠা ‘সঞ্জীবনী সভা’কে বলা যায় সুপ্ত রাজনৈতিক সমিতি। তার জাতীয় গৌরব সঞ্জীবণী সভা’র সব কাজকর্ম চলতাে বাংলাভাষায়। এবং কেউ ভুল করে ইংরেজী ব্যবহার করলে তাকে বাকপ্রতি এক পয়সা হারে জরিমানা করা হতাে; একপয়সা তখন অনেক পয়সা, ভাষার প্রতি ভালােবাসা তাে ছিলই, ছিল এই বােধও যে পৃথিবীর কোনাে জাতিই নিজেদের মধ্যে যােগাযােগের জন্য বিদেশী ভাষা ব্যবহার করে না।

কিন্তু শ্ৰেণীও তাে ছিল; যার বাইরে যাবার কথা তিনি ভাবেন নি, যে জন্য তাঁর কাজের সীমা ছিল হিন্দু মধ্যবিত্তের ভেতরেই নির্দিষ্ট। সমাজের জন্য সংস্কার ঠিক আছে, কিন্তু মৌলিক পরিবর্তন নয়। শ্রেণীবিভাজন কেন রক্ষা করতে হবে এ প্রশ্নে তার পরিষ্কার বক্তব্য ছিল,
“the world is not yet prepared for practical adoption of levellers and socialists.”
শ্রেণীতে আবদ্ধ থাকার দরুন তাঁর দেশপ্রেমিক উদারনীতি প্রতিবেশী মুসলমান সম্প্রদায়কে সঙ্গে নেবার কথা ভাবতে পারে নি। ব্যাপার অবশ্য আরাে ছিল। ব্রাহ্ম হলেও তার স্থির বিশ্বাস ছিল হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বে এবং তিনি ধারণা করতেন যে বিভিন্ন জনগােষ্ঠীতে বিভক্ত ভারতবর্ষের জন্য ঐক্যের প্রধান ভিত্তি হবে হিন্দুধর্ম। আশা রাখতেন বাঙালী, পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, রাজপুত, মারাঠী, মাদ্রাজী নিয়ে একটি ভারতীয় জাতি তৈরী হবে। বৃদ্ধ হিন্দুর আশা বইতে তিনি মহাহিন্দু সমিতি নামে সংগঠন গড়বার প্রস্তাবও করেছেন, যে-সংগঠনে মুসলমানরা অন্তর্ভুক্ত হবে না; এবং বন্দেমাতরম্ হবে যার জাতীয় সঙ্গীত।১৮
রাজনারায়ণ যে ভাবে ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে বলে আশা করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র ততটা করতে পারেন নি। হয়তাে দুই কারণে, প্রথমত তিনি কিছুটা পরবর্তী, রাজনারায়ণের ছাত্র-স্থানীয়; দ্বিতীয়ত, তার বাস্তবজ্ঞান ছিল প্রখর। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রও নিজেকে একই সঙ্গে বাঙালী ও ভারতীয় বলে মনে করতেন, এবং এই দু’য়ের ভেতর যে কোনাে বিরােধ রয়েছে এমনটা ভাবতেন না। কিন্তু বিরােধ না থাক, পার্থক্য তাে ছিলই; এবং বিরােধও ছিল আসলে, যেটা পরে স্পষ্ট হয়েছে।
নিজেদেরকে ভারতীয় হিসাবে দেখাটাতে তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। কেননা ভারত তখন একটি সাম্রাজ্যে পরিণত; ইংরেজরা তাদের শাসন-প্রশাসন, যােগাযোেগ ব্যবস্থা, আইন, শিক্ষা, অর্থনীতি বহু কিছুর সাহায্যেই ভারতবর্ষকে এক করে ফেলেছে। ভারতবাসী তখন ওই অখণ্ড রাষ্ট্রের নাগরিক। তারা যখন স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করছে, কাজটা তখনও ভারতবর্ষীয় হিসাবেই করতে হচ্ছে। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর দৈনিকের নাম রেখেছেন দি বেঙ্গলী; কিন্তু তার আধা-রাজনৈতিক সংগঠনের নাম ছিল ইন্ডিয়ান এসােসিয়েশন। এটা তাৎপর্যহীন নয় যে অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ আই সি এস হিউম যখন তৎপর হয়ে সুরেন্দ্রনাথের উদ্যোগের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নিয়ে নতুন সংগঠন গড়েন তখন তার নাম দেন ইন্ডিয়ান কংগ্রেস নয়, বরঞ্চ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস; ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারণাটা এভাবেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
বাঙালীর পক্ষে ভারতীয় বলে পরিচয় দেওয়ার একটি মনস্তাত্ত্বিক যৌক্তিকতাও ছিল বৈকি। বাংলা ছােট, ভারত অনেক বড় এবং প্রাচীন, সেই বিরাটত্ব ও প্রাচীনত্বেরউত্তরাধিকারী হিসাবে নিজেকে গণ্য করতে পারাটা অবশ্যই ছিল গৌরবজনক; ওই বিস্তৃতিতে গিয়ে বাঙালী বলতে পারতাে যে, ঘটনাক্রমে সেপরাধীন বটে, কিন্তু মােটেই খাটোনয়; ইংল্যান্ড যেখানে একটি দ্বীপমাত্র, ভারত সেখানে হচ্ছে মহাদেশ; ইংল্যান্ডের সভ্যতা গতকালের, ভারতীয় সভ্যতা গ্রীকদের চেয়েও পুরাতন। এ বঙ্কিমচন্দ্র মনেপ্রাণে বাঙালী ছিলেন। তার পত্রিকার নাম বঙ্গদর্শন; বাঙালীর ভাষা, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব নিয়ে তিনি যতটা ভেবেছেন তার কালে কেউই অতটা ভাবেন নি, তাঁর অবিস্মরণীয় সেই বন্দেমাতরম্ গান বঙ্গভূমিকে কেন্দ্র করেই রচিত। মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষা এই উভয় বােধকেই তিনি সজীব ও উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন। এর আগে বাংলাভাষাকে নানা নামে ডাকা হতাে, সপ্তদশ শতাব্দীর কবি আবদুল হাকিম বঙ্গবাণী’কে দেশী ভাষা বলেছেন, অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর কবি রামনিধি গুপ্ত বলছেন ‘স্বদেশীয়’ ভাষার কথা, যানা পেলে আশা পুরে না, যেমন বৃষ্টির জল ছাড়া তৃষ্ণা ঘোঁচেনা চাতকের; রামমােহন তার বাংলা ব্যাকরণের নাম দিয়েছেন গৌড়ীয় ব্যাকরণ। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাকে সামনে নিয়ে এলেন বাংলা ভাষা হিসাবেই। কিন্তু অতিবড় মাপের এই বাঙালী আবার। সােৎসাহী ভারতবর্ষীও ছিলেন।
প্রশ্ন হলাে বঙ্গের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযােগের গ্রন্থটি কী? ভৌগােলিক যােগ আছে, কিন্তু সেটা তেমন কার্যকর নয়, প্রথমত ভারতবর্ষ প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে ভরপুর, সেখানে ঐক্য যেমন রয়েছে, পার্থক্যও সেই তুলনায় নেহায়েৎকম নেই; দ্বিতীয়ত,অতীতে বঙ্গকে ভারতবর্যের অন্য অঞ্চল বিশেষ সমাদর করে নি, নানাভাবে গালমন্দ করেছে, বিজেতারা সবাই এসেছে উত্তর ভারত থেকে, এসে জয় করেছে এবং পীড়ন চালিয়েছে। প্রকৃতি নয়, ঐক্যের জন্য অন্যভিত্তির প্রয়ােজন ছিল, সেটি কী হতে পারে তা নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ভেবেছেন। রাজনারায়ণের, বা পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক নেতা বালগঙ্গাধর তিলকের মতাে হিন্দু ধর্মের ভিত্তিতে ঐক্য বাস্তবসম্মত নয় বলেই তার মনে হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। যে জন্য বঙ্গদর্শনের পত্র-‘সূচনা’তে তিনি ধর্মবাদ দিয়ে ভাষার সাহায্যে ঐক্যেরকথা বলেছেন। ঐক্যের আবশ্যকতা বিষয়ে তার মন্তব্য, “ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, এক পরামর্শী, একোদ্যোগী না হইলে ভারতবর্ষের উন্নতি নাই।” এখানে স্বীকার করা হচ্ছে যে, ভারতবর্ষ এক জাতির দেশ নয়, এদেশে নানা জাতির বসবাস। এই যে বিভিন্ন জাতীয়তা এর ভিত্তি কী? স্পষ্টতই ভিত্তি হচ্ছে ভাষা।
ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের এই বাস্তবিকতার মুখােমুখি সেকালের অনেক মনীষীকেই হতে হয়েছে, কিন্তু বাস্তবতাকে স্বীকার করে নেওয়া হয় নি; নিলে কিছু কিছু মৌলিক সমস্যার সমাধান হতাে, দ্বিজাতি তত্ত্বের উদ্ভব ঘটতাে না, দেশভাগ ঠেকানাে যেতাে, এবং এখনও যে উপমহাদেশে জাতিগত সমস্যার মীমাংসা হয় নি, নানা রকমের সংঘর্ষ ঘটছে তেমনটা ঘটতাে না; ভারতবর্ষে হয়তাে ইউরােপের মতাে নানা জাতি সমাবেশে একটি মহাদেশে পরিণত হয়ে নিজেদের সম্মিলিত একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে।
সে যাই হােক, বঙ্কিম ভাবছিলেন ভাষার সাহায্যেই বুঝি বিভিন্ন জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব। আগের কাল হলেওই দায়িত্বটি সংস্কৃত ভাষাকে দেওয়া যেতাে। কিন্তু ইংরেজ শাসনের কালে সংস্কৃত আর জীবিত নেই। পত্র-সূচনাতে তাই বলা হচ্ছে,
“এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্র, কৈলঙ্গী, পাঞ্জাবী ইহাদের মধ্যে সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজী ভাষা। এইরঞ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে।” পরবর্তীকালে প্রবন্ধটির এই উক্তির সঙ্গে এই পাদটীকাটি যােগ করা হয়েছে, “এখানে যাহা কথিত হইয়াছে, কংগ্রেস তাহা সিদ্ধ করিতেছেন।” স্মরণীয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র কংগ্রেসের সাংগঠনিক কার্যক্রমের প্রতি মােটেই সমর্থন জানাতে পারেন নি, কংগ্রেসের জনবিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করে, কিন্তু ঐক্যপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কংগ্রেস কাজ করছে বলে তিনি মনে করেছেন।
ঔপনিবেশিক বক্রাঘাতগুলাে বড়ই নির্মম। যে পত্র-সূচনাতে বাঙালী সমাজে ইংরেজী ক্রমবর্ধমান চর্চা দেখে ঠাট্টা করে বলা হয়েছে, এমন ভরসা করা যেতে পারে যে অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরেজীতে পঠিত হবে, তাতেই বলতে হচ্ছে যে ভারতীয় ঐক্যকে ইংরেজী ভাষার রঙ্কুতেই বাঁধতে হবে। ভারতবর্ষ যে এক জাতির দেশ নয়, তার পরােক্ষ উল্লেখ রবীন্দ্রনাথের লেখাতেও নানা জায়গায় আমরা পাবাে, একটি মহাজাতি গঠনের কথা তিনি কখনাে কখনাে উল্লেখ করেছেন ঠিকই, কিন্তু মহাজাতির তুলনায় বহুজাতির ব্যাপারটাই ছিল আসল বাস্তবতা। তবে রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও বহুজাতিক ভারতবর্ষকে মেনে নেওয়া সম্ভব হয় নি, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদে তিনিও আস্থাশীল ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনায় অধিকতর বাঙালী, এইদিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের ভেতর যে সাম্প্রদায়িকতা দেখা গেছে, রবীন্দ্রনাথ তা থেকে মুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি আবার ভারতবর্ষীয়দের ঐক্যও ঐকান্তিকভাবেই চাইতেন। প্রশ্ন হলাে এই ঐক্য আসবে কি করে? ভিত্তিটা কি? ভিত্তিটা হতে পারতাে রাজনৈতিক, অর্থাৎ ব্রিটিশকে ভারতছাড়া করবার আন্দোলন, কিন্তু ঐক্যের মতাে বড় জিনিসকে রাজনীতির মতাে ছােট জিনিসের দাসকরতে তিনি সম্মত ছিলেন না; তাঁর মতে মিলনটা হবে ‘মনুষ্যত্বের’ – রাজনীতির নয়। ঐক্য ঘটবে স্বার্থবুদ্ধির পথ দিয়ে নয়, ধৰ্ম্মবুদ্ধির পথ দিয়ে।১৯ মনুষ্যত্ব এবং ধর্মবুদ্ধি ঠিকই আছে, তারা গুরুত্বপূর্ণও বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের সকল মানুষকে মেলাবার ব্যাপারে তারা কতটা নির্ভরযােগ্য সে নিয়ে সন্দেহ করাটা অন্যায় নয়, বিশেষত ঐক্য গড়বার চেষ্টা যেখানে নানাভাবে ব্যাহতই যে কেবল হয়েছে নয়, ঐক্যপ্রচেষ্টা নিজেই যেখানে অনৈক্যেরও কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
উল্লেখপঞ্জীঃ
- ১. উদ্ধৃত, Rameschandra Majumdar, History of the Freedom Movement in India, vol II, Calcutta, 1963, p 152 মূল ইংরেজীতে, “The Bengalee inspires the Indian Nationalist Movement, … Indeed I have not taen away with me a very favourable impression of Bengal politics. There are no good political leaders there. They have excellent speakers and eloquent writers, but none of their prominent men seen to have that heaven-given capacity to lead. They are magnificent agitators (1 use the word in no uncomplimentary sense). They can prepare men to be lded, but no shepherd there steps forward to pipe the flocks to the green pasture.
- “But Begnal is perhaps doing better than political agaitation. It is translating nationalism into religion, into music and poetry, into painting and 1 literature.
- “From Bengal gush innumerable freshets of religion all flowing to revive and invigorate the Nationalist spirit.”
- ২. আমির উদ্দীন আহমদ, ‘মুসলমান শিক্ষা সমিতি’, বাসনা, ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩১৬। উদ্ধৃত মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সঙ্কলিত, সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত ১৯০১-১৯৩০; ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ২৫৯
- ৩. নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনােদিনী, ‘আমাদের কাজ’, সওগাত, ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৬৬। ঐ, পৃ. ১৬২।
- ৪. সরােজ মুখােপাধ্যায়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, বেন ১৯৮৬, পৃ.৪২৭
- ৫. Rameshchandra Majumdar, প্রগুক্ত, vol III, p 570 অন্য একজনের লেখা থেকে তিনি উদ্ধৃতি দিচ্ছেন, যেখানে বলা হয়েছে, “Not only did the communists support the demand for Pakistan but went much further by saying that every linguistic group in India had a distinct nationality and was therefore entitled, as they claimed was case in the USSR, to the right to secede.”
- ৬. উদ্ধৃত, সুনীতি কুমার ঘােষ, বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি-রাজনীতি, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ২২০
- ৭. উদ্ধৃত, নাজমা জেসমিন চৌধুরী, বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ৪১
- ৮. আহমদ শরীফ, ‘উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে জাতিদ্বেষণা’, ইতিহাসও সমাজচেতনা, ঢাকা ২০০১, পৃ. ২৯৯
- ৯. উদ্ধৃত, যােগেশচন্দ্র বাগল, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৩
- ১০. দেখুন, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ‘ঔপনিবেশিক ভারতে ইতিহাসের গতিবিধি’, নতুন দিগন্ত, দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০৪, পৃ. ৪৯
- ১১. Sumit Sarker, প্রাগুক্ত পৃ.৩৩। ইংরেজীতে, “to attempt social reform, ndustrial expansion, the moral improvement of the race without aiming first and foremost at political reform, is the very height of ignorance and futility”
- ১২. ঐ, পৃ. ৩১৬।
- ১৩. Maulana Abul Kalam Azad, India Wins Freedom, Madras, 1988, পৃ. ৫
- ১8. The English Works of Raja Rammohum Roy, Allahabad, 1906, p. 929
- ১৫. ঐ, পৃ. ৯৩০
- ১৬. উদ্ধৃত, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, একটি করে ইস্তোহারের জন্যে, পরিচয়, ঐ, পৃ. ২২৭
- ১৭. (ক) মৃণাল ঘােষ, স্বদেশী আন্দোলন : শিল্পকলার চর্চা’, ঐ পৃ. ২৭৭-৭৮।
- ১৮. এ বিষয়ে আলােচনার জন্য দেখুন, জাহেদা আহমদ, ‘হিন্দু জাতীয়তার ক্রমবিকাশ’, নতুন দিগন্ত প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০৩, পৃ. ৭১-৭৬
- ১৯, ‘পূর্ব ও পশ্চিম’, রর, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ২৬৬, ৬১১
‘নবজাগরণ’ অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপ্লিকেশনটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।
![]()
‘নবজাগরণ’ এর টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

 নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা
নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা